বিষয়ক্রম
সূচনা
জীবন সমস্যা
প্রথম পরিচ্ছেদ
জীববিজ্ঞানের শিক্ষা
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
মনোবিজ্ঞানের শিক্ষা
ফ্রয়েডীয় মতবাদ
ম্যাকডুগাল
এ্যাডলার
জুঙ
তৃতীয় পরিচ্ছেদ
রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষা
ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ
সামাজিক চুক্তিবাদ
ধনতন্র
চতুর্থ পরিচ্ছেদ
সমষ্টিকেন্দ্রিক মতবাদ
ইয়াহুদী ধর্ম
প্রাথমিক প্লেটো
মাজদাক
কার্ল মার্কস
মার্কসবাদ ও বস্তুবাদী সমাজতন্র
টলস্টয় বা নব্য খ্রিষ্টবাদ
গান্ধীবাদ
পঞ্চম পরিচ্ছেদ
মানুষের পরিচয়
পূর্ণাঙ্গ দর্শন ও ইসলাম
ইসলামের অবলম্বন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধ
আল্লাহ্র অস্তিত্বের প্রশ্ন
আল্লাহ্র সার্বভৌমত্তের সঙ্গে মানুষের অধিকারের সমন্বয়
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
ইসলামী নীতির রুপায়ণ-ব্যক্তিগত জীবনে, সমাজে ও রাষ্ট্রে ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যক্তি,সমাজ ও রাষ্ট্র
ইসলামী নীতির প্রয়োগ-ব্যক্তিগত জীবনেঃসালাত
সিয়াম ও রমযানের তাৎপর্য
হজ্জ ও কুরবানী
যাকাত
জিহাদ
সামাজিক জীবনে নর-নারী সম্পর্কঃ ইসলামি সমাজে নারীর মর্যাদা ও অধিকার
ইসলামের দৃষ্টিতে সুদপ্রথা
সাম্যবাদমূলক দায়ভাগ প্রথার প্রবর্তন
ইসলামী নীতির রুপায়ণ-রাষ্ট্রীয় জীবনেঃ মদীনার সনদের সারমর্ম
পুঁজি সৃষ্টির বিরুদ্ধে অর্ডিন্যান্স
ইসলামী গণতন্ত্রের ফলিত রুপ
খলীফার দায়িত্ব
ইসলাম ও ডিক্টেটরশিপ
সংখ্যালঘু সমস্যা
খলীফার নিয়োগ
অর্থনীতি
উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা
শাসন ও বিচার বিভাগ
সপ্তম পরিচ্ছেদ
ইসলামী রাষ্ট্রের ভাঙ্গনের কারণ
অষ্টম পরিচ্ছেদ
ইসলামী সমাজের ভূমিনীতি ও তার প্রয়োগ
ইসলামী জীবন দর্শন ও তার ফলিত রূপ
ইসলামী সমাজে ভোগদখলের অধিকার
তিনটি শর্ত রয়েছে
ভোগ-দখলের জমির পরিমাণ
জমি থেকে ফসল উৎপাদনের নীতি
উৎপাদনের পদ্ধতি
ইসলামী সমাজের ভূমিনীতি
আধুনিক যুগে ইসলামী নীতির প্রয়োগ
নবম পরিচ্ছেদ
ইসলামের বিকাশ
দশম পরিচ্ছেদ
অনাগত বিশ্বসংস্থা ও ইসলাম
ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ
গ্রন্থপঞ্জি
পরিশিষ্ট
লেখকের কৈফিয়ত
আমরা বহুকাল যাবত অবরোহ পদ্ধতিতে (Deductive Method) ইসলামকে পাঠ করে এসেছি। এতে আমাদের জীবনের প্রত্যয়শীলতা বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়েছে; তবে সে প্রত্যয় বা faith-এর মূলে কোন যুক্তির অবতারণা করতে পারেনি। তাই এ দুনিয়ার অমুসলিম বা বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তাধারায় অভ্যস্ত লোকের নিকট আমাদের এ প্রত্যয়শীলতা অন্ধবিশ্বাসের আকারেই রয়ে গেছে। তার ফলে ইসলাম যে বিশ্বজনীন ধর্ম বা মানব প্রকৃতির ধর্ম সে দিকটা রয়ে গেছে অস্পষ্ট। মানবজীবনকে একটা অতিশয় সত্য বিশয় বলে গ্রহণ করে যদি তারই ভিত্তিতে প্রকৃত সত্য লাভ করার চেষ্টা করা যায়, তা’হলে মানব-জীবনের প্রকৃত রূপ এবং তার সন্তোষ বিধানের জন্য যে বিষয়কে অবশ্য সত্য বলে গ্রহণ করতে হবে, তার আলোচনা করা প্রয়োজন। এমন একজন ধর্ম-বহির্ভূত মানুষ যার কোন মতবাদে বিশ্বাস নেই এবং যিনি জীবনের সন্তোষের জন্য যে কোন মতবাদই গ্রহণ করতে প্রস্তুত, তারই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এ পুস্তকের আলোচনা আরম্ভ হয়েছে। এজন্য তার নামকরণ করা হয়েছে, “জীবন সমস্যার সমাধানে ইসলাম”। এতে জীবনের নানাবিধ সমস্যার সমাধানে ইসলাম কিভাবে সার্থক সে বিষয়টাই মানব সাধারনের নিকট তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এজন্য কোন কোন বিষয় সাধারণ পাঠকের নিকট বিসদৃশ বলে প্রতিভাত হতে পারে। ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রত্যাদেশ বা ওহী খাস আল্লাহ্র এক দান। তা নবী মুরসালদের কাছে আল্লাহ ফেরেশতার মাধ্যমে নাযিল করেন। অথচ হিব্রুধর্ম গোষ্ঠী যথা-ইহুদী ও ঈসায়ী ধর্মাবলম্বী মানুষ ব্যতীত অপরাপর ধর্মালম্বী লোকদের নিকট তা গ্রহণযোগ্য নয়। একজন nonconformist- এর নিকট সে প্রত্যাদেশকে বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় পেশ করতে হলে তার মধ্যে নবী মুরসালদের সক্রিয়তার দিকটা প্রকাশ করা প্রয়োজনীয় গতিকে তাকে বৈজ্ঞানিক আকারেই প্রকাশ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে, বিজ্ঞান সতত পরিবর্তনশীল। কাজেই আজকের জগতে যা বৈজ্ঞানিক সত্য বলে স্বীকৃত, পরবর্তী যুগে তা স্বীকৃত নাও হতে পারে। তার উত্তরে বলা যায়, জীবনকে যদি সঠিকভাবে পরিচয় করার বাসনা কারো মনে জাগে এবং জ্ঞানের সকল ক্ষেত্র ও পদ্ধতিকে স্বীকার করা হয়, তাহলে স্বজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাদেশ বা ওহী নামক জ্ঞানকে স্বীকার করতেই হবে। কাজেই এক্ষেত্রে লেখক একজন nonconformist- এর দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই বিষয়টার আলোচনা করেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে, কোন মতবাদবিহীন একজন স্বাধীন ও স্বাতন্ত্র্যবাদী লোকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও যদি আলোচনা করা যায়, তাহলেও ওহীকে স্বীকার করতে হবে।
ইসলামকে জগৎ সভ্যতায় পেশ করা হয়েছে প্রশ্নবিহীন অবশ্যগ্রহণীয় এক প্রত্যয় হিসেবে। জীবনের নানাবিধ চাহিদা পরিপূরণে সক্ষম এক মতবাদ হিসেবে উপস্থাপন করার চেষ্টা থেকেই এ পুস্তকে নবুয়াত, রিসালার বা বেলায়েতকে যুক্তিসঙ্গত বিষয় বলে গ্রহণ করা হয়েছে। এ পুস্তকের আলোচ্য বিষয় মানবজীবনের ইসলামী সমাধান- কেবল মুসলিম জীবনের সমাধান নয়, আশা করি এ বিষয়টা বিদগ্ধ পাঠক বিবেচনা করে দেখবেন। -মোহাম্মদ আজরফ
সূচনা
জীবন সমস্যা
মানব-জীবনে কত সমস্যা। জীবন-প্রভাতেই তাতে দেখা দেয় নানা প্রশ্ন। একটুখানি চলাফেরা বা বুদ্ধি-বিবেচনা দেখা দিলেই মানুষ ভাবতে আরম্ভ করে- “আমি কোথা থেকে এলাম? কোথায় আমি যাবো? কেন এখানে এলাম? আমাকে কি এই দুনিয়া ভালবাসে না হিংসা করে?” যখন ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় আকাশ প্লাবিত হয়, তখন ছোট ছোট শিশুরা মনে করে- চাঁদের দেশে বুঝি বা কত সুখ! কত সৌন্দর্য! যখন বাসন্তী সমীরণে গাছের পাতাগুলোর আড়ালে বসে কোকিল বা এ জাতীয় কোন পাখি মধুর সুরে আপ্যায়িত করে, তখন শিশুদের মনে স্বাভাবিকভাবেই কোকিলের পার্শে বসে তার মত গান গাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ পায়। তারা মনে করে- না জানি ওই গাছের ডালে বসে ওই পাখিটা কত আনন্দ উপভোগ করছে! আবার জ্যৈষ্ঠ মাসে যখন আম, জাম ও কাঁঠাল পাকে, তখন সে কোকিল-বধূই যখন অপূর্ব গান গেয়ে রাত্রিকে সরব করে তুলে, তখন পাড়াপড়শিরা তার এ গানকে বলে “বউ কথা কও”- তখন শিশুর মনে এ পাখির প্রতি কত শ্রদ্ধাই না দেখা দেয়। সে মনে করে, বউ অভিমান করে কথা বলছে না বলে তার বরের মনে কি কষ্ট! সেজন্যই বোধ হয় বরের হয়ে পাখিটা বউকে সাধ্য-সাধনা করে বলছে- “বউ কথা কও”। ফাগুন মাসে যখন গাছে গাছে নানা জাতীয় ফুল প্রস্ফুতিত হয়ে চারদিকে সুবাসের বান বইতে থাকে, তখন শিশুর মনে সত্যিই প্রশ্ন দেখা দেয়, এ ফুলগুলো কে ফোটাচ্ছে, তাকে কি দেখা যায়, না সে লুকিয়ে থাকে- পালিয়ে বেড়ায়?
আবার যখন প্রবল ঝড়ে গাছ-গাছালি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে, ঘর-দুয়ার সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তখন সেই শিশুই ভাবতে থাকে, এ আবার কি আপদ! এ কোন দৈত্য-দানব বা জিন দেখা দিল আমাদের সামনে? হটাৎ ভীষণ গর্জন করে আকাশে কি এমন কোন ব্যক্তি রয়েছে, যার গলার স্বরই গর্জনরূপে দেখা দিচ্ছে? বান-বন্যা দেখা দিলে বা ভূমিকম্পের ফলে দেশে হেথায় হোথায় নানা ফাটল দেখা দিলে শিশুরা ভয়ে হকচকিয়ে চায়- এ আবার কোন্ দুশমনের কাজ! কে এসব অনাচার অত্যাচার করে আমাদের দেশের এ সর্বনাশ করেছে অর্থাৎ সোজা কথায় এ দুনিয়া আমাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বা আমাদের ভীষণ শত্রু, এ প্রশ্নটা তাদের মনে দোলা দেয়।
এ সকল প্রশ্নের পূর্বে যে সকল প্রশ্ন তাদের মানসে দেখা দিয়েছিল অর্থাৎ তারা কোথা থেকে এল; আবার কোথায় ফিরে যাবে? কেনই বা এল, আবার কেনই বা আবার ফিরে যাবে, ইত্যাকার প্রশ্ন বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধামাচাপা পড়ে রয়। কৈশোরের প্রারম্ভে নানা বাধাবিপত্তি থাকা সত্ত্বেও এ দুনিয়াটা মানুষের কাছে আলো-ঝলমল রূপেই দেখা দেয়। মনে হয় এ দুনিয়ার সবকিছুই সুন্দর, সবকিছুই চমৎকার। ছেলেবেলায় এ দুনিয়ার যে সব বীভৎস দৃশ্য দেখে ছেলেরা ভয়ে ও বিস্ময়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে,কৈশোরে সেগুলোর এ ভয়ঙ্কর রূপকে অগ্রাহ্য করে কিশোর ও কিশোরী তার আনন্দময় রূপেই মুগ্ধ হয়ে পড়ে। তখন তাদের কাছে ‘সাময়িকভাবে এগিয়ে চলছি” জীবনের মূলমন্ত্র হয়ে পড়ে। এর সঙ্গে অপরের প্রতিযোগিতার প্রবৃত্তি দেখা দিলেও প্রেম, সখ্য, স্নেহ-প্রীতি প্রভৃতি সুকুমার বৃত্তি তাদের মানসকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। যারা একেবারে শৈশব থেকে অপরাধপ্রবণ, তাদের মানসে অপরের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ দেখা দিলেও দলীয় মনোবৃত্তি বা Group mindedness দ্বারা তারা প্রভাবান্বিত হয় এবং দলের সভ্যদের সঙ্গে তাদের নিজেদের ঐক্য অনুভব করে, দলের স্বার্থ রক্ষার্থে নানাবিধ অপকর্ম করতেও প্রস্তুত হয়। এজন্য একালকে ব্যক্তি-স্বার্থহীনতার কাল বলা যেতে পারে। একদিকে যেমন শৈশবের যে সকল আদি প্রশ্ন সম্বন্ধে তাদের মধ্যে উদাসীনতার ভাব পরিলক্ষিত হয় তেমনি ব্যক্তিগত জীবনের গণ্ডি অতিক্রম করে বৃহত্তর গণ্ডির মধ্যে আত্মবিলোপের প্রবৃত্তি তাদের মধ্যে দেখা দেয়। জীবনের নানা ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে লালিত-পালিত হলেও সকল স্তরে কিশোর ও কিশোরীদের মানসে সে একই ভাব প্রবল হয়ে ওঠে।
এ সন্ধিক্ষণেই নারী ও পুরুষের দৈহিক পার্থক্য ক্রমশ প্রকট হয়ে দেখা দিলে একের প্রতি অপরের আকর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে হিংসার ভাবও দেখা দেয়। কোন কোন বিষয়ে পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পেলে কিশোরীদের মানসে একটু হিংসার ভাবও দেখা দেয়। আবার কিশোরদের মানসে মেয়ে ছেলের সে কমনীয়তা- সে পেলবতার প্রতি হিংসার উদ্রেক হয়। ক্রমে উভয়ের জীবনের মধ্যে বিভিন্নতা আরও প্রকট হলে তাদের মধ্যে বিচ্ছিনতার সঙ্গে সঙ্গে একে অপর থেকে শ্রেষ্ঠতর বলে প্রতিপন্ন করার ইচ্ছাও প্রবল হয়ে দেখা দেয়। এভাবে কৈশোরের স্তর পার হয়ে যৌবনের প্রবল জোয়ারের মধ্যে যখন মানুষেরা ভেসে চলে, তখন তাদের মানসে কত সাধ, আহলাদ,কত স্বপ্ন, কত লক্ষ্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তার মধ্যে অর্থের লালসার সঙ্গে সঙ্গে নর অথবা নারীর আসঙ্গ কামনা অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠে। তা থেকেই তাদের জীবনে দেখা দেয় নানাবিধ সমস্যা। অন্ন সমস্যা ও যৌন সমস্যা যেমন মানুষকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে-তেমনি তাদের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ সমস্যাও দেখা দেয়। এ সকল সমস্যাও আবার পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। অন্ন সমস্যার সমাধান করতে হলে বস্ত্র সমস্যার সমাধান করতে হয়। শীত-গ্রীষ্মের অত্যাচার থেকে শরীরকে বাঁচিয়ে রাখতে না পারলে ছুটাছুটি করে মানুষ তার আহারের সংস্থান করতে পারে না। আবার পেটের যোগাড় না হলে মানুষের কাজ করবার শক্তিও থাকে না। প্রয়োজনমত পুষ্টিকর আহার্য ব্যতীত মানুষের শরীর টিকে থাকে না। তাই অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করা মানুষের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য।
কেবলমাত্র অন্ন-বস্ত্রের সমস্যা নয়, যৌন সমস্যাও মানব জীবনে নানাভাবে দেখা দেয়। বৃদ্ধের তরুণী ভার্যা বা তরুণের বৃদ্ধা ভার্যা হলে যেমন যৌন সমস্যা দেখা দিতে পারে, অসমর্থ পুরুষের সমর্থ স্ত্রী অথবা সমর্থ স্ত্রী অসমর্থ স্বামী থাকলেও যৌন সমস্যা দেখা দিতে পারে। এসব ব্যতীত জীবন্ত ধর্ম, সমাজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানও প্রকৃত প্রেমিকার মিলনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারে। এ সকল সমস্যা ব্যতীত মানুষের মধ্যে যে বৈরীভাব রয়েছে, তার ফলে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বা জাতিতে জাতিতে প্রায় সব সময়ই নানাবিধ স্বার্থের দ্বন্দ্ব রয়েছে, যার ফলে তাদের ব্যক্তিগত জীবনে বা শ্রেণীগত জীবনেও নানাবিধ দ্বন্দ্ব-কলহ প্রায় দেখা দেয়। যৌন সমস্যাও অন্ন সমস্যার ওপর নির্ভরশীল। প্রেমিক-প্রেমিকার আসক্তি যতই প্রবল হোক না কেন, উভয়ের মধ্যে কোনও একজন উপার্জনক্ষম না হলে এবং সংসারের ঠেলা সামলাতে না পারলে, কিছুদিন পরেই তাদের প্রেমের হাটে ভাঙ্গন শুরু হয়। কোন কোন দেশের হাজার হাজার পতিতার জীবন অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, অন্ন সমস্যার সমাধানে অসমর্থ হয়েই তারা এ বৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। অন্যদিকে যৌন-জীবনের উচ্ছৃঙ্খলতা যে রোজগারের পক্ষে কত বড় প্রতিবন্ধক তার প্রমাণ ঘটে সব জায়গায়ই পাওয়া যায়। একজন লোক হয়ত উপার্জন করতে খুবই সক্ষম, কিন্তু পূর্ণ বয়সে যৌন পরিতৃপ্তির অভাবে সে হয়ত বিকৃত রুচির পরিচয় দিতে পারে এবং সেই বিকৃত পথেই হয়ত তার জীবনের সমস্ত আয়-ব্যয় করতে পারে! কাজেই তার জীবনের যৌন সমস্যার সমাধান না হলে তার পক্ষে অন্ন সমস্যার করাও অসম্ভব।
অন্নের জন্য, বস্ত্রের জন্য বা যৌন-পরিতৃপ্তির জন্য নানা কারণেই মানব জীবনে যুদ্ধ বাধে। সে যুদ্ধ যখন ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে হয়,তখন তার জন্য গোটা সমাজের মনে কোন আশঙ্কা দেখা দেয় না। সেই যুদ্ধ যদি দুই দেশের মধ্যে প্রবলভাবে বাধে, তা হলে দুই দেশেরই নরনারীর জীবনে নানাবিধ সমস্যা উগ্রমূর্তি হয়ে দেখা দেয়। যুদ্ধের প্রয়োজন সমর্থ বয়সের পুরুষেরা চাষ-আবাদ ছেড়ে কামান-বন্দুক-গোলাগুলি নিয়ে বেরিয়ে পড়লে দেশের চাহিদার পক্ষে উপযুক্ত শস্য উৎপাদন করা সম্ভবপর হয় না। সমাজ-জীবনেও না বিশৃঙ্খলা ও বৈকল্য প্রকাশ পায়। যুদ্ধের সঙ্গে অন্ন সমস্যা ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। কোন দেশ যদি তার প্রয়োজনে উপযুক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন করতে অপারগ হয়, তাহলে অন্য দেশের খাদ্যসামগ্রীর প্রতি সে আকৃষ্ট হবেই। সে দেশ থেকে তার প্রয়োজনমত খাদ্যদ্রব্য জোর করে ছিনিয়ে আনবার লোভ তার মনে প্রবলভাবে প্রকাশ পাবে। আবার যদি কোন দেশে তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপাদনের ব্যবস্থা থাকে, তাহলে সে উদ্ধুত্ত মাল অন্য দেশে চালান দিয়ে তা থেকে দু’পয়সা লাভ করতে লোভী হতে পারে। এতে বাধা পেলে যে কোন দেশ তেরিয়ে হয়ে সরাসরি হানাহানিতে লিপ্ত হয়।
অন্যান্য সমস্যার সমাধানে যখন মানুষ প্রমত্ত হয়, তখন গোটা সমাজজীবনে এত আলোড়ন হয় যে, যুদ্ধের ব্যাপারে এক হুলস্থুল কাণ্ড দেখা দেয়। সমাজজীবনে নানাভাবে আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়।
এ সকল সমস্যাই সাধারণভাবে মানবজীবনকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। যে সকল দেশে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার লোপ করে দেশের সম্পদকে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্তাধীন করা হয়েছে, সেসব দেশে অন্ন সমস্যা, বস্ত্র সমস্যা বা যৌন সমস্যা পূর্ববর্ণিত আকারে দেখা না দিলেও সেসব সমস্যার এখনও সমাধান হয়নি। সে সকল দেশের রাষ্ট্রে বা রাষ্ট্রের কর্ণধারদের পক্ষে এ সকল সমস্যার সমাধান অত্যন্ত গুরুতর কর্তব্য হয়ে দেখা দেয়। দেশের সকল লোকের পক্ষে উপযুক্ত খাদ্য, পরিধেয়, ও নর-নারীর যৌন ক্ষুধার নিবৃত্তির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করা সম্ভবপর হলেও যৌন সমস্যা বা যুদ্ধ সমস্যার সমাধান তত সহজ হয় না- কারণ সেসব রাষ্ট্রেও পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে সর্বসাধারণ মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নেই। রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য পাত্র বা পাত্রীকে বাধ্য হয়েই তার মনোমত পাত্র বা পাত্রী নির্বাচনের সম্পূর্ণ অধিকার পরিত্যাগ করতে হয়। তার ওপর ব্যক্তিগত জীবনে সকল মানুষের মানসেই অল্পবিস্তর হিংসা রিপু থাকায়- সে সব দেশেও আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য কঠোর হস্তে দুষ্কৃতকারীদের দমন করতে হয়। সেজন্য নানাবিধ পদ্ধতিতে সেসব দৃষ্টান্তকারী লোকদের এ সকল কর্মের মূলে অবস্থিত মানসিকতার বীজ আবিস্কার করা একটা মহাসমস্যা হয়ে দেখা দেয়। অপরদিকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যতীত এ দুনিয়ার অপরাপর যেসব রাষ্ট্র রয়েছে- তাদের সঙ্গে নানাবিধ বিষয় নিয়ে নানাভাবে সংঘর্ষ দেখা দেয়। এমনকি সমাজতান্ত্রিক মতবাদে প্রত্যয়শীল দেশগুলোর মধ্যে যুদ্ধের প্রস্তুতি দেখা দেয়।
এতেই স্পষ্টই প্রমাণিত হয়- মানবজীবন যে পর্যায়েই থাকুক না কেন এবং সমাজ বা রাষ্ট্র যেভাবেই গঠিত হোক না কেন- তাতে যে নানা সমস্যা রয়েছে- সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।
ব্যক্তি-জীবনে আবার এ সকল সমস্যার মধ্যে শৈশবের প্রশ্নগুলো প্রৌঢ় বয়সে পুনরায় অত্যন্ত প্রবলভাবে দেখা দেয়। শৈশবের যে আদি প্রশ্নগুলো- আমি কোথা থেকে এসেছি? আমি আবার কোথায় যাব? আমার সঙ্গে এ পৃথিবীর সম্বন্ধ কিরূপ ইত্যাকার প্রশ্ন মানুষকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। মৃত্যুর পথে মানুষ যতই অগ্রসর হতে থাকে, ততই সে জানতে চায়- সে কোথায় যাচ্ছে- সে আবার কি এ পৃথিবীতে ফিরে আসবে , না সে বিদায়ই তার পক্ষে চিরবিদায়? আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, স্ত্রি-পুত্র কন্যা সকলের নিকট থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে কি সে আবার এ জীবনের মতই টিকে থাকতে পারবে, না তার মাটির দেহ মাটিতেই মিশে যাবে- এ প্রশ্ন নর-নারী-নির্বিশেষে সকল মানুষের মনে দেখা দেয় এবং সেগুলোর মীমাংসার জন্য মানুষ কোথাও বা গুরুজনের, কোথাও বা পীর মুর্শেদ দরবেশের, কোথাও বা ধর্মাবতার, আবার কোথাও বা শেষ বিচারের আশ্রয় নেয়।
তাই স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে- মানবজীবনেই কেন এ সকল প্রশ্ন দেখা দেয়? অন্যান্য পশুপক্ষীর জীবনে তো সেসব প্রশ্ন দেখা দেয় না। দেখা দিলেও তার সমাধানের কোন লক্ষণ তাদের জীবনে পরিলক্ষিত হয় না। এজন্য প্রয়োজন গভীরভাবে মানবজীবনকে অধ্যয়ন করা। মানবজীবনের প্রকৃত সত্তার আলোকে তার জীবনের নানাবিধ সমস্যার সমাধান করতে পারলে মানুষ সুস্থ জীবন যাপনে সমর্থ হতে পারে। অন্যথায় তার জীবনের কোন বিশেষ দিকের ওপর গুরুত্ব আরোপ করার ফলে জীবনের অন্যান্য দিকগুলোতে বিদ্রোহ দেখা দিতে পারে এবং সে বিদ্রোহের ফলে জীবনের ভারসাম্য নষ্ট হওয়া অবশ্যম্ভাবী। মানবজীবনকে নানাভাবে দেখবার সুযোগ রয়েছে। যেমন দেহধারী জীব হিসেবে তাকে জীববিজ্ঞানের দিক থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তার প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করার চেষ্টা করা যায়, তেমনি সমাজবিজ্ঞান বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত অনুসারেও তার প্রকৃত রূপের পরিচয় পাওয়া সম্ভবপর হতে পারে। অপরদিকে মানসিক ক্রিয়াকলাপের অধিকারী হিসেবে তাকে মনোবিজ্ঞানের আলোকে মানবজীবনের প্রকৃত রূপের পরিচয় পাওয়া সম্ভবপর হতে পারে। অপরদিকে মানসিক ক্রিয়াকলাপের অধিকারী হিসেবে তাকে মনোবিজ্ঞানের আলোকে মানবজীবনের প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটন করা আমাদের পক্ষে কর্তব্য এবং তারই আলোকে তার জীবনের মূল লক্ষ্য সম্বন্ধে অবহিত হওয়া উচিত।
প্রথম পরিচ্ছেদ
জীববিজ্ঞানের শিক্ষা
জীববিজ্ঞান সম্বন্ধ ডারউনের মতবাদ সর্বপ্রথমে দুনিয়ার সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর ‘প্রজাতির উৎপত্তি’১ (চার্লিস ডারউইনঃ প্রজাতির উৎপত্তি) প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে। উপরিউক্ত দুটি গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমবিকাশের নীতি জীবন-বিকাশে কার্যকরী বলে সর্বত্রই গৃহীত হয়। কাজেই ডারউইনের মতবাদ নিয়েই আলোচনা শুরু করা যাক।
ডারউইনের মতে, “ প্রাণীদের মধ্যে প্রত্যেক সৃজনের ব্যাপারে বহু সন্তান উৎপাদনে সক্ষম। তাদের প্রজনন জ্যামিতিক অনুপাতে চলে”। কডফিস নামক এক জাতীয় মাছ আছে। তারা দুই কোটি ডিম পাড়ে। ধারনা করা গেছে, যদি ডেনডিলিয়ন গাছের বীজগুলো পরিণত হয় তাহলে একটা ডেনডিলিয়ন গাছই চতুর্থ বংশানুক্রমে এত গাছ উৎপাদন করবে, যাতে যুক্তরাষ্ট্রের মত রাষ্ট্রের আয়তনের দুইশত পয়ঁতাল্লিশ গুণ বড় দেশ কেবল ঐ গাছের বংশধর দ্বারা ছেয়ে ফেলা যাবে। একটি বীজাণু একদিনেই দশ লক্ষ বীজাণুর সৃষ্টি করতে পারে। ‘লিনেয়াস’৩ বলেছিলেন, “তিনটি মাছি এবং তাদের বংশধররা একটি ঘোড়ার মৃতদেহ ঠিক একটা সিংহের মতই অল্প সময়ে ভক্ষণ করতে পারে”।
“উদ্ভিদ এবং প্রাণীরা এত অধিক পরিমাণে প্রজনন করতে সক্ষম হলেও তাদের সকলের বাসস্থানের বা খাদ্যের সংস্থান নেই। এর জন্যই (উদ্ভিদ বা প্রাণীজগতে) চলছে এক জীবন-যুদ্ধ। সেই জীবন-যুদ্ধে যোগ্যতমরাই বেঁচে থাকে। তাকে ডারউইন বলেছেন, “যোগ্যতমের উদ্বর্তন”; (এখানে প্রশ্ন ওঠে) কারা যোগ্যতম? (তার উত্তরে বলা যায়) যাদের শারীরিক গঠন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খায়, (কেবল তারাই টিকে থাকে)। (তার কারণ) (আবার প্রশ্ন ওঠে) ব্যষ্ঠিদের মধ্যে পার্থক্য কেন দেখা দেয়? (দৈহিক গঠন ও তার ক্রিয়ার মধ্যে এক প্রজাতির৪ অন্তর্গত বিভিন্ন ব্যষ্টির মধ্যে, এমনকি একই পিতামাতার সন্তানের মধ্যে কিছুটা ব্যতিক্রম৫ দেখা যায়। একই রকমের প্রাণী থেকে একই জাতীয় সন্তানের উৎপত্তি হয় সত্যি, কিন্তু সন্তানেরা পিতামাতার অনুরুপ হয় না। যারা তাদের পিতামাতা থেকে ব্যতিক্রম হয়, তাদের মধ্যে যাদের ব্যতিক্রমগুলো প্রকৃতির অনুকূল তাদেরকেই প্রকৃতি বাঁচিয়ে রাখে এবং সংরক্ষণ করে। এর নামই প্রকৃতির মনোনয়ন৬। তারা বেঁচে থাকে, বেঁচে চলে এবং সম্ভবত তাদের ব্যতিক্রমগুলো তাদের সন্তান-সন্ততিতে বর্তে। যারা প্রকৃতির অনুগ্রহলাভে অসমর্থ তারা ধংসপ্রাপ্ত হয়। ক্রমশ এভাবে জীবের শারীরিক গঠন পরিবর্তিত হয় এবং কালে এ পরিবর্তন এতো বড় হয়ে দেখা দেয় যে, সম্পূর্ণ অভিনব একটা প্রজাতির উৎপত্তি হয়। ধারালো দাঁত, ছিন্ন করতে সক্ষম চংগল, শিঙ্গের মত শক্ত চামড়া, গরম পশম প্রভৃতি শত্রুদের বিরুদ্ধে এবং প্রাকৃতিক উপাদানের বিপক্ষে জীবনযুদ্ধে প্রয়োজনীয়। এগুলোর উৎপত্তি হয় আকস্মিক প্রকারণের৭ ফলে এবং তারা বংশজ গুনাবলিররূপে রক্ষিত হয়। যে সকল পাখি কোনদিন ভ্রমণশীল নয় তাদের মধ্যে যদি কোনটি হটাৎ তাদের আদিম আবাস ছেড়ে অন্যত্র চলে যায় এবং প্রচুর খাদ্যদ্রব্যের সন্ধান পায় তা’হলে সে নতুন স্থানে তারা বেঁচে থাকবে, তাদের বংশবৃদ্ধি হবে আর তাদের এ বিশেষত্ব তাদের সন্তানদের মধ্যেও দেখা দেবে। এর থেকেই সহজাত প্রবৃত্তির৮ উৎপত্তি। এমন যে মানব-চক্ষু যাতে অভিযোজনের৯ এতো বিস্ময় প্রকাশ পায়, তাও আলোর প্রতি সংবেদনশীল১০ একটিমাত্র কোষের গ্রুপ থেকে দেখা দিতে পারে; তার ফলে যারা (এ অঙ্গের) ভাগ্যবান অধিকারী তাদের বিপদ ও শিকার উভয় সম্বন্ধে পূর্বাহ্নে সতর্ক করতে পারে।
মানবজীবনও চলছে বিবর্তন তত্ত্বের এ নীতি অনুসরণ করে। মানুষের মাঝে যারা বাঘ-ভাল্লুক থেকে লুকিয়ে আত্মগোপন করার কৌশল আয়ত্ত করেছিল তারাই কেবল ঠিক রয়েছে; যারা পারেনি, তাদের নাম-গন্ধও দুনিয়ায় নেই। মানুষের নানা শাখা-উপশাখাও এইভাবেই লয় পেয়েছে। দুনিয়ার বুকে টিকে থাকার মত সামর্থ্য না থাকায় প্রাকৃতিক নিয়মেই নানাবিধ জাতি লোপ পেয়েছে। মানুষের বেলায় কেবল প্রকৃতির অন্য দশটি জীবের আক্রমণ থেকে বেঁচে থাকার শক্তি থাকলেই চলবে না, শক্তিশালী অপর মানুষের আক্রমণ থেকে বেঁচে থাকবার মত সামর্থ্যেরও প্রয়োজন।
চোখের সামনেই দেখা যায়, অনেকগুলো প্রাণীই বেঁচে থাকবার মত সংগঠনের অভাবে ক্রমেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। লাল অথবা হলদে রঙের ফড়িঙের সংখ্যা খুব কম; কারণ, তারা পাখিদের চোখে সহজেই ধরা পড়ে। সবুজ রঙের ফড়িং সংখ্যায় খুব বেশি। তাদের রঙ ঘাসের রঙের মত থাকায় তারা অতি সহজেই ঘাসের সাথে লুকিয়ে আত্মরক্ষা করতে পারে। পুরাকালের যেসব জন্তু-জানোয়ারের অস্থিপঞ্জর পাওয়া যায়, তা থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয়, একদিন দুনিয়ার বুকে তারা অবাধে বিহার করতো। জীবনযুদ্ধে উপযোগী শারীরিক সংগঠন তাদের না থাকায় প্রকৃতির বুকে নানাবিধ ঝড়-ঝঞ্ঝা, তুষারপাতের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে না পারায়, তারা স্বাভাবিকভাবেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।
মানব জাতির নানা শাখাও এভাবেই লয় পেয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসী ‘বুশম্যান’১১ বা আমাদের দেশের নানাবিধ উপজাতি-যেমন কোল, ভীল বা সাঁওতাল যেভাবে ধ্বংসের পথে চলছে, শতাধিক বছর পরে আর তাদের কোন চিহ্ন নাও থাকতে পারে। তার কারণ, জীবনযুদ্ধে ওরা বারবার পরাজিত হচ্ছে। সে পরাজয়ের ফলে বিজেতা তাদের ব্যবহার করেছে যন্ত্রপাতির মত। তাদের বংশবৃদ্ধি বা মানসিক উৎকর্ষের কোন সুযোগ দিচ্ছে না। ডারউইনের ঐ মতবাদ প্রচারিত হওয়ার পরে বিখ্যাত প্রাণীবিদ উইজম্যান১২ প্রমাণ করেছেন যে, বাচ্চাদের মধ্যে মা-বাপ থেকে প্রাপ্ত জননকোষ১৩ কোন কালেই নষ্ট হয় না। কাজেই বিভিন্ন জাতি বা প্রজাতির মধ্যে জননকোষের ধারা চিরকাল অব্যাহত থাকে। প্রকারণের দ্বারা জননকোষের তারতম্য হয় না। অন্যদিকে ডারউইনের বা লেমার্কের ১৪ ধারনা ছিল প্রকারণের দ্বারা লব্ধগুণ১৫ সন্তানদের মধ্যে দেখা দেয়। বর্তমান জীববিজ্ঞানবিদ্দের এ সব জটিল তর্কে আপাতত লিপ্ত না হয়েও ডারউইনের মতবাদের নানা ত্রুটি সহজেই ধরতে পারা যায়। আপাতত জীবজগতের সর্বত্রই জীবন-যুদ্ধের দৃশ্য হলেও ডারউইন জীবনের শত্রুতার দিকটাই লক্ষ্য করেছেন। প্রাণীজ জগৎ ও প্রকৃতির মধ্যে তিনি বৈরিতার সূত্রই আবিস্কার করেছেন, তাদের পারস্পরিক সহযোগিতার দিকটা তিনি এড়িয়ে গেছেন। তিনি জীবজগতের এ যুদ্ধকে শত্রুর বিরুদ্ধে এবং প্রাকৃতিক উপাদানের বিপক্ষে জীবের টিকে থাকার যুদ্ধ বলে অভিহিত করেছেন। কাজেই তাঁর মতানুসারে চারটে যুদ্ধই সম্ভবপর বলে ধরে নিতে হয়। জীবকে তার শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়। এ শত্রু কারা?
১। এ শত্রু একই প্রজাতির১৬ অন্তর্গত বিভিন্ন ব্যক্তি হতে পারে।
২। এক প্রজাতির বিরুদ্ধে অন্য প্রজাতিও হতে পারে।
৩। সম্পূর্ণ ভিন্ন দুই জাতিও হতে পারে।
৪। প্রাকৃতিক বিভিন্ন উপাদান১৭ যেমন-পানি, বায়ু,গ্রীষ্ম,তুষারপাত প্রভৃতিও হতে পারে।
একে একে সবকটি যুদ্ধের আলোচনা করা যাক। ডারউইনের মতবাদ অনুসারে একই পূর্বপুরুষ থেকে সকল জীবেরেই উৎপত্তি হয়েছে। কীট-পতঙ্গ থেকে শুরু করে মানবজাতি পর্যন্ত সকল জীবেরই আদি পিতা একটি মাত্র জীবকোষ। মানুষ,গরু,মহিষ,হাতি,বাঘ,ভালুককে আপাতত ভিন্ন শ্রেনী মনে হলেও তাদের আদি জনক একই জীবকোষ। আকস্মিক প্রকারণ,জীবনযুদ্ধ,উপযুক্ততমের উদবর্তন,প্রাকৃতিক নির্বাচন১৮ প্রভৃতি চিন্তার মাধ্যমে তিনি দেখিয়েছেন-এক জীব থেকেই নানাবিধ শ্রেনীর সৃষ্টি হতে পারে।
একই আদি পিতা থেকে উৎপত্তি হলেও বর্তমানে বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে কোন কোনটি সগোত্র বলে দেখা যায়। তাদের মধ্যে সাদৃশ্য বর্তমান; যেমন,বাঘ জাতীয় প্রজাতির মধ্যে বিড়াল,পুমা,চিতাবাঘ,বড় বাঘ এক গোষ্ঠী বলে পরিচিত। তেমনি গরু,মহিষ,ছাগল প্রভৃতি এক প্রজাতীয় বলে মনে হয়। পাখিদের মধ্যে শত বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হলেও তাদের মধ্যে কতকগুলো সাধারণ গুণ বর্তমান। অপরদিকে মানবজাতি১৯ ও বাঘ জাতীয় বা গরু জাতীয় জীবের মধ্যে পার্থক্য এত বেশি যে, তাদের ভিন্ন প্রজাতি না বলে ভিন্ন জাতি নামেই অভিহিত করা ভাল। বিবর্তনবাদের সূত্রানুসারে তাই জাতির সঙ্গে জাতিরও যুদ্ধ হতে পারে।
১. একই প্রজাতির অন্তর্গত বিভিন্ন ব্যষ্টির মধ্যে যুদ্ধ হয়। যেমন গো-জাতির বিভিন্ন ব্যষ্টির মধ্যে সচারাচর মারামারি,হানাহানি হয়। যারা দূর্বল, যারা পঙ্গু, তারা সহজেই সবলের হাতে নিধনপ্রাপ্ত হয়। এ সকল ঘটনা নিত্যই আমাদের চোখে পড়ে। প্রকাণ্ড ষাড় কর্তৃক ছোট ছোট বাছুরের অকাল মৃত্যু আমাদের প্রত্যেক গ্রামেই মাঝে মাঝে দেখা যায়। পুরুষ বিড়াল সুযোগ পেলেই সদ্যোজাত বিড়াল ছানাগুলোকে মেরে ফেলে। বাড়িতে শক্তিশালী পুরুষ মোরগ থাকলে তার অত্যাচারে অনেক সময় ছানা পোষা দায় হতে পড়ে। তবু এটি জীবজগতের একটি দিক মাত্র-যে, মোরগ ছানা হত্যায় আনন্দ পায়, সে-ই আবার চিলের আক্রমণ শুরু হলে চিৎকার করে অসহায় বাচ্চাদের সাবধান করে দেয়। যূথচারী প্রাণীদের-যেমন বন্য হস্তী,বন্যমহিষ প্রভৃতি বড়দের মধ্যে অত্যন্ত স্নেহপরায়ণতা বর্তমান। নিজের বাচ্চা না হলেও গোঠের অন্যান্য প্রাণীর বাচ্চাগুলোকে তারা আগলে রাখে। যে সকল পাখি একই ঋতুতে বাচ্চা তোলে-তাদের মধ্যে বেশ সহনশীলতা ও মহানুভবতার নীতি দেখা যায়;সবেমাত্র উড়তে শিখলে অনেক সময় এক বাসা থেকে বাচ্চাগুলো অন্য বাসায় ভুলে গেলেও বুড়ো পাখিরা তাদের মেরে ফেলে না। একটু ভয় দেখিয়েই ক্ষান্ত হয়।
২. এক প্রজাতির বিরুদ্ধে অন্য প্রজাতির বা এক জাতির বিরুদ্ধে অন্য জাতির লড়াই দেখা যায়। বিড়ালের ইঁদুর শিকার, সাপ ও বেজির যুদ্ধ, পাখিদের দ্বারা কীট-পতঙ্গাদির বিনাশ সব সময়ই চোখে পড়ে। মানুষ বুদ্ধিবলে সকল জীবের সেরা হলেও তাদের বাঘ,ভালুক থেকে আরম্ভ করে কীটপতঙ্গাদির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়। কাজেই প্রজাতির বিরুদ্ধে প্রজাতির অথবা জাতির যুদ্ধ জীবনে অতি সত্যিকার ঘটনা। তবু মৈত্রীর উদাহরণেরও অভাব নেই। সচরাচর এক প্রজাতির জীবের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হলেও মাঝে মাঝে দুই প্রজাতির জীবের মধ্যে মৈত্রীর সমন্ধ দৃষ্ট হয়। প্রাণী-বিজ্ঞানবিদেরা আবিস্কার করেছেন-মাংসাশী কুমীরের দাঁতের মাংস এক রকমের ছোট পাখি পরিস্কার করে নেয়। তাতে কুমীরের দাঁত যেমন পরিচ্ছন্ন হয়, তেমনি সেই পাখিগুলোরও আহারের সংস্থান হয়। গরু ও মহিষের শরীর থেকে পোকা বেছে নেয় শালিকেরা, তাতে তৃতীয় জাতীয় জীবের নিধন হলেও এই দুই জাতির মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে।
মানুষ বুদ্ধিবলে অন্যান্য সকল প্রজাতিকেই তার জীবনযাত্রার নানা প্রয়োজনে ব্যবহার করে। বাঘ,ভালুক এমনকি বিষধর সাপকে মানুষ ব্যবহার করে তার নানাবিধ প্রয়োজনে। এতে শত্রুর দ্বারা অনেক ক্ষেত্রেই তার উপরকার হয়। বিভিন্ন জাতীয় মানুষের মধ্যে যুদ্ধ চলে সত্য,কিন্তু সে যুদ্ধে একে অপরকে সম্পূর্ণ বিনাশ করে লাভবান হতে পারে না। মানুষের বেলায় এ নিয়মের ব্যতিক্রম স্বতঃসিদ্ধের মত পরিস্কার। এক জাতি কর্তৃক বিজিত অপর জাতি যদি বিজেতার হাতে সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তাহলে বিজয়ের কোন অর্থই হয় না। বিজয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য বিজিত জাতির দ্বারা কাজ আদায় করা। আধুনিক পরিভাষায় তাকে শোষণ বলা হয়। যদি বিজিত জাতিকে ধ্বংসই করা হয় তাহলে শোষণের অবকাশ কোথায়?
৩.বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদান যেমন-জল, বায়ু,শীত,গ্রীষ্ম প্রভৃতির সঙ্গে কেবল যুদ্ধ করেই জীব টেকে না; তারা জীবের বেঁচে থাকবার পক্ষেও অবশ্য প্রয়োজনীয়। জীবের দৈহিক সংগঠন উপযোগী না হলে এদের অত্যাচারে জীব লয় পায়, তেমনি দৈহিক সংগঠনের উপযুক্ত হলেও এদের অভাবে সে লয় পেতে পারে। দৈহিক সংগঠনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক উপাদানকে গ্রহণ করেই জীব বেঁচে থাকে। তাদের পরস্পরের সহযোগিতা অনেক ক্ষেত্রেই অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।
জীবিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীর জীবের মধ্যে যুদ্ধ রয়েছে সত্যিই, তবে সে যুদ্ধই জীবনের একমাত্র রূপ নয়। সে যুদ্ধের মধ্যেও প্রেম,মৈত্রী ও ভালবাসা রয়েছে। সন্তানের জন্য পিতামাতার বুকে রয়েছে অপার স্নেহ,দম্পতির মধ্যে সাধারণত রয়েছে অগাধ ভালবাসা,বাচ্চাদের প্রতি বুড়োদের রয়েছে বাৎসল্যবোধ। একই প্রজাতির বিভিন্ন ব্যষ্ঠিদের মধ্যে রয়েছে সংঘবদ্ধ হয়ে আত্মরক্ষার চেষ্ঠা। মানবজীবনে কেবল যুদ্ধই একমাত্র সারসত্য নয়। সেই যুদ্ধের অন্তরালেও মানুষের যূথচারী প্রবৃত্তি তাকে সমষ্টি-চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে। মানব-জীবনের অনেকগুলো কাজ-কর্মই নিয়ন্ত্রিত হয় প্রেম,দয়া-মায়া-স্নেহ প্রভৃতি সুকুমার বৃত্তি দ্বারা।
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
মনোবিজ্ঞানের শিক্ষা
ফ্রয়েডীয় মতবাদ
অষ্ট্রিয়ার বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানবিদ ফ্রয়েডের কামসর্বস্ববাদ২০ বা সর্বকামিতা আজ দুনিয়ার সকল জ্ঞানী লোকের নিকট পরিচিত। তাঁর মতে মানুষ তার আদি কাম দ্বারা পরিচালিত। মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা,সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূলে রয়েছে শুধুমাত্র কাম। এ সত্যটি প্রমাণ করাই ছিল ফ্রয়েডের জীবনের লক্ষ্য। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে মনস্তত্ত্ববিদ মহলে ফ্রয়েড ছিলেন রাজাধিরাজ। বর্তমানে কার্ল জুঙ২১ ও এ্যাডলারের২২ বিশ্লেষণে তাঁর মতবাদে নানা ত্রুটি ধরা গেলেও আমাদের কাব্য ও সাহিত্য তাঁর মতবাদের ছাপ রয়ে গেছে অম্লান। তাই তাঁর মতবাদ নিয়ে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন।
তাঁর ধারণা, সজ্ঞান মনে যেসব কামনা-বাসনা দূষণীয় বলে পরিত্যাক্ত হয় সেগুলো অচেতন মনে গিয়ে বাসা বাঁধে। সেখানে প্রক্ষোভের২৩ রয়েছে প্রাধান্য। সজ্ঞান মনে বাসনাগুলোকে করা হয় অবদমিত; তাই তারা অচেতন মনেই এই অন্ধকারে এসে জড়ো হয়। এতে সজ্ঞান মনের শান্তির পক্ষেই হয় সুরাহা। তবে উদ্ধায়ুজ২৪ লক্ষণ দেখা দিলে নানাভাবে মনকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। অবদমিত বাসনার সর্বজনীনতা আবিস্কার করে ফ্রয়েড তাদের প্রকাশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আবিস্কারে মনোনিবেশ করেন। সর্বপ্রথমে স্বপ্নের মধ্যে তিনি তার সন্ধান পান। তাঁর মতে স্বপ্নও অচেতন মনের ক্রিয়ার ফল। সজ্ঞান মনের বেড়াজাল ডিঙ্গিয়ে স্বপ্নে আমাদের আকাংক্ষিত বস্তু দেখা দেয়। যদিও দিনের বেলায় জাগ্রত অবস্থায় চৈতন্যের রয়েছে প্রাধান্য,নিদ্রাতে কোন প্রহরী বা মনোদ্ধারী না থাকায় অচেতনের পক্ষে যেন দুয়ার খুলে দেওয়া হয়।
অবদমনের শক্তিগুলোকে ফ্রয়েড প্রহরী২৫ বলেছেন। তাঁর মতে আমাদের মনের অনেকগুলো বাসনাই অবদমিত। আমরা সে সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নই। বাইরে থেকে নানাবিধ পুলিশী শক্তি আমাদের বাসনাগুলোকে অবদম করে, আমরা নিজেরাও পুলিশী ভাব নিয়ে তাদের রুদ্ধ করি। নিদ্রায় সে পুলিশের হুকুমবরদারী থাকে না বলেই আমাদের বাসনাগুলো হুড়হুড় করে স্বপ্নে রুপায়িত হয়ে থাকে। কেবল স্বপ্নে নয়, লক্ষণ সংক্রান্ত কার্যাবলি থেকেও ফ্রয়েড উদাহরণ সংগ্রহ করে তাঁর মতবাদ প্রমাণ করেছেন। আমরা সকলেই জানি, অনেক সময় অনবধানতাবশত আমরা অনেক কাজ করি। যেমন লিখতে বসেছি, টেবিলের একপাশে এক গ্লাস পানি রয়েছে। হটাৎ কনুই লেগে গ্লাসটা পড়ে গেল। এক আমরা অনবধানতাবশত কাজ বলে থাকি। ভাবনাবিহীন কাজও করি। যেমন পথ চলতে যেয়ে একটা লাঠি পথিমধ্যে পেয়ে লাথি দিয়ে তাকে ফেলে দিই। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অন্যান্য মানুষের সঙ্গে লেনদেনের ব্যাপারে অথবা এক কাজ করতে অন্য কাজ করাতে সজ্ঞান মনের স্রোতে কিভাবে এসব কার্যাবলি প্রকাশ পায় তার সন্ধান পাই। যদিও আপাতত এসব কার্যকে আপতিক২৬ মনে হয়, আসলে তারা অবদমিত বাসনার২৭ প্রকাশ ব্যতীত আর কিছুই নয়। যেসব কার্যের মাধ্যমে এভাবে আমাদের গুপ্ত বাসনা অনিচ্ছাকৃতভাবে প্রকাশ পায় ফ্রয়েড তার সহজ নাম দিয়েছেন ত্রুটি। প্রচলিত ভাষায় তারা ভুল-ভ্রান্তি নামে পরিচিত। এসব ভুল-ভ্রান্তি ত্রুটি-বিচ্যুতির উহ্য অর্থ আবিস্কারের মধ্যে রয়েছে ফ্রয়েডের কৃতিত্ব। স্বপ্নের মতই তাদের মধ্যে রয়েছে একটা বাহ্যিক অর্থ,একটা গূঢ় অর্থ। সেই গূঢ় অর্থই আমাদের মনের অন্তর্নিহিত উত্তেজনার প্রাবল্যে বা প্রহরীর অনুপস্থিতিতে আমাদের পেশিগুলোকে ক্রিয়াশীল করে তোলে; আমরা ভাষায় তাদের প্রকাশ করি।
আমাদের মনের সে সব অবদমিত বাসনার জন্ম কাম থেকে। জীবনের সকল স্তরের আলোচনা করে ফ্রয়েড প্রমাণ করতে চেয়েছেন কামপ্রবৃত্তির দ্বারা মানব-মন সর্বত্রই পরিচালিত। তাঁর ধারণা, মানবজীবনের মূলে রয়েছে লিবিডো২৮ বা বিরাট কামশক্তি। ছোট ছোট শিশুরা ফ্রয়েডের মতে আত্মকামী২৯। তাদের মধ্যে স্বতঃপ্রণোদিত কামের লক্ষণ প্রকাশ পায়। তাদের আদর-সোহাগ করাতে তারা আংশিকভাবে কামতৃপ্তি লাভ করে। ছোট ছোট বাচ্চাদের শরীরের নানাস্থানে কামকেন্দ্র রয়েছে। বাইরে থেকে এসব কামকেন্দ্র উত্তেজনার সৃষ্টি করলে তারা কামসুখ ভোগ করে। ফ্রয়েডের ধারণা, শৈশবের এই কামাবস্থা জন্ম থেকে পাঁচ বৎসর বয়স পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। এ সময়কে ফ্রয়েড বলছেন শৈশবাবস্থা। দ্বিতীয় পর্যায়ে শুরু হয় অস্ফুটচিত্ততার কাল৩০। তার সময় তিনি নির্দিষ্ট করেছেন, পাঁচ থেকে বারো বৎসর পর্যন্ত। এ সময় লিবিডো হয়ে পড়ে ব্যক্তিকেন্দ্রিক। শৈশব ও কৈশোরের মধ্যবর্তী এ অবস্থায় কাম-নদীতে কিছুটা ভাটার টান দেখা যায়। বারো বছর থেকে আঠারো বছর পর্যন্ত কৈশোরের সীমা। এটি যেন কামজীবনে এক ঝটিকাবিক্ষুব্ধ অবস্থা। এর সূচনায় জীবনে যেন লণ্ডভণ্ড কাণ্ড আরম্ভ হয়। ফ্রয়েডের মতে,শৈশবে মানুষ থাকে আত্মকামী, অস্ফুটচিত্ততার সময় তার কাম ধাবিত হয় একই লিঙ্গের বা বিপরীত লিঙ্গের কোন লোকের প্রতি। কৈশোরের সমাগমে সম্পূর্ণ বিপরীত লিঙ্গের লোকের প্রতি তা হয় কেন্দ্রীভূত।
জীবনের কোন পর্যায়ে কামের বিষয়বস্তুরূপে কোন কিছুকে গ্রহণ করলে, পরবর্তী পর্যায়ে তা অপরিবর্তিত থেকে যায়, তা হলে তাকে বৈকল্য৩১ বলা যায়। যেমন শৈশবের আত্মকাম যদি অস্ফুটচিত্ততার সময় আত্মকাম থেকে কোন ব্যক্তিমুখী না হয় তা হলে বুঝতে হবে সে ব্যক্তির জীবনে বৈকল্য দেখা দিয়েছে অথবা তার কাম শৈশবের পর্যায়ে স্থায়ী হয়ে রয়েছে। একে বলা হয় স্থিতাবস্থা৩২। এমনও হতে পারে যে, এক ধাপ ডিঙ্গিয়ে গিয়ে কাম আবার নিচের ধাপে ফিরে যেতে পারে যেমন কৈশোরের বিপরীত লিঙ্গের লোকের প্রতি ধাবিত না হয়ে আবার ফিরে গিয়ে শৈশবের আত্মকামে পরিণত হতে পারে। একে বলা হয় প্রতিসরণ৩৩। এরূপ বৈকল্য দেহকা দিলে বুঝতে হবে হয় স্থায়ী হয়ে, না হয় উল্টো দিকে কাম-নদীর স্রোত বইতে শুরু করেছে।
এ লিবিডোর বা কামশক্তির পশ্চাৎপটে পরিবার রয়েছে। এ জন্যই ফ্রয়েড পারিবারিক রোমান্সের বিকাশ দেখিয়েছেন; এখানে সর্বপ্রধান কূটএষণা পিতৃ অথবা মাতৃকেন্দ্রিক। তাই স্বভাবতই ছেলেরা পিতৃ-বিদ্বেষী, কারণ পিতার স্থান সে অধিকার করতে চায়। আমাদের প্রত্যেকেরই এ পাপের পথে যাত্রার রয়েছে উত্তরাধিকার। তাই স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে হলে, এ ইদিপাস*(পৌরণিক যুগের এক নায়ক,ভ্রমবশত যে আপন মাতাকে বিবাহ করেছিল।) এষণাকে নির্মূল করতে হবে। শৈশব এ এষণা প্রবলভাবে দেখা দেয় সত্য, তবু দীর্ঘকাল স্থায়ী হওয়ার দরুন পরিণত বয়েসেও নানা বিপদের সৃষ্টি করতে পারে। যেমন কৈশোরের কাম স্বভাবতই স্বাধীনভাবে পরিতৃপ্ত লাভ করে কিন্তু পিতার প্রতি ভয়ের দরুন এ পর্যায়ে তা ধ্বজচ্ছেদ কুটেশায়৩৩ পরিণত হতে পারে। এ এষণায়গ্রস্ত ব্যক্তি ভয় করতে পারে যে যৌন জীবনে সে হবে অকৃতকার্য। কাজেই ফ্রয়েডের মতে এই ইদিপাস এষণাই যৌন জীবনের বিকাশে নানাদিকে দেখা দিয়ে হয় কার্যকরী।
শিশুমাত্রই অত্যন্ত আত্মকেন্দ্রিক। এ আত্মকেন্দ্রিকতা লিবিডোর বিকাশে নানভাবে থাকে ক্রিয়াশীল। ছোট বাচ্চা মাত্রই অত্যন্ত জুলুমবাজ, সে সর্বেসর্বা হতে চায়। পরিণত জীবনে তার এ প্রবণতা ধর্ষকামে৩৪ রূপ নিয়ে দেখা দেয়, এতে কামের বস্তুর প্রতি একই সঙ্গে বাসনা ও নিষ্ঠুরতা থাকে পরস্পর সংযুক্ত এবং তাতে ধর্ষকামী সুখভোগ করে। এই যৌন মনোভাবে ঠিক উল্টো দিক হল মর্ষকাম৩৫। এতে যৌন পরিতৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে কষ্ট পাওয়াতেও মর্ষকামী সুখ ভোগ করে। লিবিডোর বিকাশের এ পর্যায়েই পুরুষ ও নারীর ভাব হয়ে পড়ে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। সাধারণত পুরুষমাত্রেই ধর্ষকামী এবং নারীমাত্রই মর্ষকামী। সেরূপ ইদিপাসের নারীরূপ হল ইলেকট্র।** (শ্রীনৃপেন্দ্র কুমার বসু তাঁর ফ্রয়েডের ভালবাসার নাম দিয়েছেন শতরূপা কূটেশা।) ফ্রয়েডের মতে মেয়েদের শৈশবে পিতৃসঙ্গ কামনা থাকে স্বাভাবিক। পরে লিবিডোর বিকাশে তাকে বাধ্য হয়েই তা ত্যাগ করতে হয়।
ছেলে ও মেয়েদের ইন্দ্রিয়গুলোর পার্থক্যের দরুন মেয়েদের মনে উপস্থঈর্ষার৩৬ সৃষ্টি হয়। একে ছেলেদের ধ্বজচ্ছেদ কূটেশার নারীরূপ বলা যায়।
এভাবে জোড়া জোড়া বিভিন্ন ও প্রতিপক্ষীয় ধারণাগুলোকে ফ্রয়েড বলেছেন জোড়া দ্বি-মেরুত্ত৩৭। সুখ-দুখ, ভালবাসা ও ঘৃণা পুরুষালী ও মেয়েলী ভাব প্রভৃতি ব্যতীত আর কিছুই নয়। তেমনি, একই সঙ্গে ভীতি,ঘৃণা ও ভালবাসা, সৃজন করা ও ধ্বংস করার প্রভৃতির নাম উভয়বলতা। লিবিডো প্রসঙ্গে আমরা ফ্রয়েডের আর একটি ধারার সঙ্গে পরিচিত হয়। তাকে বলা হয় উদ্গতি৩৮। যে শক্তিমূলে মানুষ কোন বিষয়ের প্রতি হয় আসক্ত বা কর্মশক্তি ব্যয় করে, সে নিশ্চয়ই লিবিডো ছাড়া আর কিছু নয়। আত্মকেন্দ্রিক লিভিডোর শক্তি আত্মপ্রকাশ৩৯ বা জীবনে কোন বিশিষ্ট পদ অধিকার বা সামাজিক প্রতিপত্তি লাভ প্রভৃতিতে ব্যয়িত হয়। যখন লিবিডো কোন সমস্যার সমাধানে বা কারকর্মে ব্যয়িত হয় তখন তাকে ফ্রয়েড বলে বিষয়কেন্দ্রিক লিবিডো৪০।
এই যে আত্মকেন্দ্রিক থেকে বিষয়কেন্দ্রে লিবিডোর কার্যকারিতা, ফ্রয়েড তার নাম দিয়েছেন স্থানান্তর। যে ব্যক্তির আত্ম-উত্তেজনা ছিল তার মনের মধ্যেই স্থিত সে ব্যক্তিই যখন কাব্য রচনায় পেলো সত্যিকার আনন্দ তখন বুঝতে হবে তার লিবিডোর তার বিষয়বস্তু পেয়ছে এবং আত্মকেন্দ্রিক রূপ ত্যাগ করে সে বিষয়কেন্দ্রিক৪১ হয়ে পড়েছে।
লিবিডোর এবম্বিধ প্রকাশে বা স্থানান্তরের মধ্যে তার উদ্গতির কাজও হয়। কাব্য,নাটক,রোমান্স,শৌর্য,শালীনতা প্রভৃতি লিবিডোর উদ্গত রূপ। কোন বিষয়বস্তুতে আমাদের আসক্তি দেখা দিলে বুঝতে হবে তা কামবাসনা থেকে উদ্ভূত এবং তার মধ্যে কামের সে প্রখরতা রয়েছে।
লিবিডোর পরিভ্রমনের ফলেই নানাবিধ জটিল অবস্থার সৃষ্টি। উদ্ধায়ুর৪২ বেলা,লিবিডোর কার্যকারিতার নীতি প্রয়োগ করে ফ্রয়েড স্থির-নিশ্চিত হয়েছেন যে,উদ্ধায়ু কাম-জীবনের ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই নয়। স্বাভাবিক যৌন-জীবনে উদ্ধায়ু সম্ভব নয়। ফ্রয়েডের ধারার অনুসরণ করলে জীবনের পক্ষে স্থায়ী অবস্থার৪৩ বদ্ধাবস্থায় অথবা প্রতিসরণে পৌঁছার রয়েছে আশঙ্কা। তার সোজা অর্থ এই যে, লিবিডো কোন এক বিশিষ্ট পর্যায়ে যেয়ে স্থায়ী হয়ে বসে থাকতে পারে। যেমন অস্ফুটচিত্ততার*( অস্ফুটচিত্ততার (Latency period) সময় উভয় লিঙ্গের লোকের আসক্তি স্বাভাবিক।) সময় যদি অন্য কোন ব্যক্তির প্রতি কাম ধাবিত না হয় তাহলে বুঝতে হবে এষণাগ্রস্ত হয়ে এ লিবিডো এ জায়গায়ই স্থির হয়ে পড়েছে। কৈশোরে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আসক্তি ধাবিত হতে পারে। ফ্রয়েড, মানব-মনের বিভিন্ন পর্যায়ে কতকগুলো বৈকল্প আবিস্কার করে ধরে নিয়েছেন, তারা শৈশবাবস্থায়ও বিদ্যমান। ইদিপাস-সমকামিতা বা আত্মকাম ইত্যাদি এষণা পরিণত বয়সেও মানবজীবনে দেখা দেয় বলেই তাদের অস্তিত্ব গোড়াতেই বর্তমান বলে কেমন করে প্রমাণিত হয়? পরিবেশগত ও পারিপার্শ্বিক নানাবিধ কারণের সমাবেশের ফলে তাদের উৎপত্তি হতে পারে, যেমন হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের একত্র সমাবেশ হলেই পানি হয় না, তার জন্য বিদ্যুতের দরকার। তেমনি হয়ত কেবল মাতৃকেন্দ্রিক ভালবাসার বীজ মানবমনে থাকলেই ইদিপাসের পরিণতি হতে পারে না। আরও অনেকগুলো ফ্যাকটারের প্রয়োজন। ফ্রয়েড সে ফ্যাকটারগুলোর ওপর কোন গুরুত্ব আরোপ করেননি। এতে বৈজ্ঞানিক দিক দিয়ে তার ত্রুটি সহজেই ধরা পড়ে। কেবল ইদিপাসের বেলায় নয়, অন্য সবগুলো এষণার বেলাতেও তিনি বাইরের ফ্যাকটারগুলোর উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করেননি। উদাহরণস্বরূপ ইদিপাসকেই ধরা যাক। শুধু কামের দ্বারা মানবমন পরিচালিত হলে, পিতা বা সমাজের ভয়ে এ কামের পথে যাত্রায় ছেলে নিবৃত্ত হবে কেন? পিতার স্থান যদি সে অধিকার করতে চায় তাহলে তাতে ভয়ের কোন স্থান থাকতে পারে না। যদি পিতাকে তার বিরাট বপু বা আধিপত্যের জন্য ভয় করে তবে তার স্বাভাবিক কাম-বাসনার সঙ্গে সঙ্গে ভয়কে এক আদি প্রবৃত্তি বলে স্বীকার করে নিতে হবে।
ফ্রয়েড অবদমনের শক্তিগুলোকে বলেছেন প্রহরী। তারা প্রায়ই সামাজিক শক্তি। সে সামাজিক শক্তিগুলোর উৎপত্তি কোথা থেকে? যদি বলা হয় যে, সেই আদি কাম থেকেই, তাহলে আমরা একটা বিষাক্ত বৃত্তের মধ্যে পড়ে যাই। কামনা বাসনা থেকে প্রহরী৪৪ গুলোর উৎপত্তি আর পাপ থেকে জন্ম নিয়েই তার পাপ বাসনাগুলোকে করে অবদমন। আবার যদি বলা হয়, সেগুলোর জন্ম পাপ-বাসনা থেকে নয়, অর্থনৈতিক, পারিপার্শ্বিক বা জীবনযুদ্ধের প্রয়োজনে সেগুলোর উৎপত্তি তাহলে কাম ব্যতীত আরো নানাবিধ ফ্যাকটার মানবজীবনে কার্যকরী বলে স্বীকার করে নিতে হয়।
ফ্রয়েড বলতে চেয়েছেন-আমাদের জীবনে অতৃপ্ত বাসনাগুলো মগ্ন চৈতন্য কার্যকরী থাকে বলে স্বপ্নে লক্ষণ সংক্রান্ত কার্যাবলিতে, অনবধানতাবশত কার্যবলিতে বা ভাবনাহীন কার্যাবলিতে সে অবরুদ্ধ বাসনা আত্মতৃপ্তি লাভ করে। কোন কোন ক্ষেত্রে তা হয়ত সত্য কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই যে তা সত্য তা কেমন করে বলা যায়? অনবধানতাবশত যদি একজন গভীর গর্তে পড়ে যায় তাহলে তার মনে ঐ পড়ে যাওয়ার বাসনা কার্যকরী ছিল বলে কি স্বীকার করতে হবে? তাতে তো মানুষের আদিম প্রবৃত্তিকেই অস্বীকার করা হয়।
রুদ্ধ বাসনামাত্রই সে কামজ তার প্রমাণও অত্যন্ত দুর্বল। কামজ না হয়েও আমাদের নানাবিধ বাসনা প্রকাশ পেতে পারে, এ সত্যটি অস্বীকার করেও ফ্রয়েড সত্যের অবমাননা করেছেন। মোটকথা, তার মতবাদের অনুকূল কতকগুলো তথ্যের উল্লেখ করে তাঁর বিরুদ্ধে মতের পোষণকারী তথ্যকে তিনি ধামাচাপা দিয়েছেন।
ম্যাকডুগাল
ফ্রয়েড ব্যতীত মানব-মানসের আদি রূপ নিয়ে অপর তিনজন মনস্তত্ত্ববিদও গভীরভাবে আলোচনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে ম্যাকডুগাল, এ্যাডলার ও জুঙের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। ম্যাকডুগাল যুদ্ধস্পৃহা বা Pugnacity-কেই মানব-মানসের আদি প্রবৃত্তি বলে ধারণা করেছেন। সাধারণত দেখা যায় শিশুদের মধ্যে অযথা একে অপরকে পীড়ন করার প্রবৃত্তি প্রকাশ পায়। সুযোগ ও সুবিধা পেলেই শিশুরা একে অপরকে পীড়ন করতে চায়। যদি মনে করা হয়, অদূর ভবিষ্যতে সে আক্রান্ত হয়ে তার সঙ্গীর দ্বারা ভীষণভাবে নির্যাতিত হবে, এ আশঙ্কার দ্বারা প্রণোদিত হয়েই শিশুরা এভাবে সঙ্গী-সাথীদের নানাভাবে পীড়ন করে, তা’হলে অবশ্য এ পীড়নের একটা সদুউত্তর পাওয়া যেতো। তবে যারা অত্যন্ত দুর্বল,যাদের দ্বারা কোন সময়েই কোন অত্যাচারের আশঙ্কা নেই, এরূপ ছেলেমেয়ের আক্রমণ করার কি কারণ থাকতে পারে? কাজেই এরূপ আক্রমণ করার প্রবৃত্তিকে ম্যাকডুগাল মানুষের আদি সহজাতপ্রবৃত্তি বলেছেন। তাঁর ধারণা মানুষ আজীবন এ প্রবৃত্তি দ্বারাই প্ররোচিত হয়ে নানাবিধ কাজকর্ম সম্পাদন করে। সাধারণত আমরা জীবনের নানা ক্ষেত্রে যে প্রতিযোগিতার দৃষ্টান্ত দেখতে পাই, ম্যাকডুগালের ধারণা- তা’ সেই আদি যুদ্ধস্পৃহারই এক পরিবর্তিত রূপ। বাল্যে,কৈশোরে ও যৌবনে এ প্রতিযোগিতার প্রবৃত্তি ভীষণভাবে দেখা দেয়। বিদ্যানিকেতন, খেলার মাঠ, ঘোড়া দৌড়, বল খেলা প্রভৃতিতে তা উৎকটভাবে দেখা দেয়। এগুলোকে আদিম হিংস্র প্রকৃতিরই রুপান্তর বলে গ্রহণ করতে হয়।
এ কথা অবশ্য অস্বীকার করার উপায় নেই যে, মানবজীবনে হিংসা-বিদ্বেষ রয়েছে। হয়ত বা সেই হিংসা-বিদ্বেষই ভদ্রভাবে প্রতিযোগিতার রূপ নেয়, তবে মানুষের জীবনে প্রেম, মৈত্রী ও ভালবাসার যে ক্রিয়াশীলতা রয়েছে, তাকে কিভাবে অস্বীকার করা যায়? কেবল অপরকে পীড়ন করেই কি মানুষ সুখ পায়? অপরকে সাহায্য ও সহায়তা করার প্রবৃত্তিও মানবজীবনে রয়েছে। তাকে অস্বীকার করলে সত্যের একটা দিককে অস্বীকার করা হয়। কাজেই ম্যাকডুগালের এ মতবাদের মধ্যে আংশিক সত্য রয়েছে বলে স্বীকার করা যায়। মানবজীবনে অপরাপর অনেকগুলো দিককে তিনি প্রকারান্তরে অস্বীকার করেছেন।
এ্যাডলার
মানবজীবনের আদি প্রবৃত্তি সম্বন্ধে অতি আধুনিককালে এ্যাডলারের মতবাদ অত্যন্ত প্রাধান্য লাভ করেছে। কাজেই সে সম্বন্ধেও আলোচনা করা প্রয়োজন। এ্যাডলারের মতে মানবজীবনে শক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষাই আদি বৃত্তি। তাঁর মতবাদ অনুসারে এ আকাঙ্খার উৎপত্তির মূলে রয়েছে নেতিবাচক মনোবৃত্তি। মানুষ মনে করে যে কোন সময় সে বিরুদ্ধ পক্ষীয় শক্তি দ্বারা পর্যুদস্ত হতে পারে। এজন্য সে পূর্বাহ্নেই শক্তি সঞ্চয় করে আত্মরক্ষা করতে চায়।
এ মতবাদের মধ্যেও যে আংশিক সত্য রয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। হয়ত এ জন্যই ছেলেবেলায় মানুষের যে যুদ্ধ-স্পৃহার মনোবৃত্তি দেখা দেয়, তাকে আত্মরক্ষারই এক সতর্ক সংস্করণ বলা যায়। তবে এ ব্যাখ্যার মধ্যেও ত্রুটি রয়েছে। কারণ অতি শৈশবেই মানুষের মনে যেমন অপর কোনও ব্যক্তির দ্বারা পর্যুদস্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়, তেমনি অপর মানুষ কতৃক সাহায্য লাভের আশ্বাসও তার মানসে বর্তমান থাকে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাদের সাময়িক সাহায্যের জন্য যার তার কাছে আবদার করে। হয়ত দু’ থেকে তিন চারজন একসঙ্গে একটা পথে রওয়ানা দিয়েছে- পথিমধ্যে একটা কুকুর যদি তাদের তাড়া করে, তখন তারা দৌড়ে যেয়ে সে কোন লোকের কাছে অথবা যে কোন বাড়িতে আশ্রয় নেয়। এক্ষেত্রে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে- মানুষ সব সময়ই অপরের সাহায্য ও সহায়তার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে।
জুঙ
মনোবিজ্ঞানবিদ জুঙের অভিমত এই যে, মানব-মনকে তিন স্তরে বিভক্ত করা যেতে পারে- ১.চৈতন্য, ২.ব্যাক্তিগত নির্জ্ঞান মন ও ৩. সমষ্টিগত নির্জ্ঞান মন।
ব্যক্তিগত নির্জ্ঞান মন দ্বারা এই বুঝা যায়-কোন কালে যে সব ধারণা বা সংবেদন সজ্ঞান মনে বিরাজ করতো, কোন কারণবশত তারা অপ্রীতিকর প্রতিপন্ন হলে কার্যকরী জীবনের সুবিধার জন্য তাদের অবদমন অরা হয়। এই অবদমনের ফলে মনোজগতের নতুন গ্রুপের সৃষ্টি হয়। সেই নতুন গ্রুপ স্বপ্ন ও কল্পনা ব্যতীত স্বাভাবিক চেতনাতে দেখা দেয় না। সমষ্টিগত নির্জ্ঞান মন দ্বারা বোঝায় যে, অবদমিত চিন্তাগুলো ব্যষ্টির চেতনালব্ধ নয়; বরং সেগুলো জাতীয় অভিজ্ঞতার ফল এবং তাদের একেবারে অতি পূর্ববরতী পূর্বপুরুষদের অভিজ্ঞতার ফল বলা যায়। জ্ঞানের এসব স্তর সব সময়েই মানব-মনে কার্যকরী এবং তারা সব সময়ই আমাদের কাজকর্মের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। তবু নির্জ্ঞান মন গৌণভাবে আমাদের জীবনে কার্যকরী।
জুঙের মত এই যে, আমাদের মন চার পন্থায় কাজ করে। ১.মনন ২.অনুভূতি ৩.সংবেদন ৪.বোধি। তাঁর ধারণা, মনন, অনুভূতি যুদ্ধ দ্বারা চালিত এবং তাদের প্রকাশ হয় অবরোহ পদ্ধতিতে। অপরদিকে সংবেদন ও বোধির জ্ঞানের তিন স্তরেই সম্বন্ধ রয়েছে। জুঙ বোধির দু’টা সংজ্ঞা দিয়েছেনঃ
১.সেই মানসিক ক্রিয়াকেই বোধি বলা যায়, যার ফলে প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে নির্জ্ঞান মনের স্তরে প্রেরণ করা হয়। এ ক্ষেত্রে প্রেরণ করা নয়-প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও নির্জ্ঞান মানসের ব্যাপার। বোধি নিস্ক্রিয় ও সক্রিয় দুইই হতে পারে। নিস্ক্রিয় অবস্থায় বোধির কার্যকারিতার ফলে অমূল প্রত্যক্ষ বা কল্পনার সৃষ্টি হয়। সেক্ষেত্রে বোধি সৃষ্টিধর্মী শক্তির পরিচয় প্রদান করে। মানব মানসে বোধি প্রধান শক্তি হিসেবে কার্যকরী হলে একদিকে যেমন মরমি স্বপ্নদ্রষ্টা অথবা স্রষ্টার সৃষ্টি করতে পারে,অপরদিকে তেমনি কল্পনাপ্রবণ পাগলের অথবা শিল্পীর জন্মদাতা হতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে বাস্তব জীবনে অনন্ত বিরামহীন অন্বেষণকারীও জন্ম দিতে পারে। এ শ্রেণীর বিশেষত্ব এই যে, সম্ভাবনাগুলো বাস্তবায়িত হলেই এগুলোর প্রতি এই শ্রেণীর লোকের আর কোন মনযোগ থাকে না। জুঙের ধারণার অনুসরণ করলে আমাদের স্বীকার করতে হয় মানব মনের মধ্যেই এমন একটা শক্তি রয়েছে, যার কার্যকারিতার ফলে আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ঠিক পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা লাভ না করে অন্য উপায়েও লাভ করা যায়। সে জ্ঞান ঠিক সজ্ঞান মনের ব্যাপার নয়। তার মধ্যে রয়েছে নির্জ্ঞান মনের কাজ। অথচ স্বজ্ঞান মনে যে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সৃষ্টি হয়, তার মধ্যে জ্ঞানের শক্তি রয়েছে প্রচুর। বোধি সে প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে নির্জ্ঞান মনের স্তরে প্রেরণ করে। এক্ষেত্রে এ প্রেরণ করা সজ্ঞান মনের ব্যাপার নয়। নির্জ্ঞান মন দ্বারাই তার কাজ সমাধা হয়। বোধি নিস্ক্রিয় অবস্থায় আমূল প্রত্যক্ষ বা কল্পনার সৃষ্টি করে। সক্রিয় অবস্থায় বোধির প্রভাবে একদিকে যেমন পাগল, অপরদিকে তেমনি প্রতিভাশালী শিল্পীরও সৃষ্টি হতে পারে।
জুঙের এবম্বিধ বিশ্লেষণ মানব জ্ঞানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। জুঙ মানবজীবনে ক্রিয়াশীল বিভিন্ন বৃত্তি ও প্রবৃত্তির কোন আলোচনা করেননি। কাজেই তাঁর এ আলোচনাকে একদেশদর্শী বলেই অভিহিত করা যায়।তবে তাঁর এ আলোচনার একটা বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, এ পর্যন্ত বোধিলব্ধ জ্ঞান সম্পর্কে আমাদের বৈজ্ঞানিক জগতে কোন আলোচনাই হয়নি। সে জ্ঞান যেমন হটাৎ আলোর ঝলকানির মত দেখা দেয়, তেমনি হটাৎ আবার অন্ধকারের রহস্যময় লোকে আশ্রয় নেয়। আমরা প্রত্যাদেশ বা ওহীকে(revelation) সেরূপ জ্ঞান বলে এতদিন পর্যন্ত ধারণা করে এসেছি। তার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তির অনুসন্ধান করিনি। জুঙের ধারার অনুসরণ করলে দেখা যায়, প্রত্যাদেশ কোন অবৈজ্ঞানিক বা অলীক কোন জ্ঞান নয়। তাকে বিশ্লেষণ করলেও তার মধ্যে বৈজ্ঞানিক সূত্র আবিস্কার করা যায়! এ কথা আজ সর্বজনবিদিত সত্য যে, হযরত মুহম্মদ মুস্তফা (সঃ) মানব সাধারণের মুক্তির জন্য দীর্ঘকাল যেসব চিন্তা করেছিলেন, তাঁকে তাঁর নির্জ্ঞান মনের স্তরে বোধি প্রেরণ করেছিল। সে নির্জ্ঞান মনের কার্যকারিতার ফলেই তিনি প্রত্যাদেশ লাভ করেছিলেন। এ কথার পরিপোষকতায় পাওয়া যায় একটা সর্বজনস্বীকৃত সত্য। তৎকালীন নানাবিধ সমস্যা সম্বন্ধে তাঁকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে হযরত(সঃ) সরাসরি কোন উত্তর দিতেন না। প্রত্যাদেশ বা ওহী নাযিল হলেই তাদের সমাধান বলে দিতেন। এতে একথাই প্রমাণিত হয়, তার মানসে সে প্রশ্নের উত্তরগুলোর সমাধানের ক্রিয়াশীলতা থাকত বর্তমান। বোধি সে প্রশ্নগুলো তার নির্জ্ঞান মানসে ঠেলে দিতো এবং সেখানে এ প্রশ্নগুলোর উত্তর তৈরি হলেই তিনি সেগুলো সম্বন্ধে তাঁর মতামত পরিস্কার ভাষায় বলে দিতেন।
এতে অবশ্য বোধির মানস সংক্রান্ত কার্যকারিতার ব্যাখ্যা হচ্ছে। তার মধ্যে যে বিষয়গত দিক (objective side) রয়েছে তা’ স্বীকার করা হচ্ছে। বোধির কার্যকারিতার ফলে বিষয়গত দিকে স্বয়ং কোন ফেরেশতার হাযির হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়।
তৃতীয় পরিচ্ছেদ
রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষা
রাষ্ট্রবিজ্ঞানে মানব জীবনে সম্বন্ধে আমরা নানাবিধ ধারণার সঙ্গে পরিচিত হই। মানুষকে কোথাও ভাবা হয়েছে সম্পূর্ণ একক ও নিঃসঙ্গ হিসেবে, আবার কোথাও ভাবা হয়েছে শ্রেণীবদ্ধ জীব হিসেবে। এ ধারণার সত্যা-সত্যের ওপরই বিভিন্ন মতবাদের সত্যাসত্য নির্ভরশীল।
অন্যদিকে দেখা যায়, বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদেরও কারণ রয়েছে, কোন্ বিশেষ পরিস্থিতিতে কোন্ বিশেষ মতবাদের উৎপত্তি-তার কারণ নির্ণয় করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়-এক সময় পোপের শাসনে সমস্ত ইউরোপ অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে, পোপের অধীনে বিভিন্ন দেশে মস্ত মস্ত জমিদারি গড়ে ওঠে, সে সব জমিদারির মালিক সামন্ত সর্দারের দেশের বুকে চালায় অকথ্য নির্যাতন। তাদের অধীন গরিব চাষিরা ভূমিদাসে৪৫ হয় পরিণত। এসব ভূমিদাস সামন্ত সর্দারের কাঠের কাঠুরে ও পানি সরবরাহকারী রূপে তাদের হাতের পুতুল হয়েই বেঁচে থাকে। এসব সামন্ত সর্দার দেশের উৎপাদন শক্তি তাদের হাতের মুঠোয় রেখে উৎপাদিত দ্রব্য যথেচ্ছা ভোগ করতে থাকে। তারা তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত উদ্ধৃত্ত অন্য দেশে বিক্রি করার জন্য অপর একদল লোককে দিতো। ক্রমে সেই বণিকগোষ্ঠী দেখতে পেলো দেশের সমস্ত চাহিদা পূরণের জন্য উৎপাদন করে ভূমিদাসেরা। সামন্ত সর্দারের বসে বসে ভোগ করে অথচ উৎপাদিত দ্রব্যের ওপর তাদেরই মালিকানার দওলতে তারা বণিকদের উদ্ধৃত্তকে যথেচ্ছা চালান দেওয়ার সুবিধা দেয় না। কাজেই এ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অবিচারমূলক। তার পরিবর্তে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়ারূপে দেখা দেয় নতুন দার্শনিক মতবাদ। তাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় উদারনৈতিক মতবাদ।
এ মতবাদের সূচনা হয় ইতালীর রেনেসাঁয়। জার্মানির রিফরমেশনে হয় তার বিকাশ এবং ফরাসি রাষ্ট্রবিপ্লবে তা পূর্ণ পরিণতি লাভ করে। ইতালীর রাজনৈতিক চিন্তানায়ক ম্যাকিয়াভেলিই৪৬ সর্বপ্রথম দেশের শাসন ব্যবস্থায় রাজকীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। পোপের আধিপত্য বিনাশের জন্য তার সূচনা হলেও পরবর্তীকালে ধর্মের রাজ্যে ব্যক্তি স্বাধীনতার নীতি গৃহীত হয়। আল্লাহ্ ও মানুষের অন্তর্বর্তী অন্য কোন ব্যক্তি বা শ্রেনীর আধিপত্য অস্বীকার করে মার্টিন লুথার তাঁর প্রটেসট্যান্ট ধর্ম প্রচার করেন এবং ফরাসি রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় রবোসপিয়ারের জীবনে সাম্য,মৈত্রী ও স্বাধীনতা শ্লোগান হয়ে পড়ে।
এ মতবাদের নঞর্থক দিকের বিচার করলে এক সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিদ্রোহ বলা যেতে পারে; রাজকীয় শাসন ও তার উত্তরাধিকারকে অস্বীকার না করলেও তাকে সীমাবদ্ধ করার দিকে উদারনৈতিক মতবাদের ঝোঁক ছিল। তার সদর্থক দিকের আলোচনা করলে বোঝা যায়-মানুষের অবাধ স্বাধীনতার স্বপ্নই ছিল উদারনৈতিক মতবাদের সর্বপ্রথম কাম্য। ব্যবসা-বাণিজ্যে রাজার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকা এ মতবাদ বরদাশ্ত করেনি। এর বক্তব্য হল, মানুষকে স্বাধীনতা দিতে হবে। স্বাধীনতা পেলে সে যেমন উৎপাদন করতে পারবে তেমনি উৎপাদিত দ্রব্যেরও বিলি-ব্যবস্থা করতে পারে-মানুষের মাঝে কোন বিশেষ প্রাণীর আধিপত্য স্বীকার করে নিলে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থায় নানা অসুবিধার সৃষ্টি হয়।
এভাবে, সমসাময়িক সমাজ ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়ারূপেই দেখা দেয় উদারনৈতিক মতবাদ। সেই উদারনৈতিক মতবাদই কালে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ এবং সর্বশেষে ধনতন্ত্রে পরিণত হয়। ধনতন্রের পূর্ণ প্রতিষ্ঠাকালে তার নানাবিধ ত্রুটির ফলে সমাজজীবনে যে অসাম্যের সৃষ্টি হয় তারই নিরসনকল্পে কার্ল মার্কস ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রচার করেন তাঁর বস্তুতান্ত্রিক সমাজবাদ। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার অসঙ্গতি তাঁর চোখে ভয়াবহ রূপ নিয়ে দেখা দেয়। তাই তাকে উৎখাত করার মানসে তিনি ইতিহাসের অভিনব ব্যাখ্যা করেন।
কাজেই, এভাবে উৎপত্তির কারণ বিশ্লেষণ করে রাজনৈতিক মতবাদের মূল্য নিরূপণ করা যায়। তবে এতে আপত্তির কারণ আছে। প্রথমত দেখতে হবে, যে কোন পরিবেশের চাপেই তার জন্ম হোক না কেন, যে কোন মতবাদের সত্যাসত্য নির্ভর করে তার অন্তর্নিহিত যুক্তিবত্তার উপর আমাদের বোঝায় সুবিধার জন্য কোন মতবাদের উৎপত্তির কারণ নির্ণয় করতে পারি, তবে এতে মতবাদের ঠিক মূল্য নিরূপণ হয় না। সে মতবাদ গ্রহণের ফলে মানবজীবনের সুষ্ঠু বিকাশ হয় কিনা তা আমাদের ভেবে দেখা দরকার।
দ্বিতীয়ত একই পরিবেশে একই অপব্যবস্থায় উত্যক্ত হয়েও দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন মতবাদ গড়ে উঠতে পারে। পুজিঁবাদী সমাজের পাপাচারে উত্যক্ত হয়ে মার্কস প্রচার করেন বস্তুতান্ত্রিক সমাজবাদ এবং এ পুঁজিবাদের অত্যাচার আরও চরমসীমায় পৌঁছায় পর তার নানাবিধ অকল্যাণে অতিষ্ঠ হয়ে টলষ্টয় প্রচার করেন তাঁর খ্রিষ্টীয় সমাজবাদ। কাজেই পরিবেশ দ্বারা মতবাদের মূল্য নির্ণয় নিতান্তই অবিচারমূলক কাজ। তাই রাজনৈতিক মতবাদের মূল্য নির্ণয়ে আমরা তার গুণাগুণের বিচার করবো। এ পর্যন্ত যত সব রাজনৈতিক মতবাদের উৎপত্তি হয়েছে তাদের মধ্যে সমাজজীবনে আদি সংখ্যা হিসেবে কোথাও ব্যক্তিকে, আবার কোথাও সমষ্টিকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। রাজনৈতিক মতবাদগুলোকে তাই অনায়াসেই দু’ভাগ করা যায়। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ
উদারনৈতিক মতবাদের ভিত্তিস্বরূপ যে জীবন-দর্শন গড়ে উঠেছে তাকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক বলার অর্থ এই যে, জগতের অতবার মানব-সমাজের আদি উপাদানরূপে এখানে ব্যক্তির সত্তাকেই স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। মতের বিভিন্নতা সত্ত্বেও লক৪৭ থেকে শুরু করে এ্যাডাম স্মিথ৪৮ পর্যন্ত যে চিন্তাধারার ইতিহাস পাওয়া যায় তার সারসংক্ষেপে এই বলা যায়ঃ মানুষের চিন্তারাজ্যে চলেছে আণবিক মনস্তত্ত্বের খেলা। রাষ্ট্রীয় জীবনে চলছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বা প্রাধান্যের চেষ্টা। মানুষ একক হয়েই জন্মগ্রহন করে; সেই একক মানুষের সঙ্গে বিভিন্ন মানুষের সংস্পর্শ থেকে গড়ে ওঠে তার সমাজ, তার জাতি, তার রাষ্ট্র। মানুষের আদিসত্তায় রয়েছে তার অহংবোধ৪৯ ও স্বার্থপরতা।৫০ এই আদি মানবের চলাফেরায়,ব্যবসা-বাণিজ্য, চিন্তাধারায় অবাধ স্বাধীনতা দিতে হবে-তার কাজ-কর্মে যাতে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না হয় তার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়েই রাষ্ট্র গড়ে উঠবে।
প্রশ্ন উঠেঃ মানুষকে যদি এভাবে স্বাধীনতা দেওয়া যায় তা’হলে তো তাদের মধ্যে সবসময়ই মারামারি-কাটাকাটি লেগেই থাকবে। প্রত্যেকে যদি তার সার্থসিদ্ধির জন্যই চেষ্টা করে তাহলে তো একের স্বার্থের সঙ্গে অপরের স্বার্থের সংঘর্ষের ফলে সবসময়ই মানবজীবনে দ্বন্দ্ব-কোলাহলের সৃষ্টি হবে-মানুষ শান্তিতে দুদিন তিষ্ঠাতে পারবে না। তার উত্তরে লক ধারণা করে নিয়েছেন, প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ পশুর মত পরস্পরের সঙ্গে শত্রুতায় লিপ্ত নয়, সেখানেও মানুষের মাঝে শান্তি বিরাজ করছে এবং মানুষ বিচারবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়। প্রকৃতির রাজ্যে অরাজকতার কোন স্থান নেই। প্রকৃতির আইনের প্রভাবে মানুষের স্বাভাবিক অধিকার,স্বাধীনতা ও সম্পত্তি ভোগ করার সুযোগ থাকে। তা সত্ত্বেও প্রকৃতির রাজ্যে আইনকে ব্যাখ্যা করার জন্য বা তার প্রয়োগের জন্য কোন প্রতিষ্ঠান নেই, যদিও সেই আইন-কানুন সকল মানুষের মনেই কার্যকরী। তবুও বুদ্ধির তারতম্যের দরুন এবং স্বার্থের বিভিন্নতার ফলে নানাবিধ দ্বন্দ্বের উৎপত্তি হয়। এর জন্যই সমাজ গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হয়। লকের মতে প্রত্যেক ব্যষ্টিই তার জীবন, স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য অপরের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়; তার ফলেই সম্প্রদায়ও গড়ে ওঠে। এ চুক্তির মর্ম মতে ব্যষ্টিকে প্রাকৃতিক-আইন কার্যে পরিণত করার অধিকার ত্যাগ করতে হয় এবং অপরাধের শাস্তি দান করার অধিকার থেকেও বঞ্চিত হতে হয়। ব্যষ্টিকে অবশ্য তার সমস্ত অধিকার ত্যাগ করতে হয় না, কতকগুলো অধিকার সম্প্রদায়ের হাতে তুলে দিতে হয়। তাও আবার কোন বিশেষ ব্যক্তি বা কোন দলের হাতে সে সেই অধিকারগুলো অর্পণ করে না, গোটা সম্প্রদায়ের হাতে সেগুলো ন্যস্ত করে সে নিশ্চিত হয়।
লক মানুষকে বুদ্ধিপ্রধান জীবরূপেই ধারণা করেছেন। প্রকৃতির বুকে এই বুদ্ধির দওলতেই মানুষ তার অধিকার বজায় রেখে অন্যের সঙ্গে বিরোধ না করেও চলতে পারে; তবে তাতে নানা অসুবিধার সৃষ্টি হয় বলেই মানুষ তার অধিকার সংকুচিত করে তার নিজের মঙ্গলের জন্যই সম্প্রদায়ের হাতে তার প্রাকৃতিক অধিকারগুলো তুলে দেয়।
সামাজিক চুক্তিবাদ
এই সব মতবাদের বিরুদ্ধে ফরাসি দার্শনিক ‘রুশো’ এক নতুন মতের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বড় আক্ষেপ করেই বলেছেন, মানুষ স্বাধীন হয়েই জন্মগ্রহণ করে কিন্তু সে সর্বদাই শিকলাবদ্ধ থাকে। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের ওপর কোন আদেশ-নিষেধ, আইন-কানুন চাপানো যায় না। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে নানা নীতি, নানা আইন মেনে চলতে এবং তার ফলে তার জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। ‘রুশো’ মানুষকে আবার তার স্বাভাবিক ধর্মে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আহব্বান করেছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল, প্রকৃতির কোলে স্বাভাবিক পরিবেশে মানুষের প্রক্ষোভে পূর্ণ বিকাশ লাভ করতে পারে, অপ্রাকৃত মানব-সৃষ্ট পরিবেশ তা’ হওয়া সম্ভব নয়। প্রকৃতিতে পশু, পাখি, কারো কোন দুঃখ-দৈন্য নেই। তারা অবাধে বিহার করে, তাদের অভাবেরও কোন তাড়না নেই-কারণ অভাবে উৎপত্তি হলেই তার বুদ্ধির নিবৃত্তির উপায় তার পক্ষে সহজলভ্য। মানুষ তার বুদ্ধির প্যাঁচে গড়ে তুলছে তার সমাজ, তার রাষ্ট্র, তার নানাবিধ আচার-অনুষ্ঠান। এতে মাববজীবনের পরিপূর্ণ স্ফূর্তি লাভ হয় না বলেই জীবনে যতো দুঃখের হয় উৎপত্তি। তার ধারণা ছিল, প্রকৃতি থেকে বিকাশের ধারায় কোন এককালে মানুষকে তার জন্মগত স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে হয় তার আত্মরক্ষার জন্য; অন্য মানুষের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সে গড়ে তোলে তার গোত্র, সম্প্রদায় ও রাষ্ট্র। রুশোর জীবনে তাই সর্বপ্রধান সমস্যা ছিল, অন্যান্য লোকের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে রাষ্ট্র গঠন করেও ব্যষ্টি কিভাবে তার স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা বজায় রাখতে পারে তার উপায় উদ্ভাবন।
তাঁর এ মতবাদকে বলা হয় সামাজিক চুক্তিবাদ৫১। এ চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে ব্যষ্টি তার সমস্ত অধিকার সম্প্রদায়ের হাতে ন্যস্ত করে। সকলকে একইভাবে সম্প্রদায়ের হাতে তাদের অধিকার অর্পণ করতে হয় বলে অন্যের পক্ষে পীড়াদায়ক কোন শর্ত আরোপিত হওয়ার সুযোগ পায় না। সামাজিক চুক্তিমতে সম্প্রদায়ই সার্বভৌমত্ব৫২ লাভ করে। কারণ ব্যষ্টি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই তার সমস্ত অধিকার সম্প্রদায়ের হাতে তুলে দেয়। তবুও এই সার্বভৌম সম্প্রদায় ব্যষ্টির পক্ষে ক্ষতিকর কোন কাজ করতে পারে না। কেননা ব্যষ্টির স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অধিকার ত্যাগের ফলেই সম্প্রদায়ের হয় প্রতিষ্ঠা। রুশোর জবানীতেই তাঁর মতবাদ পরিস্কারভাবে ফুটে উঠেছে;
আমরা প্রত্যেকেই তার শরীর ও শক্তি সর্বসাধারণের মহান ইচ্ছার অধীনে সমর্পণ করি এবং আমাদের সংঘবদ্ধ অবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমাদের সমগ্র সম্প্রদায়ের অবিভাজ্য অংশরূপে গ্রহণ করি। এই সমাবেশের ফলে একটা নৈতিক ও সংঘবদ্ধ সংগঠনের সৃষ্টি হয়-যার নিস্ক্রিয় অবস্থার নাম রাষ্ট্র৫৩ সক্রিয় অবস্থার নাম সার্বভৌমত্ব এবং অনুরুপ কোন সংগঠনের সম্বন্ধে যাকে বলা হয় শক্তি।৫৪* (Rousseau-Social Contract.)
ব্যষ্টি সম্বন্ধে এত উচ্চ ধারণা পোষণ করা সত্ত্বেও রুশো ব্যক্তিগত সম্পত্তি সংরক্ষণে কোন প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেননি। তিনি পরিস্কার ভাষায় বলেছেনঃ
রাষ্ট্রে সঙ্গে নাগরিকদের সম্বন্ধের ফলে রাষ্ট্রই তার নাগরিকদের সম্পত্তির একমাত্র মালিক।* (Rousseau-Social Contract.)
সূক্ষ্ম বিচারে প্রবৃত্তি হলে দেখা যায়, রুশোর ভাষায় অনেক পরস্পরবিরোধী মতামত সন্নিবেশিত রয়েছে। ব্যষ্টি যদি সম্পুর্ণ স্বাধীন হয় তাহলে সম্প্রদায় বা রাষ্ট্রে হাতে তার সম্পূর্ণ অধিকার তখনই ত্যাগ করতে পারে যদি তার ব্যক্তিগত অধিকার কোন অংশেই ক্ষুণ্ন না হয়। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অধিকার তো ক্ষুণ্ন হয়েছেই, অধিকন্তু তাকে সাধারণের ইচ্ছার ওপর তার সমস্ত অধিকার ছেড়ে দিতে হয়েছে।
মানুষের মনে যদি সর্বসাধারণের হিত করার মত কোন পরার্থপর৫৫ সৎ প্রবৃত্তি না থাকে, তাহলে তার অহংবোধ৫৬ কিছুতেই তাকে এভাবে আত্মসমর্পণ করতে দেবে না। কাজেই ব্যষ্টির স্বাতন্ত্র্য৫৭ বা তার অহংবোধ স্বীকার করে রাষ্ট্র বা তার সার্বভৌমত্তে পৌঁছা রুশোর পক্ষে যুক্তিসম্মত হয়নি।
প্রকৃতপক্ষে রুশো তাঁর মতবাদের সমর্থনে কোন মননশীলতার অবতারণা করেননি। মরিমীবাদীদের মত এক বিশেষ ভাবাবেশ উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি তাঁর দার্শনিক মতবাদ গড়ে তুলেছেন। বৈজ্ঞানিক যুক্তির সাহায্যে নয়, ভাবের আবেশে ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে মানব মনে কার্যকর করে তোলাই ছিল রুশোর জীবনের সাধনা। তাঁর জোরালো ভাষার আবেদনে ফরাসি রাষ্ট্রবিপ্লব হয়ত সহজে ঘটতে পেরেছিল কারণ তার পশ্চাতে ছিল দীর্ঘকালের নির্যাতিত মানবতার মুক্তির প্রয়াস। তবুও যুক্তির কষ্টিরপাথরে বিচার করলে তাতে নানা ত্রুটি সহজেই লক্ষ্য করা যায়।
উদারনৈতিক মতবাদ বা সামাজিক চুক্তিবাদের মধ্যে ব্যষ্টি সম্বন্ধে ধারণার বিশেষ কোন প্রভেদ নেই। উভয়ক্ষেত্রেই ব্যষ্টিকে কল্পনা করা হয়েছে একক ও সম্বন্ধহীনভাবে। পূর্বেই বলা হয়েছে, মনোবিজ্ঞানের জগতে যেমন আণবিক মনস্তত্ত্বের সূত্রপাত তেমনি মানুষকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন,স্বার্থান্বেষী জীবরূপে গ্রহণ করে এই নব্য ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ দুনিয়ার ইতিহাসে এক অভিনব চিন্তাধারার প্রবর্তন করে।
উদারনৈতিক মতবাদের আলোচনায় আমার দেখেছি কোনও বিশেষ কালে এক শ্রেণীর আধিপত্য বিস্তারের ফলে দেশের উদ্ধৃত্তের হয় অপব্যবহার। সেই বিশেষ শ্রেণী তার নিজের স্বার্থে সে উদ্ধৃত্তকে ব্যবহার করে। তারই ফলে শ্রেণী-সংঘর্ষ হয়ে ওঠে অনিবার্য। তাই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সমতা সাধন করার জন্য ব্যক্তিকে দিতে হয় অবাধ স্বাধীনতা। সে অবাধ স্বাধীনতার ফলে কোন বিশেষ শ্রেণী আর শোষণের সুযোগ পায় না। তার জন্য মানুষের আসল প্রকৃতির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে এক নতুন দর্শনের হয় সৃষ্টি। সে দর্শনের মোদ্দা ভাবার্থ এই ঃ মানুষ স্বভাবতই স্বার্থপর। তার উৎপাদনের প্রাথমিক কারণ,অভাবের নিরসন হলেও উদ্ধৃত্ত থেকে সে স্বভাবতই মুনাফা করতে চায়। সে সুযোগে বাধা উপস্থিত হলে মানুষের সঙ্গে মানুষের সংঘর্ষের হয়ে পড়ে অনিবার্য। সেই সংঘর্ষকে এড়াতে হলে মানুষের স্বাধীনতার কোন সীমারেখা টেনে নেয়া সঙ্গত নয়, তাকে দিতে হয় নিজের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের অধিকার। তা’ পেলেই সে তার অভাব নিরসনের জন্য যেমন করবে পর্যাপ্ত উৎপাদন-তেমনি সে উদ্ধৃত্তকেও সে তার নিজের সুবিধার জন্য ব্যবহার করবে। এই দার্শনিক মতবাদের নীতি হল ব্যক্তিকে একা থাকতে দাও৫৮।
ধনতন্ত্র
উদারনৈতিক মতবাদই পরিশেষে ধনতন্ত্রে বিকৃত হয়ে পড়ে। মানুষের সঙ্গে মানুষের বিশেষ করে যে কোন দেশের পুরোহিত ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর সংঘর্ষের অবসানের জন্য উৎপাদন বণ্টন ব্যবস্থার সুসামঞ্জস্যের জন্য এ নতুন মতবাদের সৃষ্টি হলেও তার চরম অভিব্যক্তিতে নয় ধনতন্ত্রের সৃষ্টি। প্রত্যেক ব্যক্তিকে উৎপাদনের অবাধ সুবিধা দেওয়ার ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আবার শুরু হয় সংঘাত ও সংঘর্ষ-আবার শুরু হয় যুদ্ধ। এ মতবাদের কল্যাণে সর্বসাধারণ মানুষ, বিশেষ করে উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ীরা অবাধ স্বাধীনতা পেয়ে তাদের ইচ্ছামত মূলধন খাটিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যে রাতারাতি দৈত্য-দানোবের মত পা ফেলে অগ্রসর হয়। দুদিনেই দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ তারা নিজেদের কুক্ষিগত করে নেয়। তার রক্ত-রাঙা ইতিহাস পাওয়া যায় অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় জাতিগুলোর কর্মসূচিতে। পৃথিবীর নানাদেশে ব্যবসায়-বাণিজ্য উপলক্ষে ছড়িয়ে পড়ে শাসন ও শোষণ করে ইউরোপীয় জাতিগুলো দুনিয়ার বুকের রক্ত শুষে নিয়েছে।
ধনতন্রের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি হয়। বিদেশের লোককে শোষণ করতে হলে স্বদেশের লোকের মধ্যে দলীয় মানসিকতার সৃষ্টি হওয়া দরকার। যতই ব্যষ্টির গুণগান করা হোক না কেন, একাকী কোন ব্যক্তি কোথাও শোষণ করতে পারে না- তার জন্য তার দেশের সর্বসাধারণের সম্মতি ও সহযোগিতার প্রয়োজন।
সেইজন্য পুঁজিবাদের প্রথম সফলতার যুগে দেশের সাহিত্যিকরা জাতীয়তার জয়গান গেয়ে দেশের সর্বসাধারণকে উদ্ধুদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন-
Rule Britania, rule the waves
Britain never shall be slaves.
একবারে নিছক কবি-জনোচিত উচ্ছ্বাস নয়। তার মূলে রয়েছে অন্যান্য জাতিকে শোষণ করার জন্য দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করার অভিসন্ধি। এ মনোবৃত্তি বিকশিত হলেই অন্য জাতির প্রতি স্বভাবত বৈরীভাব জন্মে। কারণ, এর মূলে রয়েছে জগৎ গ্রাস করার বাসনা। কাজেই দেখা যায়, পুঁজিবাদী মনোবৃত্তি থেকেই জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি হয় এবং জাতীয়বাদের উৎপত্তি হলেই পুঁজিবাদী মনোবৃত্তি আরও তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।
ধনতন্র বিকাশের প্রথম পর্যায়ে দেশে বিদেশে মূলধন বিস্তারের ফলে এ মতবাদের উপাসক ধনতান্ত্রিক দেশগুলো ফেঁপে ওঠে। বিশেষত শিল্পবিপ্লবের পর ইউরোপীয় দেশগুলো উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করে। কিন্তু জোয়ারের শেষে ভাটার টানে যখন দেশ-বিদেশে মূলধন খাটানোর আর সুবিধা থাকে না, তখনই ধনতন্ত্রবাদী বুঝতে পারে তার অন্তর্নিহিত গলদ। যখন দেশের টাকা বিদেশে খাটিয়ে পরধন আত্মসাৎ করার আর কোন সুবিধা থাকে না-যখন নিজের দেশের মজদুর শ্রেণী বিদ্রোহ ঘোষণা করে- “তখন দেশের সুখ-শান্তি আর সুবিধার নামে করতে হয় পশু শক্তির প্রয়োগ”। তাই ধনতন্রের সংকোচনের যুগে তারই প্রাতিষ্ঠানিক কৌশল হিসেবে হয় ফ্যাসিবাদের উৎপত্তি।*(Harlod Lasky, Reflections on the Revolution of our times.)
চতুর্থ পরিচ্ছেদ
সমষ্টিকেন্দ্রিক মতবাদ
উদারনৈতিক মতবাদ বা তার বংশের ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ বা সামাজিক চুক্তিবাদে মানব-জীবন সম্বন্ধে ধারণার কোন বিশেষ প্রভেদ নেই। সর্বত্রই মানুষকে ভাবা হয়েছে এককরুপে। ধনতন্ত্রে সেই মানুষকে কেবল একক ভাবা হয়নি, তাকে স্বভাবতই ভাবা হয়েছে স্বার্থপররূপে। অথচ বিরাট মানব-জীবন এসব মতবাদের বিরুদ্ধে এক তীব্র প্রতিবাদের মূর্ত প্রতীক। মানব-জীবন নিয়ে আলোচনা করলেই দেখা যায় মানুষ সব সময়েই যূথচারী জীব৫৯। জীবনের আদিতেই সে অপরের সঙ্গ কামনা করে। কোন দুর্বিপাকে সে সমাজজীবনে থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে জীবন তার কাছে হয়ে পড়ে দুর্বিষহ। সে কেবল অপরের সঙ্গই কামনা করে না, অপরের মঙ্গল কামনাও সে করে। আত্মরক্ষা, আত্মপ্রতিষ্ঠা তার জীবনে প্রধান মনোবৃত্তি হলেও প্রেম, দয়া, মায়া, বাৎসল্য, পরার্থপরতা তার জীবনে বিশেষভাবেই কার্যকর। মানুষের মাঝে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ঠ্য থাকলেও তাদের মধ্যে রয়েছে এক সার্বিক ঐক্য,সে ঐক্যের সুরটি বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে ইয়াহূদীদের ধর্মে।
য়াহূদী ধর্ম
য়াহূদীদের ধর্মে মানুষের বৃহত্তর সত্তা বিকাশের জন্য নানাবিধ আদেশ রয়েছে। স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতা, অহংবোধ ও পরার্থিতার দ্বন্দের ফলেই আরম্ভ হয় ব্যষ্টিজীবনে দ্বন্দ্ব। ব্যষ্টি ও সমষ্টির স্বার্থের সমতা সাধনের জন্য য়াহূদীয়া অভিনব উপায় গ্রহণ করেছিল। পরলোকগত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী রামজে ম্যাকডোনাল্ড বলেন, “ বোধ হয় অন্য কোনও জাতীয় আইন ও আচার ইসরাইলীদের মত দলীয়৬০ এবং ব্যষ্টিজীবনের সমতা সাধনের চেষ্টা করেনি। তারা ছিল অনুগৃহীত৬১ জাতি তাদের ধর্ম ব্যষ্টিকেন্দ্রিক হওয়া সত্ত্বেও জাতীয়তার ওপর প্রতিষ্ঠিত।...... (সর্বাবস্থায়ই) তারা ব্যক্তিগত অধিকার অক্ষুণ্ন রেখেছে। এ জন্যই মূসার অনুশাসনে বা তাঁর বিভিন্ন ধারায় দাসপ্রথা ও ভীতিপ্রদ দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে নানাবিধ প্রতিরোধ ব্যবস্থা বিদ্যমান। প্রত্যেক সাত বৎসর অন্তর য়াহূদীদের দাসগুলোকে মুক্তি দেওয়া হয়। বন্ধকাবদ্ধ বস্ত্রাদি প্রত্যেক দিন দিবাশেষে ফিরিয়ে দিতে হয়। প্রত্যেক সাত বৎসরের শেষে মাঠগুলো পতিত রাখতে হয়, যাতে সেগুলো সাধারণের সম্পত্তিরূপে গণ্য হতে পারে। জমিতে চাষীর অধিকার অক্ষুণ্ন রাখার জন্য ধর্মীয় ও সরকারি বিধান প্রয়োগ করা হয়”।* (Ramsay Macdonal d: Social Development p:21)
অনেকেই মনে করেন য়াহূদী ধর্মে এরূপ সাম্যবাদমূলক নীতি থাকলেও বাস্তব জীবনে তার রুপায়ণ হয়নি। এককালে য়াহূদীদের মত এরূপ শোষক জাতি দুনিয়ার দ্বিতীয় ছিল না। য়াহূদীদের কোন রাষ্ট্রেরও ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাই রাজনীতিতে এ মতবাদের পরীক্ষা হয়নি।** ( নবজাত ইসরাইল রাষ্ট্র কিভাবে পরিচালিত হবে, তা লক্ষণীয়।)
তবুও মানুষের আদি প্রকৃতিতে সংঘ-চেতনার৬২ দৃষ্টান্ত হিসেবে তার মূল্য রয়েছে যথেষ্ট। হয়ত ব্যষ্টি ও সমষ্টির সংস্থান ব্যবস্থা হিসেবে তাতে কোন ফাঁক থাকার দরুনই তা বাস্তব জীবনে কার্যকরী হতে পারেনি।
প্রাথমিক প্লেটো
মহাপ্রাণ প্লেটোর কালজয়ী দৃষ্টির আলোয় খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে এ সত্যটি প্রতিভাত হয়েছিল। তাঁর রিপাবলিকে৬৩ তিনি মানবজাতিকে সাধারণ মানব,সৈনিক এবং অভিভাবক-এই তিন ভাগে বিভক্ত করলেও মানুষের মাঝে যে ঐক্য বর্তমান তা তাঁর কাছে ধরা পড়েছিল। তিনি ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ সাধন করে সমস্ত বিত্ত রাষ্ট্রের করায়ত্ত করতে চেয়েছিলেন।
তাঁর ধারণা ছিল, অভিভাবকগণের ছোট ছোট বাড়ি থাকবে এবং তারা মোটা ভাতে জীবন যাপন করবে। শিবিরে যেভাবে মানুষ জীবন যাপন করে, তারা তেমনিভাবে বসবাস করবে, একত্রে আহার করবে-তাদের প্রয়োজনে অতিরিক্ত কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে না, সোনা-রুপার প্রচলন নিষিদ্ধ থাকবে। ধনী না হলেও তারা কেন সুখী হতে পারবে না? নগরের উদ্দেশ্য হবে সকল লোকের উন্নতি বিধান,কোন বিশেষ শ্রেণীর সুখসাধন নয়।
এমনকি স্ত্রীলোক ও সন্তানগণও সাধারণ সম্পত্তি পরিগণিত হবে। প্লেটোর রিপাবলিকে যে আদর্শের অনুসরণের জন্য আদেশ করা হয়েছে তাতে মনের পরহিতব্রতের প্রতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি রাখা হয়েছে এবং তাকে বাস্তবজীবনে রুপায়িত করার সাধনা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তবুও ভাবতে হবে মানব মনের স্বাভাবিক অহংবোধ থেকে কিভাবে সে পরাথির্কতার পথে অগ্রসর হবে। প্লেটো সে পদ্ধতি বাতলে দেন নি। তাই তাঁর এই আদর্শ সুখ-রাজ্যের৬৪ সমালোচনায় বলা যায়- “এতে প্রমাণ ও খণ্ডনের কোন প্রশ্নই ওঠে না। এখানে আসল প্রশ্ন হল, এ রকম রাষ্ট্র পছন্দ হয় কিনা। যদি কারো পছন্দ হয়, তা হলে ভাল-যদি না হয়, তা হলে তা খারাপ। যদি অনেক লোকের তা পছন্দ হয় এবং অনেকের তা না হয়-তা হলে যুক্তি নয়, প্রকাশ্যে বা লুক্কায়িত শক্তির জোরেই হবে তার প্রতিষ্ঠা।* (Bertrand Russell: History of Western Philosophical Thoughts.)
এ রাষ্ট্রে ব্যক্তি-স্বাধীনতার কোন অর্থ নেই। কারণ এ রাষ্ট্র জনসাধারণের ইচ্ছা ও সম্মতির উপর গড়ে ওঠে না।
মাজদাক
ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্বে ইরানে মাজদাকও মানব-প্রকৃতির পরার্থিতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে এক অভিনব মতবাদ প্রচার করেছিলেন। যাতে দেশের সম্পদ সকলেই সমানভাবে ভোগ করতে পারে, তার জন্য ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ করার উদ্দেশ্যে তিনি বিবাহ প্রথা রহিত করার জন্য ঘোষণা করেছিলেন-“ যে ভাবে সকলে বায়ু ও জল উপভোগ করে, সেভাবেই স্ত্রীলোকগণকেও ভোগ করবে* (Mushir Hussain Kidwai-Pan-islamism and Bolshevism p.51)। মাজদাক কেবল যৌন-জীবনেরই যৌথানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন বলে এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাতে সংঘবদ্ধ জীবনের কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা করতে পারেননি বলে তাঁর এ মতবাদ বেশিদিন টিকে থাকেনি।
কার্ল মার্কস
মার্কস ছিলেন দার্শনিক হেগেলের শিষ্য। জার্মান দার্শনিক হেগেলের নিকট স্বতঃসিদ্ধ৬৫ ছিল যা কিছু সত্য তাই যুক্তিসঙ্গত, আর যা’ যুক্তিসঙ্গত, তা-ই সত্য। তাঁর স্বতঃসিদ্ধের শেষ অর্ধাংশ অনেকেই স্বীকার করতে রাজি নন।
জগতে যা কিছু রয়েছে তাকে অবশ্য বলা চলে যুক্তিসঙ্গত। জগতে যা কিছু বিদ্যমান তার জন্য কোন জ্যামিতিক প্রমাণ দেয়া সম্ভবপর নয়। তবুও তাদের অস্তিত্বের পক্ষে উপযুক্ত কারণ থাকা দরকার। এ দুনিয়ার অস্তিত্বের পক্ষে উপযুক্ত রয়েছে এ দুনিয়ার বুকে। এ মানব সভ্যতার দর্শনবিজ্ঞানে এ নীতি স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। এ দুনিয়ায় যদি যুক্তি বা বিচারের কোন সুযোগ না থাকে, তাহলে বৈজ্ঞানিক গবেষণা এক পা’ও অগ্রসর হতে পারে না। কারণ বিজ্ঞানের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে আবিস্কার।
তবে যা কিছু যুক্তিসজ্ঞত তাই কেমন করে সত্য হতে পারে? আমাদের তর্ক-শাস্ত্রজাত যুক্তিধারার স্রোতে এমন অনেক অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ সত্তাকে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য হই, যার কোন অস্তিত্ব বাস্তব জীবনে কল্পনা করাও আলেয়ার পেছনে ছোটার মত হাস্যকর। তবুও এ সূত্রের ভিত্তির ওপর নির্ভর করে হেগেল গড়ে তুলেছেন তাঁর দার্শনিক সৌধ।
দুনিয়ার অস্তিত্বে আমরা বিশ্বাস করি না করি, কোন কিছুর ধারণা নিয়েই আমাদের দার্শনিক অন্বেষণ আরম্ভ করতে হয়। দর্শনের ক্ষেত্রে চরম নাস্তিবাদ৬৬ অচল। তাই বিশ্বাসসত্তাকে যদি বলা হয় অস্তিত্ব৬৭ তা’হলে সেই অস্তিত্বকে আমরা অস্তিত্বের৬৮ আলোকেই বুঝতে পারি। অস্তিত্ব ও অস্তিত্বের দ্বন্দ্বের ফলেই আমাদের মানস এর মধ্যে আশ্রয় নেয়। Becoming- এর মাঝে অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব দুই রয়েছে, অথচ তার মাঝে উভয়ের হচ্ছে সমন্বয়। হেগেল তাঁর সূচনা৬৯ কে বলেছেন অন্বয়৭০ তার প্রতিপক্ষকে ব্যত্যয় এবং তাদের সমন্বয়কে সিন্থেসিস।
মানব-মন অন্বয়,ব্যত্যয় ও সমন্বয়ের ধারায় একেবারে পরম ব্রক্ষে এসে স্বস্তি লাভ করে। পরম ব্রক্ষে আর কোন দ্বন্দ্ব নেই।
এ সকল চিন্তার মাধ্যমকে৭১ হেগেল গ্রহণ করেছেন অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ৭২ বলে। মার্কস হেগেলের শিষ্য হলেও এসব তাঁর কাছে অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ৭৩। অন্বয়,ব্যত্যয় ও সমন্বয়কে ইতিহাসের ব্যাখ্যায় প্রয়োগ করে মার্কস প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, সভ্যতার গতি এ দ্বন্দ্বের ফলেই সম্ভব হচ্ছে।
“গুহামানব৭৪ কিসে পশুচারী৭৫ মানবে পরিণত হল অথবা পশুচারী যাযাবর কি কারণে কৃষিজীবীতে পরিণত হল, সে ইতিহাস আজও নিতান্ত কল্পনার স্তরেই রয়ে গেছে। কল্পনার সুবিধার জন্য বলা হয়ঃ হয়ত নব্য প্রস্তরযুগের৭৬ শেষের দিকে ঘটনাচক্রে কোন পশুচারী যাযাবর পাথর ঘষে লাঙলের মত একটা অস্ত্র তৈরি করে ফেলে। তা দিয়ে সে মাটি খুঁড়ে দেখল তাতে বীজ পড়লে দুদিনেই তর তর করে চারা গজিয়ে ওঠে। তার শুভ ফলে পথচারী সমাজের সকল লোক আর পশু চারণ নিয়ে মশগুল থাকে না, কোন বিশেষ স্থানে গেড়ে বসে মাটি খোঁড়া ও বীজ বোনায় লেগে যায়। বছরের শেষে প্রচুর খাদ্যশস্য পেয়ে তাদের উৎসাহ বেড়ে যায়। তারা আর পথে পথে পশু নিয়ে ঘোরাফেরার কল্পনাও মনে আমল দিতে চায় না। স্থায়ীভাবে বাস করে তাতে ক্ষেতের কাজ করে তারা জীবিকার সংস্থানে অগ্রসর হয়। তাদের এ প্রণালীর সুখ-সুবিধায় মুগ্ধ হয়ে তাদের জ্ঞাতি গোষ্ঠীরা আবার পশুচারণ ত্যাগ করে তাদের সঙ্গে এসে যোগ দেয়। অথবা তাদের বিরুদ্ধাচরণ করে তাদের ফলানো ফসল লুট করে নিতে চায়। ফলে যুদ্ধ বাধে দুই দলে। বিজেতা ও বিজিত-দুই দলেরই জীবনধারা হয় পরিবর্তিত। একদল এই মিত্র-সমাজের মাঝে পশুচারণের ভার নেয়, অপর দল হাল চলনা করে ফসল ফলায়। এ দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই অগ্রসর হয় মানবসমাজ। সে দ্বন্দ্বের যেমন দেখা দিতে পারে একই সমাজের বিভিন্ন মানুষের মাঝে, তেমনি বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যেও দ্বন্দ্ব সম্ভবপর। যেমন পূর্বে উল্লিখিত একই সমাজের পশুচারী ও কৃষিজীবীদের মধ্যেও যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, সেরূপ সম্পূর্ণ ভিন্ন সমাজের দুই জাতির মধ্যেও দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে, যেমন কোন এক কৃষিজীবী সমাজে হটাৎ একদল যাযাবর পশুচারী আপতিত হয়ে তার উৎপাদন ও সমাজ-ব্যবস্থা দুটোকেই লন্ডভন্ড করে দিতে পারে তবে এ দ্বন্দ্বের ফলে পশুচারীই পরিণত হয় কৃষিজীবীতে, কৃষিজীবী আর ফিরে যায় না আদিম ব্যবস্থাতে। জীবিকার উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটলে সমাজের বাস্তব ব্যবস্থারও পরিবর্তন ঘটে। কৃষিজীবী সমাজকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে ক্ষাত্রশক্তির প্রয়োজন। নানাবিধ যন্ত্রপাতির উৎপাদন অত্যন্ত দরকার। নারী-পুরুষের মধ্যে শ্রমবিভাগ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তার জন্য দলপতি,গোষ্ঠীপতিদের মধ্যে চলে দলাদলি। পরিশেষে সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিশালী ব্যক্তিই রাজপদে অভিষিক্ত হয়। তিনি তাঁর সমাজকে বাইরের শত্রুর হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখেন। তাঁর অধীনে একদল লোক শত্রুর আক্রমণ থেকে দেশ রক্ষার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকে। তাদের আহার যোগানো হয় সমাজের পক্ষে অবশ্য-কর্তব্য। কেবল রাজাই সেই সমাজ ব্যবস্থাকে রক্ষা করতে পারেন না- প্রয়োজন হয় পুরোহিত শ্রেণীর। তাঁরা আল্লাহ্র অভিশাপ থেকে মন্ত্রবলে সমাজকে বাঁচিয়ে রাখে বলে তাদের প্রতিপত্তি সমাজ মেনে নেয়। রাজা তাঁর শাসন অক্ষুণ্ন রাখার জন্য সামন্ত সর্দারের নানা সুযোগ-সুবিধা প্রতিষ্ঠিত করেন। তার ফলে দেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় রাজতন্ত্র বা সামন্ত্রতন্ত্র। যারা সমাজে আহার যোগায় তারা ক্রমশই নিচের দিকে নেমে যায়। সামন্ত প্রভুদের কৃপার পাত্ররূপে তারা তাদের আজ্ঞাবহ হয়ে ক্রমশ দাস শ্রেণীতে পরিণত হয়।
সামন্ত যুগে এসেও মানুষ স্থির হয়ে বসে থাকে না। অবসর সময়ে সে তার জীবনযাত্রার প্রয়োজনে নানাবিধ যন্ত্রপাতি আবিস্কার করে তাকে উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রয়োগ করে। সেই নতুন ব্যবস্থায় অল্প শ্রমে প্রচুর উৎপাদন হয়। সেই উৎপাদিত দ্রব্যগুলোকে সামন্ত অথবা পুরোহিত শ্রেণীকে আর নবীন যুগের উৎপাদনকারী নজরসালামি দিতে চায় না। তাদেরই একদল লোক উদ্ধৃত্ত দ্রব্য দেশে-বিদেশে রপ্তানি করে তা থেকে দু’পয়সা লাভ করতে চায়। ফলে সামন্ত সর্দারের সঙ্গে তাদের দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এ দ্বন্দ্বে সামন্ত সর্দারের অত্যাচারে জর্জরিত দাস শ্রেণী তথা দেশের জনসাধারণ নবোত্থিত বণিক শ্রেণীর সঙ্গে যোগ দেয়। কারণ এ বণিক শ্রেণী আর দাস শ্রেণীর উপার্জনের ওপর নির্ভরশীল নয় বলে তারা দাস শ্রেণীকে সম্পূর্ণ মুক্তি দিতে হয় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সামন্ত শ্রেণীকে পরাজিত করে জয়ের পরে আকাশের চাঁদ সূর্য সবকিছু পেড়ে দেবে বলে বণিক শ্রেণী উৎসাহিত করে। এই দ্বন্দ্বে বণিক শ্রেণীরাই জয়ী হয়। জগতে আবার হয় নতুন সমাজ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা। বণিক তার কলকারখানার মুক্তিপ্রাপ্ত দাস শ্রেণীকে খাটায়। আবার তাদের পরিশ্রমের দওলতে লাখ লাখ টাকা উপার্জন করে। যতই নতুন শক্তিশালী যন্ত্রপাতির আবিস্কার হয় ততই লাভের অংক বাড়ে। শেষে মূলধন এতো ফেঁপে যায় যে, কোন বিশেষ দেশে তাকে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না; তার জন্য প্রয়োজন হয় দেশ-দেশান্তরে আধিপত্য বিস্তারের, প্রয়োজন হয় সাম্রাজ্য গড়ে তোলার। ধর্মের নামে, অনুন্নত জাতির কল্যাণের হাস্যকর অজুহাতে এক দেশ কর্তৃক অন্য দেশের লোকের রক্তমোক্ষণ চলে পুরাদমে। এইভাবে পুঁজিবাদ দুনিয়ার বুকে জেঁকে বসে।
মূলধন যত ফেঁপে যায় ততই মুষ্টিমেয় লোকের হাতে দেশের সম্পদ এসে জড়ো হয়। মূলধন বাড়তির সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার অপর একদল মানুষ হড় হড় করে নির্বিত্ত শ্রেণীতে পরিণত হয়। এতে আবার নতুনভাবে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। পুঁজিবাদী সমাজের পক্ষে নির্বিত্তের শ্রম অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, তাদের শ্রম ব্যতীত কলকারখানা চলতে পারে না। তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করলে তারা শ্রম করতে চায় না। একেবারে আহার যোগানো বন্ধ করলেও তারা মারা যায়। তাই তাদের রাখা হয় জীবন্মৃত অবস্থার মধ্যে। খাওয়া-পরা ও প্রজননের ব্যবস্থা করে দিয়েই মালিক তাঁর কর্তব্যের এ শেষ মনে করেন। অপরদিকে পুঁজিপতির পুঁজির সঙ্গে শ্রম যুক্ত হয়েই এ সমাজ ব্যবস্থায় উৎপাদন সম্ভব হয়। উৎপাদনের জন্য তাই দুইয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে,কিন্তু বণ্টনের বেলায় শ্রমিকের কৃতিত্ব করা হয় সম্পূর্ণ অস্বীকার। উৎপাদিত দ্রব্যে শ্রমিকের মালিকানা স্বীকৃত হয় না কিছুইতেই। তার ফলে নির্বিত্ত শ্রমিকেরা কালে সংঘবদ্ধ হয়ে মালিকের বিরুদ্ধে অভিযান চালায়,পুঁজিবাদীর বিলাস-সৌধ চূর্ণ করে সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের করে প্রতিষ্ঠা।*(মোহাম্মদ আজরফঃ ইতিহাসের ধারা)
সামন্ততন্ত্রকে যদি বলা যায় হেগেলীয় দর্শনের Being, তাহলে ধনতন্ত্রকে বলা যায় Non-being এবং সমাজতন্ত্রকে বলা যায় Becoming। সামন্ততন্ত্রের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের ফলেই সৃষ্টি হয় নির্বিত্ত শ্রেণী। সেই নির্বিত্ত শ্রেণীর কল্যাণের জন্য সমাজতন্ত্রই একমাত্র পন্থা। তার জন্য চাই রক্ত-বিপ্লব। মার্কস ও এঙ্গেলসের সর্বশেষ বাণীঃ সর্বদেশের মজুরশ্রেণী সংঘবদ্ধ হও।** (মার্কস ও এঙ্গেলসঃ কমিউনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো।)
সেই সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যষ্টিকে তার অধিকার৭৭ ত্যাগ করতে হবে। এখানে রাষ্ট্রই থাকবে সমস্ত কাজকর্মের নিয়ামক। প্রত্যেক তার যোগ্যতা অনুসারে কাজ করে যাবে এবং তার প্রয়োজন অনুসারে সমস্তই পাবে৭৮। বৃহত্তর মানবতাবোধে উদ্ধুদ্ধ হয়ে যখন মানুষ তার অহংবোধ বা স্বার্থপরতা সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে সকল কাজকর্মই নিজের এবং সকলের জন্য করতে শিখবে, তখন রাষ্ট্রের কোন প্রয়োজন থাকবে না, রাষ্ট্র আপ্না-আপনি মিলিয়ে যাবে। তাই মানুষকে পরার্থপর করার সাধনায় সাম্যবাদী আদর্শে রাষ্ট্রকে করতে হয় সর্বেসর্বা। প্রতিক্রিয়ার কোন সুযোগই যাতে এর মধ্যে প্রশ্রয় না পায় সেজন্যেই প্রত্যেক ব্যক্তিকে রাষ্ট্রসর্বস্ব জীবন-যাপন করার শিক্ষা দেয়া হয়। এসব শিক্ষাধারা সংস্কৃত হলে পর রাষ্ট্রের প্রয়োজন আপ্না-আপনি ফুরিয়ে যায়, মানুষের বৃহত্তর সত্তার প্রকাশের জন্য আর কোন শক্তির প্রয়োজন হয় না।
উদারনৈতিক মতবাদের আলোচনায় আমরা দেখেছি, সভ্যতার এক বিশেষ পর্যায়ে দুনিয়ায় কোন বিশেষ শ্রেণীকে ঐশী ক্ষমতাপ্রাপ্ত বলে ধারণা করার ফলে সাধারণ মানুষের দুর্গতির সীমা থাকে না। সেইজন্যই সর্বসাধারণ মানুষের মুক্তির উদাত্ত আহ্বান নিয়ে দেখা দিল উদারনৈতিক মতবাদ৭৯ , যার মূলমন্ত্র হল ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ৮০ । তার ফলে হল ধনিক ও শ্রমিক শ্রেণীর সৃষ্টি। সমাজতন্ত্রে এই নির্বিত্ত শ্রমিক শ্রেণীই আধিপত্য লাভ করে। তা সত্ত্বেও আর কোন শ্রেণী সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে না। কারণ পুঁজি খাটিয়ে তা থেকে মানুষকে শোষণ করার আর কোন অবকাশ থাকে না। অবশ্য বৃত্তিগত শ্রেণী-বৈষম্য৮১ তাতে থাকতে পারে, কিন্তু তাতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি সংরক্ষণের কোন সুযোগ না থাকায় আর কোন দ্বন্দ্বের সুবিধা হয় না। ধনতন্ত্রী সমাজ থেকে সমাজতন্ত্রী সমাজে পৌঁছতে হলে মানুষকে একটা সন্ধিক্ষণের৮২ ভেতর দিয়ে যেতে হয়। কারণ ধনতন্ত্রের আদর্শে ও ভাবধারায় প্রতিপালিত মানস নিয়ে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভবপর নয়। এই জন্য এই সন্ধিক্ষণে রাষ্ট্রে ব্যাপার ডিরেক্টরের হাতে ছেড়ে দিতে হয়। তিনি নির্বিত্তকে সমাজতান্ত্রিক আদর্শে পরিচালিত করে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র তথা সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলেন।
মার্কসের মতবাদে পরস্পরবিরোধী অনেক ভাবধারা সন্নিবেশিত রয়েছেঃ
১. প্রথমত সভ্যতার গতি নির্দেশ করতে যেয়ে মার্কস যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাকে বলা হয় অর্থনৈতিক নিশ্চয়তাবাদ৮৩ । ঠিক যেভাবে পদার্থ বিজ্ঞানবিদ অণু বা পরমাণুর কার্যকরণ দ্বারা জগতের সমস্ত ক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করেন, মার্কসও তেমনি এক কার্যকারণ শৃঙ্খলা দ্বারা জগৎসভ্যতার গতির ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর এ পদ্ধতিকে Positive Science –এর ভাষায় Judgement of facts বলা যেতে পারে। পরক্ষণেই তিনি আবার Normative Judgement দিয়ে বলেছেন, জগৎ-সভ্যতার ধারাই এই এবং মানুষের কাজকর্মের নীতিও এই হওয়া উচিত।
যদি কার্যকারণসূত্রে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাই জগৎ- সভ্যতার লক্ষ্য হয়ে থাকে, তাহলে সে ব্যবস্থা এমনি ফলে উঠবে, তার জন্য কারো কোন সাধ্য-সাধনা করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু সে সভ্যতাকে বা সেই সামাজিক ব্যবস্থাকে রুপায়িত করার জন্য আহ্বান করা হয়েছেনঃ দুনিয়ার মজদুর সব একত্র হও৮৪। যদি একত্র হওয়ার মত স্বাধীনতা মজদুর শ্রেণীর না থাকে, তবে তাদের প্রতি এ আহ্বানের কোন মূল্য আছে কি? যদি ‘স্বাধীনতা’ বলতে তিনি স্পিনোজার মত সম্মতি৮৫ মনে করতেন তাহলেও তার ব্যাখ্যার সঙ্গে স্বাধীনতার সঙ্গতি খুঁজে বের করা যেত। মার্কস কিন্তু সম্মতি অর্থে স্বাধীনতা স্বীকার করেননি। তাঁর মতে ‘স্বাধীনতা’ শব্দের অর্থ নির্বিত্ত শ্রেণীর সক্রিয় অংশগ্রহণ। অর্থনৈতিক নিশ্চয়তাবাদের সঙ্গে নির্বিত্তের সক্রিয় অংশগ্রহণের কোন সুসঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।
২. দ্বিতীয়ত, মার্কসকে আশাবাদী নিশ্চয়ই বলতে হবে। কারণ, তিনি অনাগত সমাজ ব্যবস্থার রুপায়ণে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। তাঁর ধারণা ছিল, শ্রেণী-সংগ্রামের ভেতরে দিয়েই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। সন্ধিক্ষণে কিন্তু বারবার ব্যষ্টিচৈতন্য৮৬ বা স্বার্থপরতা আবার মাথা তুলে দাড়াঁতে পারে, এই ভয়ে তিনি নির্বিত্তের নেতৃত্বের৮৭ ব্যবস্থা রেখেছেন। এখানেও মানবচরিত্র সম্বন্ধে আশা ও নিরাশার দ্বন্দ্ব তাঁর মনে রয়েছে।
অবশ্য শেষ পর্যন্ত তিনি আশাবাদীই রয়ে গেছেন। কারণ তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, সাম্যবাদী রাষ্ট্র গঠিত হবেই হবে। তবে বহুদিনের পুঁজিবাদী সংস্কার মন থেকে নির্মূল করতে হলে রাষ্ট্রের পক্ষে বজ্রকঠোর হস্তে স্বার্থপরতাকে দমন করতে হবে।
তাঁর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সঙ্গে এরূপ আশাবাদ কী করে খাপ কায়? জগতের কার্যকরন ব্যবস্থায় সে আশাবাদের কোন মূল্য আছে কি? এ যাবত হয়তো মার্কস প্রদর্শিত ধারায় সভ্যতা অগ্রসর হচ্ছে, কিন্তু তাই বলে এ পথেই যে সভ্যতা ধেয়ে চলবে, কি করে বলা যায়? তাই বার্ট্রান্ড রাসেল সত্যই বলেছেন, “ মার্কস নিজেকে নাস্তিক বলে ঘোষণা করতেন, কিন্তু তিনি যে জাগতিক আশাবাদ৮৮ মনে পোষণ করতেন, তা কেবল আস্তিকের পক্ষেই শোভন”। * ( দার্শনিক শ্রেষ্ঠ স্পিনোজার ধারণা ছিল, জগতের প্রত্যেক বস্তুই Substance বা সারবস্তুর Mode বা খণ্ডিত অংশ। সেই Substance- এর অনেকগুলো গুণ(Attribute); মানুষ মাত্র তার দুটো গুণকেই জানতে পারে। কারণ মানব জীবনে সে দুটো গুণ-স্থিতি (Extension) ও মননশীলতা (Thought) বর্তমান। তাঁর এ মতবাদকে সমান্তরালবাদ (parallelism) বলা হয়। তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল, মানব জীবনের এ দুটো দিক পরস্পর বিচ্ছিন্ন এবং তাদের মধ্যে কোন সংযোগ সম্ভবপর নয়। আবার বস্তু জগতে বা ভাব জগতে যা কিছু রয়েছে, তাঁর মূল উৎস সেই সারসত্তা বা Substance. তিনি তার তাঁর দর্শনে এক জায়গায় ঠাট্টা করে বলেছেন-যদি উড্ডীয়মান তীরেরও চেতনা থাকত তা’ হলে সে মনে করত,তার উড়ে যাওয়ার মূল কারণ সে নিজেই। এ মতবাদের আস্থা স্থাপন করলে ইচ্ছশক্তির স্বাধীনতার মূল্য থাকে না। সব কিছুর মূলে সারসত্তা বর্তমান থাকলে আমাদের প্রতি কাজকর্মেও সেই সারবস্তুর কার্যকারিতা বর্তমান। ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতার মূলে এভাবে কুঠারাঘাত করেও স্পিনরাজ্য আবার অন্য অর্থে তাকে ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে স্বাধীনতার অর্থ বিশ্ব-সত্তা থেকে কিভাবে বিভিন্ন mode বেরিয়ে আসছে, তাই দেখে জ্ঞান লাভ করে ধন্য হওয়া। জ্ঞানেরও সর্বপ্রধান স্তররূপে তিনি স্বজ্ঞা বা Intuition কে স্বীকার করে নিয়েছেন। সেই স্বাধীনতার অর্থ দাঁড়ায় সম্পত্তি বা acquisance মানবজীবনের এ পর্যায়ে যে রকম জ্ঞান লাভ হয় তার ফলে সে লাভ করে প্রশান্তি (Beatitude) )।
৩. ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর শোষণের ভয়াবহ রূপ দেখে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের প্রতি মার্কস স্বভাবতই ছিলেন বিমুখ। তাঁর ধারণা ছিল, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ থেকেই শোষণের উৎপত্তি। তাই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মূল উচ্ছেদ করবার জন্য তিনি তাকে পুঁজিবাদের মূল উৎস বলেই ধরে নিয়েছেন। বাস্তবিক পক্ষে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যবোধ অনেকস্থলেই শোষণের কারণ হয়ে দাঁড়ালেও সব ক্ষেত্রেই তা হয় না। দুনিয়ার যাঁরা মনীষী, মননধর্মী, যাঁদের গবেষণার ফলে দুনিয়ার প্রগতি হয়েছে সম্ভবপর-তাঁরা ছিলেন আত্মপ্রচারবাদী৮৯ কিন্তু স্বার্থপর ছিলেন না। মননধর্মী মানুষ মাত্রেরই স্রষ্টা৯০ হিসেবে বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে, কিন্তু তাই বলে তাঁরা স্বার্থপর নন। মার্কসের সংস্থায় এদের কোন স্থান নেই, কারণ সমাজতন্ত্রই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সর্বশেষ কথা। অন্য কোন বিশ্বসংস্থার চিন্তা করা প্রতিক্রিয়ারই ছদ্মবেশ।
কাজেই যে শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থার প্রথম সোপানরূপে মার্কস শ্রেণী সংগ্রামের পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন,তাতে অর্থনৈতিক সংগ্রামের নিরসন হতে পারে, তবে তাতেও সমাজ জীবন অন্যভাবে সংগ্রাম দেখা দিতে পারে। মার্কসের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যাঁদের অটল বিশ্বাস,মনন রাজ্যে তাঁরাও নতুন নতুন আবিস্কারের দওলতে মার্কসের দার্শনিক মতের বিরোধিতা করতে পারেন। উদাহরণচ্ছলে বলা যায়, আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় কেউ যদি জগতের সর্বত্র সাশ্রয়ী অণুর লীলাখেলাই দেখতে পান তাহলে আদর্শ হিসেবে প্রয়োজনীয় বলে গ্রহণ করলেও মার্কসীয় নিশ্চয়তাবাদে তার বিশ্বাস অটল রইবে না। যদিও সমাজ ব্যবস্থার দৃঢ় অস্তিত্বের জন্য তিনি মার্কসবাদকেই দুনিয়ার চূড়ান্ত মতবাদ বলে ব্যবহারিক জীবনে গ্রহণ করেন, তাহলেও তাঁর ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে মননধর্মী জীবনের সংঘাত ও সংঘর্ষ হয়ে পড়বে অনিবার্য।
৪. তখনকার দিনের প্রচলিত বৈজ্ঞানিক মতবাদের উপর ভিত্তি স্থাপন করে মার্কস তাঁর যে অর্থনৈতিক নিশ্চয়তাবাদ প্রচার করেছিলেন তার ভিত্তি ছিল জড় পদার্থের মধ্যে কার্যকারণ পরম্পরা সূত্রের অমোঘ কার্যকারিতা। আধুনিক বিজ্ঞানের আলোয় সে মতবাদের ভ্রান্তি প্রমাণিত হয়েছে। বর্তমানে জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানবিদ পরলোকগত স্যার জেম্স জিনস বলেছেন, “ সাবেকী পদার্থবিদ্যা ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতার পথে প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে বলেই মনে হয়। নতুন পদার্থবিদ্যা এ রকম কোন ঝোঁক নেই বরং হাতলের সন্ধান পেলে যে এ দরজা খোলা যায়, এই ভাবধারার উদ্রেক হয়। পুরাতন পদার্থবিদ্যায় আমরা যে জগৎ দেখেছিলাম, তাতে বাস করার পক্ষে উপযুক্ত ঘরের চেয়ে কারাগারের মতই বেশি দেখাত। নতুন পদার্থবিদ্যায় আমরা যে জগতের সন্ধান পাচ্ছি, মনে হয় তা পশুর আবাসস্থল না হয়ে মানবজাতির উপযুক্ত বাসস্থান হওয়ার যোগ্য বিবেচিত হতে পারে। এ বাসস্থানে আমাদের ইচ্ছামত ঘটনাগুলোকে গড়ে তুলতে পারার সম্ভাবনা রইবে এবং এখানে আমরা অধ্যবসায়ের দ্বারা অনেক কিছু লাভ করতে পারব”।
৫. মার্কসের অর্থনৈতিক নিশ্চয়তাবাদের মধ্যে আসল কথা অহংবোধ ও পরার্থিতা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা। অহংবোধ ও পরার্থিতাকে সাবেক আমলের মনোবিজ্ঞান তখন পর্যন্ত দু’টো পরস্পরবিরোধী গুণ বলেই স্বীকার করেছিল। মার্কস অহংবোধকেই যত অনর্থের মূল ধারণা করেছেন। তাঁর আগেও দুনিয়ার সকল ধর্মপ্রবর্তক স্বার্থপরতাকে পরার্থিকতার চেয়ে নিকৃষ্টতর বৃত্তি বলেই স্বীকার করেছেন। তবে স্বার্থপরতার অহংবোধ হয়। অহংবোধ ও স্বার্থপরতার মধ্যে প্রভেদ রয়েছে। সে অহংবোধের একেবারে নিরসন হয় কিনা, মানুষকে সম্পূর্ণ পরার্থপর করে তোলা যায় কিনা, সে সম্বন্ধে তর্কের অবকাশ রয়েছে প্রচুর।
মার্কসবাদ ও বস্তুবাদী সমাজতন্ত্র
আসল কথা বল এই যে, অতি আধুনিক গোঁড়া মার্কসবাদীরা বস্তুবাদী সমাজতন্ত্রের সাথে মার্কসবাদীকে অভিন্ন মনে করেই ভুল করেন। মার্কসবাদকে কম্যুনিজমের দৃষ্টিভঙ্গি বা তার কার্যক্রমের মূলে কম্যুনিষ্ট রয়েছে সত্যিই কিন্তু মার্কসবাদ কম্যুনিজম থেকে বৃহত্তর। মার্কসবাদ কেবল কম্যুনিজম নয়, মানব সভ্যতার প্রত্যেকটি বিকাশের ধারাও মার্কসবাদের অন্তর্গত। মার্কসবাদের চূড়ান্ত সত্য বলে কিছুই নেই। মার্কসবাদের পদ্ধতির প্রয়োগেই মার্কবাদের সারসত্ত্ব। এই প্রয়োগের অনুসরণে যদি আমরা প্রবৃত্ত হই, তাহলে আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে মার্কসবাদকে উন্নত করা, বিস্তার করা ও পুনঃপরীক্ষা কেবল সঙ্গতেই হবে না-হবে অবশ্যই কর্তব্য।
টলস্টয় বা নব্য খ্রিষ্টবাদ
মানব-মনের অহংবোধ ও পরার্থতার সমন্বয় সাধনাই ছিল মার্কসের পরবর্তী চিন্তানায়ক মহামতি টলষ্টয়ের জীবন-সাধনা। বর্তমান সভ্যতার নানা ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে টলষ্টয় দেখতে পেয়েছিলেন এতসব অসঙ্গতির মূলে রয়েছে ব্যক্তিগত মালিকানা এবং তার পথ সুগম করার জন্য নানাবিধ কলকারখানা প্রতিষ্ঠা। আবার এসবের মূলে রয়েছে খ্রিষ্টের প্রদর্শিত পথ থেকে দূরে সরে পড়া।
তাই, ঊনবিংশ শতাব্দীর মানব-সভ্যতার নানা ত্রুটি-বিচ্যুতিতে উত্যক্ত হয়ে তিনি আবার খ্রিষ্ট ধর্মের প্রতিষ্ঠাকল্পে ছিলেন উদ্যোগী । আত্মজিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হয়ে টলষ্টয় তাঁর পরিণতিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানাকেই সব অনর্থের মূল বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। কারণ মালিকানা থেকেই দুনিয়ার যত অমঙ্গলের রয়েছে সম্ভবনা। অপূর্ব ভাষায় তিনি ব্যক্তিগত সম্পত্তির নীতিকে আক্রমণ করেছেন- ব্যক্তিগত সম্পত্তিই বর্তমানে সব অনর্থের মূল। এ আপদের যারা অধিকারী অথবা অনধিকারী তাদের উভয়ের যন্ত্রণায় মুহ্যমান তাদের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য। রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে অথবা রাষ্ট্র ও সরকারের সর্বদাই পরস্পরের সঙ্গে এ বিত্তের জন্যই কূটনীতির চালবাজি চলে। এ বিত্তের জন্যই তাদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ জ্বলে ওঠে। কখনও বা তা আফ্রিকার মাটির জন্য, কখনও বা চীন বা বলকানের বিশাল ভূখণ্ডের জন্য তার সূচনা হয়। ব্যাংকার, ব্যবসায়ী,উৎপাদনকারী, জমিদার সকলেই বিত্তের জন্য পরিশ্রম করে-বিত্তের জন্যই ফন্দি এঁটে নিজেদের বিপন্ন করে, অপরকে যন্ত্রণা দেয়। সরকারী কর্মচারগণও পরস্পরের সঙ্গে শত্রুতা করে বঞ্চনার প্রশ্রয় দেয়, নির্যাতন করে, নিজেরাও নির্যাতিত হয়। এ বিত্তের জন্য আমাদের আদালত, আমাদের পুলিশ সকলেই সম্পত্তির সংরক্ষণে বদ্ধপরিকর। শাস্তির উদ্দেশ্যে রক্ষিত আমাদের কারাগার, পাপের জন্য আমাদের বিভীষিকাময় আকস্মিক দমন, সকলেরই একমাত্র লক্ষ্য বিত্তের সংরক্ষণ।
“চোরাই মালের মস্ত বড় আড়তদার আমাদের রাষ্ট্র। এ রাষ্ট্রই বর্তমানে সমস্ত সামাজিক অবিচারকে বুকের তলায় আগলে রাখে। এর মূলে রয়েছে সেই ব্যক্তিগত মালিকান। সেই উদ্দেশ্যেই রাষ্ট্র বর্বরজনোচিত জুলুমের ঘোরজালে দেশকে দেশ ঘিরে ফেলেছে। এর জন্যই আইন-কানুনের সৃষ্টি, এর জন্যই পুলিশের লোক,সৈন্যসামন্তের প্রয়োজন”।
সেই ব্যক্তিগত মালিকানা কিন্তু রাষ্ট্র কর্তৃক কোন আদেশের বলে হটাৎ বিলুপ্ত হবে না অথবা বিপ্লববাদীদের মত তা’ ব্যক্তির হাত থেকে ছিনিয়ে আনা হবে না।
মালিক স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে সে বিত্ত আপনিই ত্যাগ করবে, তা হলেই বিত্তশালী ও বিত্তহারার এ ব্যবধান আপনা আপনি নষ্ট হয়ে যাবে, ধনীকে তার সম্পদ, মননশীলকে তার ঔদ্ধত্য ত্যাগ করতে হবে। শিল্পীকে সর্বসাধারণের চিত্র আঁকতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার উপার্জনের ওপর নির্ভর করে জীবন যাপন করতে হবে। জীবনের আদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত সে কিছুই গ্রহণ করবে না।
তাঁর বক্তব্যের সারাংশ সোজা কথায় বলা চলে, “ বিত্তবাদীরা যেরুপ দাবী করে-মালিকের নিকট থেকে জোর করে সমস্ত সম্পদ কেড়ে নিলেই সামাজিক অসাম্যের সমাধান হবে, তা মোটেই সত্য নয়। নিচের স্তরে এ সমতা সাধন সম্ভবপর নয়। ধনীদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অধিকার ত্যাগের মাঝেই তার সাফল্য বর্তমান”।
তাঁর এ মতবাদকে ধর্মীয় সমাজতন্ত্র বলা যেতে পারে। কারণ আদি খ্রিষ্ট ধর্মের প্রেরণায় ব্যক্তি যখন তার প্রয়োজনাতিরিক্ত আর কিছুই গ্রহণ করবে না তখনই হবে আদর্শ সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা- তখন মানুষে মানুষে আর কোন দ্বন্দ্ব থাকা সম্ভব নয়-দুনিয়া হয়ে পড়ে সুখরাজ্য।
ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে সাম্যবাদের যোগ করার মহৎ ইচ্ছায় টলষ্টয় যে জীবনবাদের অনুসরণের জন্য মানব সমাজকে আহ্বান করেছেন, তার মাঝে রয়েছে মস্ত বড় অসঙ্গতি। ব্যষ্টির যদি আত্ম-নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ অধিকার থাকে, তাহলে সে কেন সমষ্টির কল্যাণ কামনায় তার স্বার্থ ত্যাগ করবে। তার উত্তর টলষ্টয় বলছেন, তার জীবনে শান্তি ফিরে আসবে এবং সেই জন্যই যীশু খ্রিষ্ট আত্মত্যাগের পথে অগ্রসর হয়ে মানবজাতিকে আহ্বান করেছিলেন। এ ক্ষেত্রেও অহংবোধকে পরার্থিতার অধীন করার জন্য এক অভিনব সাধনার পরিচয় পাওয়া যায়। তবু আমাদের দেখতে হবে ব্যক্তি স্বাধীনতাকে সম্পূর্ণ স্বীকার করে নিলে, সম্পত্তির উপর মানুষের অধিকারের নীতিকে স্বীকার করে নিলে এ সমাজতন্ত্র কিসে সম্ভব হতে পারে? যদি ব্যষ্টির মনে আত্মকেন্দ্রিক মনোবৃত্তি প্রবল থাকে, তার দমনের জন্য কোন উপদেশ দিলেই চলবে না, তার অধিকারকে সম্পূর্ণ বিলোপ করে তাকে মাত্র সম্পত্তির রক্ষক হিসেবে পরিণত করা দরকার।
টলষ্টয়ের চিন্তাধারায় দুস্থ মানবতার জন্য অকপট দরদ ফুটে উঠলেও তিনি ব্যষ্টির স্বাধীনতার সঙ্গে তার মতবাদকে সুসামঞ্জস্য করে তুলতে পারেন নি। কোন্ নীতিতে তার জন্মগত অধিকার ত্যাগ করে মানুষ এক আদর্শ সুখরাজ্য গড়ে তুলবে তার পরিস্কার পদ্ধতি টলষ্টয় দিয়ে যাননি।
আমাদের ভুললে চলবে না যে, সমালোচনা করা সহজ কিন্তু গঠনমূলক সৃষ্টি অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপার।
“ যে কোন অবস্থায়ই মানুষ তার যুগের বাইরে শূন্যে অবস্থান করতে পারে না। যেখানে বিভিন্ন স্তরে লক্ষ লক্ষ মানুষ একত্রিত রয়েছে-প্রাত্যহিক জীবনে সেখানে প্রতিভাশালীর সঙ্গে হয় বেতনভোগীর সমাবেশ-সেখানে জীবনযাত্রার সুসম্বন্ধ রীতি প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। যে মুহুর্তে টলষ্টয় রোগের কারণ নির্ণয় থেকে চিকিৎসা বিধানে মনোনিবেশ করেছেন অর্থাৎ সোজা কথায় যখন তিনি বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাকে অস্বীকার বা নিন্দা করা ছেড়ে ভবিষ্যতের উন্নততর সাধারণতন্ত্রের প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন, তখনই তাঁর চিন্তাধারা নীহারিকাপুঞ্জের মত অস্পষ্ট ও ধোঁয়াটে রূপ ধারণ করেছে”।* ( Grefan Zewig-Tolstoi.)
গান্ধীবাদ
টলষ্টয়ের ভারতীয় শিষ্য মহাত্মা গান্ধীর অহিংস নিরুপদ্রব প্রতিরোধের মধ্যেও রয়েছে পরস্পরবিরোধী নানা ভাবের সংঘর্ষ। ব্যক্তি-স্বাধীনতার সঙ্গে আদর্শ সাম্যবাদ বা (গান্ধীর ভাষায়) রামরাজ্যের প্রতিষ্ঠায় গান্ধীজির জীবন দর্শনে এক মস্ত ফাটল দেখা দিয়েছে। মানুষ যদি স্বভাবতই আত্মসর্বস্ব হয়, তাহলে পরহিতে তার সব অধিকার ত্যাগ কোনকালেই সফল হতে পারে না। শুধু আত্মিক শক্তির বলে ইন্দ্রিয় তথা চক্রজয় সব সময় সম্ভবপর হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বার্থপরতা মাথা তুলে দাঁড়ায়। তার ফলে, মুখে সাম্যবাদ প্রচার করলেও মানুষের শোষণের অবসান হয় না।
এক্ষেত্রে অবশ্য অস্বীকার করার উপায় নেই যে, গান্ধীজির এ মতবাদ মানব-কল্যাণের উদ্দেশ্যেই গঠিত হয়েছিল। একথা সর্বতোভাবে সত্য যে, ১৯২১ সালে গান্ধীজি কর্তৃক প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনের ফলে এ উপমহাদেশের রাজনীতিতে এক প্রবল বিপ্লব দেখা দিয়েছিল। ইংরেজ শাসক ও শোষকদের বিরুদ্ধে অহসযোগ নীতি পালন করে, তাদের শাসন ব্যবস্থাকে বান্চাল করে দেওয়াই ছিল গান্ধিজির জীবনের সর্বপ্রধান মন্ত্র। এ মন্ত্র বাস্তবায়নের চেষ্টার ফলেই এদেশে ইংরেজ শাসন ক্রমশ শিথিল হয়ে পড়ে। তবে এ অসহযোগ নীতির সঙ্গে যুক্তিসঙ্গতভাবেই যুক্ত ছিল ব্যক্তিস্বাধীনতার কীর্তি। এ অসহযোগ নীতিকে কারো ওপর বলপ্রয়োগে চাপানো যায় না। ব্যক্তিমানস স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই তাকে গ্রহণ করবে। তাই যদি হয় তাহলে স্বাধীনতা লাভের পরে সে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠায় কেন কোন ব্যক্তি অগ্রসর হবে, তার কোন যুক্তি গান্ধিজি প্রদর্শন করেননি। স্বভাবত স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির ব্যাপারে অভ্যস্ত ব্যক্তির পক্ষে রামরাজ্যের মত আদর্শিক সাম্যবাদমূলক রাষ্ট্র গঠনে প্রবৃত্ত হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার নয়। এজন্য ব্যষ্টি-মানসেও সাম্যবাদের বীজ রয়েছে এবং অনুশীলনের ফলে তা বিকশিল হতে পারে-এ সূত্রটিও গান্ধীজীর প্রদর্শন করা উচিত ছিল।
ব্যষ্টি-চেতনা ও সমষ্টি-চেতনা বা সাম্যবাদের চেতনার মধ্যে যে বিরাট ফাঁক রয়েছে তার যোগসূত্র আবিস্কারের মধ্যেই রয়েছে রাজনীতিতে সফলতার চাবিকাঠি। গান্ধীজি ঐ সূত্রটি আমাদের দিয়ে যাননি।
পঞ্চম পরিচ্ছেদ
মানুষের পরিচয়
একটি সত্য স্বভাবতই চোখে পড়ে। এ যাবত সেসব মতবাদের উৎপত্তি হয়েছে, তাতে মানবজীবনের কোন বিশেষ দিকের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে, তারই আলোকে গোটা জীবনের ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য হয়েছে প্রয়াস। যদিও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নামে তারা জগতে প্রচারিত তবুও তাদের মধ্যে রয়েছে অবৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি। বিজ্ঞানের আসল কথা, জীবনের সকল তথ্যকে গ্রহণ করে, তার ব্যাখ্যার জন্য সার্বিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। এসব ব্যাখ্যায় সকল তথ্যকে গ্রহণ না করে বিশেষ থিয়োরি বা মতবাদের সঙ্গে খাপ খাওয়াবার চেষ্টায় অনেকগুলোকে করা হয়েছে অস্বীকার অথবা তাদের বিকৃতি করে ফেলে দেয়া হয়েছে ছকের মধ্যে। তাতে আরোহ৯১ পদ্ধতির করা হয়েছে অবমাননা। কারণ বিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য বিশেষ৯২ থেকে সার্বিকে৯৩ উপস্থিত হওয়া। অবরোহ পদ্ধতিতে৯৪ কোন বিশেষ নীতিকে গ্রহণ করে নিচের দিকে নেমে যাওয়া বৈজ্ঞানিক জগতে আত্মহত্যারই নামান্তর। অথচ লক্ষণীয় যে, আরোহ পদ্ধতিই বৈজ্ঞানিক জগতে একমাত্র বিষয় পদ্ধতি বলে স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও সেই অবরোহ পদ্ধতির প্রভাব বিজ্ঞান এড়িয়ে যেতে পারেনি। তাই গোড়াতে জীব জগতে যুদ্ধ৯৫ বা কামপ্রবৃত্তির মৌলিকতা, মানুষের স্বার্থপরতা প্রভৃতি সূত্রগুলোকে স্বীকার করে তাদের একচোখা আলোকে জটিল জীবনের সবগুলো দিকের ব্যাখ্যা দেয়া হচ্ছে।
এমনকি, যে কার্ল মার্কস হেগেলের চিন্তা মাধ্যমগুলোকে শ্রেণী-সংগ্রামে রুপান্তরিত করে উৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থার সূত্রে জীবনের গতি ও ক্রমবিকাশের ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন, তাঁর মনেও সবসময় হেগেলীয় দর্শনের প্রভাবই ছিল কার্যকরী। তাই তাকে অস্বীকার করেও জীবনের বিচিত্র ক্ষেত্রে তারই অমোঘতা স্বীকার করে নিয়েছেন। উৎপাদন ব্যবস্থা ছাড়া মানবজীবনে যতো সব ফ্যাকটর কার্যকরী সেগুলোকে তিনি করেছেন সম্পূর্ণ অস্বীকার বা যুক্তিবাদের প্রভাবে তিনি একটি ছকে ফেলে মানবজীবনে সবগুলো দিকের ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। তাই দেখা দিয়েছে অবৈজ্ঞানিক মনোভাব।
দ্বিতীয়ত, আধুনিক বিজ্ঞানে যুক্তি ও অভিজ্ঞতাকেই জ্ঞানের একমাত্র পন্থা বলে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। এগুলো ব্যতীত মানবজীবনে জ্ঞানের অপর কোন পন্থা নেই বলে ধরে নেয়া হয়েছে।এ মনোভাবের মধ্যেও বিজ্ঞানের রয়েছে এক মস্তবড় গোঁড়ামি।
তৃতীয়ত, এসব আলোচনার ফলে আমরা দেখেত পেয়েছি মানবজীবনের মধ্যে রয়েছে মস্তবড় দ্বন্দ্ব। এক-চোখামি করে মানবজীবনের কোন ব্যাখ্যা করতে গেলেই মানবজীবনের অন্য দিক বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তার ফলে অন্য মতবাদের উৎপত্তি হয়। তাতেও জীবনের ব্যাখ্যা সুষ্ঠু হয় বলে দেখা দেয় দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্বের উৎপত্তি ও সংঘাতের মধ্য দিয়েই মানব-সভ্যতার গতি চলছে ধেয়ে। কাজেই মানবজীবন সম্বন্ধে কোন সার্বিক সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছার আগে তার সম্বন্ধে পেতে হবে পূর্ণ জ্ঞান। সে পূর্ণ জ্ঞানের আলোকেই গড়ে উঠবে তার জীবন-দর্শন।
মানবজীবনের অসংখ্য বৃত্তি ও প্রবৃত্তির সন্ধান পাওয়া যায়। তার জীবনে রয়েছে যেমন স্ববোধ৯৬ তেমনি রয়েছে পরার্থপরতা৯৭ । তার যেমন রয়েছে ক্ষুদা, যৌন প্রেরনা, প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হওয়ার বাসনা, সৌন্দর্য ভোগ করার প্রবৃত্তি, তেমনি রয়েছে প্রেম, আত্মত্যাগ, স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা, রুচিবোধ, নীতিবোধ, এ বিশ্বের প্রকৃত পরিচয় পাওয়ার জন্য অদম্য আকাঙ্ক্ষা।
মানব-মনে রয়েছে মনন ক্ষমতা৯৮ প্রক্ষোভ৯৮ ইচ্ছাশক্তি১০০। মানবমনের সম্ভাব্য উৎসের বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বোধি১০১ ভুয়োদর্শন১০২ ও যুক্তির১০৩ মাধ্যম আদি থেকেই মানুষ জ্ঞানলাভ করছে। গোড়াতে যে কোন একটিতে জ্ঞানের সূচনা হলেও পরবর্তীকালে তার বিস্তৃতি ও ব্যাখ্যার জন্য অপরটির প্রয়োগও সম্ভবপর।
আধুনিক মনোবিজ্ঞানে বোধিলব্ধ জ্ঞানের তেমন কার্যকারিতা স্বীকার করা হয় না; কার্যকারণ-পরম্পরা সূত্রের১০৪ অমোঘ বিধান ধ্রুব সত্য বলে গৃহীত হওয়ার পরই বোধিলব্ধ জ্ঞানকে অসুস্থ ব্যক্তির বিকৃত কল্পনা বলে অন্ধকারে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। অথচ কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, বিজ্ঞান অথবা তত্ত্বজ্ঞানের জগতেও বোধির মাধ্যমেই সবগুলো আবিস্কার হয় সম্ভবপর। নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ বা আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ১০৫তর্কবুদ্ধির দ্বারা আবিষ্কৃত হয়নি। তাদের সূচনা বাইরের উদ্দীপক১০৬ দ্বারা হলেও ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের দ্বারা তারা আবিষ্কৃত হয়নি। হটাৎ আলোর ঝলকানির মত মনীষীদের মনের আকাশে প্রকৃতির এসব সূত্র হয়ে ওঠে জলজ্যান্ত।
মানবজীবনে দেখা যায়, কোন এক বিশেষ বৃত্তির অতিরিক্ত অনুশীলনে ব্যক্তিজীবনে দেখা দেয় নৈরাজ্য। ক্ষুধার নিবৃত্তির জন্য মানুষ আহার করে। সেই আহার করতে গিয়ে চব্বিশ ঘণ্টাই তাতে মগ্ন থাকে, তা হলে তার স্বাস্থ্যহানি তো হবেই, তার ওপর তাকে সম্মুখীন হতে হবে আরও নানাবিধ সমস্যার। তেমনি কামকলার অতিরিক্ত অনুশীলনে মানবজীবনে চরম অধঃপতনের স্তরে উপস্থিত হয়। কাজেই দেখা যায়, কোন বিশেষ বৃত্তির অতিরিক্ত বিকাশের ফলে অন্যান্য বৃত্তিগুলো হয় অবদমিত এবং তার পরিণতিতে এক বৃত্তির সঙ্গে অন্য বৃত্তির সংঘাত ও সংঘর্ষ হয়ে পড়ে অনিবার্য।
সেরূপ কেবল একটি পদ্ধতির অনুরণেরও জ্ঞানের অন্যান্য পন্থাগুলো হয়ে পড়ে অকেজো। জ্ঞানের অন্যান্য শক্তিগুলো১০৭ হয়ে পড়ে সম্পূর্ণ অসাড়। তাই বিকাশের পথে দেখা দেয় চরম অন্তরায়।
মানবজীবনকে সুস্থ,সবল ও স্বাভাবিকভাবে বিকশিত করে তুলতে হলে তার জৈব-জীবনের নানাবিধ প্রবৃত্তির সুস্থ বিকাশ তার পক্ষে অতীব প্রয়োজন। জ্ঞানের ক্ষেত্রেও বোধি,বিচারবুদ্ধি ও ভূয়োদর্শনের যথাযথ স্থান নির্দেশ করে তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করলেই জ্ঞানের পথ হয় সুগম। মানুষ সত্যের সঙ্গে পরিচয় লাভে হয় ধন্য।
মানুষের জৈব-জীবনের বিভিন্ন বৃত্তির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা দরকার। সেই যোগসূত্রের১০৮ কল্যাণে পরস্পরবিরোধী ভিন্নমুখী প্রবৃত্তির মধ্যে শৃঙ্খলা হয় প্রতিষ্ঠিত এবং ব্যষ্টিজীবনে স্থাপিত হয় ভারসাম্য। মানব মনের আদিম স্ববোধ ও পরার্থিতার মধ্যে সমতা সাধিত হলে সমাজ-ব্যবস্থা১০৯ ও ব্যষ্টিকেন্দ্রিকতা বা সমষ্টি-কেন্দ্রিকতার দোলায় না দুলে প্রগতির পথে হয় অগ্রসর।
মানবজীবনে নানাবিধ সহজাত বৃত্তি ও প্রবৃত্তির আলোচনা করলে বা মনন, প্রক্ষোভ বা ইচ্ছাশক্তির আলোচনা করলে দেখা যায়-তারা আপাতত পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন বা পরস্পরবিরোধী মনে হলেও তাদের মধ্যে একটা মৌলিক ঐক্য রয়েছে। সে ঐক্যের মূলে রয়েছে মানুষের আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি এবং আত্ম-প্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি(Self perpetuation)। মানুষ প্রাথমিক পর্যায়ে তার স্বজাতীয় ও বিজাতীয় নানাশ্রেণীর শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে চায়। এজন্যই তার মধ্যে সহজাত নানাবিধ বৃত্তি দেখা দেয়। আবার এ বিশ্বের নানাবিধ শত্রু থেকে নিরাপদ হলে সে এ বিশ্বে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হতে চায়। এ দুটো বৃত্তিকে একত্রে আত্ম-সংরক্ষণ(Self preservation) – এর বৃত্তি বলা যায়। অনুধাবন করলে দেখা যায়-মানুষের ক্ষুধা,যৌন প্রেরণা, প্রকৃতির সঙ্গে একীভূত হওয়ার বসনা, সৌন্দর্য ভোগ করার প্রবৃত্তি, প্রেম, আত্মত্যাগ,স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, এ বিশ্বের প্রকৃতি পরিচয় লাভ করার জন্য বাসনা, রুচিবোধ, নীতিবোধ প্রভৃতি সকল বৃত্তির মূলে রয়েছে সেই আত্মরক্ষা বা আত্মপ্রতিষ্ঠার বাসনা। ক্ষুধা নিবারিত না হলে মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা নেই। এজন্য এ বৃত্তির চরিতার্থতা তার জীবনের পক্ষে প্রয়োজন। যৌন প্রেরণার মাধ্যমে মানুষ এ বিশ্বে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ পায়। সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে মানুষ অমরত্ব লাভ করতে চায়। প্রকৃতির সঙ্গে বিরোধিতা করে মানুষ টিকে থাকতে পারে না বলে –তার আত্মরক্ষার জন্য প্রকৃতির সঙ্গে মৈত্রীর সম্বন্ধে আবদ্ধ হতে চায়। সৌন্দর্য ভোগের মধ্যে এমন এক চিরন্তন সত্তার সন্ধান পেতে চায়, যাকে লাভ করার ফলে সে এ বিশ্বে চিরস্থায়ী হয়ে বাস করতে পারে। প্রেমের মাধ্যমে সে তার জীবনে বলিষ্ঠতা লাভ করতে চায়, যার ফলে সে সবকিছুকেই তুচ্ছ করে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে। এ বিশ্বের প্রকৃত পরিচয় লাভ তার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন। কারণ এ পরিচয় লাভ করতে পারলেই তার পক্ষে স্থায়ী স্থিতির রয়েছে সমূহ সম্ভাবনা। ভাল ও মন্দের পার্থক্য বিচার করার মধ্যেই তার মধ্যে রুচিবোধ প্রকাশিত হয়। এ পার্থক্য বিচারের মূল ভিত্তি হচ্ছে-তার জীবনের পক্ষে সহায়ক ও জীবনের পক্ষে মারাত্মক বিষয়ের পৃথকীকরণ। এ পার্থক্য বিচার না করতে পারলে সে বহু পূর্বেই ধরাপৃষ্ঠ থেকে উধাও হয়ে যেত। এ বিচারই কালে জীবন থেকে পৃথক নীতিবোধ হলে স্বতন্ত্র এক নীতিতে পরিণত হয়। কাজেই এ সকল বৃত্তি ও প্রবৃত্তির আলোচনা করলে একথাই প্রমাণিত হয়-সবগুলো বৃত্তির মূলেই রয়েছে দুটো লক্ষ্য। একটা হচ্ছে-মানুষের আত্মরক্ষা (Self protection) অপরটা হচ্ছে আত্মপ্রতিষ্ঠা (Self perpetuation)।
এ সব বৃত্তি এ প্রবৃত্তির মূলত উদ্দেশ্য সাধনমূলক স্থিতি থাকলেও বর্তমানে তারা স্বয়ংসম্পূর্ণরূপেই দেখা দিচ্ছে। তবে এ ব্যাপারটি কেবল বৃত্তি ও প্রবৃত্তির বেলায়ি সত্য নয়। মানবজীবনের নানাবিধ আচরণেও তা প্রকাশ পায়। একদা দেহের পুষ্টির জন্যই মানুষ আহার করত, লজ্জা শরম নিবারণের জন্য কাপড় পরতো। এখন আহার্যের ব্যাপারে মানুষের লক্ষ্য শুধু ক্ষুধার নিবৃত্তি নয়-জিহ্বার স্বাদেরও পরিতৃপ্ত বটে। তেমনি নানাবিধ সূক্ষ্ম বস্ত্রাদি তৈরি করে মানুষ শুধু লজ্জা নিবারণই করতে চায় না সঙ্গে সঙ্গে পরিহিত বস্ত্রের মাধ্যমে তাকে অন্যান্য লোকের কাছে মোহনীয়ও করতে চায়। তবে গোড়াতে আহার্য পুষ্টিকর না হলে যতই সুস্বাদু হোক না কেন তাতে দীর্ঘকাল মানুষ মজে থাকতে পারে না। তেমনি পরিধানের বস্ত্র দ্বারা লজ্জা নিবারণ না হলে তার দ্বারা বস্ত্র পরিধানের আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না।
এ জন্য মানবজীবনকে সুষ্ঠুভাবে বিকাশের পথে নিয়ে যেতে হলে তার জন্য এমন এক প্রকল্প(Hypothesis) গ্রহণ করতে হবে যাতে তার জীবনে সম্পূর্ণভাবে সন্তোষ বিধান সম্ভবপর হয়। তার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে আমাদের এমন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে, যা আমাদের জীবনকে নানাবিধ শত্রুর আক্রমণ থেকে নিরাপদ রাখতে পারে। তার দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে- এ প্রকল্পের মধ্যে এমন প্রতিশ্রুতি থাকবে- যাতে এ বিশ্বে আমরা অমরত্ব বা আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করার সান্তনা পেতে পারি।
যদিও নানাবিধ বৃত্তি ও প্রবৃত্তির মূলে রয়েছে আত্মরক্ষা বা আত্মপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্য-তবুও তারা আপাতত স্বাধীন ও স্বনির্ভর রূপেই দেখা দিচ্ছে, এজন্য সে প্রকল্পের মধ্যে এমন উপাদান থাকে- যাতে সে বৃত্তি ও প্রবৃত্তিগুলো ও সন্তোষ লাভ করতে পারে।
এ প্রকল্পের মধ্যে শুধু পূর্বোক্ত বিষয়গুলোর সন্তোষ বিধান হলেই হবে না- তার মধ্যে জ্ঞানের নানাবিধ মাধ্যমেরও সন্তোষ ও বিকাশ হওয়া বাঞ্ছনীয়।
আমরা পূর্বেই দেখেছি-জ্ঞানকে শুধু পঞ্চেন্দ্রিয়জাত সীমার মধ্যে আবদ্ধ করলে জ্ঞানের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় না। তেমনি জ্ঞানকে শুধু বুদ্ধি অথবা বোধির মধ্যে সীমাবদ্ধ করলেও জ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপ প্রকটিত হয় না। পঞ্চেন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতা বা বুদ্ধি ও বোধির অনুশীলনের ফলে যে ব্যাপক ও সর্বাত্মক আকারে জ্ঞান দেখা দেয়- তারই ভিত্তিতে এ বিশ্ব জগৎ বা স্থিতি সম্বন্ধে যে প্রকল্প গঠন করা হয় সে প্রকল্পই প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের সর্বাত্মক সন্তোষ দানে সমর্থ।
অতএব আমাদের জীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ও তার সন্তোষ বিধানের এরূপ একটা প্রকল্প গঠন করা অত্যাবশ্যক।
এ ক্ষেত্রে বুদ্ধির সন্তোষ ও জীবনের সন্তোষের মধ্যেও পার্থক্য প্রদর্শন করা অবশ্য কর্তব্য। বুদ্ধির সন্তোষ দানের জন্য যুগে যুগে নানাবিধ দার্শনিক মতবাদের উৎপত্তি ও প্রতিষ্ঠা হয়েছে। অতি আদিকালের গ্রিকদের মধ্যে যে সংস্কৃতির বিকাশ হয়েছিল- তাতে একে একে জড় বস্তুগুলোকে এ জগতের আদি সত্তা হিসেবে গ্রহণ করে ক্রমশ গ্রিক চিন্তাধারা অমূর্ত বিষয়ের দিকে ধাবিত হয়েছে। তাতে সাময়িকভাবে মানস-মানস, বিশেষত মানববুদ্ধি সন্তোষ লাভ করলেও মানবজীবন তাতে সম্পূর্ণ সন্তোষ লাভ করেনি। কারণ, বুদ্ধিই মানবজীবনের একমাত্র বৃত্তি নয়। তার সঙ্গে প্রক্ষোভ বা ইচ্ছাশক্তি তো রয়েছেই; তার ওপর নানাবিধ উপরিভাগজাত বৃত্তিও রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়-বুদ্ধিকে অভিজ্ঞতানিরপেক্ষ কোন আদিম বৃত্তি বলেও গণ্য করা যায়, - তাহলেও প্রত্যক্ষণজাত ইমেজ(image) বা কল্পনা প্রভৃতিকে অস্বীকার করার উপায় নেই। তেমনি প্রক্ষোভজাত নানাবিধ বিষয় এবং ইচ্ছাশক্তির নানবিধ দাবী ও প্রকাশকেও অস্বীকার করা যায় না। কাজেই যে ক্ষেত্রে শুধু বৃদ্ধির সন্তোষ বিধানের জন্যই রয়েছে একমাত্র লক্ষ্য- সে মনোবৃত্তি বা তদ্জাত সিদ্ধান্তকে জীবনের চরম সন্তোষ বিধানের সূত্র হিসেবে গ্রহণ করা যায় না।
এ জন্যই এক্ষেত্রে দর্শন ও জীবন-দর্শনের অর্থাৎ শুধু বুদ্ধিজাত সিদ্ধান্তের ও নানাবিধ বৃত্তির সন্তোষ বিধানকল্পে গঠিত প্রকল্পের পার্থক্য সম্বন্ধে অবহিত হওয়া কর্তব্য। বুদ্ধির কারসাজিতে এখন পর্যন্ত মানুষ যেসব সিদ্ধান্তে এসে উপনীত হয়েছে-তাতে কেবল বুদ্ধিই সন্তোষলাভ করেছে। মানবজীবনের আরও নানাবিধ বৃত্তি বা প্রবৃত্তি তাতে সন্তোষলাভ করেনি।
এখানেই দর্শন ও ধর্মের মধ্যে রয়েছে গুরুতর পার্থক্য। দর্শন মানুষের বুদ্ধিকে সন্তোষদানে সাময়িকভাবে সমর্থ হয়। ধর্ম বা জীবনদর্শনের সার্থকতা হচ্ছে মানবজীবনের নানা বিষয়ের সন্তোষদানের সামর্থ্য। এজন্য মানবজীবনের দর্শনের প্রভাবের চেয়ে ধর্মের প্রভাব গুরুতর ও দীর্ঘস্থায়ী। সমগ্র আদি যুগে কেবল দর্শনের চর্চা করা সত্ত্বেও খ্রিষ্ট ধর্মের আবির্ভাবের ফলে মানুষের মন সে ধর্মের প্রতি এমনভাবে আকৃষ্ট হল কেন, এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়-জীবনের একমাত্র বৃত্তি বুদ্ধির সন্তোষ বিধানে পর্যবসিত হওয়ার অন্যান্য বৃত্তি ও প্রবৃত্তির সন্তোষ-বিধানের জন্যই সে প্রতিক্রিয়া এরূপ প্রচণ্ডভাবে দেখা দিয়েছিল। দর্শন ও জীবন-দর্শনের মধ্যে আমরা এরূপ পার্থক্য করিনে বলে অনেক সময় শুধু বুদ্ধির আলোকে আমরা জীবন-দর্শনের আলোচনায় প্রবৃত্ত হই।
আমাদের তাই এ পার্থক্যকে সামনে রেখেই সে প্রকল্পের গঠনে অগ্রসর হতে হবে। আমাদের লক্ষ্য হবে এমন এক প্রকল্প গ্রহণ, যাতে কেবল বুদ্ধি নয়, সকল বৃত্তিও সন্তোষ লাভে হয় সমর্থ। এরূপ একটা প্রকল্পের সন্ধান আমরা পাচ্ছি ইসলামের আল্লাহ্ নামক ধারণার মধ্যে। এ ধারণার কোন ইন্দ্রিয়লব্ধ বা প্রত্যক্ষণজাত ধারণা নয়। বুদ্ধি দ্বারাও এ ধারণার সন্ধান পাওয়া যায়নি। এ ধারণার সন্ধান পেয়েছেন হযরত রসূলই-ই আকরাম (সঃ) প্রত্যাদেশ বা revelation-এর মাধ্যমে। এ প্রত্যদেশ স্বজ্ঞারই এক বিশেষ সংস্করণ। আমরা মানব-জ্ঞানের আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্বেই দেখতে পেয়েছি স্বজ্ঞা থেকে নানাবিধ আবিস্কার সম্ভব হতে পারে। জুঙের বর্ণনা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, স্বজ্ঞার কার্যকারিতার ফলে দ্রষ্টার সৃষ্টি হতে পারে। হযরত রসূল-ই আকরাম (সঃ) দীর্ঘকাল হেরা পর্বতে সত্য লাভ করার জন্য যে তপস্যা করেছিলেন তারই ফল হিসেবে প্রথমে ২৭ শে রমযানের রাত্রিতে আল্লাহ্র বাণী নিয়ে ফেরেশতা জিবরাইল (আঃ) দেখা দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্ সম্বন্ধে পূর্ণ ধারণা হযরতের মানসে জীবন্ত হয়ে দেখা দেয়।
এ জন্যই দেখা যায়, জ্ঞানের রাজ্যে অন্বেষণকারী যাতে অবলীলাক্রমে অগ্রসর হতে পারে, তার জন্য অন্য কোন স্বতঃসিদ্ধের প্রয়োজন দেখা দেয়নি। জ্ঞানবিস্তার আলোচনা করলে দেখা যায়-সাধারণত পঞ্চেন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান ও বুদ্ধিজাত জ্ঞানকেই শুধু দুটো রূপ বলে ধরে নেয়া হয়। অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকদের মতবাদ অনুসারে আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমরা যে সব সংবেদন লাভ করি, তার ভিত্তিতেই আমাদের জ্ঞানের সৌধ গড়ে তুলতে হবে। এজন্য এ মতবাদের প্রবর্তক জন্ লক মন্তব্য করেছেন- There is nothing in the intellect; which was not previously in sensation- অর্থাৎ আমাদের বুদ্ধিতে এমন কোন কিছুই নেই যা পূর্বে সংবেদনের মধ্যে ছিল না।
অপরদিকে বুদ্ধিবাদীদের বক্তব্য হচ্ছে-বুদ্ধি দ্বারাই সত্যের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের রয়েছে একমাত্র সম্ভাবনা। বুদ্ধি বা যুক্তিবাদীদের মুখপাত্র হিসেবে সুপ্রসিদ্ধ জার্মান দার্শনিক হেগেল বলেছেন- Whatever is real is rational and whatever is rational is real. অর্থাৎ যা কিছু বাস্তব বা যুক্তিপূর্ণ এবং যা কিছু যুক্তিপূর্ণ তা বাস্তব। এ নীতির প্রথম দিকটা গ্রহণ করতে সকলেই সম্মত। কারণ যা কিছু সত্য তা যুক্তিপূর্ণ হতে বাধ্য। যাতে কোন যুক্তির অবকাশ নেই- তা হয় কাল্পনিক, না হয় মিথ্যা। তবে যা যুক্তিপূর্ণ তা বাস্তব বলা সব সময় ঠিক নয়। কারণ যুক্তির ধারায় আমাদের পক্ষে এমন এক স্তরেও আসা সম্ভবপর, যার স্থিতির স্বপক্ষে কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণ নেই বা অন্য কোন প্রমাণও নেই। তবে অভিজ্ঞতাকে বা যুক্তিকে- যে কোন পদ্ধতিকেই জ্ঞান লাভের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করি না কেন- অভিজ্ঞতা বা যুক্তি সে আমাদের সঠিক জ্ঞান দান করতে পারে, সে সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত হতে পারিনে। এক্ষেত্রে আমাদের অভিজ্ঞতা বা যুক্তির বহির্ভূত অন্য কোন প্রত্যয়ের ওপর আস্থা স্থাপন করতে হবে। কেননা, এ বিশ্ব বিধানে এমন কোন শক্তি থাকতে পারে, যা সবসময়ই মানুষকে প্রতারিত করে। আধুনিক দর্শনের পিতা ডেকার্থ তাঁর অনুসন্ধানের প্রথম স্তরে এজন্য সবকিছুইকেই অবিশ্বাস করতে ছিলেন প্রস্তুত। অবশেষে Cogito Ergo Sum (আমি চিন্তা করি বলে আমি আছি) এ সত্যে এসে উপনীত হন। তবে এখানে প্রশ্নের অবকাশ রয়েছে। তিনি যে চিন্তা করেছেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই- তবে সে চিন্তার বিষয়বস্তু সত্য কিনা তার তো বিচার হয়নি। এমনও তো হতে পারে যে, তাঁর চিন্তা সত্য, তবে তিনি চিন্তার ক্ষেত্রে বারবার শয়তানের দ্বারা প্রতারিত হচ্ছেন। তারঁ চিন্তা তাঁর সামনে যত সব বিষয় উপস্থাপিত করছে- বাস্তবে সে সবের কোন অস্তিত্ব নেই। চিন্তার বিষয়বস্তু পরিচ্ছন্ন হলেই তা সত্য হয় না। কোন চিন্তা সত্য হতে হলে বাস্তবের সঙ্গে তার যোগ চাই। সে যোগ যে চিন্তার পক্ষে সম্ভব হয়েছে,- তার কোন সার্টিফিকেট আমরা পাচ্ছিনে। এজন্য আমাদের ধরে নিতে হয় এ বিশ্ব চরাচরের সবকিছুই এমনভাবে সৃষ্ট যে, তা মানব জ্ঞানের পক্ষে অধিগম্য। সে স্বতঃপ্রমাণের ভিত্তি অভিজ্ঞতা বা যুক্তি নয়। সে স্বতঃপ্রমাণ আসে প্রত্যয় থেকে। ইসলামী মতে বলা হয়-আল্লাহ্কে স্বীকার করলে জ্ঞাতার সঙ্গে জ্ঞেয় বস্তুর সম্বন্ধ সবসময়ই পরিস্কার হয়ে দেখা দেয়। আল্লাহ্র বিধান মতে জ্ঞাতা সত্যিকার জ্ঞানলাভে সমর্থ। কেননা আল্লাহ্ এ বিশ্বকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, তাতে জ্ঞাতার পক্ষে গান লাভ করার রয়েছে সমূহ সম্ভবনা।
আল্লাহ্র এ ধারণাকে মানবজীবনের সকল সমস্যার সমাধানে সফল বলে স্পষ্টই প্রমাণিত হয়। কারণ, আমরা পূর্বেই দেখেছি-শুধু বিচার-বুদ্ধির সন্তোষ লাভই মানবজীবনের কাম্য নয়। মানুষের মধ্যে তার সবগুলো বৃত্তি ও প্রবৃত্তির সন্তোষ লাভের রয়েছে অদম্য আকাঙ্ক্ষা। তার মধ্যে যেমন যৌন আবেগের পরিতৃপ্তির জন্য আকাঙ্ক্ষা তেমনি ক্রোধ, লোভ সবগুলো রিপুকেই যথাযথ ব্যবহার করার জন্যে রয়েছে তাগিদ। আল্লাহ্ নামক এ ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর আদেশ-নিষেধপূর্ন যে পুস্তক-কুরআন-উল-করীমের আলোকে মানুষ তা সহজেই লাভ করতে পারে। এমনকি যে কল্পনাকে মানুষ শিশুদের জীবনে কার্যকরী এক বৃত্তি বলে উপহাস করে-সেই কল্পনারও যথাযথ সন্তোষ বিধানের সূত্র রয়েছে। অতএব জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আল্লাহ্র বিভিন্ন গুণ কিভাবে কার্যকরী হতে পারে-সে সম্বন্ধে আমাদের আলোচনার প্রয়োজন।
পূর্ণাঙ্গ দর্শন ও ইসলাম
সে দর্শনের উপকরণ হবে জীবন্ত মানুষের সবগুলো বৃত্তি ও প্রবৃত্তি। তার লক্ষ্য হবে পূর্ণ মানুষ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ। তার নৈতিক আদর্শ হবে পরস্পর ভিন্নমুখী প্রবৃত্তির সামঞ্জস্যবিধান। তার সামাজিক ও রাষ্ট্রিক আদর্শ হবে ব্যষ্টি ও সমষ্টির অধিকারের সমন্বয়।
সে পূর্ণাঙ্গ জীবন-দর্শনেরই অপর নাম ইসলাম। ইসলামকে তাই বলা হয় মানবতার ধর্ম। সেই ধর্মের উৎপত্তি হযরত মুহাম্মদ মুস্তফার (সঃ) প্রচার থেকে নয়-সৃষ্টির আদি থেকেই নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ভুল-ভ্রান্তির পথে মানুষ তার পূর্ণ পরিচয় লাভের জন্য এ পথেই চলছে। প্রয়োগ১১০ অথবা বৃদ্ধির১১১ আলোকে সে বিশাল জীবনের আংশিক আভাস যে মানুষ পেতে পারে না, তা নয়। কিন্তু সে আংশিক সত্যকে পূর্ণ সত্য ভ্রমে তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে মানুষ হয়ে পড়ে দিশেহারা।
হযরত মুহাম্মদের (সঃ) পূর্বে যারা দুনিয়ার সত্য প্রচার করেছিলেন ইসলাম তাঁদের অস্বীকার করেনি, বরং যথেষ্ট শ্রদ্ধার সঙ্গেই তাঁদের স্মৃতি বহন করছে। তাঁদের মতবাদ কোন বিশেষ দেশের বা বিশেষ কওমের লোকের ওপর প্রযোজ্য হওয়ার অথবা মানবজীবনের কোন বিশেষ দিকের ওপর জোর দেওয়ার কালে তাদের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়। তবুও ইতিহাসের ধারায় জ্ঞানের ও নীতির এক একটা বিশিষ্ট পর্যায় হিসেবে এখনও তাদের মূল্য রয়েছে যথেষ্ট। ইসলামকে বলা হয় মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। মানব প্রকৃতির সঙ্গে তার অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ বর্তমান। মানুষের নবী হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) বলেছেনঃ
“ সদ্যোজাত শিশু সত্য ধর্মেই জন্ম নেয়; তার পিতামাতা তাকে য়াহূদী, ক্রিশ্চিয়ান বা সেবিয়ান করে তোলে”।
ইসলাম গোড়াতেই মানবজীবনকে দেখেছে পূর্ণভাবে; সেজন্য বিভিন্ন প্রবৃত্তি বা জ্ঞানের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে তারতম্য করলেও কোনটাকেই অস্বীকার করেনি। মানবজীবনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি-ক্ষুধা, যৌনস্পৃহা প্রভৃতিকে ইসলাম কোনদিনই অস্বীকার করেনি; বরং কিভাবে ক্ষুধার নিবৃত্তি সুষ্ঠুভাবে হতে পারে, কিভাবে মানুষ জীবনে শান্তি পায়-তার ব্যবস্থা করেছে। মানব-প্রকৃতির স্বাভাবিক বিকাশের পথ সুগম করার জন্য এ জীবনদর্শনে মানবজীবনের বৈচিত্র্য গোড়াতেই স্বীকৃত হয়েছে। জগতের পূর্ণ পরিচয়ের পদ্ধতিরুপে বোধির সঙ্গে প্রয়োগ ও যুক্তি গৃহীত হয়েছে। জ্ঞানের ক্ষেত্রে যাতে কোনো কালেই কোন সীমারেখা টেনে দেওয়া না হয়, সেজন্য মানুষের নবী হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) উদাত্ত স্বরে ঘোষণা করেছেনঃ
জ্ঞান আহরণের জন্য যদি প্রয়োজন হয় চীন দেশেও যাও’।
অপর এক বাণীতে বলেছেনঃ
“জ্ঞান অর্জন প্রত্যেক মুসলিম পুরুষ ও নারীর পক্ষে ফরয (অবশ্য কর্তব্য)”।
এক্ষেত্রে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, জ্ঞান বলতে তিনি শুধু ঐশী জ্ঞানকেই বুঝতেন না। জ্ঞান ছিল তাঁর কাছে ব্যাপক। সে চীন দেশের মনীষীর জ্ঞানই হোক তার সুদূর ইউরোপের জ্ঞানই হোক, যে কোন উপায়ে লব্ধ জ্ঞানকে তিনি জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদানরূপে গ্রহণ করতেন।
এ দর্শনে ব্যষ্টিকে সমাজজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন স্বয়ম্ভরূপে কল্পনা করা হয়নি। দেহের এক অঙ্গের সঙ্গে অপর অঙ্গের যেমন অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বর্তমান, তেমনি মানুষের মধ্যেও যে একই প্রকৃতি, একই রক্তধারা বর্তমান-সে সত্যটি গোড়াতেই ঘোষণা করা হয়েছেঃ
“ এই যে তোমাদিগের জাতি-ইহা তো একই জাতি”। (সুরা আম্বিয়াঃ ২১-৬-৯১)
অপর জায়গায় বলা হয়েছেঃ
“প্রকৃতপক্ষে তোমাদের এ ভ্রাতৃত্ব একই ভ্রাতৃত্ব এবং আমি তোমাদের প্রভু; সুতরাং আমাকে ভয় কর। মানুষেরা তাদের বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত করেছে এবং প্রত্যেক জাতি তার আইন-কানুন ও লোকাচারে আনন্দ বোধ করে”। ( আল মুমিনুনঃ ২৩: ৩৫২-৫৩)
আরও জোরালো ভাষায় অন্য এক স্থানে মানুষের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়া হয়েছেঃ
‘মানুষেরা গোড়াতেই একই জাতি ছিল কিন্তু পরবর্তীকে তাতে নানা বিভিন্নতা সৃষ্টি করেছে। (সূরা ইউনুসঃ ১০: ২-১৯)
কুরআনের এই যে শিক্ষা, সে সম্বন্ধে প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে- সে জ্ঞান কোন্ পর্যায়ের? তা’প্রয়োগলব্ধ, না অন্য কোন উপায় গৃহীত? তা কি সকল মানুষের পক্ষে সহজলভ্য? না, দুনিয়ার কয়েকজন সেরা প
মানুষের পক্ষেই সে জ্ঞানলাভ সম্ভবপর? কুরআনের শিক্ষা কি অন্য উপায়ে পাওয়ার ব্যবস্থা নেই?
কুরআনের জ্ঞান হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ) লাভ করেন বোধির১১২ মাধ্যমে। তাকে অন্যান্য বোধিলব্ধ জ্ঞান থেকে পৃথক করার উদ্দেশ্য বলা হয় প্রত্যাদেশ১১৩ । সে জ্ঞান প্রয়োগ১১৪ বা যুক্তি১১৫ বিরোধী নয়। সে জ্ঞানলাভ সকল মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। যেমন বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলোর আবিস্কার সকল মানুষের পক্ষে অসাধ্য। মানুষের জীবনকে সর্বাবস্থায় সুসামঞ্জস্য ও সুস্থ করার জন্য এ প্রত্যাদেশমূলক জ্ঞানের ছিল অত্যন্ত প্রয়োজন। তা থেকে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষ কিভবে তাকে নিয়ন্ত্র করবে, সে সম্বন্ধে রয়েছে স্পষ্ট নির্দেশ। তবে প্রত্যাদেশমূলক জ্ঞানের আর যে বিশেষ প্রয়োজন নেই, তা হযরত মুহাম্মদের (সঃ) বাণী থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়। মনীষী ইকবাল তাই উদাত্ত স্বরে ঘোষণা করেছেনঃ ইসলামের নবুয়ত তার পরিপূর্ণতা লাভ ক’রে আবিস্কার করতে সমর্থ হয় যে, তার বিলোপের রয়েছে একান্ত প্রয়োজন। এ আবিস্কার আর কিছু নয়, শুধু এ উপলব্ধি যে, জীবন চিরকাল নেতৃত্বের সূত্রে আবদ্ধ থাকতে পারে না- তার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভের জন্য মানুষকে তার স্বীয় শক্তির ওপরই নির্ভরশীল হতে হবে
তাই স্পষ্ট বোঝা যায়, কুরআনের শিক্ষা গোড়াতেই মানুষকে বুঝতে দিয়েছিল যে, মানুষের পক্ষে আর প্রত্যাদেশ পাওয়ার প্রয়োজন নেই। মানুষকে তার প্রকৃতিদত্ত বিচারবুদ্ধি বা পঞ্চ ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের ওপর নির্ভর করতে হবে। তা’ থেকে আরও অবরোহ১১৩ বা deductions টেনে নেওয়া যায়; কুরআনের বাণীগুলো মানুষ গ্রহণ করেও তার বুদ্ধি ও বিচার বুদ্ধিকে কার্যকরী রাখতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, পবিত্র কুরআন মজিদে যেসব আদেশ-নির্দেশ প্রদত্ত হয়েছে সেগুলোও মানুষ তাদের বিচার-বুদ্ধির আলোকে যাচাই করে দেখতে পারে। তবে এ সম্বন্ধে মানুষের হতে হবে হুঁশিয়ার। কুরআনের আদেশাবলী এ দুনিয়ার যেমন কার্যকরী, এ দুনিয়ার পরবর্তী অপর এক দুনিয়ায়ও ফলদায়ক। কাজেই সে আদেশাবলীর মধ্যে যেগুলো কেবল এ দুনিয়ার কার্যকরী, তাদেরই বিচার সম্ভবপর। অপরগুলোর বিচার হতে পারে না। তার ওপর কুরআনের জ্ঞান প্রত্যাদেশ বলে সে জ্ঞানলাভ সম্বন্ধেও থাকতে হবে স্পষ্ট ধারণা।
প্রত্যাদেশ এমন কোন অবাস্তব জ্ঞান নয়, যার সম্বন্ধে কোন কথা বলার কারও কোন অধিকার নেই। প্রত্যাদেশ বোধিরই এক সংস্করণ এবং বোধিলব্ধ জ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞানের জগতে ও মনোবিজ্ঞানে যথেষ্ট আলোচনা করা হয়েছে। কাজেই প্রত্যাদেশের সঙ্গে বোধির কি সম্বন্ধ এবং বোধি বাস্তবিকই জ্ঞানের এক পদ্ধতি কিনা, সে সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা করা দরকার।
ইসলামের অবলম্বন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধ
ইসলামী প্রত্যাদেশ থেকে আমরা সর্বপ্রথম পাই আল্লাহ্র ধারণা। ইসলামী চিন্তাধারার মূল সূত্র আল্লাহ্। কুরআন শরীফে আল্লাহ্র স্বরূপ সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা রয়েছে। আল্লাহ্কে সর্বপ্রথমে ধারণা করা হয়েছে সকল স্থিতির মূলরূপে। সূরা ফাতিহায় বলা হয়েছেঃ
“ যত স্তুতি সবই তো আল্লাহ্র
রব তিনি বিশ্বসমূহের”* (মরহুম মুনাওয়ার আলী কৃত অনুবাদ।)
‘রব’ শব্দের অর্থ কেবল সৃষ্টিকর্তা নয়, ‘রব’ পালনকর্তা ও বিবর্তনকারীও বটে। ‘রব’ শব্দের অর্থ সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও বিবর্তনকারী।১১৭ অথচ, এই কুরআনেই অন্যান্য স্থানে তাঁকে সর্বব্যাপী সত্তারূপে১১৮, সর্বব্যাপী ও তুরীয় সত্তারূপে১১৯ ধারণা করা হয়েছে। আবার কোথাও কেবল জগৎ বহির্ভূত স্রষ্টারূপে১২০ ধারণা করা হয়েছে।
আবার এই কুরআন শরীফেই আল্লাহ্র শরণ নেওয়ার জন্য আদেশ করা হয়েছে। সূরা ফাতিহায় আল্লাহ্ মানুষকে শিখিয়ে দিচ্ছেন প্রার্থনা করতেঃ
সাহায্যের তরে যাচি
কেবলই তোমারে,
নেতা হয়ে আমাদের নিয়ে যাও
ঋজু পথে পথে।** (মরহুম মুনাওয়ার আলী কৃত অনুবাদ।)
কুরআন শরীফের সর্বত্রই মানুষের জন্য আল্লাহ্র অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা তাঁর শক্তির সাহায্য ব্যতীত মানবজীবনের ব্যর্থতা ঘোষণা করা হয়েছে।
তা’হলে প্রশ্ন দাঁড়ায়, এর মধ্যে কোন্টি সঠিক ধারণা? তিনি রব্১২১ , না তিনি সর্বব্যাপী১২২,না সর্বব্যাপী ও তুরীয়১২৩ অথবা শুধু স্রষ্টা মাত্র? অপরদিকে গোড়াতেই যদি তাঁকে স্বীকার করে নেওয়া যায়, তা হলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের পক্ষে এক মস্তবড় প্রতিবন্ধক দেখা দেয়। এ স্বীকৃতি তো বিজ্ঞানের জয়যাত্রার পথে মস্তবড় প্রতিবন্ধক দেখা দেয়। এ স্বীকৃতি তো বিজ্ঞানের জয়যাত্রার পথে মস্তবড় বিঘ্নের সৃষ্টি করে মানব-মনকে করে তোলে গোঁড়া।১২৪ যদি আল্লাহ্র দ্বারাই জগতের সবকিছু নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহলে মানুষের পক্ষে কাজকর্ম করার বা জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনার কি প্রয়োজন? তাঁর দ্বারাই তো সবকিছু সুসম্পন্ন হচ্ছে ও হবে। আবার এই কুরআন শরীফেই মানুষকে কর্মপ্রেরণা দেয়া হয়েছে তীব্রভাবে।
বলা হয়েছেঃ
‘যে পর্যন্ত না কোন জাতি তাদের নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করে আল্লাহ্ ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের ভাগ্য পরিবর্তন করেন না’।
কুরআনে বিজ্ঞানের গবেষণার জন্যও জোরালো তাগিদ দেয়া হয়েছেঃ ‘নিশ্চয়ই যে কোন সমস্যার সমাধান রয়েছে প্রত্যেক দুরূহতার জন্য প্রতিকার রয়েছে। তাই যখনই তুমি মুক্ত (অন্যান্য বিষয় থেকে ) তোমার ধ্যানকে তোমার প্রভু আল্লাহ্র দিকে কেন্দ্রিভূত করো__’।
অন্য এক স্থানে বলা হয়েছেঃ
‘ প্রভু যাকে ইচ্ছা তাকে হিকমত দান করেন এবং যারা হিকমত লাভ করে, তারা একটা পরম সুবিধা লাভ করে’।
কুরআন শরীফের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার আল্লাহ্র রসূল (সঃ) জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঐকান্তিক সাধনার জন্য মানব জাতিকে উদাত্ত স্বরে আহ্বান করেছেন। তাঁর বিভিন্ন বাণী থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর আকুল আগ্রহের জাজ্বল্যমান প্রমাণ পাওয়া যায়।
তিনি বলেছেনঃ
‘শহীদের লোহু থেকে জ্ঞানীর দোয়াতের কালি অধিকতর পবিত্র’।* (Misbah us Sirat: Spirit of Islam Ameer Ali, p.361)
এক ঘণ্টার জন্যও বিজ্ঞানের পাঠ শ্রবণ ও জ্ঞানের অনুশীলন হাজার শহীদের জানাযাতে শামিল হওয়ার চেয়ে পূণ্যতর – হাজার রাত্রির নামাযের কাতারে দাঁড়ানোর চেয়ে পুণ্যতর কাজ’।
বারবার জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলনের জন্য তিনি প্রেরণা দিয়েছেনঃ
জ্ঞানী ব্যক্তির বাণী শ্রবণ এবং হৃদয়ে বিজ্ঞান পাঠের আলোকসম্পাত ধর্মীয় কার্যাবলি থেকে উৎকৃষ্টতর- কৃতদাসের মুক্তি দেয়ার চেয়েও উন্নততর।** (Spirit of Islam: Ameer Ali)
ইসলাম জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী হযরত আলী (রাঃ) বলেছেনঃ
‘বিজ্ঞানের (অনুশীলনে) সম্মান লাভ সবচেয়ে বড় সম্মান। সে জ্ঞানের ক্ষেত্রে জীবন সঞ্চার করে সে অমর’।
বিজ্ঞানের জগতে কিন্তু আরোহ পদ্ধতিই১২৫ একমাত্র পন্থা। অতি ক্ষুদ্র, অতি তুচ্ছকে উপকরণ বা দড়ি১২৬ রূপ গ্রহণ করে তার ভিত্তিতে সার্বিক সত্যে এসে উপনীত হওয়া বিজ্ঞানের লক্ষ্য। বিজ্ঞানে অবরোহ১২৭ পদ্ধতি মোটেই গ্রহণীয় নয়। কোন কিছুকে গোড়াতে স্বীকার করে তা’ থেকে ফলাফল অবরোহ১২৮ করা বিজ্ঞানে জগত অচল।
তাই প্রশ্ন দাঁড়ায়, আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণার মধ্যে কিভাবে সঙ্গতি১২৯ আনা যায় আর আল্লাহ্র ধারণার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কিসে খাপ খেতে পারে? কুরআন শরীফে আল্লাহ্কে ধারণা করা হয়েছে প্রথমে স্বতঃসিদ্ধরূপে১৩০ তার পরে সৃষ্টিকর্তা১৩১ সর্বব্যাপী১৩২ এবং সর্বব্যাপী ও তুরীয়১৩৩ শক্তিরূপে ধারণা করা হয়েছে। আল্লাহ্কে এভাবে ধারণা না করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষ অগ্রসর হতে পারে না বলেই ধারণাগুলোর প্রয়োজন ছিল। তাঁকে চিন্তার স্বতঃসিদ্ধ১৩৪ রূপে গ্রহণ করে চিন্তার পরিণতিতে তাঁকে সৃষ্টিকর্তা, সর্বব্যাপী ও তুরীয় সত্তারূপে ধারণা করার ইঙ্গিত রয়েছে পবিত্র কুরআন শরীফে। আল্লাহ্র এ নানাবিধ ধারণা মানব-চিন্তার বিভিন্ন পর্যায়ের ফল। মানব মন অন্বেষণের প্রারম্ভে এ জগতের জ্ঞেয়তা১৩৫ এবং জ্ঞাতার শক্তির ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে বাধ্য হয়। এ বিশ্বাস কেবল আল্লাহ্র অস্তিত্বের ওপর প্রত্যয়ের ফলেই সম্ভব হয়। এ প্রত্যয়ে বলীয়ান হয়ে অন্বেষণকারী তার জ্ঞান অনুযায়ী আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণায় পৌঁছতে সমর্থ হয় এবং তা নির্ভর করে তার অভিজ্ঞতা১৩৬ ও যুক্তির ওপর। সাধারণ বুদ্ধির অন্বেষণকারী পক্ষে আল্লাহ্কে সৃষ্টিকর্তারূপে গ্রহণ করাই সহজ। মননধর্মী তত্ত্বজ্ঞানী তাঁকে সর্বব্যাপীরূপে১৩৭ গ্রহণ করেন। তত্ত্বজ্ঞান ও নৈতিক জীবনের মানগুলোর সমন্বয় সাধনের জন্য তাঁকে ধারণা করা হয় সর্বব্যাপী ও তুরীয়রূপে। উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিস্কার হয়ে পড়বে। এ দুনিয়ার নানা কলাকৌশলের নিদর্শন দেখে মনে হয় এতে নিশ্চয়ই কোন কারিগরের হাত রয়েছে। কাজেই তাঁরা মনে করেন এতে এক জগৎ বহির্ভূত কারিগর রয়েছেন।
মননধর্মী মানুষ এতে দেখতে পান ন্যায়শাস্ত্রের নানানীতির প্রকাশ। মানব মন ন্যাশাস্ত্রের যে রীতি অনুসারে দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে এক ধারণায় পৌঁছে স্বস্তি লাভ করে, তেমনি জগতের মাঝেও চলেছে এক মহাদ্বন্দ্বের লীলা। আল্লাহ্কে সর্বব্যাপী মূলাধররূপে ধারণা করলেই জগতের এ মহাদ্বন্দ্বের মীমাংসা হতে পারে। কাজেই এঁরা আল্লাহ্কে ধারণা করেন সর্বব্যাপী সত্তারূপে।* ( এ সম্বন্ধে দর্শনশাস্ত্রে শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাওয়া যায়-হেগেলীয় Pan logism-এ এবং হেগেলের ইংরেজ শিষ্য ব্রাডলির সিদ্ধান্তে।)
আল্লাহ্ সর্বব্যাপী সত্তা বলে গৃহীত হলে দুনিয়ায় পাপ-পুণ্যের আর কোন বিচার থাকে না। তিনি সর্বমূলাধার অস্তিত্ব হওয়ায় পাপ-পুণ্য সমস্তই তাঁর সত্তা থেকে সৃষ্টি হয়। কাজেই ধর্মীয় ও নৈতিক জীবনের মানগুলোর সঙ্গে তর্ক-বুদ্ধিজাত জ্ঞানের সমন্বয় সাধন করে ওরা বলেন, সর্বব্যাপী মাত্র নয়, জগতের বাইরেও তাঁর সত্তা রয়েছে সেজন্য তিনি এসব পাপ-পুণ্যের অতীত।
মানবজীবনের সকল পর্যায়ের সঙ্গে কুরআন শরীফের গভীর যোগ থাকার জন্যই আল্লাহ্কে বিভিন্নভাবে ধারণা করা হয়েছে, যাতে সকল স্তরে এবং সকল পর্যায়ের মানুষই এ থেকে শান্তি ও স্বস্তি পেতে পারে। কুরআন শরীফে আল্লাহ্ সংক্রান্ত বিভিন্ন ধারণা তাই পরস্পরবিরোধী নয় বরং মানব-জ্ঞানের পক্ষে উপযোগী করেই তাদের পরিবেশন করা হয়েছে।
তেমনি আল্লাহ্কে স্বতঃসিদ্ধ১৩৮ হিসেবে গ্রহণ করেও বিজ্ঞানের পথে কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয় না। বরং আল্লাহ্র এ ধারণাকে গ্রহণ না করলে অন্বেষণকারীর পক্ষে জ্ঞানের ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনা নেই।
আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তিস্বরূপ যেসব ন্যায়শাস্ত্রের নীতি বর্তমান, সেগুলোর আলোচনা করলেই বিষয়টি আরও পরিস্কার হবে।
জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভিত্তি তর্কশাস্ত্র। তর্কশাস্ত্রের বুনিয়াদের উপরই বিজ্ঞান গড়ে তুলেছে তার সৌধ। যা ন্যায় অনুমোদিত নয়, তা কিছুতেই বিজ্ঞানের সম্মান লাভ করতে পারে না। যে ন্যাশাস্ত্রের স্বতঃসিদ্ধ রূপে চারটি নীতি গোড়াতেই গ্রহণ করা হয়, তাদেরকে যথাক্রমে একত্বের নীতি১৩৯ , দ্বন্দ্বের নীতি১৪০ , মধ্যপন্থা অর্জনের নীতি১৪১ ও যথাযোগ্য কারণের নীতি১৪২ বলা হয়।
একত্বের নীতিতে বলা হয়, জ্ঞানের রাজ্যে জ্ঞেয় বিষয়কে এককরূপে ধরে নেওয়া দরকার। কারণ জ্ঞেয় বিষয় সবসময়ই তার স্বরূপ অক্ষুণ্ণ রাখে। যেমন কোন গাছ সম্বন্ধে ভাবতে গেলে তাকে একক হিসেবেই ভাবতে হবে। যদি গাছকে এক না ভাবা যায় তাহলে তার সম্বন্ধে কোন কিছু বলার কোন অর্থ থাকে না। কাজেই সে গাছ সম্বন্ধে কোন চিন্তা করতে হলে বা তার সম্বন্ধে কোন যুক্তি-তর্কের অবতারণা করতে হলে তাকে সব সময়ই এক সত্তারূপে ধরে নিতে হবে।
অথচ জগতের সর্বত্র দেখা যায় পরিবর্তন১৪৩। যে গাছে একদা মাত্র দুটো পল্লব দেখা দিয়েছিল, কালে তা-ই নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে মহামহীয়ান বৃক্ষরূপে ঊর্ধ্বে মাথা তুলে অসংখ্য পাখির আবাসে পরিণত হয়। আবার কালের করাল গতিতে সেই গাছই জীর্ণ হয়ে পত্রবিহীন, শাখাবিহীন কিম্ভূতকিমাকাররূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এ গাছের উৎপত্তি ও বিকাশের ধারায় মুহূর্তে মুহূর্তে নানাবিধ পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে। তার বিভিন্ন বয়সের ভিন্ন ভিন্ন ফটোগ্রাফ একত্র করলে দেখা যাবে, তাতে কত পরিবর্তন হয়েছে। তা সত্ত্বেও গাছের মধ্যে এমন একটা শক্তি১৪৪ কাজ করেছে, যার কার্যকারিতায় পরিবর্তনের মধ্যেও রয়েছে এক ঐক্য। সেজন্যই এতসব পরিবর্তনের মধ্যেও তাকে একই গাছেরূপে আমরা পরিচিত করতে পারি। কাজেই আমাদের ব্যবহারিক জীবনে বা মনকে তার সম্বন্ধে আলোচনায় তার পরিবর্তনকে উপেক্ষা করে, একত্বকেই গ্রহণ করতে হয়। অপরদিকে যে মানসে গাছ সম্বন্ধে কোন ধারণার সৃষ্টি হয় তাতেও মিনিটে মিনিটে দেখা দিচ্ছে পরিবর্তন। সেও চলেছে বিকাশের পথে। তাতেও দেখা দিচ্ছে নতুন নতুন রূপ। তবু মনের এত সব পরিবর্তনের মধ্যেও যদি তার ঐক্য স্বীকার করা না যায় তাহলে গাছ সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণার তুলনা করার জন্য কোন ঐক্যসূত্র না থাকলে কোন কথা বলারই অবকাশ থাকে না। পরিবর্তনকে মানব-মনের সত্যিকার রূপ বলে ধরে নিলে, মানব মন বলে কোন কিছুই থাকে না। বিভিন্ন সংবেদনের১৪৫ উৎপত্তিও লয়ের ফলে তাতে দেখা দিচ্ছে ছায়াচিত্রের মত ভাবধারার উদয় ও অস্ত, তাদের কারো সঙ্গে কারোর কোন যোগসূত্র নেই। সেইজন্য জ্ঞানের ক্ষেত্রে মানব মনকে ‘এক’ বলে ধরে নিতে আমরা বাধ্য এবং তাতে একটা একীকরণের১৪৬ শক্তি১৪৭ কার্যকরী বলে ভাবা অনিবার্য হয়ে পড়ে।
কাজেই, আমাদের ধরে নিতে হবে-ভাববার বিষয় ও ভাববার শক্তিকে নির্বিকাররূপেই ভাবতে হবে। একেই ন্যাশাস্ত্রে ঐক্যের নীতি১৪৮ বলা হয়। এ নীতির স্বীকৃতি ব্যতীত আমাদের ভাববার বা যুক্তির অবতারণা করবার অধিকার থাকে না।
দ্বন্দ্বের নীতিতে১৪৯ বলা হয়, কোন বস্তু বা বিষয় সম্বন্ধে ভাবতে গেলে তাতে পরস্পরবিরোধী১৫০ গুণের সমাবেশ করা যায় না। কোন বস্তুকে স্থিতিশীল১৫১ ও অস্থিতিশীল১৫২ বলে আমরা ভাবতে পারি না। কোন বস্তুকে একই সঙ্গে কালো ও কালো নয় রূপে ভাবা মানব-মনের পক্ষে অসম্ভব।
মধ্যপন্থা বর্জনের নীতিতে১৫৩ বলা হয়, কোন বস্তুতে যেমন পরস্পরবিরোধী দুটো গুনের১৫৪ সমাবেশ ভাবা অসাধ্য, তেমনি পরস্পরবিরোধী দুটো গুণের বহির্ভূত অন্য কোন মধ্যবর্তী গুণ থাকাও কোন বস্তুতে সম্ভব নয়। রঙের দিক থেকে বিচার করলে যে কোন বস্তুই, হয় কালো না হয় কালো-নয়ই, হবে। এ দুটো গুণের বাইরে রঙের জগতে আর কিছুই নেই।
এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, দ্বন্দ্বের নীতি বা মধ্যপন্থা বর্জনের নীতি ঐক্যের নীতির ওপর নির্ভরশীল। ভাববার বিষয় যদি তার ঐক্য বজায় রাখতে না পারে, তা হলে তার মধ্যে পরস্পরবিরোধী গুণ থাকা না থাকার কোন মানে হয় না। আমাদের চিন্তার বিষয়১৫৫ এক থাকে বলেই তাতে পরস্পরবিরোধী গুণাবলির সমাবেশ করা যায় না বা পরস্পরবিরোধী গুণের একটিকে তাতে আরোপ করতে হয়। যদি বিষয়বস্তু বলে কোন কিছুরই অস্তিত্ব না থাকে, তাহলে পরস্পরবিরোধী গুণের সমাবেশ বা তাদের কোনও একটি গ্রহণ বা বর্জনের প্রশ্নই ওঠে না। তাহলে দেখা যায়, একত্বের নীতির১৫৬ মৌলিক নীতি। প্রয়োগের জন্য স্বীকার করতে হয় দ্বন্দ্বের নীতি বা মধ্যপন্থা বর্জনের নীতিকে।
যথাযোগ্য কারণের নীতিতে১৫৭ বলা হয়, জগতের যা কিছু ঘটেছে বা রয়েছে তার জন্য একটা উপযুক্ত কারণ আছে। এ জগৎ যদি খাপছাড়া হত, এতে যদি সবকিছুই স্বতঃউৎসারিত হত তাহলে এর স্থিতি সম্বন্ধে বা এর অন্তর্গত তার কারণ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা হত অসম্ভব। কোন বিষয়কে জানার অর্থ তার কারণ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ সম্ভব হয়। একেই ন্যায়শাস্ত্রের আরোহ বিভাগে বলা হয় কারণের নীতি। এ কার্যকারণের নীতিকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করলে একে প্রকৃতির সমরুপতা রূপেই গ্রহণ করতে হয়। প্রকৃতিতে কার্যকারণের সূত্র রয়েছে সত্য। দুনিয়ার সকল কিছুই এই কারণের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় কিন্তু কার্যকারণের মধ্যে বা গোটা পৃথিবীর মধ্যে যদি সমরূপতা না থাকে; তাহলে কেবল কারণ দ্বারা কোন কিছুর ব্যাখ্যা করা যায় না।
কারণের নীতিতে বলা হয়-জগতে যা কিছু আছে বা ঘটেছে, তার মূলে রয়েছে একটা কারণ। একজনের হাত যদি পুড়ে যায় তাহলে আগুনকেই বলতে হবে তার কারণ। কিন্তু যদি মানুষ ও আগুন উভয়েরই প্রকৃতি বদলে যায় তাহলে আজকে পোড়ার কারণ আগুন হলেও অনাগতকালে তা আর কারণ থাকবে না। মানুষের শরীরের উত্তাপ যদি আগুনের উত্তাপ থেকে আরও বেড়ে যায়, তাহলে আগুনের স্পর্শে জ্বালা-যন্ত্রণা পাওয়া দূরের কথা, হয়ত চন্দনের প্রলেপের সুখ অনুভব করতে পারে অথবা যদি আগুন তার দাহিকা শক্তি হারায়, তাহলেও তার স্পর্শে বর্তমানেও আমরা আর জ্বালা-যন্ত্রণা পাবো না। তাহলে দাহিকা ও আগুনের মধ্যে যে কার্যকারণের সম্বন্ধে তাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে ভাবতে হবে, তাদের প্রকৃতি বদলায় না। তারা চিরদিনই এক এবং অবিকৃত থাকলেই তাদের কার্যকারণ সম্বন্ধে অব্যাহত থাকতে পারে। ন্যায়শাস্ত্রে তাকে বলা হয় Uniformity of essence অথবা সারের সমরূপতা।
দ্বিতীয়ত-আগুন ও উত্তাপের প্রকৃতি চিরকাল অবিকৃত থাকলেও বর্তমানে তাদের যে সম্বন্ধ তাই বা কেমন করে অব্যাহত থাকবে? আমরা কি ভাবতে পারি না-আজকে না হয় কোন বস্তুতে আগুন দিলে দেখা যায় তা’ জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে যায়-আগুন ও দাহিকার সম্বন্ধে তাই বলে কি চিরদিন অব্যাহত থাকবে? ভবিষ্যতে তাদের এ কার্যকারিতার সম্বন্ধে তো নাও থাকতে পারে।
তার জন্য আমাদের স্বীকার করে নিতে হয় যে, তাদের ব্যবহারিক দিকের কোন পরিবর্তন হয় না। আজ তারা যেভাবে কাজ করে যাচ্ছে অনাগত ভবিষ্যতে বা চিরদিনই তাদের স্বভাবে এ ব্যবহার প্রকাশ পারবে। একেই বলা হয় ব্যবহারের সমরূপতা।
তাহলে আমাদের চিন্তাধারার জন্য এবং বৈজ্ঞানিক বা ব্যবহারিক জীবনের ব্যাখ্যার জন্য শেষ পর্যন্ত দুটো নীতির স্বীকৃতিই অবশ্য গ্রহণীয়। একত্বের নীতি১৫৮ ও প্রকৃতির সমরূপতা নীতি১৫৯ না মেনে নিলে চিন্তাও চলে না, কোন গবেষণাও চলতে পারে না।
অথচ এ দুটোর কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব নয়। কারণ এগুলোর ব্যাখ্যা দিতে গেলেই এগুলোকে গ্রহণ করে নিতে হবে। তাতে ন্যায়শাস্ত্রের ভাষায় Petitio principal হয়ে যাবে।
তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে, এ দুটো নীতির পশ্চাতেও রয়েছে আরও দুটো স্বতঃসিদ্ধ। একত্বের নীতিতে বলা হয়, কোন বস্তু বা বিষয় তারই মত। তাকে সাংকেতিকভবে প্রকাশ করা হয় ক=ক। অর্থাৎ বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্যেও ‘ক’ নামক বিষয়ের মধ্যে রয়েছে এক ঐক্য। এ ছাড়া আমরা ‘ক’ সম্বন্ধে কোন বিষয় ভাবতেও পারি না এবং বলতেও পারি না। যেহেতু পারি না, তাই আমদের ধরে নিতে হবে ‘ক’ নামক বিষয়ের বিভিন্ন পরিবর্তনকে তুচ্ছ করে তার একত্বকেই আমাদের গ্রহণ করতে হবে।
সমরূপতা নীতিতে১৬০ আমারা স্বীকার করে নিচ্ছি, পৃথিবীর সর্বত্র রয়েছে সমরূপতা১৬১ , কোন বস্তু বা শ্রেণী তার প্রকৃতি বদলায় না এবং দুটো বিষয়ের মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ স্থাপিত হলে তার মধ্যেও কোন ছেদ হয় না।
এখানে ভেবে দেখবার বিষয় এই যে, আমরা চিন্তা করতে বা তর্কশাস্ত্রে অগ্রসর হতে পারি না বলে কেন এই নীতিকে গ্রহণ করবো? না হয় না-ই ভাবলাম, না-ই তর্ক করলাম, তাতে কি যায় আসে? জ্ঞানের রাজ্যের কার্যকারণ আবিস্কার না করলে হয়ত আমাদের অগ্রসর হওয়ার পথ নেই। তাতে এমন কি হল? না-ই বা অগ্রসর হলাম!
কিন্তু মানব-মন তাতে আশ্বস্ত হয় না। সে গোড়াতেই ধরে নেয়- এ জগৎ জ্ঞেয়১৬২ এবং মানুষ হিসাবে আমরা সকলেই জ্ঞাতা১৬৩ । মানবমন জ্ঞান অন্বেষণের আদিতেই স্বীকার করে নেয়, এ জগৎ কোন দুর্বোধ্য পুঁথি নয় এবং তাকে জানবার শক্তি মানুষের মধ্যে রয়েছে। কাজেই এটাই জ্ঞানের রাজ্যে আদিম নীতি, এটাই সবচেয়ে বড় স্বতঃসিদ্ধ। যদিও আমরা আপাতত এ স্বতঃসিদ্ধ সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল নই, তবুও জ্ঞানের রাজ্যে একে গ্রহণ করেই আমরা অগ্রসর হই।
অপরদিকে জ্ঞানের চরম পরিণতিতে আবার এসে চরম ঐক্যে পৌঁছার প্রবৃত্তিও রয়েছে মানুষের মনে। সকল বিশৃঙ্খলা, সকল বৈসাদৃশ্যের অন্তরালেও মানুষ আবিস্কার করতে চায় এক চিরন্তন নিয়ম, এক চরম শৃঙ্খলা প্রবণতা যদি স্বতঃসিদ্ধ নয়, তবুও তাকে মানব-মনের এক বিশেষ ঝোঁক বলতে হবে।
বিজ্ঞান ও দর্শনের ইতিহাসে রয়েছে তার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত। ভাববাদ বা জড়বাদে জগতের আদি সত্তারুপে স্বীকার করে নেয়া হয় এক আদি নীতি। ভাববাদী দর্শনে সাধারণত জ্ঞানের পদ্ধতিরুপে স্বীকার করে নেয়া হয় যুক্তিকে। সে যুক্তির ধারার দ্বন্দ্বের ফলে অবশেষে উপস্থিত হতে হয় পরম ব্রহ্মে। তার উদাহরণস্বরূপ রয়েছে হেগেলীয় দর্শন। জড়বাদে জগতের আদি উপকরনরূপে স্বীকার করে নেয়া হয় কতকগুলো অবিভাজ্য অণুকে। জড়বাদী দর্শনে জ্ঞানের একমাত্র পদ্ধতি ভূয়োদর্শন অথবা ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান। সে জ্ঞানের আলোকে জগতের সব বস্তুর বিশ্লেষণ করলে ধরা পড়ে চেতনাহীন, সমগুণ বিশিষ্ট অণু ও পরমাণুর খেলা।
বহুবাদের বিভিন্ন রূপ থাকা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে রয়েছে এক ঐক্য। লাইবনিটজের১৬৪ বা জেমসের১৬৫ মধ্যেও রয়েছে সাদৃশ্য। লাইবনিট্জ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন তাঁর স্বতন্ত্র monad১৬৬ গুলোর মধ্যে রয়েছে এক সংস্থা১৬৭ ও ঐক্য১৬৮ ,কারণ তাদের মধ্যে সমগ্রের রূপ প্রতিভাত হয়। তারা যুক্তিসঙ্গত নীতি দ্বারা পরিচালিত এবং তাদের প্রত্যেকের মধ্যেই সেই যুক্তিসঙ্গত সংস্থা এক বিশেষ দিকে বা বিশেষ স্তরে প্রতিবিম্বিত হয়।* (Patrick: Introduction to Philosophy,p.228)
উইলিয়াম জেম্স্ বস্তুর বা বিষয়ের স্বাতন্ত্র্যের১৬৯ ওপর গুরুত্ব আরোপ করে নিয়ম ও শৃঙ্খলা পশ্চাৎভূমিতে ঠেলে দিয়ে বলেছেন, নিয়ম জাগতিক অভ্যাস, জীবনের পদ্ধতি ব্যতীত আর কিছুই নয়। বস্তুগুলো একত্র জড়ো হয়েছে আকস্মিকভাবে এবং তাদের স্ব-ইচ্ছায়ই একত্র আছে-তারাই নিয়মগুলো সৃষ্টি করেছে। যেমনভাবে পরস্পরের মিলনের জন্য সাম্প্রদায়িক নিয়ম গঠিত হয় তেমনি তারা নিয়ম গঠন করেছে১৭০। ** ( William James: The Will to Believe.) কিন্তু তারপরেই আবার বলেছেন, ‘সেই স্বতঃউৎসারিত স্বতন্ত্র সত্তাগুলোর সমষ্টির অভ্যাসের ফলেই প্রাকৃতিক নিয়মাবলির উৎপত্তি হয় এবং সে স্বতন্ত্র সত্তাগুলো এ সব নিয়ম থেকে অধিকতর বাস্তব১৭১ । কাজেই তাদের যে সমষ্টিগত অভ্যাস থেকে জগতের নিয়ম ও শৃঙ্খলার উৎপত্তি হয়, তাকে তিনি অস্বীকার করতে পারেননি। সুতরাং শত অস্বীকার করলেও সকল চিন্তার পরিণতিতেই মান-মন নিয়ম, শৃঙ্খলা ও সংস্থা আবিস্কার করতে বাধ্য হয়।
তা’হলে স্পষ্টই বোঝা যায়, জ্ঞানের রাজ্য চলছে চক্রাকারে। ঐক্যের নীতি সমরূপতার নীতিকে স্বতঃসিদ্ধরূপে গ্রহণ করে জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ করে।অনুসন্ধানের পরিণতিতে মানব-মনে এসে পৌঁছায় সেই নিয়ম-শৃঙ্খলা বা একত্বের নীতিতে।
স্বতঃসিদ্ধের আলোচনায় আমরা পূর্বেই দেখেছি, সর্ব-মূলাধার স্বতঃসিদ্ধ হচ্ছে জ্ঞাতার শক্তির উপর ও জ্ঞেয়তার উপর বিশ্বাস এবং যেহেতু বিজ্ঞান বা দর্শন সেই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের সম্বন্ধে বিশ্বাসের ওপর নির্ভরশীল। বিজ্ঞান ও দর্শন আজও স্বতঃসিদ্ধের কোন প্রমাণ দিতে পারেনি। এগুলো ব্যতীত জ্ঞানের চর্চা চনে না বলে এগুলোকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। ইসলাম ধরে নিয়েছে জ্ঞাতার পক্ষে জ্ঞেয় সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ সম্ভবপর, যেহেতু উভয়ে একই কারণ থেকে উদ্ভূত। তাদের উভয়েরই উৎপত্তি একই আল্লাহ্ থেকে। আল্লাহ্ স্থিতির মূল উৎস বিধায় তাঁরই কার্যকারিতার ফলে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মধ্যে এ মিলন সম্ভবপর। ইসলামী চিন্তাধারায় তাই আল্লাহ্কে স্বতঃসিদ্ধের ভিত্তিরূপেই গ্রহণ করা হয়েছে।
মানব-মন যে স্বাভাবিক প্রবণতার ফলে স্থিতির১৭২ মূলে আবিস্কার করে চরম ঐক্য ও শৃঙ্খলা, ইসলাম সেই শৃঙ্খলা ও ঐক্যকে মানব-মনের প্রতিভাস বলে মনে করেনি। আল্লাহ্র অস্তিত্বের ওপর বিশ্বাস করার ফলে এবং সেই ঐক্যও যে জগতের আদি সত্তায় বর্তমান তার ভিত্তি সুদৃঢ় করেছে। আল্লাহ্র অস্তিত্বে বিশ্বাস বা কুরআন শরীফের বাণীতে আস্থা স্থাপন, জ্ঞান অন্বেষণের পথে তাই বিঘ্ন নয় বরং জ্ঞানের পথকে সুগম করে-তার ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে।
এ দুনিয়ার সমস্ত কিছুর জ্ঞান মানবের পক্ষে সম্ভবপর; জ্ঞানের পথে মানুষের কোন প্রতিবন্ধক নেই- জ্ঞানের চরম পরিণতিতে মানুষ আবিস্কার করবে নিয়ম-শৃঙ্খলা- এটাই ইসলামী জীবন-দর্শনের গোড়ার কথা।
বৈজ্ঞানিক গবেষণার আরোহ পদ্ধতিকে১৭৩ গ্রহণ তাই ইসলামের দৃষ্টিতে বর্জনীয় নয় বরং তার মূলকে দৃঢ় করার ভিত্তিস্বরূপ। আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তিরূপ যেমন একত্বের নীতি১৭৪ বা সমরূপতা নীতি১৭৫ অবশ্য গ্রহণীয়, তেমনি জ্ঞাতা১৭৬ এবং জ্ঞেয়ের১৭৭ সম্বন্ধ স্বীকারও অবশ্য প্রয়োজনীয়। পরবর্তী নীতি স্বীকার করে নিলে আমাদের অবশ্যই মেনে নিতে হয়, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে মৌলিক ঐক্য। সে মৌলিক ঐক্যের স্বীকৃতি ব্যতীত আমাদের পক্ষে এক পা অগ্রসর হওয়ার সাধ্য নেই। ইসলামী চিন্তাধারায় তাই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মৌলিক ঐক্যস্বরূপ আল্লাহ্র অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে।
বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার আলোচনায়ও আমরা দেখতে পাই মানব মন তার সকল চিন্তার পরিণতিতে এসে পৌঁছায় এক ঐক্যে। সে ঐক্য জড় বা চৈতন্যময়-দু’ই হতে পারে। তাকে জড়বস্তু বলে ধারণা করলে আমাদের মানসে দেখা দেয় নানাবিধ দ্বন্দ্ব- নৈতিক ও উচ্চতর মানগুলো তাতে কোন ভিত্তি খুঁজে পায় না। অপরদিকে কার্যকারণ পরস্পরা নীতির১৭৮ সুষ্ঠু ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। মানব-মনের বিভিন্ন চিন্তা নীতি ইত্যাদি বোধঃ শক্তিহীন জড়পদার্থ থেকে উৎপন্ন হলে আমাদের স্বীকার করতে হয়, আদিতে কারণে কোন গুণ না থাকলেও কার্যে যেসব গুণের উৎপত্তি হতে পারে। অথচ কার্যকারণের নীতিতে বলা হয় শূন্য থেকে শূন্যই আসে১৭৯ । সে নীতিকে কার্যকরী রাখতে হলেও আমাদের ধরে নিতে হয়, যদিও জড় বলে জগতের আদি সত্তা আমাদের ইন্দ্রিয়ের কাছে প্রতিভাত হয়, যদিও জড় হলে জগতের যাবতীয় সম্পদ তা সে মননধারারই হোক বা সামাজিকই হোক, উহ্য রয়েছে। সমাজ বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে তারা বাহ্য হয়ে পড়ে।
ইসলাম তাই কুরআনের ভাষায় মানুষের চোখে আঙ্গুল দিয়ে এ জগতের আদি কারণকে চৈতন্যময় সত্তারুপে নির্দেশ করেছে। ইসলামের নিকট তাই আল্লাহ্র অস্তিত্ব একাধারে স্বতঃসিদ্ধ১৮০ ও মানব চিন্তার চরম পরিণতি। আল্লাহ্র অস্তিত্বের স্বীকৃতি ব্যতীত জ্ঞানের পথে মানুষ এক তিল অগ্রসর হতে পারে না। অপরদিকে আল্লাহ্র অস্তিত্ব মানুষের জ্ঞানের চরম পরিণতি। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনায় মানুষ সর্বশেষে তাঁরই অস্তিত্বে আস্থা স্থাপন করে স্বস্তিলাভ করে।
বিজ্ঞানের প্রাথমিক ভিত্তির আলোচনায়ও আমারা দেখেছি একত্বের নীতি, সমরূপতার নীতি প্রভৃতি মৌলিক নীতিকে স্বীকার করে চিন্তার পরিণতিতে মানুষ আবার এ দুনিয়ার মধ্যে এক চরম ঐক্য আবিস্কার করে। ইসলামী চিন্তাধারার মূলসূত্র আল্লাহ্র অস্তিত্বের স্বীকৃতি তাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের পক্ষে প্রতিবন্ধক নয় বরং প্রেরণাদানকারী।
আল্লাহ্র অস্তিত্বের প্রশ্ন
‘আল্লাহ্ আছেন কি না’- প্রশ্নটি মানব জীবনে নতুন নয়। মানব মনের চিন্তার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে এ সম্বন্ধে মানুষ ভেবেছে, এখনও ভাবছে। এ প্রশ্নের উত্তর আল্লাহ্র সংজ্ঞার ওপরই নির্ভর করে। আল্লাহ্ বলতে যদি আমরা চতুর্দশ লুই বা হিটলারের মত এক প্রচণ্ড শক্তিশালী দণ্ডধর বা আসমানের অধীশ্বর বলে কল্পনা করি, তাহলে তাঁর অস্তিত্ব কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। আল্লাহ্ বলতে যদি মনে করা হয়-সদ্,চিদ্ ও আনন্দ স্বরূপ এক বিশ্ব-সত্তা, তাহলে জ্যামিতিক প্রমাণ না দেওয়া গেলেও একটা গ্রহণযোগ্য প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে।
সাধারণত আল্লাহ্ বলতে আমরা বুঝতে পারি এ বিশ্বের স্রষ্টা পরম মঙ্গলময়, পরম বুদ্ধিমান, সর্বগুণাধার, বিশ্বের সকল বস্তুর নিয়ামক এক শক্তি। আল্লাহ্র এবং বিধ ধারণার পোষকতায় দর্শনশাস্ত্রে তিনটে প্রমাণ পেশ করা হয়েছে।
আমাদের জাগতিক অভিজ্ঞতায় আমরা দেখতে পারি, জগতে যা কিছু ঘটে তার মূলে রয়েছে একটা কারণ। কারণ ব্যতীত কোন কার্যের উৎপত্তি হয় না। তাই আমরা ভাবতে বাধ্য হই, নিশ্চয়ই এ বিশ্ব-সৃষ্টির মূলে রয়েছে একটা বিরাট কারণ। কার্যকারণ-পরস্পরা-সূত্রের অমোঘতা স্বীকার করে নিলে তখন প্রশ্ন দাঁড়ায়, সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টির মূলে কার কার্যকারিতা বিদ্যমান? দর্শনশাস্ত্রে তাই এই স্রষ্টা তত্ত্ববিষয়ক প্রমাণের১৮১ উপর কোন বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়নি।
দ্বিতীয় প্রমাণস্বরূপ বলা যায়, দুনিয়ার সর্বত্র রয়েছে বুদ্ধি ও করুণার নিদর্শন, তাতে প্রমাণিত হয় দুনিয়ার সৃষ্টির মূলে রয়েছে এক পরম মঙ্গলময়ের হস্ত। মানব জীবনের নানা ঘটনা থেকেই বুঝতে পারা যায়, এতে রয়েছে এক মহান উদ্দেশ্য। সন্তানের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই মায়ের বুকে দুধ সঞ্চিত হয়। যদি তা না হত, তাহলে পৃথিবীর এতগুলো শিশু আহারের অভাবে অকালে মারা যেত। অবুঝ ইতর প্রাণীদের মধ্যে যদি অপত্য স্নেহ না থাকত তাহলে সদ্যোজাত বাচ্চাগুলো শত্রুর আক্রমণে জন্মের সঙ্গে-সঙ্গেই লয় পেত। এতে প্রমাণ পাওয়া যায়, জীবের বিকাশের জন্য উপায়স্বরূপ১৮২ জনক-জননীর বুকে এই স্নেহ কেউ গোড়াতেই ঢেলে দিয়েছেন। এই যুক্তিকে দার্শনিক পরিভাষায় বলা হয় ধর্মতত্ত্বমূলক যুক্তি১৮৩। তার বিরুদ্ধে বলা যায়-দুনিয়ার সর্বত্র লক্ষ্য ও উপায় সুসামঞ্জস্য নেই। অনেকগুলো জীব পিতামাতার যত্নের অভাবে অকালে মারা যায়। অনেকগুলো পরিবেশের সঙ্গে যুদ্ধে লোপ পায়। আবার অনেকগুলোর জন্য পর্যাপ্ত আহারের ব্যবস্থা নেই।
জীব-জগৎ ব্যতীত দুনিয়ায় অনেকগুলো জরা-ব্যাধি, প্রাকৃতিক উৎপাদন১৮৪ রয়েছে। তাদের অস্তিত্বের কোন প্রয়োজন আবিস্কার করা যায় না। সাহারা বা গোবি মরুভূমি দুনিয়ার কার কোন্ প্রয়োজনে সৃষ্টি হয়েছে? আগ্নেয়গিরির উৎপাত জগতের কোন্ কাজে লাগছে? যদি পৃথিবীর মঙ্গলময় দিকের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই তাকে এক আদর্শ কারিগরের সৃষ্টি বলে ধরে নেয়া হয়-তাহলে অপরদিকে অশুভ ও অকল্যাণকর দিকের বিচার করলে তাকে এক পিশাচের সৃষ্টিই বলতে হয়।
এ দুটো বৃত্তিই আল্লাহ্ সম্বন্ধে ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ্কে ধারণা করা হয়েছে সর্বত্রুটিহীন, সর্বগুণাধার, সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তারুপে। তাই তার প্রমাণস্বরূপ বিশ্ব সৃষ্টি থেকে বিশ্বের নানাবিধ কলাকৌশল১৮৫ থেকে নযীর তুলে বলা হয় আল্লাহ্ই এসব কার্যের১৮৬ মূলাধার।
তার তৃতীয় যুক্তিস্বরূপ বলা হয় আল্লাহ্র অস্তিত্ব নিশ্চয়ই রয়েছে। কারণ আল্লাহ্র ধারণা থেকেই তাঁর অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। যিনি সর্ব গুণাধার, তাঁর মাঝে অস্তিত্ব নামক গুণের অভাব হলে তাঁকে সর্বগুণাধার বলা পরস্পরবিরোধী উক্তি মাত্র। মধ্যযুগে সেন্ট এলসেম এ যুক্তির অবতারণা করে বেশ বাহবা পেয়েছিলেন।
এ যুক্তিও ত্রুটিহীন নয়। আল্লাহ্কে সর্বগুণাধার বলে আমরা মাত্র তাঁর অস্তিত্ব ঘোষণা করছি-তাঁর কোন প্রমাণ দিতে পারিনি। দার্শনিক শ্রেষ্ঠ ক্যান্ট একে উপহাস করে বলেছেন, ‘আমার পকেটে একশত ডলার রয়েছে বলে যদি আমার ধারণা থাকে, তাতে কি প্রমাণ হয় যে, বাস্তবিকই একশত ডলারের অস্তিত্ব রয়েছে’।
এসব যুক্তির দ্বারা আল্লাহ্র অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়নি। এ তিনটি প্রমাণের মধ্যে প্রণিধানযোগ্যে বিষয়টি এইঃ দুটোতে অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করতে তার অনুকূলে প্রমাণ দেয়া হয়েছে। অপরটিতে ধারণা থেকে অস্তিত্বের প্রমাণ নেয়া হয়েছে। তবে তিনটি যুক্তিতেই স্বীকার করে নেয়া হয়েছে ধারণার সত্যাসত্য বিষয়ের সঙ্গে যোগসূত্রই নির্ধারিত হবে। আল্লাহ্র অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের মনে যে ধারণা রয়েছে- যদি বাস্তব জগতে সেরূপ কোন সত্তা থেকে তাহলে এটি সত্য’। যদি না থেকে তাহলে মিথ্যা। কাজেই আল্লাহ্ সম্বন্ধে আমাদের ধারণাগুলো সত্য না মিথ্যা, এ প্রশ্নের মীমাংসা করতে হলে সত্য ও মিথ্যার সংজ্ঞা নির্দেশ করতে হয়।
সাধারণত সত্য বলতে বোঝা যায়-প্রতিষঙ্গ১৮৭ । আমাদের মনে রয়েছে অনেকগুলো ধারণা। বাইরের জগতে রয়েছে অসংখ্য বস্তু ও গুণাবলি। কোন ধারণা সত্য হলে তার সঙ্গে বাইরের বস্তু বা গুণাবলির যোগ থাকা চাই। যেমন ধরা যাক, কারো মনে জ্বিন কোন জাত আছে বলে যদি ধারণা থাকে, তাহলে তা সত্য কি মিথ্যা বিচার করতে হলে তলিয়ে দেখতে হবে জ্বিন বলে কোন জাত আছে কি না। যদি থাকে, তাহলে এ ধারণা সত্য। যদি না থাকে, তাহলে তা মিথ্যা। একে দর্শনের পরিভাষায় সত্যের প্রতিষঙ্গমূলক মতবাদ১৮৮ বলা হয়। এখানে প্রশ্ন দাঁড়ায় পাওয়া যায়, তাহলে সেও আমাদের মনেরই একটা ধারণা হবে। কাজেই কোন ধারণার সত্যাসত্যের বিচার অপর ধারণার দ্বারাই করতে হবে।
তার ওপর এতে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে বিষয়বস্তু বা গুণাবলি অপরিবর্তনীয়। তাদের সম্বন্ধে আমাদের ধারণা সব সময় একই থাকবে। আমাদের অভিজ্ঞতায় কিন্তু দেখতে পাই বস্তুজগতে চলছে এক দ্রুত পরিবর্তন। উদ্দীপক থেকে যে সংবেদন আমরা পাই, বিভিন্ন চিন্তার মাধ্যমে১৮৯ তাকে আমরা যেসব বস্তু সম্বন্ধে পূর্বে যেসব ধারণা করে নিয়েছি, তার সত্য বিচার করতে গিয়ে যদি পূর্বের ধারণাগুলোকে আবার বস্তুর সঙ্গে তুলনা করি, তাহলে স্পষ্টই দেখতে পাব- আমাদের ধারণার পরিবর্তন অত্যাবশ্যক। কারণ বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে বস্তু পরিবর্তিত হয়ে গেছে অথচ আমাদের ধারণার পরিবর্তন হয়নি অথবা বস্তু অপরিবর্তিত রয়েছে কিন্তু তার সম্বন্ধে আমাদের ধারণার হয়েছে পরিবর্তন।
তাছাড়া সত্যাসত্য বিচার কেবল বাইরের বস্তুর সঙ্গে আমাদের তুলনা করেই শেষ হয় না। মানব মনের আবিষ্কৃত অনেকগুলো তত্ত্বের সঙ্গে আমাদের পরবর্তী ধারণাগুলোর সত্যাসত্য নির্ণয় করা চলে। জ্যামিতি শাস্ত্রের একটা প্রতিপাদ্য১৯০ বা সম্পাদ্য১৯১ সত্য না মিথ্যা বিচার করতে হলে পূর্ববর্তী প্রতিপাদ্য, সম্পাদ্য বা স্বতঃসিদ্ধ থেকে তাকে যুক্তিসহকারে অবরোহন করা১৯২ যায় কি না, তাই বিচার করতে হয়। কাজেই সত্যের এ সংজ্ঞা নির্দেশ নিতান্তই একদেশদর্শী।
এ থিয়োরির সমালোচনাতেই সঙ্গতিবাদের১৯৩ উৎপত্তি। Coherence theory মতে আমাদের মনে যেসব ধারণা বর্তমান তাদের মধ্যে যদি সঙ্গতি থাকে তাহলে বুঝতে হবে তারা সত্য। যদি কোন ধারণার সঙ্গে অন্য সুপ্রতিষ্ঠিত ধারণার সংঘর্ষ বাধে, তবে সবগুলো ধারণার আলোকেই নতুন বেখাপ্পা ধারণার বিচার করতে হবে।
এ থিয়োরি মতে অনেক অসত্যকেও সত্য বলে চালিয়ে দেয়া যেতে পারে। সাধারণত সত্য বলতে ধারণার সঙ্গে বিষয়ের যোগ বোঝা যায়। যদি ধারণার সঙ্গতি-অসঙ্গতি সত্যাসত্য বিচারের মানদন্ড হয়, তাহলে বাস্তবে অস্তিত্ব নেই এমন অনেক বিষয়কে সত্য ব’লে চালিয়ে দেয়া যেতে পারে। ধরা যাক, একটি স্কুলের ছেলে এসে তার আম্মার নিকট অভিযোগ করল যে, তাকে হেডমাস্টার কান ম’লে দিয়েছেন। তার আম্মা অনুসন্ধান করে দেখল বাস্তবিকই ছেলেটির কান লাল। তার চোখের কোণেও রয়েছে পানির দাগ। আম্মার নিশ্চয় বিশ্বাস হবে,তার ছেলের অভিযোগ সত্য। বাস্তবিক পক্ষে হেডমাস্টার তাকে মারেননি। অন্য ছেলের সঙ্গে লড়াই করতে দেখে হেডমাস্টার তাকে ধমক দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে ছেলে তার আম্মার কাছে যে জবানবন্দি দিচ্ছে, তাতে কোন অসঙ্গতি নেই। মাস্টার ছাত্রের সম্পর্ক বা হেডমাষ্টারের কড়া মেজাজের সম্বন্ধে তার আম্মার ধারণাগুলোর সঙ্গে ছেলের বিবরণ হুবহু খাপ খাচ্ছে, কাজেই আম্মার তাকে ধরে নিচ্ছে সত্য বলে। আদতে কিন্তু বর্ণনাটি নিছক কাল্পনিক ও বিদ্বেষমূলক।
তার ওপর গোটা মনোজগতের সবগুলো ধারণার সঙ্গে নতুন ধারণার সঙ্গতি দ্বারা যদি তার সত্য বিচার করা যায়, তাহলে অন্যদিকে মস্ত অন্যায় করা হবে। কারণ আমাদের পূর্বতন ধারণাগুলোও সম্পূর্ণ অলীক হতে পারে। জগতে নানাবিধ আবিস্কারের সূচনাতে তাদের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন হয়েছে। কোপারনিকাসের১৯৪ সূর্যকেন্দ্রিক সিদ্ধান্ত১৯৫ বা ডারউনের বিবর্তনবাদের বিরুদ্ধে সমসাময়িক যুগে নানা কটূক্তি বর্ষিত হয়েছে। পরবর্তীকালে আবার সেই সব ধারণার আলোকেই জগতের মানব-কাঠামো পুনর্গঠিত হয়। সঙ্গতি কথার তাহলে অর্থ থাকে কি?
উইলিয়াম জেমস তাই সত্য সম্বন্ধে প্রয়োগবোধ১৯৬ নামক তাঁর নিজস্ব মতবাদ প্রচার করেন। তাঁর ধারণা ছিল বাস্তব জগতে স্থিতিশীল বলে কোন কিছু নেই, সব কিছুই পরিবর্তনশীল। তাই কোন ধারণার সত্যাসত্য তার কার্যকারিতার ওপর নির্ভর করে। তাঁর পূর্ববর্তী দার্শনিকদের ধারণা ছিল, যা সত্য তাই কার্যকরী। জেমস তার বিরুদ্ধে ঘোষনা করেন, যা কার্যকরী তাই সত্য। প্রকৃতপক্ষে আমাদের মনে নানা ধারণা, নানা ভাব, নানা থিয়োরি বর্তমান। তাদের প্রত্যেকটি সম্বন্ধে আমরা সত্যের দাবি করি। তাদের কার্যকারিতা দিয়েই সত্যের বিচার করে। যদি তাদের মধ্যে কোনোটা কার্যকরী হয়, তাহলে সেটি সত্য, যদি কার্যকরী না হয়, তাহলে মিথ্যা।
ধর্ম সম্বন্ধে সে মতবাদ অনুসারে বলা যায়, জীবনে ধর্মের কার্যকারিতা রয়েছে, কাজেই ধর্মের ধারণাগুলো সত্য। জেমস তাঁর বলিষ্ঠ ভাষায় প্রকাশ করেছেন, আমাদের প্রক্ষোভজাত প্রয়োজন দুনিয়াকে ধার্মিকের মনোবৃত্তি নিয়ে গ্রহণ করার মত দুঃসাহসিক কর্মের পোষকতা করে। ধর্ম সত্য হতে পারে, এই আশাকে পোষণ করা ধর্ম মিথ্যা, এই আশঙ্কার চেয়ে ভালো, কারণ এ দুটো বিশ্বাসের একটাকে আমাদের গ্রহণ করতেই হবে। কাজেই আল্লাহ্র অস্তিত্বের ধারণা আমাদের জীবনের অনেকগুলো কাজকর্মকে নিয়ন্ত্রিত করে, সেইজন্যই এটি আমাদের জীবনে সত্য।
এ মতবাদের জের টানলে এক বিরূপ সিদ্ধান্তে এসে উপস্থিত হতে হয়। correspondence Theory বা Coherence Theory দুটোই সত্যের কার্যকারিতা স্বীকার করে নেয়। যা সত্য তা জীবনে কার্যকরী হবেই। কিন্তু যা কার্যকরী তা সত্য কি করে হতে পারে? যেমন ধরা যাক, গভীর রাতে কোন ব্যক্তির যদি রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, তাহলে ভ্রমের বশবর্তী হয়ে সে ভয় পায় এবং সঙ্গে সঙ্গেই দৌড়ায়। কিন্তু তা বলেই কি বুঝতে হবে সেই রজ্জু বাস্তবিকই একটা সাপ? এ যুক্তির ধারামতে একটা ভুল হলেও সাময়িকভাবে সত্য। কারণ সেই ভ্রমাত্মক ধারণা সেই ব্যক্তির জীবনে কার্যকরী। কাজের মধ্যেই সত্যের সার্থকতা। যদি রজ্জুকে সাপ মনে করে পথিক ভুল করে ভয় পায়, তাহলে একটা জীবন্ত সাপ ঠিক তার মনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, এই রজ্জুও সেই প্রতিক্রিয়ারই সৃষ্টি করে এবং এই জন্যই তা’ সত্য।
এভাবে বিচার করলে অবশ্য জেমসের মতবাদের যৌক্তিকতা আমাদের কাছে অত্যন্ত দুর্বল মনে হয়। তাহলে সত্যাসত্যের বিচার নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। যা একজনের কাছে এক বিশেষ সময়ে সত্য, তা অপরের নিকট সত্য নাও হতে পারে। দুনিয়া তখন হয়ে পড়ে ছন্নছাড়া খেয়ালী রাজ্য। সত্য সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলাই হয়ে পড়ে অসঙ্গত।
জেমস নিশ্চয়ই এই অর্থে সত্য শব্দের প্রয়োগ করেন নি। ব্যষ্টির ব্যক্তিগত জীবন ব্যতীত সমষ্টি জীবনে এমন কতকগুলো ধারণা কার্যকরী, যেগুলোর সপক্ষে ন্যায়শাস্ত্র অনুমোদিত কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, অথচ মানবচিন্তার সূচনা থেকে সেগুলোর ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। স্থান ও কাল আমাদের সকল চিন্তার মূলেই রয়েছে। এ দুটো ধারণাকে প্রমাণ করা সহজ নয়। অথচ কোন বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা করতে হলে স্থান-কালের মাধ্যমেই চিন্তা করতে হয়। দার্শনিক ক্যান্ট তাদের বলেছেন, Forms of Institutions.
কার্যকারণ পরস্পরাসূত্র১৯৭ এবং বস্তু১৯৮, এগুলোও প্রামাণ্য ধারণা নয়। এগুলো ব্যতিরেকে মানবজীবনের অভিজ্ঞতা বা বিজ্ঞান এক পা-ও অগ্রসর হতে পারে না। কাজেই তাদের সত্যতা স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। আল্লাহ্র অস্তিত্ব যদি এমন কোন ধারণা হয় যা স্বীকৃতি ব্যতীত আমরা জাগতিক অভিজ্ঞতার কোন সুষ্ঠু ব্যাখ্যা করতে পারি না, তাহলে তাকে স্বীকার করতে আমরা বাধ্য। সম্ভবত এই অর্থেই জেমস বলেছিলেন, যা জীবন কার্যকরী, তা-ই সত্য।
এখানে প্রশ্ন দাঁড়ায়, আল্লাহ্র অস্তিত্ব বাস্তবিকই সেরূপ কোন ধারণা কিনা। আমাদের অভিজ্ঞতাকে যদি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের জগতে সীমাবদ্ধ করা যায় তা’হলে অবিচার করা হবে। বিজ্ঞানের জগতে আমরা পরিচালিত হই বুদ্ধিবৃত্তি১৯৯ দ্বারা। সেখানে বোধির কোন স্থান নেই। পরিদৃশ্যমান জগতের বিভিন্ন উদ্দীপক থেকে যে সংবেদন আমরা পাই, বিভিন্ন চিন্তার মাধ্যমে তাকে আমরা সুসংবদ্ধ করে সার্বিক সিদ্ধান্তে২০০ এসে পৌঁছি। সেই সিদ্ধান্তগুলোকে ব্যবহারিক জীবনে কার্যকরী করে তোলা ফলিত বিজ্ঞানের কাজ। বৈজ্ঞানিক জগৎ ব্যতীত নৈতিক বা ধর্মীয়জীবনে নানা অভিজ্ঞতা আমাদের হয়। সেগুলোর ভিত্তিতেও নীতিবিজ্ঞান বা ধর্মীয় বিজ্ঞান গড়ে তোলা সম্ভবপর। তবে বাস্তবজীবনে তাদের প্রয়োগ ঠিক প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মত ফলপ্রসূ নয়। তাদের দ্বারা মানুষের জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান ঠিক প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পর্যায়ের নয়। মানবমনের বিকাশসাধন করে তারা সমাজজীবনে নানাভাবে উন্নত করে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ফলিত রূপের নানা দওলতে আপাতত মুগ্ধ হয়ে আমরা আমাদের অভিজ্ঞতাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতা বলে ভুল করে থাকি। এজন্যই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের সঙ্গে নৈতিক জীবনের বা ধর্মীয়জীবনের নানাবিধ দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। বুদ্ধি ও বোধির এ দ্বন্দ্ব বাস্তবিকই মারাত্মক।
মানবজীবনের সবগুলো অভিজ্ঞতা ও তার জ্ঞানের সবগুলো পদ্ধতিকে স্বীকার করে নিলে, তবে এই দ্বন্দ্বের নিরসন হতে পারে।
আল্লাহ্র অস্তিত্বের যেসব প্রমাণ পাওয়া যায়, তাতে মাত্র এক সুরই প্রমাণিত হয়। ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ শক্তিতে মানবমন তার প্রকৃত সত্তা খুঁজে পায় না বলে আজীবন অসীম সত্তার আশ্রয়ে সে স্বস্তিলাভ করতে চায়। এখানেই রয়েছে ধর্মের অপরিহার্যতা, যাকে ইংরেজ দার্শনিক জন কেয়ার্ড বলেছেন, Necessity of Religion.
মানবজীবনের নানাবিধ অভিজ্ঞতায় আল্লাহ্র অস্তিত্বের স্বীকৃতি অনিবার্যরুপে দেখা দেয়। তাকে বুদ্ধির আলোকে প্রমাণ করতে চাইলে তাতে ত্রুটি দেখা দেয়া সত্য। কিন্তু যা কবির চোখে, ধ্যানীর মর্মে একান্ত বাস্তব, যা ব্যক্তি-জীবনের নানাবিধ অভিজ্ঞতার সুসামঞ্জস্য বিধানে কার্যকরী, রাষ্ট্রীয় জীবনে যে ধারণার কল্যাণে হয় ব্যষ্টি ও সমষ্টির অধিকারের সমন্বয়, তাকে অবাস্তব বলার অর্থ সত্যকে অস্বীকার করা।
পরলোকগত ইংরেজ কবি ওয়ার্ডস ওয়ার্থ আল্লাহ্র অস্তিত্বের কোন প্রমাণ চাননি। তাঁর কাছে তাঁর নিজের অস্তিত্বের মতই তা’ই ছিল জীবন্ত সত্য। অনবদ্য ভাষায় তিনি বলেছেনঃ
‘ যে প্রকাশ আমায় সমুন্নত চিন্তার দ্বারা বিচলিত করে, যার মহান অনুভূতি অত্যন্ত গভীরভাবে (আমার সত্তায়) অনুপ্রবেশ করে, যার আবাস অস্তগামী সূর্যের রশ্মিতে, সমুদ্রের দিকবলয়ে, মুক্ত জীবন্ত বাতাসে, ঘন-নীল আকাশে এবং মানব মনে (রয়েছে বিরাজমান) যে গতি ও আত্মা সকল চিন্তাশীল জীবকে ও চিন্তার বিষয়বস্তুকে দোলা দেয় এবং সকল বস্তুতে প্রবাহিত তা আমার কাছে জীবন্ত সত্য।২০১
উইলিয়াম জেমসও ঠিক ওয়ার্ডস ওয়ার্থের মত আল্লাহ্র অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁর ধারণা প্রকাশ করেছেনঃ
“ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান যেভাবে বিশ্বসংস্থাকে জানবার চেষ্টা করে তাতে তার মাঝে সুসংবদ্ধ পারমার্থিক অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। ( এভাবে দেখলে) তাকে চন্সি রাঈটের ভাষায় আবহ বলতে হয়- উদ্দেশ্যবিহীন ভাঙ্গা গড়াই তার খেলা।
আর কিছু হোক না কেন- এটি নিশ্চিত যে, বর্তমান কালের প্রাকৃতিক বিজ্ঞানজাত জ্ঞানের দ্বারা আমরা পৃথিবীর যে সন্ধান পাই, সে পৃথিবী অন্য এক বৃহত্তর পৃথিবী দ্বারা পরিবেষ্টিত। তার সেই অবশিষ্ট গুণাবলী সম্বন্ধে বর্তমানে আমরা কোন সার্থক ধারণা করতে পারি না।*২০২
কেন পারি না তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি আবার বলেছেনঃ
‘যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা জাতিকে এবং সার্বিক (সত্য) নিয়ে আলোচনা করি ততক্ষণ আমরা সত্যের সংকেত নিয়েই আলোচনা করি। যেই ব্যক্তিগত ও ব্যক্তিত্বগত বিষয় নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হই তখনই মাত্র সত্যের সর্বাঙ্গীণ রূপের আলোচনা আমাদের দ্বারা হয়।২০৩
আমাদের জীবনে অনেকগুলো আদর্শ বর্তমান, সত্য শিব ও সুন্দর সব সময়েই জ্ঞানের রাজ্যে, কর্মের ক্ষেত্রে ও সৌন্দর্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে আমাদের প্রেরণা যোগায়। এগুলোর মূল্য কি? বাস্তব জগতে পরম সত্য ও পরম শুভ বা পরম সুন্দর বলে কিছু আছে কিনা এ প্রশ্ন আমাদের মনে ওঠে। এগুলো সম্বন্ধেও ন্যায়শাস্ত্রসম্মত কোন প্রমাণ দেওয়া যায় না। তবু এগুলো জীবনে কার্যকরী। কেবল ব্যক্তিজীবনে এগুলো কার্যকরী নয়, সমষ্টি জীবনেও কার্যকরী, কাজেই এগুলোর স্থিতি সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত, তাই আমরা ভাবতে বাধ্য হই-বিশ্বসত্তায় সেগুলো বর্তমান। ব্যবহারিক জীবনে আল্লাহ্র অস্তিত্বে আস্থা স্থাপন অনেক ক্ষেত্রেই হয়ে পড়ে অপরিহার্য। জীবনের নানবিধ সংকট-সঙ্কুল অবস্থায়, নানা বিপর্যয় ও সংঘর্ষের মধ্যে কেবল আল্লাহ্র অস্তিত্বের ওপর প্রচণ্ড বিশ্বাসের ফলে মানুষ বেঁচে থাকতে পারে। আদর্শের অনুসরণ ও রুপায়ণে আল্লাহ্র অস্তিত্বে আস্থা স্থাপন হয়ে পড়ে অনিবার্য। আল্লাহ্র অস্তিত্বে বিশ্বাস নৈতিক জীবন যাপন করার পক্ষে অত্যাবশ্যক। ‘আল্লাহ্ আছেন’ বলার সোজা অর্থ দাঁড়ায় দুনিয়া এমনভাবেই তৈরি যাতে পাপের ক্ষয় ও পুণ্যের জয় হয়। অর্থাৎ এ দুনিয়ায় রয়েছে এক নৈতিক শাসন ব্যবস্থা। সকল আইন-কানুনকে ফাঁকি দেওয়া চলে কিন্তু একে ফাঁকি দেওয়া চলে না। এই যে নৈতিক শাসনব্যবস্থা২০৪ যার ওপর বিশ্বাস স্থাপনের ফলে মুজাহিদ জ্বলন্ত অনলের লেলিহান শিখা তুচ্ছ করে তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে, এ বিশ্বাসের ফলেই সত্য-অনুসন্ধানী নানা উত্থান ও পতনের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও অকুতোভয়ে আদর্শের অনুসরণ করে।
রাজনৈতিক জীবনেও সত্য, শিব ও সুন্দরের আদর্শ গ্রহণ আরও প্রয়োজনীয়। জগতের সত্তা যদি অণু-পরমাণুর লীলাক্ষেত্রই হয়, জীব-জগৎ যদি ডারউইনের বিবর্তনবাদের সূত্র অবলম্বন করেই চলে, তা’হলে কেবল উপযুক্ততমের উদ্বর্তনের নীতিই গ্রহণ করতে হয়। যারা এ জীবন-যুদ্ধে উপযুক্ততম কেবল তারাই বেঁচে থাকবে-যারা দুর্বল, যারা পঙ্গু তাদের মরতে হবে। এবং বিধ মতবাদে বিশ্বাসী লোকদের পক্ষে রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব নয়। কারণ রাষ্ট্র হবে সকল লোকেরই রক্ষাকর্তা। তার মাঝে সবলের সঙ্গে দুর্বলও আশ্রয় পাবে। রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য সবলের অত্যাচার থেকে দুর্বলকে রক্ষা করা। তা’ রাষ্ট্র কেন করবে? এ জগতের মূলে নৈতিক শাসন আছে বলেই রাষ্ট্র তা’করতে বাধ্য, যদি কোন নৈতিক শাসন না থাকে তাহলে দুর্বলকে রক্ষার কোন প্রশ্নই ওঠে না।
তাই সকল রাষ্ট্র বা সরকার গঠন করার মূলে একটা অদৃশ্য নৈতিক শাসন স্বীকার করে নেয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। দুনিয়ার সম্পদের অধিকার নিয়েও ব্যষ্টি ও সমষ্টির মধ্যে দ্বন্দ্বের অন্ত নেই। ব্যষ্টির হাতে সম্পদের অধিকার ছেড়ে দিলে দু’দিনেই এক শ্রেণী চল্লিশ তলার উপর দাঁড়ায়, আর অন্য এক শ্রেণী বেওয়ারিশ কুকুরের মত পথে-ঘাটে ধুঁকে মরে। সমষ্টির হাতে সমস্ত অধিকার ছেড়ে দিলে ব্যষ্টি তার স্বাধীনতা হারায় আর সমস্ত অধিকার আল্লাহ্র হাতে ছেড়ে দিলে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রেখেও মানুষ পৃথিবীর সম্পদ ভোগ করতে পারে। অপরদিকে রাষ্ট্র জনমতের দ্বারা গঠিত হলেও জন্মের পরে জনসমষ্টি থেকে তার সত্তা পৃথক হয়ে পড়ে। পুঁজিবাদ বা সমাজতান্ত্রিক মতবাদ দ্বারা গঠিত রাষ্ট্রে সর্বসাধারণের কর্তৃত্ব থাকে না। তার নিয়ামকরূপে রাষ্ট্র পরিচালনা করে মুষ্টিমেয় লোক। তাদের ব্যক্তিগত জীবনের ছায়া সর্বাবস্থায়ই রাষ্ট্রের ওপর পড়া অপরিহার্য। কাজেই এদের মনে যদি কোন বৃহত্তর আদর্শের চেতনা কার্যকরী না থাকে তাহলে তাতে জনগণের নানা অমঙ্গল ঘটাবার সম্ভাবনা।
সর্বাবস্থায়ই আদর্শকেন্দ্রিক রাষ্ট্র সর্বশ্রেষ্ঠ। সেই আদর্শ যদি মানবজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ গুণগুলো- যেমন ব্যক্তিত্ব, শক্তি,ন্যায়-বিচার প্রভৃতির আলোকে গ্রহণ করা যায়, তাহলেই রাষ্ট্র পরিচালনায় পারদর্শিতা দেখা দিতে পারে।
এখন উপসংহারে আমরা এ সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছতে পারি। আল্লাহ্র অস্তিত্বের প্রমাণের মূলে রয়েছে মানব-মনের এক চিরন্তন নির্ভরশীলতা।
মানুষ আপনাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে না বলে স্বয়ংসম্পূর্ণ কোন সত্তাকে আশ্রয়রূপে গ্রহণ করতে চায়। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানই জ্ঞানের একমাত্র পথ নয়। বিচার-বুদ্ধির বাইরে, বোধির মাধ্যমে জ্ঞানলাভ সম্ভবপর। সে জ্ঞানের আলোকে দেখলে আল্লাহ্র অস্তিত্বের জন্য কোন প্রমাণের প্রয়োজন নেই, কারণ সেটি বোধিলব্ধ জ্ঞানের ব্যাপার এবং তা সরাসরি অভিজ্ঞতার২০৫ উপর নির্ভরশীল।
নানাবিধ বৈজ্ঞানিক প্রত্যয়ের মত আল্লাহ্র অস্তিত্বের ধারণা আমাদের ভূয়োদর্শনকে সুসংবদ্ধ করার জন্য প্রয়োজন। সমাজজীবনে ও রাজনৈতিক জীবনে এ প্রত্যয়ের মূল্য সর্বাপেক্ষা অধিক। সুতরাং তথাকথিত বিজ্ঞানের দ্বারা সে প্রত্যয়ের অনুকূলে কোন সত্তার অস্তিত্ব না পাওয়া গেলেও আল্লাহ্র অস্তিত্ব আমাদের জীবনে কেবল সত্যি নয় জলজ্যান্ত সত্যি। এজন্যই ইসলাম গোড়াতেই আল্লাহ্র অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েছে।
আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের মানুষের অধিকারের সমন্বয়
আল্লাহ্র অস্তিত্বের স্বীকৃতি ব্যতীত অনেকগুলো অভিজ্ঞতার কোন সুষ্ঠু ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না বলে এবং সমাজজীবন বা রাষ্ট্রজীবনে চরম নৈরাজ্য দেখা দেয় বলে ইসলাম গোড়াতেই এ দুনিয়ার সকল অধিকার, সকল সম্পদ আল্লাহ্র হাতে তুলে দিয়েছে। পবিত্র কুরআন শরীফে ঘোষণা করা হয়েছে- ‘আসমান যমীনে যা কিছু রয়েছে তার মালিক আল্লাহ্’ (নিসা ৪:১৯:১৩১)। তাহলে স্বীকার করে নিতে হবে, এ দুনিয়ার একমাত্র সার্বভৌম অধিকার আল্লাহরই। অথচ এই কুরআন শরীফের অন্যত্র বলা হয়েছেঃ
‘হু আল্লাযি খালাকালাকুম মা’ফিল আরদে জামিয়া’- আল্লাহ্ দুনিয়ার সবই মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন।
তা’হলে আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের মধ্যেও মানুষের ভোগের অধিকার রয়েছে। এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ আলিম মাওলানা মাহমুদুল হাসান বলেনঃ
‘সব জিনিসই মানুষের সম্পত্তিবিশেষ অর্থাৎ আল্লাহ্ সকল জিনিসই মানুষের প্রয়োজন মিটাবার জন্য সৃষ্টি করেছেন। কোন জিনিসই সৃষ্টির দিক থেকে ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি নয়, পক্ষান্তরে সকলেরই সম্পত্তি। সব জিনিসই মানুষের মঙ্গলের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে- তাই সকল জিনিসেই মানুষের দখল-ভোগের অধিকার আছে। যখন কোন জিনিস কারো ভোগ-দখলে থাকবে তখন তাকেই কেবল সে জিনিসের একমাত্র মালিক বলে গণ্য করা হবে। অন্য কেউ তার ওপর আধিপত্য স্থাপন করতে পারবে না। হাঁ! কোন জিনিসের দখলকারীর জেনে রাখা উচিত, সে নিজের প্রয়োজনে অতিরিক্ত বস্তু অনর্থক নিজ কবলে না রেখে অন্যকে অবাধে ভোগ-দখল করতে দেবে। কেননা, মানুষ হিসেবে সৃষ্টির ভোগ প্রত্যেক মানুষেরই প্রাপ্য’।
এ কারণেই রীতিমত যাকাত আদায় করা সত্ত্বেও প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাল সঞ্চয় করা সঙ্গত নয়। নবীগণ ও ধর্মভীরু লোকগণ এ কারণেই ধন সঞ্চয়ে বিরত রয়েছেন। এমনকি হাদীস দ্বারা পরিস্কার বোঝা যায়, সাহাবা ও তাবেয়ীগণ প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তু রাখা বা ব্যবহার করাকে হারাম বলেছেন।
প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তু সঞ্চয় বা ব্যবহার অনুচিত বা অসঙ্গত তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। কারণ প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তুতে তার কোন আবশ্যকতা নেই। ‘সব সৃষ্টিই মানুষের জন্য’ নীতিতে (সব কিছুতেই) সকলের দাবি রয়েছে, বরং প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তু ভোগ দখলকারী (তার নিজের প্রয়োজনের অংশের অতিরিক্ত ভোগ করার দরুন) অন্যায় দখলকারীরূপে মালিক বটে।* ( ইজাহুল আদিল্লাঃ পৃ,২৬৮। ইসলাম কা ইকতেসাধি নিজাম পৃ,৪২।)
ব্যষ্টিকে তাই দুনিয়ার সম্পদ যথেচ্ছ ভোগ করার অধিকার ইসলাম দেয়নি। যে দুনিয়ার সমস্ত মালিকানা আল্লাহ্র, যে রাজ্যে মানুষ তার প্রতিনিধি,হিসাব রক্ষক, সেখানে আল্লাহ্র খলীফা হিসেবে সে তার প্রয়োজনমত ভোগ করবে---
প্রয়োজনের অতিরিক্ত একতিলও সে অপব্যয় করবে না।
স্পষ্ট বোঝা যায়-আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের সঙ্গে ব্যক্তি-স্বাধীনতার নীতি স্বীকার করা হয়েছে। তবে যাতে এ স্বাধীনতা আধুনিক কালের বীজমন্ত্র Laissez Faire- এ পরিণত না হয়, তার জন্য কুরআন শরীফে নানাবিধ নৈতিক কানুনের প্রবর্তন করা হয়েছে।
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
ইসলামী নীতির রূপায়ণ-ব্যক্তিগত জীবনে সমাজে ও রাষ্ট্রে
ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র
ইসলামের ব্যক্তি-জীবন ও সমাজ-জীবনের জন্য কোন পৃথক আইন নেই। আদেশ রয়েছে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই আল্লাহ্র আদর্শে জীবন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। জনাব রাসূলে আকরাম (সঃ) বলেছেন- ‘তাখাল্লাকু বি আখলাকিল্লাহ’। আল্লাহ্র গুনে গুণান্বিত হও। সে আদেশ ব্যক্তি-জীবনের পক্ষে যেমন প্রযোজ্য, সমাজ-জীবনে ও রাষ্ট্র-জীবনের পক্ষেও তেমনই সমানভাবে প্রযোজ্য। সোজা কথায় ব্যক্তি যেমন আল্লাহ্র আদর্শে জীবন গঠন করবে, তেমনি সমাজ ও রাষ্ট্র ও গঠিত হবে আল্লাহ্র আদর্শেই। ইসলামের নানাবিধ প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য ব্যক্তিকে তার ব্যক্তিগত জীবনে, সমাজে ও রাষ্ট্রে আদর্শরুপে গড়ে তোলা। সমাজকে রাষ্ট্রের মধ্যে বিলীন করে দেওয়ার জন্য ইসলামের কোন আদর্শ না থাকলেও ইসলামের শাসন-অনুশাসন যাতে সর্বদা সহজভাবে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়জীবনে চালু হতে পারে, তার জন্য রয়েছে পরিস্কার নির্দেশ। সালাত, সিয়াম, হজ্জ, যাকাত প্রভৃতির প্রাথমিক উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত জীবনের বিশুদ্ধি, দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ব্যক্তি-জীবনকে সংঘ-জীবনের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী করে তোলা।
ইসলামী নীতির প্রয়োগ-ব্যক্তিগত জীবনেঃ সালাত
আমাদের দুর্ভাগ্যই বলতে হবে- আমারা আমাদের বাংলা ভাষায় ‘সালাত’ শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে ‘নামায’ শব্দ ব্যবহার করি। কুরআন-উল-করীমে যে ‘সালাত’ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তার প্রতিশব্দ হিসেবে ফারসি ‘নামায’ শব্দ ব্যবহৃত হতে পারে না। ‘নামায’ শব্দের উৎপত্তিগত অর্থ উপাসনা। এ উপাসনা অগ্নিউপাসক পার্সিদের মধ্যে ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেও প্রচলিত ছিল। সে উপাসনার বিষয়বস্তু ছিল অগ্নি। কুরআন-উল-করীমে ব্যবহৃত ‘সালাত’ শব্দের অর্থ শুধু উপাসনা নয়। তার অর্থ হচ্ছে যে সর্বশক্তিমান ও সার্বভৌম সৃষ্টিকর্তার আদেশ-নির্দেশের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করে তার কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ।
সালাতের মূল লক্ষ্য হচ্ছে একদিকে জীবনকে নানান রিপু এবং অসৎ প্রবৃত্তির প্ররোচনা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে সেই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র ওপর নির্ভরশীল হওয়ার জন্য প্রস্তুতি এবং সঙ্গে সঙ্গে তার গুণাবলী এ জগতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া।
এ সালাতের মধ্যে ইসলামের অপরাপর কর্তব্যের মত দুটো দিক রয়েছে। একটিকে বলা যায় তার পারমার্থিক দিক, অপরটিকে বলা যায় তার সামাজিক দিক। সামাজিক দিকের আলোচনা করলে দেখা যায় এতে দিনে পাঁচবার সকল মুমিন-মুসলিমকে একত্রিত হওয়ার জন্য তাগিদ রয়েছে। আল্লাহ্র রসূল (সঃ) নির্দেশ নিয়েছিলেন, ‘যদি কেউ মসজিদে সালাত আদায় না করে বাড়িতে আদায় করে তা হলে তার ঘর পুড়িয়ে দাও’। এতে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে সালাতের উদ্দেশ্যে মুমিন মুসলিমদের একত্রিত হওয়াও তার একটা লক্ষ্য ছিল। মুসলিমদের জীবনে ঐক্য,প্রেম,মৈত্রী,সৌহার্দ্য প্রভৃতি সৃষ্টির জন্য তাদের প্রত্যেক দিবারাত্রিতে অন্ততপক্ষে পাচঁবার একত্রিত হওয়ার সুযোগ দান করে বলে সালাতের রয়েছে এক সামাজিক গুরুত্ব। প্রকৃতপক্ষে হযরত রসূল-ই-আকরাম (সঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে মসজিদ ছিল একাধারে মুসলিমদের পার্লিয়ামেন্ট, সুপ্রীম কোর্ট, গবেষণাগার ও বিশ্ববিদ্যালয়। মসজিদকে কেন্দ্র করেই জীবনবিকাশের ধারাগুলো চালু ছিল। এজন্য আল্লাহ্র আদেশ পালন করার জন্যতো বটেই, পরোক্ষে মুসলিম জীবনের নানাবিধ আইন-কানুন প্রণয়ন করার জন্য বা বিচার লাভের জন্য মসজিদে জমায়েত হওয়া ছিল অবশ্য প্রয়োজনীয়। এ মসজিদে অবস্থান করেই মুসলিমরা এ সৃষ্টিতত্ত্ব বা এ দুনিয়ার বিকাশের আদি কারণ সম্বন্ধে গবেষণা করতেন। এ মসজিদে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে শিক্ষালাভ করতেন। কাজেই এ দুনিয়ার নানা বিষয়ে খাঁটি জ্ঞান লাভের জন্য সালাত সম্পাদন উপলক্ষে মসজিদে সমবেত হওয়া মুসলিমদের জীবনে অবশ্য কর্তব্য ছিল।
অপরদিকে সালাতের মধ্যে মানব-জীবনের যে পূর্ণ আত্মসমর্পণের ভার রয়েছে সে সূত্রে মানুষের পক্ষে আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভেরও সম্ভাবনা রয়েছে। আল্লাহ্র কাছে আত্মসমর্পণের মাধ্যমেই আল্লাহ্র প্রকৃতরূপের পরিচয় পাওয়া যায় বলে মানব-জীবনে রয়েছে দৃঢ় প্রত্যয়। ইসলামের অপর দিক হচ্ছে মারিফত। তাতে বলা হয় সালাতের মাধ্যমে সালাত আদায়কারীর দিলের মধ্যে রোশনী বা জ্যোতির আবির্ভাব হয় এবং সে জ্যোতির আলোকে আল্লাহ্র স্বরূপ সম্বন্ধে মানুষের পক্ষে উপলব্ধি করার সুযোগ দেখা দেয়।
যেহেতু ইসলামের মধ্যে ইহলৌকিক অথবা পারলৌকিক বলে এমন কোন স্পষ্ট ভেদরেখা নেই, এজন্য সালাতের মধ্যে যদিও এরূপ কোন ভাগ করা হয়নি তবুও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সালাতের মধ্যে আধ্যাত্মিক জীবন বিকাশেও পদ্ধতি রয়েছে।
সিয়াম ও রমযানের তাৎপর্য
আমরা সওমের পরিবর্তে ‘রোযা’ শব্দ ব্যবহার করি। ‘রোযা’ ফারসি ভাষার একটি শব্দ। তার সোজা অর্থ উপবাস বা যাকে ইংরেজিতে বলে fasting। কুরআনুল কারীমের ভাষায় যাকে মুসলিমদের জীবনে আমল করার জন্য তাগিদ দেয়া হয়েছে তা কেবল উপবাস নয়, তার নাম সওম। তার অভিধানগত অর্থ নিবৃত্তি। কিসের নিবৃত্তি? এ সম্বন্ধে শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহলভী বলেছেন, ‘যেহেতু পাশবিক কামনার প্রাবল্য ফেরেশতাসুলভ চরিত্র অর্জনের পক্ষে অন্তরায়, সুতরাং উহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা পরিহার্য। যেহেতু পাশবিক শক্তির প্রাবল্য উহার উত্তেজনা ও উহার প্রতিরোধ কঠিন হওয়ার কারণ অথবা পানাহার এবং জৈবিক আসক্তি পূত চরিত্র অর্জনের পক্ষে একটি পর্দা বা অন্তরায় যে, শুধু পানাহারে স্বাধীনতা এতবড় অন্তরায় নয়। সুতরাং এই সকল উপকরণকে পরাভূত করে পাশবিক শক্তিকে আওয়ত্তাধীন করা হইতেছে সওমের সূক্ষতম তাৎপর্য। এতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় সওমের প্রকৃত লক্ষ্য হচ্ছে পাশবিক প্রবৃত্তির দমন ও উন্নততর প্রকৃতির বিকাশ।
এজন্য দেখা যায়, এ দুনিয়ার যারা সত্যিকার মনুষ্যত্ব লাভ করেছেন অর্থাৎ নবী-মুরসালগণ তাঁর আল্লাহ্র প্রত্যাদেশ পাওয়ার পূর্বে দীর্ঘকাল সওমের সাধনা করেছেন। মরহুম মাওলানা সুলেমান নদভীর বর্ণনা থেকে পাওয়া যায় হযরত মূসা আলায়হি ওয়া সাল্লাম তুর পাহাড়ে আল্লাহ্র প্রত্যাদেশ হিসেবে তওরাত গ্রহণ করার সময় দীর্ঘ চল্লিশ দিন পর্যন্ত আহার পানীয় ত্যাগ করে মানবিক জীবনের বহু উর্ধ্বে আরোহণ করেছিলেন। হযরত ঈসা আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইনজীল প্রাপ্ত হওয়ার লগ্নে দীর্ঘ চল্লিশ দিন অনুরূপ সাধনায় জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। কুরআনুল করীম নাযিল হওয়ার পূর্বে হযরত রাসূলে আকরম (সঃ)- ও দীর্ঘ একমাস কাল হেরার গুহার সাধনায় জীবন যাপন করেছেন। এ পুণ্য সময়েই লায়লাতুল কদরের মহীয়ান রাত্রে তাঁর প্রতি কুরআন নাযিল হয়েছিল। এতে সিয়ামের গুরুত্ব সম্বন্ধে এ প্রমাণ পাওয়া যায়ঃ আল্লাহ্র তরফ থেকে তার বাণী বা নির্দেশপ্রাপ্তির পূর্বে নবী ও মুরসালদের পক্ষে চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা ছিল। প্রশ্ন হচ্ছে, কিভাবে চিত্তশুদ্ধি হয় এবং সে চিত্তশুদ্ধির মূল অর্থ কি? তার উত্তরে সৈয়দ সুলেমান নদভী বলেছেন- ‘এতে সর্বপ্রথম শিক্ষা হচ্ছেঃ মানবজীবন ভোগের জন্য নয়—মানবজীবন ত্যাগের জন্য। ত্যাগের ফলে মানবজীবনে যে তৃপ্তি দেখা দেয়- ভোগের ফলে সে তৃপ্তি দেখা দেয় না’।
সে সওমের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আল্লামা ইকবাল বড় চমৎকার ভাষায় বলেছেন, ‘সওমকে ব্যক্তিগতজীবনে পালন করাও সম্ভব। অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধির জন্য এক ব্যক্তি হয়ত বৈশাখ মাসে অথবা মহররম মাসে সওমের নীতি পালন করবেন। অপর ব্যক্তি জ্যৈষ্ঠ মাসে বা সফর মাসে সে নীতি পালন করবেন, তাতে আপত্তি হওয়ার কারণ কি? তার উত্তরে বলা যায়-এক্ষেত্রে আল্লাহ্ সুবহানা তা’আলার উদ্দেশ্য- কেবল ব্যষ্টি জীবনের সংশোধন নয়। এক্ষেত্রে আল্লাহ্র উদ্দেশ্য গোটা মানবজাতির আত্মার শুদ্ধি। এজন্য একটা নির্দিষ্ট চান্দ্রমাসে আল্লাহ্র কালামে প্রত্যয়শীল সকল মানুষের জন্যই ‘সওম’কে অবশ্যপালনীয় কর্তব্য হিসেবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এতে বিশুদ্ধ মানবজীবন তথা মুসলিম জীবনে সাম্য-ঐক্যের নীতি প্রতিষ্ঠার প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে। সকল মানুষ যাতে একই আদর্শে উদ্ধুদ্ধ হয়ে তাদের পাশবিক প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণ দমন করে, প্রকৃত মানবিক চরিত্রের বিকাশের জন্য একসঙ্গে সাধনায় লিপ্ত হয়, তার জন্য একটা বিশেষ মাসে সকলকেই তার অনুশীলনে তাগিদ দেয়া হয়েছে।
প্রকৃতপক্ষে সালাত(নামায) বা সিয়াম ইসলামী জীবনধারার কোন খাপছাড়া অনুশীলন নয়। ইসলামের মূল ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহ্র রব নামক গুণ ও সার্বভৌমত্বের ওপর প্রত্যয়। আল্লাহ্কে এক, অদ্বিতীয় স্রষ্টা, প্রতিপালক ও বিবর্তনকারী হিসেবে গ্রহণ করলে এবং তাকেই এ বিশ্বজগতের একমাত্র মালিক বলে স্বীকার করলে সওম বা সালাত অপরিহার্য রূপে দেখা দেয়। আল্লাহ্ যদি এ জগতের স্রষ্টা হন এবং তিনি যদি এ জগতের সকল জীবকে প্রতিপালন করেন এবং তিনিই যদি এ দুনিয়াকে অবনত পর্যায় থেকে উন্নততর পর্যায়ে নিয়ে যান এবং এ বিশ্ব বিধানে যা কিছু রয়েছে তার মালিকানা একমাত্র তাঁরই হয়-তাহলে তাঁর সেসব গুণের আলোকে এ দুনিয়াকে ঢালাই করে সাজানো-গোছানো প্রত্যেক মুমিন-মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়ে। এ দুনিয়ায় জন্মগত তারতম্য রয়েছে কেউ বা সুন্দর, কেউ বা কুৎসিত, কেউ বা কালো, কেউ বা সাদা, কেউ বা ধনী, কেউ বা নির্ধন, কেউ শক্তিশালী, কেউ বা নিতান্তই দুর্বল। সকলের স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহ্র সকলের প্রতিই রয়েছে সমান স্নেহ, সমান করুণা, সমান সহানুভূতি। অথচ মানুষ তার নিজ সম্বন্ধে এতো বেশি কেন্দ্রিক যে, সে তার নিজের সম্বন্ধে ভাবনায় সবসময়ই লিপ্ত। এজন্য যাতে সে দরিদ্র জনসাধারণের অর্থাৎ যারা সারা মাসে একবেলাও পেট ভরে আহার করতে পারে না, তাদের দুঃখ-কষ্টের অনুভূতি যাতে অপরাপর সকল মানুষের হয়, তার জন্য ধনী, দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেই যাতে ক্ষুধার যাতনা বুঝতে পারে, তার জন্য রমযান মাসে দিনের বেলা সকলের জন্যই পানাহার থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। এতে ‘রব’ হিসেবে আল্লাহ্ কেবল এ দুনিয়াকে নয়- দুনিয়ার মানুষকে বিবর্তনকারী হিসেবে উন্নততর মানসিকতার পর্যায়ে উত্তোলন করতে প্রয়াসী।
দ্বিতীয়ত, এ মাসে ‘সওমের’ অনুশীলনে রত মানুষ যাতে সর্বাবস্থায় বুঝতে পারে,তার অধিকারে ধন-দওলত থাকলেও সে দওলত যথেচ্ছ ব্যয় করার অধিকার বা ভোগ করার অধিকার তার নেই; তাকে ভোগ করতে হবে সে সার্বভৌম শক্তির নির্দেশমতো। তাকে বুঝতে হবে তার অধিকারভুক্ত সম্পদে তার মালিকানা নেই। মালিকানা রয়েছে সর্বতোভাবে আল্লাহ্ সুবহানা তা’আলার। তাই সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও এ মাসে সে সম্পদের ভোগ থেকে বিরত থাকতে হচ্ছে।
তাই আমাদের পক্ষে রমযান মাসকে শুধু পানাহার থেকে বিরত থাকার মাস হিসেবে গণ্য করলে চলবে না। যাতে পাশবিক প্রবৃত্তিকে দমন করে প্রকৃত মনুষ্যত্ব আমরা লাভ করতে পারি এবং আল্লাহ্র ‘রব’ ও ‘ মালিক’ নামক গুণাবলির রুপায়নে সফল ও সার্থক হতে পারি সে-ই হবে রমযান মাসে আমার সাধনা।
হজ্জ ও কুরবানী
ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে হজ্জের একটা বিশেষ স্থান রয়েছে। হজ্জ ও কুরবানী উভয়েই একই সূরার পাশাপাশি তিনটি আয়াতে অবতীর্ণ হয়েছে বলে তাদের মধ্যে যে পারস্পরিক যোগসূত্র রয়েছে সে সম্বন্ধেও আমাদের অবহিত হওয়া উচিত। সঙ্গে সঙ্গে তাদের মর্মও আমাদের উপলব্ধি করা কর্তব্য।
প্রত্যেক ধর্মেরই একটা রয়েছে প্রচারিত দিক, অপরটি হচ্ছে আনুষ্ঠানিক দিক। প্রত্যেক ধর্মেরই প্রত্যয়ের মূলে থাকে ঐতিহাসিক পটভূমি ও দার্শনিক তত্ত্ব। অনুষ্ঠানে সে প্রত্যয়েরই মূর্ত রূপ দেওয়া হয়। অনুষ্ঠান প্রবল হয়ে উঠলে ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানের ভিত্তিতে অবস্থিত ঐতিহাসিক ও দার্শনিক দিকের আলোচনাও আমাদের কর্তব্য।
কুরআন-উল-করীমের ‘হজ্জ’ নামক সূরার হজ্জ সমাপন সম্বন্ধে বলা হয়েছে-
“ এবং যখন আমি ইবরাহীমের জন্য সেই গৃহের স্থান নির্ধারণ করিয়া বলিয়াছিলাম যে, আমার সহিত কোন বিষয়কেই অংশীদার করিও না এবং প্রশিক্ষণকারীগণের জন্য ও দন্ডায়মানগণের জন্য এবং রুকু ও সিজদাকারীগণের জন্য আমাদের গৃহকে পবিত্র রাখিও”। (সূরা হজ্জ)
“ এবং মানবগণের মধ্যে হজ্জ সম্বন্ধে ঘোষণা কর, -তাহারা তোমার নিকট পদব্রজে ও ক্ষীণকায় উষ্ট্রোপরি সমস্ত সুদূর পথ অতিক্রম করিয়া আগমন করিবে”।(সূরা হজ্জ)
“যেহেতু তাহারা নিজেদের উপকারের জন্য উপস্থিত হয় এবং পরিজ্ঞাত দিনসমূহে তিনি তাহাদিগকে পালিত পশু হইতে যাহা দান করিয়াছেন যেন তদুপরি তাহারা আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করে”। (সূরা হজ্জ)
প্রথমোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ মক্কার পবিত্র কাবাগৃহের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র সঙ্গে যেন অন্য কোন কিছুকে অংশীদার না করা হয় এবং যারা মনোনীত উপাসনা, প্রার্থনা ও প্রদক্ষিণ করতে আসে তাদের জন্য এ ঘরকে পবিত্র রেখো। উপরোক্ত আয়াতের শানে নযুলে লিখা হয়েছে, আরবের অংশীবাদী পৌত্তলিকেরা এবং আরববাসী য়াহুদী ও খ্রিষ্টান সম্প্রদায় হযরত ইবরাহীম (আঃ)- কে একজন মহামান্য নবী বলে সম্মান প্রদর্শন করতো। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রতিমা পূজা থেকে বিরত হয়নি। জনাব রসূল-ই-আকরাম (সঃ) ও তাঁর অনুগামীগণ আল্লাহ্র অংশীবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না বলে কুরায়শরা তাদের কা’বাগৃহে প্রবেশ করতে দিত না। তাদের অত্যাচার ও অনাচারের বিরুদ্ধে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে ভ্রান্ত ও বিপথগামী আরবগণকে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে—“ হে আরববাসী! আমরাই আদেশে ইবরাহীম (আঃ) নবী এ ঘর তৈরি করেছিলেন এবং আমারই আদেশে বিশ্ববাসীর কাছে হজ্জ ও কুরবানীর মর্ম ঘোষণা করেছিলেন। আমি তাকে আদেশ করেছিলাম অংশবাদিতা ও পৌত্তলিকতা থেকে আমার ঘরকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে আমার ইবাদত করতে। তোমরা এতই অকৃতজ্ঞ যে, ইবরাহীমের আদেশ লঙ্ঘন করেছো এবং তার উপদেশের বিরুদ্ধে এ পবিত্র গৃহে প্রতিমা স্থাপন করে তার উপাসনা করেছো।আমি আমার সত্য উপাসকগণের জন্যই এ পবিত্র গৃহ নির্ধারিত করেছি, তোমরা তাদের বাধা দিয়ে ধর্মদ্রোহিতার চরম নিদর্শন প্রকাশ করছো। শেষোক্ত আয়াতদ্বয়ে হযরত ইবরাহীম (আঃ) কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, “তুমি সমগ্র মানবজাতির জন্য হজ্জ সম্বন্ধে ঘোষণা করে দাও, তারা যেন নিজেদের কল্যাণ ও পাপ মুক্তির জন্য প্রতি বৎসরের নির্ধারিত দিনে এ পুণ্যধামে উপস্থিত হয় এবং তাদের জন্য আমি যে গৃহপালিত পশু বৈধ করেছি, তা থেকে যেন তারা তাদের মনোনীত ও নির্ধারিত পশু আমার নামে উৎসর্গ করে”।
এক্ষেত্রে মানুষের কল্যাণ কোথায়? নিশ্চয়ই এক বিশেষ কল্যাণ রয়েছে। কারণ হজ্জব্রত পালন উপলক্ষে দেশ-বিদেশের নানা ভাষাভাষী লোকেরা এখানে সমবেত হলে তাদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান হবে। এক দেশের সঙ্গে অপর দেশের লোকের পরিচয় হবে এবং তাদের মধ্যে ইখওয়ান বা ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে উঠবে। গৃহপালিত পশু উৎসর্গ করতে আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্য ও তার সৃষ্ট জীবকে তারই নামে উৎসর্গ করার রয়েছে মহান সুযোগ। প্রকৃতপক্ষে গৃহপালিত গরু,মহিষ,উট, দুম্বা বা বকরি মানুষের কাছে এমন প্রিয় হয়ে ওঠে যে, তাদের অনুপস্থিতিতে বা মৃতুতে মানুষ শোকে বিহ্বল হয়ে পড়ে। কুরবানীতে সেই সব মনোনীত ও প্রিয় পশুকে আল্লাহ্র নামে উৎসর্গ করতে এ প্রথার লক্ষ্য স্পষ্ট হয়ে পড়ে। এতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন আল্লাহ্র বান্দা তার সবকিছুকে আল্লাহ্র নামে উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত হয়। প্রকৃতপক্ষে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কুরবানী প্রথার সৃষ্টি হয়েছে। কুরাবানীর ঐতিহ্যের মধ্যে হযরত ইবরাহীম খলিলউল্লাহ (আঃ) কর্তৃক তাঁর পুত্র ইসমাইল (আঃ) কে কুরবানী দেওয়ার ঘটনা। যে ক্ষেত্রে পিতা হয়েও আল্লাহ্র সন্তোষ লাভের জন্য নবী মুরসাল তার পুত্রের গর্দানে ছুরি চালাতে সবসময় প্রস্তুত ছিলেন-সেক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ গরু, উট,দুম্বা,বকরি প্রভৃতি পশুকে আল্লাহ্র নামে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হবে না কেন?
কাজেই ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে হজ্জ ও কুরবানীর সার্থকতা সম্বন্ধে অনুধাবন করলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো আমাদের কাছে পরিস্কার হয়ে পড়ে। হজ্জব্রত পালনের সঙ্গে রয়েছে হযরত ইবারাহীম (আঃ)- এর স্মৃতি বিজড়িত। আল্লাহ্ তাঁকে দিয়ে একমাত্র তাঁরই উপাসনার জন্য এ ঘর তৈরি করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।
অথচ তাঁরই বংশধর ও তাঁর স্বদেশবাসী লোকেরা সে ঘরেই করত প্রতিমা পূজা এবং প্রকৃতপক্ষে যারা একেশ্বরবাদী তাদের সে ঘরে প্রবেশের অনুমতি দিতো না। আল্লাহ্র অভিপ্রায় অনুসারে যারা হজব্রত পালন করেন তারা একেশ্বরবাদের স্বাদ পাবেন এবং পরস্পরের সঙ্গে তারই মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের পর্যায়ে উন্নীত হবেন।
হজ্জ ও কুরবানীর দার্শনিক দিকের আলোচনা করলে দেখা যায়, হজ্জের মূল লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহ্র তওহীদবাদের প্রতিষ্ঠা। যাতে সে তওহীদের গোড়া পত্তনকারী হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ধ্যান-ধারণার সঙ্গে মানুষ পরিচিত হয় তার জন্যই মানুষকে একালে আহ্বান করা হয়েছে। তওহীদবাদের প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এত জোরালো দাবি কেন? তওহীদের সার্থকতা হচ্ছে মানুষে মানুষে প্রভেদের বিলোপ সাধন। একই আল্লাহ্র বান্দা হিসেবে এ দুনিয়ার মানুষ সকলেই সমান। ভাষা, বর্ণ, রক্ত, আর্থিক প্রভেদ যাতে এ দুনিয়ার মানুষের মধ্যে কোন ভেদবুদ্ধি সৃষ্টি করতে না পারে, সেজন্য ভৌগোলিক পূজ্য দেবতাদের বা পিতৃপিতামহদের পূজ্য দেবতাদের বর্জন করে তওহীদের ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হওয়ার জন্য কুরআনুল করীমে তাগিদ দেয়া হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, ‘ইবরাহীম (আঃ)- এর বংশধর বলে দাবি করা সত্ত্বেও তোমরা আমার আদেশ পালন করছো না- তাতে তোমরা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হচ্ছো।
তওহীদের ধারণা অত্যন্ত ব্যাপক। তার মধ্যে সতত সচেতন, ক্রিয়াশীল সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, বিবর্তনকারী, এক সত্তার যেমন ধারণা রয়েছে তেমনি ন্যায়বিচারক ও সার্বভৌম সত্তার ধারণাও রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তওহীদপন্থীর কাছে আল্লাহ্র নিরানব্বইটা নাম এক একটি গুণও বটে এবং মানবজীবনের পক্ষে আল্লাহ্র পরিচয়েরও এক একটি মাধ্যম বটে। সঙ্গে সঙ্গে এগুলো মানবজীবনের আদর্শও বটে। মানুষ এদের মাধ্যমে আল্লাহ্র সর্বাঙ্গীণ পরিচয় না পাক, এগুলোর অনুসরণ করে নিজের জীবনকেও উন্নত করতে পারে। এদের মধ্যে আবার অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ। রব হলে যেমন তাঁকে সৃষ্টিকর্তা, বিবর্তনকারী ও পালনকর্তা হতে হবে তেমনি তাঁকে বিচারপতিও হতে হবে, তাকে দয়ালুও হতে হবে। ন্যায়বিচারক হলে এ দুনিয়ার সকল জীবের প্রতি তাঁর সমদৃষ্টি থাকতে হবে, যাতে সকল জীবই আহার লাভ করতে পারে তার ব্যবস্থাও করতে হবে। মানুষের বেলায় শোষক ও শোষিত বলে কোন বিশেষ শ্রেণী থাকবে না। এ দুনিয়ার সম্পদ যাতে এ দুনিয়ার সকল মানুষই সমানভাবে ভাগ করে ভোগ করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। কাজেই সমাজ ব্যবস্থা সাম্যবাদমূলক হওয়া উচিত।
কুরআনুল করীমে এ জন্যই তওহীদের ওপর এত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কারণ তওহীদ কেবল বিশুদ্ধ দার্শনিক ধারণা নয়, তওহীদ ও তার আনুষঙ্গিক নানাবিধ গুণের সঙ্গে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের সংশ্রব বর্তমান।
কুরবানীর মূল তাৎপর্য কুরাআনুল-করীমের মধ্যেই বর্ণনা করা হয়েছে। “কুরবানীর পশুর গোশত অথবা উহাদের রক্ত আল্লাহ্র নিকট উপনীত হয় না বরং তোমাদের সংযমই উপনীত হয়ে থাকে”। এতে স্পষ্ট বোঝা যায়, কুরবানী একটা পশুহত্যার নিষ্ঠুর অনুষ্ঠান নয়। এতে প্রিয় পশুকে আল্লাহ্র পথে উৎসর্গ করাতে যে দৃঢ়চিত্ততা,কর্তব্যবোধ ও সংযমের প্রয়োজন তারই পরীক্ষার মূল।
যাকাত
স্বতঃপ্রণোদিত, উদ্ধৃত্ত অর্থ বা অন্য কোন সম্পদ আত্মার কল্যাণের জন্য দান করাই যাকাতের মূল উদ্দেশ্য। পূর্বেই বলা হয়েছে, আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করে নিলে এ দুনিয়ার কোন সম্পদের ওপরই মানুষের মালিকানা থাকতে পারে না।
মানুষ নিজেকে তার কাছে অর্পিত অথবা তার উপার্জিত সম্পদের হিফাজতকারি(Custodian) বলে গণ্য করে সে সম্পদকে আল্লাহ্র নির্দেশ মতে ভোগ করবে। তবে এ নীতি গ্রহণ করেও তার চিত্তের বা রূহের বিশুদ্ধির জন্য তার কাছে সঞ্চিত বা উপার্জনকৃত সম্পদের জন্য তাকে একটা নির্দিষ্ট অংশ প্রকৃতপক্ষে যারা হকদার তাদের উদ্দেশ্য দান করতে হবে। সেসব দেশের বায়তুলমালে সে সম্পদের অংশ দান করতে হবে।
কুরআনুল-করীমের নির্দেশ ও আল্লাহ্র রসূলের ব্যাখ্যা মতে সোনারূপা যাদের কাছে সঞ্চিত তাদের পক্ষে শতকরা আড়াই ভাগ রূহের বিশুদ্ধির জন্য দিতে হবে।
তবে এ সর্বাবস্থায় এ দানকে ইনকাম ট্যাক্স বলে গণ্য করা যাবে না। এ ট্যাক্স হচ্ছে রূহের বা আত্মার বিশুদ্ধির জন্য। ইসলামী রাষ্ট্রের সকল সম্পদের মালিকানা একমাত্র আল্লাহ্র। কাজেই সে রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য যখনই যা প্রয়োজন রাষ্ট্র ব্যক্তিবিশেষের কাছে রক্ষিত সম্পদ থেকে অবাধে আদায় করতে পারে। ইসলামী রাষ্ট্রে ব্যক্তিবিশেষকে উপার্জনের অধিকার দান করলেও সে উৎপাদিত সম্পদ ভোগের সীমা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। এ সম্বন্ধে ইমাম ইবনে হাজম তাঁর ‘মুহাল্লা’য় বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।
জিহাদ
জিহাদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে কঠোর পরিশ্রম বা অবিরাম চেষ্টা বা সাধনাতে লিপ্ত হওয়া। তার সাধারণত ইসলামকে এ বিশ্বে টিকিয়ে রাখার জন্য সংগ্রামে লিপ্ত হওয়াকে জিহাদ নামে অভিহিত করা হয়। তবে এ কথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, ইসলামের পরিভাষায় জিহাদ অত্যন্ত ব্যাপক অর্থেই ব্যবহৃত হয়। মানবজীবনকে সুন্দর, সরল ও মঙ্গলময় পথে পরিচালনা করার যতগুলো প্রতিবন্ধক রয়েছে- তার বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম করাই জিহাদের মূল লক্ষ্য-সংগ্রাম ব্যক্তিবিশেষের জীবনে (ক) প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে যেমন হতে পারে, (খ) তেমনি তার দৈহিক নিরাপত্তার জন্য আততায়ীর বিরুদ্ধেও হতে পারে, (গ) স্বীয় এবং সামাজিক আর্থিক বিধানের বিরুদ্ধেও হতে পারে, (ঘ) মানবজীবনের কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধেও হতে পারে এবং (ঙ) নফস ও কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ। একে একে তার আলোচনা করা যাক।
(ক) ব্যক্তিগত কর্তব্য পালনে জিহাদের অর্থ হচ্ছে- সকল প্রতিকূল পরিবেশে-ঈমানকে বজায় রেখে কর্তব্য পালনে সচেষ্ট থাকা অর্থাৎ মানুষের পক্ষে আল্লাহ্ যেসব কর্তব্য নির্ধারণ করেছেন- সকল প্রকার প্রতিকূল পরিবেশেও সে কর্তব্য পালন করতে মানুষ যেন কোন অবস্থায়ই নিবৃত্ত না হয়। এ প্রকার জিহাদের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় মক্কার নবদীক্ষিত মুসলিমদের উৎসর্গীকৃত জীবনে। দীর্ঘ তেরো বৎসরকাল তাঁরা মক্কার কুরায়েশদের হাতে যে অমানুষিক নির্যাতন সহ্য করেছিলেন দুনিয়ার ইতিহাসে তার কোন দৃষ্টান্ত নেই। অথচ এসব মুমিন-মুসলিমগণ তাদের প্রত্যয় থেকে একবিন্দুও বিচলিত হননি। শত অত্যাচার সহ্য করেও স্বকীয় প্রত্যয় থেকে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে তাঁরা এ বিশ্বে জিহাদের এক আদর্শ স্থাপন করেছেন।
(খ) সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠায় ও প্রচারে প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধাচরণ যখন সীমা অতিক্রম করে এবং ন্যায়পন্থীদের জ্ঞান ও মালের নিরাপত্তার চরম সংকট দেখা দেয় তখন এ জিহাদ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। আত্মরক্ষার জন্য আততায়ীকে যেমন মানুষ হত্যা করতে পারে,তেমনি ধর্মের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপকারীদের হাত থেকে ধর্ম রক্ষার্থে তাদের সাথে জিহাদ করাও অবশ্য কর্তব্য।
আত্মরক্ষায় সশস্ত্র যুদ্ধ করার অনুমতি দিয়ে এই আয়াত নাযিল হয়। “ যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয় তারা অত্যাচারিত বলে তাদের (যুদ্ধের) অনুমতি দেয়া হলো। আর এ কথা নিশ্চিত যে, আল্লাহ্ তাদের জয়যুক্ত করতে সম্পূর্ণ ক্ষমতাবান। (যুদ্ধ দ্বারা অত্যাচারিত তারাই) যাদেরকে তাদের দেশ থেকে অন্যায়ভাবে বহিস্কার করা হয়েছে-শুধু এই কথা বলার অপরাধে যে, “আমাদের রব(প্রভু) আল্লাহ্”।
(গ) এই কথা আজ সর্বজনস্বীকৃত যে, আর্থিক সংস্থান ব্যতীত কোন মহৎ কর্মই সম্পাদিত হতে পারে না। এজন্য আর্থিক দিক থেকে জিহাদের প্রয়োজন রয়েছে। আর্থিক জিহাদের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্র রাজত্ব এ দুনিয়ার প্রতিষ্ঠা করার জন্য সর্বপ্রকার আর্থিক সম্পদ ত্যাগের জন্য প্রস্তুতি। মানুষ অন্যায়ভাবে ধনসম্পদকে জীবনযাত্রার মাধ্যম হিসেবে গণ্য না করে জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য বলে জ্ঞান করে সকল সময়েই তাকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়। তবে যারা এ জীবনে আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বে সম্পূর্ণ প্রত্যয়শীল তাদের পক্ষে তাদের কাহচে সঞ্চিত ধন-দওলত গচ্ছিত সামগ্রীর মত। তারা অবাধেই আল্লাহ্র রাস্তায় সবকিছু বিলিয়ে দিতে পারে। তবে যেহেতু সকল মানুষই একই জীবনের অধিকারী তাই যাতে সকল মানুষই একইভাবে আল্লাহ্র পথে ধনসম্পদে বিতরণের জন্য প্রস্তুত হয়- এজন্যই এ আর্থিক জিহাদের জন্যও তাগিদ দেয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে কুরআনুল-কারীমে বলা হয়েছে, “যুদ্ধোপকরণ অল্প হোক আর অধিক হোক-তোমরা বহির্গত হও এবং তোমাদের ধনসম্পদ ও জীবন উৎসর্গ করে আল্লাহ্র পথে জিহাদ কর। ইহা তোমাদের পক্ষে উত্তম যদি তোমরা বিজ্ঞ হয় (সূরা তওবাঃ ৬)”। অন্যত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, “নিশ্চয়ই মুমিন তারাই, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তৎপর তারা এ বিষয়ে কোন সন্দেহ করেনি এবং ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করেছে, তারাই (ঈমানের দাবিতে) সত্যবাদী (হুজুরাতঃ ২)”।
(ঘ) এ কথা সর্ববাদীসম্মত যে, যখনই কোন জাতি জ্ঞানচর্চায় পরাংমুখ হয়েছে, তখনই সে জাতির জীবনে নেমে এসেছে চরম দুর্ভোগ। পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায়, সত্য ও অসত্যের মধ্যে প্রভেদ করতে না পেরে তখনই সে জাতি তার জীবনে ডেকে এনেছে ঘোর অমঙ্গল। কথিত আছে- মিসরের সম্রাট যখন খোদায়ীর দাবি করতে প্রস্তুতি নিচ্ছিল তখন তার পূর্বে সে তার রাজ্যে জ্ঞানচর্চা বন্ধ করে দিয়েছিল। শুধু তাই নয়-সবগুলো শিক্ষাকেন্দ্র ধ্বংস করে দিয়েছিল। তার ফলে সমগ্র দেশ অজ্ঞানতার অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয়ে গেল তখনই তার পক্ষে খোদায়ী দাবি করা সহজ হয়ে পড়লো। এজন্য খাঁটি মুমিনের পক্ষে সর্বদা জ্ঞানের দীপশিখা প্রজ্বলিত করার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত হতে হবে। জ্ঞানের জন্য জিহাদের অর্থ হচ্ছে-সর্বপ্রকার অজ্ঞানতা ও আদর্শ বিচ্যুতির বিরুদ্ধে জিহাদ। ইসলাম মানবজীবনের আলোকেই এ জিহাদের নীতির প্রবর্তন করেছে। এ জিহাদের অর্থ হচ্ছে কোন অবস্থায়ই মানবজীবনের অজ্ঞানতার অন্ধকার ঘনীভূত হওয়ার সুযোগ দান না করা, ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনকে সর্বদাই-সর্বাবস্থায় অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে মুক্ত রাখা।
(ঙ) নাফস বা কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ-মানব জীবনে প্রবৃত্তির স্বেচ্ছাচারিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতাই নৈতিক ও আত্মিক অবনতির একমাত্র কারণ। মানুষ যদি নাফসকে বল্গাহীন অশ্বের মত যথাতথা বিচরণ করতে ছেড়ে দেয়-তা’হলে সে প্রবৃত্তির দ্বারা তার ব্যক্তিগত জীবনের যেমন অমঙ্গল হতে পারে, তেমনি সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় জীবনেরও সর্বপ্রকার অকল্যাণ হতে পারে। বল্গাবিহীন অশ্বের দ্বারা যেমন অঘটন ঘটতে পারে তেমনি বল্গাবিহীন নাফসের দ্বারাও নানা সংকট দেখা দিতে পারে। এজন্য শুধু ইসলাম ধর্মে নয়, জগতের সকল ধর্মেই সংযত জীবন যাপন করার জন্য উপদেশ দেয়া হয়েছে। তবে ইসলামে এ নাফসের বিরুদ্ধে জিহাদকে সর্বোত্তম জিহাদ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ইসলামে এ জিহাদকে বলা হয়েছে ‘জিহাদ-ই-আকবার’। ইসলামের ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে – একদা একদল সাহাবা যখন কোনও এক ধর্মযুদ্ধ থেকে ফিরে এলেন, তখন হযরত রসূলই আকরম (সঃ) তাঁদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন, “এইবার তোমার ছোট জিহাদ থেকে প্রত্যাবৃত্ত হলে”। অর্থাৎ নিজের নাফসের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য তোমাদের প্রস্তুতি নিতে হলো। এক হাদীসের বর্ণনায় রয়েছে- একদা হযরত নবী করীম (সঃ) সাহাবাগণকে জিজ্ঞেস করলেন, “তোমরা মল্লবীর বা পাহ্লোয়ান কাকে বলে থাকো-? সাহাবাগণ আরয করলেন- যাকে কুস্তিতে কেউ পরাভূত করতে পারে না আমার তাকেই পাহলোয়ান বলে থাকি। জনাব রসূলল্লাহ (সঃ) বললেন- না, তা নয়, বরং যে ব্যক্তি তীব্র ক্রোধের সময়ও নিজের নাফসকে সংযত রাখতে পারে সে-ই (প্রকৃত) পাহলোয়ান”।
এতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয়, ইসলামের দৃষ্টিতে আমাদের পাশবিক প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই প্রকৃষ্টতম জিহাদ।
সামাজিক জীবনে নর-নারী সম্পর্কঃ ইসলামী সমাজে নারীর মর্যাদা ও অধিকার
ইসলামের দৃষ্টিতে আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশের বেলা নরনারীর মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। স্ত্রী-পুরুষের দাবী দাওয়াও পরস্পরের ওপর সমান। বরং দেনমোহর ইত্যাদি বাবত স্ত্রীর দাবি পুরুষের ওপর প্রবল। স্ত্রীর খোরপোশ প্রভৃতি সম্পূর্ণ বহন করা পুরুষের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে নারীকে পুরুষের সমান অধিকার দেওয়া হয়নি-যেমন উত্তরাধিকার, বহুবিবাহ ইত্যাদি নারীর অধিকার পুরুষের সমান নয়।
কেন নারীর অধিকার পুরুষের সমান নয়- এ সম্বন্ধে আলোচনা করলে দেখা যায় অনেকটা কারণ বর্তমান। সকল সমাজেই এবং সকল দেশেই মর্যাদা ও অধিকারের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কোন ব্যক্তিকে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা দান করলে তাকে সর্বশ্রেষ্ঠ অধিকার নাও দেওয়া যেতে পারে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ অধিকার দান করলেও সর্বোচ্চ মর্যাদা দান নাও করা হতে পারে। পুরাকালে সকল দেশেই রাজাকে সর্বশ্রেষ্ঠ অধিকার দান করা হত। এখনও যেসব দেশে রাজতন্ত্র টিকে রয়েছে, সে সব দেশে রাজার অধিকার সর্বোচ্চ। তবে সেসব দেশের জনগণ আন্তরিকভাবে রাজাকে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা দান করতে প্রস্তুত নাও হতে পারে। রাজার মর্যাদা নির্ভর করে তার কৃতকর্মের ওপর। তিনি মানবপ্রেমিক বা মানবদরদী হলে অবশ্যই সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী হবেন। তবে তার আচার-ব্যবহার কুৎসিৎ এ জঘন্য হলে তাকে কেউই গুরুজনে মর্যাদা দান করতে প্রস্তুত হবে না।
মর্যাদা ও অধিকারের এ পার্থক্য আমাদের এ উপমহাদেশেই বিশেষভাবে ফলে উঠেছে। প্রায় সবসময়েই রাজন্যবর্গকে সকল রকমের অধিকার দেয়া হয়েছে। তবে রাজন্যবর্গ আধ্যাত্মিক সাধনায় উন্নত থেকে, সন্ন্যাসী বা পীর-দরবেশগণের নিকট সর্বদাই কৃতাঞ্জলিপুটে উপস্থিত হয়েছেন। অবদান শতকের একটা তরজমা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেনঃ
নৃপতি বিম্বিসার-
নামিয়া যুদ্ধে মাগিয়া লইয়া পদ-নখ-কণা তার-
এত বড় রাজা বিম্বিসার, যার অধিকারের কোন সীমা ছিল না, সেই রাজা বিম্বিসার মর্যাদার দিক থেকে মহাজ্ঞানী বুদ্ধের পদ নখ-কণা সংগ্রহের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন।
আমরা সাধারণত মর্যাদা ও অধিকারের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না বলে অনেক সময় আমাদের বিচারের মধ্যে ভ্রান্তি দেখা দেয়। আমাদের দেশে সাম্প্রতিক নারীজাগরণের আলোকে ইসলামী সমাজে নারীর অধিকার নিয়ে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এ অধিকারের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে অনেকেই অধিকারের সঙ্গে মর্যাদাকে এক পর্যায়ভুক্ত করে এ সমস্যাটিকে আরও জটিল করে তুলেছেন। তাই এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা উচিত। ইসলামী সমাজে নারীর মর্যাদা ও অধিকার সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করতে হলে আমাদের কুরআনুল-করীম ও হাদীসের উক্তিগুলোকে বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে। কারণ কুরআন-উল-করীম ও হাদীস শাস্ত্র হচ্ছে ইসলামের বুনিয়াদ। ইসলাম এক কালে ( অর্থাৎ খুলাফায়ে রাশেদীনের সময়) এ দুই বুনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। বর্তমানে এ দুনিয়ার কোথাও ইসলামী সমাজ বা রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নেই, তবে অদূর ভবিষ্যতে ইসলামী সমাজ গঠিত হলে এ দুটো মূল ভিত্তির ওপরই গঠিত হবে। পাক কুরআনুল-করীমে বলা হয়েছে, “তাদের জন্য তোমাদের ওপর সেই অধিকার তোমাদের জন্য যেমন তাদের ওপর রয়েছে। (সূরা নিসা)”
এ সূরা নিসাতেই আবার বলা হয়েছে,
“পুরুষ জাতির নেতৃত্ব রয়েছে নারীদের ওপর”।
আবার অপর এক সূরায় বলা হয়েছেঃ
“ তোমরা গৃহে অবস্থান কর এবং জাহিলী যুগের নারীদের মত উচ্ছৃঙ্খলভাবে চলাফেরা করো না”। (সূরা আহযাব)
ইসলাম জগতে আল্লাহ্র রসূল (সঃ)-কে গণ্য করা হয় জীবন্ত কুরআন রূপে। কুরআনুল-করীমের প্রতিটি অক্ষর তাঁর জীবনে রূপায়িত হয়েছে বলে তিনি এ দুনিয়ার কুরআনুল-করীমের অতুলনীয় ভাষ্যকার। নারী জাতি সম্বন্ধে তাঁর উক্তির মধ্যে নিন্মলিখিত কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্যঃ
১. সন্তানের বেহেশ্ত মায়ের পদতলে।
২. পিতামাতার মধ্যে কাকে প্রথম সম্মান প্রদর্শন করবে, এ প্রসঙ্গে কোন এক ছেলের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেনঃ প্রথমে তোমার আম্মাকে, তারপর তোমার আম্মাকে, তারপরে তোমার আম্মাকে, তারপরে তোমার আব্বাকে।
৩. স্ত্রীলোকেরা পুরুষের যময অর্ধেক।
৪. একজন স্ত্রীলোকের চারটি গুণের জন্য বিয়ে হতে পারেঃ
(ক) সে ধনী হলে, (খ) কুল গৌরবে উচ্চস্থানীয় হলে, (গ) সুন্দরী হলে ও (ঘ) পুণ্যশীলা হলে। কাজেই যে স্ত্রীলোক পুণ্যশীলা তার সন্ধান কর; যদি তুমি অন্য চিন্তা দ্বারা প্রভাবান্বিত হও, তাহলে তোমার দু’হাত কর্দমাক্ত হবে।
৫.এ পৃথিবী ও তার অন্তর্গত সবকিছুই সম্পদ, তবে এ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ ধার্মিক নারী।
৬. আরব দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ স্ত্রীলোক কুরায়েশদের মধ্যে সে নারীগণ যারা শিশুদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ ও তাদের স্বামীদের সম্পদের দিকে সতর্ক দৃষ্টি।
৭.আল্লাহ্র আদেশ তোমরা তোমাদের নারীদের প্রতি উত্তম ব্যবহার করবে। কারণ, তারা তোমাদের মাতা, কন্যা ও স্ত্রী।
৮. নারীদের অধিকার পবিত্র। যাতে তাদের অধিক কষ্ট না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রেখো।
৯. তোমাদের নারীদের মসজিদে আসতে বাধা দিও না। তবে তাদের বাড়ি তাদের পক্ষে উত্তম স্থান।
কুরআনুল করীম ও হাদীসের এসব উক্তিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়-নারীর মর্যাদা ও অধিকারের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। যখন বলা হয়েছে পুরুষের ওপর নারীর, নারীর ওপর পুরুষের অধিকার সমান তখন এ বিশ্বে নারীর অধিকার পুরুষের অধিকারের সমান বলে গণ্য হয়েছে। এ আয়াতের পোষকতায় রয়েছে আল্লাহ্র রসূল (সঃ)-এর হাদীসঃ স্ত্রীলোকেরা পুরুষের যময অর্ধেক। নারীদের অধিকার পবিত্র। যাতে তাদের অধিক কষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবে।
কাজেই অধিকারের বেলায় নারী, পুরুষের মধ্যে কোন ভেদাভেদ ইসলামী সমাজে হতে পারে না। প্রশ্ন হচ্ছে কিসের অধিকার? সে অধিকারের যখন কোন সীমার মধ্যে আবদ্ধ করা হয়, তখন তাকে জীবনের সকল খেত্রের অধিকার বলেই গণ্য করতে হবে। মানবজীবনের প্রাথমিক চাহিদা হচ্ছে অন্ন-বস্ত্রের সন্ধান। অন্ন-বস্ত্র বিতরণের সময় যেমন নারী-পুরুষের মধ্যে কোন ভেদাভেদ থাকতে পারে না, তেমনি শিক্ষা, সংস্কৃতি বা জীবনের অন্যান্য অধিকার লাভের ক্ষেত্রেও তাদের অধিকার ক্ষুণ্ন করা হবে না। বর্তমান কালের গনতন্রের যুগে প্রতিনিধি নির্বাচনেও নারীর অধিকারকে পুরুষের সমতুল্য অধিকার বলেই গণ্য করতে হবে। একথা অবশ্য সত্যি যে, আল্লাহ্র রসূলের ইন্তেকালের পরে খলীফা নির্বাচনে কোন নারী অংশগ্রহণ করেন নি। সে যুগে নারীরা রাজনীতি বা রাষ্ট্রনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেননি বলে তাতে তাঁরা অগ্রসর হননি। অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অবতীর্ণ হতেও দ্বিধাবোধ করেননি। হযরত উসমান (রাঃ)- এর শাহাদাতের পরে উমাইয়াদের প্রচারণার ফলে মুসলিম জননী হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁর এ কার্যকলাপে ইজতিহাদী গলদ থাকতে পারে, তবে এতে যে নারীর রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সূচনা হয়েছে তা’অনায়াসেই বলা যায়। বর্তমান কালের রাজনীতিতে নারীরা ন্যায়-অন্যায়বোধে কেন সংগ্রামে অবতীর্ণ হবেন না তার কোন সদুত্তর নেই।
কেবল রাজনীতি নয়, জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে যেখানে নারী ধর্মের বিপরীত কোন কাজকর্মে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে, সেখানে নারীর অধিকারকে কোন অবস্থায়ই পুরুষের অধিকারের চেয়ে খাটো করা হয়নি।
এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে নারীর উত্তরাধিকার নিয়ে। নারীকে পুরুষের সমান উত্তরাধিকার দেয়া হয়নি। আম্মা অথবা আব্বার সম্পত্তিতে ছেলেরা যে অংশ পায়, মেয়েদের জন্য তার অর্ধেক নির্ধারিত রয়েছে। একজন পুরুষের স্ত্রী তার পরিত্যাজ্য সম্পত্তিতে সন্তান-সন্ততি থাকলে দুই আনা অংশের মালিক হয়। অথচ একজন নারী তার স্বামীর আগে মৃত্যুবরণ করলে, স্বামী তার সম্পত্তির চার আনার উত্তরাধিকার লাভ করবে।
সাক্ষীদানকালে শুধু নারীর সাক্ষ্য ইসলামী বিধানমতে গণ্য হয় না। শতাধিক নারী হলেও তার সঙ্গে একজন পুরুষ মানুষের সাক্ষ্যের প্রয়োজন। বিয়ের বেলায় একজন পুরুষের চার স্ত্রী গ্রহণ করাও চলে। অপরদিকে নারীর পক্ষে একাধিক স্বামী একসঙ্গে গ্রহণ করার কোন উপায় নেই।
এ সব বিষয়ে আলোচনা করতে হলে আমাদের মনে রাখতে হবে, ইসলামী সমাজ পিতৃপ্রধান বা Patriarchal। সুদূর অতীতে এবং আমাদের রসূল-ই-আকরমের (সঃ) জন্মের একশত বৎসর পূর্বেও সারা আরব দেশে মাতৃপ্রধান (Matriarchal Society) সমাজ ছিল। এমনকি হযরতের জন্মের সময়ও ইয়েমেনে মাতৃপ্রধান সমাজ প্রচলিত ছিল। পুরুষেরা নানাবিধ সংগ্রামের মধ্যে তাদের স্বাধীনতা লাভ করেছিল এবং তারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ জাহিলিয়াতের যুগে মাতৃজাতির ওপর নানাবিধ নির্যাতন করা হত। জাহিলিয়াতের যুগে পর্যুদস্ত নারী সমাজকে পুরুষের বিলাসসামগ্রী বলে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হত। সে প্রতিক্রিয়াশীলতার যুগে জন্মগ্রহণ করেও হযরত রাসূল-ই-আকরাম (সঃ) নারীকে পরম মর্যাদা দান করেছেন।
উত্তরাধিকারের বেলায় নারীকে কেন পুরুষের সমান অধিকার দান করা হয়নি, তার উত্তরে বলা যায়-নারীদের পক্ষে পিতার সম্পত্তিতে অধিকার লাভ করার পরও স্বামীর কাছে তাদের নিরাপত্তার জন্য কাবিন লাভ করার সুযোগ রয়েছে। পুরুষের পক্ষে এরূপ সুযোগ নেই। তার ওপর নিজের স্ত্রীর ও সন্তানের ভরণ-পোষণের জন্য পরিবারের কর্তা হিসেবে পুরুষই সম্পূর্ণ দায়ী। নারীকে ভরণ-পোষণের দায়িত্ব থেকে মুক্ত করা হয়েছে। এমনকি সন্তানকে স্তন্য দান করাও নারীর পক্ষে অবশ্য কর্তব্য নয়। সে ইচ্ছা করলে সন্তানকে দুগ্ধ দান করতেও পারে, নাও করতে পারে। তার গর্ভজাত সকল সন্তানের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তার স্বামীর।
জাহিলিয়ার নারীদের মত মুসলিম নারীগণ ভবঘুরের বা আওয়ারার মত চলাফেরা করবে না বলে তারা যাতে তাদের বাড়িতেই অবস্থান করে এরূপ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নারীরা আদেশ পালন করুন বা অন্য কোন কাজে লিপ্ত থাকুন, তাদের চলাফেরা বা অভিজ্ঞতা পুরুষ মানুষের মত এতো ব্যাপক না হওয়ারই কথা। এ জন্য তাদের সাক্ষ্যের পরিপূরক হিসেবে একজন পুরুষের সাক্ষ্যের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করা হয়েছে।
তবে ইসলামে ‘অধিকার’ শব্দটি সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। ইসলামে ‘অধিকার’ শব্দের অর্থ কোন কিছুর ওপর ব্যক্তির মালিকানা নয়, তার হিফাজত মাত্র। যাকে ইংরাজীতে বলে Custodianship। ইসলামী সমাজে নর অথবা নারী কেউই তার ইচ্ছামত কোন সম্পদ ব্যয় বা ধ্বংস করতে পারে না। তাকে সে সম্পদের রক্ষক হিসেবে আল্লাহ্র পথে মানুষের কল্যাণের জন্য ব্যয় করতে হবে।
বিবাহের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের অধিকারের তারতম্য সম্বন্ধে বলা যায়-ইসলামের দৃষ্টিতে যিনা বা ব্যভিচার হচ্ছে মহাপাপ। তাই যাতে কোন অবস্থায়ই নর অথবা নারী এ কাজে লিপ্ত না হয় সেজন্যই পুরুষকে বহুবিবাহের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এ দুনিয়ার মানবজাতির সংখ্যা নিয়ে আলোচনাকালে দেখা গিয়েছে, প্রত্যেক দেশেই নারীর সংখ্যা থেকে পুরুষের সংখ্যা অধিক। সাধারণভাবে শীতপ্রধান দেশে বিবাহযোগ্য পুরুষের বয়স ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ এবং বিবাহযোগ্য নারীর বয়স পঁচিশ থেকে চল্লিশ এবং বিবাহযোগ্য নারীর বয়স পনের থেকে ত্রিশ বৎসর বলা যায়। শীতপ্রধান বা গ্রীষ্মপ্রধান উভয় অঞ্চলেই বিবাহযোগ্য পুরুষের সংখ্যা নারীর চেয়ে কম। কারণ এ বয়সে পুরুষেরা নানাবিধ কাজকর্মে লিপ্ত থেকে প্রাকৃতিক বা যান্ত্রিক গন্ডগোলের জন্য প্রাণ হারায়। জগৎব্যাপী মহাসমরের সময় যুদ্ধে লিপ্ত দেশসমূহের বিবাহযোগ্য পুরুষ মানুষের সংখ্যা গুরুতরভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। কাজেই এসব সংকটকালীন সময়ের ব্যবস্থার জন্য ইসলামে একাধিক বিবাহের অনুমতি বা provision রয়েছে। তবে এসব সুযোগ দেয়া সত্ত্বেও কুরআনুল করীমে ঘোষণা করা হয়েছে, “তোমরা যদি আশঙ্কা কর যে, ইয়াতিমদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে বিয়ে করবে নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে, দু’তিন বা চার”। যেহেতু কোন ব্যক্তির পক্ষেই একাধিক স্ত্রীর সঙ্গে সমান ব্যবহার করা সম্ভব নয়, এজন্য প্রয়োজনে ব্যতীত প্রকারান্তরে তাতে নিষেধ আরোপ করা হয়েছে।
সমানভাবে ব্যবহার করতে সক্ষম না হলে যে কোন পুরুষের পক্ষে একাধিক বিবাহ জায়েয নয় ইমাম আবু হানীফা (রঃ) বহু পুর্বেই রায় দিয়েছেন। তাঁর সমসাময়িক আব্বাসী বংশের তথাকথিত খলীফা আবু মনসুর প্রৌঢ় বয়সে এক কিশোরীর সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে তাকে বিয়ে করতে চাইলে তাঁর স্ত্রী তা সম্পূর্ণভাবে নাজায়েয বলে বাধা দেন। উভয়ের সম্মতিতে ইমাম আবু হানীফা (রঃ) কে রায় দানের জন্য আহ্বান করা হলে তিনি বলেন, “ এ সম্বন্ধে আপনি (অর্থাৎ আল-মনসুরও) রায় দিতে পারেন”। সূরা নিসার তৃতীয় আয়াতে রয়েছে- “তোমরা যদি আশংকা কর যে, ইয়াতিমদের প্রতি অবিচার করতে পারবে না, তবে বিয়ে করবে নারীদের মধ্যে যাকে, তোমাদের ভাল লাগে দু’তিন বা চার”। এতটুকু পর্যন্ত শুনে আল-মনসুর উল্লসিত হয়ে বলেন – “শুনুন বেগম সাহেবা”। তার পরে ইমাম সাহেব বলেন,- “তবে যদি মনে কর, তাদের সঙ্গে সমান ব্যবহার করতে পারবে না- তাহলে তাদের মধ্য থেকে একজনকে বিয়ে করবে। একথা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে বেগম সাহেবা উল্লসিত হয়ে বলেন- ‘শুনুন খলীফা’। তাহলে এ দুটো উক্তির মধ্যে কোনটা গ্রহণীয়-এ প্রশ্ন করা হলে ইমাম আবু হানীফা (রঃ) বলেন- যদি উভয়ের সঙ্গে সমান ব্যবহার করতে না পারেন তাহলে পুনরায় বিবাহ আপনার পক্ষে জায়েয হবে না। আল-মনসুর স্বীকার করেন-তিনি উভয়ের সঙ্গে সমান ব্যবহার করতে পারবেন না। কাজেই ইমাম সাহেব তার পক্ষে পুনরায় বিবহ নাজায়েয বলে ঘোষণা করেন। এতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয়, এক স্ত্রী উপস্থিত থাকাকালে পুনরায় বিবাহ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি যদি উভয়ের সঙ্গে সমান ব্যবহার করতে পারবে না বলে পূর্বেহ্নেই ওয়াকিফহাল হয়, তা হলে তার পক্ষে পুনরায় বিয়ে করা জায়েয হবে না। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়- আমাদের সমাজে বিবাহের এ মূল সূত্রের প্রথম দিকের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে শেষের দিকের প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে বহুবিবাহের প্রচলন হয়েছে।
পুরুষের সঙ্গে স্ত্রী একই সমতলে বা একই কাজ করতে পারবে না-তার পক্ষে কুরআনুল-করীম ও হাদীস শরীফে কোন নির্দেশ নেই। শাসন বা বিচার বিভাগীয় কাজে, শিক্ষা ক্ষেত্রে, সাংস্কৃতিক জীবনের নানা পর্যায়ে নারীরা কেন পুরুষের সমান মর্যাদা ভোগ করবেন না। বিপক্ষে কুরআনুল-করীম বা হাদীসে কোন উক্তি নেই। কাজেই জীবনে কোন ক্ষেত্রেই নারীর অধিকারকে ক্ষুণ্ন করা হয়নি। মর্যাদার বেলায় বলা হয়েছে-পুরুষ জাতির নেতৃত্ব রয়েছে নারীর ওপর। এ নেতৃত্ব ব্যাপক অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে। বাস্তবজীবনে পুরুষের পক্ষে জীবনের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে অধিকতর অগ্রণী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে পুরুষদের পক্ষেই নেতৃত্ব গ্রহণ করার রয়েছে সমূহ সম্ভাবনা। এ নেতৃত্বের অর্থ এ নয় যে, পুরুষেরা যা বলবে বা যা করবে তা’কুরআনুল করীম বা হাদীসের বিরুদ্ধে হলেও নারী তা অবনত মস্তকে স্বীকার করবে। আর সোজা অর্থ হচ্ছে শারীরিক দিক দিয়ে পুরুষেরা অধিকতর শক্তিশালী বলে এবং জীবনের চলার পথে পুরুষদের অধিকতর অভিজ্ঞ হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় পুরুষের পক্ষে নেতৃত্ব গ্রহণ করা উচিত। তবে সর্বাবস্থায় সে নেতৃত্ব যেন নাসের (কুরআনুল-করীম ও হাদীসের) বিরুদ্ধে না হয়।
কুরআনুল-করীমের অপর যে আয়াতে নারীদের আপন গৃহে অবস্থার করার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছে, তা এ আধুনিক বিশ্বেও নারীদের প্রতি প্রযোজ্য। জাহিলিয়া বা অন্ধকার যুগে নারীরা রাত্রিতে উচ্ছৃঙ্খলভাবে ঘোরাফেরা করতো এবং তাদের মধ্যে আবার বীরাঙ্গনা পেশারও প্রচলন ছিল। কাজেই মুসলিম মহিলা কেন, যে কোন নারীর পক্ষে তা সর্বক্ষণ পরিত্যাজ্য। এ স্থলে মর্যাদা বা অধিকারের প্রশ্ন তোলা হয়নি। নারীকে উপদেশ দেয়া হয়েছে। নারীদের পক্ষে যেমন সৎ জীবন যাপন করা কর্তব্য- পুরুষদের পক্ষেও তেমনি কর্তব্য। প্রশ্ন হচ্ছে, তা’হলে পুরুষদের উদ্দেশ না করে শুধু নারীদের সম্বোধন করে এ উপদেশ দেয়া হয়েছে কেন? তার উত্তরে বলা যায়-নারী চরিত্রকে যে কোন সমাজে সূচি বা (Index) বলা যায়। সে সমাজের নারী-জীবনে যৌন অভিশাপ দেখা দেয়, সে সমাজে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ধ্বংস হয়। নারী-সমাজে যৌনকাতরতা ব্যাপকভবে দেখা না দিলে, পুরুষ সমাজ সহজে ধ্বংস হয় না। একথা এজ সর্বজনস্বীকৃত যে, যৌন- জীবনের আবেগে পুরুষ যেভাবে অস্থির হয় নারীরা সেভাবে হয় না। তাদের মধ্যে সংযম,ধৈর্য ও সহ্যক্ষমতা অনেক বেশি। যখন নারী-সমাজ থেকে এসব গুণ অন্তর্হিত হয়, তখন নারীরাই অগ্রসর হয়ে পুরুষের সঙ্গ কামনা করে। দুর্বলচিত্ত পুরুষ তাতে অতিসহজেই সাড়া দেয় এবং সমাজজীবনে ব্যভিচারের বন্যাস্রোত হইতে থাকে। এজন্য কেবল সূরা আহযাবের মধ্যে নয়, সূরা ইউসুফের মধ্যেও প্রকারান্তরে নারীদের সাবধান করে দেয়া হয়েছে। হযরত ইউসুফের (আঃ) রূপে মুগ্ধ ইসরাতুল আযীয বা আযীযের স্ত্রী মুসলিম সমাজে জোলায়খা নামে পরিচিত। সে যখন নানাভাবে হযরত ইউসুফকে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করছিল, তখন মিসরের সম্ভ্রান্ত বংশীয়া নারীগণ তাকে ভৎর্সনা করে বলেছিল- ছি, ছি, তুমি এক গোলামের রূপে আসক্ত হয়ে আমাদের অর্থাৎ মিসরের সম্ভ্রান্ত বংশীয় নারীদের অপমান করেছো। ইসরাতুল আযীয তাঁর এ আকর্ষণ যে অনিবার্য তা প্রমাণ করার জন্য চল্লিশজন ভদ্র মহিলাকে দাওয়াত দিয়ে তাদের চল্লিশটি লেবু ও চল্লিশটি মেওয়াতরাশ হাতে দিয়ে লেবুগুলো কেটে খেতে অনুরোধ করেন। সঙ্গে সঙ্গে হযরত ইউসুফকে নাম ধরে ডাকতে থাকেন। তিনি উপস্থিত হলে তাঁর সৌন্দর্য অভিভূত কামার্ত মহিলাগন লেবু না কেটে তাদের হাতের আঙ্গুল কাটতে শুরু করে। এতে প্রত্যক্ষে বলা হয়েছে- “হে মুমিনগণ, সাবধান হও, তোমরা তোমাদের নারীগণকে কামাতুরা হতে দিও না; যদি দাও, তা’হলে মিসরের আযীযের স্ত্রীর সখিগণের মতই তাদের দশা হবে”।
পূর্বেই বলা হয়েছে-নারী-জীবন হচ্ছে সমাজের সূচি। কাজেই তাকে পবিত্র রাখার দায়িত্ব কেবল নারীর নয়, পুরুষেরও। কারণ নারীরা পুরুষেরই মা, ভগ্নি, স্ত্রী ও কন্যা। এভাবে সরাসরি নারীদের উল্লেখ করে সূরা আহযাবে এবং পরোক্ষে সূরা ইউসুফে যে উপদেশ দেয়া হয়েছে- তা সর্বকালের এবং সর্বদেশের নারীদের পালন করা উচিত। এক্ষেত্রে নারীদের সহায়ক হিসেবে পুরুষদের সর্বতোভাবে সাহায্য করা উচিত।
মর্যাদা প্রসঙ্গে হাদীসে যেসব উক্তি রয়েছে, তাতে স্পষ্টই বোঝা যায়, নারীর স্থান পুরুষের ঊর্ধ্বে, মাতার সম্মান পিতার সম্মানের তিনগুণ। এ পৃথিবীর স্রেষ্ঠ সম্পদ হিসেবে ধার্মিক পুরুষকে নয়, ধার্মিক নারীকে গণ্য করা হয়েছে। সে ধার্মিক নারীকে যাতে কোন ধন-দওলতের মোহে আকৃষ্ট না হয়ে পুরুষেরা বিয়ে করে তার জন্য উপদেশ দান করা হয়েছে।
প্রশ্ন হচ্ছে নারীকে এত ঊর্ধ্বে সম্মান দান করা সত্ত্বেও অধিকারের ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয়ে পুরুষের সমান আসন দেয়া হয়নি কেন? তার উত্তরে বলা যায়-নারীর শারীরিক ও মানসিক দিকের প্রতি লক্ষ্য রেখেই তাকে কোন কোন অধিকারের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। পূর্বেই বলা হয়েছে, ইসলামের দৃষ্টিতে এ দুনিয়ার সবকিছুর একমাত্র মালিকানা আল্লাহ্ সুবহানাতা’আলার। মানুষকে তার কাছে গচ্ছিত বিষয়ের ভোগ-দখলের অধিকার দেয়া হয়েছে বটে, তবে সে ভোগ-দখলকে সে যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পারে না। সে ভোগ- দখলের জন্য যে নীতি নির্ধারিত হয়েছে তারই নির্দেশিত পথে তাকে ভোগ করতে হবে। এজন্য মুমিন মুসলিমদের অধীন সম্পদ ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তির মত আল্লাহ্র আইন মুতাবিক পরিচালিত হবে। এ পরিচালনা অত্যন্ত কঠিন কাজ এবং এর দায়িত্ব ততোধিক কঠিন। নারীদের শারীরিক দুর্বলতা এবং সন্তান লালন-পালনে তাদের অধিক দায়িত্ব থাকায় তাদের কোন কোন বিষয়ের দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যেই তাদের হিফাজতকারী বা (Custodian)-এর দায়িত্ব থেকে সরিয়ে রাখা হয়েছে। তবে মর্যাদার দিক থেকে তাদের স্থান পুরুষের ঊর্ধ্বে নির্দেশিত হয়েছে।
ইসলামের দৃষ্টিতে সুদপ্রথা
দুনিয়ার সবকিছুর স্বত্ব-স্বামিত্ব আল্লাহ্র ন্যস্ত করার ফলে যাতে মানুষের পক্ষে মানুষকে পীড়নের কোন সুবিধা না থাকে, তার জন্য রিবা বা সুদ প্রথাকে ইসলাম গোড়াতেই বাতিল করে দিয়েছে। কুরাআনুল-করীমের আল্লাহ্ আদেশ করেছেন, “যারা সুদ খায় তারা টিকে থাকতে পারে না, কেবল সে ব্যক্তির মতই টিকে থাকে, যাকে শয়তান তার স্পর্শ দ্বারা পাগলামিতে ঠেলে দিয়েছে”। (সূরা বাকারা ২:৩৮:২৭৫)
অন্য এক স্থানে সুদের বিরুদ্ধে অভিসম্পাত বর্ষণ করা হয়েছে “আল্লাহ্ সুদকে সমস্ত নিয়ামত থেকে বঞ্চিত করবেন, কিন্তু দান সংক্রান্ত কার্যাবলিকে বিশাল করবেন”। (সূরা বাকারা ১:৩৮:২৭৬)
কুরআনুল করীমের উপরোক্ত বাণীর মধ্যে ‘সে ব্যক্তির মতই টিকে থাকতে পারে-যাকে শয়তান তার স্পর্শ দ্বারা পাগলামিতে ঠেলে দিয়েছে’-বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, মানুষের প্রবৃত্তির মধ্যে প্রেম,স্নেহ, দয়া, মায়া প্রভৃতি উচ্চ পর্যায়ের প্রবৃত্তি। এগুলো অনুশীলন ব্যতীত মানুষের মধ্যে সত্যিকার মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় না। অথচ সুদ গ্রহণ ও সুদ দান দ্বারা মানুষের সেসব প্রবৃত্তির বিকাশে নানাবিধ অন্তরায় দেখা দেয়। মানুষ যখন নানাবিধ বিপদের সম্মুখীন হয় এবং তার পক্ষে তার কাছে রক্ষিত অর্থের দ্বারা তা সংকুলান হয়ে ওঠে না, তখনই সে ধার পাওয়ার জন্য অন্যের দ্বারস্থ হয়। মানুষ হিসেবে আমাদের কর্তব্য হচ্ছে তখন তাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করা। তার এ দুর্বলতার সুযোগে তাকে ধার দিয়ে তা থেকে এক মোটা অংক আদায় করা কোন মানুষের কাজ হতে পারে না। তার একমাত্র কাজ হচ্ছে সে শয়তানের, যে মানুষকে সর্বাবস্থায় বিপথগামী করে। এক্ষেত্রে শয়তানের সে কাজকে সুদখোরকে পাগল করে দেয়া বলা হয়েছে। কারণ, পাগলামি মানুষের সাধারণ বা প্রকৃতিস্থ রূপ নয়। এ হচ্ছে মানুষের এক বিকৃত রূপ। সুদ গ্রহণ করা, এ জন্য বলা হয়েছে এতে মানুষ তার সত্যিকার রূপ সম্পূর্ণভাবে পরিহার করে মাংসাশী প্রাণীর মত অপরের রক্ত মোক্ষণে অগ্রসর হয়। যে মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হচ্ছে মানুষকে ভালবাসা বা তাকে সাহায্য করা, এক্ষেত্রে সে মানুষই তার সে আদিম প্রবৃত্তির সম্পূর্ণভাবে অবমাননা করে তার বিপরীত দিকে ধাবিত হয় এবং রক্তলোলুপ প্রাণীর মত অপর মানুষের রক্ত শোষণ করতে চায়।
আল্লাহ্ মানুষকে ইনসান-ই-কামিল রূপে গড়ে তুলতে চান। সে ইনসান-ই-কামিল হবে মানুষের বন্ধু। কাজেই যে প্রথা দ্বারা মানুষ ইনসানের শত্রুতা করতে অভ্যস্ত হয়, তাকে কোন অবস্থায়ই আল্লাহ্ গ্রহণ করতে পারেন না। বরং সর্বাবস্থায় তাকে পরিহার করার জন্য তাগিদ দেন।
বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতাতে দেখা যায়, সুদখোরের সন্তান-সন্ততির মধ্যে আলস্য ও বিলাসিতা আসে। কোন কাজকর্মে না করে ঘরে বসে বিনা পরিশ্রমে প্রচুর রোজগার হয় বলে সুদখোরের সন্তান-সন্ততি বিলাসী হতে বাধ্য। পরিণামে এসব পরিবার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।
সাম্যবাদমূলক দায়ভাগ প্রথার প্রবর্তন
মালিকানা সম্পূর্ণ আল্লাহ্র বলে স্বীকৃতি লাভ করার পরে এ বিশ্বের সম্পদের সংরক্ষণ এবং সে সম্পদের হস্তান্তর সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় প্রশ্ন দেখা দেয়। এ বিশ্বের সমস্ত সম্পদের মালিক আল্লাহ্ তা’আলা তো বটেনই। তবে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এ সম্পদকে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। সাধারণত রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত না হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সে সম্পদ কোন না কোন ব্যক্তিবিশেষের করায়ত্ত থাকে। সে ব্যক্তির মৃত্যুর পরে, - এ সম্পদের কতটুকু কার দায়িত্বের মধ্যে অর্পিত হবে, সে সম্বন্ধে কুরআনুল করীমের পরিস্কার নির্দেশ রয়েছে।পুরুষ বা নারীর ইন্তেকালের পরে তার পুত্র, কন্যা ও স্বামী বা স্ত্রী সে সম্পদের কত অংশের হিফাজতকারী হবে তাতে কুরআনুল-করীমে নির্দেশ রয়েছে। সে নির্দেশকে সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে দেখা যায়, ইসলামের লক্ষ্য হচ্ছে সমাজের সকল স্তরের মানুষের মধ্যে অর্থের সহজ ও অবাধ গতির পথ প্রশস্তকরণ। অর্থাৎ যাতে এ জগতের ধন-দওলতে, টাকা-কড়ি অতি সহজেই সকল স্তরের লোকের কাছে পৌঁছতে পারে, ইসলামে রয়েছে তারই বিধি ব্যবস্থা অর্থাৎ ইসলাম কোন অবস্থায়ই টাকা-পয়সা কোন ব্যক্তি-বিশেষের হতে সঞ্চিত হয়ে পুঞ্জিতে পরিণত হউক এরূপ কোন ব্যবস্থার প্রশ্রয় দেয় না। একদিকে যেমন ইসলাম অলস মূলধনের (Idle Capital) অস্তিত্ব বরদাশ্ত করে না, তেমনি তাকে সঞ্চিত হওয়ারও কোন সুযোগ দিতে চায় না। এজন্য ইসলামী সমাজের দায়ভাগে সম্পত্তিকে ছোট ছোট ভাগে বণ্টন করার জন্য রয়েছে বিধি ব্যবস্থা।
ইসলামী নীতির রুপায়ণ-রাষ্ট্রীয় জীবনেঃ মদীনার সনদের সারমর্ম
মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর জীবনের অধিক ভাগই দুর্ধর্ষ কুরায়েশ জাতির সঙ্গে নানাবিধ যুদ্ধে অতিবাহিত হয়। কুরায়েশদের বিরোধিতার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় য়াহূদীদের বিশ্বাসঘাতকতা। তা সত্ত্বেও তিনি কোন জাতির বা ধর্মাবলম্বীর কোন মতামতের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেননি। মদীনাতে হিজরত করার পরে তিনি যে রাষ্ট্র গঠন করেন, তাতে ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার সে মর্মবাণীই ফুটে উঠেছে। মদীনা সনদের প্রথম কথাই হল-মদীনার য়াহূদী, পৌত্তলিক ও মুসলমান সকলেই এক দেশবাসী। য়াহূদী, পৌত্তলিক এবং মুসলমান সকলেই নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে, কেউ কারো ধর্মে হস্তক্ষেপ করবে না। এ ক্ষেত্রে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য বিষয় হচ্ছে এই- সে রাষ্ট্রে মুসলিমেরা সংখাগরিষ্ঠ হলেও সংখ্যালঘু য়াহূদী ও পৌত্তলিকদের নামই প্রথমে বলা হয়েছে। এতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়- তখনকার নানাবিধ অত্যাচার ও অনাচারের যুগে ইসলামী সমাজে বা রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুকে যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করা হত। দ্বিতীয়ত, সেই সনদে সংখ্যাগুরু সমাজের নেতা আল্লাহ্র রসূল (সঃ)-এর নির্দেশ পালন করার জন্য সংখ্যা
লঘু সমাজের লোকেরা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অর্থাৎ গণতন্ত্রকে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করা হয়েছে। যদি য়াহূদী বা পৌত্তলিকেরা সংখ্যাগুরু হত তা হলে তাদের নেতার আদেশে সংখ্যালঘু মুসলিমদের পরিচালিত হওয়ার প্রতিশ্রুতি থাকতো। তবে যেহেতু মুসলিমেরাই সংখ্যাগুরু ছিল, এজন্য মুসলিমদের সর্বসম্মত জননেতা-হযরত রসূলই-আকরমের (সঃ) নেতৃত্বই স্বীকার করে নেয়া হয়েছিল। তবে যাতে কোন অবস্থায়ই বর্তমান কালের তথাকথিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অর্থের দওলতে নানাবিধ দুর্নীতির সৃষ্টি না হয়- সে দিকে ইসলামী রাষ্ট্রে প্রখন দৃষ্টি ছিল। ইসলামী রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের মধ্যে যাতে কোনকালে অর্থের দ্বারা কোন সুযোগ-সুবিধা আদায় করা না হয়, এজন্য খলীফা পদ প্রার্থীকে সাচ্চা মুসলিম হতে হবে। অর্থের প্রাধান্যের জন্য বর্তমান কালের গণতন্ত্রের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে-তা’ সত্যিই অসংস্কৃতব্য । মুখে গণতন্রের নামে নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়ে, অর্থের জোরে নরপিশাচ শ্রেণীর মানুষেরাও সফলতা লাভ করে। এতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা থেকে যে সার্বভৌমত্বের সৃষ্টি হয়, তার সঙ্গে অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্বের ভীষণ দ্বন্দ্ব দেখা দেয় বলে এ গনতন্ত্রকে অধ্যাপক হ্যারল্ড লাস্কি তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছেন। অথচ বর্তমান কালের গনতন্রে এ দ্বন্দ্ব সর্বত্রই বর্তমান। এ গণতন্রের নির্বাচন প্রার্থীর চরিত্রকে বিচার করা হয় না, তার জনপ্রিয়তাকেই বিচার করা হয় বলে নিতান্ত চরিত্রহীন লোকের পক্ষেও নির্বাচিত হওয়ার সমূহ সুযোগ থাকে। ইসলামী গণতন্ত্রে নির্বাচন প্রার্থী লোকের ব্যক্তিগত জীবনযাত্রা প্রণালি, ইসলামের রীতিনীতির সঙ্গে তার যোগ প্রভৃতি বিষয় বিচার করা হয় বলে এ দ্বন্দ্ব দেখা দেয় না।
কাজেই দেখা যায়, ইসলামী রাষ্ট্রে রয়েছে একদিকে ব্যক্তিস্বাধীনতা। যে ব্যক্তি-স্বাধীনতার জন্য এ যুগে এত হৈ চৈ শোনা যায়-চৌদ্দশত বৎসর পূর্বেই মানুষের নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সে স্বাধীনতার চার্টার জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলেই দান করেছেন। অপরদিকে এ গণতন্রে অর্থের মাধ্যমে যাতে কোন দুর্নীতি প্রশ্রয় না পায়- তার জন্য এ গণতন্ত্রের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রকদের চরিত্র সম্বন্ধেও গুরুত্ব আরোপ করা হয়।
পুঁজি সৃষ্টির বিরুদ্ধে অর্ডিন্যান্স
ইসলামী নীতি অনুসারে জীবন যাপন করলে কোন অবস্থায়ই মানুষের হাতে পুঁজি সৃষ্টি হতে পারে না। যাকাত ব্যতীতও নানাবিধ দান সবসময়ই ধনী ব্যক্তিকে করতে হবে। জবিল কুরবা, ইয়াতামা, মাসাকিনা ও ইবলে সবিল অর্থাৎ পিতৃমাতৃকুলের আত্মীয়-স্বজন,অনাথ, পিতৃমাতৃহীন ছেলেমেয়ে, বিত্তহারা ও সহায়-সম্বলহীন পথিকের দাবি রয়েছে ধনীর মালের ওপর। কুরআনে শরীফে এদের প্রাপ্য প্রদান করার জন্য রয়েছে জেদ তাগিদ। কেবল কুরআন শরিফেই নয়, হাদীস শরীফেও দানের মাহাত্ম্য ঘোষণা করা হয়েছে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন-
“ আল্লাহ্র রসূল (সঃ) বলেছেন, “কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ জিজ্ঞেস করবেন, ‘হে বনি আদম, আমি পীড়িত ছিলাম কিন্তু তুমি আমায় দেখো নি’। সে উত্তর করবে, ‘ হে আমার প্রভু, আমি তোমাকে কিভাবে দেখবো, তুমি যে নিখিল বিশ্বের প্রভু?’ তিনি (আল্লাহ্) বলবেন, ‘তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা পীড়িত ছিল, কিন্তু তুমি তাকে দেখো নি, তুমি কি জানতে না যে, যদি তুমি তাকে দেখতে ( শুস্রষা করতে) তাহলে তার মাঝেই আমাকে পেতে? হে বনি আদম! আমি তোমার কাছে আহার চেয়েছিলাম কিন্তু তুমি আমার আহার দাও নি’। সে উত্তর দেবে, ‘হে আমার প্রভু, আমি তোমাকে কিভাবে খেতে দিতে পারতাম- যেহেতু তুমি সমস্ত ভুবনের প্রভু?’ তিনি (আল্লাহ্) বলবেন, ‘তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে চাওয়া সত্ত্বেও তুমি তাকে খেতে দাওনি-তুমি কি জানতে না যদি তুমি তাকে খেতে দিতে তাহলে আমাকেই খেতে দিতে?’* (Al-Muslim….Al-Hadis,Sec.p,35,273 Maulana Fazlul Karim.)
এতসব আইন-কানুন থাকা সত্ত্বেও যদি মানুষের মধ্যে অযথা সঞ্চয় করার প্রবৃত্তি জেগে ওঠে তাহলে প্রয়োজনবোধে খলীফা বা আমির ধনীদিগকে দরিদ্রের দায়িত্ব গ্রহণে বাধ্য করতে পারেন। ইবনে হাজম এ অর্ডিন্যান্সের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, “প্রত্যেক মহল্লার ধনীদের ওপর গরীব-দুঃখীদের জীবিকার জন্য দায়ী (জামিন) হওয়া ফরয (অবশ্য কর্তব্য)। যদি বায়তুলমালের আমদানি ঐ গরিবদের জীবিকার পক্ষে যথেষ্ট না হয়, তাহলে শাসক বা আমির ধনীদের এ কাজের জন্য বাধ্য করতে পারেন। অর্থাৎ তাদের অতিরিক্ত মাল বলপূর্বক গরিবদের প্রয়োজনে খরচ করতে পারেন। তাদের জীবিকার সংস্থানের জন্য আবশ্যক-ক্ষুধার অন্ন, পরিধানের বস্ত্র এবং ঝড়-বৃষ্টি, গরম রোদ ও প্লাবন থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে এমন বাসগৃহ’।* (মুহাল্লাঃ ৬ষ্ঠ খন্ড,পৃ,১৫৬;মিসলাঃপৃ,৭২৫,মওলানা হিফজুর রহমানঃ ‘ইসলাম কা ইক্ তেসাদি নিজাম’ থেকে গৃহীত।)
ইসলামী গনতন্রের ফলিত রূপ
হযরত রসূল আকরম (সঃ)-এর জীবিতকালে এবং পরবর্তী সময়ে সে আদর্শ রাষ্ট্রে স্বাধীনতা যে চরম বিকাশ লাভ করেছিল, তার নিদর্শনস্বরূপ বহু ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রসঙ্গত মাত্র দুটি ঘটনার উল্লেখ করা হচ্ছে। ইসলামী গণতন্রের স্বরূপ বর্ণনা করতে যেয়ে দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রাঃ)এক জনসভায় বক্তৃতায় বলেছিলেনঃ
“ আমি আপনাদের একজন খাদিম মাত্র। আমার কাছ থেকে আপনাদের সর্বপ্রকার মঙ্গলজনক কাজ আদায় করার পূর্ণ অধিকার রয়েছে”।
হযরত উমর (রাঃ)আর একদিন জনসভায় বক্তৃতাকালে শ্রোতৃমন্ডলীর মধ্য থেকে হটাৎ এক ব্যক্তি বলে উঠলো, “ হে উমর,আল্লাহ্কে ভয় করো”। সমবেত জনতা চাইলো তাকে থামিয়ে দিতে কিন্তু হযরত উমর (রাঃ) বললেন, “না, না, একে নিজের মতামত ব্যক্ত করতে দিন। নিজের মতামত ব্যক্ত না করলে ইসলাম প্রদত্ত স্বাধীনতা ভোগ ও সাম্যের সম্মান আপনারা কি প্রকারে করবেন? ইসলাম জননেতা ও জনগণের মধ্যে কোন ইতর-বিশেষ করেনি। শুধু পার্থক্য এই যে,জননেতার দায়িত্ব অধিক। সকলেরই সম্মতি ও আপত্তিতে কর্ণপাত করা রাষ্ট্রনেতা হিসেবে আমার কর্তব্য”।** (বিপ্লবী উমরঃ সম্পাদক-আবদুল গফুর।)
সে ব্যক্তি-স্বাধীনতা যাতে স্বেচ্ছাচার ও জুলুমে পরিণত না হয় তার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেই মুসলিম রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল। সে আদর্শ সাম্যবাদে আমির-ফকিরে কোন পার্থক্য ছিল না।
খলীফার দায়িত্ব
সাধারণের অর্থ খলীফার তত্ত্বাবধানে থাকলেও তা থেকে যথেচ্ছ ব্যয় করার অধিকার খলীফার ছিল না। কোন কোন ক্ষেত্রে এরূপ সন্দেহের উদ্রেক হলে জনসাধারণের পক্ষে প্রকাশ্যে খলীফার সমালোচনা করার অধিকার ছিল। তাকে impeach করতে হলে অপসারণের প্রয়োজন হ’ত না। এর উদাহরণ রয়েছে ইসলামের স্বর্ণযুগের ইতিহাসে। খলীফা উসমানের (রাঃ) খিলাফতের সময় কয়েকজন দুষ্ট প্রকৃতির লোক তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করলে তিনি মুসলিমদের এক সাধারণ সভা আহ্বান করে তাঁর ওপর আরোপিত অভিযোগ খণ্ডনের উদ্দেশ্যে বলেনঃ
“ আল্লাহ্র নামে শপথ নিয়ে বলছি- আমি কোন শহরের উপর তার সাধ্যাতীত কর ধার্য করিনি, কাজেই আমার বিরুদ্ধে আনীত এ অভিযোগ নিছক মিথ্যা। আমি সর্বসাধারণের থেকে যা গ্রহণ করছি তাদেরই হিতের জন্যই ব্যয় করছি। যে লভ্যাংশের এক-পঞ্চমাংশ আমার নিকট এসেছে তাও আমার ব্যক্তিগত ভোগের জন্য ব্যয় করা আইনসঙ্গত নয়। তাই তার সমস্তই মুসলিমরা ব্যয় করেছে- আমি করিনি। সাধারণ ধনাগারের এক কপর্দকও তসরুফ করা হয়নি, আমি তা থেকে একটি পয়সাও নিইনি। আমি আমার নিজের উপার্জনের ওপর নির্ভর করেই জীবিকা নির্বাহ করি”।
তারপর তিনি আরও বলেন- “তোমরা জানো, খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পূর্বে আরব দেশে আমি ছিলাম উট ও ছাগীর সবচেয়ে বড় মালিক। খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর দু’টো উট ব্যতীত আমার আর কোন পশু নেই। সেগুলোও আমি হজ্জের সময় মক্কায় যাওয়ার জন্য ব্যবহার করি”।
ইসলাম ও ডিক্টেটরশিপ
হযরত রসূলে করীম (সঃ)-এর ইন্তেকালের পর তাঁরই আদর্শের অনুসরণে গণতান্ত্রিক ভিত্তিতেই রাষ্ট্র গঠিত হয়। নবনির্বাচিত খলীফা হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর ঘোষণাতে ন্যায়-বিচার ও খলীফার ক্ষমতা প্রয়োগের একটা স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায়। তিনি তাঁর নির্বাচনের পরে সমবেত জনতার উদ্দেশে বলেনঃ “সঙ্গীগণ, আমি তোমাদের খলীফা নির্বাচিত হয়েছি। আমি তোমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে দাবি করি না। তোমাদের মধ্যে যারা সবচেয়ে শক্তিশালী তাকেই আমি দুর্বলতম মনে করব- যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে দখলকৃত (দুর্বলদের) সামান্যতম অধিকারকে আমি ফিরিয়ে আনতে পারি এবং যারা তোমাদের মধ্যে দুর্বলতম- তারাই আমার কাছে সবলতম- যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তাদের অধিকারকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করি। ভাইগণ, আমাকে তোমাদের মতই আল্লাহ্র আইন মেনে চলতে হবে এবং আমি তোমাদের ওপর কোন নতুন আইন চাপাতে পারবো না। আমি তোমাদের উপদেশ ও সাহায্য চাই। যদি সৎপথে চলি, তোমরা আমার সহায়তা করবে, যদি ভুলপথে চলি তাহলে আমাকে সংশোধন করবে”।
কাজেই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, খলীফার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল দুনিয়ার ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা কর। জনগণের দ্বারা নির্বাচিত খলীফা কোনদিনই জনমতকে উপেক্ষা করেননি। মানুষ হিসেবে তাঁদের ভুল-ভ্রান্তি সম্বন্ধে তাঁরা ছিলেন সততই সজাগ। ইসলামের উজ্জ্বল রত্ন খলীফা উমর (রাঃ) একদিন এক সাধারণ সভায় আদেশ করেছিলেন-মোহরানা যেন বেশি নেওয়া না হয়। তাঁর কথা শোনামাত্রই এক বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে কুরআন শরীফের এক আয়াতের উল্লেখ করে দেখিয়ে দেন যে, কুরআনে মোহরানার পরিমাণ নির্দিষ্ট করা হয়নি। খলীফা অম্লানে তাঁর ভুল স্বীকার করেন।
কাজেই দেখা যাচ্ছে, বর্তমান যুগের রাষ্ট্র পরিচালকদের চরিত্রের সঙ্গে খলীফাদের চরিত্রের কোন তুলনাই চলে না। তাঁরা সবসময়েই নিজেদের সাধারণ মানুষ বলেই মনে করতেন-দুনিয়ার সব ত্রুটি-বিচ্যুতির উর্ধ্বে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত ‘অতিমানব’ বলে তাঁরা নিজেদের কোনদিন ভাবতে পারতেন না।
সংখ্যালঘু সমস্যা
দুনিয়ার সকল দেশে সকল যুগেই সংখ্যালঘু সমস্যা ছিল ও রয়েছে। আধুনিককালে গণতন্ত্রমূলক রাষ্ট্র গঠিত হলেও তাতে সংখ্যালঘু একদল লোক থেকে যায় যারা বিরোধী দল নামে পরিচিত। ইসলামী রাষ্ট্রে চার্চ ও পার্লিয়ামেন্টের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই বলে এ রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুদের দুদিক থেকে দেখা যেতে পারে। সংখ্যালঘু বলতে রাষ্ট্রের অধিকাংশ লোকদের মতাবলম্বী নয় এমন একদল লোককে যেমন বোঝা যায়- তেমনি অন্য ধর্মাবলম্বী লোককেও বোঝা যায়। ইসলামী রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুর স্থান কোথায়, তা-ই আমাদের বিবেচ্য। ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলিমদের মধ্যে সংখ্যালঘু বলে কেউ থাকতে পারে না। কারণ, মুসলিমেরা সকলেই ইসলাম ধর্মাবলম্বী বলে ইসলামেরই অনুসারী ও ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের রুপায়ণে এক মতাবলম্বী হতে বাধ্য। ভিন্ন ধর্মের লোকদের ইসলামী রাষ্ট্রে বলা হয় যিম্মি। তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি অক্ষুণ্ন রাখতে ইসলামী রাষ্ট্র সর্বতোভাবে বাধ্য। এজন্যই ইসলামের শাসন বিধান অনুসারে ইসলামী রাষ্ট্রে এমন কোন আইন গৃহীত হতে পারে না- যা যিম্মির সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতিকূল। তাই আধুনিক গণতন্ত্রের চেয়ে এক্ষেত্রে ইসলামী নীতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। কারণ, আধুনিক গনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যে কোন আইন জনমতের জোরে গৃহীত হয়ে যেতে পারে, যা সম্পূর্ণই সংখ্যালঘুর সংস্কৃতির প্রতিকূল। কাজেই শুধু ‘যিম্মি’ শব্দ শুনেই যাঁরা অস্থির হয়ে পড়েন তাঁদের প্রবোধের জন্য বলা যেতে পারে যিম্মি অর্থ রক্ষিত নয়- তার অর্থ ইসলামী শাসন বিধানে যাতে কোন অনিষ্ট বা অমঙ্গল না হয় তার জন্য রক্ষাকবচের ব্যবস্থা।
যিম্মি সম্বন্ধে হযরত আলীর উক্তি রয়েছে- যিম্মির রক্ত আমারই রক্ত। ইসলামী রাষ্ট্রে যিম্মির মুসলিমদের মত সমান অধিকার রয়েছে। প্রশ্ন ওঠে সংখ্যালঘু ভিন্ন ধর্মাবলম্বী কোন ব্যক্তি বা ভিন্ন মতাবলম্বী হয়েও ইসলামী রাষ্ট্রের আদর্শে বিশ্বাসী হতে পারে কিনা। এরূপ ক্ষেত্রে শাসন ব্যবস্থায় মুসলমানদের মত তার সমান অধিকার থাকতে পারে কিনা। তার উত্তরে বলা যায়, ইসলাম অবিভাজ্য মতবাদ বলে ধরে নেয়া হয়-ইসলামের আংশিক দিককে গ্রহণ করে ইসলামী শাসন ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ চালু করা কারো পক্ষে সহজ নয়। আল্লাহ্র ওয়াহদানীয়ত ও সার্বভৌমত্বের ওপর ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। সে মৌলিক ভিত্তিকে অস্বীকার করে কোন ব্যক্তির পক্ষে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা চালু করা অসম্ভব। তাই ভিন্ন ধর্মাবলম্বী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তিকে ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনা করার ভার ইসলামী সমাজে দেয়া হয়নি। তবে এতে সংখ্যালঘু ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর পক্ষে অসুবিধার বিশেষ কারণ আছে বলে মনে হয় না। কারণ, রাষ্ট্রের পরিচালনা খুব সুখের বিষয় নয় এবং কোন রাষ্ট্রে বাস করে তার সকল অধিকার ভোগ করে কেবল রাষ্ট্র পরিচালনার অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে তাতে ব্যক্তিবিশেষের কোন ক্ষোভের কারণ থাকতে পারে না। আধুনিক কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রগুলোতে কমিউনিষ্ট ব্যতীত অন্য কাউকে নির্বিঘ্নে বাস করতে দেয়া হয় না- পরিচালনা তো দূরের কথা।
খলীফার নিয়োগ
আল্লাহ্র রসূল (সঃ)-এর পরে আল্লাহ্র রাষ্ট্রে তাঁর প্রতিনিধির নিয়োগে কখনও বা নির্বাচন, কখনও – মনোনয়ন, কখনও বা নির্বাচনের জন্য প্যানেল মনোনয়ন করা হয়েছে। মুসলিমেরা প্রত্যেকেই আল্লাহ্র প্রতিনিধি বলে তাদের প্রত্যেকেরই আল্লাহ্র প্রতিনিধি নির্বাচন করার অধিকার রয়েছে। দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারুকের নির্দেশ থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় সর্বসাধারণ মুসলিমদের নির্বাচন হবে আল্লাহ্র রসূল (সঃ)-এর প্রতিনিধি বা খলীফা নির্বাচনের ভিত্তি। তিনি আদেশ করেছিলেন-
“ সর্বসাধারণ মুসলিমের সম্মতি ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি যদি কারো প্রভুত্ব স্বীকার করে তাহলে যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চায় এবং যে আনুগত্য স্বীকার করে তাদের দুজনেরই মৃত্যুদন্ড হওয়া উচিত* (Shaik Mushir Hussain Kidwai-Pan Islamism & Bolshevism p 212-13)- তবে এক্ষেত্রেও ইসলামী গণতন্রের সঙ্গে আধুনিক গণতন্ত্রের পার্থক্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আধুনিক গণতন্ত্রের ভিত্তি হচ্ছে প্রার্থীর জনপ্রিয়তা, কোন ব্যবস্থাপক সভা অথবা পরিষদে নির্বাচিত হতে হলে প্রার্থীর পক্ষে অধিক সংখ্যক ভোট সংগ্রহ করা প্রয়োজনীয়। প্রার্থীর জনপ্রিয়তার সঙ্গে তার ব্যক্তিগত চরিত্রের কোন যোগ নেই। তার নির্বাচকমন্ডলীর লোকদের সে যে কোনভাবেই সন্তুষ্ট করেই জনপ্রিয় হতে পারে। সে হয়ত টাকা পয়সা ঘুষ দিয়ে অথবা নানাবিধ বিলাসের সামগ্রী সরবরাহ করে জনপ্রিয় হতে পারে। ইসলামী গণতন্ত্রে এরূপ লোকের কোন স্থান হতে পারে না। যাকে শর্তবিহীন অবাধ গণতন্ত্র বলে বর্তমানে সম্মান প্রদর্শন করা হয়, তাকে সুবিখ্যাত রাষ্ট্রনীতিবিদ হ্যারলড লাস্কি ঠাট্টা করে বলেছেন- এটা দ্বন্দ্বসংকুল গণতন্ত্র। এতে একদিকে সংখ্যার সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অর্থের সার্বভৌমত্বও স্বীকার করে নেওয়া হয়। এ গণতন্ত্রে সকল মানুষের সমান অধিকার স্বীকার করা হলেও কার্যক্ষেত্রে ধনীরা তাদের অর্থের মাধ্যমে গরিবদের কাছ থেকে অতি সহজে তার ভোট কিনে নিতে পারে। কাজেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা এ গণতন্রের মূলভিত্তি হলেও সংখ্যালঘু ধনীদের দ্বারা তা নিয়ন্ত্রিত হয়। ইসলামী সমাজে এজন্য প্রার্থীর চরিত্রের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ইসলাম ধর্মের বিপরীত যে কোন কাজকর্মে লিপ্ত ব্যক্তি ইসলামী রাষ্ট্রের খলীফা পদের যেমন প্রার্থী হতে পারে না, তেমনি জনসাধারণও এরূপ ব্যক্তিকে ভোটদান করতে পারে না। ইসলামী গণতন্ত্রে মূল লক্ষ্য হচ্ছে-এ বিশ্বে আল্লাহ্র শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। এজন্য যে ব্যক্তি আল্লাহ্র শাসন কামনা করে না অথবা আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ মানতে চায় না, সে ব্যক্তি আল্লাহ্র খলীফা নির্বাচিত হতে পারে না।
ইসলামী জীবনধারার বিপরীতমুখী জীবন যাপন করাতে অভ্যস্ত ব্যক্তির খলীফাপদে নিয়োগের প্রতিবাদ করার ফলেই কারবালা প্রান্তরে সে হৃদয়বিদারক ও মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে।
হযরত মু’আবিয়া তারই জীবনকালে তার পুত্র ইয়াযিদকে ইসলামী জগতের খলীফা মনোনীত করার প্রতিবাদকল্পেই শহীদরাজ হাসান, হোসেন কারবার প্রান্তরে এবং আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়র মক্কাতে শাহাদাত বরণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে উমাইয়াদের শাসনকালে খলীফার পদে বংশানুক্রমিক হয়ে পড়লেও সে বংশেরই অতি ন্যায়বান ও পরম সত্যবাদী হযরত উমর ইবেনে আবদুল আযীয খানদানী সূত্রে খলীফার পদ লাভ করেও তাতে ইস্তফা দিয়ে জনগণের মত পরিক্ষা করে নিয়েছিলেন। সর্বসাধারণ মুসলিম একবাক্যে তাঁর নিয়োগ সমর্থন করার পরে তিনি সে দায়িত্ব গ্রহণ করতে সম্মত হন। তবে তিনি দীর্ঘকাল তাঁর এ পদে টিকে থাকতে পারেন নি। তাঁরই বংশের লোকদের মত প্রচলিত নানাবিধ দুষ্কর্মের উচ্ছেদ করতে যেয়ে তিনি তাদের কারসাজির ফলে নিহত হন।
তারপরে মুসলিম সমাজে ইসলামী গণতন্ত্রে যে ছায়াটুকু মাত্র অবশিষ্ট থাকে তা’ সত্যিকার ঈমানদার কেন, অন্য মানুষের কাছেও হাস্যাস্পদ। তথাকথিত খলীফাগণ উত্তরাধিকারসূত্রে খিলাফত লাভ করে মুসলিম জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে তাদের কাছ থেকে পদপ্রাপ্তির পরে বায়’আত গ্রহণ করতেন। উমাইয়া ও আব্বাসীয় উভয় পক্ষের মধ্যে এ আচরণ প্রচলিত ছিল।
অর্থনীতি
এ রাষ্ট্রের অর্থনীতি পরিচালিত হয় সর্বসাধারণের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে। যুদ্ধলব্ধ বিত্ত (আল-গনীমাহ), যাকাত, সাদাকা, জিযিয়া, খিরাজ, আল-ফায়, আল-উশর প্রভৃতি বিভিন্ন কর ধার্য করে এ রাষ্ট্রের আর্থিক সৌধ গড়ে তুললেও পরিবর্তিত অবস্থায় সেগুলোর পরিবর্তনও স্বীকার করে নেওয়া হয়।
হযরত উমর (রাঃ)-এর লক্ষ্য ছিল রাষ্ট্রের সমস্ত মুসলিম অধিবাসীকে রাষ্ট্রের অঙ্গ জ্ঞান করে রাষ্ট্রগতপ্রাণ করে তোলা। সে জন্য তিনি তাদের প্রত্যেকের বৃত্তি নির্ধারণ করেছিলেন এবং যাতে করে তারা জীবিকার সংস্থানের জন্য অন্য কোন কাজে লিপ্ত না হয় তার প্রতি কড়া দৃষ্টি রাখতেন। তাঁর খিলাফতের সময় কোন অমুসলিম মুসলমান হয়ে গেলে তার সম্পত্তি দেশের লোকের মধ্যে বেঁটে দেয়া হতো।
এ রাষ্ট্রে যাতে কোন অবস্থায় কোন লোকের হাতে পুঁজি সঞ্চিত না হয় সেজন্য আদেশ করা হয়েছেঃ
“ এবং যারা সোনারূপা সঞ্চয় করে, আল্লাহ্র পথে (মানবতার কল্যাণের জন্য) ব্যয় করে না-তাদের নিকট এক কষ্টদায়ক শাস্তি ঘোষণা করে দাও”। (সূরা তওবা, আয়াত ৩৪)
এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রসূল আকরাম (সঃ) যা বলেছেন, সাহাবী আবু হুরায়রা (রাঃ) তা’ বর্ণনা করে বলেন, “রোজ কিয়ামতে এ সকল লোকদের পার্শ্বদেশ, কপাল ও পিঠে দাগ দেয়া হবে”।
উমাইয়াদের আধিপত্য বিস্তারের সূচনায় এবং সিরিয়াতে মু’আবিয়া গভর্নর থাকাকালে এ আয়াতের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করে হযরতের প্রিয় সাহাবী হযরত আবু যর গিফারী* (রাঃ)(ইতিহাসে উপেক্ষিত একটি চরিত্রঃ মুহাম্মদ আজরফ ও এ. জেড. এম. শামসুল আলম) বিপ্লবের সূচনা করেন। তাঁর সুদৃঢ় অভিমত ছিল, প্রয়োজনে অতিরিক্ত কোন বিত্তই কেউ রাখতে পারে না।
সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইবনে হাজম জাহেরী ‘মুহাল্লা’য় উল্লেখ করেছেন- হযরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেছেনঃ আল্লাহ্র রসূল বলেছেন, যে ব্যক্তির কাছে শক্তি ও সামর্থ্যের সরঞ্জাম নিজ আবশ্যকের অতিরিক্ত রয়েছে তার উচিত-ঐ অতিরিক্ত সামান-সরঞ্জাম দুর্বলকে দান করা। যে ব্যক্তির কাছে খাওয়া-পরার অতিরিক্ত উপাদান রয়েছে তার পক্ষে উচিত-অতিরিক্ত সামান দীন-দুঃখীকে দান করা”। আবু সাঈদ খুদরী আরও বলেছেন, “নবী করীম (সঃ) এভাবে নানা প্রকারের উল্লেখ করেছেন তাতে আমার এরূপ ধারণা জন্মেছে যে, আমাদের মধ্যে কারো কোন প্রকারের মালের দাবি থাকতে পারে না।
হযরত রসূল করীম (সঃ)- এর প্রধান সাহাবী ও ঘনিষ্ঠতম আত্মীয় হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, ‘আল্লাহ্ তা’আলা ধনীদের ওপর গরিবদের আবশ্যকীয় জীবিকা পরিপূর্নভাবে সরবরাহ করা ফরয করেছেন। যদি তারা (গরিবেরা) ভুখা, নগ্ন থাকে অথবা জীবিকার জন্য বিপদগ্রস্ত হয় তাহলে ধনীরা দায়িত্বশীল নয় বলেই বুঝতে হবে- এজন্য আল্লাহ্র কাছে তাদের কিয়ামতের দিন জবাবদিহি হতে হবে এবং সংকীর্ণতার জন্য শাস্তি ভোগ করতে হবে। এবং বিধ আরও হাদীস ও কুরআনের দলীলের দ্বারা মুহাদ্দিস ইবনে হাজম এ বিষয় ব্যাখ্যা করে বলেছেন-
“প্রত্যেক মহল্লার ধনীদের ওপর গরিব-দুঃখীদের জীবিকার জন্য দায়ী (জামিন) হওয়া ফরয (অবশ্য কর্তব্য) । যদি বায়তুলমালের আমদানি ঐ গরিবদের জীবিকার সরবরাহের জন্য যথেষ্ট না হয়, তাহলে শাসক বা আমীর ধনীদিগকে এ কাজের জন্য বাধ্য করতে পারেন অর্থাৎ তাদের মাল বলপূর্বক গরিবদের প্রয়োজনে খরচ করতে পারেন-তাদের জীবিকার সংস্থানের জন্য কমপক্ষে অত্যাবশ্যক প্রয়োজন অনুযায়ী ক্ষুধার অন্ন, পরিধানের বস্ত্র এবং ঝড়বৃষ্টি, গরম-রোদ ও প্লাবন থেকে রক্ষা করতে পারে এমন বাসগৃহ”।
এ রাষ্ট্রে তাহলে বিত্ত সঞ্চয় বা শোষণের কোন অবকাশই থাকতে পারে না। রাষ্ট্র ও জনসাধারণের মধ্যবর্তী কোন বিশেষ প্রাণীও রাষ্ট্রে থাকতে পারে না। ইরাক ও সিরিয়া বিজিত হওয়ার পর সাহাবীদের শত অনুনয়-বিনয় সত্ত্বেও হযরত উমর ফারুক (রাঃ) তাদের জায়গীর দান করেননি বরং সমস্ত ভূমি সরকারের অধীনে রেখে তার আয় সকল অধিবাসীর প্রয়োজন ও আবশ্যকাদির জন্য ওয়াকফ গণ্য করেছেন।
এমনকি, প্রয়োজনে অতিরিক্ত ভূমি যাতে কোন জোতদারের হাতে না থাকে তার জন্য হযরত বিলাল (রাঃ)-এর জায়গীর থেকেও অতিরিক্ত জমি ছিনিয়ে নিয়ে হযরত উমর ফারুক (রাঃ) চাষীদের মধ্যে বেঁটে দিয়েছেন।
কাজেই ব্যক্তি-স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রেখে যাতে সর্ববস্থায় সমান অংশে দুনিয়ার সম্পদ মানুষ ভোগ করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই মানবসমাজে সংঘ-চেতনার পথে এগিয়ে দেয়া হয়েছে।
উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা
অর্থনীতির সঙ্গে উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থার গূঢ় সম্বন্ধ বর্তমান। উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যষ্টির একাধিপত্য স্বীকৃত হলে বন্টনের ব্যাপারে তার আধিপত্যের নীতি স্বীকার করে নিতে হয়। সকল যুগেই দেখা যায়, মানুষ একাকী উৎপাদনে কোনদিনই সক্ষম হয়নি । অথচ বন্টনের ব্যাপারে উৎপাদনকারী তার যথেচ্ছ স্বাধীনতা প্রয়োগ করতে চায়। আধুনিক জগতে তাই দেখা দিয়েছে এক মহাদ্বন্দ্ব।
ইসলাম উৎপাদনের ব্যাপারে কোন বিধি-নিষেধ আরোপ করেনি। মানুষ ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে উৎপাদন করতে পারে, তবে বন্টনের ব্যাপারে সব সময়েই তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত সবকিছু সমাজের অথবা রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য ব্যয় করতে সে বাধ্য। এ নীতি ইসলামের জীবনদর্শন থেকেই পাওয়া যায়। কারণ, ইসলামী দর্শনে আসমান জমিনের সবকিছুরই মালিদ খোদ আল্লাহ্ তা’আলা। মানুষ তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে যেমন উৎপাদন করবে,তেমনি তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর নিয়ামত সকল মানুষ সমান অংশে ভোগ করবে। আধুনিক জগতের উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার অসামঞ্জস্য তাই ইসলামে দেখা দিতে পারে না। * (আধুনিক যুগের মত তখন শিল্প এতটা বিস্তৃত হয়নি। তবুও যাতে উৎপাদন ব্যবস্থায় সমষ্টির দায়িত্ব ও কতৃত্ব অব্যাহত থাকে তার নজিরস্বরূপ হযরত রসূলে আকরাম (সঃ)-এর এক সহীহ্ হাদীদ পাওয়া যায়। ইসলামের ইতিহাসের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁআরা জানেন, মদীনায় হিজরতের পরে মুহাজিরগণ আনসারদের কাছ থেকে আশাতিরিক্ত সাহায্য ও সহানুভূতি লাভে সমর্থ হন। আনসারদের প্রত্যেকেই তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি মুহাজিরগণের সঙ্গে ভাগ করে ভোগ করতে প্রস্তুত হন। ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলতে তাদের খেজুর গাছের ফল,উট, দুম্বা ও জমিজিরাতই বোঝাত। কোন এক আনসার রসূলে আকরাম (সঃ)-কে খেজুর গাছগুলো তাদের ও আনসারদের মধ্যে ভাগ করে নিতে অনুরোধ করলে তিনি বলেন, “আমরা যে এর উপস্বত্ব ভোগ করছি তাই যথেষ্ট এবং তোমাদের দান এ ফলের সঙ্গে তোমাদের (সহানুভূতিও) আমরা পাচ্ছি”। তারা তাঁর এ আদেশ শিরোধার্য করে। এতে সুস্পষ্ট বোঝা যায়, ভ্রাতৃত্ববোধ অক্ষুণ্ন রাখার জন্য সমষ্টিগত উৎপাদন ব্যবস্থাই রসূলে আকরম (সঃ) প্রকৃষ্ট পন্থা বলে মনে করতেন। -Al-Hadis-BK 11 P 306-Fazlul Karim)
শাসন ও বিচার বিভাগ
অতি আধুনিক কালে শাসন বিভাগকে বিচার বিভাগ থেকে পৃথক করার জন্য প্রায় সকল দেশেই আন্দোলন দেখা দিয়েছে। একই ব্যক্তির হাতে শাসন ও বিচারের ক্ষমতা থাকলে তার হাতে সুবিচারের প্রত্যাশা কিছুতেই করা যায় না। কোন ব্যক্তির কোন দেশের বা জেলার শাসনকর্তার কোপে পতিত হলে সে শাসনকর্তা থেকে সে কোনমতেই সুবিচারের আশা করতে পারে না। এজন্য শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ সকল দেশেই একান্ত কাম্য হয়ে দেখা দিয়েছে। এক্ষেত্রেও আধুনিক শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা বা বিচার ব্যবস্থার পার্থক্য বিশেষভাবেই লক্ষণীয়।
ইসলামী শাসন ও বিচারের মূল উৎস একই। এ দুনিয়ায় আল্লাহ্রই রয়েছে একমাত্র সার্বভৌমত্ব এবং তিনি তাঁর প্রেরিত পুস্তকে কুরআন উল-করীমের মাধ্যমে মানবজীবনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যেসব নীতি নির্দেশ দিয়েছেন তারই আলোকে খলিফা শাসন পরিচালনা করেন। সে একই নীতির আলোকে খলীফা বা তাঁর প্রতিনিধিগণ বিচার করবেন। এজন্য যারা সত্যিকার মুসলিম তাদের পক্ষে একই সঙ্গে শাসন পরিচালনা ও বিচার করা সম্ভবপর। ইসলামের গৌরবের যুগে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব হয়নি। কোনও এক জিহাদের সময় হযরত আলী এক য়াহূদীকে পর্যুদস্ত করে তার বুকের উপর সওয়ার হয়ে তার গর্দানে খঞ্জর হানতে উদ্যত হওয়াকালে, চতুর য়াহূদী তার মুখমন্ডলে থুথু ফেলে দেয়। তিনি তার এ আকস্মিক আচরণে নিতান্ত ক্রোধান্বিত হলেও তাকে মৃত্যুদণ্ড থেকে অব্যাহতি দান করে মুক্তি দান করেন। তাঁর এ অস্বাভাবিক ব্যবহারে বিস্মিত হয়ে সে প্রশ্ন করল- “আপনি আমাকে হত্যা করেননি কেন?” তার উত্তরে হযরত আলী বলেন- “এখন যদি আমি তোমাকে হত্যা করি- তাহলে আমাকে যে তুমি অপমান করেছো- এ আক্রোশের জন্যই করবো- অথচ তোমাকে আমি আল্লাহ্র দুশমন বলেই পূর্বে হত্যা করতে চেয়েছিলাম”। তাঁর এ আচরণে অভিভূত হয়ে য়াহূদী তৎক্ষণাৎ তাঁর হাতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। এতে বিচারের যে মহৎ দৃষ্টান্তের পরিচয় পাওয়া যায় এ দুনিয়ার ইতিহাসে তা সত্যিই বিরল।
এক্ষেত্রে শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছেঃ বিচার করলে পূর্বে বিচারকের জীবনে কতকগুলো শর্ত পালনীয় হওয়া প্রয়োজন। তাকে খাঁটি মুসলিম হতে হবে। তার পক্ষে হককুল আল্লাহ্, হককুল এবাদ প্রভৃতি সম্বন্ধে পরিস্কার ধারণা থাকতে হবে এবং সেসব পালন করার জন্য আল্লাহ্ যে বিধি ব্যবস্থা করেছেন- সে সম্বন্ধে তার সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। সর্বোপরি বিচারকালে তাকে সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক মানস নিয়ে করতে হবে। অভিযুক্ত ব্যক্তির সঙ্গে তার শত বিবাদ বিসম্বাদ থাক না কেন সে কোন অবস্থায়ই সে সব ব্যক্তিগত ব্যাপার দ্বারা প্রভাবান্বিত হবে না। বাস্তব জীবনে দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রেই তা সম্ভবপর নয়। কারণ, যাদের হাতে শাসন বিভাগ রয়েছে-তারা তাদের ব্যক্তিগত আচরণের বিরোধী দলের লোকদের প্রতি প্রায়ই বিমুখ থাকেন। তারা বিচারে প্রবৃত্ত হলে তাদের ব্যক্তিগত আক্রোশের বশবর্তী হয়ে ন্যায়বিচার পরাঙ্মুখ হতে পারেন বলে শাসন বিভাগকে বিচার বিভাগ থেকে পৃথক করা সকল ক্ষেত্রেই বাঞ্ছনীয়।
সপ্তম পরিচ্ছেদ
ইসলামী রাষ্ট্রের ভাঙনের কারণ
আল্লাহ্র একত্ব, সার্বভৌমত্ব ও মানুষের খিলাফতের ভিত্তিতে গঠিত মানব-প্রকৃতির সম্পূর্ণ অনুকূল ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা রসূলে আকরাম (সঃ)-এর দ্বারা হলেও তাকে পূর্ণ বিকাশের পথে নিয়ে যায় দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রাঃ)। তাঁর ইন্তেকালের পরে নানাবিধ কার্যকারণের ফলে সে রাষ্ট্রে অচিরেই শাহানশাহীতে পরিণত হয়।
পরবর্তীকালে দামিশকে উমাইয়াদের, বাগদাদে আব্বাসীয়দের, গ্রানাডায় মুরদের, ভারতে মুঘলদের বা তুর্কিতে উসমানীয়দের আধিপত্য বা রাজ্যবিস্তারকে ইসলামী রাষ্ট্র বলা যায় না। তারা ইসলামের নামে জনসাধারণের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। কোন বিশেষ রাজ্যের ভাঙ্গাগড়া তখন বিশেষ বংশের উত্থান-পতনের অপর নাম হয়ে দাঁড়ায়।
এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, মানব প্রকৃতির সম্পূর্ণ অনুকূল সে আদর্শ রাষ্ট্র-ব্যবস্থা অকালে ধ্বংস হয়ে গেল কেন? তাতে কি প্রমাণ হয় না যে, হয়ত সে রাষ্ট্র ব্যবস্থা মানব-প্রকৃতির সম্পূর্ণ অনুকূল ছিল না অথবা তার অর্থনৈতিক ভিত্তি এতই দুর্বল ছিল যে, তাতে মহান আদর্শ থাকলেও তার দুর্বলতার জন্যেই অকালে লয় পেয়ে গেছে?
বস্তুতান্ত্রিক সাম্যবাদীরা মনে করেন, ইতিহাসের ধারায় অর্থনৈতিক কার্যকারণের ফলেই মানুষের সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে মানুষের সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে পড়ে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে আরবের মাটিতে উৎপাদনের যে ব্যবস্থা ছিল- তার পরিবর্তন হওয়ায় ইসলামী সমাজেও তার কার্যকারিতার প্রতিফলন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। ইসলামের অভ্যুদয়ের সময় একদিকে যাযাবর বেদুঈনেরা ছিল পশুচারিক পর্যায়ের২০৬ অপরদিকে মক্কা ও মদীনার অপেক্ষাকৃত উন্নত কেন্দ্রগুলোয় ছিল একদল ব্যবসায়ী। ইসলামের বিস্তৃতির ফলে ইরাক, সিরিয়া, বাহরাইন বিজিত হলে মুসলিমেরা ভূমির সংস্পর্শে আসে। তাই ভূমিতে উৎপাদনের ব্যবস্থাতে তারা অভ্যস্ত হওয়ার ফলে আস্তে আস্তে তাদের সমাজে সামন্ততন্ত্রের ভাবধারা প্রবেশ করে। কাজেই সমস্ত জগৎ যে ভাবধারা ধরে চলেছিল, সে ধারা ইসলামের মধ্যেও প্রবেশ করে। ইসলামের বিশিষ্ট অর্থনীতি তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। কাজেই ধর্ম হিসেবে ইসলামের বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে কিন্তু অর্থনীতিতে ইসলামের কোন বৈশিষ্ট্য নেই। যে অর্থনৈতিক সূত্র ধরে দুনিয়া বস্তুতান্ত্রিক সমাজবাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছে-ইসলামপন্থীকেও সেই পথেই অগ্রসর হতে হবে। ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের ভাঙনের কারণের মধ্যে তাই আশ্চর্য কোন কিছুই নেই। এ ভাঙ্গন তার কাছে ছিল অবধারিত।
মাত্র সেদিন প্রকাশিত (Modern Islam in India) নামক পুস্তক উইলফ্রেড কেন্টওয়েল স্মিথ এ তত্ত্বই প্রমাণ করতে চেয়েছেন। তাঁর মতে ভারতের মুসলিমদের মতবাদও যুগে যুগে অর্থনৈতিক কারণের ফলে পরিবর্তিত হয়েছে।
এঁদের যুক্তির মধ্যে রয়েছে এক বিরাট ফাঁক। তার জন্যই আপাতত অবিশ্বাসী মানব-মনকে মুগ্ধ করলেও ন্যায়শাস্ত্রের কষ্টিপাথরে এঁদের যুক্তি কিছুতেই টেকে না। তাঁদের পক্ষে প্রমাণ করা উচিত (১) ইসলামী অর্থনীতি মানবজীবনে কার্যকরী হতে পারে না, তাকে সমাজে প্রয়োগ করলেও সে অন্য অর্থনীতিতে লয় পেতে বাধ্য। (২) সে অর্থনীতি গ্রহণ করে এবং তাকে বাস্তবজীবনে রূপায়িত করেও ইসলামী সমাজ টিকে থাকেনি।
এ দুটো বিষয় প্রমাণ না করে যদি জোর করে বলা হয়-যেহেতু ইসলামী অর্থনীতি টিকে থাকেনি- সেজন্যই তা অচল-তা’হলে কি বলতে হবে দুনিয়ার বুকে যা-ই ঘটে, তা-ই সচল ও সত্যি, আর যা এককালে ফলে ওঠেনি অথচ পরে রূপায়িত হয়েছে তা তখন ছিল অসত্য এবং বর্তমানে সত্য? মার্কসীয় অর্থনীতির সূত্র জগতে প্রথম প্রচারিত হয় Das Capital প্রকাশিত হওয়ার পরে। তাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য মার্কস ও এঞ্জেলস কমিউনিষ্ট মেনিফেষ্টো প্রকাশ করেন ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে। তার ফলে ফরাসী রাষ্ট্র বিপ্লবের পরিণতিতে প্যারিস কমিউন প্রতিষ্ঠিত হয় সে অর্থনীতিকে রূপায়িত করার জন্য, কিন্তু তা টিকে থাকেনি। মাত্র সেদিন ১৯৭১ সালে মার্কসীয় মতবাদের প্রতিষ্ঠাকল্পে রাশিয়ায় রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে। সে জন্য কি বলতে হবে- মানব জীবনের পক্ষে মার্কসীয় মতবাদ তখন ছিল অকার্যকরী বা মার্কসীয় মতবাদ গ্রহণ করার ফলেই প্যারিস কমিউন ভেঙ্গে গেছে ?
তার উত্তরে যদি বলা যায়, প্যারিস কমিউন ভেঙ্গে যাওয়ার কারণ সমাজজীবন যেসব ধাপের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজন, সে ধাপগুলো তখন ডিঙ্গিয়ে যায়নি বলে অর্থনীতি গ্রহণ করতে পারেনি, তার অর্থনৈতিক বা সামাজিক কাঠামো ভেঙ্গে যায়নি- তা’হলে ইসলামী সমাজের বেলায়ও তো এই যুক্তিই প্রয়োগ করে বলা যেতে পারে-মানবজীবনের পূর্ন বিকাশের পক্ষে ইসলামী অর্থনীতি গ্রহণযোগ্য বলে তখনকার সমাজে তা আর দীর্ঘকাল কার্যকরী হয়নি।
জগৎ সভ্যতার আলোচনা করলে বিশেষভাবে এ সত্যই প্রমাণিত হয়। মানব সভ্যতার ইতিহাসের আলোচনায় দেখা যায়, মানবজীবনের বিকাশের সহায়করুপে ক্রমেই কতকগুলো মৌলিক অধিকারের২০৭ নীতি স্বীকৃত হয়েছে। বর্তমান জগতে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতাকে মানবজীবনে বিকশিত করার জন্য ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের দার্শনিক ভিত্তির ওপর গড়ে উঠেছে পুঁজিবাদী সমাজ। তার অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের ফলে বস্তুতান্ত্রিক সমাজবাদী প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে অবশ্যম্ভাবীরূপে। তার ফলে সমাজবাদী রাষ্ট্র গঠনের চলছে প্রচেষ্টা, তাতে সাম্য, মৈত্রী বিশেষভাবে ফলে উঠলেও স্বাধীনতাকে দেয়া হয়েছে বিসর্জন। মানবজীবনের মৌলিক অধিকার মানব-মনে দানা বাঁধতে থাকলে অনাগত বিশ্বসংস্থা গড়ে উঠবে এই তিনটে মৌলিক অধিকারের ভিত্তিতে-যা কেবল ইসলামী ব্যবস্থাতেই সম্ভব।
দ্বিতীয়ত ইসলামী সমাজ ইসলামের অর্থনৈতিক ভিত্তি অক্ষুণ্ন রেখেই ধ্বংস হয়নি, বরং বর্জন করেই ধ্বংস হয়েছে। এইটেই আজকের দিনে বিশেষভাবে প্রণিদানের বিষয়। যদি সে অর্থনীতি গ্রহণ করে ইসলামী সমাজ তলিয়ে যেতো, তা’হলে অবশ্য বলবার কারণ হতো-ইসলামের অর্থনৈতিক ভিত্তির দুর্বলতার জন্য ইসলামী সমাজ লয় পেতে বাধ্য হয়েছে।
সত্যিকার ইতিহাস পাঠকমাত্রেই জানেন, ইসলামী অর্থনীতি যতদিন পর্যন্ত সমাজজীবনে চালু ছিল, ততদিন রাষ্ট্রে অভাব-অভিযোগ বলে কিছুই ছিল না। যেই তাতে শাহানশাহীর ভাবধারার প্রবর্তন হয়, তখনই তাতে জনগণের দুঃখ-দারিদ্র্যের সৃষ্টি হয় । খলীফা উমর (রাঃ)-এর খিলাফতের সময়কে ইসলামী সমাজে সুবর্ণ যুগ বলা যেতে পারে, সে সময় বায়তুল মালের আমদানি সব সময়ই উদ্ধৃত্ত থাকতো। কাজেই, যাঁরা ইসলামের অর্থনীতি সম্বন্ধে এরূপ মন্তব্য করেন তাঁদের এসব মন্তব্য বিদ্ধেষপ্রসূতই বলতে হবে।
খোলা চোখে বিচার করলে দেখা যায়, অর্থনৈতিক দুর্বলতার জন্য নয়, নানাবিধ কারণেই ইসলামী রাষ্ট্র ভেঙ্গে গেছে। ইসলামী রাষ্ট্রের ভাঙনের কারণঃ
১.যে জীবন দর্শনের ওপর ইসলাম প্রতিষ্ঠিত, তা আরব-জীবনে রূপায়িত হয়নি। তার পক্ষে নানা প্রতিবন্ধকতা ছিল বর্তমান। ইসলামের মূল ভিত্তি আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব ও মানুষের প্রতিনিধিত্ব। সে ভিত্তিতে রাষ্ট্রকে রূপায়িত করতে হলে মানুষকে আল্লাহ্র গুনে গুণান্বিত হতে হয়। আল্লাহ্র প্রতিনিধিত্ব দুনিয়ার বুকে তার রাষ্ট্র রূপায়িত করার জন্য গুণের মাপকাঠিতে আল্লাহ্র রসূলের খলীফা বা প্রতিনিধি নির্বাচন করতে বাধ্য। তাতে আধুনিক গণতন্ত্রে২০৮ যেমন সংখার দিক দিয়ে গুরুত্ব আরোপ করে প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়, তা না করে গুণের ভিত্তিতে খলীফা নির্বাচন করা ছিল সুযোগ ও সুবিধা। এতে সর্বসাধারণের ভোটের অধিকার স্বীকৃত হয়েছিল। পরবর্তীকালে বিস্তৃতির ফলে ইসলাম আরব থেকে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়লে বিজিত দেশের লোকেরা ইসলামী সমাজে তাদের কোন প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। তাই ইসলাম ক্রমেই আরবকেন্দ্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় পরিণত হয়। ইসলামের বিস্তারের ফলে ক্রমশ সিরিয়া, ইরাক, ইরান, মিসর প্রভৃতি দেশ ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে এলে পর, সে দেশের সদ্য ধর্মান্তরিত মুসলিমেরা আরব দেশীয় নানা গোত্রের সঙ্গে এক কাল্পনিক রক্ত সম্পর্ক স্থাপনে হয় উৎসুক। এ প্রথাকে মাওলি প্রথা বলা হয়।
এতে একদিকে মুসলিমদের মধ্যে সম্পর্ক গাঢ়তর হলেও অন্যদিকে তার ফল বিষের মত দেখা দেয়। কারণ এভাবে আরব গোত্রের লোকের সঙ্গে রক্ত সম্পর্ক স্থাপন করার ফলে তারা খলীফা নির্বাচনে আরবের মাটিতে তাদের মাওলাদের ওপর সমস্ত ভার ছেড়ে দিত। ইসলামের মূলনীতি অস্বীকার করে স্বয়ং তাতে হস্তক্ষেপ না করে মাওলাদের মারফতে তাদের অভিমত ব্যক্ত করত। তার ফলে খলীফার নির্বাচনে আরবেরা সরাসরি নির্বাচনে২০৯ ও আরব জাতিরা পরোক্ষ নির্বাচনে২১০ অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। গোটা মুসলিম জাতি তার জন্য অখন্ড জাতিতে পরিণত হতে পারেনি। বলা বাহুল্য, সে জন্য নির্বাচনের ব্যাপারে আরব দেশীয় অভিজাত সম্প্রদায়ের মতামতই ছিল বেশি গ্রহণযোগ্য।
হযরত আবুবকর (রাঃ) ও হযরত উমর (রাঃ)-এর খিলাফতের সময় আরবের মাটিতে বনি হাশিম ও বনি উমাইয়ার আধিপত্য প্রতিষ্ঠার কোন সুবিধা না হওয়ায় আরবের লোকের প্রাধান্যের জন্য কোন ক্ষতি হয়নি। তাদের ইন্তিকালের পরে ক্রমেই বনি হাশিম ও বনি উমাইয়ার দ্বন্দ্ব প্রকট মূর্তি ধারণ করায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রকৃতপক্ষে বনি হাশিম ও বনি উমাইয়ার মত দুই শিবিরে বিভক্তে হয়ে পড়ে। তার ফলে (ক) ইসলামী রাষ্ট্রে আরবের গৃহযুদ্ধ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে (খ) ইসলামের মূলনীতি সর্বসাধারন মুসলিমের খলীফা নির্বাচনে সাধারণ অধিকার প্রকারান্তরে অস্বীকৃত হয় এবং (গ) সর্বসাধারণ মুসলিমের মনে সংঘ-চেতনা দানা বাঁধতে পারেনি।
খলীফার নির্বাচনে মদিনার উচ্চ শ্রেণীর মতামত গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হওয়ায় আরবের মাটির অন্যান্য অবজ্ঞাত সমাজেও বিদ্রোহ দেখা দেয়। হযরত আলী (রাঃ) ও মু’আবিয়ার দ্বন্দ্বে খারিজিরা তখনকার দিনের মুসলিম জনসাধারণের বিক্ষুব্ধ মানসেরই পরিচয় দিয়েছে। তারা চেয়েছিল সবসময়ই খলীফা নির্বাচনে সর্বসাধারণ মুসলিম অভিমতই গ্রহণ করা হবে। ধর্ম সংক্রান্ত অন্যান্য মতবাদে খারিজিরা অন্ধত্বের পরিচয় দিয়েছে সত্য, তবু তাদের রাজনৈতিক মতবাদের সত্যিকার ইসলামী নীতির প্রতি শ্রদ্ধা আজও আমাদের বিস্ময়ের বিষয়।
তখন পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্রে দাস-প্রথা এবং কুরায়েশদের প্রাধান্য অক্ষুণ্ন থাকায় তাদের এ অভিমত বৈপ্লবিক ঘোষণার মত শুনিয়েছিল। ইসলামী সমাজে সে কালে কিছুতেই দাসপ্রথা থাকতে পারে না, এ সত্য মুসলিম জনসাধারণ বুঝতে পারেনি বলে খারিজিরা তখন সমাজজীবনে অপাংক্তেয় হয়ে পড়ে। খারিজিদের নীতি গৃহীত হলে ইসলামী রাষ্ট্র এভাবে আরবদেশীয় বিভিন্ন গোত্রের দ্বন্দ্বে বিচ্ছিন্ন হত না, অপরদিকে মাওলি প্রথার প্রবর্তন না হলে গোটা মুসলিম অখন্ড জাতিরুপেই পরিগণিত হতে পারত।
২. হযরত রসূলে আকরাম (সঃ)-এর আহ্বানে যারা ইসলাম কবুল করেছিল তাদের মধ্যে অনেকেই ছিল মুনাফিক। ইসলামের সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার আদর্শ তাদের মুগ্ধ করেনি। নব-প্রবর্তিত বৈপ্লবিক জীবনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ব্যর্থকাম হয়েই তারা ইসলামে প্রবেশ করে। ঘরের শত্রু হয়ে ইসলামের ধ্বংস ত্বরান্বিত করার দুরভিসন্ধি ছিল তাদের মনে বদ্ধমূল। এদের হাতেই ইসলাম পরবর্তীকালে শাহানশাহীতে পরিণত হয় এবং এদের হাতেই অমুসলিমদের চেয়ে ইসলামের অবমাননা হয় বেশি। এদের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে যুগে যুগে সত্যিকার ইসলামপন্থীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন।
আমীর মুআবিয়ার জীবনেই ইসলামী সমাজে শাহানশাহীর ভাবধারা প্রথম প্রকাশিত হয়। হযরত উসমান (রাঃ)-এর সরলতার সুযোগ নিয়ে দামিশ্কে তিনি পুঁজিবাদী নীতির প্রবর্তন করলে তার বিরুদ্ধে রসূলে আকরাম (সঃ)-এর প্রিয় সাহাবী হযরত আবু যর গিফারী (রাঃ) বিদ্রোহ ঘোষণা করে, ইসলামের শৈশবাবস্থা স্মরণ করে স্বেচ্ছায় নির্জনবাসে চলে যান। হযরত আলী (রাঃ) ও তাঁর প্রিয় পুত্র হোসেন (রাঃ) ইসলামী আদর্শকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্য শাহাদাত বরণ করেন।
পরবর্তীকালে উমাইয়া ও আব্বাসীয় আমলে মুসলিম রাষ্ট্র প্রগতির পথে আর অগ্রসর হতে পারেনি। তার স্রোত উল্টো বইতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে যে বিপ্লবের প্রেক্ষাপটে প্রথম দুই খলীফার সময় ইসলামী রাষ্ট্র প্রবল গতিতে আদর্শ বাস্তবায়নে ছুটে চলে হযরত উসমান (রাঃ)-এর খিলাফতের সময় থেকেই প্রতিবিপ্লবের২১১ ফলে আস্তে আস্তে উল্টোদিকে চলতে শুরু করে। বনি উমাইয়া ও বনি আব্বাসীয়ের মধ্যে উমর ইবনে আব্দুল আযীয বা আব্দুল্লাহ আল-মামুন তাঁদের বংশের ব্যক্তিক্রম হলেও সে সময়কার বাদশাহী স্রোতের তলায় তাঁদের ব্যক্তিগত সদিচ্ছা কার্যকরী হতে পারেনি।
৩. ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভাঙনের কারণস্বরূপ বলা যেতে পারে- ভূমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার নীতি গ্রহণের২১২ ফলেই ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনীতির মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। ইসলাম কোন অবস্থাতেই মাটির ওপর ব্যক্তির মালিকানা স্বীকার করেনি। আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের সঙ্গে ব্যক্তিগত মালিকানা কিছুতেই খাপ খায় না। ইসলামী সমাজে ব্যক্তিকে রক্ষক২১৩ বা ভোগদখলকারী হিসাবে তার প্রয়োজনমত আল্লাহ্র নিয়ামত ভোগ করতে দেওয়া হয়।
ইসলামী রাষ্ট্রের সুবর্ণ যুগে হযরত উমর (রাঃ) সে নীতিই গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর আদর্শ ছিল সর্বাবস্থায় মুসলিম জনসাধারণকে রাষ্ট্রের অঙ্গ জ্ঞান করে তাদের খোরাক-পোশাক প্রভৃতি জীবন যাপনের সমস্ত উপকরণ রাষ্ট্র থেকে সরবরাহ করা। তাঁর বিজিত দেশের ভূমি তিনি মুসলমানদের মধ্যে ভাগ করেননি, বিজিত জাতির মধ্যে তিনি সে ভূমি ভাগ করে দেন। সে আদর্শ রাষ্ট্র সকল সময়েই জনসাধারণের সুখ-দুঃখের জন্য দায়ী থাকায় ব্যক্তিগত শোষণ বা ভোগ-বিলাসের যাতে কোন সুবিধা না হয়, তার সকল ব্যবস্থাই তিনি করেছিলেন। তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রাঃ)-এর সরলতার সুযোগ নিয়ে সিরিয়ার গভর্নর মুআবিয়া সিরিয়াতে এক বিস্তৃত ভুখন্ড জায়গীর স্বরূপ আদায় করেন। মুআবিয়া তাঁর শাসনকালে মিসরের সমস্ত রাজস্ব আমর বিন’আসকে দান করেন।
এসব কার্যকারণের ফলেই আল্লাহ্র রাষ্ট্রের মালিকানা অবশেষে ব্যক্তিবিশেষ বা বংশবিশেষের হাতে চলে যায় ও ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। যার ফলে জায়গীরপ্রাপ্ত ভূমি থেকে আয় বন্ধ হয়ে ক্রমেই সেই রাষ্ট্রের অন্যান্য নানা প্রয়োজনীয় খাতে ব্যয় করার পক্ষে উপযুক্ত অর্থের অভাব দেখা দেয়।
৪.ইসলামী রাষ্ট্রের ভাঙনের সর্বপ্রধান কারণ তার অগ্রবর্তিতা। ইসলাম যে আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা দুনিয়ায় কায়েম করতে চেয়েছে, সে সময়কার সাধারণ মানুষ সে ব্যবস্থ মোটেই বুঝতে পারেনি। মানব জীবনকে ব্যাপক ও পূর্ণভাবে বিকশিত করে তুলতে হলে যে মানবিক অধিকার গোড়াতেই স্বীকার করে নিতে হয়, সেগুলো তখনকার আরব সমাজে মোটেই স্বীকৃত হয়নি।
মানবজীবনের এই সন্ধিক্ষণে এসে দেখা দিয়েছিল মানুষের নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)। জীবন বিকাশের যে চাবিকাঠি তিনি নিয়ে এসেছিলেন তখনকার অনুন্নত আরব সমাজ তার প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করতে পারেনি। আল্লাহ্র ওয়াহ্দানীয়ত ও সার্বভৌমত্ব মন্ত্র তারা গ্রহণ করেছিল বটে তবে তার সুদূরপ্রসারী ফলে মানবজীবনে বিভিন্ন সমস্যার কিভাবে সমাধান করা যায় এবং তার প্রয়োগে জীবনধারা কিভাবে সরলরেখায় অগ্রসর হতে পারে সে তত্ত্ব উপলব্ধি করার শক্তি তাদের ছিল না। কাজেই আল্লাহ্র রসূলের ব্যক্তিগত চরিত্রমাধুর্য ও নিষ্কলঙ্ক জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েই তারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল। ইসলামের বৈপ্লবিক প্রেরণায় তারা উদ্ধুদ্ধ হয়নি। খুলাফায়ে রাশেদীন, হযরত আবু যর গিফারী (রাঃ) বা আরও দু’একজন দূরদর্শী মহাপ্রাণ ব্যক্তি ব্যতীত মানবজীবনের কল্যাণ সাধনে ইসলাম কিভাবে কার্যকরী সে তত্ত্ব অনেকের কাছেই সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল।
ইসলামের বাইরের খোলস দেখে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল, পরবর্তীকালে উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে তাদের মনেই আবার গায়ের ইসলামী ভাবধারা প্রবল হয়ে পড়ে।
কুরআন শরীফের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল মনোবৃত্তিতে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। কুরআন শরীফে মানবজীবনকে চিরকাল পরিচালিত করার জন্য রয়েছে কতগুলো আদর্শ নীতি। আবার কতগুলোতে আরবের তৎকালীন সমাজজীবনের রীতিনীতি পরবর্তিত অবস্থায় গ্রহণ করা হয়। সেগুলো যে জীবন বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানবজীবন থেকেক নিশ্চিহ্ন হতে বাধ্য তার ইঙ্গিতও কুরআন শরীফে রয়েছে। সুদ,ব্যভিচার,শরাব,শূকরের গোশত ইসলামে চিরকালই অকল্যাণকর। তাই সকল যুগেই তা’ হারাম ও নিষিদ্ধ। দাসপ্রথা, বহুবিবাহ প্রথা সে আরব সমাজে ছিল বিশেষভাবে প্রচলিত। সেগুলো কুরআন শরীফে নিষিদ্ধ হয়নি সত্য কিন্তু তাদের ওপর যে শর্ত আরোপ করা হয়েছে, তা প্রতিপালন করা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই কুরআন শরীফে বাহ্যত নিষিদ্ধ নয়, এমন কতকগুলো নীতি যে পরবর্তী সমাজব্যবস্থায় নিশ্চিহ্ন করা হবে, তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।
সামাজিক রীতিনীতির মধ্যেও কুরআন শরীফের আদেশ-নিষেধগুলোর মধ্যে একটি পার্থক্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যে সকল কার্যকলাপ ইসলাম চিরকালের জন্য নিষিদ্ধ করে দিয়েছে, সেগুলো প্রচলনের কোন সুবিধা নেই। সুদ,যিনা (ব্যভিচার)শরাব- কোনকালে কোন অবস্থাতেই জায়েয হতে পারে না। কিন্ত কতগুলো জায়েয কাজকে পরবর্তীকালের মুসলিমদের সর্ববাদীসম্মত অভিমত (ইজমা) দ্বারা পরিবর্তন করা না-জায়েয নয়। চার স্ত্রীর পরিবর্তে এক স্ত্রী গ্রহণ বা দাস প্রথারবিলোপ ইসলামের চোখে নিন্দনীয় নয়।
অনেক ক্ষেত্রেই স্বীয় বিচার-বুদ্ধির ব্যবহার ইসলাম অনুমোদন করেছে। আফসোসের বিষয়, পতন যুগে ইসলামের মূল আদর্শ হারিয়ে কুরআন শরীফ অথবা হাদিস শরীফের শাব্দিক ব্যাখ্যা নিয়ে মাথা ঘামানো মুসলিম সমাজে অভ্যাসে পরিণত হয়। ফলে যে বৈপ্লবিক জীবনধারার প্রবর্তনের জন্য ইসলাম নাযিল হয়েছিল তা’ ব্যর্থ হয়। এর জন্য দায়ী ছিল অনুন্নত সমাজজীবন। সে সমাজজীবন মানবতার পারিপার্শ্বিক আদর্শ গ্রহণ করে সে সমাজ ব রাষ্ট্র সামন্ততন্ত্রের আওতায় চলে যায়।
অষ্টম পরিচ্ছেদ
ইসলামী সমাজের ভূমিনীতি ও তার প্রয়োগ
ইসলামী জীবনদর্শন ও তার ফলিত রূপ
ইসলামী জীবনদর্শনের আলোকেই ইসলামী সমাজের ভূমি-নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব ইসলামী রাষ্ট্রের চরম ও পরম তত্ত্ব। মানুষ আল্লাহ্র প্রতিনিধি হিসাবে সে আদর্শ রাষ্ট্র গড়ে তুলবে। সেখানে ব্যক্তিগত অথবা সমাজগৎ সুখ-সুবিধার জন্য বিলাসিতা প্রশ্রয় পেতে পারে না।
ইসলামী সমাজ অথবা রাষ্ট্রের কোন বস্তুর ওপরই কারো ব্যক্তিগত মালিকানা নেই, আছে শুধু ভোগের জন্য দখলের অধিকার। রাব্বুল আলামীনের খলীফা হিসেবে ব্যক্তিগত জীবনে অথবা সামাজিক জীবনে মানুষ আল্লাহ্র মালিকানাকে মেনে নিয়ে সেই সম্পদকে ভোগ করতে পারে, এর অতিরিক্ত কোন দাবিই করতে পারে না।
তাই, ইসলামী সমাজে মানবসাধারণকে জীবন ধারণের জন্য উপযুক্ত জমিরক্ষক হিসেবে ভোগ করতে দেওয়া হয়। অতিরিক্ত সম্পত্তি রাষ্ট্রের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়, অথবা গো-চারণ ভূমি, কবরস্থান, সর্বসাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত হয়, যাতে ভূমি ব্যক্তিবিশেষের বা বংশবিশেষের সম্পত্তিতে পরিণত না হয়, তার প্রতি লক্ষ্য রেখেই ইসলামী রাষ্ট্রের ভূমি বন্টনের নিয়ম প্রবর্তন করা হয়েছে।
ইসলামী সমাজে ভোগ দখলের অধিকার
নবী করীম (সঃ)-এর মক্কা থেকে মদীনাতে হিজরতের পর ভূ-সম্পত্তিতে যে ইতিহাস পাওয়া যায় তা থেকে দেখা যায়, “আনসার ও মুহাজিরগণের ভূ-সম্পত্তির স্বত্বাধিকারের অর্থ এই যে, নবী করীম (সঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীন দান ও জায়গীরস্বরূপ যে জমি তাদের দিয়েছেন তাই তাদের সরল জীবন যাপনেও কাজে লাগতো”।
“বনজর’ (অনাবাদী) ভূমিকে আবাদ করে তাঁরা ফসলের উপযোগী করতেন। এগুলোও আয়তনের দিক থেকে বর্তমান যুগের বড় বড় গ্রাম বা মৌজার মত ছিল না। মাত্র কতক আবাদী জমির সমষ্টি ছিল-কাজেই দেখা যায়, ইসলামী সমাজে দুইভাবে রক্ষক হিসেবে জমির উপর মানুষের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। (১) যে সকল জমি কৃষকেরা নবী করীম (সঃ) অথবা খুলাফায়ে রাশেদীনের কাছ থেকে দান অথবা জায়গীরস্বরূপ পেয়েছিলেন অথবা (২) যে সকল অনাবাদী জমিকে তাঁরা আবাদ করে ফসলের উপযোগী করে তুলেছিলেন, মাত্র সেসব জমিতেই তাঁদের ভোগ দখলের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কোন কোন শর্তে বনজর জমিতে জোত স্বত্ব বর্তাতে পারে, তার নজিরস্বরূপ দেখা যায়, কৃষিকার্যের উন্নতি এবং আবাদীর প্রচেষ্টাকে ইসলামী অর্থনীতিতে মৃতের জীবন দানের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। পতিত, অনাবাদী জমিকে কৃষি উপযোগী করে তুললে তাতে রক্ষক হিসেবে চাষীর জোতস্বত্ব বর্তাতে পারে। ... “পতিত জমিকে চাষের উপযোগী করার অর্থ তাকে পূর্ণ জীবন দেওয়া। নীরস, অনুর্বর জমি, বালুকাময় জমি, প্রস্তরপূর্ণ জমি বা টিলা সাধারণভাবে অনুপযুক্ত জমিরুপে পরিগণিত। শক্ত পরিশ্রমের দ্বারা অধিক পরিমিত ভূমিকে কৃষির উপযুক্ত করা সম্ভব। এরূপ অনুপযুক্ত সমস্ত জমিজমাকে কৃষিকার্যের উপযুক্ত করা এবং কাচাঁমাল দ্বারা দেশের সমৃদ্ধি সাধন ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রধানতম অংশ। যথাসাধ্য পতিত জমি থাকতে না দেয়া, যেসব জমি কৃষির উপযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও পতিত পড়ে রয়েছে তাকে কৃষির উপযুক্ত করে তোলা-প্রভৃতির জন্য ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় দুটো উপায় রয়েছেঃ
১.প্রথমত আমিরুল মুমিনিন দেশের জনসাধারণকে উৎসাহিত করবেন এবং এই মর্মে প্রচার করবেন যে, যে যতখানি পতিত জমি আবাদ করবে সে-ই তার অধিকারী হবে।
২.ইমামের কর্তব্য-পতিত জমিকে অথবা উত্তরাধিকারবিহীন, অধিকারীহীন জমিকে জায়গীরের মত দেশের লোকের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া, যাতে ঐ সব জমি কৃষির উপযুক্ত হতে পারে এবং এগুলোর বিলি ব্যবস্থায় সর্বসাধারণ মুসলমানের উপকার হয়।
ফিকাহ শাস্ত্রকারগণের মতে-যদি এরূপ বনজর জমি তৈরি করা অধিক ব্যয়সাপেক্ষ হয়, তাহলে দু’তিন বছরের খাজনা মাফ করার অধিকার ইমামের রয়েছে। এ সমস্ত জমি সম্বন্ধে জনাব রসূলে করীম (সঃ) ফরমায়েছেন-যে জমির কোন স্বত্বাধিকারী নেই, এরূপ জমিকে কেউ কৃষিকার্যের উপযুক্ত করে নিলে- সে ব্যক্তিই এ জমিনের স্বত্বাধিকারী (অবশ্য রক্ষক অর্থে) হওয়ার অধিকারী। যে ব্যক্তি মৃত জমিকে পুনর্জীবিত করে সে জমি তারই।
তিনটি শর্ত রয়েছে
(ক) জমি যেন শহরতলীতে না হয়, শহরের প্রয়োজনে না লাগে এবং গ্রামবাসীগণের ফায়, গোবর ও কবরস্থান না হয়। আব্বাসীয় খলীফা হারুন-অর-রশিদকে সম্বোধন করে ইমাম আবু ইউসুফ বলেছেন, “ হে আমিরুল মুমিনিন, যে সব জমি যুদ্ধ বিগ্রহ অথবা সন্ধির দ্বারা বিজিত হয়েছে সে সব জমি ও যেসব গ্রাম-অঞ্চলের জমি এমন অবস্থায় পড়ে রয়েছে যে, তাতে ঘর-বাড়ি বা ক্ষেত-খামারের কোন চিহ্ন নেই, সে জমি সম্বন্ধে আপনি আমার অভিমত জানতে চেয়েছেন। তার উত্তরে বলা যায়-যেসব জমিতে কোন ঘর-বাড়ির চিহ্ন না থাকে, গ্রামবাসীগণের কোন ‘ফায়’ সম্পত্তি, কবরস্থান চারণভূমি যা নয়, কারো স্বত্বাধিকার অথবা দখলাধিকার নয়-এরুপ জমিকে মৃত জমি বলা হয়। যে ব্যক্তি এরূপ জমিকে অথবা কোন অংশকে পুনর্জীবিত অর্থাৎ কৃষিকার্যের উপযোগী করে তুলে তার স্বত্ব (ভোগ দখলের) বর্তাবে। আপনার বিবেচনা মত এসব ভূমি জায়গীরের মত বন্দোবস্ত দিতে পারেন। ‘কিতাবুল খারাজ’ ‘ইসলাম কা একতেসাদি নেজামে’ ‘ফায় সম্পত্তির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, যদি ইসলামী সেনার কাছে পরাজিত হয়ে অথবা ভয় পেয়ে যুদ্ধ না করে বিধর্মী তাদের সম্পত্তি ফেলে পলায়ন করে অথবা যুদ্ধের ভয়ে তাদের আপন জমি তাদের হাতে রেখেই ইসলামী রাষ্ট্রকে নির্দিষ্ট কর দিতে চায় অথবা যদি তাদের খাজনা বা জিযিয়া নির্দিষ্ট করে তাদের কাছেই তাদের জমি বন্দোবস্ত দেওয়া যায়- তাহলে সেই নির্দিষ্ট কর, খাজনা অথবা জিযিয়াকে ‘কর’বলে। এ নীতি অনুসারে জিযিয়া বা খাজনাকে ‘ফায়’ বলে গণ্য করা হয়
(খ) যদি কেউ ইমামের কাছ থেকে এ জমি অধিকার করার পর তিনি বছর পর্যন্ত পতিত ফেলে রাখে আর জায়গীর দেওয়ার যে উদ্দেশ্য ছিল, তা পূর্ণ না করে তা’হলে তার হাত থেকে এ জমি ছিনিয়ে নিয়ে অন্য ব্যক্তিকে বন্দোবস্ত দেওয়া যাবে।
(গ) তৃতীয় শর্ত- এই জমির মধ্যে শহর, তালাব, জলাশয়, ‘হবীম’ বা মসজিদ-সংলগ্ন ভূমি থাকবে না। সে ‘হবীমের’ পরিমাণ ৪০ গজ এবং ক্ষেতের জন্য নির্দিষ্ট ভূমির পরিমাণ ৬০ গজ।
এবং বিধ শর্তসাপেক্ষে যে কেউ-মুসলিম অথবা অমুসলিম-পতিত জমিকে আবার করলে তাতেও তার ভোগ-দখলের অধিকার বর্তাবে।
ভোগ-দখলের জমির পরিমাণ
সে জমির পরিমাণ হবে কোন ব্যক্তির বা তার পরিবারের জীবিকার পক্ষে উপযুক্ত, তার বেশি জমিতে তাকে কোন মতেই ভোগ-দখলের অধিকার দেওয়া যাবে না। হযরত উমর ফারুক (রাঃ)-এর কার্যাবলি থেকে এ নীতিরই সমর্থন পাওয়া যায়। যাতে কোন অবস্থায়ই জমিদারি বা বড় বড় জোতদারির সৃষ্টি না হয়, তার প্রতি দৃষ্টি রেখে তিনি ইসলামী সমাজে ভূমি বিলির ব্যবস্থা করেছেন। ইরাক ও সিরিয়া বিজিত হলে তিনি সাহাবীদের শত আবেদন সত্ত্বেও সেসব দেশের জমি তাদের জায়গিরস্বরূপ দান করেননি, তার ওপর প্রয়োজনের অতিরিক্ত বলে হযরত বিলালের জায়গিরপ্রাপ্ত জমি থেকে একটি অংশ কেটে নিয়ে প্রকৃত হকদারের হাতে তুলে দিয়েছেন।
জমি থেকে ফসল উৎপাদনের নীতি
সে জমিতে চাষী কিভাবে ফসল উৎপাদন করবে, তার স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে ইসলামী সমাজে। চাষী তার জমি নিজে চাষাবাদ করে তা’ থেকে ফসল উৎপাদন করবে। যদি কোন কারণবশত তাতে অসমর্থ হয় তা’হলে তার অপর ভাইকে সহানুভূতি প্রদর্শনপূর্বক চাষ করতে দেবে।
উঁচু স্তরের সাহাবীরা জমি থেকে উপস্বত্ব ভোগের এ পদ্ধতিকেই খাঁটি ইসলামী পদ্ধতি বলে গ্রহণ করেছে। এ সম্বন্ধে হযরত রাফে বিন খাদিজ (রাঃ) বলেন-আল্লাহ্র রসূল (সঃ) আমাদের এমন কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন, যাতে বাহ্যত আমাদের উপকার হতে পারে। যেমন আমাদের মধ্যে যদি কারো জমি থাকে, তবে সে জমিকে ভাগে অথবা লগ্নিতে দিতে পারবে না। হযরত (সঃ) ফরমিয়েছেন-যার জমি আছে, সে নিজেই তা চাষ-আবাদ করবে অথবা অন্য মুসলমান ভাইকে বিনালাভে সহানুভূতি প্রদর্শনপূর্বক চাষ করতে দেবে।
রাফে-বিন খাদিজের মতে, ভাগে চাষাবাদের প্রবর্তন হলে নানা ঝঞ্ঝাটের সৃষ্টি হতে পারে। কারণ জমি যদি ভাগে দেওয়ার প্রচলন হয়, তা’হলে ভোগ-দখলকারী চাইবে জমির উর্বর অংশ থেকে ফসল নিতে। অপরদিকে যে আবাদ করেছে, সেও চাইবে অনুরূপ অংশ। তার ফলে নানা ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টির ভয়ে আল্লাহ্র রসূল এ প্রথাকে নিষিদ্ধ করেছেন।
হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেছেন- “আল্লাহ্র রসূল ফরমিয়েছেন-যার জমি আছে সে নিজেই তা চাষাবাদ করবে বা, অন্যকে বিনালাভে সহানুভূতি প্রদর্শন করে চাষ করতে দেবে। অস্বীকারকারীর প্রতি হযরত (সঃ) অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিলেন”।
হযরত জাবির (রাঃ) বলেছেন- “আল্লাহ্র রসূল (সঃ) জমির পরিবর্তে কোন কিছু গ্রহণ বা ইজারা দ্বারা উপকৃত হতে নিষেধ করেছেন”।
হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) তাঁর জমিকে হযরত (সঃ)-এর আমল থেকে মু’আবিয়ার আমলের প্রথম ভাগ পর্যন্ত চাষীদের মধ্যে লগ্নিতে বন্দোবস্ত দিতেন, কিন্তু যখন তিনি রাফে (রাঃ)-এর হাদীস শুনতে পেলেন তখন তিনি এ কাজ ভয়ে ছেড়ে দিলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হল-সম্ভবত হযরত (সঃ) তাঁর শেষজীবনে এ সম্পর্কে এ মীমাংসায় উপনীত হয়েছেন।
হযরত আবুযর গিফারী (রাঃ)-এর মত এই যে, ‘জমি নগদ লগ্নি বা ভাগে দেওয়া নাজায়েয এবং জমিদারি প্রথা কোন অবস্থায়ই জায়েয নয়”।
হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন- ‘নবী করীম (সঃ)-এর নিষেধের অর্থ মুসলমান নিজে চাষাবাদ করবে অথবা একে অন্যের সৌহার্দ্য বা বন্ধুত্ত স্থাপনের উদ্দেশ্যে অন্যের প্রয়োজন অনুযায়ী অন্য ভাইকে বিনালাভে দেবে।
শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভীও ইজারা দেওয়াকে বিশেষ গর্হিত কাজ বলে অভিহিত করেছেন।
প্রশ্ন উঠতে পারে, যদি কোন ব্যক্তি অসুস্থতার দরুন অথবা কোন কার্য উপলক্ষে স্বয়ং উপস্থিত না থেকে চাষাবাদ করতে না পারে অথচ জমির উপস্বত্ব ব্যতীত তার বেঁচে থাকবারও অন্য কোন উপায় না থাকে-সেরূপ অবস্থায় জমির কি ব্যবস্থা করা হবে?
ইসলামের মূলনীতি ভ্রাতৃত্ববোধের আলোকে তার মীমাংসা করতে হলে বলতে হবে, তার পাড়া-পড়শি অন্য ভাইরা তার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে কোন মুনাফা না নিয়েই তার জমি চাষ করে দেবে। যাতে কোন অবস্থায় মুনাফা স্বীকারের কোন সুযোগ ও সুবিধা না থাকে, ইসলামী সমাজে সে নীতিই গ্রহণ করা হয়েছে।
উৎপাদনের পদ্ধতি
আবার প্রশ্ন দাঁড়ায়-চাষী একাকী চাষ-আবাদ করবে না প্রয়োজনবোধে সমষ্টিগতভাবে২১৪ ফসল উৎপাদন করবে? এ সম্বন্ধে ইসলামী সমাজে দুটো পদ্ধতিই স্বীকৃত হয়েছে-
এ প্রশ্ন মীমাংসার জন্য অংশীদারের স্বত্ব২১৫ এবং চুক্তিকৃত২১৬ স্বত্বের মধ্যে প্রভেদ বিশেষ লক্ষণীয়। কোন সম্পত্তিতে কারো স্বত্ব তখনই বর্তে, যখন সে সম্পত্তিতে অন্যের সঙ্গে কোন ব্যক্তির ন্যায্য অংশ থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোন ব্যক্তি সম্পত্তি রেখে পরলোকগমন করলে তার সম্পত্তিতে তার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সকলেরই অংশ স্বীকৃত হয়। অপরদিকে দশজন লোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাদের সম্পত্তি আরও বিশজনের মধ্যে ভাগ করে নিতে পারে বা সে সম্পত্তির সমান অংশে ভোগ করার জন্য চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারে।
ইসলামের মূলনীতি দুনিয়ার সম্পদ রক্ষক২১৭ হিসেবে মানুষ ভোগ দখল করবে, এতে কোন মালিকানা থাকবে না। তাই উৎপাদন ব্যবস্থার অংশীদারি স্বত্ব যেমন থাকতে পারে চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার ফলেও স্বত্বের সৃষ্টি হতে পারে। চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ায় কিভাবে ভোগ-দখলের স্বত্বের সৃষ্টি হয় তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন রয়েছে ইসলামের ইতিহাসে। মদীনাতে হযরত (সঃ)-এর হিজরতের পরে আনসাররা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাদের খেজুর গাছগুলো ফল মুহাজিরদের সঙ্গে সমভাবে ভোগ করতে স্বীকৃত হন। তার ফলে উৎপন্ন খেজুর তাঁরা সমানভাবেই ভোগ করতেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, ‘(তারপরে) আনসাররা আল্লাহ্র রসূল (সঃ)-কে এসে বললেন- আমরা ও আমাদের ভাইগণের (মুহাজিরগণের) মধ্যে আপনি গাছগুলো ভাগ করে দিন’। তার উত্তরে আল্লাহ্র রসূল (সঃ) বলেন, ‘না আমরা যে উপস্বত্ব পাচ্ছি, তা-ই যথেষ্ট এবং তোমাদের সঙ্গে ফলের অংশ আমরা ভোগ করছি এই ভালো’। তাঁরা বলেন, ‘আমরা আপনার কথা শুনেছি- আদেশও প্রতিপালন করবো’।
কাজেই চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে অন্যের সঙ্গে সম শরীকানা ভোগ করা ইসলাম অনুমোদন করে। বন্টনের নীতি ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত যে কোনোভাবেই উৎপাদন করুক না কেন, উৎপন্ন ফসল চাষীর নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত হলে তার কি ব্যবস্থা করা হবে- এ প্রশ্নটিও অত্যন্ত স্বাভাবিক। তার উত্তরে বলা যায়, তার বা তাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে অতিরিক্ত দ্রব্যে আত্মীয়-স্বজন, দীন-দুঃখীদের হক রয়েছে।
কুরআন শরীফে রসূল (সঃ)-কে লক্ষ্য করে আল্লাহ্ বলেছেন, “তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে তারা (আল্লাহ্র পথে) কত (অংশ) ব্যয় করবে। তাদের বলো- তোমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা কিছু”।
কেবল কুরআন শরীফেই নয়, হাদীসেও প্রয়োজনের অতিরিক্ত সবকিছু আল্লাহ্র পথে অর্থাৎ মানুষের কল্যাণের জন্য ব্যয় করা কর্তব্য বলে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইবনে হাজম জাহেরী তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ ‘মুহাল্লা’তে উল্লেখ করেছেন- হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, “আল্লাহ্র রসূল (সঃ) বলেছেন যে, যে ব্যক্তির কাছে শক্তি ও সামর্থ্যের সরঞ্জাম নিজেদের আবশ্যকের অতিরিক্ত রয়েছে, তাদের উচিত অতিরিক্ত সামান দীন-দুঃখীকে বিতরণ করা”। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেছেন- ‘নবী করীম (সঃ) এভাবে নানা প্রকারের উল্লেখ করেছেন, তাতে আমার এরূপ ধারণা জন্মেছে যে, আমাদের মধ্যে কারো কোন প্রকার মালের উপর দাবি থাকতে পারে না”।
হযরত উমর ফারুক (রাঃ) বলেছেন- “যে-যে বিষয়ে আজ আমার ধারণা জন্মেছে সে সম্পর্কে যদি প্রথম থেকে অনুরূপ ধারণা জন্মাতো- তাহলে আমি কখনও দেরি করতাম না এবং নিঃসন্দেহে ধনীদের অতিরিক্ত ধন এনে গরিব মুহাজিরদের মধ্যে বিলিয়ে দিতাম”।
হযরত আবু উবায়দা (রাঃ) ও তিনশত সাহাবা দ্বারা সত্য বলে গৃহীত বর্ণনা থেকে জানা যায়, কোন এক সময়ে যখন খাওয়া-পরার দ্রব্যাদির শেষ হওয়ার উপক্রম হয়, তখন হযরত রসূল করীম (সঃ) হুকুম দেন, ‘যার যা কিছু আছে,এনে উপস্থিত করো’। তারপর সমস্ত দ্রব্য এক জায়গায় জড়ো করে সকল কিছু তাদের মাঝে সমানভাবে বেঁটে সকলের জীবন ধারণের উপযুক্ত পরিমাণ বন্দোবস্ত করে দেন।
হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন- “ আল্লাহ্ তা’আলা ধনীদের ওপর গরিবের আবশ্যকীয় জীবিকা সরবরাহ করা ফরয করেছেন। যদি তারা (গরিবেরা) ভুখা থাকে, নগ্ন থাকে অথবা জীবিকার জন্য বিপদগ্রস্ত হয় তাহলে ধনীরা দায়িত্বশীল নয় বলেই বুঝতে হবে এবং সংকীর্ণতার জন্য তাদের শাস্তি ভোগ করতে হবে। নানাবিধ হাদীস ও কুরআন শরীফের দলীল দ্বারা মুহাদ্দিস ইবনে হাজম এ বিষয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছেন- “প্রত্যেক মহল্লার ধনীদের ওপর গরিব-দুঃখীদের জীবিকার জন্য জামিন (দায়ী) হওয়া ফরয (অবশ্য কর্তব্য)। যদি বায়তুলমালের আমাদানি গরিবদের জীবিকা সরবরাহের জন্য যথেষ্ট না হয়, তাহলে (সময়ের) শাসক বা আমীর (সামন্ততন্ত্রীয় অর্থে নয়) ধনীদিগকে এ কাজের জন্য বাধ্য করতে পারেন। অর্থাৎ তাদের মাল বলপূর্বক গরিবদের প্রয়োজনে ব্যয় করতে পারেন। তাদের জীবিকার সংস্থানের জন্য কমপক্ষে অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য জরুরি আবশ্যক অনুযায়ী ক্ষুধার অন্ন, পরিধানের বস্ত্র এবং ঝড়, বৃষ্টি, গরম , রোদ ও প্লাবন থেকে রক্ষা করতে পারে এমন বাসগৃহ”। কাজেই সর্ববস্থায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপাদিত শস্য কোন চাষী ইসলামী সমাজে মুনাফার জন্য ব্যবহার করতে পারে না। উদ্ধৃত্ত সবকিছুই তাকে সমাজের কল্যাণের জন্য ব্যয় করতে হয়।
ইসলামী সমাজের ভূমিনীতি
উপরের আলোচনা থেকে ইসলামী সমাজের ভূমি-নীতির ছ’টি সূত্র পাওয়া যায়ঃ
১.রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণেই ভূমির বিলি-ব্যবস্থা হবে। চাষীকে রাষ্ট্রের নিকট থেকে দানপত্র ভোগ-দখলের অধিকার হিসেবে অথবা রাষ্ট্রের অনুমতি নিয়ে অনুর্বর ভূমিকে আবাদের যোগ্য করে তাতে ভোগ-দখলের অধিকার পেতে হবে ।
২. যারা নিজেরা চাষাবাদ করে না, তাদের ভূমির ওপর ভোগ দখলের অধিকার নেই। এক্ষেত্রে ‘লাঙ্গল যার মাটি তার’ নীতিই গ্রহণীয় হয়েছে।
৩.রাষ্ট্রের বিবেচনায় কোনও কৃষকের জমি প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিবেচিত হলে রাষ্ট্রে অবাধে সেই জমিকে আয়ত্ত করে নিতে পারে।
৪.জমি থেকে উপস্বত্ব ভোগ করার অধিকার চাষীর আছে, তবে শোষণের কোন সুযোগ নেই।
৫. উৎপাদন ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবেও চলতে পারে।
৬.প্রয়োজনের অতিরিক্ত ফসল চাষীকে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়েই অপর গরিব লোকদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে হবে, তাতে ত্রুটি দেখা দিলে রাষ্ট্র আইন প্রয়োগে২১৮ তা কার্যকরী করতে পারে।
আধুনিক যুগে ইসলামী নীতির প্রয়োগ
বর্তমানকালে শুধু হাতের দ্বারা মানুষ কোন কাজই করতে পারে না। শিল্প-বিপ্লবের পরে জীবনযাত্রার প্রত্যেক কাজকর্মেই যন্ত্রের প্রয়োগে সল্প পরিশ্রমে প্রচুরতম উৎপাদন করা যায়। যন্ত্রপাতি প্রয়োগের আর একটি বিশেষ সুবিধা এই যে, তাতে ব্যক্তিজীবনের সুখ-দুঃখ, আরাম-ব্যারামের ফলে উৎপাদন-ব্যবস্থায় কোন তারতম্য হয় না।
উৎপাদন-ব্যবস্থায় যন্ত্রপাতি প্রয়োগ করতে গেলেই সংঘবদ্ধভাবে২১৯ উৎপাদন করতে হয়। কেননা, যন্ত্রপাতি প্রয়োগের জন্য বহু লোকের শ্রম ও তার বিভাগ দরকার। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে লাঙ্গল এক ব্যক্তি চালনা করতে সক্ষম। কিন্তু একটা ট্রাক্টর চালনা করতে হলে অনেক লোকের প্রয়োজন। লাঙ্গল দ্বারা জমি যে সময়ের মধ্যে এবং যেভাবে কর্ষিত হয় ট্রাক্টর দ্বারা তার কম সময়ে কর্ষিত হতে পারে। জমি ফসলের পক্ষেও উপযোগী হয় বেশি। এতে শ্রম ও সময় দু’ই ই বাঁচে।
দ্বিতীয়ত, সেচের বা বাঁধের জন্য সবসময় যন্ত্রপাতির সাহায্য নেওয়া অবশ্য প্রয়োজনীয়। আমাদের দেশে বর্তমানে যেভাবে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সেচ অথবা বাঁধের কাজ চলে তাতে জমির পক্ষে উপযুক্ত সেচ অথবা বাঁধের ব্যবস্থা করা হয় না।
কাজেই, এ যন্ত্রযুগে কৃষিকার্যের উন্নতির জন্য যে যন্ত্রের সাহায্য নিতেই হবে, যন্ত্রের সাহায্য নিতে গেলেই বহু লোকের সাহায্য ও সহযোগিতার দরকার। সুতরাং ব্যক্তিগতভবে উৎপাদন-ব্যবস্থার নীতি ত্যাগ করে সংঘবদ্ধভাবে উৎপাদন-ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে।
তার জন্য সর্বপ্রথম দরকার সমস্ত জমিকে রাষ্ট্রের করায়ত্ত করে লোকসংখ্যার অনুপাতে জমি বিলির ব্যবস্থা করা। জমি বিলিতে যারা চাষী, চাষ-আবাদ করে জীবিকা নির্বাহ করা যাদের জীবনের কাম্য, তাদের মাঝেই জমি বেঁটে দেয়া দরকার। পতিত অনাবাদী ‘বনজর’ জমিকে চাষ-আবাদ করার উপযুক্ত করে তোলার জন্য উৎসাহ দান করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের পক্ষে খাজনা না দিয়ে এসব জমি পত্তন করা উচিত। বাঁধ, সেচ অথবা যন্ত্রপাতি ক্রয় করার জন্য অগ্রিম টাকা ধারে দেওয়া কর্তব্য। প্রত্যেকটি গ্রামকে কেন্দ্র করে যাতে সমবায়মূলক পদ্ধতিতে২২০ উৎপাদন চলতে থাকে, তার জন্য একটি সরকারি বিভাগ খোলা উচিত। সেই বিভাগের প্রধান কাজ হবে চাষীদের সংঘবদ্ধভাবে উৎপাদনের জন্য প্রস্তুত করা। তারা যাতে যন্ত্রপাতির সাহায্যে অল্প শ্রমে অধিক উৎপাদনে সমর্থ হয় তার জন্য সংগঠনের ব্যবস্থা করা। চাষের পক্ষে উপযুক্ত যন্ত্রপাতি সংগ্রহ পূর্বে প্রয়োজনবোধে গরু-মহিষাদি দ্বারা হাল চালনা দরকার হলে প্রত্যেক গ্রামের জন্য কতক জমি গোচারণভূমি রিজার্ভ রাখতে হবে। উৎপাদিত শস্য যাতে কোন অবস্থায়ই নষ্ট না হয় তার জন্য প্রত্যেক গ্রামেই সরকারি খরচে একটি গোলা গড়ে তোলা দরকার। অতিরিক্ত শস্যাদি যাতে চাষীদের মুনাফা শিকারের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে না পারে তার জন্য প্রত্যেক সংঘের ওপর কড়া দৃষ্টি রাখতে পারে এরূপ নৈতিক চরিত্র-বলে উন্নত সরকারি কর্মচারী নিয়োগ প্রয়োজন।
সকলের উপরে প্রয়োজন মানুষের মন থেকে স্বার্থপরতা, নিচাশয়তা প্রভৃতি দূরীকরণের জন্য শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তন। রাষ্ট্রকে যাতে চাষী ভাইরা অপ্রয়োজনীয় মনে না করে, তার জন্য চাই রাষ্ট্রেরও তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার। আপদে-বিপদে রাষ্ট্র তাদের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে তাদের জীবনের সুখ-দুঃখের ভাগী হলে তবেই রাষ্ট্রের প্রতি তাদের দরদ ও সহানুভূতির সৃষ্টি হতে পারে।
ইসলামী সমাজে ব্যক্তিস্বাধীনতার নীতি স্বীকার করে নিয়েও কিভাবে শোষণের পথ বন্ধ করা যায় তার ব্যবস্থা নবী করীম (সঃ) ও প্রথম দুই খলীফার জীবন ও কার্যাবলি থেকে বিশেষভাবে পাওয়া যায়। বর্তমানে যুগের পুঁজিবাদী ও বস্তুতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার মাঝখানে সিরাতুল মুস্তাকিম হল ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা। সেখানে সাম্য-মৈত্রী ও স্বাধীনতার সমন্ব্য করা হয়েছে বলে ব্যক্তি স্বাধীনতার মৌলিক অধিকার স্বীকার করেও শোষণের পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অনাগত বিশ্বসংস্থা গড়ে উঠবে মানবিক অধিকারের এই নীতিকে স্বীকার করেই। ইসলাম চৌদ্দশত বছর পূর্বেই এ নীতিগুলোকে স্বীকার করে গড়ে তুলেছিল তার রাষ্ট্র, প্রতিকূল পরিবেশে তা টিকে থাকেনি সত্য কিন্তু সেদিন দূরে নয়, যখন আবার এ মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েই জগৎসভ্যতাকে হতে হবে অগ্রসর।
নবম পরিচ্ছেদ
ইসলামের বিকাশ
ইসলামকে ধারণা করা হয় পূর্ণ মানবতার ধর্ম বলে। মানবজীবনের সর্বাঙ্গিণ মঙ্গলের জন্য তার নানাবিধ সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করতে পারে বলেই ইসলামের সার্থকতা। ইসলামের ইতিহাসে কিন্তু দেখা যায়, যে পূর্ণ বিকশিত মানবজীবনের আদর্শ সম্মুখে রেখে ইসলাম উল্কার গতিতে অগ্রসর হয়েছিল, দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রাঃ)-এর খিলাফতের পরে তাতে প্রতিবিপ্লবের সূচনা দেখা দেয় এবং আমীর মুআবিয়ার হাতে ইসলামী রাষ্ট্র সম্পূর্ণ উল্টা দিকে চলতে শুরু করে। তার পরিণতিতে এখনও মুসলিম প্রধান দেশগুলোতে ইসলামের নামে চলছে অপব্যবহার। এখন তা হলে প্রশ্ন ওঠেঃ ইসলামের পক্ষে কি বিকাশের কোন সম্ভাবনা আছে? ইসলাম কি আবার সত্যিকার রূপ ফিরে পেতে পারে?
এ সম্বন্ধে অনেকেই সন্দিহান। এঁরা বলেন, ইসলামী রাষ্ট্রের এরূপ পরিবর্তনের মূলে দুনিয়ার অর্থনৈতিক কারণগুলো কার্যকরী। সে উৎপাদন ব্যবস্থার মূলে দুনিয়ার সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো যুগে যুগে পরিবর্তিত হচ্ছে, ইসলামের মধ্যেও তার ছাপ পড়েছে। কাজেই, সামন্ততন্ত্রের যুগে ইসলামী রাষ্ট্রের যে রূপ ছিল, ধনতন্রের যুগে তার সে রূপ থাকেনি। সমাজতন্ত্রের যুগে আবার তার জন্য অন্য রূপ দেখা দিতে বাধ্য। ইসলামের নানাবিধ সমাধান থেকে নজির তুলে বলা হয়, ইসলাম মধ্যযুগে সে সমাধান দিতে সক্ষম হয়েছিল, বর্তমানে যুগে তাতে আর কৃতকার্য হতে পারবে না। কেননা সমাজতন্ত্রের যুগে ইসলাম যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল-বর্তমান কালের মত সেগুলো এত জটিল ছিল না। দুনিয়ার পুঁজিবাদের উত্থানের ফলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে সে সময় এরূপ পরিস্থিতি ছিল না বলে ইসলামের পক্ষে তা সম্ভব হয়েছে। এখনকার বিরূপ পরিস্থিতিতে তা সম্ভব নয়।
প্রথমেই আমাদের বিচার করতে হবে- ইসলাম বলতে ওঁরা কি মনে করেন। ইসলাম একাধারে এক ধর্মবিশ্বাস, দার্শনিক মতবাদ, জীবন-পদ্ধতি। ইসলাম জীবনকে গ্রহণ করেছে পূর্ণভাবে। তাই মানবজীবনের নানাবিধ সমস্যার সমাধানে তৎপর হয়েছে। একথা অবশ্য সত্য যে, অর্থনৈতিক বা অন্যান্য কারণে দুনিয়ার পরিস্থিতি যুগে যুগে ভিন্ন রূপ ধারণ করে। তবুও বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্যে মানুষের সত্যিকার রূপের কোন পরিবর্তন হয়নি,হতে পারে না। মানুষ গোড়াতে ক্ষুধা-তৃষ্ণার তাড়নায় অধীর হত, বর্তমানেও হয়। মানুষের মধ্যে তখনও কাম-প্রবৃত্তি সহজ ছিল-বর্তমানেও রয়েছে। অপত্য-স্নেহ সুখচারী প্রবৃত্তি২২১ প্রভৃতি যেমন ছিল, বর্তমানেও রয়েছে। সেগুলোর পরিতৃপ্তিতে হয়ত পদ্ধতির পরিবর্তন হতে পারে কিন্তু তাদের সত্যিকার রূপের কোন পরিবর্তন হয়নি। মানুষের স্বভাবের যদি কোন পরিবর্তন না হয়, তাহলে তার বিকাশের উপায় ও পথের পরিবর্তন হলেও তাতে কিছু যায় আসে না।
ইসলাম চায় মানবজীবনের সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক বিকাশ, সে বিকাশের পক্ষে অনুকূল পরিস্থিতিতে ইসলাম তার মূলনীতি পরিত্যাগ না করে যে কোন পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারে।
ইসলামে এক আদর্শ রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনের জন্য তাকিদ রয়েছে। সে আদর্শ রাষ্ট্রের ভিত্তিপ্রস্তর হযরত রসূলে আকরম (সঃ) স্থাপন করেছিলেন। দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রাঃ)-এর খিলাফতের সময় সে রাষ্ট্র বিশেষ বিকাশ লাভ করে। আমীর মু’আবিয়ার কার্যকারিতার ফলে তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রাঃ)-এর খিলাফতের সময় প্রতিবিপ্লবের বীজ উপ্ত হয় এবং আমীর মু’আবিয়ার শাসনকালে তা সম্পূর্ণ উল্টা দিকে ধাবিত হয়। তাই ইসলামের রাষ্ট্রীয় আদর্শ সম্পূর্ণ রূপায়িত হতে পারেনি।
প্রতিপক্ষ ইসলামী রাষ্ট্র বলতে বিভিন্ন কালের মুসলিম রাষ্ট্রকে মনে করে এক মস্ত বড় ভুল করে থাকেন। ইসলামের মূলনীতি আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব২২২ ও মানুষের প্রতিনিধিত্ব২২৩। এই দুই ভিত্তি ব্যতীত গঠিত কোন রাজ্য বা রাষ্ট্রকে ইসলামী রাষ্ট্র বলা যায় না। কাজেই ইসলামের নামে ব্যক্তিগত বা বংশগত আধিপত্যের যাঁরা প্রতিষ্ঠা করেছেন তাঁদের রাজ্যকে কিছুতেই ইসলামী রাষ্ট্র বলা যায় না। গ্রানাডার মুরদের, ভারতীয় মোগল বা উসমানী তুর্কিদের রাজ্যকে কিছুতেই ইসলামী বলা যায় না। তাদের রাজ্যগুলো ইসলামী রাষ্ট্র নয় বলেই বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে এ প্রভাব বাড়তে পারে না। কারণ ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনীতিকে কোন ছকের মধ্যে ফেলা যায় না। তাকে সামন্ততন্রীয়, ধনতন্ত্রীয় বা বস্তুবাদী সমাজতন্ত্রীয় বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। দুনিয়ার বুকে যেসব অর্থনৈতিক অসামঞ্জস্যের দরুন এসব মতবাদের সৃষ্টি হয়েছিল ইসলাম গোড়াতেই সে অর্থনীতিকে বর্জন করে এমন এক অর্থনৈতিক মতবাদ গ্রহণ করেছে,যার ফলে মানবসভ্যতাকে সামন্ততন্ত্র, ধনতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র নামক বিভিন্ন ধাপ ডিঙিয়ে অগ্রসর হতে হয় না। মানবজীবনের পূর্ণ বিকাশের পক্ষে অনুকূল অর্থনীতি গ্রহণ করার ফলে একই সূত্র ধরে সে অগ্রসর হতে পারে। ইসলাম যে আদর্শ রাষ্ট্র গঠনের নীতি নির্ধারণ করেছিল, তারই আলোকে বর্তমানে বা অদূর ভবিষ্যতে সে রাষ্ট্র রূপায়িত হওয়ার বিস্তর সম্ভাবনা করেছে। এ সম্বধে শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলভী বা মাওলানা উবায়েদ উল্লাহ সিন্ধির বক্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তাঁদের দুজনের কাছেই ইসলামী রাষ্ট্র একটি আদর্শ জীবনসংস্থা, যা এখনও সম্পূর্ণ রূপায়িত হয়নি, ভবিষ্যতে হতে বাধ্য।
সে আশা আমরা পাই ইসলামের প্রতিকৃতির মধ্যে। সে প্রতিকৃতি সফল হতে বাধ্য। কারণ ইসলামের পরিস্থিতিতে তার বিকাশের পক্ষে অনুকূল পদ্ধতি গ্রহণ করার সুবিধা রয়েছে। সকলেই জানেন, ইসলামী আইন-কানুনের বুনিয়াদ চারটি স্তরের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ্র বাণী কুরআনের বাণীর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে যেসব কথা বলেছিলেন বা যেসব কাজ করেছিলেন পরবর্তীকালে তা-ই হাদীস হয়ে পড়ে। কুরআনের আদেশ-নিষেধ ব্যতীত হাদীসের আইন-কানুনগুলোও ইসলামপন্থীর পক্ষে অবশ্য পালনীয়। ইসলামী আইনের তৃতীয় স্তম্ভ ইজমা বা সর্বসাধারণ মুসলিম কর্তৃক গৃহীত আইন এবং চতুর্থ কিয়াস। এ চারটি উৎস থেকেই পরবর্তীকালে ফিকাহ শাস্ত্র গড়ে ওঠে। ইসলামের পতন যুগে যুক্তিকে অগ্রাহ্য করে এই চারটি উৎসের মধ্যেই আইন-কানুনকে সীমাবদ্ধ করা হয়। তবুও আনন্দের কথা এই যে, ইসলামের মধ্যেই রয়েছে বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগের তাকিদ। এই বিচার-বুদ্ধির আলোকে মুসলিম মানস সর্বাবস্থায় চিন্তা করার প্রয়াস পেয়েছে এবং নতুন পরিস্থিতিতে পুরাতন জীবনকে আবার নতুন জ্ঞানের আলোকে দেখবার জন্য সচেষ্ট হয়েছে। জাতিগত না হলেও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার মধ্যে মুসলিম মানসের সে পরিচয় রয়েছে ইতিহাসের পৃষ্ঠায়। হিজরী শতকের মধ্যভাগ থেকে চতুর্থ হিজরীর সূচনা পর্যন্ত মুসলিমদের মধ্যে উনিশটি আইন সংক্রান্ত মতবাদের সৃষ্টি হয়েছিল এবং তাদের প্রেরণার উৎস ছিল ইজতিহাদ।
প্রশ্ন করেন, ‘যদি আল্লাহ্র রসূলের জীবন থেকে পূর্ববর্তী কোন উদাহরণ না পাও? তার উত্তরে মা’আজ বলেন, তাহলে আমি আমার বিচার-বুদ্ধির প্রয়োগ করবো’। তাঁর এ উত্তরে আল্লাহ্র রসূল (সঃ) বিশেষ সন্তোষ লাভ করেন।
এ ইজতিহাদের জোরে ইসলামপন্থীরা নানা যুগে জীবন সমস্যার সমাধান করতে সমর্থ হয়েছে। চারটা সুন্নী মতবাদ, অসংখ্য শিয়া মতবাদের উৎপত্তি ও স্থায়িত্বের পরে মুসলিম-মানস যুগে যুগে জীবনকে আবার নতুন করে দেখবার চেষ্টা করেছে।
এ জন্যেই বোধ হয় এ যুগের মনীষী জর্জ বার্নার্ড শ’র মত সূক্ষ্ম সমালোচক বলতে বাধ্য হয়েছেন- “ It is the only religion which appears to me to prosses assimilating capacity to the changing phase of existence which can make its appeal to every age. I believe if a man like Mohammad were to assume the dictatorship of the world, he would succeed in solving the problem in a way that would bring in much needed peace and happiness.”
বুদ্ধির প্রয়োগের দ্বারা যদি যুগে যুগে পরিবর্তিত অবস্থার মধ্যে নানবিধ সমস্যার সমাধান করার সুবিধা ইসলামের মধ্যে থাকে, তাহলে মৌলিক নীতি পরিত্যাগ না করে এ পরিবর্তনের যুগেও উপায় ও পদ্ধতি গ্রহণের বেলায় ইসলাম ইজতিহাদের সাহায্য নিতে পারে। ইসলামের পক্ষে তাই কোন পরিস্থিতিতেই অবরুদ্ধ থাকার কোন কারণ নেই। প্রায় চৌদ্দ শত বছর আগে বছর ত্রিশেক বিকশিত হয়ে তার গতি রোধ হলেও বর্তমান পরিস্থিতিতে ইজতিহাদকৃত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বা রাজনৈতিক কাঠামো তৈরি তার পক্ষে খুবই সম্ভব-এইটেই সবচেয়ে বড় আশার কথা।
দশম পরিচ্ছেদ
অনাগত বিশ্ব-সংস্থা ও ইসলাম
দুনিয়া আজ শতধা-বিচ্ছিন্ন। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, ব্যক্তিতে রাষ্ট্রে এবং রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে চলছে অবিরাম সংগ্রাম। এ সংগ্রাম আপাতত বিভিন্ন মানুষের জাতীয় সংগ্রাম বলে মনে হলেও আসলে তা মতবাদেরই সংগ্রাম-মানব জীবনকে বিভিন্ন সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার ফলে যে একদেশদর্শী মতবাদের সৃষ্টি হয়, তার ফলে ভিন্নমত পোষণকারী লোকদের মধ্যে শুরু হয় ভীষণ যুদ্ধ।
আধুনিক কালে ধনতন্ত্র ও বস্তুবাদী সমাজতন্ত্রের সংঘর্ষে দুনিয়ার আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠেছে। ধনতন্ত্রের দার্শনিক ভিত্তি ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদে। তার গোড়ার কথা প্রত্যেক মানুষের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সমষ্টি থেকে তার পার্থক্য। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের মূলে রয়েছে ব্যষ্টির স্বার্থপরতার স্বীকৃতি। সমাজতন্ত্রের দার্শনিক ভিত্তি পরার্থপরতা। ধনতন্র স্বার্থপরতাকেই মানুষের আদি ও কৃত্রিম মনোবৃত্তি বলে মেনে নিয়েছে। সমাজতন্ত্র তার স্বার্থপরতাকে স্বাভাবিক প্রধান বৃত্তি বলে গ্রহণ করেছে। বর্তমান জগতের এ সংগ্রামের মূলে রয়েছে মানুষের এক বৃত্তির সঙ্গে অপর বৃত্তির সংগ্রাম। বিশ্লেষণ করলে স্পষ্টই বোঝা যায়, এই দ্বন্দ্বের মূলে (১) মানব জীবন সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা, (২) তারই অবশ্যম্ভাবী ফল ভুয়া অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যান্য দাবি, (৩) প্রকৃত মৌলিক অধিকারগুলোর মাঝে সমন্বয়ের ব্যর্থতা, (৪) জ্ঞানের রাজ্যে সামঞ্জস্যের অভাব।
১. ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের সমাজের আদি-উপকরণরূপে ব্যষ্টির সত্তাকেই স্বীকার করে নেওয়া হয়ছে। মতের সামান্য ভিন্নতা সত্ত্বেও ইংরেজ দার্শনিক লক থেকে শুরু করে এ্যাডাম স্মিথ পর্যন্ত যে চিন্তাধারা পাওয়া যায়, তার সারসংক্ষেপ এই বলা যায়ঃ মানুষের চিন্তারাজ্যে চলেছে অণুর খেলা। একটা সংবেদন অন্য একটা সংবেদন২২৪ থেকে ভিন্ন। একটা ধারণা অপর ধারণা থেকে ভিন্ন। একটা অণু অন্য একটা অণু থেকে ভিন্ন। অনেকগুলো ধারণার কার্যকারিতার ফলে গড়ে ওঠে মনোজগৎ। আবার অনেকগুলো অণুর সমবায়ে সৃষ্টি হয় জড়জগৎ। তেমনি সমাজে বা রাষ্ট্রে চলেছে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বা প্রাধান্যের চেষ্টা। মানুষ সর্বদাই একক। সেই একক মানুষের সঙ্গে অন্যান্য মানুষের সংস্পর্শে গড়ে ওঠে তার সমাজ, জাতি বা রাষ্ট্র। মানুষের আদি সত্তায় রয়েছে অহংবোধ ও স্বার্থপরতা।
তাই সেই আদি মানুষের চলাফেরা, ব্যবসা-বাণিজ্য, চিন্তাধারায় অবাধ স্বাধীনতা দিতে হবে। তার কাজ-কর্ম বা গতিবিধিতে যাতে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না হয়, তার প্রতি লক্ষ্য রেখেই রাষ্ট্র গড়ে উঠবে। ফরাসি দার্শনিক রুশো এ মতবাদের বিরোধিতা করলেও তাঁর মতবাদও ব্যষ্টিকেন্দ্রিক। শুধু পার্থক্য এই যে, লক প্রমুখ ইংরেজ দার্শনিক মানবমনের মননশীলতার ওপর জোর দিয়েছেন, রুশো গুরুত্ব আরোপ করেছেন তার প্রক্ষোভের ওপর। তিনি আক্ষেপের সঙ্গে বলেছেন, ‘মানুষ স্বাধীন হয়েই জন্মগ্রহণ করে; কিন্তু সে সর্বত্রই শিকলাবদ্ধ থাকে’। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের ওপর কোন আইন-কানুন চাপানো যায় না। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে নানা আইন মেনে চলতে হয় এবং তার ফলে তার জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। রুশো মানুষকে আবার তার স্বাভাবিক ধর্মে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আহ্বান করেছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল, প্রকৃতির কোলে স্বাভাবিক পরিবেশে মানুষের প্রক্ষোভ পূর্ণ বিকাশ লাভ করতে পারে। অপ্রাকৃত মানব-সৃষ্ট পরিবেশে তা হওয়া সম্ভব নয়। প্রকৃতিতে পশু, পাখি কারো কোন দুঃখ-দৈন্য নেই। তারা অবাধে বিহার করে। তাদের অভাবেরও কোন তাড়না নেই, কারণ অভাবের উৎপত্তি হলেই তারা নিবৃত্তির উপায়ও তার পক্ষে সহজলভ্য। মানুষ তার বুদ্ধির প্যাঁচে গড়ে তুলেছে তার সমাজ, তার রাষ্ট্র, নানবিধ আচার-অনুষ্ঠান। এতে মানবজীবনের পরিপূর্ণ স্ফূর্তি লাভ হয় না বলেই জীবনে দুঃখের হয় উৎপত্তি। তার ধারণা ছিল, প্রকৃতি থেকে বিকাশের ধারায় কোন এক সময়ে মানুষকে তার জন্মগত স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে হয়। তার আত্মরক্ষার জন্য অন্য মানুষের সঙ্গে মিলিত হয়ে সে গড়ে তোলে তার গোত্র, সম্প্রদায় ও রাষ্ট্র। রুশোর জীবনে তাই সর্বপ্রধান সমস্যা ছিল অন্যান্য লোকের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে রাষ্ট্র গঠন করেও ব্যষ্টি কিভাবে তার স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা বজায় রাখতে পারে তার উপায় উদ্ভাবন।
মানুষের সত্যিকার স্বরূপ সম্বন্ধে এতে যে কল্পনা-প্রবণতা স্থান পেয়েছে তা সহজেই বুঝতে পারা যায়। ইতিহাসের ধারার আলোচনা করলেই দেখা যায় মানুষ কোনকালেই একক ছিল না। তার উৎপত্তি যেভাবেই হোক না কেন সে স্বভাবতই যূথচারী জীব। অন্যের সংশ্রব ও সংস্পর্শ ব্যতিরেকে সে এক মুহূর্তেও তিষ্ঠাতে পারে না। শরীরের মধ্যে যেমন বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের একত্র সমাবেশের ফলে শরীরযন্ত্র কার্যক্ষম থাকে, তেমনি বিভিন্ন মানুষের সমবায়মূলক কার্যকারিতায় গড়ে ওঠে মানুষের সমাজ, তার রাষ্ট্র। তলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারা যায়,মানুষের চিন্তাধারায় যুগ-যুগান্তর মননের রয়েছে স্পষ্ট ছাপ, বহু যুগের বিবর্তন। সে কোন সময়েই সম্পূর্ণ একা নয়।
আপাতদৃষ্টিতে ষড়রিপু মানুষকে সমষ্টি-চেতনা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। কাম, ক্রোধ প্রভৃতি রিপু ব্যক্তিকে অন্য দশজন মানুষ থেকে পৃথক করে বলেই আমাদের ধারণা। বাস্তবিক পক্ষে তা নয়। কাম রিপু স্বভাবতই বহির্মুখী। একেবারে নিছক বিকল্প না হলে আপনার দেহেই কেউ মজে থাকতে পারে না। আত্মকাম সুস্থ মনের লক্ষণ নয়। কাম জাগৃতিক সময়২২৫ থেকেই বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গ কামনা মনের মাঝে স্ফুরিত হয়। সে ব্যক্তির সংশ্রবে যে তৃতীয় জীবের সৃষ্টি হয় তার উপর নারী, পুরুষ উভয়ের গরজ হয় কেন্দ্রীভূত।
যে কোন রিপু নিয়েই আলোচনা চলুক না কেন, আমাদের বাধ্য হয়েই স্বীকার করতে হয়, নিছক আত্মকেন্দ্রিক ভোগসর্বস্ববাদ বলে দুনিয়ায় কিছু নেই। ব্যক্তি নিয়ে রওয়ানা দিলে তার পরিণতি সমষ্টিতে এসে থামতে হয়। কাজেই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ যেমন ধরে নেয়া হয়, ব্যক্তিমাত্রেই একক২২৬ বাস্তবিক পক্ষে দুনিয়ার বুকে তেমন কোন ইউনিট নেই।
অপরদিকে বস্তুতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রে যেভাবে ইউনিট হিসেবে শ্রেণীগুলোকে নেয়া হয়েছে, তাও এক মহাভ্রান্তির ফল। বস্তুতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদের পিতা কার্ল মার্কস ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর শোষণের ভয়াবহ রূপ দেখে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মূল উচ্ছেদ করার জন্য তিনি তাকে পুঁজিবাদের উৎস বলে ধরে নিয়েছেন।
বাস্তবিক পক্ষে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যবোধ শোষণের কোন কারণ হতে পারে না। দুনিয়ায় যাঁরা মনীষী, মননধর্মী, যাঁদের গবেষণার ফলে দুনিয়ার প্রগতি হয়েছে সম্ভবপর-তাঁরা সকলেই ছিলেন আত্মপ্রচারবাদী কিন্তু কেউই স্বার্থপর ছিলেন না। মননধর্মী মানুষমাত্রেরই স্রষ্টা হিসেবে বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে, কিন্তু তাই বলে তাঁরা স্বার্থপর নন।
কাজেই বস্তুতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদীরা যেভাবে মনে করেন ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যবোধ, স্বার্থপরতা এক ও অবিভাজ্য- তা কোন মতেই মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে টিকতে পারে না।
স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতার মধ্যে কোন মৌলিক প্রভেদ নেই। তাদের সবসময়ই আপেক্ষিকতার সূত্রে বিচার করতে হয় । কোন ব্যক্তি যখন কেবল তার নিজের সুখ-সুবিধার জন্যই মরিয়া হয়ে পরিশ্রম করে, তখন তাকে বলা হয় স্বার্থপর। আবার সেই ব্যক্তিই যখন তার পরিবারের জন্য পরিশ্রম করে তখন তাকে বলা হয় পরার্থপর। তার ঐ পরার্থপরতা ও কওমের পরার্থপরতার তুলনায় স্বার্থপর ও সংকীর্ণ, যে স্বদেশ-প্রেমিক স্বজাতি ও স্বদেশের মঙ্গলের জন্য হাসিমুখে আত্মোৎসর্গ করে, তাকে বলা হয় নিঃস্বার্থ ব্যক্তি, কিন্তু বিশ্বপ্রেম ও বিশ্বমৈত্রীর তুলনায় তাও অকিঞ্চিৎকর।
মানুষের জীবন এক ও অবিভাজ্য। মনে হয় স্বার্থপরতার সৃষ্টি সংস্কৃতি ও বৈদগ্ধের ফলে তারই হয় প্রসার। তখন আত্মকেন্দ্রিক সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ত্যাগ করে সে বৃহত্তর সত্তার মধ্যে তার আত্মার দোসর খুঁজে পায়। আমাদের সকল শিক্ষারই আসল লক্ষ্য মনের সম্প্রসারণ।
২. সমাজে বা রাষ্ট্রে প্রাথমিক ইউনিট, না সমষ্টিই প্রাথমিক সংখ্যা- এ প্রশ্নের মীমাংসার পর রাষ্ট্রের স্বরূপ সম্পূর্ণ নির্ভর করে। ব্যষ্টির দাবি অগ্রগণ্য হলে দুনিয়ার সমস্ত অধিকার ব্যষ্টির হাতেই ছেড়ে দিতে হয়। অপরপক্ষে সমষ্টির দাবি প্রধান হলে ব্যষ্টির অধিকার বলে কিছুই থাকে না। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ব্যষ্টিকেই আদি সংখ্যা হিসেবে গণ্য করায় দুনিয়ার সম্পদের ওপর ব্যষ্টির অখন্ড অধিকার স্বীকার করে নিয়েছে। অপরদিকে সমাজতন্ত্রবাদে ব্যষ্টির কোন অস্তিত্বই স্বীকার করা হয় না। কাজেই সমাজতন্ত্রবাদের মতানুযায়ী রাষ্ট্র গঠিত হলে সেখানে ব্যষ্ট্রি স্বীকৃত অধিকার বলে কোন কিছু থাকে না। প্রকৃতপক্ষে ব্যষ্টি ব্যতীত সমষ্টি একটা সাধারণ ধারণা মাত্র, আবার সমষ্টি-জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যষ্টি-জীবন কল্পনাই করা যায় না। উভয়েই উভয়ের পরিপূরক ও পরিবর্ধক। আমরা পূর্বেই দেখেছি, ব্যক্তি-জীবনে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যে স্থান, সমষ্টি-জীবনে ব্যষ্টিরও সেই স্থান। কাজেই ব্যষ্টি বা সমষ্টির স্বার্থ পরস্পরবিরোধী নয়। অথচ দুনিয়ার ইতিহাসের পাতায় পাতায় রয়েছে ব্যষ্টি ও সমষ্টির দ্বন্দ্বের রক্তচিহ্ন।
ব্যষ্টি ও সমষ্টির বিরুদ্ধ ও বৈরীভাবের পরেই বর্তমানে চলছে দুনিয়ার হত্যাকাণ্ড। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় স্বীকৃত হয়েছে ব্যষ্টির একমাত্র অধিকার, অপরপক্ষে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ব্যষ্টির অধিকার করা হয়েছে সম্পূর্ণ বিলোপ।
ব্যষ্টি ও সমষ্টির এ ভুয়ো দ্বন্দ্বের তখনই নিরসন হতে পারে, যখন তাদের প্রকৃত স্বরূপের আলোকে তাদের অধিকারের ব্যবস্থা করা হয়। ব্যষ্টি ও সমষ্টির স্বার্থ যদি প্রকৃতপক্ষে পরস্পরবিরোধী না হয়, তাহলে তাদের এ মৌলিক পার্থক্য অস্বীকার করার সঙ্গে তাদের ভুয়ো অধিকার বিলোপ করাও প্রয়োজন।
৩. ব্যষ্টি বা সমষ্টির অধিকার ভুয়ো হলে মানব জীবনে কতকগুলো মৌলিক অধিকার সর্বত্রই স্বীকৃত হয়েছে, যে সকল অধিকারের বলে মানুষ ব্যক্তিজীবনে বা সমাজজীবনে পূর্ণ বিকশিত হতে পারে তাদের মধ্যে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা সর্বপ্রধান। ফরাসী রাষ্ট্র-বিল্পবের পর থেকে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে মানুষের মৌলিক অধিকার বলে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। নিতান্ত দুঃখের বিষয়, আধুনিককালে দুনিয়ার বুকে এমন কোন রাষ্ট্র গঠন সম্ভব হয়নি, যাতে মানবজীবনের এই তিনটি মৌলিক অধিকারের সমন্বয় সাধন সম্ভবপর হয়েছে। কোথাও স্বাধীনতার নামে সাম্য ও মৈত্রিকে দেয়া হয়েছে বলিদান-কুরবানী, সাম্য ও মৈত্রীর জন্য স্বাধীনতাকে দেয়া হয়েছে বিসর্জন।
একথা অবশ্য সত্য যে, রাষ্ট্র গঠিত হলে তার একটা নিজস্ব শক্তি সঞ্চিত হয় এবং তার নিজস্ব একটা অস্তিত্বের সৃষ্টি হয়। গনতন্ত্রমূলক রাষ্ট্রেও রাষ্ট্রের একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের অস্তিত্ব স্বীকার করে নেয়া হয়। সেখানে যে কোন ব্যক্তিকে যা’তা করতে দেবার অধিকার দেয়া হয় না। তার গতিবিধি কার্যকলাপ অনেক স্থলেই রাষ্ট্র কতৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। এমন যে অবাধ স্বাধীনতার মন্ত্র বা ‘একা থাকতে দাও’ নীতি সেখানেও ব্যষ্টিকে অবাধ উৎপাদন ও যদৃচ্ছ বণ্টনের স্বাধীনতা দেয়া আপাতত স্বীকৃত হলেও তার মধ্যে নানা শর্ত আরোপ করা হয়। পুঁজিবাদী দেশগুলোতেও রাষ্ট্রের পক্ষে অকল্যাণকর কোন দ্রব্য কোন ব্যক্তিকে বা প্রতিষ্ঠানকে উৎপাদন করবার স্বাধীনতা দেয়া হয় না।
কাজেই সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতাকে আপক্ষিকভাবেই গ্রহণ করতে হবে। যেসব দেশে মানুষের জীবনের ক্ষেত্রে রয়েছে অপেক্ষাকৃত বেশী স্বাধীনতার সুযোগ সেগুলোকে বলতে হবে- স্বাধীনতার সুযোগদানকারী। আর যেসব রাষ্ট্রে জীবনযাত্রার প্রাথমিক চাহিদা পূরণের ব্যাপারে ইতর-ভদ্র ভেদাভেদ নেই, সেখানে সাম্যবাদ বা মৈত্রী ফলে উঠেছে বলেই ধরে নিতে হবে।
বর্তমানকালে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোতে সাম্য ও মৈত্রী বলতে কিছুই নেই। অপরদিকে বস্তুতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রীয় রাষ্ট্রে স্বাধীনতাকে অত্যন্ত সংকুচিত করা হয়েছে। দুনিয়ার বুকে আব্র শান্তি ফিরিয়ে আনতে হলে এমন কোন সমাজ বা রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রবর্তনের দরকার যাতে সাম্য ও মৈত্রীর স্বাধীনতাও পাশাপাশি স্থান পায়।
৪.মানব জীবনের জ্ঞানের ক্ষেত্রগুলোকে পৃথকীকরণের ফলে মানব সভ্যতার ইতিহাসে হয়েছে একটা বিকট দ্বন্দ্বের উৎপত্তি। মধ্যযুগে যাজক সম্প্রদায় সর্বসাধারন মানুষের ওপর অকথ্য নির্যাতন করতো বলে রাষ্ট্রকে চার্চ থেকে পৃথক করার নীতি গৃহীত হয়। সে নীতি এখনও দুনিয়ার বুকে চালু রয়েছে। ইতালির রেনেসাঁয় তার সূচনা হয়। জার্মানিতে রিফরমেশন সে চিন্তাধারা আরো বিকাশ লাভ করে এবং ফরাসি রাষ্ট্রবিপ্লবে তা’ পূর্ণ পরিণতি লাভ করে।
এর ফলে যাজকের অন্তর্ধানে সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের প্রভাব থেকেও রাষ্ট্র মুক্তি পায়। মানব-মনের আদিম বৃত্তি ধর্মপ্রবণতা থেকে রাজনীতি বিচ্ছিন্ন হওয়ার রাজনৈতিক জীবনে নানাবিধ দুর্নীতি অবাধে প্রবেশ করে।
প্রত্যেক ধর্মের মধ্যেই রয়েছে কতকগুলো নৈতিক আইন, যেগুলোর প্রয়োগ নির্ভর করে প্রয়োগকারীর ব্যক্তিগত চরিত্রের ওপর। সে উন্নত চরিত্রের লোক হঁলে সেই নৈতিক আইনগুলো সমাজ-জীবনকে উচ্ছৃঙ্খলতার পঙ্কিল প্রবাহ থেকে মুক্ত রাখে। অপরদিকে প্রয়োগকারী স্বয়ং দুষ্কৃতকারী হলে সমাজজীবনে চলে অন্যায় ও অবিচারের বন্যা।
মধ্যযুগীয় যাজক সম্প্রদায় নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির বাসনায় উন্মত্ত হয়ে পড়লে রাষ্ট্রকে তাদের প্রভাব থেকে মুক্ত করার অদম্য উৎসাহে ধর্মের প্রভাব থেকেও রাজনীতিকে মুক্ত করার হয়েছে। তার ফলে ব্যক্তিগত জীবনে যেসব নীতি অবশ্য পালনীয় বলে সবাই একবাক্যে স্বীকার করে, রাজনীতিতে সে সব নীতি মোটেই গ্রহণীয় হয় না। অনেকেই রাজনীতিকে ধর্মের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করার উৎসাহে বলে থাকেন, “সীজারের যা প্রাপ্য সীজারকে দাও, খোদার প্রাপ্য খোদাকে দাও”। ভেবে দেখবার বিষয়-এভাবে মানব-মনকে কি দুটো কামরায় ভাগ করা যেতে পারে? যে ব্যক্তি সীজারের প্রাপ্য সীজারকে দিতে চাইবে, তার মনের নিভৃত কোণে কি এ প্রশ্ন জাগবে না? বাস্তবিকপক্ষে সীজারের প্রাপ্য কি আল্লাহ্কে বঞ্চিত করার ওপরই নির্ভর করে? কেবল রাষ্ট্র-জীবনকে ধর্ম-জীবন থেকে পৃথক করার ফলেই দুনিয়ার অশান্তির আগুন জ্বলে ওঠে না। জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত না হলেও তাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বে মানব-জীবন নানা অশান্তির সৃষ্টি হয়। ধর্মজতৎ, কর্মজগৎ, মনোজগৎ, বাইরের জগৎ, অন্তরের জগৎ- যে কোন জগতেই হোক না কেন সকল জগতে একই জীবন, একই মন থাকে ক্রিয়াশীল। জ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে যোগসূত্র ও সামঞ্জস্যের সৃষ্টি না হলেও তাতে নানা সংঘর্ষ বাধে। তার ফলে ব্যক্তিজীবনে বা সমাজজীবনের ভারসাম্য হয় নষ্ট।
জ্ঞানের রাজ্যে সামঞ্জস্যের সৃষ্টি করতে হলে জ্ঞানের সবগুলো সিদ্ধান্তের মধ্যে সংহতি সৃষ্টি হওয়া দরকার। সেই সংহতির আলোকে জীবনের নানাবিধ সমস্যার সমাধান হলে তবেই মানবজীবনে শান্তি ও স্বস্তি ফিরে আসতে পারে।
কোন ব্যক্তির জীবনে পরস্পরবিরোধী ভাবধারা বর্তমান থাকলে বুঝতে হবে, তার জীবনে রয়েছে সংহতির অভাব। সেরূপ সমাজজীবনে নানাবিধ বিরোধী ভাবের সৃষ্টি হলেও সেই জীবনে জ্ঞানের মধ্যে সামঞ্জস্যের সৃষ্টি হয় নাই বলে স্বীকার করতে হবে।
তাই মানবজীবনে শান্তি ফিরিয়ে আনতে হলে মানবজীবনকে গভীরভাবে পাঠ করতে হবে সর্বপ্রথমে। খোলা মন নিয়ে তার জীবনের প্রতিটি দিককে তলিয়ে দেখতে হবে।
এ ব্যাপারে অবরোহ পদ্ধতিতে আমাদের অগ্রসর হতে হবে। মানবজীবন সম্বন্ধে কোন এক স্বতঃসিদ্ধকে ধ্রুব সত্য বলে প্রথমে ধরে নিয়ে আরোহ পদ্ধতিতে কোন সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছলে পূর্বতন ভুলেরই পুনরাবৃত্তি হবে।
মানবজীবনের ছোটখাটো তুচ্ছ অভিজ্ঞতা ও উপকরণকে স্বীকার করে তারই ভিত্তিতে সঠিক সত্যে উপনীত হওয়াই জ্ঞানের চরম লক্ষ্য। মানবজীবনের বিভিন্ন জ্ঞানের ক্ষেত্রে এভাবে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত এসে পৌঁছে, সেগুলোর মধ্যে সংহতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে যেসব নীতি বা সত্তাকে স্বীকার করে প্রয়োজন তাকে কার্যকরী সিদ্ধান্ত হিসেবে ধরে নিয়ে হতে হবে অগ্রসর। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বর্তমানকালের পদার্থবিদ্যার সিদ্ধান্ত অনিশ্চয়তাবাদের সঙ্গে জীববিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের সামঞ্জস্য বিধান করতে গেলে কী পাওয়া যায়? অনিশ্চয়তাবাদের পরমাণুর মধ্যে এক সাশ্রয়ী লীলাই আবিষ্কৃত হয়েছে, অপরদিকে জীববিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত অনুসারে শক্তিমানের উদ্বর্তন ও জীবনযুদ্ধের সূত্র ধরেই জীবন চলছে তার বিকাশের পথে। এ দুটো মতবাদকে সুসমঞ্জস করে তুলতে হলে আমাদের ধরে নিতে হবে-বিশ্বের আদিতে রয়েছে এক সাশ্রয়ী শক্তির স্থিতি-সেই শক্তিই জড় পদার্থরূপে, জীবনরূপে ক্রমবিকাশের ধারায় নানাবিধ মান সৃষ্টি করে চলছে।
তার সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের বা সমাজবিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলো যুক্ত করলে সেই পূর্বেকার সার্বিক সিদ্ধান্তকে আরও ব্যাপক আকারে পরিবর্ধিত করতে গেলে এবং তাদের নিদ্দগিএ সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করলে, সে সিদ্ধান্তের আরও পরিবর্তন বা পরিবর্ধনের প্রয়োজন হতে পারে।
মোটামুটি আমাদের জীবনের প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতাকে স্বীকার করে তার ব্যাখ্যার জন্য এমন একটি সার্বিক সত্যে এসে পৌঁছা দরকার, যাতে জীবনের সকল দিকের প্রতি সুবিচার করা হয় এবং জীবনের বিভিন্ন জ্ঞানের ক্ষেত্রে হয় সামঞ্জস্য সাধন।
ইসলামে মানবজীবনকে সূক্ষ্মভাবে অধ্যয়ন করার জন্য রয়েছে বিশেষ তাগিদ। দ্বিতীয়ত যে দ্বন্দ্বে আজকের দিনের দুনিয়া রক্তকলুষিত সে দ্বন্দ্বের নিরসনের উপায় উদ্ভাবনেরও চেষ্টা ইসলাম করেছে। জ্ঞানের রাজ্যে কৃত্রিম ভেদরেখা তুলে নিয়ে একই সূত্রে জীবনের সকল ক্ষেত্রের করা হয়েছে ব্যাখ্যা এবং মানবীয় বিভিন্ন অধিকারের করা হয়েছে সমন্বয় সাধন। ইসলাম গোড়াতেই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে স্বার্থপরতার যোগ স্বীকার করেনি, ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যকে ইসলাম সবসময়েই তার বিকাশের হেতু বলে ধরে নিয়েছে। সেই ব্যক্তিত্ব বিকাশের অর্থ এ নয় যে, অপরকে শোষণ করে সে তার উদর পূর্তি করবে। তার পরিস্কার অর্থ এই- জীবনের সবগুলো বৃত্তির পরিপূর্ণ বিকাশের পর তাদের আসল কর্তব্যে নিয়োগ করা। ইসলামী পরিভাষায় খুদীর অর্থ কোন কালের স্বার্থপরতা নয়। মরহুম আল্লামা ইকবাল যে খুদীর বিকাশের জন্য মানবতাকে আহ্বান করেছিলেন, তা স্বার্থপরতা তো নয়ই-বরং তার উল্টো বৃত্তি। সে খুদী বিকশিত হলে মানুষ আর মানুষ থাকে না, সে হয় ইনসান-ই-কামিল। তখন সে অপরকে শোষণ করতে চায় না বরং আপনারই মত বিকাশের পথে টেনে নেয়। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের যে সূত্রপাত লক থেকে হয়েছিল, তারই পূর্ণ পরিণতিতে পাওয়া যায় নীটশের অতিমানবকে। সে অতি-মানবকে অতিদানবও বলা যায়। কারণ তার মাঝে মানবীয় গুণের দেয়ে দানবীয় গুণেরই প্রাধান্য বেশি। ইনসান-ই-কামিলের মাঝে মানব-জীবনের সবগুলো বৃত্তির সুষ্ঠু বিকাশই তার সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়। রাজনৈতিক জীবনে সে যেমন আপনার স্বার্থের জন্য নয় তৎপর, তেমনি আপনার সঙ্গে অপরের অচ্ছেদ্য যোগসূত্র স্বীকার করে বলে আপনার ও সমাজের স্বার্থে কোন তারতম্য দেখতে পায় না।
যে অধিকার নিয়ে ব্যষ্টি ও সমষ্টিতে চলছে অবিরাম সংগ্রাম, ব্যষ্টি ও সমষ্টির এরূপ পরস্পরবিরোধী পার্থক্য স্বীকার না করার ফলে ইসলামের মধ্যে এ সমস্যা এমন উগ্ররুপ ধারণ করেনি। ব্যষ্টি ও সমষ্টিকে একই ইউনিট হিসেবে ধরে নেয়ার জন্য তাদের তথাকথিত অধিকার লোপ করা হয়েছে। আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব স্বীকার করার ফলে ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনের দ্বন্দ্বের হয়েছে নিরসন।
অপরদিকে দুনিয়ার মালিকানা ও সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ্র –স্বীকার করে নিয়েও মানবজীবনে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার সমন্বয় সাধনের জন্য ইসলাম দিয়েছে পূর্ণ সুযোগ-ইসলামী জীবন দর্শনের মূল কথাঃ এ বিশ্বের আদি কারণ সব মঙ্গলময় পরম শক্তিশালী আল্লাহ্তা’আলা তাঁর সত্তা থেকে বিশ্বের সবকিছুর উৎপত্তি এবং তাঁর মাঝেই সবকিছুর লয়, মানবজাতির উৎপত্তিও তার থেকেই হওয়ায় তারা পরস্পর ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ। পবিত্র কুরআন শরীফে বলা হয়েছে এবং পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে-প্রকৃতপক্ষে তোমাদের এ ভ্রাতৃত্ব এক (অবিভাজ্য) এবং আমি তোমাদের প্রভু (আল-মুমিন ২৩-৩-৫২-৫৩)। আরও বলা হয়েছেঃ নিশ্চয়ই মানুষের ভ্রাতৃত্ব- একই ভ্রাতৃত্ব। (আম্বিয়া ২১-৬-৯২) কাজেই ইসলাম সর্বাবস্থায় সাম্য ও মৈত্রীর রুপায়নে মানুষকে উদ্ধুদ্ধ করে। মানুষের মাঝে সাম্য ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠা হওয়া সত্ত্বেও যাতে তাদের মধ্যে কাজে-কর্মে বা উৎপাদন ব্যবস্থায় আপেক্ষিক স্বাধীনতা বজায় থাকে তার জন্য ইসলাম কোন অবস্থায়ই কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেনি। ব্যক্তিগত বা সমাজগৎ জীবনে যাতে মানুষ স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পারে বা উৎপাদন ব্যবস্থায় স্বীয় অভিমত অনুসারে চলতে পারে, তার জন্য ইসলামী সমাজে রয়েছে প্রচুর সুযোগ। ব্যষ্টি ইচ্ছা করলেই যেমন একা উৎপাদন করতে পারে, তেমনি সংঘবদ্ধভাবে অপর দশজনের সঙ্গে মিলিত হয়েও সে উৎপাদন করতে পারে। ইসলামের মধ্যে এ সুযোগ থাকার দরুন মানব জীবনের বিকাশের পথের এক মস্ত বড় সুযোগ স্বাধীনতা ভোগ করার রয়েছে প্রচুর সম্ভাবনা।
জ্ঞানের রাজ্যে প্রয়োগ, যুক্তি ও স্বজ্ঞা, প্রত্যেক পন্থাকেই স্বীকার করে নেওয়ায় জগতের জ্ঞানের রাজ্যে ইসলাম কোন ভেদরেখা টেনে দেয়নি। যে কোন উপায়েই জ্ঞান লাভ হতে পারে এবং বিভিন্ন পদ্ধতিতে লব্ধ জ্ঞানরাজিকে সুসংবদ্ধ করা যায়, ইসলাম তা গোড়াতেই স্বীকার করে নিয়েছে। তার ফলে প্রায়োগিক, যুক্তিসর্বস্ব ও সজ্ঞালব্ধ জ্ঞানের ভিত্তির ওপর নির্ভর করে সার্বিক সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছার পক্ষে রয়েছে সুবিধা।
বর্তমান জগতে যেমন ক্ষেত্রগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে তাদের মধ্যে পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্তে পৌঁছার রয়েছে সুযোগ, ইসলাম মানব-মনকে এভাবে বিভক্ত করেনি বলে তার পক্ষে জ্ঞানের ক্ষেত্রে নৈরাজ্যের উৎপত্তি হয়নি।
বাস্তবিক পক্ষে ইহলোকিক, পারলৌকিক, রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয়, বৈজ্ঞানিক বা নৈতিক-ইত্যাদিরূপ ভেদরেখা সৃষ্টির মূলে রয়েছে আমাদের জ্ঞানের ক্ষেত্রে কাল্পনিক বিভাগ। মানব মন সর্বদাই এক ও অবিভাজ্য। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের মাধ্যমে কোন সত্যে উপনীত হলে তাতে যদি কোন ত্রুটি ধরা পড়ে, তা হলে আমরা অনতিবিলম্বে তাকে শুধরে নেই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় সূর্য পূর্বদিকে ওঠে-এ অভিজ্ঞতা আমাদের নিত্যকার ব্যাপার। কিন্তু যখন এ অভিজ্ঞতাকে আমরা যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করি, তখন তাকে সংশোধিত আকারে গ্রহণ করতে হয়। বলতে হয় আমরা দেখি বটে সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে তবে প্রকৃতপক্ষে সূর্য ওঠে না। পৃথিবীর আবর্তনের ফলেই আমাদের এ ভ্রান্তি হয়।
যুক্তি ও লব্ধজ্ঞানেরও সংশোধন করা অনেক সময় প্রয়োজন হয়ে পড়ে। জগতে যা কিছু আমরা দেখতে পাই তাতে দেখি পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। এক বিরাট পরিবর্তন চলছে দুনিয়ার বুকে। আজ যে শিশু,কাল সে যুবা। আবার দু’দিন যেতে না যেতে সে বৃদ্ধ হয়ে কবরের পথে অগ্রসর হয়। কাজেই মানবজীব অসার, অনিত্য। আজ আমি বেঁচে আছি, কাল হয়ত থাকবো না। কাল কেন, হয়ত পরমুহূর্তেই থাকবো না। আমার পক্ষে তা হলে কোন কিছু করার কি অর্থ থাকতে পারে? খাওয়া-পরা, ভোগ-বিলাস, আয়াস-আরাম সবকিছুই অনিত্ব ও অসার। তাই- হয় নিস্ক্রিয়, নিরস থেকে তিলে তিলে মরে যাওয়াই ভাল। না হয় যা খুশি তাই করে দু’দিনের এ ভবখেলা সাঙ্গ করে যাওয়াই ভালো। যুক্তিধারার এ প্রবল স্রোতে কিন্তু মানুষ ভেসে যেতে চায় না। কারণ এভাবে চিন্তা করলে মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না। তার বেঁচে থাকার ইচ্ছা তাকে এ সংকটজনক পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করেছে, সে তাকে অভয় দিচ্ছে- তোমাকে বাঁচতেই হবে। জীবনযুদ্ধে তোমাকে বুঝতেই হবে। তার জীবনধর্মই তাকে কর্মের পথে, প্রেরণার পথে এগিয়ে দিচ্ছে। এ জ্ঞান সে যুক্তি থেকে পাচ্ছে না, পাচ্ছে সহজাত জ্ঞান থেকে।
ধর্মজগতে বা নৈতিক-জগতে স্বজ্ঞাজাত জ্ঞান সবসময়ই মানুষের হয়ে থাকে। সেজন্য যুক্তি-জ্ঞানকে ধর্মীয় ও নৈতিক জ্ঞান দ্বারা পরিশোধিত করে তোলা দরকার। সেই পরিশোধনের ফলে যে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির সৃষ্টি হয়, সে জ্ঞানই মানব জীবনের চরম ও পরম জ্ঞান।
ইসলাম গোড়াতেই ইহলৌকিক, পারলৌকিক, ধর্মীয় বা রাষ্ট্রীয় বলে জ্ঞানের কোন পৃথক জগৎ স্বীকার করেনি। সমগ্র জীবন দিয়ে সত্য লাভের চেষ্টা ইসলামের কাম্য। ইসলাম মানবজীবনকে পূর্ণ বিকাশের পথে এগিয়ে দিতে চায় বলে জ্ঞানের প্রত্যেকটি পদ্ধতি স্বীকার করে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে জীবন সমস্যার সমাধান করতে চায়, তার ফলে ধর্ম-জীবনের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় জীবনের, কর্ম জীবনের সঙ্গে নৈতিক জীবনের দ্বন্দ্বের হয় অবসান।
বিভিন্ন জ্ঞানের উপকরণকে সমন্বয় করে ইসলাম এসে উপনীত হয় এক সার্বিক সিদ্ধান্তে- যেখানে মানব মনের সবগুলো দাবি সন্তোষ লাভে হয় সমর্থ। বর্তমান কালে ধর্ম ও রাষ্ট্রের যে দ্বন্দ্ব তার মূলে রয়েছে আমাদের একদেশদর্শী জ্ঞানের কার্যকারিতা। যুক্তিসর্বস্ব জ্ঞানের আলোকে আমরা গড়ে তুলি রাষ্ট্র। তাতে কোথাও ব্যষ্টির, আবার কোথাও সমষ্টির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করি। ধর্ম-জীবনকে রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে পৃথক করে দেখি বলে রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয়জীবনে শুরু হয় ভীষণ দ্বন্দ্ব। ধর্মজীবনে যা ন্যায়-নীতি বলে সর্বত্র স্বীকৃত হয় রাষ্ট্রজীবনে তা অনেক স্থলেই উপহাসের বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। তার প্রধান কারণ, আমরা একই সত্যকে কোথাও দেখি বিশুদ্ধ জ্ঞানের আলোকে, আবার কোথাও দেখি স্বজ্ঞার মাধ্যমে। সামগ্রিক দৃষ্টি নিয়ে একে বুঝবার চেষ্টা করলে একই সত্যের দুটো রূপ বলে ধরা পড়বে। রাষ্ট্রজীবনে জীবনকে দেখা হয় শুধু বুদ্ধির আলোকে। সে জন্য এখানে ধর্মীয় ও নৈতিক মানগুলো কোন স্থান পায় না। ধর্মীয় ও নৈতিক জীবনের মানগুলো স্বজ্ঞার মাধ্যমেই পাওয়া যায়। বুদ্ধির সঙ্গেই বোধির যোগ হলে তবেই সত্যের সমগ্র রূপ ধরা পড়ে। সেই যোগসূত্র স্থাপনের জন্য রয়েছে তাগিদ। সে জন্যই ইসলাম রাজনীতিকে ধর্মনীতি থেকে পৃথক করে কোন কালেও দেখেনি। কেবল ধর্ম ও রাজনীতি নয় আধ্যাত্মিক বা জাগতিক বলে ইসলামের কোন বিভাগ নেই। আল্লামা ইকবাল সত্যিই বলেছেন- “ ইসলামে আধ্যাত্মিক ও জাগতিক বলে দুটো ভিন্ন ক্ষেত্র নেই। যতই জাগতিক (উদ্দেশ্য প্রণোদিত) হোক না কেন, কর্তার মনের ভাবধারার আলোকেই কর্মের নির্ধারণ হয়ে থাকে। ইসলামে একই সত্যকে এক দৃষ্টিভঙ্গিতে চার্চ বলা হয়, অন্য দৃষ্টিভঙ্গিতে বলা হয় রাষ্ট্র। চার্চ ও রাষ্ট্রকে একটি বস্তুর দুটো দিক বললে ঠিক বলা হবে না। ইসলাম বিশ্লেষণের অতীত এক সত্য। আমাদের দৃষ্টিকোণের পরিবর্তনের ফলে তাকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখায়। এই ভুলের কারণস্বরূপ বলা যেতে পারে, ঐক্যকে দ্বিখণ্ডিত করে দুটো ভিন্ন সত্যের সৃষ্টির ফলেই এর উৎপত্তি। আসল সত্য হল জড় পদার্থ, স্থান-কালের সম্বন্ধে আত্মা বৈ কার কিছু নয়”।
কাজেই সব দেখে শুনে মনে হয়, অনাগত বিশ্ব সংস্থার জন্য যে কয়টি মৌলিক নীতির স্বীকৃতির প্রয়োজন এবং যে মানসিকতার অত্যন্ত প্রয়োজন- ইসলামের মধ্যে তার সমস্ত রয়েছে। তাই এ ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ দুনিয়ার বুকে আবার শান্তি ফিরিয়ে আনতে হলে মানব-সভ্যতাকে ইসলামের নীতি গ্রহণ করতে হবে।
ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ
প্রথম পরিচ্ছদে
- \n
- প্রজাতির উৎপত্তি Origin of species
- \n
- মানুষের উৎপত্তি Descent of man
- \n
- লিনেয়াস Lenneus
- \n
- প্রজাতি Species
- \n
- ব্যতিক্রম Variation
- \n
- প্রকৃতির মনোনয়ন Natural selection
- \n
- আকস্মিক প্রকারণ Accidental variations
- \n
- সহজাত প্রবৃত্তি Instincts
- \n
- অভিযোজন Adaptation
- \n
- সংবেদনশীল Sensitive
- \n
- বুশম্যান Bushman
- \n
- উইজম্যান Weisman
- \n
- জননকোষ Germ cell
- \n
- লেমার্ক Lamarck
- \n
- লব্ধগুণ Acquired characteristic
- \n
- প্রজাতি Species
- \n
- উপাদান Elements
- \n
- প্রাকৃতিক নির্বাচন Natural selection
- \n
- জাতি Kind
- \n
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
- \n
- কামসর্বস্ববাদ Pan-sexualism
- \n
- কার্ল জুঙ Carl jung
- \n
- এডলার Adler
- \n
- প্রক্ষোভ Emotion
- \n
- উদ্বায়ুজ লক্ষণ Neuric symptom
- \n
- প্রহরী Censor
- \n
- আপতিক Accidental
- \n
- অবদমিত বাসনা Repressed desire
- \n
- লিবিডো Libido
- \n
- আত্মকামী Narcissist
- \n
- অস্ফুট চিত্ততার কাল Lateny period
- \n
- বৈকল্য Perverse
- \n
- স্থিতাবস্থা Fixation
- \n
- প্রতিসরণ Regression
- \n
(ক) ধ্বজচ্ছেদ কূটেশা Castration complex
- \n
- ধর্ষকাম Sadism
- \n
- মর্ষকাম Masochism
- \n
- উপস্থ ঈর্ষা Penis envy
- \n
- দ্বিমেরুত্ব Polarity
- \n
- উদগতি Sublimation
- \n
- আত্মপ্রকাশ Self- assertion
- \n
- লিবিডো Libido
- \n
- বিষয়কেন্দ্রিক Objective
- \n
- উদ্বায়ু Psychosis
- \n
- স্থায়ী অবস্থা Fixed state
- \n
- প্রহরী Censor
- \n
তৃতীয় পরিচ্ছেদ
- \n
- ভূমিদাস Serf
- \n
- ম্যাকিয়াভেলি Machiavelli
- \n
- লক Locke
- \n
- এ্যাডাম স্মিথ Adam smith
- \n
- অহংবোধ Egoism
- \n
- স্বার্থপরতা Selfishness
- \n
- সামাজিক চুক্তিবাদ Social cantract theory
- \n
- সার্বভৌমত্ব Sovereignty
- \n
- রাষ্ট্র State
- \n
- শক্তি Power
- \n
- পরার্থপর Altruistic
- \n
- অহংবোধ Egoism
- \n
- ব্যষ্টির স্বাতন্ত্র্য Individualism
- \n
- ব্যক্তিকে একা থাকতে দাও Laissez Faire-Let alone
- \n
চতুর্থ পরিচ্ছেদ
- \n
- যূথচারী Gregarious animal
- \n
- মত দলীয় Group
- \n
- অনুগৃহীত Chosen
- \n
- সংঘ চেতনা Collective consciousness
- \n
- রিপাবলিক Republic
- \n
- আদর্শ সুখরাজ্যে Uthopia
- \n
- স্বতঃসিদ্ধ Postulate
- \n
- চরম নাস্তিবাদ Absoulute Nihilism
- \n
- অস্তিত্ব Being
- \n
- অন-অস্তিত্ব Non-being
- \n
- সূচনা Starting point
- \n
- অন্ব্য় Thesis
- \n
- মাধ্যম Category
- \n
- অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ Apriori
- \n
- অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ Empirical aposteriori
- \n
- গুহামানব Cave man
- \n
- পশুচারী Pastoral
- \n
- প্রস্তর যুগ Neolithic age
- \n
- অধিকার Right
- \n
- প্রয়োজন অনুসারে সমস্তই পাবে To each according to his capacity and to each according to his needs
- \n
- উদারনৈতিক মতবাদ Liberalism
- \n
- ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ Individualism
- \n
- বৃত্তিগত শ্রেণী বৈষম্য Professional class distinction
- \n
- সন্ধিক্ষণ Transition period
- \n
- অর্থনৈতিক নিশ্চয়তাবাদ Economic determinism
- \n
- দুনিয়ার মজদুর সব একত্র হও Working men of all countries unite
- \n
- সম্মতি Acquiescence
- \n
- ব্যষ্টি চৈতন্য Egoism
- \n
- নির্বিত্তের নেতৃত্ব Dictatorship of the Proletariate
- \n
- জাগতিক আশাবাদ Cosmic optimism
- \n
- আত্মপ্রচারবাদী Self-assertive
- \n
- স্রষ্টা Creator
- \n
পঞ্চম পরিচ্ছেদ
- \n
- আরোহ Inductive
- \n
- মূল লক্ষ্য বিশেষ The particular good
- \n
- সার্বিক Universal
- \n
- অবরোহ পদ্ধতি Deductive method
- \n
- জীবজগতের যুদ্ধ Struggle for existence
- \n
- স্ববোধ Egoism
- \n
- পরার্থপরতা Altruism
- \n
- মনন-ক্ষমতা Power of intellection
- \n
- প্রক্ষোভ Emotion
- \n
- ইচ্ছাশক্তি Will
- \n
- বোধি Instution
- \n
- ভূয়োদর্শন Experience
- \n
- যুক্তি Reason
- \n
- কার্যকরণ-পরস্পরা সূত্র Low of causality
- \n
- আপেক্ষিকতবাদ Theory of relativity
- \n
- উদ্দীপক Stimulus
- \n
- জ্ঞানের অন্যান্য শক্তিগুলো The other faculties of knowledge
- \n
- যোগসূত্র Co-ordination
- \n
- সমাজ ব্যবস্থা Social order
- \n
- প্রয়োগ Experience
- \n
- বুদ্ধি Intellect
- \n
- বোধি Intitution
- \n
- প্রত্যাদেশ Revelation
- \n
- প্রয়োগ Experience
- \n
- যুক্তি Reason
- \n
- অবরোহ Deductive
- \n
- বিবর্তনকারী Evolver
- \n
- সর্বব্যাপী সত্তারুপে Immanent principle
- \n
- সর্বব্যাপী ও তুরীয় সত্তারুপে Immanent and transcendent
- \n
- জগৎ-বহির্ভূত স্রষ্টা Deistic conception
- \n
- রব্ Creator, Evolver & Sustainer
- \n
- সর্বব্যাপী Immanent
- \n
- তুরীয় Transcendent
- \n
- গোঁড়া Orthodox
- \n
- আরোহ পদ্ধতি Inductive method
- \n
- দড়ি Data
- \n
- অবরোহ Deductive
- \n
- অবরোহ Deductive
- \n
- সঙ্গতি Consistency
- \n
- স্বতঃসিদ্ধ Postulate
- \n
- সৃষ্টিকর্তা Creator
- \n
- সর্বব্যাপী Immanent
- \n
- সর্বব্যাপী ও তুরীয় Immanent and transcendent
- \n
- স্বতঃসিদ্ধ Axiom
- \n
- জ্ঞেয়েতা Knowability
- \n
- অভিজ্ঞতা Experience
- \n
- সর্বব্যাপীরুপে As an Immanent principle
- \n
- স্বতঃসিদ্ধ Postulate
- \n
- একত্বের নীতি Law of Identity
- \n
- দ্বন্দ্বের নীতি Law of contradiction
- \n
- মধ্যপন্থা বর্জনের নীতি Law of excluded midle
- \n
- যথাযোগ্য কারণের নীতি Law of sufficient reason
- \n
- পরিবর্তন Change
- \n
- শক্তি Power
- \n
- সংবেদন Sensation
- \n
- একীকরণ Assimilation
- \n
- শক্তি Power
- \n
- ঐক্যের নীতি Law of identity
- \n
- দ্বন্দ্বের নীতি Law of contradiction
- \n
- পরস্পর বিরোধী Contradictory
- \n
- স্থিতিশীল Static
- \n
- অ-স্থিতিশীল Dynamic
- \n
- মধ্যপন্থা বর্জনের নীতি Law of excluded middle
- \n
- দুটো গুণ Two qualities
- \n
- চিন্তার বিষয় Object of thought
- \n
- একত্বের নীতি Law of identity
- \n
- যথাযোগ্য কারণের নিতি Law of sufficient reason
- \n
158.একত্বের নীতি Law of identity
159.সমরূপতার নীতি Law of unoformity
160.সমরূপতার নীতি la w of uniformity
161.সমরূপতা Uniformity
162.জ্ঞেয় Knowable
163জ্ঞাতা Knower
164.লাইবনিটজ Leibnitz
165.জেম্স James
166.মনাড Monad
167.এক সংস্থা One order
168.ঐক্য Unity
169.স্বাতন্ত্র্য Individuality
- \n
- তারা নিয়ম গঠন করছে They are framing laws
- \n
- অধিকতর বাস্তব Much more real
- \n
- স্থিতি Existence
- \n
- আরোহ পদ্ধতি Inductive method
- \n
- একত্বের নীতি Law of identity
- \n
- সমরূপতার নীতি Law of uniformity of nature
- \n
- জ্ঞাতা Knower
- \n
- জ্ঞেয় Knowable
- \n
- কার্যকারণ পরস্পরা নীতি Law of causation
- \n
- শুন্য থেকেই শুন্য আসে Exnhilo nihilfit
- \n
- স্বতঃসিদ্ধ Axiom
- \n
- তত্ত্ববিষয়ক প্রমাণ Casual proof
- \n
- উপায়স্বরূপ Means of an end
- \n
- ধর্মতত্ত্বমূলক যুক্তি Teleological argument
- \n
- প্রাকৃতিক উৎপাত Natural calamities
- \n
- কলাকৌশল Design
- \n
- কার্য Effect
- \n
- প্রতিষঙ্গ Correspondencde
- \n
- প্রতিষঙ্গমূলক মতবাদ Correspondence theory
- \n
- চিন্তার মাধ্যমে Categories
- \n
- প্রতিপাদ্য Theorem
- \n
- সম্পাদ্য Problem
- \n
- অবরোহণ করা Deduction
- \n
- সঙ্গতিবাদ Coherence theory
- \n
- কোপারনিকাস Copernicus
- \n
- সূর্যকেন্দ্রিক সিদ্ধান্ত Heloi Centric Theory
- \n
- প্রয়োগবাদ Pragmatism
- \n
- কার্যকারন পরস্পরা সূত্র Law of causation
- \n
- বস্তু Object
- \n
- বুদ্ধিবৃত্তি Intellect
- \n
- সার্বিক সিদ্ধান্ত General conclusion
- \n
- A presence that disturbs me with Joy of elevated thoughts, e sense of sublime of something far more deeply interfused, whose dwelling is light of setting uns and the round ocean and the living air ad the blue sky, and the mind of man, a motion and a spirit that impels all thinking things, all objects of all thoughts and rolls though all things.
- \n
- The Physical order of nature taken simply as science knows it canot be held to reveal any one harmonious spiritual intent. It is a more weather as Chauncey Wright called it doing and undoing without an end.
- \n
Whatever else be certain this at least is certain that the world of our present natural knowledge is enveloped in larger world of some sort of whose residula properties we at present can form no positive idea-
- \n
- So long as dea only with the cosmic and general, we deal with the symbols of reality but as soon as we deal with private and personal phenomena as such we deal with realities in the complete sense of the terms…..,
- \n
- নৈতিক শাসন ব্যবস্থা Moral Government of the universe
- \n
- সরাসরি অভিজ্ঞতা Direct experience
- \n
যষ্ঠ পরিচ্ছেদ
*
সপ্তম পরিচ্ছেদ
- \n
- পশুচারিক পর্যায় Pastoral stage
- \n
- মৌলিক অধিকার Fundamental rights
- \n
- আধুনিক গণতন্ত্র Modern democracy
- \n
- সরাসরি নির্বাচন Direct election
- \n
- পরোক্ষ নির্বাচন Indirect election
- \n
- প্রতিবিপ্লব Counter revolution
- \n
- মালিকানার নীতি Proprietory rights
- \n
- রক্ষক Custodian
- \n
অষ্টম পরিচ্ছেদ
- \n
- সমষ্টিগতভাবে Collectively
- \n
- অংশীদারের স্বত্ব The rights of partnership
- \n
- চুক্তিস্বত্ব Rights of contract
- \n
- রক্ষক Custodian
- \n
- আইন প্রয়োগ By the enforcement of laws
- \n
- সংঘবদ্ধভাবে Collectively
- \n
- সমবায়মূলক পদ্ধতি In a Co-operative method
- \n
নবম পরিচ্ছেদ
- \n
- সুখচারী প্রবৃত্তি Gregarious Instinct
- \n
- আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব Sovereignty of Allah
- \n
- মানুষের প্রতিনিধিত্ব Vicegerency of man
- \n
দশম পরিচ্ছেদ
- \n
- সংবেদন Sensation
- \n
- কাম জাগৃতির সময় Phallic stage
- \n
- একক সংখ্যা Unit
- \n
বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও দার্শনিক জনাব অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ লিখিত ‘জীবন সমস্যার সমাধানে ইসলাম’ নামক জনপ্রিয় পুস্তকটিতে ওহী ও প্রত্যাদেশের স্বরূপ বর্ণনা সম্পর্কে জনৈক সুধী পাঠকের সমালোচনা পাঠ করলাম। আমার ধারণা ওহী বা প্রত্যাদেশ ও এলহাম প্রভৃতি বিষয়গুলোর স্বরূপ এবং বাংলা ভাষাভাষী পাঠকগণকে তা বোঝানোর জন্য এর চাইতে সহজ এবং বোধগম্য কোন ভাষা ব্যবহার করা যায় না। জনাব দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের লেখায় ওহী সম্পর্কিত ইসলামের মৌলিক আকীদা ক্ষুন্ন হয়েছে বলে আমি মনে করি না। এ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানতে হলে সমকালীন মুসলিম বিশ্বের দুজন শীর্ষস্থানীয় দার্শনিক আলেম মুফতী আবদুহুর আকীদা সম্পর্কিত পুস্তিকা এবং সাঈদ আহমদ আকবরাবাদী লিখিত ‘ওয়াহীয়ে-ইলাহী’ নামক দুটি পুস্তক দেখা যেতে পারে। -মাওলানা মুহিউদ্দীন খান
', 'জীবন সমস্যার সমাধানে ইসলাম', '', 'publish', 'closed', 'closed', '', '%e0%a6%9c%e0%a7%80%e0%a6%ac%e0%a6%a8-%e0%a6%b8%e0%a6%ae%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%b8%e0%a6%ae%e0%a6%be%e0%a6%a7%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%87-%e0%a6%87%e0%a6%b8%e0%a6%b2', '', '', '2015-03-12 11:56:35', '2015-03-12 05:56:35', '
\r\n
জীবন সমস্যার সমাধানে ইসলাম
\r\n
দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ
\r\n\r\n\r\n
\r\n\r\n
স্ক্যান কপি ডাউনলোড
\r\n
\r\n
বিষয়ক্রম
\r\n
সূচনা
\r\n
জীবন সমস্যা
\r\n
প্রথম পরিচ্ছেদ
\r\n
জীববিজ্ঞানের শিক্ষা
\r\n
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
\r\n
মনোবিজ্ঞানের শিক্ষা
\r\n
ফ্রয়েডীয় মতবাদ
\r\n
ম্যাকডুগাল
\r\n
এ্যাডলার
\r\n
জুঙ
\r\n
তৃতীয় পরিচ্ছেদ
\r\n
রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষা
\r\n
ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ
\r\n
সামাজিক চুক্তিবাদ
\r\n
ধনতন্র
\r\n
চতুর্থ পরিচ্ছেদ
\r\n
সমষ্টিকেন্দ্রিক মতবাদ
\r\n
ইয়াহুদী ধর্ম
\r\n
প্রাথমিক প্লেটো
\r\n
মাজদাক
\r\n
কার্ল মার্কস
\r\n
মার্কসবাদ ও বস্তুবাদী সমাজতন্র
\r\n
টলস্টয় বা নব্য খ্রিষ্টবাদ
\r\n
গান্ধীবাদ
\r\n
পঞ্চম পরিচ্ছেদ
\r\n
মানুষের পরিচয়
\r\n
পূর্ণাঙ্গ দর্শন ও ইসলাম
\r\n
ইসলামের অবলম্বন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধ
\r\n
আল্লাহ্র অস্তিত্বের প্রশ্ন
\r\n
আল্লাহ্র সার্বভৌমত্তের সঙ্গে মানুষের অধিকারের সমন্বয়
\r\n
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
\r\n
ইসলামী নীতির রুপায়ণ-ব্যক্তিগত জীবনে, সমাজে ও রাষ্ট্রে ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যক্তি,সমাজ ও রাষ্ট্র
\r\n
ইসলামী নীতির প্রয়োগ-ব্যক্তিগত জীবনেঃসালাত
\r\n
সিয়াম ও রমযানের তাৎপর্য
\r\n
হজ্জ ও কুরবানী
\r\n
যাকাত
\r\n
জিহাদ
\r\n
সামাজিক জীবনে নর-নারী সম্পর্কঃ ইসলামি সমাজে নারীর মর্যাদা ও অধিকার
\r\n
ইসলামের দৃষ্টিতে সুদপ্রথা
\r\n
সাম্যবাদমূলক দায়ভাগ প্রথার প্রবর্তন
\r\n
ইসলামী নীতির রুপায়ণ-রাষ্ট্রীয় জীবনেঃ মদীনার সনদের সারমর্ম
\r\n
পুঁজি সৃষ্টির বিরুদ্ধে অর্ডিন্যান্স
\r\n
ইসলামী গণতন্ত্রের ফলিত রুপ
\r\n
খলীফার দায়িত্ব
\r\n
ইসলাম ও ডিক্টেটরশিপ
\r\n
সংখ্যালঘু সমস্যা
\r\n
খলীফার নিয়োগ
\r\n
অর্থনীতি
\r\n
উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা
\r\n
শাসন ও বিচার বিভাগ
\r\n
সপ্তম পরিচ্ছেদ
\r\n
ইসলামী রাষ্ট্রের ভাঙ্গনের কারণ
\r\n
অষ্টম পরিচ্ছেদ
\r\n
ইসলামী সমাজের ভূমিনীতি ও তার প্রয়োগ
\r\n
ইসলামী জীবন দর্শন ও তার ফলিত রূপ
\r\n
ইসলামী সমাজে ভোগদখলের অধিকার
\r\n
তিনটি শর্ত রয়েছে
\r\n
ভোগ-দখলের জমির পরিমাণ
\r\n
জমি থেকে ফসল উৎপাদনের নীতি
\r\n
উৎপাদনের পদ্ধতি
\r\n
ইসলামী সমাজের ভূমিনীতি
\r\n
আধুনিক যুগে ইসলামী নীতির প্রয়োগ
\r\n
নবম পরিচ্ছেদ
\r\n
ইসলামের বিকাশ
\r\n
দশম পরিচ্ছেদ
\r\n
অনাগত বিশ্বসংস্থা ও ইসলাম
\r\n
ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ
\r\n
গ্রন্থপঞ্জি
\r\n
পরিশিষ্ট
\r\n
\r\n\r\n
লেখকের কৈফিয়ত
\r\n
\r\n
আমরা বহুকাল যাবত অবরোহ পদ্ধতিতে (Deductive Method) ইসলামকে পাঠ করে এসেছি। এতে আমাদের জীবনের প্রত্যয়শীলতা বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়েছে; তবে সে প্রত্যয় বা faith-এর মূলে কোন যুক্তির অবতারণা করতে পারেনি। তাই এ দুনিয়ার অমুসলিম বা বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তাধারায় অভ্যস্ত লোকের নিকট আমাদের এ প্রত্যয়শীলতা অন্ধবিশ্বাসের আকারেই রয়ে গেছে। তার ফলে ইসলাম যে বিশ্বজনীন ধর্ম বা মানব প্রকৃতির ধর্ম সে দিকটা রয়ে গেছে অস্পষ্ট। মানবজীবনকে একটা অতিশয় সত্য বিশয় বলে গ্রহণ করে যদি তারই ভিত্তিতে প্রকৃত সত্য লাভ করার চেষ্টা করা যায়, তা’হলে মানব-জীবনের প্রকৃত রূপ এবং তার সন্তোষ বিধানের জন্য যে বিষয়কে অবশ্য সত্য বলে গ্রহণ করতে হবে, তার আলোচনা করা প্রয়োজন। এমন একজন ধর্ম-বহির্ভূত মানুষ যার কোন মতবাদে বিশ্বাস নেই এবং যিনি জীবনের সন্তোষের জন্য যে কোন মতবাদই গ্রহণ করতে প্রস্তুত, তারই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এ পুস্তকের আলোচনা আরম্ভ হয়েছে। এজন্য তার নামকরণ করা হয়েছে, “জীবন সমস্যার সমাধানে ইসলাম”। এতে জীবনের নানাবিধ সমস্যার সমাধানে ইসলাম কিভাবে সার্থক সে বিষয়টাই মানব সাধারনের নিকট তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এজন্য কোন কোন বিষয় সাধারণ পাঠকের নিকট বিসদৃশ বলে প্রতিভাত হতে পারে। ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রত্যাদেশ বা ওহী খাস আল্লাহ্র এক দান। তা নবী মুরসালদের কাছে আল্লাহ ফেরেশতার মাধ্যমে নাযিল করেন। অথচ হিব্রুধর্ম গোষ্ঠী যথা-ইহুদী ও ঈসায়ী ধর্মাবলম্বী মানুষ ব্যতীত অপরাপর ধর্মালম্বী লোকদের নিকট তা গ্রহণযোগ্য নয়। একজন nonconformist- এর নিকট সে প্রত্যাদেশকে বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় পেশ করতে হলে তার মধ্যে নবী মুরসালদের সক্রিয়তার দিকটা প্রকাশ করা প্রয়োজনীয় গতিকে তাকে বৈজ্ঞানিক আকারেই প্রকাশ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে, বিজ্ঞান সতত পরিবর্তনশীল। কাজেই আজকের জগতে যা বৈজ্ঞানিক সত্য বলে স্বীকৃত, পরবর্তী যুগে তা স্বীকৃত নাও হতে পারে। তার উত্তরে বলা যায়, জীবনকে যদি সঠিকভাবে পরিচয় করার বাসনা কারো মনে জাগে এবং জ্ঞানের সকল ক্ষেত্র ও পদ্ধতিকে স্বীকার করা হয়, তাহলে স্বজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাদেশ বা ওহী নামক জ্ঞানকে স্বীকার করতেই হবে। কাজেই এক্ষেত্রে লেখক একজন nonconformist- এর দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই বিষয়টার আলোচনা করেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে, কোন মতবাদবিহীন একজন স্বাধীন ও স্বাতন্ত্র্যবাদী লোকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও যদি আলোচনা করা যায়, তাহলেও ওহীকে স্বীকার করতে হবে।
\r\n
ইসলামকে জগৎ সভ্যতায় পেশ করা হয়েছে প্রশ্নবিহীন অবশ্যগ্রহণীয় এক প্রত্যয় হিসেবে। জীবনের নানাবিধ চাহিদা পরিপূরণে সক্ষম এক মতবাদ হিসেবে উপস্থাপন করার চেষ্টা থেকেই এ পুস্তকে নবুয়াত, রিসালার বা বেলায়েতকে যুক্তিসঙ্গত বিষয় বলে গ্রহণ করা হয়েছে। এ পুস্তকের আলোচ্য বিষয় মানবজীবনের ইসলামী সমাধান- কেবল মুসলিম জীবনের সমাধান নয়, আশা করি এ বিষয়টা বিদগ্ধ পাঠক বিবেচনা করে দেখবেন। -মোহাম্মদ আজরফ
\r\n
\r\n
\r\n\r\n
সূচনা
\r\n
জীবন সমস্যা
\r\n
\r\n
মানব-জীবনে কত সমস্যা। জীবন-প্রভাতেই তাতে দেখা দেয় নানা প্রশ্ন। একটুখানি চলাফেরা বা বুদ্ধি-বিবেচনা দেখা দিলেই মানুষ ভাবতে আরম্ভ করে- “আমি কোথা থেকে এলাম? কোথায় আমি যাবো? কেন এখানে এলাম? আমাকে কি এই দুনিয়া ভালবাসে না হিংসা করে?” যখন ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় আকাশ প্লাবিত হয়, তখন ছোট ছোট শিশুরা মনে করে- চাঁদের দেশে বুঝি বা কত সুখ! কত সৌন্দর্য! যখন বাসন্তী সমীরণে গাছের পাতাগুলোর আড়ালে বসে কোকিল বা এ জাতীয় কোন পাখি মধুর সুরে আপ্যায়িত করে, তখন শিশুদের মনে স্বাভাবিকভাবেই কোকিলের পার্শে বসে তার মত গান গাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ পায়। তারা মনে করে- না জানি ওই গাছের ডালে বসে ওই পাখিটা কত আনন্দ উপভোগ করছে! আবার জ্যৈষ্ঠ মাসে যখন আম, জাম ও কাঁঠাল পাকে, তখন সে কোকিল-বধূই যখন অপূর্ব গান গেয়ে রাত্রিকে সরব করে তুলে, তখন পাড়াপড়শিরা তার এ গানকে বলে “বউ কথা কও”- তখন শিশুর মনে এ পাখির প্রতি কত শ্রদ্ধাই না দেখা দেয়। সে মনে করে, বউ অভিমান করে কথা বলছে না বলে তার বরের মনে কি কষ্ট! সেজন্যই বোধ হয় বরের হয়ে পাখিটা বউকে সাধ্য-সাধনা করে বলছে- “বউ কথা কও”। ফাগুন মাসে যখন গাছে গাছে নানা জাতীয় ফুল প্রস্ফুতিত হয়ে চারদিকে সুবাসের বান বইতে থাকে, তখন শিশুর মনে সত্যিই প্রশ্ন দেখা দেয়, এ ফুলগুলো কে ফোটাচ্ছে, তাকে কি দেখা যায়, না সে লুকিয়ে থাকে- পালিয়ে বেড়ায়?
\r\n
আবার যখন প্রবল ঝড়ে গাছ-গাছালি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে, ঘর-দুয়ার সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তখন সেই শিশুই ভাবতে থাকে, এ আবার কি আপদ! এ কোন দৈত্য-দানব বা জিন দেখা দিল আমাদের সামনে? হটাৎ ভীষণ গর্জন করে আকাশে কি এমন কোন ব্যক্তি রয়েছে, যার গলার স্বরই গর্জনরূপে দেখা দিচ্ছে? বান-বন্যা দেখা দিলে বা ভূমিকম্পের ফলে দেশে হেথায় হোথায় নানা ফাটল দেখা দিলে শিশুরা ভয়ে হকচকিয়ে চায়- এ আবার কোন্ দুশমনের কাজ! কে এসব অনাচার অত্যাচার করে আমাদের দেশের এ সর্বনাশ করেছে অর্থাৎ সোজা কথায় এ দুনিয়া আমাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বা আমাদের ভীষণ শত্রু, এ প্রশ্নটা তাদের মনে দোলা দেয়।
\r\n
এ সকল প্রশ্নের পূর্বে যে সকল প্রশ্ন তাদের মানসে দেখা দিয়েছিল অর্থাৎ তারা কোথা থেকে এল; আবার কোথায় ফিরে যাবে? কেনই বা এল, আবার কেনই বা আবার ফিরে যাবে, ইত্যাকার প্রশ্ন বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধামাচাপা পড়ে রয়। কৈশোরের প্রারম্ভে নানা বাধাবিপত্তি থাকা সত্ত্বেও এ দুনিয়াটা মানুষের কাছে আলো-ঝলমল রূপেই দেখা দেয়। মনে হয় এ দুনিয়ার সবকিছুই সুন্দর, সবকিছুই চমৎকার। ছেলেবেলায় এ দুনিয়ার যে সব বীভৎস দৃশ্য দেখে ছেলেরা ভয়ে ও বিস্ময়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে,কৈশোরে সেগুলোর এ ভয়ঙ্কর রূপকে অগ্রাহ্য করে কিশোর ও কিশোরী তার আনন্দময় রূপেই মুগ্ধ হয়ে পড়ে। তখন তাদের কাছে ‘সাময়িকভাবে এগিয়ে চলছি” জীবনের মূলমন্ত্র হয়ে পড়ে। এর সঙ্গে অপরের প্রতিযোগিতার প্রবৃত্তি দেখা দিলেও প্রেম, সখ্য, স্নেহ-প্রীতি প্রভৃতি সুকুমার বৃত্তি তাদের মানসকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। যারা একেবারে শৈশব থেকে অপরাধপ্রবণ, তাদের মানসে অপরের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ দেখা দিলেও দলীয় মনোবৃত্তি বা Group mindedness দ্বারা তারা প্রভাবান্বিত হয় এবং দলের সভ্যদের সঙ্গে তাদের নিজেদের ঐক্য অনুভব করে, দলের স্বার্থ রক্ষার্থে নানাবিধ অপকর্ম করতেও প্রস্তুত হয়। এজন্য একালকে ব্যক্তি-স্বার্থহীনতার কাল বলা যেতে পারে। একদিকে যেমন শৈশবের যে সকল আদি প্রশ্ন সম্বন্ধে তাদের মধ্যে উদাসীনতার ভাব পরিলক্ষিত হয় তেমনি ব্যক্তিগত জীবনের গণ্ডি অতিক্রম করে বৃহত্তর গণ্ডির মধ্যে আত্মবিলোপের প্রবৃত্তি তাদের মধ্যে দেখা দেয়। জীবনের নানা ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে লালিত-পালিত হলেও সকল স্তরে কিশোর ও কিশোরীদের মানসে সে একই ভাব প্রবল হয়ে ওঠে।
\r\n
এ সন্ধিক্ষণেই নারী ও পুরুষের দৈহিক পার্থক্য ক্রমশ প্রকট হয়ে দেখা দিলে একের প্রতি অপরের আকর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে হিংসার ভাবও দেখা দেয়। কোন কোন বিষয়ে পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পেলে কিশোরীদের মানসে একটু হিংসার ভাবও দেখা দেয়। আবার কিশোরদের মানসে মেয়ে ছেলের সে কমনীয়তা- সে পেলবতার প্রতি হিংসার উদ্রেক হয়। ক্রমে উভয়ের জীবনের মধ্যে বিভিন্নতা আরও প্রকট হলে তাদের মধ্যে বিচ্ছিনতার সঙ্গে সঙ্গে একে অপর থেকে শ্রেষ্ঠতর বলে প্রতিপন্ন করার ইচ্ছাও প্রবল হয়ে দেখা দেয়। এভাবে কৈশোরের স্তর পার হয়ে যৌবনের প্রবল জোয়ারের মধ্যে যখন মানুষেরা ভেসে চলে, তখন তাদের মানসে কত সাধ, আহলাদ,কত স্বপ্ন, কত লক্ষ্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তার মধ্যে অর্থের লালসার সঙ্গে সঙ্গে নর অথবা নারীর আসঙ্গ কামনা অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠে। তা থেকেই তাদের জীবনে দেখা দেয় নানাবিধ সমস্যা। অন্ন সমস্যা ও যৌন সমস্যা যেমন মানুষকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে-তেমনি তাদের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ সমস্যাও দেখা দেয়। এ সকল সমস্যাও আবার পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। অন্ন সমস্যার সমাধান করতে হলে বস্ত্র সমস্যার সমাধান করতে হয়। শীত-গ্রীষ্মের অত্যাচার থেকে শরীরকে বাঁচিয়ে রাখতে না পারলে ছুটাছুটি করে মানুষ তার আহারের সংস্থান করতে পারে না। আবার পেটের যোগাড় না হলে মানুষের কাজ করবার শক্তিও থাকে না। প্রয়োজনমত পুষ্টিকর আহার্য ব্যতীত মানুষের শরীর টিকে থাকে না। তাই অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করা মানুষের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য।
\r\n
কেবলমাত্র অন্ন-বস্ত্রের সমস্যা নয়, যৌন সমস্যাও মানব জীবনে নানাভাবে দেখা দেয়। বৃদ্ধের তরুণী ভার্যা বা তরুণের বৃদ্ধা ভার্যা হলে যেমন যৌন সমস্যা দেখা দিতে পারে, অসমর্থ পুরুষের সমর্থ স্ত্রী অথবা সমর্থ স্ত্রী অসমর্থ স্বামী থাকলেও যৌন সমস্যা দেখা দিতে পারে। এসব ব্যতীত জীবন্ত ধর্ম, সমাজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানও প্রকৃত প্রেমিকার মিলনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারে। এ সকল সমস্যা ব্যতীত মানুষের মধ্যে যে বৈরীভাব রয়েছে, তার ফলে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বা জাতিতে জাতিতে প্রায় সব সময়ই নানাবিধ স্বার্থের দ্বন্দ্ব রয়েছে, যার ফলে তাদের ব্যক্তিগত জীবনে বা শ্রেণীগত জীবনেও নানাবিধ দ্বন্দ্ব-কলহ প্রায় দেখা দেয়। যৌন সমস্যাও অন্ন সমস্যার ওপর নির্ভরশীল। প্রেমিক-প্রেমিকার আসক্তি যতই প্রবল হোক না কেন, উভয়ের মধ্যে কোনও একজন উপার্জনক্ষম না হলে এবং সংসারের ঠেলা সামলাতে না পারলে, কিছুদিন পরেই তাদের প্রেমের হাটে ভাঙ্গন শুরু হয়। কোন কোন দেশের হাজার হাজার পতিতার জীবন অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, অন্ন সমস্যার সমাধানে অসমর্থ হয়েই তারা এ বৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। অন্যদিকে যৌন-জীবনের উচ্ছৃঙ্খলতা যে রোজগারের পক্ষে কত বড় প্রতিবন্ধক তার প্রমাণ ঘটে সব জায়গায়ই পাওয়া যায়। একজন লোক হয়ত উপার্জন করতে খুবই সক্ষম, কিন্তু পূর্ণ বয়সে যৌন পরিতৃপ্তির অভাবে সে হয়ত বিকৃত রুচির পরিচয় দিতে পারে এবং সেই বিকৃত পথেই হয়ত তার জীবনের সমস্ত আয়-ব্যয় করতে পারে! কাজেই তার জীবনের যৌন সমস্যার সমাধান না হলে তার পক্ষে অন্ন সমস্যার করাও অসম্ভব।
\r\n
অন্নের জন্য, বস্ত্রের জন্য বা যৌন-পরিতৃপ্তির জন্য নানা কারণেই মানব জীবনে যুদ্ধ বাধে। সে যুদ্ধ যখন ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে হয়,তখন তার জন্য গোটা সমাজের মনে কোন আশঙ্কা দেখা দেয় না। সেই যুদ্ধ যদি দুই দেশের মধ্যে প্রবলভাবে বাধে, তা হলে দুই দেশেরই নরনারীর জীবনে নানাবিধ সমস্যা উগ্রমূর্তি হয়ে দেখা দেয়। যুদ্ধের প্রয়োজন সমর্থ বয়সের পুরুষেরা চাষ-আবাদ ছেড়ে কামান-বন্দুক-গোলাগুলি নিয়ে বেরিয়ে পড়লে দেশের চাহিদার পক্ষে উপযুক্ত শস্য উৎপাদন করা সম্ভবপর হয় না। সমাজ-জীবনেও না বিশৃঙ্খলা ও বৈকল্য প্রকাশ পায়। যুদ্ধের সঙ্গে অন্ন সমস্যা ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। কোন দেশ যদি তার প্রয়োজনে উপযুক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন করতে অপারগ হয়, তাহলে অন্য দেশের খাদ্যসামগ্রীর প্রতি সে আকৃষ্ট হবেই। সে দেশ থেকে তার প্রয়োজনমত খাদ্যদ্রব্য জোর করে ছিনিয়ে আনবার লোভ তার মনে প্রবলভাবে প্রকাশ পাবে। আবার যদি কোন দেশে তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপাদনের ব্যবস্থা থাকে, তাহলে সে উদ্ধুত্ত মাল অন্য দেশে চালান দিয়ে তা থেকে দু’পয়সা লাভ করতে লোভী হতে পারে। এতে বাধা পেলে যে কোন দেশ তেরিয়ে হয়ে সরাসরি হানাহানিতে লিপ্ত হয়।
\r\n
অন্যান্য সমস্যার সমাধানে যখন মানুষ প্রমত্ত হয়, তখন গোটা সমাজজীবনে এত আলোড়ন হয় যে, যুদ্ধের ব্যাপারে এক হুলস্থুল কাণ্ড দেখা দেয়। সমাজজীবনে নানাভাবে আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়।
\r\n
এ সকল সমস্যাই সাধারণভাবে মানবজীবনকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। যে সকল দেশে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার লোপ করে দেশের সম্পদকে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্তাধীন করা হয়েছে, সেসব দেশে অন্ন সমস্যা, বস্ত্র সমস্যা বা যৌন সমস্যা পূর্ববর্ণিত আকারে দেখা না দিলেও সেসব সমস্যার এখনও সমাধান হয়নি। সে সকল দেশের রাষ্ট্রে বা রাষ্ট্রের কর্ণধারদের পক্ষে এ সকল সমস্যার সমাধান অত্যন্ত গুরুতর কর্তব্য হয়ে দেখা দেয়। দেশের সকল লোকের পক্ষে উপযুক্ত খাদ্য, পরিধেয়, ও নর-নারীর যৌন ক্ষুধার নিবৃত্তির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করা সম্ভবপর হলেও যৌন সমস্যা বা যুদ্ধ সমস্যার সমাধান তত সহজ হয় না- কারণ সেসব রাষ্ট্রেও পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে সর্বসাধারণ মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নেই। রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য পাত্র বা পাত্রীকে বাধ্য হয়েই তার মনোমত পাত্র বা পাত্রী নির্বাচনের সম্পূর্ণ অধিকার পরিত্যাগ করতে হয়। তার ওপর ব্যক্তিগত জীবনে সকল মানুষের মানসেই অল্পবিস্তর হিংসা রিপু থাকায়- সে সব দেশেও আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য কঠোর হস্তে দুষ্কৃতকারীদের দমন করতে হয়। সেজন্য নানাবিধ পদ্ধতিতে সেসব দৃষ্টান্তকারী লোকদের এ সকল কর্মের মূলে অবস্থিত মানসিকতার বীজ আবিস্কার করা একটা মহাসমস্যা হয়ে দেখা দেয়। অপরদিকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যতীত এ দুনিয়ার অপরাপর যেসব রাষ্ট্র রয়েছে- তাদের সঙ্গে নানাবিধ বিষয় নিয়ে নানাভাবে সংঘর্ষ দেখা দেয়। এমনকি সমাজতান্ত্রিক মতবাদে প্রত্যয়শীল দেশগুলোর মধ্যে যুদ্ধের প্রস্তুতি দেখা দেয়।
\r\n
এতেই স্পষ্টই প্রমাণিত হয়- মানবজীবন যে পর্যায়েই থাকুক না কেন এবং সমাজ বা রাষ্ট্র যেভাবেই গঠিত হোক না কেন- তাতে যে নানা সমস্যা রয়েছে- সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।
\r\n
ব্যক্তি-জীবনে আবার এ সকল সমস্যার মধ্যে শৈশবের প্রশ্নগুলো প্রৌঢ় বয়সে পুনরায় অত্যন্ত প্রবলভাবে দেখা দেয়। শৈশবের যে আদি প্রশ্নগুলো- আমি কোথা থেকে এসেছি? আমি আবার কোথায় যাব? আমার সঙ্গে এ পৃথিবীর সম্বন্ধ কিরূপ ইত্যাকার প্রশ্ন মানুষকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। মৃত্যুর পথে মানুষ যতই অগ্রসর হতে থাকে, ততই সে জানতে চায়- সে কোথায় যাচ্ছে- সে আবার কি এ পৃথিবীতে ফিরে আসবে , না সে বিদায়ই তার পক্ষে চিরবিদায়? আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, স্ত্রি-পুত্র কন্যা সকলের নিকট থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে কি সে আবার এ জীবনের মতই টিকে থাকতে পারবে, না তার মাটির দেহ মাটিতেই মিশে যাবে- এ প্রশ্ন নর-নারী-নির্বিশেষে সকল মানুষের মনে দেখা দেয় এবং সেগুলোর মীমাংসার জন্য মানুষ কোথাও বা গুরুজনের, কোথাও বা পীর মুর্শেদ দরবেশের, কোথাও বা ধর্মাবতার, আবার কোথাও বা শেষ বিচারের আশ্রয় নেয়।
\r\n
তাই স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে- মানবজীবনেই কেন এ সকল প্রশ্ন দেখা দেয়? অন্যান্য পশুপক্ষীর জীবনে তো সেসব প্রশ্ন দেখা দেয় না। দেখা দিলেও তার সমাধানের কোন লক্ষণ তাদের জীবনে পরিলক্ষিত হয় না। এজন্য প্রয়োজন গভীরভাবে মানবজীবনকে অধ্যয়ন করা। মানবজীবনের প্রকৃত সত্তার আলোকে তার জীবনের নানাবিধ সমস্যার সমাধান করতে পারলে মানুষ সুস্থ জীবন যাপনে সমর্থ হতে পারে। অন্যথায় তার জীবনের কোন বিশেষ দিকের ওপর গুরুত্ব আরোপ করার ফলে জীবনের অন্যান্য দিকগুলোতে বিদ্রোহ দেখা দিতে পারে এবং সে বিদ্রোহের ফলে জীবনের ভারসাম্য নষ্ট হওয়া অবশ্যম্ভাবী। মানবজীবনকে নানাভাবে দেখবার সুযোগ রয়েছে। যেমন দেহধারী জীব হিসেবে তাকে জীববিজ্ঞানের দিক থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তার প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করার চেষ্টা করা যায়, তেমনি সমাজবিজ্ঞান বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত অনুসারেও তার প্রকৃত রূপের পরিচয় পাওয়া সম্ভবপর হতে পারে। অপরদিকে মানসিক ক্রিয়াকলাপের অধিকারী হিসেবে তাকে মনোবিজ্ঞানের আলোকে মানবজীবনের প্রকৃত রূপের পরিচয় পাওয়া সম্ভবপর হতে পারে। অপরদিকে মানসিক ক্রিয়াকলাপের অধিকারী হিসেবে তাকে মনোবিজ্ঞানের আলোকে মানবজীবনের প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটন করা আমাদের পক্ষে কর্তব্য এবং তারই আলোকে তার জীবনের মূল লক্ষ্য সম্বন্ধে অবহিত হওয়া উচিত।
\r\n
\r\n
\r\n\r\n
প্রথম পরিচ্ছেদ
\r\n
জীববিজ্ঞানের শিক্ষা
\r\n
জীববিজ্ঞান সম্বন্ধ ডারউনের মতবাদ সর্বপ্রথমে দুনিয়ার সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর ‘প্রজাতির উৎপত্তি’১ (চার্লিস ডারউইনঃ প্রজাতির উৎপত্তি) প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে। উপরিউক্ত দুটি গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমবিকাশের নীতি জীবন-বিকাশে কার্যকরী বলে সর্বত্রই গৃহীত হয়। কাজেই ডারউইনের মতবাদ নিয়েই আলোচনা শুরু করা যাক।
\r\n
ডারউইনের মতে, “ প্রাণীদের মধ্যে প্রত্যেক সৃজনের ব্যাপারে বহু সন্তান উৎপাদনে সক্ষম। তাদের প্রজনন জ্যামিতিক অনুপাতে চলে”। কডফিস নামক এক জাতীয় মাছ আছে। তারা দুই কোটি ডিম পাড়ে। ধারনা করা গেছে, যদি ডেনডিলিয়ন গাছের বীজগুলো পরিণত হয় তাহলে একটা ডেনডিলিয়ন গাছই চতুর্থ বংশানুক্রমে এত গাছ উৎপাদন করবে, যাতে যুক্তরাষ্ট্রের মত রাষ্ট্রের আয়তনের দুইশত পয়ঁতাল্লিশ গুণ বড় দেশ কেবল ঐ গাছের বংশধর দ্বারা ছেয়ে ফেলা যাবে। একটি বীজাণু একদিনেই দশ লক্ষ বীজাণুর সৃষ্টি করতে পারে। ‘লিনেয়াস’৩ বলেছিলেন, “তিনটি মাছি এবং তাদের বংশধররা একটি ঘোড়ার মৃতদেহ ঠিক একটা সিংহের মতই অল্প সময়ে ভক্ষণ করতে পারে”।
\r\n
“উদ্ভিদ এবং প্রাণীরা এত অধিক পরিমাণে প্রজনন করতে সক্ষম হলেও তাদের সকলের বাসস্থানের বা খাদ্যের সংস্থান নেই। এর জন্যই (উদ্ভিদ বা প্রাণীজগতে) চলছে এক জীবন-যুদ্ধ। সেই জীবন-যুদ্ধে যোগ্যতমরাই বেঁচে থাকে। তাকে ডারউইন বলেছেন, “যোগ্যতমের উদ্বর্তন”; (এখানে প্রশ্ন ওঠে) কারা যোগ্যতম? (তার উত্তরে বলা যায়) যাদের শারীরিক গঠন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খায়, (কেবল তারাই টিকে থাকে)। (তার কারণ) (আবার প্রশ্ন ওঠে) ব্যষ্ঠিদের মধ্যে পার্থক্য কেন দেখা দেয়? (দৈহিক গঠন ও তার ক্রিয়ার মধ্যে এক প্রজাতির৪ অন্তর্গত বিভিন্ন ব্যষ্টির মধ্যে, এমনকি একই পিতামাতার সন্তানের মধ্যে কিছুটা ব্যতিক্রম৫ দেখা যায়। একই রকমের প্রাণী থেকে একই জাতীয় সন্তানের উৎপত্তি হয় সত্যি, কিন্তু সন্তানেরা পিতামাতার অনুরুপ হয় না। যারা তাদের পিতামাতা থেকে ব্যতিক্রম হয়, তাদের মধ্যে যাদের ব্যতিক্রমগুলো প্রকৃতির অনুকূল তাদেরকেই প্রকৃতি বাঁচিয়ে রাখে এবং সংরক্ষণ করে। এর নামই প্রকৃতির মনোনয়ন৬। তারা বেঁচে থাকে, বেঁচে চলে এবং সম্ভবত তাদের ব্যতিক্রমগুলো তাদের সন্তান-সন্ততিতে বর্তে। যারা প্রকৃতির অনুগ্রহলাভে অসমর্থ তারা ধংসপ্রাপ্ত হয়। ক্রমশ এভাবে জীবের শারীরিক গঠন পরিবর্তিত হয় এবং কালে এ পরিবর্তন এতো বড় হয়ে দেখা দেয় যে, সম্পূর্ণ অভিনব একটা প্রজাতির উৎপত্তি হয়। ধারালো দাঁত, ছিন্ন করতে সক্ষম চংগল, শিঙ্গের মত শক্ত চামড়া, গরম পশম প্রভৃতি শত্রুদের বিরুদ্ধে এবং প্রাকৃতিক উপাদানের বিপক্ষে জীবনযুদ্ধে প্রয়োজনীয়। এগুলোর উৎপত্তি হয় আকস্মিক প্রকারণের৭ ফলে এবং তারা বংশজ গুনাবলিররূপে রক্ষিত হয়। যে সকল পাখি কোনদিন ভ্রমণশীল নয় তাদের মধ্যে যদি কোনটি হটাৎ তাদের আদিম আবাস ছেড়ে অন্যত্র চলে যায় এবং প্রচুর খাদ্যদ্রব্যের সন্ধান পায় তা’হলে সে নতুন স্থানে তারা বেঁচে থাকবে, তাদের বংশবৃদ্ধি হবে আর তাদের এ বিশেষত্ব তাদের সন্তানদের মধ্যেও দেখা দেবে। এর থেকেই সহজাত প্রবৃত্তির৮ উৎপত্তি। এমন যে মানব-চক্ষু যাতে অভিযোজনের৯ এতো বিস্ময় প্রকাশ পায়, তাও আলোর প্রতি সংবেদনশীল১০ একটিমাত্র কোষের গ্রুপ থেকে দেখা দিতে পারে; তার ফলে যারা (এ অঙ্গের) ভাগ্যবান অধিকারী তাদের বিপদ ও শিকার উভয় সম্বন্ধে পূর্বাহ্নে সতর্ক করতে পারে।
\r\n
মানবজীবনও চলছে বিবর্তন তত্ত্বের এ নীতি অনুসরণ করে। মানুষের মাঝে যারা বাঘ-ভাল্লুক থেকে লুকিয়ে আত্মগোপন করার কৌশল আয়ত্ত করেছিল তারাই কেবল ঠিক রয়েছে; যারা পারেনি, তাদের নাম-গন্ধও দুনিয়ায় নেই। মানুষের নানা শাখা-উপশাখাও এইভাবেই লয় পেয়েছে। দুনিয়ার বুকে টিকে থাকার মত সামর্থ্য না থাকায় প্রাকৃতিক নিয়মেই নানাবিধ জাতি লোপ পেয়েছে। মানুষের বেলায় কেবল প্রকৃতির অন্য দশটি জীবের আক্রমণ থেকে বেঁচে থাকার শক্তি থাকলেই চলবে না, শক্তিশালী অপর মানুষের আক্রমণ থেকে বেঁচে থাকবার মত সামর্থ্যেরও প্রয়োজন।
\r\n
চোখের সামনেই দেখা যায়, অনেকগুলো প্রাণীই বেঁচে থাকবার মত সংগঠনের অভাবে ক্রমেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। লাল অথবা হলদে রঙের ফড়িঙের সংখ্যা খুব কম; কারণ, তারা পাখিদের চোখে সহজেই ধরা পড়ে। সবুজ রঙের ফড়িং সংখ্যায় খুব বেশি। তাদের রঙ ঘাসের রঙের মত থাকায় তারা অতি সহজেই ঘাসের সাথে লুকিয়ে আত্মরক্ষা করতে পারে। পুরাকালের যেসব জন্তু-জানোয়ারের অস্থিপঞ্জর পাওয়া যায়, তা থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয়, একদিন দুনিয়ার বুকে তারা অবাধে বিহার করতো। জীবনযুদ্ধে উপযোগী শারীরিক সংগঠন তাদের না থাকায় প্রকৃতির বুকে নানাবিধ ঝড়-ঝঞ্ঝা, তুষারপাতের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে না পারায়, তারা স্বাভাবিকভাবেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।
\r\n
মানব জাতির নানা শাখাও এভাবেই লয় পেয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসী ‘বুশম্যান’১১ বা আমাদের দেশের নানাবিধ উপজাতি-যেমন কোল, ভীল বা সাঁওতাল যেভাবে ধ্বংসের পথে চলছে, শতাধিক বছর পরে আর তাদের কোন চিহ্ন নাও থাকতে পারে। তার কারণ, জীবনযুদ্ধে ওরা বারবার পরাজিত হচ্ছে। সে পরাজয়ের ফলে বিজেতা তাদের ব্যবহার করেছে যন্ত্রপাতির মত। তাদের বংশবৃদ্ধি বা মানসিক উৎকর্ষের কোন সুযোগ দিচ্ছে না। ডারউইনের ঐ মতবাদ প্রচারিত হওয়ার পরে বিখ্যাত প্রাণীবিদ উইজম্যান১২ প্রমাণ করেছেন যে, বাচ্চাদের মধ্যে মা-বাপ থেকে প্রাপ্ত জননকোষ১৩ কোন কালেই নষ্ট হয় না। কাজেই বিভিন্ন জাতি বা প্রজাতির মধ্যে জননকোষের ধারা চিরকাল অব্যাহত থাকে। প্রকারণের দ্বারা জননকোষের তারতম্য হয় না। অন্যদিকে ডারউইনের বা লেমার্কের ১৪ ধারনা ছিল প্রকারণের দ্বারা লব্ধগুণ১৫ সন্তানদের মধ্যে দেখা দেয়। বর্তমান জীববিজ্ঞানবিদ্দের এ সব জটিল তর্কে আপাতত লিপ্ত না হয়েও ডারউইনের মতবাদের নানা ত্রুটি সহজেই ধরতে পারা যায়। আপাতত জীবজগতের সর্বত্রই জীবন-যুদ্ধের দৃশ্য হলেও ডারউইন জীবনের শত্রুতার দিকটাই লক্ষ্য করেছেন। প্রাণীজ জগৎ ও প্রকৃতির মধ্যে তিনি বৈরিতার সূত্রই আবিস্কার করেছেন, তাদের পারস্পরিক সহযোগিতার দিকটা তিনি এড়িয়ে গেছেন। তিনি জীবজগতের এ যুদ্ধকে শত্রুর বিরুদ্ধে এবং প্রাকৃতিক উপাদানের বিপক্ষে জীবের টিকে থাকার যুদ্ধ বলে অভিহিত করেছেন। কাজেই তাঁর মতানুসারে চারটে যুদ্ধই সম্ভবপর বলে ধরে নিতে হয়। জীবকে তার শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়। এ শত্রু কারা?
\r\n
১। এ শত্রু একই প্রজাতির১৬ অন্তর্গত বিভিন্ন ব্যক্তি হতে পারে।
\r\n
২। এক প্রজাতির বিরুদ্ধে অন্য প্রজাতিও হতে পারে।
\r\n
৩। সম্পূর্ণ ভিন্ন দুই জাতিও হতে পারে।
\r\n
৪। প্রাকৃতিক বিভিন্ন উপাদান১৭ যেমন-পানি, বায়ু,গ্রীষ্ম,তুষারপাত প্রভৃতিও হতে পারে।
\r\n
একে একে সবকটি যুদ্ধের আলোচনা করা যাক। ডারউইনের মতবাদ অনুসারে একই পূর্বপুরুষ থেকে সকল জীবেরেই উৎপত্তি হয়েছে। কীট-পতঙ্গ থেকে শুরু করে মানবজাতি পর্যন্ত সকল জীবেরই আদি পিতা একটি মাত্র জীবকোষ। মানুষ,গরু,মহিষ,হাতি,বাঘ,ভালুককে আপাতত ভিন্ন শ্রেনী মনে হলেও তাদের আদি জনক একই জীবকোষ। আকস্মিক প্রকারণ,জীবনযুদ্ধ,উপযুক্ততমের উদবর্তন,প্রাকৃতিক নির্বাচন১৮ প্রভৃতি চিন্তার মাধ্যমে তিনি দেখিয়েছেন-এক জীব থেকেই নানাবিধ শ্রেনীর সৃষ্টি হতে পারে।
\r\n
একই আদি পিতা থেকে উৎপত্তি হলেও বর্তমানে বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে কোন কোনটি সগোত্র বলে দেখা যায়। তাদের মধ্যে সাদৃশ্য বর্তমান; যেমন,বাঘ জাতীয় প্রজাতির মধ্যে বিড়াল,পুমা,চিতাবাঘ,বড় বাঘ এক গোষ্ঠী বলে পরিচিত। তেমনি গরু,মহিষ,ছাগল প্রভৃতি এক প্রজাতীয় বলে মনে হয়। পাখিদের মধ্যে শত বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হলেও তাদের মধ্যে কতকগুলো সাধারণ গুণ বর্তমান। অপরদিকে মানবজাতি১৯ ও বাঘ জাতীয় বা গরু জাতীয় জীবের মধ্যে পার্থক্য এত বেশি যে, তাদের ভিন্ন প্রজাতি না বলে ভিন্ন জাতি নামেই অভিহিত করা ভাল। বিবর্তনবাদের সূত্রানুসারে তাই জাতির সঙ্গে জাতিরও যুদ্ধ হতে পারে।
\r\n
১. একই প্রজাতির অন্তর্গত বিভিন্ন ব্যষ্টির মধ্যে যুদ্ধ হয়। যেমন গো-জাতির বিভিন্ন ব্যষ্টির মধ্যে সচারাচর মারামারি,হানাহানি হয়। যারা দূর্বল, যারা পঙ্গু, তারা সহজেই সবলের হাতে নিধনপ্রাপ্ত হয়। এ সকল ঘটনা নিত্যই আমাদের চোখে পড়ে। প্রকাণ্ড ষাড় কর্তৃক ছোট ছোট বাছুরের অকাল মৃত্যু আমাদের প্রত্যেক গ্রামেই মাঝে মাঝে দেখা যায়। পুরুষ বিড়াল সুযোগ পেলেই সদ্যোজাত বিড়াল ছানাগুলোকে মেরে ফেলে। বাড়িতে শক্তিশালী পুরুষ মোরগ থাকলে তার অত্যাচারে অনেক সময় ছানা পোষা দায় হতে পড়ে। তবু এটি জীবজগতের একটি দিক মাত্র-যে, মোরগ ছানা হত্যায় আনন্দ পায়, সে-ই আবার চিলের আক্রমণ শুরু হলে চিৎকার করে অসহায় বাচ্চাদের সাবধান করে দেয়। যূথচারী প্রাণীদের-যেমন বন্য হস্তী,বন্যমহিষ প্রভৃতি বড়দের মধ্যে অত্যন্ত স্নেহপরায়ণতা বর্তমান। নিজের বাচ্চা না হলেও গোঠের অন্যান্য প্রাণীর বাচ্চাগুলোকে তারা আগলে রাখে। যে সকল পাখি একই ঋতুতে বাচ্চা তোলে-তাদের মধ্যে বেশ সহনশীলতা ও মহানুভবতার নীতি দেখা যায়;সবেমাত্র উড়তে শিখলে অনেক সময় এক বাসা থেকে বাচ্চাগুলো অন্য বাসায় ভুলে গেলেও বুড়ো পাখিরা তাদের মেরে ফেলে না। একটু ভয় দেখিয়েই ক্ষান্ত হয়।
\r\n
২. এক প্রজাতির বিরুদ্ধে অন্য প্রজাতির বা এক জাতির বিরুদ্ধে অন্য জাতির লড়াই দেখা যায়। বিড়ালের ইঁদুর শিকার, সাপ ও বেজির যুদ্ধ, পাখিদের দ্বারা কীট-পতঙ্গাদির বিনাশ সব সময়ই চোখে পড়ে। মানুষ বুদ্ধিবলে সকল জীবের সেরা হলেও তাদের বাঘ,ভালুক থেকে আরম্ভ করে কীটপতঙ্গাদির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়। কাজেই প্রজাতির বিরুদ্ধে প্রজাতির অথবা জাতির যুদ্ধ জীবনে অতি সত্যিকার ঘটনা। তবু মৈত্রীর উদাহরণেরও অভাব নেই। সচরাচর এক প্রজাতির জীবের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হলেও মাঝে মাঝে দুই প্রজাতির জীবের মধ্যে মৈত্রীর সমন্ধ দৃষ্ট হয়। প্রাণী-বিজ্ঞানবিদেরা আবিস্কার করেছেন-মাংসাশী কুমীরের দাঁতের মাংস এক রকমের ছোট পাখি পরিস্কার করে নেয়। তাতে কুমীরের দাঁত যেমন পরিচ্ছন্ন হয়, তেমনি সেই পাখিগুলোরও আহারের সংস্থান হয়। গরু ও মহিষের শরীর থেকে পোকা বেছে নেয় শালিকেরা, তাতে তৃতীয় জাতীয় জীবের নিধন হলেও এই দুই জাতির মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে।
\r\n
মানুষ বুদ্ধিবলে অন্যান্য সকল প্রজাতিকেই তার জীবনযাত্রার নানা প্রয়োজনে ব্যবহার করে। বাঘ,ভালুক এমনকি বিষধর সাপকে মানুষ ব্যবহার করে তার নানাবিধ প্রয়োজনে। এতে শত্রুর দ্বারা অনেক ক্ষেত্রেই তার উপরকার হয়। বিভিন্ন জাতীয় মানুষের মধ্যে যুদ্ধ চলে সত্য,কিন্তু সে যুদ্ধে একে অপরকে সম্পূর্ণ বিনাশ করে লাভবান হতে পারে না। মানুষের বেলায় এ নিয়মের ব্যতিক্রম স্বতঃসিদ্ধের মত পরিস্কার। এক জাতি কর্তৃক বিজিত অপর জাতি যদি বিজেতার হাতে সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তাহলে বিজয়ের কোন অর্থই হয় না। বিজয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য বিজিত জাতির দ্বারা কাজ আদায় করা। আধুনিক পরিভাষায় তাকে শোষণ বলা হয়। যদি বিজিত জাতিকে ধ্বংসই করা হয় তাহলে শোষণের অবকাশ কোথায়?
\r\n
৩.বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদান যেমন-জল, বায়ু,শীত,গ্রীষ্ম প্রভৃতির সঙ্গে কেবল যুদ্ধ করেই জীব টেকে না; তারা জীবের বেঁচে থাকবার পক্ষেও অবশ্য প্রয়োজনীয়। জীবের দৈহিক সংগঠন উপযোগী না হলে এদের অত্যাচারে জীব লয় পায়, তেমনি দৈহিক সংগঠনের উপযুক্ত হলেও এদের অভাবে সে লয় পেতে পারে। দৈহিক সংগঠনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক উপাদানকে গ্রহণ করেই জীব বেঁচে থাকে। তাদের পরস্পরের সহযোগিতা অনেক ক্ষেত্রেই অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।
\r\n
জীবিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীর জীবের মধ্যে যুদ্ধ রয়েছে সত্যিই, তবে সে যুদ্ধই জীবনের একমাত্র রূপ নয়। সে যুদ্ধের মধ্যেও প্রেম,মৈত্রী ও ভালবাসা রয়েছে। সন্তানের জন্য পিতামাতার বুকে রয়েছে অপার স্নেহ,দম্পতির মধ্যে সাধারণত রয়েছে অগাধ ভালবাসা,বাচ্চাদের প্রতি বুড়োদের রয়েছে বাৎসল্যবোধ। একই প্রজাতির বিভিন্ন ব্যষ্ঠিদের মধ্যে রয়েছে সংঘবদ্ধ হয়ে আত্মরক্ষার চেষ্ঠা। মানবজীবনে কেবল যুদ্ধই একমাত্র সারসত্য নয়। সেই যুদ্ধের অন্তরালেও মানুষের যূথচারী প্রবৃত্তি তাকে সমষ্টি-চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে। মানব-জীবনের অনেকগুলো কাজ-কর্মই নিয়ন্ত্রিত হয় প্রেম,দয়া-মায়া-স্নেহ প্রভৃতি সুকুমার বৃত্তি দ্বারা।
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n\r\n
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
\r\n
মনোবিজ্ঞানের শিক্ষা
\r\n
\r\n
ফ্রয়েডীয় মতবাদ
\r\n
\r\n
অষ্ট্রিয়ার বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানবিদ ফ্রয়েডের কামসর্বস্ববাদ২০ বা সর্বকামিতা আজ দুনিয়ার সকল জ্ঞানী লোকের নিকট পরিচিত। তাঁর মতে মানুষ তার আদি কাম দ্বারা পরিচালিত। মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা,সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূলে রয়েছে শুধুমাত্র কাম। এ সত্যটি প্রমাণ করাই ছিল ফ্রয়েডের জীবনের লক্ষ্য। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে মনস্তত্ত্ববিদ মহলে ফ্রয়েড ছিলেন রাজাধিরাজ। বর্তমানে কার্ল জুঙ২১ ও এ্যাডলারের২২ বিশ্লেষণে তাঁর মতবাদে নানা ত্রুটি ধরা গেলেও আমাদের কাব্য ও সাহিত্য তাঁর মতবাদের ছাপ রয়ে গেছে অম্লান। তাই তাঁর মতবাদ নিয়ে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন।
\r\n
তাঁর ধারণা, সজ্ঞান মনে যেসব কামনা-বাসনা দূষণীয় বলে পরিত্যাক্ত হয় সেগুলো অচেতন মনে গিয়ে বাসা বাঁধে। সেখানে প্রক্ষোভের২৩ রয়েছে প্রাধান্য। সজ্ঞান মনে বাসনাগুলোকে করা হয় অবদমিত; তাই তারা অচেতন মনেই এই অন্ধকারে এসে জড়ো হয়। এতে সজ্ঞান মনের শান্তির পক্ষেই হয় সুরাহা। তবে উদ্ধায়ুজ২৪ লক্ষণ দেখা দিলে নানাভাবে মনকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। অবদমিত বাসনার সর্বজনীনতা আবিস্কার করে ফ্রয়েড তাদের প্রকাশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আবিস্কারে মনোনিবেশ করেন। সর্বপ্রথমে স্বপ্নের মধ্যে তিনি তার সন্ধান পান। তাঁর মতে স্বপ্নও অচেতন মনের ক্রিয়ার ফল। সজ্ঞান মনের বেড়াজাল ডিঙ্গিয়ে স্বপ্নে আমাদের আকাংক্ষিত বস্তু দেখা দেয়। যদিও দিনের বেলায় জাগ্রত অবস্থায় চৈতন্যের রয়েছে প্রাধান্য,নিদ্রাতে কোন প্রহরী বা মনোদ্ধারী না থাকায় অচেতনের পক্ষে যেন দুয়ার খুলে দেওয়া হয়।
\r\n
অবদমনের শক্তিগুলোকে ফ্রয়েড প্রহরী২৫ বলেছেন। তাঁর মতে আমাদের মনের অনেকগুলো বাসনাই অবদমিত। আমরা সে সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নই। বাইরে থেকে নানাবিধ পুলিশী শক্তি আমাদের বাসনাগুলোকে অবদম করে, আমরা নিজেরাও পুলিশী ভাব নিয়ে তাদের রুদ্ধ করি। নিদ্রায় সে পুলিশের হুকুমবরদারী থাকে না বলেই আমাদের বাসনাগুলো হুড়হুড় করে স্বপ্নে রুপায়িত হয়ে থাকে। কেবল স্বপ্নে নয়, লক্ষণ সংক্রান্ত কার্যাবলি থেকেও ফ্রয়েড উদাহরণ সংগ্রহ করে তাঁর মতবাদ প্রমাণ করেছেন। আমরা সকলেই জানি, অনেক সময় অনবধানতাবশত আমরা অনেক কাজ করি। যেমন লিখতে বসেছি, টেবিলের একপাশে এক গ্লাস পানি রয়েছে। হটাৎ কনুই লেগে গ্লাসটা পড়ে গেল। এক আমরা অনবধানতাবশত কাজ বলে থাকি। ভাবনাবিহীন কাজও করি। যেমন পথ চলতে যেয়ে একটা লাঠি পথিমধ্যে পেয়ে লাথি দিয়ে তাকে ফেলে দিই। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অন্যান্য মানুষের সঙ্গে লেনদেনের ব্যাপারে অথবা এক কাজ করতে অন্য কাজ করাতে সজ্ঞান মনের স্রোতে কিভাবে এসব কার্যাবলি প্রকাশ পায় তার সন্ধান পাই। যদিও আপাতত এসব কার্যকে আপতিক২৬ মনে হয়, আসলে তারা অবদমিত বাসনার২৭ প্রকাশ ব্যতীত আর কিছুই নয়। যেসব কার্যের মাধ্যমে এভাবে আমাদের গুপ্ত বাসনা অনিচ্ছাকৃতভাবে প্রকাশ পায় ফ্রয়েড তার সহজ নাম দিয়েছেন ত্রুটি। প্রচলিত ভাষায় তারা ভুল-ভ্রান্তি নামে পরিচিত। এসব ভুল-ভ্রান্তি ত্রুটি-বিচ্যুতির উহ্য অর্থ আবিস্কারের মধ্যে রয়েছে ফ্রয়েডের কৃতিত্ব। স্বপ্নের মতই তাদের মধ্যে রয়েছে একটা বাহ্যিক অর্থ,একটা গূঢ় অর্থ। সেই গূঢ় অর্থই আমাদের মনের অন্তর্নিহিত উত্তেজনার প্রাবল্যে বা প্রহরীর অনুপস্থিতিতে আমাদের পেশিগুলোকে ক্রিয়াশীল করে তোলে; আমরা ভাষায় তাদের প্রকাশ করি।
\r\n
আমাদের মনের সে সব অবদমিত বাসনার জন্ম কাম থেকে। জীবনের সকল স্তরের আলোচনা করে ফ্রয়েড প্রমাণ করতে চেয়েছেন কামপ্রবৃত্তির দ্বারা মানব-মন সর্বত্রই পরিচালিত। তাঁর ধারণা, মানবজীবনের মূলে রয়েছে লিবিডো২৮ বা বিরাট কামশক্তি। ছোট ছোট শিশুরা ফ্রয়েডের মতে আত্মকামী২৯। তাদের মধ্যে স্বতঃপ্রণোদিত কামের লক্ষণ প্রকাশ পায়। তাদের আদর-সোহাগ করাতে তারা আংশিকভাবে কামতৃপ্তি লাভ করে। ছোট ছোট বাচ্চাদের শরীরের নানাস্থানে কামকেন্দ্র রয়েছে। বাইরে থেকে এসব কামকেন্দ্র উত্তেজনার সৃষ্টি করলে তারা কামসুখ ভোগ করে। ফ্রয়েডের ধারণা, শৈশবের এই কামাবস্থা জন্ম থেকে পাঁচ বৎসর বয়স পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। এ সময়কে ফ্রয়েড বলছেন শৈশবাবস্থা। দ্বিতীয় পর্যায়ে শুরু হয় অস্ফুটচিত্ততার কাল৩০। তার সময় তিনি নির্দিষ্ট করেছেন, পাঁচ থেকে বারো বৎসর পর্যন্ত। এ সময় লিবিডো হয়ে পড়ে ব্যক্তিকেন্দ্রিক। শৈশব ও কৈশোরের মধ্যবর্তী এ অবস্থায় কাম-নদীতে কিছুটা ভাটার টান দেখা যায়। বারো বছর থেকে আঠারো বছর পর্যন্ত কৈশোরের সীমা। এটি যেন কামজীবনে এক ঝটিকাবিক্ষুব্ধ অবস্থা। এর সূচনায় জীবনে যেন লণ্ডভণ্ড কাণ্ড আরম্ভ হয়। ফ্রয়েডের মতে,শৈশবে মানুষ থাকে আত্মকামী, অস্ফুটচিত্ততার সময় তার কাম ধাবিত হয় একই লিঙ্গের বা বিপরীত লিঙ্গের কোন লোকের প্রতি। কৈশোরের সমাগমে সম্পূর্ণ বিপরীত লিঙ্গের লোকের প্রতি তা হয় কেন্দ্রীভূত।
\r\n
জীবনের কোন পর্যায়ে কামের বিষয়বস্তুরূপে কোন কিছুকে গ্রহণ করলে, পরবর্তী পর্যায়ে তা অপরিবর্তিত থেকে যায়, তা হলে তাকে বৈকল্য৩১ বলা যায়। যেমন শৈশবের আত্মকাম যদি অস্ফুটচিত্ততার সময় আত্মকাম থেকে কোন ব্যক্তিমুখী না হয় তা হলে বুঝতে হবে সে ব্যক্তির জীবনে বৈকল্য দেখা দিয়েছে অথবা তার কাম শৈশবের পর্যায়ে স্থায়ী হয়ে রয়েছে। একে বলা হয় স্থিতাবস্থা৩২। এমনও হতে পারে যে, এক ধাপ ডিঙ্গিয়ে গিয়ে কাম আবার নিচের ধাপে ফিরে যেতে পারে যেমন কৈশোরের বিপরীত লিঙ্গের লোকের প্রতি ধাবিত না হয়ে আবার ফিরে গিয়ে শৈশবের আত্মকামে পরিণত হতে পারে। একে বলা হয় প্রতিসরণ৩৩। এরূপ বৈকল্য দেহকা দিলে বুঝতে হবে হয় স্থায়ী হয়ে, না হয় উল্টো দিকে কাম-নদীর স্রোত বইতে শুরু করেছে।
\r\n
এ লিবিডোর বা কামশক্তির পশ্চাৎপটে পরিবার রয়েছে। এ জন্যই ফ্রয়েড পারিবারিক রোমান্সের বিকাশ দেখিয়েছেন; এখানে সর্বপ্রধান কূটএষণা পিতৃ অথবা মাতৃকেন্দ্রিক। তাই স্বভাবতই ছেলেরা পিতৃ-বিদ্বেষী, কারণ পিতার স্থান সে অধিকার করতে চায়। আমাদের প্রত্যেকেরই এ পাপের পথে যাত্রার রয়েছে উত্তরাধিকার। তাই স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে হলে, এ ইদিপাস*(পৌরণিক যুগের এক নায়ক,ভ্রমবশত যে আপন মাতাকে বিবাহ করেছিল।) এষণাকে নির্মূল করতে হবে। শৈশব এ এষণা প্রবলভাবে দেখা দেয় সত্য, তবু দীর্ঘকাল স্থায়ী হওয়ার দরুন পরিণত বয়েসেও নানা বিপদের সৃষ্টি করতে পারে। যেমন কৈশোরের কাম স্বভাবতই স্বাধীনভাবে পরিতৃপ্ত লাভ করে কিন্তু পিতার প্রতি ভয়ের দরুন এ পর্যায়ে তা ধ্বজচ্ছেদ কুটেশায়৩৩ পরিণত হতে পারে। এ এষণায়গ্রস্ত ব্যক্তি ভয় করতে পারে যে যৌন জীবনে সে হবে অকৃতকার্য। কাজেই ফ্রয়েডের মতে এই ইদিপাস এষণাই যৌন জীবনের বিকাশে নানাদিকে দেখা দিয়ে হয় কার্যকরী।
\r\n
শিশুমাত্রই অত্যন্ত আত্মকেন্দ্রিক। এ আত্মকেন্দ্রিকতা লিবিডোর বিকাশে নানভাবে থাকে ক্রিয়াশীল। ছোট বাচ্চা মাত্রই অত্যন্ত জুলুমবাজ, সে সর্বেসর্বা হতে চায়। পরিণত জীবনে তার এ প্রবণতা ধর্ষকামে৩৪ রূপ নিয়ে দেখা দেয়, এতে কামের বস্তুর প্রতি একই সঙ্গে বাসনা ও নিষ্ঠুরতা থাকে পরস্পর সংযুক্ত এবং তাতে ধর্ষকামী সুখভোগ করে। এই যৌন মনোভাবে ঠিক উল্টো দিক হল মর্ষকাম৩৫। এতে যৌন পরিতৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে কষ্ট পাওয়াতেও মর্ষকামী সুখ ভোগ করে। লিবিডোর বিকাশের এ পর্যায়েই পুরুষ ও নারীর ভাব হয়ে পড়ে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। সাধারণত পুরুষমাত্রেই ধর্ষকামী এবং নারীমাত্রই মর্ষকামী। সেরূপ ইদিপাসের নারীরূপ হল ইলেকট্র।** (শ্রীনৃপেন্দ্র কুমার বসু তাঁর ফ্রয়েডের ভালবাসার নাম দিয়েছেন শতরূপা কূটেশা।) ফ্রয়েডের মতে মেয়েদের শৈশবে পিতৃসঙ্গ কামনা থাকে স্বাভাবিক। পরে লিবিডোর বিকাশে তাকে বাধ্য হয়েই তা ত্যাগ করতে হয়।
\r\n
ছেলে ও মেয়েদের ইন্দ্রিয়গুলোর পার্থক্যের দরুন মেয়েদের মনে উপস্থঈর্ষার৩৬ সৃষ্টি হয়। একে ছেলেদের ধ্বজচ্ছেদ কূটেশার নারীরূপ বলা যায়।
\r\n
এভাবে জোড়া জোড়া বিভিন্ন ও প্রতিপক্ষীয় ধারণাগুলোকে ফ্রয়েড বলেছেন জোড়া দ্বি-মেরুত্ত৩৭। সুখ-দুখ, ভালবাসা ও ঘৃণা পুরুষালী ও মেয়েলী ভাব প্রভৃতি ব্যতীত আর কিছুই নয়। তেমনি, একই সঙ্গে ভীতি,ঘৃণা ও ভালবাসা, সৃজন করা ও ধ্বংস করার প্রভৃতির নাম উভয়বলতা। লিবিডো প্রসঙ্গে আমরা ফ্রয়েডের আর একটি ধারার সঙ্গে পরিচিত হয়। তাকে বলা হয় উদ্গতি৩৮। যে শক্তিমূলে মানুষ কোন বিষয়ের প্রতি হয় আসক্ত বা কর্মশক্তি ব্যয় করে, সে নিশ্চয়ই লিবিডো ছাড়া আর কিছু নয়। আত্মকেন্দ্রিক লিভিডোর শক্তি আত্মপ্রকাশ৩৯ বা জীবনে কোন বিশিষ্ট পদ অধিকার বা সামাজিক প্রতিপত্তি লাভ প্রভৃতিতে ব্যয়িত হয়। যখন লিবিডো কোন সমস্যার সমাধানে বা কারকর্মে ব্যয়িত হয় তখন তাকে ফ্রয়েড বলে বিষয়কেন্দ্রিক লিবিডো৪০।
\r\n
এই যে আত্মকেন্দ্রিক থেকে বিষয়কেন্দ্রে লিবিডোর কার্যকারিতা, ফ্রয়েড তার নাম দিয়েছেন স্থানান্তর। যে ব্যক্তির আত্ম-উত্তেজনা ছিল তার মনের মধ্যেই স্থিত সে ব্যক্তিই যখন কাব্য রচনায় পেলো সত্যিকার আনন্দ তখন বুঝতে হবে তার লিবিডোর তার বিষয়বস্তু পেয়ছে এবং আত্মকেন্দ্রিক রূপ ত্যাগ করে সে বিষয়কেন্দ্রিক৪১ হয়ে পড়েছে।
\r\n
লিবিডোর এবম্বিধ প্রকাশে বা স্থানান্তরের মধ্যে তার উদ্গতির কাজও হয়। কাব্য,নাটক,রোমান্স,শৌর্য,শালীনতা প্রভৃতি লিবিডোর উদ্গত রূপ। কোন বিষয়বস্তুতে আমাদের আসক্তি দেখা দিলে বুঝতে হবে তা কামবাসনা থেকে উদ্ভূত এবং তার মধ্যে কামের সে প্রখরতা রয়েছে।
\r\n
লিবিডোর পরিভ্রমনের ফলেই নানাবিধ জটিল অবস্থার সৃষ্টি। উদ্ধায়ুর৪২ বেলা,লিবিডোর কার্যকারিতার নীতি প্রয়োগ করে ফ্রয়েড স্থির-নিশ্চিত হয়েছেন যে,উদ্ধায়ু কাম-জীবনের ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই নয়। স্বাভাবিক যৌন-জীবনে উদ্ধায়ু সম্ভব নয়। ফ্রয়েডের ধারার অনুসরণ করলে জীবনের পক্ষে স্থায়ী অবস্থার৪৩ বদ্ধাবস্থায় অথবা প্রতিসরণে পৌঁছার রয়েছে আশঙ্কা। তার সোজা অর্থ এই যে, লিবিডো কোন এক বিশিষ্ট পর্যায়ে যেয়ে স্থায়ী হয়ে বসে থাকতে পারে। যেমন অস্ফুটচিত্ততার*( অস্ফুটচিত্ততার (Latency period) সময় উভয় লিঙ্গের লোকের আসক্তি স্বাভাবিক।) সময় যদি অন্য কোন ব্যক্তির প্রতি কাম ধাবিত না হয় তাহলে বুঝতে হবে এষণাগ্রস্ত হয়ে এ লিবিডো এ জায়গায়ই স্থির হয়ে পড়েছে। কৈশোরে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আসক্তি ধাবিত হতে পারে। ফ্রয়েড, মানব-মনের বিভিন্ন পর্যায়ে কতকগুলো বৈকল্প আবিস্কার করে ধরে নিয়েছেন, তারা শৈশবাবস্থায়ও বিদ্যমান। ইদিপাস-সমকামিতা বা আত্মকাম ইত্যাদি এষণা পরিণত বয়সেও মানবজীবনে দেখা দেয় বলেই তাদের অস্তিত্ব গোড়াতেই বর্তমান বলে কেমন করে প্রমাণিত হয়? পরিবেশগত ও পারিপার্শ্বিক নানাবিধ কারণের সমাবেশের ফলে তাদের উৎপত্তি হতে পারে, যেমন হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের একত্র সমাবেশ হলেই পানি হয় না, তার জন্য বিদ্যুতের দরকার। তেমনি হয়ত কেবল মাতৃকেন্দ্রিক ভালবাসার বীজ মানবমনে থাকলেই ইদিপাসের পরিণতি হতে পারে না। আরও অনেকগুলো ফ্যাকটারের প্রয়োজন। ফ্রয়েড সে ফ্যাকটারগুলোর ওপর কোন গুরুত্ব আরোপ করেননি। এতে বৈজ্ঞানিক দিক দিয়ে তার ত্রুটি সহজেই ধরা পড়ে। কেবল ইদিপাসের বেলায় নয়, অন্য সবগুলো এষণার বেলাতেও তিনি বাইরের ফ্যাকটারগুলোর উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করেননি। উদাহরণস্বরূপ ইদিপাসকেই ধরা যাক। শুধু কামের দ্বারা মানবমন পরিচালিত হলে, পিতা বা সমাজের ভয়ে এ কামের পথে যাত্রায় ছেলে নিবৃত্ত হবে কেন? পিতার স্থান যদি সে অধিকার করতে চায় তাহলে তাতে ভয়ের কোন স্থান থাকতে পারে না। যদি পিতাকে তার বিরাট বপু বা আধিপত্যের জন্য ভয় করে তবে তার স্বাভাবিক কাম-বাসনার সঙ্গে সঙ্গে ভয়কে এক আদি প্রবৃত্তি বলে স্বীকার করে নিতে হবে।
\r\n
ফ্রয়েড অবদমনের শক্তিগুলোকে বলেছেন প্রহরী। তারা প্রায়ই সামাজিক শক্তি। সে সামাজিক শক্তিগুলোর উৎপত্তি কোথা থেকে? যদি বলা হয় যে, সেই আদি কাম থেকেই, তাহলে আমরা একটা বিষাক্ত বৃত্তের মধ্যে পড়ে যাই। কামনা বাসনা থেকে প্রহরী৪৪ গুলোর উৎপত্তি আর পাপ থেকে জন্ম নিয়েই তার পাপ বাসনাগুলোকে করে অবদমন। আবার যদি বলা হয়, সেগুলোর জন্ম পাপ-বাসনা থেকে নয়, অর্থনৈতিক, পারিপার্শ্বিক বা জীবনযুদ্ধের প্রয়োজনে সেগুলোর উৎপত্তি তাহলে কাম ব্যতীত আরো নানাবিধ ফ্যাকটার মানবজীবনে কার্যকরী বলে স্বীকার করে নিতে হয়।
\r\n
ফ্রয়েড বলতে চেয়েছেন-আমাদের জীবনে অতৃপ্ত বাসনাগুলো মগ্ন চৈতন্য কার্যকরী থাকে বলে স্বপ্নে লক্ষণ সংক্রান্ত কার্যাবলিতে, অনবধানতাবশত কার্যবলিতে বা ভাবনাহীন কার্যাবলিতে সে অবরুদ্ধ বাসনা আত্মতৃপ্তি লাভ করে। কোন কোন ক্ষেত্রে তা হয়ত সত্য কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই যে তা সত্য তা কেমন করে বলা যায়? অনবধানতাবশত যদি একজন গভীর গর্তে পড়ে যায় তাহলে তার মনে ঐ পড়ে যাওয়ার বাসনা কার্যকরী ছিল বলে কি স্বীকার করতে হবে? তাতে তো মানুষের আদিম প্রবৃত্তিকেই অস্বীকার করা হয়।
\r\n
রুদ্ধ বাসনামাত্রই সে কামজ তার প্রমাণও অত্যন্ত দুর্বল। কামজ না হয়েও আমাদের নানাবিধ বাসনা প্রকাশ পেতে পারে, এ সত্যটি অস্বীকার করেও ফ্রয়েড সত্যের অবমাননা করেছেন। মোটকথা, তার মতবাদের অনুকূল কতকগুলো তথ্যের উল্লেখ করে তাঁর বিরুদ্ধে মতের পোষণকারী তথ্যকে তিনি ধামাচাপা দিয়েছেন।
\r\n
ম্যাকডুগাল
\r\n
ফ্রয়েড ব্যতীত মানব-মানসের আদি রূপ নিয়ে অপর তিনজন মনস্তত্ত্ববিদও গভীরভাবে আলোচনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে ম্যাকডুগাল, এ্যাডলার ও জুঙের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। ম্যাকডুগাল যুদ্ধস্পৃহা বা Pugnacity-কেই মানব-মানসের আদি প্রবৃত্তি বলে ধারণা করেছেন। সাধারণত দেখা যায় শিশুদের মধ্যে অযথা একে অপরকে পীড়ন করার প্রবৃত্তি প্রকাশ পায়। সুযোগ ও সুবিধা পেলেই শিশুরা একে অপরকে পীড়ন করতে চায়। যদি মনে করা হয়, অদূর ভবিষ্যতে সে আক্রান্ত হয়ে তার সঙ্গীর দ্বারা ভীষণভাবে নির্যাতিত হবে, এ আশঙ্কার দ্বারা প্রণোদিত হয়েই শিশুরা এভাবে সঙ্গী-সাথীদের নানাভাবে পীড়ন করে, তা’হলে অবশ্য এ পীড়নের একটা সদুউত্তর পাওয়া যেতো। তবে যারা অত্যন্ত দুর্বল,যাদের দ্বারা কোন সময়েই কোন অত্যাচারের আশঙ্কা নেই, এরূপ ছেলেমেয়ের আক্রমণ করার কি কারণ থাকতে পারে? কাজেই এরূপ আক্রমণ করার প্রবৃত্তিকে ম্যাকডুগাল মানুষের আদি সহজাতপ্রবৃত্তি বলেছেন। তাঁর ধারণা মানুষ আজীবন এ প্রবৃত্তি দ্বারাই প্ররোচিত হয়ে নানাবিধ কাজকর্ম সম্পাদন করে। সাধারণত আমরা জীবনের নানা ক্ষেত্রে যে প্রতিযোগিতার দৃষ্টান্ত দেখতে পাই, ম্যাকডুগালের ধারণা- তা’ সেই আদি যুদ্ধস্পৃহারই এক পরিবর্তিত রূপ। বাল্যে,কৈশোরে ও যৌবনে এ প্রতিযোগিতার প্রবৃত্তি ভীষণভাবে দেখা দেয়। বিদ্যানিকেতন, খেলার মাঠ, ঘোড়া দৌড়, বল খেলা প্রভৃতিতে তা উৎকটভাবে দেখা দেয়। এগুলোকে আদিম হিংস্র প্রকৃতিরই রুপান্তর বলে গ্রহণ করতে হয়।
\r\n
এ কথা অবশ্য অস্বীকার করার উপায় নেই যে, মানবজীবনে হিংসা-বিদ্বেষ রয়েছে। হয়ত বা সেই হিংসা-বিদ্বেষই ভদ্রভাবে প্রতিযোগিতার রূপ নেয়, তবে মানুষের জীবনে প্রেম, মৈত্রী ও ভালবাসার যে ক্রিয়াশীলতা রয়েছে, তাকে কিভাবে অস্বীকার করা যায়? কেবল অপরকে পীড়ন করেই কি মানুষ সুখ পায়? অপরকে সাহায্য ও সহায়তা করার প্রবৃত্তিও মানবজীবনে রয়েছে। তাকে অস্বীকার করলে সত্যের একটা দিককে অস্বীকার করা হয়। কাজেই ম্যাকডুগালের এ মতবাদের মধ্যে আংশিক সত্য রয়েছে বলে স্বীকার করা যায়। মানবজীবনে অপরাপর অনেকগুলো দিককে তিনি প্রকারান্তরে অস্বীকার করেছেন।
\r\n
\r\n
এ্যাডলার
\r\n
মানবজীবনের আদি প্রবৃত্তি সম্বন্ধে অতি আধুনিককালে এ্যাডলারের মতবাদ অত্যন্ত প্রাধান্য লাভ করেছে। কাজেই সে সম্বন্ধেও আলোচনা করা প্রয়োজন। এ্যাডলারের মতে মানবজীবনে শক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষাই আদি বৃত্তি। তাঁর মতবাদ অনুসারে এ আকাঙ্খার উৎপত্তির মূলে রয়েছে নেতিবাচক মনোবৃত্তি। মানুষ মনে করে যে কোন সময় সে বিরুদ্ধ পক্ষীয় শক্তি দ্বারা পর্যুদস্ত হতে পারে। এজন্য সে পূর্বাহ্নেই শক্তি সঞ্চয় করে আত্মরক্ষা করতে চায়।
\r\n
এ মতবাদের মধ্যেও যে আংশিক সত্য রয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। হয়ত এ জন্যই ছেলেবেলায় মানুষের যে যুদ্ধ-স্পৃহার মনোবৃত্তি দেখা দেয়, তাকে আত্মরক্ষারই এক সতর্ক সংস্করণ বলা যায়। তবে এ ব্যাখ্যার মধ্যেও ত্রুটি রয়েছে। কারণ অতি শৈশবেই মানুষের মনে যেমন অপর কোনও ব্যক্তির দ্বারা পর্যুদস্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়, তেমনি অপর মানুষ কতৃক সাহায্য লাভের আশ্বাসও তার মানসে বর্তমান থাকে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাদের সাময়িক সাহায্যের জন্য যার তার কাছে আবদার করে। হয়ত দু’ থেকে তিন চারজন একসঙ্গে একটা পথে রওয়ানা দিয়েছে- পথিমধ্যে একটা কুকুর যদি তাদের তাড়া করে, তখন তারা দৌড়ে যেয়ে সে কোন লোকের কাছে অথবা যে কোন বাড়িতে আশ্রয় নেয়। এক্ষেত্রে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে- মানুষ সব সময়ই অপরের সাহায্য ও সহায়তার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে।
\r\n
জুঙ
\r\n
মনোবিজ্ঞানবিদ জুঙের অভিমত এই যে, মানব-মনকে তিন স্তরে বিভক্ত করা যেতে পারে- ১.চৈতন্য, ২.ব্যাক্তিগত নির্জ্ঞান মন ও ৩. সমষ্টিগত নির্জ্ঞান মন।
\r\n
ব্যক্তিগত নির্জ্ঞান মন দ্বারা এই বুঝা যায়-কোন কালে যে সব ধারণা বা সংবেদন সজ্ঞান মনে বিরাজ করতো, কোন কারণবশত তারা অপ্রীতিকর প্রতিপন্ন হলে কার্যকরী জীবনের সুবিধার জন্য তাদের অবদমন অরা হয়। এই অবদমনের ফলে মনোজগতের নতুন গ্রুপের সৃষ্টি হয়। সেই নতুন গ্রুপ স্বপ্ন ও কল্পনা ব্যতীত স্বাভাবিক চেতনাতে দেখা দেয় না। সমষ্টিগত নির্জ্ঞান মন দ্বারা বোঝায় যে, অবদমিত চিন্তাগুলো ব্যষ্টির চেতনালব্ধ নয়; বরং সেগুলো জাতীয় অভিজ্ঞতার ফল এবং তাদের একেবারে অতি পূর্ববরতী পূর্বপুরুষদের অভিজ্ঞতার ফল বলা যায়। জ্ঞানের এসব স্তর সব সময়েই মানব-মনে কার্যকরী এবং তারা সব সময়ই আমাদের কাজকর্মের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। তবু নির্জ্ঞান মন গৌণভাবে আমাদের জীবনে কার্যকরী।
\r\n
জুঙের মত এই যে, আমাদের মন চার পন্থায় কাজ করে। ১.মনন ২.অনুভূতি ৩.সংবেদন ৪.বোধি। তাঁর ধারণা, মনন, অনুভূতি যুদ্ধ দ্বারা চালিত এবং তাদের প্রকাশ হয় অবরোহ পদ্ধতিতে। অপরদিকে সংবেদন ও বোধির জ্ঞানের তিন স্তরেই সম্বন্ধ রয়েছে। জুঙ বোধির দু’টা সংজ্ঞা দিয়েছেনঃ
\r\n
১.সেই মানসিক ক্রিয়াকেই বোধি বলা যায়, যার ফলে প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে নির্জ্ঞান মনের স্তরে প্রেরণ করা হয়। এ ক্ষেত্রে প্রেরণ করা নয়-প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও নির্জ্ঞান মানসের ব্যাপার। বোধি নিস্ক্রিয় ও সক্রিয় দুইই হতে পারে। নিস্ক্রিয় অবস্থায় বোধির কার্যকারিতার ফলে অমূল প্রত্যক্ষ বা কল্পনার সৃষ্টি হয়। সেক্ষেত্রে বোধি সৃষ্টিধর্মী শক্তির পরিচয় প্রদান করে। মানব মানসে বোধি প্রধান শক্তি হিসেবে কার্যকরী হলে একদিকে যেমন মরমি স্বপ্নদ্রষ্টা অথবা স্রষ্টার সৃষ্টি করতে পারে,অপরদিকে তেমনি কল্পনাপ্রবণ পাগলের অথবা শিল্পীর জন্মদাতা হতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে বাস্তব জীবনে অনন্ত বিরামহীন অন্বেষণকারীও জন্ম দিতে পারে। এ শ্রেণীর বিশেষত্ব এই যে, সম্ভাবনাগুলো বাস্তবায়িত হলেই এগুলোর প্রতি এই শ্রেণীর লোকের আর কোন মনযোগ থাকে না। জুঙের ধারণার অনুসরণ করলে আমাদের স্বীকার করতে হয় মানব মনের মধ্যেই এমন একটা শক্তি রয়েছে, যার কার্যকারিতার ফলে আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ঠিক পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা লাভ না করে অন্য উপায়েও লাভ করা যায়। সে জ্ঞান ঠিক সজ্ঞান মনের ব্যাপার নয়। তার মধ্যে রয়েছে নির্জ্ঞান মনের কাজ। অথচ স্বজ্ঞান মনে যে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সৃষ্টি হয়, তার মধ্যে জ্ঞানের শক্তি রয়েছে প্রচুর। বোধি সে প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে নির্জ্ঞান মনের স্তরে প্রেরণ করে। এক্ষেত্রে এ প্রেরণ করা সজ্ঞান মনের ব্যাপার নয়। নির্জ্ঞান মন দ্বারাই তার কাজ সমাধা হয়। বোধি নিস্ক্রিয় অবস্থায় আমূল প্রত্যক্ষ বা কল্পনার সৃষ্টি করে। সক্রিয় অবস্থায় বোধির প্রভাবে একদিকে যেমন পাগল, অপরদিকে তেমনি প্রতিভাশালী শিল্পীরও সৃষ্টি হতে পারে।
\r\n
জুঙের এবম্বিধ বিশ্লেষণ মানব জ্ঞানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। জুঙ মানবজীবনে ক্রিয়াশীল বিভিন্ন বৃত্তি ও প্রবৃত্তির কোন আলোচনা করেননি। কাজেই তাঁর এ আলোচনাকে একদেশদর্শী বলেই অভিহিত করা যায়।তবে তাঁর এ আলোচনার একটা বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, এ পর্যন্ত বোধিলব্ধ জ্ঞান সম্পর্কে আমাদের বৈজ্ঞানিক জগতে কোন আলোচনাই হয়নি। সে জ্ঞান যেমন হটাৎ আলোর ঝলকানির মত দেখা দেয়, তেমনি হটাৎ আবার অন্ধকারের রহস্যময় লোকে আশ্রয় নেয়। আমরা প্রত্যাদেশ বা ওহীকে(revelation) সেরূপ জ্ঞান বলে এতদিন পর্যন্ত ধারণা করে এসেছি। তার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তির অনুসন্ধান করিনি। জুঙের ধারার অনুসরণ করলে দেখা যায়, প্রত্যাদেশ কোন অবৈজ্ঞানিক বা অলীক কোন জ্ঞান নয়। তাকে বিশ্লেষণ করলেও তার মধ্যে বৈজ্ঞানিক সূত্র আবিস্কার করা যায়! এ কথা আজ সর্বজনবিদিত সত্য যে, হযরত মুহম্মদ মুস্তফা (সঃ) মানব সাধারণের মুক্তির জন্য দীর্ঘকাল যেসব চিন্তা করেছিলেন, তাঁকে তাঁর নির্জ্ঞান মনের স্তরে বোধি প্রেরণ করেছিল। সে নির্জ্ঞান মনের কার্যকারিতার ফলেই তিনি প্রত্যাদেশ লাভ করেছিলেন। এ কথার পরিপোষকতায় পাওয়া যায় একটা সর্বজনস্বীকৃত সত্য। তৎকালীন নানাবিধ সমস্যা সম্বন্ধে তাঁকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে হযরত(সঃ) সরাসরি কোন উত্তর দিতেন না। প্রত্যাদেশ বা ওহী নাযিল হলেই তাদের সমাধান বলে দিতেন। এতে একথাই প্রমাণিত হয়, তার মানসে সে প্রশ্নের উত্তরগুলোর সমাধানের ক্রিয়াশীলতা থাকত বর্তমান। বোধি সে প্রশ্নগুলো তার নির্জ্ঞান মানসে ঠেলে দিতো এবং সেখানে এ প্রশ্নগুলোর উত্তর তৈরি হলেই তিনি সেগুলো সম্বন্ধে তাঁর মতামত পরিস্কার ভাষায় বলে দিতেন।
\r\n
এতে অবশ্য বোধির মানস সংক্রান্ত কার্যকারিতার ব্যাখ্যা হচ্ছে। তার মধ্যে যে বিষয়গত দিক (objective side) রয়েছে তা’ স্বীকার করা হচ্ছে। বোধির কার্যকারিতার ফলে বিষয়গত দিকে স্বয়ং কোন ফেরেশতার হাযির হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়।
\r\n\r\n
তৃতীয় পরিচ্ছেদ
\r\n
রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষা
\r\n
\r\n
রাষ্ট্রবিজ্ঞানে মানব জীবনে সম্বন্ধে আমরা নানাবিধ ধারণার সঙ্গে পরিচিত হই। মানুষকে কোথাও ভাবা হয়েছে সম্পূর্ণ একক ও নিঃসঙ্গ হিসেবে, আবার কোথাও ভাবা হয়েছে শ্রেণীবদ্ধ জীব হিসেবে। এ ধারণার সত্যা-সত্যের ওপরই বিভিন্ন মতবাদের সত্যাসত্য নির্ভরশীল।
\r\n
অন্যদিকে দেখা যায়, বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদেরও কারণ রয়েছে, কোন্ বিশেষ পরিস্থিতিতে কোন্ বিশেষ মতবাদের উৎপত্তি-তার কারণ নির্ণয় করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়-এক সময় পোপের শাসনে সমস্ত ইউরোপ অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে, পোপের অধীনে বিভিন্ন দেশে মস্ত মস্ত জমিদারি গড়ে ওঠে, সে সব জমিদারির মালিক সামন্ত সর্দারের দেশের বুকে চালায় অকথ্য নির্যাতন। তাদের অধীন গরিব চাষিরা ভূমিদাসে৪৫ হয় পরিণত। এসব ভূমিদাস সামন্ত সর্দারের কাঠের কাঠুরে ও পানি সরবরাহকারী রূপে তাদের হাতের পুতুল হয়েই বেঁচে থাকে। এসব সামন্ত সর্দার দেশের উৎপাদন শক্তি তাদের হাতের মুঠোয় রেখে উৎপাদিত দ্রব্য যথেচ্ছা ভোগ করতে থাকে। তারা তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত উদ্ধৃত্ত অন্য দেশে বিক্রি করার জন্য অপর একদল লোককে দিতো। ক্রমে সেই বণিকগোষ্ঠী দেখতে পেলো দেশের সমস্ত চাহিদা পূরণের জন্য উৎপাদন করে ভূমিদাসেরা। সামন্ত সর্দারের বসে বসে ভোগ করে অথচ উৎপাদিত দ্রব্যের ওপর তাদেরই মালিকানার দওলতে তারা বণিকদের উদ্ধৃত্তকে যথেচ্ছা চালান দেওয়ার সুবিধা দেয় না। কাজেই এ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অবিচারমূলক। তার পরিবর্তে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়ারূপে দেখা দেয় নতুন দার্শনিক মতবাদ। তাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় উদারনৈতিক মতবাদ।
\r\n
এ মতবাদের সূচনা হয় ইতালীর রেনেসাঁয়। জার্মানির রিফরমেশনে হয় তার বিকাশ এবং ফরাসি রাষ্ট্রবিপ্লবে তা পূর্ণ পরিণতি লাভ করে। ইতালীর রাজনৈতিক চিন্তানায়ক ম্যাকিয়াভেলিই৪৬ সর্বপ্রথম দেশের শাসন ব্যবস্থায় রাজকীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। পোপের আধিপত্য বিনাশের জন্য তার সূচনা হলেও পরবর্তীকালে ধর্মের রাজ্যে ব্যক্তি স্বাধীনতার নীতি গৃহীত হয়। আল্লাহ্ ও মানুষের অন্তর্বর্তী অন্য কোন ব্যক্তি বা শ্রেনীর আধিপত্য অস্বীকার করে মার্টিন লুথার তাঁর প্রটেসট্যান্ট ধর্ম প্রচার করেন এবং ফরাসি রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় রবোসপিয়ারের জীবনে সাম্য,মৈত্রী ও স্বাধীনতা শ্লোগান হয়ে পড়ে।
\r\n
এ মতবাদের নঞর্থক দিকের বিচার করলে এক সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিদ্রোহ বলা যেতে পারে; রাজকীয় শাসন ও তার উত্তরাধিকারকে অস্বীকার না করলেও তাকে সীমাবদ্ধ করার দিকে উদারনৈতিক মতবাদের ঝোঁক ছিল। তার সদর্থক দিকের আলোচনা করলে বোঝা যায়-মানুষের অবাধ স্বাধীনতার স্বপ্নই ছিল উদারনৈতিক মতবাদের সর্বপ্রথম কাম্য। ব্যবসা-বাণিজ্যে রাজার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকা এ মতবাদ বরদাশ্ত করেনি। এর বক্তব্য হল, মানুষকে স্বাধীনতা দিতে হবে। স্বাধীনতা পেলে সে যেমন উৎপাদন করতে পারবে তেমনি উৎপাদিত দ্রব্যেরও বিলি-ব্যবস্থা করতে পারে-মানুষের মাঝে কোন বিশেষ প্রাণীর আধিপত্য স্বীকার করে নিলে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থায় নানা অসুবিধার সৃষ্টি হয়।
\r\n
এভাবে, সমসাময়িক সমাজ ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়ারূপেই দেখা দেয় উদারনৈতিক মতবাদ। সেই উদারনৈতিক মতবাদই কালে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ এবং সর্বশেষে ধনতন্ত্রে পরিণত হয়। ধনতন্রের পূর্ণ প্রতিষ্ঠাকালে তার নানাবিধ ত্রুটির ফলে সমাজজীবনে যে অসাম্যের সৃষ্টি হয় তারই নিরসনকল্পে কার্ল মার্কস ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রচার করেন তাঁর বস্তুতান্ত্রিক সমাজবাদ। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার অসঙ্গতি তাঁর চোখে ভয়াবহ রূপ নিয়ে দেখা দেয়। তাই তাকে উৎখাত করার মানসে তিনি ইতিহাসের অভিনব ব্যাখ্যা করেন।
\r\n
কাজেই, এভাবে উৎপত্তির কারণ বিশ্লেষণ করে রাজনৈতিক মতবাদের মূল্য নিরূপণ করা যায়। তবে এতে আপত্তির কারণ আছে। প্রথমত দেখতে হবে, যে কোন পরিবেশের চাপেই তার জন্ম হোক না কেন, যে কোন মতবাদের সত্যাসত্য নির্ভর করে তার অন্তর্নিহিত যুক্তিবত্তার উপর আমাদের বোঝায় সুবিধার জন্য কোন মতবাদের উৎপত্তির কারণ নির্ণয় করতে পারি, তবে এতে মতবাদের ঠিক মূল্য নিরূপণ হয় না। সে মতবাদ গ্রহণের ফলে মানবজীবনের সুষ্ঠু বিকাশ হয় কিনা তা আমাদের ভেবে দেখা দরকার।
\r\n
দ্বিতীয়ত একই পরিবেশে একই অপব্যবস্থায় উত্যক্ত হয়েও দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন মতবাদ গড়ে উঠতে পারে। পুজিঁবাদী সমাজের পাপাচারে উত্যক্ত হয়ে মার্কস প্রচার করেন বস্তুতান্ত্রিক সমাজবাদ এবং এ পুঁজিবাদের অত্যাচার আরও চরমসীমায় পৌঁছায় পর তার নানাবিধ অকল্যাণে অতিষ্ঠ হয়ে টলষ্টয় প্রচার করেন তাঁর খ্রিষ্টীয় সমাজবাদ। কাজেই পরিবেশ দ্বারা মতবাদের মূল্য নির্ণয় নিতান্তই অবিচারমূলক কাজ। তাই রাজনৈতিক মতবাদের মূল্য নির্ণয়ে আমরা তার গুণাগুণের বিচার করবো। এ পর্যন্ত যত সব রাজনৈতিক মতবাদের উৎপত্তি হয়েছে তাদের মধ্যে সমাজজীবনে আদি সংখ্যা হিসেবে কোথাও ব্যক্তিকে, আবার কোথাও সমষ্টিকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। রাজনৈতিক মতবাদগুলোকে তাই অনায়াসেই দু’ভাগ করা যায়। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ
\r\n
উদারনৈতিক মতবাদের ভিত্তিস্বরূপ যে জীবন-দর্শন গড়ে উঠেছে তাকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক বলার অর্থ এই যে, জগতের অতবার মানব-সমাজের আদি উপাদানরূপে এখানে ব্যক্তির সত্তাকেই স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। মতের বিভিন্নতা সত্ত্বেও লক৪৭ থেকে শুরু করে এ্যাডাম স্মিথ৪৮ পর্যন্ত যে চিন্তাধারার ইতিহাস পাওয়া যায় তার সারসংক্ষেপে এই বলা যায়ঃ মানুষের চিন্তারাজ্যে চলেছে আণবিক মনস্তত্ত্বের খেলা। রাষ্ট্রীয় জীবনে চলছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বা প্রাধান্যের চেষ্টা। মানুষ একক হয়েই জন্মগ্রহন করে; সেই একক মানুষের সঙ্গে বিভিন্ন মানুষের সংস্পর্শ থেকে গড়ে ওঠে তার সমাজ, তার জাতি, তার রাষ্ট্র। মানুষের আদিসত্তায় রয়েছে তার অহংবোধ৪৯ ও স্বার্থপরতা।৫০ এই আদি মানবের চলাফেরায়,ব্যবসা-বাণিজ্য, চিন্তাধারায় অবাধ স্বাধীনতা দিতে হবে-তার কাজ-কর্মে যাতে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না হয় তার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়েই রাষ্ট্র গড়ে উঠবে।
\r\n
প্রশ্ন উঠেঃ মানুষকে যদি এভাবে স্বাধীনতা দেওয়া যায় তা’হলে তো তাদের মধ্যে সবসময়ই মারামারি-কাটাকাটি লেগেই থাকবে। প্রত্যেকে যদি তার সার্থসিদ্ধির জন্যই চেষ্টা করে তাহলে তো একের স্বার্থের সঙ্গে অপরের স্বার্থের সংঘর্ষের ফলে সবসময়ই মানবজীবনে দ্বন্দ্ব-কোলাহলের সৃষ্টি হবে-মানুষ শান্তিতে দুদিন তিষ্ঠাতে পারবে না। তার উত্তরে লক ধারণা করে নিয়েছেন, প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ পশুর মত পরস্পরের সঙ্গে শত্রুতায় লিপ্ত নয়, সেখানেও মানুষের মাঝে শান্তি বিরাজ করছে এবং মানুষ বিচারবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়। প্রকৃতির রাজ্যে অরাজকতার কোন স্থান নেই। প্রকৃতির আইনের প্রভাবে মানুষের স্বাভাবিক অধিকার,স্বাধীনতা ও সম্পত্তি ভোগ করার সুযোগ থাকে। তা সত্ত্বেও প্রকৃতির রাজ্যে আইনকে ব্যাখ্যা করার জন্য বা তার প্রয়োগের জন্য কোন প্রতিষ্ঠান নেই, যদিও সেই আইন-কানুন সকল মানুষের মনেই কার্যকরী। তবুও বুদ্ধির তারতম্যের দরুন এবং স্বার্থের বিভিন্নতার ফলে নানাবিধ দ্বন্দ্বের উৎপত্তি হয়। এর জন্যই সমাজ গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হয়। লকের মতে প্রত্যেক ব্যষ্টিই তার জীবন, স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য অপরের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়; তার ফলেই সম্প্রদায়ও গড়ে ওঠে। এ চুক্তির মর্ম মতে ব্যষ্টিকে প্রাকৃতিক-আইন কার্যে পরিণত করার অধিকার ত্যাগ করতে হয় এবং অপরাধের শাস্তি দান করার অধিকার থেকেও বঞ্চিত হতে হয়। ব্যষ্টিকে অবশ্য তার সমস্ত অধিকার ত্যাগ করতে হয় না, কতকগুলো অধিকার সম্প্রদায়ের হাতে তুলে দিতে হয়। তাও আবার কোন বিশেষ ব্যক্তি বা কোন দলের হাতে সে সেই অধিকারগুলো অর্পণ করে না, গোটা সম্প্রদায়ের হাতে সেগুলো ন্যস্ত করে সে নিশ্চিত হয়।
\r\n
লক মানুষকে বুদ্ধিপ্রধান জীবরূপেই ধারণা করেছেন। প্রকৃতির বুকে এই বুদ্ধির দওলতেই মানুষ তার অধিকার বজায় রেখে অন্যের সঙ্গে বিরোধ না করেও চলতে পারে; তবে তাতে নানা অসুবিধার সৃষ্টি হয় বলেই মানুষ তার অধিকার সংকুচিত করে তার নিজের মঙ্গলের জন্যই সম্প্রদায়ের হাতে তার প্রাকৃতিক অধিকারগুলো তুলে দেয়।
\r\n
\r\n
সামাজিক চুক্তিবাদ
\r\n
এই সব মতবাদের বিরুদ্ধে ফরাসি দার্শনিক ‘রুশো’ এক নতুন মতের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বড় আক্ষেপ করেই বলেছেন, মানুষ স্বাধীন হয়েই জন্মগ্রহণ করে কিন্তু সে সর্বদাই শিকলাবদ্ধ থাকে। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের ওপর কোন আদেশ-নিষেধ, আইন-কানুন চাপানো যায় না। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে নানা নীতি, নানা আইন মেনে চলতে এবং তার ফলে তার জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। ‘রুশো’ মানুষকে আবার তার স্বাভাবিক ধর্মে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আহব্বান করেছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল, প্রকৃতির কোলে স্বাভাবিক পরিবেশে মানুষের প্রক্ষোভে পূর্ণ বিকাশ লাভ করতে পারে, অপ্রাকৃত মানব-সৃষ্ট পরিবেশ তা’ হওয়া সম্ভব নয়। প্রকৃতিতে পশু, পাখি, কারো কোন দুঃখ-দৈন্য নেই। তারা অবাধে বিহার করে, তাদের অভাবেরও কোন তাড়না নেই-কারণ অভাবে উৎপত্তি হলেই তার বুদ্ধির নিবৃত্তির উপায় তার পক্ষে সহজলভ্য। মানুষ তার বুদ্ধির প্যাঁচে গড়ে তুলছে তার সমাজ, তার রাষ্ট্র, তার নানাবিধ আচার-অনুষ্ঠান। এতে মাববজীবনের পরিপূর্ণ স্ফূর্তি লাভ হয় না বলেই জীবনে যতো দুঃখের হয় উৎপত্তি। তার ধারণা ছিল, প্রকৃতি থেকে বিকাশের ধারায় কোন এককালে মানুষকে তার জন্মগত স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে হয় তার আত্মরক্ষার জন্য; অন্য মানুষের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সে গড়ে তোলে তার গোত্র, সম্প্রদায় ও রাষ্ট্র। রুশোর জীবনে তাই সর্বপ্রধান সমস্যা ছিল, অন্যান্য লোকের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে রাষ্ট্র গঠন করেও ব্যষ্টি কিভাবে তার স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা বজায় রাখতে পারে তার উপায় উদ্ভাবন।
\r\n
তাঁর এ মতবাদকে বলা হয় সামাজিক চুক্তিবাদ৫১। এ চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে ব্যষ্টি তার সমস্ত অধিকার সম্প্রদায়ের হাতে ন্যস্ত করে। সকলকে একইভাবে সম্প্রদায়ের হাতে তাদের অধিকার অর্পণ করতে হয় বলে অন্যের পক্ষে পীড়াদায়ক কোন শর্ত আরোপিত হওয়ার সুযোগ পায় না। সামাজিক চুক্তিমতে সম্প্রদায়ই সার্বভৌমত্ব৫২ লাভ করে। কারণ ব্যষ্টি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই তার সমস্ত অধিকার সম্প্রদায়ের হাতে তুলে দেয়। তবুও এই সার্বভৌম সম্প্রদায় ব্যষ্টির পক্ষে ক্ষতিকর কোন কাজ করতে পারে না। কেননা ব্যষ্টির স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অধিকার ত্যাগের ফলেই সম্প্রদায়ের হয় প্রতিষ্ঠা। রুশোর জবানীতেই তাঁর মতবাদ পরিস্কারভাবে ফুটে উঠেছে;
\r\n
আমরা প্রত্যেকেই তার শরীর ও শক্তি সর্বসাধারণের মহান ইচ্ছার অধীনে সমর্পণ করি এবং আমাদের সংঘবদ্ধ অবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমাদের সমগ্র সম্প্রদায়ের অবিভাজ্য অংশরূপে গ্রহণ করি। এই সমাবেশের ফলে একটা নৈতিক ও সংঘবদ্ধ সংগঠনের সৃষ্টি হয়-যার নিস্ক্রিয় অবস্থার নাম রাষ্ট্র৫৩ সক্রিয় অবস্থার নাম সার্বভৌমত্ব এবং অনুরুপ কোন সংগঠনের সম্বন্ধে যাকে বলা হয় শক্তি।৫৪* (Rousseau-Social Contract.)
\r\n
ব্যষ্টি সম্বন্ধে এত উচ্চ ধারণা পোষণ করা সত্ত্বেও রুশো ব্যক্তিগত সম্পত্তি সংরক্ষণে কোন প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেননি। তিনি পরিস্কার ভাষায় বলেছেনঃ
\r\n
রাষ্ট্রে সঙ্গে নাগরিকদের সম্বন্ধের ফলে রাষ্ট্রই তার নাগরিকদের সম্পত্তির একমাত্র মালিক।* (Rousseau-Social Contract.)
\r\n
সূক্ষ্ম বিচারে প্রবৃত্তি হলে দেখা যায়, রুশোর ভাষায় অনেক পরস্পরবিরোধী মতামত সন্নিবেশিত রয়েছে। ব্যষ্টি যদি সম্পুর্ণ স্বাধীন হয় তাহলে সম্প্রদায় বা রাষ্ট্রে হাতে তার সম্পূর্ণ অধিকার তখনই ত্যাগ করতে পারে যদি তার ব্যক্তিগত অধিকার কোন অংশেই ক্ষুণ্ন না হয়। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অধিকার তো ক্ষুণ্ন হয়েছেই, অধিকন্তু তাকে সাধারণের ইচ্ছার ওপর তার সমস্ত অধিকার ছেড়ে দিতে হয়েছে।
\r\n
মানুষের মনে যদি সর্বসাধারণের হিত করার মত কোন পরার্থপর৫৫ সৎ প্রবৃত্তি না থাকে, তাহলে তার অহংবোধ৫৬ কিছুতেই তাকে এভাবে আত্মসমর্পণ করতে দেবে না। কাজেই ব্যষ্টির স্বাতন্ত্র্য৫৭ বা তার অহংবোধ স্বীকার করে রাষ্ট্র বা তার সার্বভৌমত্তে পৌঁছা রুশোর পক্ষে যুক্তিসম্মত হয়নি।
\r\n
প্রকৃতপক্ষে রুশো তাঁর মতবাদের সমর্থনে কোন মননশীলতার অবতারণা করেননি। মরিমীবাদীদের মত এক বিশেষ ভাবাবেশ উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি তাঁর দার্শনিক মতবাদ গড়ে তুলেছেন। বৈজ্ঞানিক যুক্তির সাহায্যে নয়, ভাবের আবেশে ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে মানব মনে কার্যকর করে তোলাই ছিল রুশোর জীবনের সাধনা। তাঁর জোরালো ভাষার আবেদনে ফরাসি রাষ্ট্রবিপ্লব হয়ত সহজে ঘটতে পেরেছিল কারণ তার পশ্চাতে ছিল দীর্ঘকালের নির্যাতিত মানবতার মুক্তির প্রয়াস। তবুও যুক্তির কষ্টিরপাথরে বিচার করলে তাতে নানা ত্রুটি সহজেই লক্ষ্য করা যায়।
\r\n
উদারনৈতিক মতবাদ বা সামাজিক চুক্তিবাদের মধ্যে ব্যষ্টি সম্বন্ধে ধারণার বিশেষ কোন প্রভেদ নেই। উভয়ক্ষেত্রেই ব্যষ্টিকে কল্পনা করা হয়েছে একক ও সম্বন্ধহীনভাবে। পূর্বেই বলা হয়েছে, মনোবিজ্ঞানের জগতে যেমন আণবিক মনস্তত্ত্বের সূত্রপাত তেমনি মানুষকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন,স্বার্থান্বেষী জীবরূপে গ্রহণ করে এই নব্য ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ দুনিয়ার ইতিহাসে এক অভিনব চিন্তাধারার প্রবর্তন করে।
\r\n
উদারনৈতিক মতবাদের আলোচনায় আমার দেখেছি কোনও বিশেষ কালে এক শ্রেণীর আধিপত্য বিস্তারের ফলে দেশের উদ্ধৃত্তের হয় অপব্যবহার। সেই বিশেষ শ্রেণী তার নিজের স্বার্থে সে উদ্ধৃত্তকে ব্যবহার করে। তারই ফলে শ্রেণী-সংঘর্ষ হয়ে ওঠে অনিবার্য। তাই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সমতা সাধন করার জন্য ব্যক্তিকে দিতে হয় অবাধ স্বাধীনতা। সে অবাধ স্বাধীনতার ফলে কোন বিশেষ শ্রেণী আর শোষণের সুযোগ পায় না। তার জন্য মানুষের আসল প্রকৃতির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে এক নতুন দর্শনের হয় সৃষ্টি। সে দর্শনের মোদ্দা ভাবার্থ এই ঃ মানুষ স্বভাবতই স্বার্থপর। তার উৎপাদনের প্রাথমিক কারণ,অভাবের নিরসন হলেও উদ্ধৃত্ত থেকে সে স্বভাবতই মুনাফা করতে চায়। সে সুযোগে বাধা উপস্থিত হলে মানুষের সঙ্গে মানুষের সংঘর্ষের হয়ে পড়ে অনিবার্য। সেই সংঘর্ষকে এড়াতে হলে মানুষের স্বাধীনতার কোন সীমারেখা টেনে নেয়া সঙ্গত নয়, তাকে দিতে হয় নিজের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের অধিকার। তা’ পেলেই সে তার অভাব নিরসনের জন্য যেমন করবে পর্যাপ্ত উৎপাদন-তেমনি সে উদ্ধৃত্তকেও সে তার নিজের সুবিধার জন্য ব্যবহার করবে। এই দার্শনিক মতবাদের নীতি হল ব্যক্তিকে একা থাকতে দাও৫৮।
\r\n
ধনতন্ত্র
\r\n
উদারনৈতিক মতবাদই পরিশেষে ধনতন্ত্রে বিকৃত হয়ে পড়ে। মানুষের সঙ্গে মানুষের বিশেষ করে যে কোন দেশের পুরোহিত ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর সংঘর্ষের অবসানের জন্য উৎপাদন বণ্টন ব্যবস্থার সুসামঞ্জস্যের জন্য এ নতুন মতবাদের সৃষ্টি হলেও তার চরম অভিব্যক্তিতে নয় ধনতন্ত্রের সৃষ্টি। প্রত্যেক ব্যক্তিকে উৎপাদনের অবাধ সুবিধা দেওয়ার ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আবার শুরু হয় সংঘাত ও সংঘর্ষ-আবার শুরু হয় যুদ্ধ। এ মতবাদের কল্যাণে সর্বসাধারণ মানুষ, বিশেষ করে উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ীরা অবাধ স্বাধীনতা পেয়ে তাদের ইচ্ছামত মূলধন খাটিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যে রাতারাতি দৈত্য-দানোবের মত পা ফেলে অগ্রসর হয়। দুদিনেই দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ তারা নিজেদের কুক্ষিগত করে নেয়। তার রক্ত-রাঙা ইতিহাস পাওয়া যায় অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় জাতিগুলোর কর্মসূচিতে। পৃথিবীর নানাদেশে ব্যবসায়-বাণিজ্য উপলক্ষে ছড়িয়ে পড়ে শাসন ও শোষণ করে ইউরোপীয় জাতিগুলো দুনিয়ার বুকের রক্ত শুষে নিয়েছে।
\r\n
ধনতন্রের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি হয়। বিদেশের লোককে শোষণ করতে হলে স্বদেশের লোকের মধ্যে দলীয় মানসিকতার সৃষ্টি হওয়া দরকার। যতই ব্যষ্টির গুণগান করা হোক না কেন, একাকী কোন ব্যক্তি কোথাও শোষণ করতে পারে না- তার জন্য তার দেশের সর্বসাধারণের সম্মতি ও সহযোগিতার প্রয়োজন।
\r\n
সেইজন্য পুঁজিবাদের প্রথম সফলতার যুগে দেশের সাহিত্যিকরা জাতীয়তার জয়গান গেয়ে দেশের সর্বসাধারণকে উদ্ধুদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন-
\r\n
Rule Britania, rule the waves
\r\n
Britain never shall be slaves.
\r\n
একবারে নিছক কবি-জনোচিত উচ্ছ্বাস নয়। তার মূলে রয়েছে অন্যান্য জাতিকে শোষণ করার জন্য দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করার অভিসন্ধি। এ মনোবৃত্তি বিকশিত হলেই অন্য জাতির প্রতি স্বভাবত বৈরীভাব জন্মে। কারণ, এর মূলে রয়েছে জগৎ গ্রাস করার বাসনা। কাজেই দেখা যায়, পুঁজিবাদী মনোবৃত্তি থেকেই জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি হয় এবং জাতীয়বাদের উৎপত্তি হলেই পুঁজিবাদী মনোবৃত্তি আরও তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।
\r\n
ধনতন্র বিকাশের প্রথম পর্যায়ে দেশে বিদেশে মূলধন বিস্তারের ফলে এ মতবাদের উপাসক ধনতান্ত্রিক দেশগুলো ফেঁপে ওঠে। বিশেষত শিল্পবিপ্লবের পর ইউরোপীয় দেশগুলো উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করে। কিন্তু জোয়ারের শেষে ভাটার টানে যখন দেশ-বিদেশে মূলধন খাটানোর আর সুবিধা থাকে না, তখনই ধনতন্ত্রবাদী বুঝতে পারে তার অন্তর্নিহিত গলদ। যখন দেশের টাকা বিদেশে খাটিয়ে পরধন আত্মসাৎ করার আর কোন সুবিধা থাকে না-যখন নিজের দেশের মজদুর শ্রেণী বিদ্রোহ ঘোষণা করে- “তখন দেশের সুখ-শান্তি আর সুবিধার নামে করতে হয় পশু শক্তির প্রয়োগ”। তাই ধনতন্রের সংকোচনের যুগে তারই প্রাতিষ্ঠানিক কৌশল হিসেবে হয় ফ্যাসিবাদের উৎপত্তি।*(Harlod Lasky, Reflections on the Revolution of our times.)
\r\n
\r\n\r\n
চতুর্থ পরিচ্ছেদ
\r\n
সমষ্টিকেন্দ্রিক মতবাদ
\r\n
উদারনৈতিক মতবাদ বা তার বংশের ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ বা সামাজিক চুক্তিবাদে মানব-জীবন সম্বন্ধে ধারণার কোন বিশেষ প্রভেদ নেই। সর্বত্রই মানুষকে ভাবা হয়েছে এককরুপে। ধনতন্ত্রে সেই মানুষকে কেবল একক ভাবা হয়নি, তাকে স্বভাবতই ভাবা হয়েছে স্বার্থপররূপে। অথচ বিরাট মানব-জীবন এসব মতবাদের বিরুদ্ধে এক তীব্র প্রতিবাদের মূর্ত প্রতীক। মানব-জীবন নিয়ে আলোচনা করলেই দেখা যায় মানুষ সব সময়েই যূথচারী জীব৫৯। জীবনের আদিতেই সে অপরের সঙ্গ কামনা করে। কোন দুর্বিপাকে সে সমাজজীবনে থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে জীবন তার কাছে হয়ে পড়ে দুর্বিষহ। সে কেবল অপরের সঙ্গই কামনা করে না, অপরের মঙ্গল কামনাও সে করে। আত্মরক্ষা, আত্মপ্রতিষ্ঠা তার জীবনে প্রধান মনোবৃত্তি হলেও প্রেম, দয়া, মায়া, বাৎসল্য, পরার্থপরতা তার জীবনে বিশেষভাবেই কার্যকর। মানুষের মাঝে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ঠ্য থাকলেও তাদের মধ্যে রয়েছে এক সার্বিক ঐক্য,সে ঐক্যের সুরটি বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে ইয়াহূদীদের ধর্মে।
\r\n
\r\n
য়াহূদী ধর্ম
\r\n
য়াহূদীদের ধর্মে মানুষের বৃহত্তর সত্তা বিকাশের জন্য নানাবিধ আদেশ রয়েছে। স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতা, অহংবোধ ও পরার্থিতার দ্বন্দের ফলেই আরম্ভ হয় ব্যষ্টিজীবনে দ্বন্দ্ব। ব্যষ্টি ও সমষ্টির স্বার্থের সমতা সাধনের জন্য য়াহূদীয়া অভিনব উপায় গ্রহণ করেছিল। পরলোকগত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী রামজে ম্যাকডোনাল্ড বলেন, “ বোধ হয় অন্য কোনও জাতীয় আইন ও আচার ইসরাইলীদের মত দলীয়৬০ এবং ব্যষ্টিজীবনের সমতা সাধনের চেষ্টা করেনি। তারা ছিল অনুগৃহীত৬১ জাতি তাদের ধর্ম ব্যষ্টিকেন্দ্রিক হওয়া সত্ত্বেও জাতীয়তার ওপর প্রতিষ্ঠিত।...... (সর্বাবস্থায়ই) তারা ব্যক্তিগত অধিকার অক্ষুণ্ন রেখেছে। এ জন্যই মূসার অনুশাসনে বা তাঁর বিভিন্ন ধারায় দাসপ্রথা ও ভীতিপ্রদ দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে নানাবিধ প্রতিরোধ ব্যবস্থা বিদ্যমান। প্রত্যেক সাত বৎসর অন্তর য়াহূদীদের দাসগুলোকে মুক্তি দেওয়া হয়। বন্ধকাবদ্ধ বস্ত্রাদি প্রত্যেক দিন দিবাশেষে ফিরিয়ে দিতে হয়। প্রত্যেক সাত বৎসরের শেষে মাঠগুলো পতিত রাখতে হয়, যাতে সেগুলো সাধারণের সম্পত্তিরূপে গণ্য হতে পারে। জমিতে চাষীর অধিকার অক্ষুণ্ন রাখার জন্য ধর্মীয় ও সরকারি বিধান প্রয়োগ করা হয়”।* (Ramsay Macdonal d: Social Development p:21)
\r\n
\r\n
অনেকেই মনে করেন য়াহূদী ধর্মে এরূপ সাম্যবাদমূলক নীতি থাকলেও বাস্তব জীবনে তার রুপায়ণ হয়নি। এককালে য়াহূদীদের মত এরূপ শোষক জাতি দুনিয়ার দ্বিতীয় ছিল না। য়াহূদীদের কোন রাষ্ট্রেরও ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাই রাজনীতিতে এ মতবাদের পরীক্ষা হয়নি।** ( নবজাত ইসরাইল রাষ্ট্র কিভাবে পরিচালিত হবে, তা লক্ষণীয়।)
\r\n
তবুও মানুষের আদি প্রকৃতিতে সংঘ-চেতনার৬২ দৃষ্টান্ত হিসেবে তার মূল্য রয়েছে যথেষ্ট। হয়ত ব্যষ্টি ও সমষ্টির সংস্থান ব্যবস্থা হিসেবে তাতে কোন ফাঁক থাকার দরুনই তা বাস্তব জীবনে কার্যকরী হতে পারেনি।
\r\n
প্রাথমিক প্লেটো
\r\n
মহাপ্রাণ প্লেটোর কালজয়ী দৃষ্টির আলোয় খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে এ সত্যটি প্রতিভাত হয়েছিল। তাঁর রিপাবলিকে৬৩ তিনি মানবজাতিকে সাধারণ মানব,সৈনিক এবং অভিভাবক-এই তিন ভাগে বিভক্ত করলেও মানুষের মাঝে যে ঐক্য বর্তমান তা তাঁর কাছে ধরা পড়েছিল। তিনি ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ সাধন করে সমস্ত বিত্ত রাষ্ট্রের করায়ত্ত করতে চেয়েছিলেন।
\r\n
তাঁর ধারণা ছিল, অভিভাবকগণের ছোট ছোট বাড়ি থাকবে এবং তারা মোটা ভাতে জীবন যাপন করবে। শিবিরে যেভাবে মানুষ জীবন যাপন করে, তারা তেমনিভাবে বসবাস করবে, একত্রে আহার করবে-তাদের প্রয়োজনে অতিরিক্ত কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে না, সোনা-রুপার প্রচলন নিষিদ্ধ থাকবে। ধনী না হলেও তারা কেন সুখী হতে পারবে না? নগরের উদ্দেশ্য হবে সকল লোকের উন্নতি বিধান,কোন বিশেষ শ্রেণীর সুখসাধন নয়।
\r\n
এমনকি স্ত্রীলোক ও সন্তানগণও সাধারণ সম্পত্তি পরিগণিত হবে। প্লেটোর রিপাবলিকে যে আদর্শের অনুসরণের জন্য আদেশ করা হয়েছে তাতে মনের পরহিতব্রতের প্রতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি রাখা হয়েছে এবং তাকে বাস্তবজীবনে রুপায়িত করার সাধনা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তবুও ভাবতে হবে মানব মনের স্বাভাবিক অহংবোধ থেকে কিভাবে সে পরাথির্কতার পথে অগ্রসর হবে। প্লেটো সে পদ্ধতি বাতলে দেন নি। তাই তাঁর এই আদর্শ সুখ-রাজ্যের৬৪ সমালোচনায় বলা যায়- “এতে প্রমাণ ও খণ্ডনের কোন প্রশ্নই ওঠে না। এখানে আসল প্রশ্ন হল, এ রকম রাষ্ট্র পছন্দ হয় কিনা। যদি কারো পছন্দ হয়, তা হলে ভাল-যদি না হয়, তা হলে তা খারাপ। যদি অনেক লোকের তা পছন্দ হয় এবং অনেকের তা না হয়-তা হলে যুক্তি নয়, প্রকাশ্যে বা লুক্কায়িত শক্তির জোরেই হবে তার প্রতিষ্ঠা।* (Bertrand Russell: History of Western Philosophical Thoughts.)
\r\n
এ রাষ্ট্রে ব্যক্তি-স্বাধীনতার কোন অর্থ নেই। কারণ এ রাষ্ট্র জনসাধারণের ইচ্ছা ও সম্মতির উপর গড়ে ওঠে না।
\r\n
মাজদাক
\r\n
ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্বে ইরানে মাজদাকও মানব-প্রকৃতির পরার্থিতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে এক অভিনব মতবাদ প্রচার করেছিলেন। যাতে দেশের সম্পদ সকলেই সমানভাবে ভোগ করতে পারে, তার জন্য ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ করার উদ্দেশ্যে তিনি বিবাহ প্রথা রহিত করার জন্য ঘোষণা করেছিলেন-“ যে ভাবে সকলে বায়ু ও জল উপভোগ করে, সেভাবেই স্ত্রীলোকগণকেও ভোগ করবে* (Mushir Hussain Kidwai-Pan-islamism and Bolshevism p.51)। মাজদাক কেবল যৌন-জীবনেরই যৌথানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন বলে এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাতে সংঘবদ্ধ জীবনের কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা করতে পারেননি বলে তাঁর এ মতবাদ বেশিদিন টিকে থাকেনি।
\r\n
কার্ল মার্কস
\r\n
মার্কস ছিলেন দার্শনিক হেগেলের শিষ্য। জার্মান দার্শনিক হেগেলের নিকট স্বতঃসিদ্ধ৬৫ ছিল যা কিছু সত্য তাই যুক্তিসঙ্গত, আর যা’ যুক্তিসঙ্গত, তা-ই সত্য। তাঁর স্বতঃসিদ্ধের শেষ অর্ধাংশ অনেকেই স্বীকার করতে রাজি নন।
\r\n
জগতে যা কিছু রয়েছে তাকে অবশ্য বলা চলে যুক্তিসঙ্গত। জগতে যা কিছু বিদ্যমান তার জন্য কোন জ্যামিতিক প্রমাণ দেয়া সম্ভবপর নয়। তবুও তাদের অস্তিত্বের পক্ষে উপযুক্ত কারণ থাকা দরকার। এ দুনিয়ার অস্তিত্বের পক্ষে উপযুক্ত রয়েছে এ দুনিয়ার বুকে। এ মানব সভ্যতার দর্শনবিজ্ঞানে এ নীতি স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। এ দুনিয়ায় যদি যুক্তি বা বিচারের কোন সুযোগ না থাকে, তাহলে বৈজ্ঞানিক গবেষণা এক পা’ও অগ্রসর হতে পারে না। কারণ বিজ্ঞানের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে আবিস্কার।
\r\n
তবে যা কিছু যুক্তিসজ্ঞত তাই কেমন করে সত্য হতে পারে? আমাদের তর্ক-শাস্ত্রজাত যুক্তিধারার স্রোতে এমন অনেক অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ সত্তাকে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য হই, যার কোন অস্তিত্ব বাস্তব জীবনে কল্পনা করাও আলেয়ার পেছনে ছোটার মত হাস্যকর। তবুও এ সূত্রের ভিত্তির ওপর নির্ভর করে হেগেল গড়ে তুলেছেন তাঁর দার্শনিক সৌধ।
\r\n
দুনিয়ার অস্তিত্বে আমরা বিশ্বাস করি না করি, কোন কিছুর ধারণা নিয়েই আমাদের দার্শনিক অন্বেষণ আরম্ভ করতে হয়। দর্শনের ক্ষেত্রে চরম নাস্তিবাদ৬৬ অচল। তাই বিশ্বাসসত্তাকে যদি বলা হয় অস্তিত্ব৬৭ তা’হলে সেই অস্তিত্বকে আমরা অস্তিত্বের৬৮ আলোকেই বুঝতে পারি। অস্তিত্ব ও অস্তিত্বের দ্বন্দ্বের ফলেই আমাদের মানস এর মধ্যে আশ্রয় নেয়। Becoming- এর মাঝে অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব দুই রয়েছে, অথচ তার মাঝে উভয়ের হচ্ছে সমন্বয়। হেগেল তাঁর সূচনা৬৯ কে বলেছেন অন্বয়৭০ তার প্রতিপক্ষকে ব্যত্যয় এবং তাদের সমন্বয়কে সিন্থেসিস।
\r\n
মানব-মন অন্বয়,ব্যত্যয় ও সমন্বয়ের ধারায় একেবারে পরম ব্রক্ষে এসে স্বস্তি লাভ করে। পরম ব্রক্ষে আর কোন দ্বন্দ্ব নেই।
\r\n
এ সকল চিন্তার মাধ্যমকে৭১ হেগেল গ্রহণ করেছেন অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ৭২ বলে। মার্কস হেগেলের শিষ্য হলেও এসব তাঁর কাছে অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ৭৩। অন্বয়,ব্যত্যয় ও সমন্বয়কে ইতিহাসের ব্যাখ্যায় প্রয়োগ করে মার্কস প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, সভ্যতার গতি এ দ্বন্দ্বের ফলেই সম্ভব হচ্ছে।
\r\n
“গুহামানব৭৪ কিসে পশুচারী৭৫ মানবে পরিণত হল অথবা পশুচারী যাযাবর কি কারণে কৃষিজীবীতে পরিণত হল, সে ইতিহাস আজও নিতান্ত কল্পনার স্তরেই রয়ে গেছে। কল্পনার সুবিধার জন্য বলা হয়ঃ হয়ত নব্য প্রস্তরযুগের৭৬ শেষের দিকে ঘটনাচক্রে কোন পশুচারী যাযাবর পাথর ঘষে লাঙলের মত একটা অস্ত্র তৈরি করে ফেলে। তা দিয়ে সে মাটি খুঁড়ে দেখল তাতে বীজ পড়লে দুদিনেই তর তর করে চারা গজিয়ে ওঠে। তার শুভ ফলে পথচারী সমাজের সকল লোক আর পশু চারণ নিয়ে মশগুল থাকে না, কোন বিশেষ স্থানে গেড়ে বসে মাটি খোঁড়া ও বীজ বোনায় লেগে যায়। বছরের শেষে প্রচুর খাদ্যশস্য পেয়ে তাদের উৎসাহ বেড়ে যায়। তারা আর পথে পথে পশু নিয়ে ঘোরাফেরার কল্পনাও মনে আমল দিতে চায় না। স্থায়ীভাবে বাস করে তাতে ক্ষেতের কাজ করে তারা জীবিকার সংস্থানে অগ্রসর হয়। তাদের এ প্রণালীর সুখ-সুবিধায় মুগ্ধ হয়ে তাদের জ্ঞাতি গোষ্ঠীরা আবার পশুচারণ ত্যাগ করে তাদের সঙ্গে এসে যোগ দেয়। অথবা তাদের বিরুদ্ধাচরণ করে তাদের ফলানো ফসল লুট করে নিতে চায়। ফলে যুদ্ধ বাধে দুই দলে। বিজেতা ও বিজিত-দুই দলেরই জীবনধারা হয় পরিবর্তিত। একদল এই মিত্র-সমাজের মাঝে পশুচারণের ভার নেয়, অপর দল হাল চলনা করে ফসল ফলায়। এ দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই অগ্রসর হয় মানবসমাজ। সে দ্বন্দ্বের যেমন দেখা দিতে পারে একই সমাজের বিভিন্ন মানুষের মাঝে, তেমনি বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যেও দ্বন্দ্ব সম্ভবপর। যেমন পূর্বে উল্লিখিত একই সমাজের পশুচারী ও কৃষিজীবীদের মধ্যেও যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, সেরূপ সম্পূর্ণ ভিন্ন সমাজের দুই জাতির মধ্যেও দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে, যেমন কোন এক কৃষিজীবী সমাজে হটাৎ একদল যাযাবর পশুচারী আপতিত হয়ে তার উৎপাদন ও সমাজ-ব্যবস্থা দুটোকেই লন্ডভন্ড করে দিতে পারে তবে এ দ্বন্দ্বের ফলে পশুচারীই পরিণত হয় কৃষিজীবীতে, কৃষিজীবী আর ফিরে যায় না আদিম ব্যবস্থাতে। জীবিকার উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটলে সমাজের বাস্তব ব্যবস্থারও পরিবর্তন ঘটে। কৃষিজীবী সমাজকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে ক্ষাত্রশক্তির প্রয়োজন। নানাবিধ যন্ত্রপাতির উৎপাদন অত্যন্ত দরকার। নারী-পুরুষের মধ্যে শ্রমবিভাগ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তার জন্য দলপতি,গোষ্ঠীপতিদের মধ্যে চলে দলাদলি। পরিশেষে সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিশালী ব্যক্তিই রাজপদে অভিষিক্ত হয়। তিনি তাঁর সমাজকে বাইরের শত্রুর হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখেন। তাঁর অধীনে একদল লোক শত্রুর আক্রমণ থেকে দেশ রক্ষার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকে। তাদের আহার যোগানো হয় সমাজের পক্ষে অবশ্য-কর্তব্য। কেবল রাজাই সেই সমাজ ব্যবস্থাকে রক্ষা করতে পারেন না- প্রয়োজন হয় পুরোহিত শ্রেণীর। তাঁরা আল্লাহ্র অভিশাপ থেকে মন্ত্রবলে সমাজকে বাঁচিয়ে রাখে বলে তাদের প্রতিপত্তি সমাজ মেনে নেয়। রাজা তাঁর শাসন অক্ষুণ্ন রাখার জন্য সামন্ত সর্দারের নানা সুযোগ-সুবিধা প্রতিষ্ঠিত করেন। তার ফলে দেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় রাজতন্ত্র বা সামন্ত্রতন্ত্র। যারা সমাজে আহার যোগায় তারা ক্রমশই নিচের দিকে নেমে যায়। সামন্ত প্রভুদের কৃপার পাত্ররূপে তারা তাদের আজ্ঞাবহ হয়ে ক্রমশ দাস শ্রেণীতে পরিণত হয়।
\r\n
সামন্ত যুগে এসেও মানুষ স্থির হয়ে বসে থাকে না। অবসর সময়ে সে তার জীবনযাত্রার প্রয়োজনে নানাবিধ যন্ত্রপাতি আবিস্কার করে তাকে উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রয়োগ করে। সেই নতুন ব্যবস্থায় অল্প শ্রমে প্রচুর উৎপাদন হয়। সেই উৎপাদিত দ্রব্যগুলোকে সামন্ত অথবা পুরোহিত শ্রেণীকে আর নবীন যুগের উৎপাদনকারী নজরসালামি দিতে চায় না। তাদেরই একদল লোক উদ্ধৃত্ত দ্রব্য দেশে-বিদেশে রপ্তানি করে তা থেকে দু’পয়সা লাভ করতে চায়। ফলে সামন্ত সর্দারের সঙ্গে তাদের দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এ দ্বন্দ্বে সামন্ত সর্দারের অত্যাচারে জর্জরিত দাস শ্রেণী তথা দেশের জনসাধারণ নবোত্থিত বণিক শ্রেণীর সঙ্গে যোগ দেয়। কারণ এ বণিক শ্রেণী আর দাস শ্রেণীর উপার্জনের ওপর নির্ভরশীল নয় বলে তারা দাস শ্রেণীকে সম্পূর্ণ মুক্তি দিতে হয় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সামন্ত শ্রেণীকে পরাজিত করে জয়ের পরে আকাশের চাঁদ সূর্য সবকিছু পেড়ে দেবে বলে বণিক শ্রেণী উৎসাহিত করে। এই দ্বন্দ্বে বণিক শ্রেণীরাই জয়ী হয়। জগতে আবার হয় নতুন সমাজ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা। বণিক তার কলকারখানার মুক্তিপ্রাপ্ত দাস শ্রেণীকে খাটায়। আবার তাদের পরিশ্রমের দওলতে লাখ লাখ টাকা উপার্জন করে। যতই নতুন শক্তিশালী যন্ত্রপাতির আবিস্কার হয় ততই লাভের অংক বাড়ে। শেষে মূলধন এতো ফেঁপে যায় যে, কোন বিশেষ দেশে তাকে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না; তার জন্য প্রয়োজন হয় দেশ-দেশান্তরে আধিপত্য বিস্তারের, প্রয়োজন হয় সাম্রাজ্য গড়ে তোলার। ধর্মের নামে, অনুন্নত জাতির কল্যাণের হাস্যকর অজুহাতে এক দেশ কর্তৃক অন্য দেশের লোকের রক্তমোক্ষণ চলে পুরাদমে। এইভাবে পুঁজিবাদ দুনিয়ার বুকে জেঁকে বসে।
\r\n
মূলধন যত ফেঁপে যায় ততই মুষ্টিমেয় লোকের হাতে দেশের সম্পদ এসে জড়ো হয়। মূলধন বাড়তির সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার অপর একদল মানুষ হড় হড় করে নির্বিত্ত শ্রেণীতে পরিণত হয়। এতে আবার নতুনভাবে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। পুঁজিবাদী সমাজের পক্ষে নির্বিত্তের শ্রম অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, তাদের শ্রম ব্যতীত কলকারখানা চলতে পারে না। তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করলে তারা শ্রম করতে চায় না। একেবারে আহার যোগানো বন্ধ করলেও তারা মারা যায়। তাই তাদের রাখা হয় জীবন্মৃত অবস্থার মধ্যে। খাওয়া-পরা ও প্রজননের ব্যবস্থা করে দিয়েই মালিক তাঁর কর্তব্যের এ শেষ মনে করেন। অপরদিকে পুঁজিপতির পুঁজির সঙ্গে শ্রম যুক্ত হয়েই এ সমাজ ব্যবস্থায় উৎপাদন সম্ভব হয়। উৎপাদনের জন্য তাই দুইয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে,কিন্তু বণ্টনের বেলায় শ্রমিকের কৃতিত্ব করা হয় সম্পূর্ণ অস্বীকার। উৎপাদিত দ্রব্যে শ্রমিকের মালিকানা স্বীকৃত হয় না কিছুইতেই। তার ফলে নির্বিত্ত শ্রমিকেরা কালে সংঘবদ্ধ হয়ে মালিকের বিরুদ্ধে অভিযান চালায়,পুঁজিবাদীর বিলাস-সৌধ চূর্ণ করে সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের করে প্রতিষ্ঠা।*(মোহাম্মদ আজরফঃ ইতিহাসের ধারা)
\r\n
সামন্ততন্ত্রকে যদি বলা যায় হেগেলীয় দর্শনের Being, তাহলে ধনতন্ত্রকে বলা যায় Non-being এবং সমাজতন্ত্রকে বলা যায় Becoming। সামন্ততন্ত্রের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের ফলেই সৃষ্টি হয় নির্বিত্ত শ্রেণী। সেই নির্বিত্ত শ্রেণীর কল্যাণের জন্য সমাজতন্ত্রই একমাত্র পন্থা। তার জন্য চাই রক্ত-বিপ্লব। মার্কস ও এঙ্গেলসের সর্বশেষ বাণীঃ সর্বদেশের মজুরশ্রেণী সংঘবদ্ধ হও।** (মার্কস ও এঙ্গেলসঃ কমিউনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো।)
\r\n
সেই সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যষ্টিকে তার অধিকার৭৭ ত্যাগ করতে হবে। এখানে রাষ্ট্রই থাকবে সমস্ত কাজকর্মের নিয়ামক। প্রত্যেক তার যোগ্যতা অনুসারে কাজ করে যাবে এবং তার প্রয়োজন অনুসারে সমস্তই পাবে৭৮। বৃহত্তর মানবতাবোধে উদ্ধুদ্ধ হয়ে যখন মানুষ তার অহংবোধ বা স্বার্থপরতা সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে সকল কাজকর্মই নিজের এবং সকলের জন্য করতে শিখবে, তখন রাষ্ট্রের কোন প্রয়োজন থাকবে না, রাষ্ট্র আপ্না-আপনি মিলিয়ে যাবে। তাই মানুষকে পরার্থপর করার সাধনায় সাম্যবাদী আদর্শে রাষ্ট্রকে করতে হয় সর্বেসর্বা। প্রতিক্রিয়ার কোন সুযোগই যাতে এর মধ্যে প্রশ্রয় না পায় সেজন্যেই প্রত্যেক ব্যক্তিকে রাষ্ট্রসর্বস্ব জীবন-যাপন করার শিক্ষা দেয়া হয়। এসব শিক্ষাধারা সংস্কৃত হলে পর রাষ্ট্রের প্রয়োজন আপ্না-আপনি ফুরিয়ে যায়, মানুষের বৃহত্তর সত্তার প্রকাশের জন্য আর কোন শক্তির প্রয়োজন হয় না।
\r\n
উদারনৈতিক মতবাদের আলোচনায় আমরা দেখেছি, সভ্যতার এক বিশেষ পর্যায়ে দুনিয়ায় কোন বিশেষ শ্রেণীকে ঐশী ক্ষমতাপ্রাপ্ত বলে ধারণা করার ফলে সাধারণ মানুষের দুর্গতির সীমা থাকে না। সেইজন্যই সর্বসাধারণ মানুষের মুক্তির উদাত্ত আহ্বান নিয়ে দেখা দিল উদারনৈতিক মতবাদ৭৯ , যার মূলমন্ত্র হল ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ৮০ । তার ফলে হল ধনিক ও শ্রমিক শ্রেণীর সৃষ্টি। সমাজতন্ত্রে এই নির্বিত্ত শ্রমিক শ্রেণীই আধিপত্য লাভ করে। তা সত্ত্বেও আর কোন শ্রেণী সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে না। কারণ পুঁজি খাটিয়ে তা থেকে মানুষকে শোষণ করার আর কোন অবকাশ থাকে না। অবশ্য বৃত্তিগত শ্রেণী-বৈষম্য৮১ তাতে থাকতে পারে, কিন্তু তাতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি সংরক্ষণের কোন সুযোগ না থাকায় আর কোন দ্বন্দ্বের সুবিধা হয় না। ধনতন্ত্রী সমাজ থেকে সমাজতন্ত্রী সমাজে পৌঁছতে হলে মানুষকে একটা সন্ধিক্ষণের৮২ ভেতর দিয়ে যেতে হয়। কারণ ধনতন্ত্রের আদর্শে ও ভাবধারায় প্রতিপালিত মানস নিয়ে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভবপর নয়। এই জন্য এই সন্ধিক্ষণে রাষ্ট্রে ব্যাপার ডিরেক্টরের হাতে ছেড়ে দিতে হয়। তিনি নির্বিত্তকে সমাজতান্ত্রিক আদর্শে পরিচালিত করে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র তথা সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলেন।
\r\n
মার্কসের মতবাদে পরস্পরবিরোধী অনেক ভাবধারা সন্নিবেশিত রয়েছেঃ
\r\n
১. প্রথমত সভ্যতার গতি নির্দেশ করতে যেয়ে মার্কস যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাকে বলা হয় অর্থনৈতিক নিশ্চয়তাবাদ৮৩ । ঠিক যেভাবে পদার্থ বিজ্ঞানবিদ অণু বা পরমাণুর কার্যকরণ দ্বারা জগতের সমস্ত ক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করেন, মার্কসও তেমনি এক কার্যকারণ শৃঙ্খলা দ্বারা জগৎসভ্যতার গতির ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর এ পদ্ধতিকে Positive Science –এর ভাষায় Judgement of facts বলা যেতে পারে। পরক্ষণেই তিনি আবার Normative Judgement দিয়ে বলেছেন, জগৎ-সভ্যতার ধারাই এই এবং মানুষের কাজকর্মের নীতিও এই হওয়া উচিত।
\r\n
যদি কার্যকারণসূত্রে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাই জগৎ- সভ্যতার লক্ষ্য হয়ে থাকে, তাহলে সে ব্যবস্থা এমনি ফলে উঠবে, তার জন্য কারো কোন সাধ্য-সাধনা করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু সে সভ্যতাকে বা সেই সামাজিক ব্যবস্থাকে রুপায়িত করার জন্য আহ্বান করা হয়েছেনঃ দুনিয়ার মজদুর সব একত্র হও৮৪। যদি একত্র হওয়ার মত স্বাধীনতা মজদুর শ্রেণীর না থাকে, তবে তাদের প্রতি এ আহ্বানের কোন মূল্য আছে কি? যদি ‘স্বাধীনতা’ বলতে তিনি স্পিনোজার মত সম্মতি৮৫ মনে করতেন তাহলেও তার ব্যাখ্যার সঙ্গে স্বাধীনতার সঙ্গতি খুঁজে বের করা যেত। মার্কস কিন্তু সম্মতি অর্থে স্বাধীনতা স্বীকার করেননি। তাঁর মতে ‘স্বাধীনতা’ শব্দের অর্থ নির্বিত্ত শ্রেণীর সক্রিয় অংশগ্রহণ। অর্থনৈতিক নিশ্চয়তাবাদের সঙ্গে নির্বিত্তের সক্রিয় অংশগ্রহণের কোন সুসঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।
\r\n
২. দ্বিতীয়ত, মার্কসকে আশাবাদী নিশ্চয়ই বলতে হবে। কারণ, তিনি অনাগত সমাজ ব্যবস্থার রুপায়ণে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। তাঁর ধারণা ছিল, শ্রেণী-সংগ্রামের ভেতরে দিয়েই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। সন্ধিক্ষণে কিন্তু বারবার ব্যষ্টিচৈতন্য৮৬ বা স্বার্থপরতা আবার মাথা তুলে দাড়াঁতে পারে, এই ভয়ে তিনি নির্বিত্তের নেতৃত্বের৮৭ ব্যবস্থা রেখেছেন। এখানেও মানবচরিত্র সম্বন্ধে আশা ও নিরাশার দ্বন্দ্ব তাঁর মনে রয়েছে।
\r\n
অবশ্য শেষ পর্যন্ত তিনি আশাবাদীই রয়ে গেছেন। কারণ তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, সাম্যবাদী রাষ্ট্র গঠিত হবেই হবে। তবে বহুদিনের পুঁজিবাদী সংস্কার মন থেকে নির্মূল করতে হলে রাষ্ট্রের পক্ষে বজ্রকঠোর হস্তে স্বার্থপরতাকে দমন করতে হবে।
\r\n
তাঁর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সঙ্গে এরূপ আশাবাদ কী করে খাপ কায়? জগতের কার্যকরন ব্যবস্থায় সে আশাবাদের কোন মূল্য আছে কি? এ যাবত হয়তো মার্কস প্রদর্শিত ধারায় সভ্যতা অগ্রসর হচ্ছে, কিন্তু তাই বলে এ পথেই যে সভ্যতা ধেয়ে চলবে, কি করে বলা যায়? তাই বার্ট্রান্ড রাসেল সত্যই বলেছেন, “ মার্কস নিজেকে নাস্তিক বলে ঘোষণা করতেন, কিন্তু তিনি যে জাগতিক আশাবাদ৮৮ মনে পোষণ করতেন, তা কেবল আস্তিকের পক্ষেই শোভন”। * ( দার্শনিক শ্রেষ্ঠ স্পিনোজার ধারণা ছিল, জগতের প্রত্যেক বস্তুই Substance বা সারবস্তুর Mode বা খণ্ডিত অংশ। সেই Substance- এর অনেকগুলো গুণ(Attribute); মানুষ মাত্র তার দুটো গুণকেই জানতে পারে। কারণ মানব জীবনে সে দুটো গুণ-স্থিতি (Extension) ও মননশীলতা (Thought) বর্তমান। তাঁর এ মতবাদকে সমান্তরালবাদ (parallelism) বলা হয়। তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল, মানব জীবনের এ দুটো দিক পরস্পর বিচ্ছিন্ন এবং তাদের মধ্যে কোন সংযোগ সম্ভবপর নয়। আবার বস্তু জগতে বা ভাব জগতে যা কিছু রয়েছে, তাঁর মূল উৎস সেই সারসত্তা বা Substance. তিনি তার তাঁর দর্শনে এক জায়গায় ঠাট্টা করে বলেছেন-যদি উড্ডীয়মান তীরেরও চেতনা থাকত তা’ হলে সে মনে করত,তার উড়ে যাওয়ার মূল কারণ সে নিজেই। এ মতবাদের আস্থা স্থাপন করলে ইচ্ছশক্তির স্বাধীনতার মূল্য থাকে না। সব কিছুর মূলে সারসত্তা বর্তমান থাকলে আমাদের প্রতি কাজকর্মেও সেই সারবস্তুর কার্যকারিতা বর্তমান। ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতার মূলে এভাবে কুঠারাঘাত করেও স্পিনরাজ্য আবার অন্য অর্থে তাকে ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে স্বাধীনতার অর্থ বিশ্ব-সত্তা থেকে কিভাবে বিভিন্ন mode বেরিয়ে আসছে, তাই দেখে জ্ঞান লাভ করে ধন্য হওয়া। জ্ঞানেরও সর্বপ্রধান স্তররূপে তিনি স্বজ্ঞা বা Intuition কে স্বীকার করে নিয়েছেন। সেই স্বাধীনতার অর্থ দাঁড়ায় সম্পত্তি বা acquisance মানবজীবনের এ পর্যায়ে যে রকম জ্ঞান লাভ হয় তার ফলে সে লাভ করে প্রশান্তি (Beatitude) )।
\r\n
৩. ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর শোষণের ভয়াবহ রূপ দেখে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের প্রতি মার্কস স্বভাবতই ছিলেন বিমুখ। তাঁর ধারণা ছিল, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ থেকেই শোষণের উৎপত্তি। তাই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মূল উচ্ছেদ করবার জন্য তিনি তাকে পুঁজিবাদের মূল উৎস বলেই ধরে নিয়েছেন। বাস্তবিক পক্ষে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যবোধ অনেকস্থলেই শোষণের কারণ হয়ে দাঁড়ালেও সব ক্ষেত্রেই তা হয় না। দুনিয়ার যাঁরা মনীষী, মননধর্মী, যাঁদের গবেষণার ফলে দুনিয়ার প্রগতি হয়েছে সম্ভবপর-তাঁরা ছিলেন আত্মপ্রচারবাদী৮৯ কিন্তু স্বার্থপর ছিলেন না। মননধর্মী মানুষ মাত্রেরই স্রষ্টা৯০ হিসেবে বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে, কিন্তু তাই বলে তাঁরা স্বার্থপর নন। মার্কসের সংস্থায় এদের কোন স্থান নেই, কারণ সমাজতন্ত্রই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সর্বশেষ কথা। অন্য কোন বিশ্বসংস্থার চিন্তা করা প্রতিক্রিয়ারই ছদ্মবেশ।
\r\n
কাজেই যে শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থার প্রথম সোপানরূপে মার্কস শ্রেণী সংগ্রামের পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন,তাতে অর্থনৈতিক সংগ্রামের নিরসন হতে পারে, তবে তাতেও সমাজ জীবন অন্যভাবে সংগ্রাম দেখা দিতে পারে। মার্কসের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যাঁদের অটল বিশ্বাস,মনন রাজ্যে তাঁরাও নতুন নতুন আবিস্কারের দওলতে মার্কসের দার্শনিক মতের বিরোধিতা করতে পারেন। উদাহরণচ্ছলে বলা যায়, আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় কেউ যদি জগতের সর্বত্র সাশ্রয়ী অণুর লীলাখেলাই দেখতে পান তাহলে আদর্শ হিসেবে প্রয়োজনীয় বলে গ্রহণ করলেও মার্কসীয় নিশ্চয়তাবাদে তার বিশ্বাস অটল রইবে না। যদিও সমাজ ব্যবস্থার দৃঢ় অস্তিত্বের জন্য তিনি মার্কসবাদকেই দুনিয়ার চূড়ান্ত মতবাদ বলে ব্যবহারিক জীবনে গ্রহণ করেন, তাহলেও তাঁর ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে মননধর্মী জীবনের সংঘাত ও সংঘর্ষ হয়ে পড়বে অনিবার্য।
\r\n
৪. তখনকার দিনের প্রচলিত বৈজ্ঞানিক মতবাদের উপর ভিত্তি স্থাপন করে মার্কস তাঁর যে অর্থনৈতিক নিশ্চয়তাবাদ প্রচার করেছিলেন তার ভিত্তি ছিল জড় পদার্থের মধ্যে কার্যকারণ পরম্পরা সূত্রের অমোঘ কার্যকারিতা। আধুনিক বিজ্ঞানের আলোয় সে মতবাদের ভ্রান্তি প্রমাণিত হয়েছে। বর্তমানে জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানবিদ পরলোকগত স্যার জেম্স জিনস বলেছেন, “ সাবেকী পদার্থবিদ্যা ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতার পথে প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে বলেই মনে হয়। নতুন পদার্থবিদ্যা এ রকম কোন ঝোঁক নেই বরং হাতলের সন্ধান পেলে যে এ দরজা খোলা যায়, এই ভাবধারার উদ্রেক হয়। পুরাতন পদার্থবিদ্যায় আমরা যে জগৎ দেখেছিলাম, তাতে বাস করার পক্ষে উপযুক্ত ঘরের চেয়ে কারাগারের মতই বেশি দেখাত। নতুন পদার্থবিদ্যায় আমরা যে জগতের সন্ধান পাচ্ছি, মনে হয় তা পশুর আবাসস্থল না হয়ে মানবজাতির উপযুক্ত বাসস্থান হওয়ার যোগ্য বিবেচিত হতে পারে। এ বাসস্থানে আমাদের ইচ্ছামত ঘটনাগুলোকে গড়ে তুলতে পারার সম্ভাবনা রইবে এবং এখানে আমরা অধ্যবসায়ের দ্বারা অনেক কিছু লাভ করতে পারব”।
\r\n
৫. মার্কসের অর্থনৈতিক নিশ্চয়তাবাদের মধ্যে আসল কথা অহংবোধ ও পরার্থিতা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা। অহংবোধ ও পরার্থিতাকে সাবেক আমলের মনোবিজ্ঞান তখন পর্যন্ত দু’টো পরস্পরবিরোধী গুণ বলেই স্বীকার করেছিল। মার্কস অহংবোধকেই যত অনর্থের মূল ধারণা করেছেন। তাঁর আগেও দুনিয়ার সকল ধর্মপ্রবর্তক স্বার্থপরতাকে পরার্থিকতার চেয়ে নিকৃষ্টতর বৃত্তি বলেই স্বীকার করেছেন। তবে স্বার্থপরতার অহংবোধ হয়। অহংবোধ ও স্বার্থপরতার মধ্যে প্রভেদ রয়েছে। সে অহংবোধের একেবারে নিরসন হয় কিনা, মানুষকে সম্পূর্ণ পরার্থপর করে তোলা যায় কিনা, সে সম্বন্ধে তর্কের অবকাশ রয়েছে প্রচুর।
\r\n
মার্কসবাদ ও বস্তুবাদী সমাজতন্ত্র
\r\n
আসল কথা বল এই যে, অতি আধুনিক গোঁড়া মার্কসবাদীরা বস্তুবাদী সমাজতন্ত্রের সাথে মার্কসবাদীকে অভিন্ন মনে করেই ভুল করেন। মার্কসবাদকে কম্যুনিজমের দৃষ্টিভঙ্গি বা তার কার্যক্রমের মূলে কম্যুনিষ্ট রয়েছে সত্যিই কিন্তু মার্কসবাদ কম্যুনিজম থেকে বৃহত্তর। মার্কসবাদ কেবল কম্যুনিজম নয়, মানব সভ্যতার প্রত্যেকটি বিকাশের ধারাও মার্কসবাদের অন্তর্গত। মার্কসবাদের চূড়ান্ত সত্য বলে কিছুই নেই। মার্কসবাদের পদ্ধতির প্রয়োগেই মার্কবাদের সারসত্ত্ব। এই প্রয়োগের অনুসরণে যদি আমরা প্রবৃত্ত হই, তাহলে আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে মার্কসবাদকে উন্নত করা, বিস্তার করা ও পুনঃপরীক্ষা কেবল সঙ্গতেই হবে না-হবে অবশ্যই কর্তব্য।
\r\n
টলস্টয় বা নব্য খ্রিষ্টবাদ
\r\n
মানব-মনের অহংবোধ ও পরার্থতার সমন্বয় সাধনাই ছিল মার্কসের পরবর্তী চিন্তানায়ক মহামতি টলষ্টয়ের জীবন-সাধনা। বর্তমান সভ্যতার নানা ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে টলষ্টয় দেখতে পেয়েছিলেন এতসব অসঙ্গতির মূলে রয়েছে ব্যক্তিগত মালিকানা এবং তার পথ সুগম করার জন্য নানাবিধ কলকারখানা প্রতিষ্ঠা। আবার এসবের মূলে রয়েছে খ্রিষ্টের প্রদর্শিত পথ থেকে দূরে সরে পড়া।
\r\n
তাই, ঊনবিংশ শতাব্দীর মানব-সভ্যতার নানা ত্রুটি-বিচ্যুতিতে উত্যক্ত হয়ে তিনি আবার খ্রিষ্ট ধর্মের প্রতিষ্ঠাকল্পে ছিলেন উদ্যোগী । আত্মজিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হয়ে টলষ্টয় তাঁর পরিণতিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানাকেই সব অনর্থের মূল বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। কারণ মালিকানা থেকেই দুনিয়ার যত অমঙ্গলের রয়েছে সম্ভবনা। অপূর্ব ভাষায় তিনি ব্যক্তিগত সম্পত্তির নীতিকে আক্রমণ করেছেন- ব্যক্তিগত সম্পত্তিই বর্তমানে সব অনর্থের মূল। এ আপদের যারা অধিকারী অথবা অনধিকারী তাদের উভয়ের যন্ত্রণায় মুহ্যমান তাদের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য। রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে অথবা রাষ্ট্র ও সরকারের সর্বদাই পরস্পরের সঙ্গে এ বিত্তের জন্যই কূটনীতির চালবাজি চলে। এ বিত্তের জন্যই তাদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ জ্বলে ওঠে। কখনও বা তা আফ্রিকার মাটির জন্য, কখনও বা চীন বা বলকানের বিশাল ভূখণ্ডের জন্য তার সূচনা হয়। ব্যাংকার, ব্যবসায়ী,উৎপাদনকারী, জমিদার সকলেই বিত্তের জন্য পরিশ্রম করে-বিত্তের জন্যই ফন্দি এঁটে নিজেদের বিপন্ন করে, অপরকে যন্ত্রণা দেয়। সরকারী কর্মচারগণও পরস্পরের সঙ্গে শত্রুতা করে বঞ্চনার প্রশ্রয় দেয়, নির্যাতন করে, নিজেরাও নির্যাতিত হয়। এ বিত্তের জন্য আমাদের আদালত, আমাদের পুলিশ সকলেই সম্পত্তির সংরক্ষণে বদ্ধপরিকর। শাস্তির উদ্দেশ্যে রক্ষিত আমাদের কারাগার, পাপের জন্য আমাদের বিভীষিকাময় আকস্মিক দমন, সকলেরই একমাত্র লক্ষ্য বিত্তের সংরক্ষণ।
\r\n
“চোরাই মালের মস্ত বড় আড়তদার আমাদের রাষ্ট্র। এ রাষ্ট্রই বর্তমানে সমস্ত সামাজিক অবিচারকে বুকের তলায় আগলে রাখে। এর মূলে রয়েছে সেই ব্যক্তিগত মালিকান। সেই উদ্দেশ্যেই রাষ্ট্র বর্বরজনোচিত জুলুমের ঘোরজালে দেশকে দেশ ঘিরে ফেলেছে। এর জন্যই আইন-কানুনের সৃষ্টি, এর জন্যই পুলিশের লোক,সৈন্যসামন্তের প্রয়োজন”।
\r\n
সেই ব্যক্তিগত মালিকানা কিন্তু রাষ্ট্র কর্তৃক কোন আদেশের বলে হটাৎ বিলুপ্ত হবে না অথবা বিপ্লববাদীদের মত তা’ ব্যক্তির হাত থেকে ছিনিয়ে আনা হবে না।
\r\n
মালিক স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে সে বিত্ত আপনিই ত্যাগ করবে, তা হলেই বিত্তশালী ও বিত্তহারার এ ব্যবধান আপনা আপনি নষ্ট হয়ে যাবে, ধনীকে তার সম্পদ, মননশীলকে তার ঔদ্ধত্য ত্যাগ করতে হবে। শিল্পীকে সর্বসাধারণের চিত্র আঁকতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার উপার্জনের ওপর নির্ভর করে জীবন যাপন করতে হবে। জীবনের আদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত সে কিছুই গ্রহণ করবে না।
\r\n
তাঁর বক্তব্যের সারাংশ সোজা কথায় বলা চলে, “ বিত্তবাদীরা যেরুপ দাবী করে-মালিকের নিকট থেকে জোর করে সমস্ত সম্পদ কেড়ে নিলেই সামাজিক অসাম্যের সমাধান হবে, তা মোটেই সত্য নয়। নিচের স্তরে এ সমতা সাধন সম্ভবপর নয়। ধনীদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অধিকার ত্যাগের মাঝেই তার সাফল্য বর্তমান”।
\r\n
তাঁর এ মতবাদকে ধর্মীয় সমাজতন্ত্র বলা যেতে পারে। কারণ আদি খ্রিষ্ট ধর্মের প্রেরণায় ব্যক্তি যখন তার প্রয়োজনাতিরিক্ত আর কিছুই গ্রহণ করবে না তখনই হবে আদর্শ সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা- তখন মানুষে মানুষে আর কোন দ্বন্দ্ব থাকা সম্ভব নয়-দুনিয়া হয়ে পড়ে সুখরাজ্য।
\r\n
ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে সাম্যবাদের যোগ করার মহৎ ইচ্ছায় টলষ্টয় যে জীবনবাদের অনুসরণের জন্য মানব সমাজকে আহ্বান করেছেন, তার মাঝে রয়েছে মস্ত বড় অসঙ্গতি। ব্যষ্টির যদি আত্ম-নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ অধিকার থাকে, তাহলে সে কেন সমষ্টির কল্যাণ কামনায় তার স্বার্থ ত্যাগ করবে। তার উত্তর টলষ্টয় বলছেন, তার জীবনে শান্তি ফিরে আসবে এবং সেই জন্যই যীশু খ্রিষ্ট আত্মত্যাগের পথে অগ্রসর হয়ে মানবজাতিকে আহ্বান করেছিলেন। এ ক্ষেত্রেও অহংবোধকে পরার্থিতার অধীন করার জন্য এক অভিনব সাধনার পরিচয় পাওয়া যায়। তবু আমাদের দেখতে হবে ব্যক্তি স্বাধীনতাকে সম্পূর্ণ স্বীকার করে নিলে, সম্পত্তির উপর মানুষের অধিকারের নীতিকে স্বীকার করে নিলে এ সমাজতন্ত্র কিসে সম্ভব হতে পারে? যদি ব্যষ্টির মনে আত্মকেন্দ্রিক মনোবৃত্তি প্রবল থাকে, তার দমনের জন্য কোন উপদেশ দিলেই চলবে না, তার অধিকারকে সম্পূর্ণ বিলোপ করে তাকে মাত্র সম্পত্তির রক্ষক হিসেবে পরিণত করা দরকার।
\r\n
টলষ্টয়ের চিন্তাধারায় দুস্থ মানবতার জন্য অকপট দরদ ফুটে উঠলেও তিনি ব্যষ্টির স্বাধীনতার সঙ্গে তার মতবাদকে সুসামঞ্জস্য করে তুলতে পারেন নি। কোন্ নীতিতে তার জন্মগত অধিকার ত্যাগ করে মানুষ এক আদর্শ সুখরাজ্য গড়ে তুলবে তার পরিস্কার পদ্ধতি টলষ্টয় দিয়ে যাননি।
\r\n
আমাদের ভুললে চলবে না যে, সমালোচনা করা সহজ কিন্তু গঠনমূলক সৃষ্টি অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপার।
\r\n
“ যে কোন অবস্থায়ই মানুষ তার যুগের বাইরে শূন্যে অবস্থান করতে পারে না। যেখানে বিভিন্ন স্তরে লক্ষ লক্ষ মানুষ একত্রিত রয়েছে-প্রাত্যহিক জীবনে সেখানে প্রতিভাশালীর সঙ্গে হয় বেতনভোগীর সমাবেশ-সেখানে জীবনযাত্রার সুসম্বন্ধ রীতি প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। যে মুহুর্তে টলষ্টয় রোগের কারণ নির্ণয় থেকে চিকিৎসা বিধানে মনোনিবেশ করেছেন অর্থাৎ সোজা কথায় যখন তিনি বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাকে অস্বীকার বা নিন্দা করা ছেড়ে ভবিষ্যতের উন্নততর সাধারণতন্ত্রের প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন, তখনই তাঁর চিন্তাধারা নীহারিকাপুঞ্জের মত অস্পষ্ট ও ধোঁয়াটে রূপ ধারণ করেছে”।* ( Grefan Zewig-Tolstoi.)
\r\n
গান্ধীবাদ
\r\n
টলষ্টয়ের ভারতীয় শিষ্য মহাত্মা গান্ধীর অহিংস নিরুপদ্রব প্রতিরোধের মধ্যেও রয়েছে পরস্পরবিরোধী নানা ভাবের সংঘর্ষ। ব্যক্তি-স্বাধীনতার সঙ্গে আদর্শ সাম্যবাদ বা (গান্ধীর ভাষায়) রামরাজ্যের প্রতিষ্ঠায় গান্ধীজির জীবন দর্শনে এক মস্ত ফাটল দেখা দিয়েছে। মানুষ যদি স্বভাবতই আত্মসর্বস্ব হয়, তাহলে পরহিতে তার সব অধিকার ত্যাগ কোনকালেই সফল হতে পারে না। শুধু আত্মিক শক্তির বলে ইন্দ্রিয় তথা চক্রজয় সব সময় সম্ভবপর হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বার্থপরতা মাথা তুলে দাঁড়ায়। তার ফলে, মুখে সাম্যবাদ প্রচার করলেও মানুষের শোষণের অবসান হয় না।
\r\n
এক্ষেত্রে অবশ্য অস্বীকার করার উপায় নেই যে, গান্ধীজির এ মতবাদ মানব-কল্যাণের উদ্দেশ্যেই গঠিত হয়েছিল। একথা সর্বতোভাবে সত্য যে, ১৯২১ সালে গান্ধীজি কর্তৃক প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনের ফলে এ উপমহাদেশের রাজনীতিতে এক প্রবল বিপ্লব দেখা দিয়েছিল। ইংরেজ শাসক ও শোষকদের বিরুদ্ধে অহসযোগ নীতি পালন করে, তাদের শাসন ব্যবস্থাকে বান্চাল করে দেওয়াই ছিল গান্ধিজির জীবনের সর্বপ্রধান মন্ত্র। এ মন্ত্র বাস্তবায়নের চেষ্টার ফলেই এদেশে ইংরেজ শাসন ক্রমশ শিথিল হয়ে পড়ে। তবে এ অসহযোগ নীতির সঙ্গে যুক্তিসঙ্গতভাবেই যুক্ত ছিল ব্যক্তিস্বাধীনতার কীর্তি। এ অসহযোগ নীতিকে কারো ওপর বলপ্রয়োগে চাপানো যায় না। ব্যক্তিমানস স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই তাকে গ্রহণ করবে। তাই যদি হয় তাহলে স্বাধীনতা লাভের পরে সে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠায় কেন কোন ব্যক্তি অগ্রসর হবে, তার কোন যুক্তি গান্ধিজি প্রদর্শন করেননি। স্বভাবত স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির ব্যাপারে অভ্যস্ত ব্যক্তির পক্ষে রামরাজ্যের মত আদর্শিক সাম্যবাদমূলক রাষ্ট্র গঠনে প্রবৃত্ত হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার নয়। এজন্য ব্যষ্টি-মানসেও সাম্যবাদের বীজ রয়েছে এবং অনুশীলনের ফলে তা বিকশিল হতে পারে-এ সূত্রটিও গান্ধীজীর প্রদর্শন করা উচিত ছিল।
\r\n
ব্যষ্টি-চেতনা ও সমষ্টি-চেতনা বা সাম্যবাদের চেতনার মধ্যে যে বিরাট ফাঁক রয়েছে তার যোগসূত্র আবিস্কারের মধ্যেই রয়েছে রাজনীতিতে সফলতার চাবিকাঠি। গান্ধীজি ঐ সূত্রটি আমাদের দিয়ে যাননি।
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n\r\n
পঞ্চম পরিচ্ছেদ
\r\n
মানুষের পরিচয়
\r\n
একটি সত্য স্বভাবতই চোখে পড়ে। এ যাবত সেসব মতবাদের উৎপত্তি হয়েছে, তাতে মানবজীবনের কোন বিশেষ দিকের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে, তারই আলোকে গোটা জীবনের ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য হয়েছে প্রয়াস। যদিও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নামে তারা জগতে প্রচারিত তবুও তাদের মধ্যে রয়েছে অবৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি। বিজ্ঞানের আসল কথা, জীবনের সকল তথ্যকে গ্রহণ করে, তার ব্যাখ্যার জন্য সার্বিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। এসব ব্যাখ্যায় সকল তথ্যকে গ্রহণ না করে বিশেষ থিয়োরি বা মতবাদের সঙ্গে খাপ খাওয়াবার চেষ্টায় অনেকগুলোকে করা হয়েছে অস্বীকার অথবা তাদের বিকৃতি করে ফেলে দেয়া হয়েছে ছকের মধ্যে। তাতে আরোহ৯১ পদ্ধতির করা হয়েছে অবমাননা। কারণ বিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য বিশেষ৯২ থেকে সার্বিকে৯৩ উপস্থিত হওয়া। অবরোহ পদ্ধতিতে৯৪ কোন বিশেষ নীতিকে গ্রহণ করে নিচের দিকে নেমে যাওয়া বৈজ্ঞানিক জগতে আত্মহত্যারই নামান্তর। অথচ লক্ষণীয় যে, আরোহ পদ্ধতিই বৈজ্ঞানিক জগতে একমাত্র বিষয় পদ্ধতি বলে স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও সেই অবরোহ পদ্ধতির প্রভাব বিজ্ঞান এড়িয়ে যেতে পারেনি। তাই গোড়াতে জীব জগতে যুদ্ধ৯৫ বা কামপ্রবৃত্তির মৌলিকতা, মানুষের স্বার্থপরতা প্রভৃতি সূত্রগুলোকে স্বীকার করে তাদের একচোখা আলোকে জটিল জীবনের সবগুলো দিকের ব্যাখ্যা দেয়া হচ্ছে।
\r\n
এমনকি, যে কার্ল মার্কস হেগেলের চিন্তা মাধ্যমগুলোকে শ্রেণী-সংগ্রামে রুপান্তরিত করে উৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থার সূত্রে জীবনের গতি ও ক্রমবিকাশের ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন, তাঁর মনেও সবসময় হেগেলীয় দর্শনের প্রভাবই ছিল কার্যকরী। তাই তাকে অস্বীকার করেও জীবনের বিচিত্র ক্ষেত্রে তারই অমোঘতা স্বীকার করে নিয়েছেন। উৎপাদন ব্যবস্থা ছাড়া মানবজীবনে যতো সব ফ্যাকটর কার্যকরী সেগুলোকে তিনি করেছেন সম্পূর্ণ অস্বীকার বা যুক্তিবাদের প্রভাবে তিনি একটি ছকে ফেলে মানবজীবনে সবগুলো দিকের ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। তাই দেখা দিয়েছে অবৈজ্ঞানিক মনোভাব।
\r\n
দ্বিতীয়ত, আধুনিক বিজ্ঞানে যুক্তি ও অভিজ্ঞতাকেই জ্ঞানের একমাত্র পন্থা বলে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। এগুলো ব্যতীত মানবজীবনে জ্ঞানের অপর কোন পন্থা নেই বলে ধরে নেয়া হয়েছে।এ মনোভাবের মধ্যেও বিজ্ঞানের রয়েছে এক মস্তবড় গোঁড়ামি।
\r\n
তৃতীয়ত, এসব আলোচনার ফলে আমরা দেখেত পেয়েছি মানবজীবনের মধ্যে রয়েছে মস্তবড় দ্বন্দ্ব। এক-চোখামি করে মানবজীবনের কোন ব্যাখ্যা করতে গেলেই মানবজীবনের অন্য দিক বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তার ফলে অন্য মতবাদের উৎপত্তি হয়। তাতেও জীবনের ব্যাখ্যা সুষ্ঠু হয় বলে দেখা দেয় দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্বের উৎপত্তি ও সংঘাতের মধ্য দিয়েই মানব-সভ্যতার গতি চলছে ধেয়ে। কাজেই মানবজীবন সম্বন্ধে কোন সার্বিক সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছার আগে তার সম্বন্ধে পেতে হবে পূর্ণ জ্ঞান। সে পূর্ণ জ্ঞানের আলোকেই গড়ে উঠবে তার জীবন-দর্শন।
\r\n
মানবজীবনের অসংখ্য বৃত্তি ও প্রবৃত্তির সন্ধান পাওয়া যায়। তার জীবনে রয়েছে যেমন স্ববোধ৯৬ তেমনি রয়েছে পরার্থপরতা৯৭ । তার যেমন রয়েছে ক্ষুদা, যৌন প্রেরনা, প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হওয়ার বাসনা, সৌন্দর্য ভোগ করার প্রবৃত্তি, তেমনি রয়েছে প্রেম, আত্মত্যাগ, স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা, রুচিবোধ, নীতিবোধ, এ বিশ্বের প্রকৃত পরিচয় পাওয়ার জন্য অদম্য আকাঙ্ক্ষা।
\r\n
মানব-মনে রয়েছে মনন ক্ষমতা৯৮ প্রক্ষোভ৯৮ ইচ্ছাশক্তি১০০। মানবমনের সম্ভাব্য উৎসের বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বোধি১০১ ভুয়োদর্শন১০২ ও যুক্তির১০৩ মাধ্যম আদি থেকেই মানুষ জ্ঞানলাভ করছে। গোড়াতে যে কোন একটিতে জ্ঞানের সূচনা হলেও পরবর্তীকালে তার বিস্তৃতি ও ব্যাখ্যার জন্য অপরটির প্রয়োগও সম্ভবপর।
\r\n
আধুনিক মনোবিজ্ঞানে বোধিলব্ধ জ্ঞানের তেমন কার্যকারিতা স্বীকার করা হয় না; কার্যকারণ-পরম্পরা সূত্রের১০৪ অমোঘ বিধান ধ্রুব সত্য বলে গৃহীত হওয়ার পরই বোধিলব্ধ জ্ঞানকে অসুস্থ ব্যক্তির বিকৃত কল্পনা বলে অন্ধকারে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। অথচ কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, বিজ্ঞান অথবা তত্ত্বজ্ঞানের জগতেও বোধির মাধ্যমেই সবগুলো আবিস্কার হয় সম্ভবপর। নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ বা আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ১০৫তর্কবুদ্ধির দ্বারা আবিষ্কৃত হয়নি। তাদের সূচনা বাইরের উদ্দীপক১০৬ দ্বারা হলেও ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের দ্বারা তারা আবিষ্কৃত হয়নি। হটাৎ আলোর ঝলকানির মত মনীষীদের মনের আকাশে প্রকৃতির এসব সূত্র হয়ে ওঠে জলজ্যান্ত।
\r\n
মানবজীবনে দেখা যায়, কোন এক বিশেষ বৃত্তির অতিরিক্ত অনুশীলনে ব্যক্তিজীবনে দেখা দেয় নৈরাজ্য। ক্ষুধার নিবৃত্তির জন্য মানুষ আহার করে। সেই আহার করতে গিয়ে চব্বিশ ঘণ্টাই তাতে মগ্ন থাকে, তা হলে তার স্বাস্থ্যহানি তো হবেই, তার ওপর তাকে সম্মুখীন হতে হবে আরও নানাবিধ সমস্যার। তেমনি কামকলার অতিরিক্ত অনুশীলনে মানবজীবনে চরম অধঃপতনের স্তরে উপস্থিত হয়। কাজেই দেখা যায়, কোন বিশেষ বৃত্তির অতিরিক্ত বিকাশের ফলে অন্যান্য বৃত্তিগুলো হয় অবদমিত এবং তার পরিণতিতে এক বৃত্তির সঙ্গে অন্য বৃত্তির সংঘাত ও সংঘর্ষ হয়ে পড়ে অনিবার্য।
\r\n
সেরূপ কেবল একটি পদ্ধতির অনুরণেরও জ্ঞানের অন্যান্য পন্থাগুলো হয়ে পড়ে অকেজো। জ্ঞানের অন্যান্য শক্তিগুলো১০৭ হয়ে পড়ে সম্পূর্ণ অসাড়। তাই বিকাশের পথে দেখা দেয় চরম অন্তরায়।
\r\n
মানবজীবনকে সুস্থ,সবল ও স্বাভাবিকভাবে বিকশিত করে তুলতে হলে তার জৈব-জীবনের নানাবিধ প্রবৃত্তির সুস্থ বিকাশ তার পক্ষে অতীব প্রয়োজন। জ্ঞানের ক্ষেত্রেও বোধি,বিচারবুদ্ধি ও ভূয়োদর্শনের যথাযথ স্থান নির্দেশ করে তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করলেই জ্ঞানের পথ হয় সুগম। মানুষ সত্যের সঙ্গে পরিচয় লাভে হয় ধন্য।
\r\n
মানুষের জৈব-জীবনের বিভিন্ন বৃত্তির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা দরকার। সেই যোগসূত্রের১০৮ কল্যাণে পরস্পরবিরোধী ভিন্নমুখী প্রবৃত্তির মধ্যে শৃঙ্খলা হয় প্রতিষ্ঠিত এবং ব্যষ্টিজীবনে স্থাপিত হয় ভারসাম্য। মানব মনের আদিম স্ববোধ ও পরার্থিতার মধ্যে সমতা সাধিত হলে সমাজ-ব্যবস্থা১০৯ ও ব্যষ্টিকেন্দ্রিকতা বা সমষ্টি-কেন্দ্রিকতার দোলায় না দুলে প্রগতির পথে হয় অগ্রসর।
\r\n
মানবজীবনে নানাবিধ সহজাত বৃত্তি ও প্রবৃত্তির আলোচনা করলে বা মনন, প্রক্ষোভ বা ইচ্ছাশক্তির আলোচনা করলে দেখা যায়-তারা আপাতত পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন বা পরস্পরবিরোধী মনে হলেও তাদের মধ্যে একটা মৌলিক ঐক্য রয়েছে। সে ঐক্যের মূলে রয়েছে মানুষের আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি এবং আত্ম-প্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি(Self perpetuation)। মানুষ প্রাথমিক পর্যায়ে তার স্বজাতীয় ও বিজাতীয় নানাশ্রেণীর শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে চায়। এজন্যই তার মধ্যে সহজাত নানাবিধ বৃত্তি দেখা দেয়। আবার এ বিশ্বের নানাবিধ শত্রু থেকে নিরাপদ হলে সে এ বিশ্বে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হতে চায়। এ দুটো বৃত্তিকে একত্রে আত্ম-সংরক্ষণ(Self preservation) – এর বৃত্তি বলা যায়। অনুধাবন করলে দেখা যায়-মানুষের ক্ষুধা,যৌন প্রেরণা, প্রকৃতির সঙ্গে একীভূত হওয়ার বসনা, সৌন্দর্য ভোগ করার প্রবৃত্তি, প্রেম, আত্মত্যাগ,স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, এ বিশ্বের প্রকৃতি পরিচয় লাভ করার জন্য বাসনা, রুচিবোধ, নীতিবোধ প্রভৃতি সকল বৃত্তির মূলে রয়েছে সেই আত্মরক্ষা বা আত্মপ্রতিষ্ঠার বাসনা। ক্ষুধা নিবারিত না হলে মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা নেই। এজন্য এ বৃত্তির চরিতার্থতা তার জীবনের পক্ষে প্রয়োজন। যৌন প্রেরণার মাধ্যমে মানুষ এ বিশ্বে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ পায়। সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে মানুষ অমরত্ব লাভ করতে চায়। প্রকৃতির সঙ্গে বিরোধিতা করে মানুষ টিকে থাকতে পারে না বলে –তার আত্মরক্ষার জন্য প্রকৃতির সঙ্গে মৈত্রীর সম্বন্ধে আবদ্ধ হতে চায়। সৌন্দর্য ভোগের মধ্যে এমন এক চিরন্তন সত্তার সন্ধান পেতে চায়, যাকে লাভ করার ফলে সে এ বিশ্বে চিরস্থায়ী হয়ে বাস করতে পারে। প্রেমের মাধ্যমে সে তার জীবনে বলিষ্ঠতা লাভ করতে চায়, যার ফলে সে সবকিছুকেই তুচ্ছ করে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে। এ বিশ্বের প্রকৃত পরিচয় লাভ তার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন। কারণ এ পরিচয় লাভ করতে পারলেই তার পক্ষে স্থায়ী স্থিতির রয়েছে সমূহ সম্ভাবনা। ভাল ও মন্দের পার্থক্য বিচার করার মধ্যেই তার মধ্যে রুচিবোধ প্রকাশিত হয়। এ পার্থক্য বিচারের মূল ভিত্তি হচ্ছে-তার জীবনের পক্ষে সহায়ক ও জীবনের পক্ষে মারাত্মক বিষয়ের পৃথকীকরণ। এ পার্থক্য বিচার না করতে পারলে সে বহু পূর্বেই ধরাপৃষ্ঠ থেকে উধাও হয়ে যেত। এ বিচারই কালে জীবন থেকে পৃথক নীতিবোধ হলে স্বতন্ত্র এক নীতিতে পরিণত হয়। কাজেই এ সকল বৃত্তি ও প্রবৃত্তির আলোচনা করলে একথাই প্রমাণিত হয়-সবগুলো বৃত্তির মূলেই রয়েছে দুটো লক্ষ্য। একটা হচ্ছে-মানুষের আত্মরক্ষা (Self protection) অপরটা হচ্ছে আত্মপ্রতিষ্ঠা (Self perpetuation)।
\r\n
এ সব বৃত্তি এ প্রবৃত্তির মূলত উদ্দেশ্য সাধনমূলক স্থিতি থাকলেও বর্তমানে তারা স্বয়ংসম্পূর্ণরূপেই দেখা দিচ্ছে। তবে এ ব্যাপারটি কেবল বৃত্তি ও প্রবৃত্তির বেলায়ি সত্য নয়। মানবজীবনের নানাবিধ আচরণেও তা প্রকাশ পায়। একদা দেহের পুষ্টির জন্যই মানুষ আহার করত, লজ্জা শরম নিবারণের জন্য কাপড় পরতো। এখন আহার্যের ব্যাপারে মানুষের লক্ষ্য শুধু ক্ষুধার নিবৃত্তি নয়-জিহ্বার স্বাদেরও পরিতৃপ্ত বটে। তেমনি নানাবিধ সূক্ষ্ম বস্ত্রাদি তৈরি করে মানুষ শুধু লজ্জা নিবারণই করতে চায় না সঙ্গে সঙ্গে পরিহিত বস্ত্রের মাধ্যমে তাকে অন্যান্য লোকের কাছে মোহনীয়ও করতে চায়। তবে গোড়াতে আহার্য পুষ্টিকর না হলে যতই সুস্বাদু হোক না কেন তাতে দীর্ঘকাল মানুষ মজে থাকতে পারে না। তেমনি পরিধানের বস্ত্র দ্বারা লজ্জা নিবারণ না হলে তার দ্বারা বস্ত্র পরিধানের আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না।
\r\n
এ জন্য মানবজীবনকে সুষ্ঠুভাবে বিকাশের পথে নিয়ে যেতে হলে তার জন্য এমন এক প্রকল্প(Hypothesis) গ্রহণ করতে হবে যাতে তার জীবনে সম্পূর্ণভাবে সন্তোষ বিধান সম্ভবপর হয়। তার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে আমাদের এমন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে, যা আমাদের জীবনকে নানাবিধ শত্রুর আক্রমণ থেকে নিরাপদ রাখতে পারে। তার দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে- এ প্রকল্পের মধ্যে এমন প্রতিশ্রুতি থাকবে- যাতে এ বিশ্বে আমরা অমরত্ব বা আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করার সান্তনা পেতে পারি।
\r\n
যদিও নানাবিধ বৃত্তি ও প্রবৃত্তির মূলে রয়েছে আত্মরক্ষা বা আত্মপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্য-তবুও তারা আপাতত স্বাধীন ও স্বনির্ভর রূপেই দেখা দিচ্ছে, এজন্য সে প্রকল্পের মধ্যে এমন উপাদান থাকে- যাতে সে বৃত্তি ও প্রবৃত্তিগুলো ও সন্তোষ লাভ করতে পারে।
\r\n
এ প্রকল্পের মধ্যে শুধু পূর্বোক্ত বিষয়গুলোর সন্তোষ বিধান হলেই হবে না- তার মধ্যে জ্ঞানের নানাবিধ মাধ্যমেরও সন্তোষ ও বিকাশ হওয়া বাঞ্ছনীয়।
\r\n
আমরা পূর্বেই দেখেছি-জ্ঞানকে শুধু পঞ্চেন্দ্রিয়জাত সীমার মধ্যে আবদ্ধ করলে জ্ঞানের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় না। তেমনি জ্ঞানকে শুধু বুদ্ধি অথবা বোধির মধ্যে সীমাবদ্ধ করলেও জ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপ প্রকটিত হয় না। পঞ্চেন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতা বা বুদ্ধি ও বোধির অনুশীলনের ফলে যে ব্যাপক ও সর্বাত্মক আকারে জ্ঞান দেখা দেয়- তারই ভিত্তিতে এ বিশ্ব জগৎ বা স্থিতি সম্বন্ধে যে প্রকল্প গঠন করা হয় সে প্রকল্পই প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের সর্বাত্মক সন্তোষ দানে সমর্থ।
\r\n
অতএব আমাদের জীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ও তার সন্তোষ বিধানের এরূপ একটা প্রকল্প গঠন করা অত্যাবশ্যক।
\r\n
এ ক্ষেত্রে বুদ্ধির সন্তোষ ও জীবনের সন্তোষের মধ্যেও পার্থক্য প্রদর্শন করা অবশ্য কর্তব্য। বুদ্ধির সন্তোষ দানের জন্য যুগে যুগে নানাবিধ দার্শনিক মতবাদের উৎপত্তি ও প্রতিষ্ঠা হয়েছে। অতি আদিকালের গ্রিকদের মধ্যে যে সংস্কৃতির বিকাশ হয়েছিল- তাতে একে একে জড় বস্তুগুলোকে এ জগতের আদি সত্তা হিসেবে গ্রহণ করে ক্রমশ গ্রিক চিন্তাধারা অমূর্ত বিষয়ের দিকে ধাবিত হয়েছে। তাতে সাময়িকভাবে মানস-মানস, বিশেষত মানববুদ্ধি সন্তোষ লাভ করলেও মানবজীবন তাতে সম্পূর্ণ সন্তোষ লাভ করেনি। কারণ, বুদ্ধিই মানবজীবনের একমাত্র বৃত্তি নয়। তার সঙ্গে প্রক্ষোভ বা ইচ্ছাশক্তি তো রয়েছেই; তার ওপর নানাবিধ উপরিভাগজাত বৃত্তিও রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়-বুদ্ধিকে অভিজ্ঞতানিরপেক্ষ কোন আদিম বৃত্তি বলেও গণ্য করা যায়, - তাহলেও প্রত্যক্ষণজাত ইমেজ(image) বা কল্পনা প্রভৃতিকে অস্বীকার করার উপায় নেই। তেমনি প্রক্ষোভজাত নানাবিধ বিষয় এবং ইচ্ছাশক্তির নানবিধ দাবী ও প্রকাশকেও অস্বীকার করা যায় না। কাজেই যে ক্ষেত্রে শুধু বৃদ্ধির সন্তোষ বিধানের জন্যই রয়েছে একমাত্র লক্ষ্য- সে মনোবৃত্তি বা তদ্জাত সিদ্ধান্তকে জীবনের চরম সন্তোষ বিধানের সূত্র হিসেবে গ্রহণ করা যায় না।
\r\n
এ জন্যই এক্ষেত্রে দর্শন ও জীবন-দর্শনের অর্থাৎ শুধু বুদ্ধিজাত সিদ্ধান্তের ও নানাবিধ বৃত্তির সন্তোষ বিধানকল্পে গঠিত প্রকল্পের পার্থক্য সম্বন্ধে অবহিত হওয়া কর্তব্য। বুদ্ধির কারসাজিতে এখন পর্যন্ত মানুষ যেসব সিদ্ধান্তে এসে উপনীত হয়েছে-তাতে কেবল বুদ্ধিই সন্তোষলাভ করেছে। মানবজীবনের আরও নানাবিধ বৃত্তি বা প্রবৃত্তি তাতে সন্তোষলাভ করেনি।
\r\n
এখানেই দর্শন ও ধর্মের মধ্যে রয়েছে গুরুতর পার্থক্য। দর্শন মানুষের বুদ্ধিকে সন্তোষদানে সাময়িকভাবে সমর্থ হয়। ধর্ম বা জীবনদর্শনের সার্থকতা হচ্ছে মানবজীবনের নানা বিষয়ের সন্তোষদানের সামর্থ্য। এজন্য মানবজীবনের দর্শনের প্রভাবের চেয়ে ধর্মের প্রভাব গুরুতর ও দীর্ঘস্থায়ী। সমগ্র আদি যুগে কেবল দর্শনের চর্চা করা সত্ত্বেও খ্রিষ্ট ধর্মের আবির্ভাবের ফলে মানুষের মন সে ধর্মের প্রতি এমনভাবে আকৃষ্ট হল কেন, এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়-জীবনের একমাত্র বৃত্তি বুদ্ধির সন্তোষ বিধানে পর্যবসিত হওয়ার অন্যান্য বৃত্তি ও প্রবৃত্তির সন্তোষ-বিধানের জন্যই সে প্রতিক্রিয়া এরূপ প্রচণ্ডভাবে দেখা দিয়েছিল। দর্শন ও জীবন-দর্শনের মধ্যে আমরা এরূপ পার্থক্য করিনে বলে অনেক সময় শুধু বুদ্ধির আলোকে আমরা জীবন-দর্শনের আলোচনায় প্রবৃত্ত হই।
\r\n
আমাদের তাই এ পার্থক্যকে সামনে রেখেই সে প্রকল্পের গঠনে অগ্রসর হতে হবে। আমাদের লক্ষ্য হবে এমন এক প্রকল্প গ্রহণ, যাতে কেবল বুদ্ধি নয়, সকল বৃত্তিও সন্তোষ লাভে হয় সমর্থ। এরূপ একটা প্রকল্পের সন্ধান আমরা পাচ্ছি ইসলামের আল্লাহ্ নামক ধারণার মধ্যে। এ ধারণার কোন ইন্দ্রিয়লব্ধ বা প্রত্যক্ষণজাত ধারণা নয়। বুদ্ধি দ্বারাও এ ধারণার সন্ধান পাওয়া যায়নি। এ ধারণার সন্ধান পেয়েছেন হযরত রসূলই-ই আকরাম (সঃ) প্রত্যাদেশ বা revelation-এর মাধ্যমে। এ প্রত্যদেশ স্বজ্ঞারই এক বিশেষ সংস্করণ। আমরা মানব-জ্ঞানের আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্বেই দেখতে পেয়েছি স্বজ্ঞা থেকে নানাবিধ আবিস্কার সম্ভব হতে পারে। জুঙের বর্ণনা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, স্বজ্ঞার কার্যকারিতার ফলে দ্রষ্টার সৃষ্টি হতে পারে। হযরত রসূল-ই আকরাম (সঃ) দীর্ঘকাল হেরা পর্বতে সত্য লাভ করার জন্য যে তপস্যা করেছিলেন তারই ফল হিসেবে প্রথমে ২৭ শে রমযানের রাত্রিতে আল্লাহ্র বাণী নিয়ে ফেরেশতা জিবরাইল (আঃ) দেখা দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্ সম্বন্ধে পূর্ণ ধারণা হযরতের মানসে জীবন্ত হয়ে দেখা দেয়।
\r\n
এ জন্যই দেখা যায়, জ্ঞানের রাজ্যে অন্বেষণকারী যাতে অবলীলাক্রমে অগ্রসর হতে পারে, তার জন্য অন্য কোন স্বতঃসিদ্ধের প্রয়োজন দেখা দেয়নি। জ্ঞানবিস্তার আলোচনা করলে দেখা যায়-সাধারণত পঞ্চেন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান ও বুদ্ধিজাত জ্ঞানকেই শুধু দুটো রূপ বলে ধরে নেয়া হয়। অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকদের মতবাদ অনুসারে আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমরা যে সব সংবেদন লাভ করি, তার ভিত্তিতেই আমাদের জ্ঞানের সৌধ গড়ে তুলতে হবে। এজন্য এ মতবাদের প্রবর্তক জন্ লক মন্তব্য করেছেন- There is nothing in the intellect; which was not previously in sensation- অর্থাৎ আমাদের বুদ্ধিতে এমন কোন কিছুই নেই যা পূর্বে সংবেদনের মধ্যে ছিল না।
\r\n
অপরদিকে বুদ্ধিবাদীদের বক্তব্য হচ্ছে-বুদ্ধি দ্বারাই সত্যের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের রয়েছে একমাত্র সম্ভাবনা। বুদ্ধি বা যুক্তিবাদীদের মুখপাত্র হিসেবে সুপ্রসিদ্ধ জার্মান দার্শনিক হেগেল বলেছেন- Whatever is real is rational and whatever is rational is real. অর্থাৎ যা কিছু বাস্তব বা যুক্তিপূর্ণ এবং যা কিছু যুক্তিপূর্ণ তা বাস্তব। এ নীতির প্রথম দিকটা গ্রহণ করতে সকলেই সম্মত। কারণ যা কিছু সত্য তা যুক্তিপূর্ণ হতে বাধ্য। যাতে কোন যুক্তির অবকাশ নেই- তা হয় কাল্পনিক, না হয় মিথ্যা। তবে যা যুক্তিপূর্ণ তা বাস্তব বলা সব সময় ঠিক নয়। কারণ যুক্তির ধারায় আমাদের পক্ষে এমন এক স্তরেও আসা সম্ভবপর, যার স্থিতির স্বপক্ষে কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণ নেই বা অন্য কোন প্রমাণও নেই। তবে অভিজ্ঞতাকে বা যুক্তিকে- যে কোন পদ্ধতিকেই জ্ঞান লাভের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করি না কেন- অভিজ্ঞতা বা যুক্তি সে আমাদের সঠিক জ্ঞান দান করতে পারে, সে সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত হতে পারিনে। এক্ষেত্রে আমাদের অভিজ্ঞতা বা যুক্তির বহির্ভূত অন্য কোন প্রত্যয়ের ওপর আস্থা স্থাপন করতে হবে। কেননা, এ বিশ্ব বিধানে এমন কোন শক্তি থাকতে পারে, যা সবসময়ই মানুষকে প্রতারিত করে। আধুনিক দর্শনের পিতা ডেকার্থ তাঁর অনুসন্ধানের প্রথম স্তরে এজন্য সবকিছুইকেই অবিশ্বাস করতে ছিলেন প্রস্তুত। অবশেষে Cogito Ergo Sum (আমি চিন্তা করি বলে আমি আছি) এ সত্যে এসে উপনীত হন। তবে এখানে প্রশ্নের অবকাশ রয়েছে। তিনি যে চিন্তা করেছেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই- তবে সে চিন্তার বিষয়বস্তু সত্য কিনা তার তো বিচার হয়নি। এমনও তো হতে পারে যে, তাঁর চিন্তা সত্য, তবে তিনি চিন্তার ক্ষেত্রে বারবার শয়তানের দ্বারা প্রতারিত হচ্ছেন। তারঁ চিন্তা তাঁর সামনে যত সব বিষয় উপস্থাপিত করছে- বাস্তবে সে সবের কোন অস্তিত্ব নেই। চিন্তার বিষয়বস্তু পরিচ্ছন্ন হলেই তা সত্য হয় না। কোন চিন্তা সত্য হতে হলে বাস্তবের সঙ্গে তার যোগ চাই। সে যোগ যে চিন্তার পক্ষে সম্ভব হয়েছে,- তার কোন সার্টিফিকেট আমরা পাচ্ছিনে। এজন্য আমাদের ধরে নিতে হয় এ বিশ্ব চরাচরের সবকিছুই এমনভাবে সৃষ্ট যে, তা মানব জ্ঞানের পক্ষে অধিগম্য। সে স্বতঃপ্রমাণের ভিত্তি অভিজ্ঞতা বা যুক্তি নয়। সে স্বতঃপ্রমাণ আসে প্রত্যয় থেকে। ইসলামী মতে বলা হয়-আল্লাহ্কে স্বীকার করলে জ্ঞাতার সঙ্গে জ্ঞেয় বস্তুর সম্বন্ধ সবসময়ই পরিস্কার হয়ে দেখা দেয়। আল্লাহ্র বিধান মতে জ্ঞাতা সত্যিকার জ্ঞানলাভে সমর্থ। কেননা আল্লাহ্ এ বিশ্বকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, তাতে জ্ঞাতার পক্ষে গান লাভ করার রয়েছে সমূহ সম্ভবনা।
\r\n
আল্লাহ্র এ ধারণাকে মানবজীবনের সকল সমস্যার সমাধানে সফল বলে স্পষ্টই প্রমাণিত হয়। কারণ, আমরা পূর্বেই দেখেছি-শুধু বিচার-বুদ্ধির সন্তোষ লাভই মানবজীবনের কাম্য নয়। মানুষের মধ্যে তার সবগুলো বৃত্তি ও প্রবৃত্তির সন্তোষ লাভের রয়েছে অদম্য আকাঙ্ক্ষা। তার মধ্যে যেমন যৌন আবেগের পরিতৃপ্তির জন্য আকাঙ্ক্ষা তেমনি ক্রোধ, লোভ সবগুলো রিপুকেই যথাযথ ব্যবহার করার জন্যে রয়েছে তাগিদ। আল্লাহ্ নামক এ ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর আদেশ-নিষেধপূর্ন যে পুস্তক-কুরআন-উল-করীমের আলোকে মানুষ তা সহজেই লাভ করতে পারে। এমনকি যে কল্পনাকে মানুষ শিশুদের জীবনে কার্যকরী এক বৃত্তি বলে উপহাস করে-সেই কল্পনারও যথাযথ সন্তোষ বিধানের সূত্র রয়েছে। অতএব জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আল্লাহ্র বিভিন্ন গুণ কিভাবে কার্যকরী হতে পারে-সে সম্বন্ধে আমাদের আলোচনার প্রয়োজন।
\r\n
পূর্ণাঙ্গ দর্শন ও ইসলাম
\r\n
সে দর্শনের উপকরণ হবে জীবন্ত মানুষের সবগুলো বৃত্তি ও প্রবৃত্তি। তার লক্ষ্য হবে পূর্ণ মানুষ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ। তার নৈতিক আদর্শ হবে পরস্পর ভিন্নমুখী প্রবৃত্তির সামঞ্জস্যবিধান। তার সামাজিক ও রাষ্ট্রিক আদর্শ হবে ব্যষ্টি ও সমষ্টির অধিকারের সমন্বয়।
\r\n
সে পূর্ণাঙ্গ জীবন-দর্শনেরই অপর নাম ইসলাম। ইসলামকে তাই বলা হয় মানবতার ধর্ম। সেই ধর্মের উৎপত্তি হযরত মুহাম্মদ মুস্তফার (সঃ) প্রচার থেকে নয়-সৃষ্টির আদি থেকেই নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ভুল-ভ্রান্তির পথে মানুষ তার পূর্ণ পরিচয় লাভের জন্য এ পথেই চলছে। প্রয়োগ১১০ অথবা বৃদ্ধির১১১ আলোকে সে বিশাল জীবনের আংশিক আভাস যে মানুষ পেতে পারে না, তা নয়। কিন্তু সে আংশিক সত্যকে পূর্ণ সত্য ভ্রমে তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে মানুষ হয়ে পড়ে দিশেহারা।
\r\n
হযরত মুহাম্মদের (সঃ) পূর্বে যারা দুনিয়ার সত্য প্রচার করেছিলেন ইসলাম তাঁদের অস্বীকার করেনি, বরং যথেষ্ট শ্রদ্ধার সঙ্গেই তাঁদের স্মৃতি বহন করছে। তাঁদের মতবাদ কোন বিশেষ দেশের বা বিশেষ কওমের লোকের ওপর প্রযোজ্য হওয়ার অথবা মানবজীবনের কোন বিশেষ দিকের ওপর জোর দেওয়ার কালে তাদের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়। তবুও ইতিহাসের ধারায় জ্ঞানের ও নীতির এক একটা বিশিষ্ট পর্যায় হিসেবে এখনও তাদের মূল্য রয়েছে যথেষ্ট। ইসলামকে বলা হয় মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। মানব প্রকৃতির সঙ্গে তার অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ বর্তমান। মানুষের নবী হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) বলেছেনঃ
\r\n
“ সদ্যোজাত শিশু সত্য ধর্মেই জন্ম নেয়; তার পিতামাতা তাকে য়াহূদী, ক্রিশ্চিয়ান বা সেবিয়ান করে তোলে”।
\r\n
ইসলাম গোড়াতেই মানবজীবনকে দেখেছে পূর্ণভাবে; সেজন্য বিভিন্ন প্রবৃত্তি বা জ্ঞানের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে তারতম্য করলেও কোনটাকেই অস্বীকার করেনি। মানবজীবনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি-ক্ষুধা, যৌনস্পৃহা প্রভৃতিকে ইসলাম কোনদিনই অস্বীকার করেনি; বরং কিভাবে ক্ষুধার নিবৃত্তি সুষ্ঠুভাবে হতে পারে, কিভাবে মানুষ জীবনে শান্তি পায়-তার ব্যবস্থা করেছে। মানব-প্রকৃতির স্বাভাবিক বিকাশের পথ সুগম করার জন্য এ জীবনদর্শনে মানবজীবনের বৈচিত্র্য গোড়াতেই স্বীকৃত হয়েছে। জগতের পূর্ণ পরিচয়ের পদ্ধতিরুপে বোধির সঙ্গে প্রয়োগ ও যুক্তি গৃহীত হয়েছে। জ্ঞানের ক্ষেত্রে যাতে কোনো কালেই কোন সীমারেখা টেনে দেওয়া না হয়, সেজন্য মানুষের নবী হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) উদাত্ত স্বরে ঘোষণা করেছেনঃ
\r\n
জ্ঞান আহরণের জন্য যদি প্রয়োজন হয় চীন দেশেও যাও’।
\r\n
অপর এক বাণীতে বলেছেনঃ
\r\n
“জ্ঞান অর্জন প্রত্যেক মুসলিম পুরুষ ও নারীর পক্ষে ফরয (অবশ্য কর্তব্য)”।
\r\n
এক্ষেত্রে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, জ্ঞান বলতে তিনি শুধু ঐশী জ্ঞানকেই বুঝতেন না। জ্ঞান ছিল তাঁর কাছে ব্যাপক। সে চীন দেশের মনীষীর জ্ঞানই হোক তার সুদূর ইউরোপের জ্ঞানই হোক, যে কোন উপায়ে লব্ধ জ্ঞানকে তিনি জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদানরূপে গ্রহণ করতেন।
\r\n
এ দর্শনে ব্যষ্টিকে সমাজজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন স্বয়ম্ভরূপে কল্পনা করা হয়নি। দেহের এক অঙ্গের সঙ্গে অপর অঙ্গের যেমন অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বর্তমান, তেমনি মানুষের মধ্যেও যে একই প্রকৃতি, একই রক্তধারা বর্তমান-সে সত্যটি গোড়াতেই ঘোষণা করা হয়েছেঃ
\r\n
“ এই যে তোমাদিগের জাতি-ইহা তো একই জাতি”। (সুরা আম্বিয়াঃ ২১-৬-৯১)
\r\n
অপর জায়গায় বলা হয়েছেঃ
\r\n
“প্রকৃতপক্ষে তোমাদের এ ভ্রাতৃত্ব একই ভ্রাতৃত্ব এবং আমি তোমাদের প্রভু; সুতরাং আমাকে ভয় কর। মানুষেরা তাদের বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত করেছে এবং প্রত্যেক জাতি তার আইন-কানুন ও লোকাচারে আনন্দ বোধ করে”। ( আল মুমিনুনঃ ২৩: ৩৫২-৫৩)
\r\n
আরও জোরালো ভাষায় অন্য এক স্থানে মানুষের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়া হয়েছেঃ
\r\n
‘মানুষেরা গোড়াতেই একই জাতি ছিল কিন্তু পরবর্তীকে তাতে নানা বিভিন্নতা সৃষ্টি করেছে। (সূরা ইউনুসঃ ১০: ২-১৯)
\r\n
কুরআনের এই যে শিক্ষা, সে সম্বন্ধে প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে- সে জ্ঞান কোন্ পর্যায়ের? তা’প্রয়োগলব্ধ, না অন্য কোন উপায় গৃহীত? তা কি সকল মানুষের পক্ষে সহজলভ্য? না, দুনিয়ার কয়েকজন সেরা প
\r\n
মানুষের পক্ষেই সে জ্ঞানলাভ সম্ভবপর? কুরআনের শিক্ষা কি অন্য উপায়ে পাওয়ার ব্যবস্থা নেই?
\r\n
কুরআনের জ্ঞান হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ) লাভ করেন বোধির১১২ মাধ্যমে। তাকে অন্যান্য বোধিলব্ধ জ্ঞান থেকে পৃথক করার উদ্দেশ্য বলা হয় প্রত্যাদেশ১১৩ । সে জ্ঞান প্রয়োগ১১৪ বা যুক্তি১১৫ বিরোধী নয়। সে জ্ঞানলাভ সকল মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। যেমন বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলোর আবিস্কার সকল মানুষের পক্ষে অসাধ্য। মানুষের জীবনকে সর্বাবস্থায় সুসামঞ্জস্য ও সুস্থ করার জন্য এ প্রত্যাদেশমূলক জ্ঞানের ছিল অত্যন্ত প্রয়োজন। তা থেকে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষ কিভবে তাকে নিয়ন্ত্র করবে, সে সম্বন্ধে রয়েছে স্পষ্ট নির্দেশ। তবে প্রত্যাদেশমূলক জ্ঞানের আর যে বিশেষ প্রয়োজন নেই, তা হযরত মুহাম্মদের (সঃ) বাণী থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়। মনীষী ইকবাল তাই উদাত্ত স্বরে ঘোষণা করেছেনঃ ইসলামের নবুয়ত তার পরিপূর্ণতা লাভ ক’রে আবিস্কার করতে সমর্থ হয় যে, তার বিলোপের রয়েছে একান্ত প্রয়োজন। এ আবিস্কার আর কিছু নয়, শুধু এ উপলব্ধি যে, জীবন চিরকাল নেতৃত্বের সূত্রে আবদ্ধ থাকতে পারে না- তার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভের জন্য মানুষকে তার স্বীয় শক্তির ওপরই নির্ভরশীল হতে হবে
\r\n
তাই স্পষ্ট বোঝা যায়, কুরআনের শিক্ষা গোড়াতেই মানুষকে বুঝতে দিয়েছিল যে, মানুষের পক্ষে আর প্রত্যাদেশ পাওয়ার প্রয়োজন নেই। মানুষকে তার প্রকৃতিদত্ত বিচারবুদ্ধি বা পঞ্চ ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের ওপর নির্ভর করতে হবে। তা’ থেকে আরও অবরোহ১১৩ বা deductions টেনে নেওয়া যায়; কুরআনের বাণীগুলো মানুষ গ্রহণ করেও তার বুদ্ধি ও বিচার বুদ্ধিকে কার্যকরী রাখতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, পবিত্র কুরআন মজিদে যেসব আদেশ-নির্দেশ প্রদত্ত হয়েছে সেগুলোও মানুষ তাদের বিচার-বুদ্ধির আলোকে যাচাই করে দেখতে পারে। তবে এ সম্বন্ধে মানুষের হতে হবে হুঁশিয়ার। কুরআনের আদেশাবলী এ দুনিয়ার যেমন কার্যকরী, এ দুনিয়ার পরবর্তী অপর এক দুনিয়ায়ও ফলদায়ক। কাজেই সে আদেশাবলীর মধ্যে যেগুলো কেবল এ দুনিয়ার কার্যকরী, তাদেরই বিচার সম্ভবপর। অপরগুলোর বিচার হতে পারে না। তার ওপর কুরআনের জ্ঞান প্রত্যাদেশ বলে সে জ্ঞানলাভ সম্বন্ধেও থাকতে হবে স্পষ্ট ধারণা।
\r\n
প্রত্যাদেশ এমন কোন অবাস্তব জ্ঞান নয়, যার সম্বন্ধে কোন কথা বলার কারও কোন অধিকার নেই। প্রত্যাদেশ বোধিরই এক সংস্করণ এবং বোধিলব্ধ জ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞানের জগতে ও মনোবিজ্ঞানে যথেষ্ট আলোচনা করা হয়েছে। কাজেই প্রত্যাদেশের সঙ্গে বোধির কি সম্বন্ধ এবং বোধি বাস্তবিকই জ্ঞানের এক পদ্ধতি কিনা, সে সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা করা দরকার।
\r\n
ইসলামের অবলম্বন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধ
\r\n
ইসলামী প্রত্যাদেশ থেকে আমরা সর্বপ্রথম পাই আল্লাহ্র ধারণা। ইসলামী চিন্তাধারার মূল সূত্র আল্লাহ্। কুরআন শরীফে আল্লাহ্র স্বরূপ সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা রয়েছে। আল্লাহ্কে সর্বপ্রথমে ধারণা করা হয়েছে সকল স্থিতির মূলরূপে। সূরা ফাতিহায় বলা হয়েছেঃ
\r\n
“ যত স্তুতি সবই তো আল্লাহ্র
\r\n
রব তিনি বিশ্বসমূহের”* (মরহুম মুনাওয়ার আলী কৃত অনুবাদ।)
\r\n
‘রব’ শব্দের অর্থ কেবল সৃষ্টিকর্তা নয়, ‘রব’ পালনকর্তা ও বিবর্তনকারীও বটে। ‘রব’ শব্দের অর্থ সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও বিবর্তনকারী।১১৭ অথচ, এই কুরআনেই অন্যান্য স্থানে তাঁকে সর্বব্যাপী সত্তারূপে১১৮, সর্বব্যাপী ও তুরীয় সত্তারূপে১১৯ ধারণা করা হয়েছে। আবার কোথাও কেবল জগৎ বহির্ভূত স্রষ্টারূপে১২০ ধারণা করা হয়েছে।
\r\n
আবার এই কুরআন শরীফেই আল্লাহ্র শরণ নেওয়ার জন্য আদেশ করা হয়েছে। সূরা ফাতিহায় আল্লাহ্ মানুষকে শিখিয়ে দিচ্ছেন প্রার্থনা করতেঃ
\r\n
সাহায্যের তরে যাচি
\r\n
কেবলই তোমারে,
\r\n
নেতা হয়ে আমাদের নিয়ে যাও
\r\n
ঋজু পথে পথে।** (মরহুম মুনাওয়ার আলী কৃত অনুবাদ।)
\r\n
কুরআন শরীফের সর্বত্রই মানুষের জন্য আল্লাহ্র অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা তাঁর শক্তির সাহায্য ব্যতীত মানবজীবনের ব্যর্থতা ঘোষণা করা হয়েছে।
\r\n
তা’হলে প্রশ্ন দাঁড়ায়, এর মধ্যে কোন্টি সঠিক ধারণা? তিনি রব্১২১ , না তিনি সর্বব্যাপী১২২,না সর্বব্যাপী ও তুরীয়১২৩ অথবা শুধু স্রষ্টা মাত্র? অপরদিকে গোড়াতেই যদি তাঁকে স্বীকার করে নেওয়া যায়, তা হলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের পক্ষে এক মস্তবড় প্রতিবন্ধক দেখা দেয়। এ স্বীকৃতি তো বিজ্ঞানের জয়যাত্রার পথে মস্তবড় প্রতিবন্ধক দেখা দেয়। এ স্বীকৃতি তো বিজ্ঞানের জয়যাত্রার পথে মস্তবড় বিঘ্নের সৃষ্টি করে মানব-মনকে করে তোলে গোঁড়া।১২৪ যদি আল্লাহ্র দ্বারাই জগতের সবকিছু নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহলে মানুষের পক্ষে কাজকর্ম করার বা জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনার কি প্রয়োজন? তাঁর দ্বারাই তো সবকিছু সুসম্পন্ন হচ্ছে ও হবে। আবার এই কুরআন শরীফেই মানুষকে কর্মপ্রেরণা দেয়া হয়েছে তীব্রভাবে।
\r\n
বলা হয়েছেঃ
\r\n
‘যে পর্যন্ত না কোন জাতি তাদের নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করে আল্লাহ্ ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের ভাগ্য পরিবর্তন করেন না’।
\r\n
কুরআনে বিজ্ঞানের গবেষণার জন্যও জোরালো তাগিদ দেয়া হয়েছেঃ ‘নিশ্চয়ই যে কোন সমস্যার সমাধান রয়েছে প্রত্যেক দুরূহতার জন্য প্রতিকার রয়েছে। তাই যখনই তুমি মুক্ত (অন্যান্য বিষয় থেকে ) তোমার ধ্যানকে তোমার প্রভু আল্লাহ্র দিকে কেন্দ্রিভূত করো__’।
\r\n
অন্য এক স্থানে বলা হয়েছেঃ
\r\n
‘ প্রভু যাকে ইচ্ছা তাকে হিকমত দান করেন এবং যারা হিকমত লাভ করে, তারা একটা পরম সুবিধা লাভ করে’।
\r\n
কুরআন শরীফের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার আল্লাহ্র রসূল (সঃ) জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঐকান্তিক সাধনার জন্য মানব জাতিকে উদাত্ত স্বরে আহ্বান করেছেন। তাঁর বিভিন্ন বাণী থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর আকুল আগ্রহের জাজ্বল্যমান প্রমাণ পাওয়া যায়।
\r\n
তিনি বলেছেনঃ
\r\n
‘শহীদের লোহু থেকে জ্ঞানীর দোয়াতের কালি অধিকতর পবিত্র’।* (Misbah us Sirat: Spirit of Islam Ameer Ali, p.361)
\r\n
এক ঘণ্টার জন্যও বিজ্ঞানের পাঠ শ্রবণ ও জ্ঞানের অনুশীলন হাজার শহীদের জানাযাতে শামিল হওয়ার চেয়ে পূণ্যতর – হাজার রাত্রির নামাযের কাতারে দাঁড়ানোর চেয়ে পুণ্যতর কাজ’।
\r\n
বারবার জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলনের জন্য তিনি প্রেরণা দিয়েছেনঃ
\r\n
জ্ঞানী ব্যক্তির বাণী শ্রবণ এবং হৃদয়ে বিজ্ঞান পাঠের আলোকসম্পাত ধর্মীয় কার্যাবলি থেকে উৎকৃষ্টতর- কৃতদাসের মুক্তি দেয়ার চেয়েও উন্নততর।** (Spirit of Islam: Ameer Ali)
\r\n
ইসলাম জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী হযরত আলী (রাঃ) বলেছেনঃ
\r\n
‘বিজ্ঞানের (অনুশীলনে) সম্মান লাভ সবচেয়ে বড় সম্মান। সে জ্ঞানের ক্ষেত্রে জীবন সঞ্চার করে সে অমর’।
\r\n
বিজ্ঞানের জগতে কিন্তু আরোহ পদ্ধতিই১২৫ একমাত্র পন্থা। অতি ক্ষুদ্র, অতি তুচ্ছকে উপকরণ বা দড়ি১২৬ রূপ গ্রহণ করে তার ভিত্তিতে সার্বিক সত্যে এসে উপনীত হওয়া বিজ্ঞানের লক্ষ্য। বিজ্ঞানে অবরোহ১২৭ পদ্ধতি মোটেই গ্রহণীয় নয়। কোন কিছুকে গোড়াতে স্বীকার করে তা’ থেকে ফলাফল অবরোহ১২৮ করা বিজ্ঞানে জগত অচল।
\r\n
তাই প্রশ্ন দাঁড়ায়, আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণার মধ্যে কিভাবে সঙ্গতি১২৯ আনা যায় আর আল্লাহ্র ধারণার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কিসে খাপ খেতে পারে? কুরআন শরীফে আল্লাহ্কে ধারণা করা হয়েছে প্রথমে স্বতঃসিদ্ধরূপে১৩০ তার পরে সৃষ্টিকর্তা১৩১ সর্বব্যাপী১৩২ এবং সর্বব্যাপী ও তুরীয়১৩৩ শক্তিরূপে ধারণা করা হয়েছে। আল্লাহ্কে এভাবে ধারণা না করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষ অগ্রসর হতে পারে না বলেই ধারণাগুলোর প্রয়োজন ছিল। তাঁকে চিন্তার স্বতঃসিদ্ধ১৩৪ রূপে গ্রহণ করে চিন্তার পরিণতিতে তাঁকে সৃষ্টিকর্তা, সর্বব্যাপী ও তুরীয় সত্তারূপে ধারণা করার ইঙ্গিত রয়েছে পবিত্র কুরআন শরীফে। আল্লাহ্র এ নানাবিধ ধারণা মানব-চিন্তার বিভিন্ন পর্যায়ের ফল। মানব মন অন্বেষণের প্রারম্ভে এ জগতের জ্ঞেয়তা১৩৫ এবং জ্ঞাতার শক্তির ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে বাধ্য হয়। এ বিশ্বাস কেবল আল্লাহ্র অস্তিত্বের ওপর প্রত্যয়ের ফলেই সম্ভব হয়। এ প্রত্যয়ে বলীয়ান হয়ে অন্বেষণকারী তার জ্ঞান অনুযায়ী আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণায় পৌঁছতে সমর্থ হয় এবং তা নির্ভর করে তার অভিজ্ঞতা১৩৬ ও যুক্তির ওপর। সাধারণ বুদ্ধির অন্বেষণকারী পক্ষে আল্লাহ্কে সৃষ্টিকর্তারূপে গ্রহণ করাই সহজ। মননধর্মী তত্ত্বজ্ঞানী তাঁকে সর্বব্যাপীরূপে১৩৭ গ্রহণ করেন। তত্ত্বজ্ঞান ও নৈতিক জীবনের মানগুলোর সমন্বয় সাধনের জন্য তাঁকে ধারণা করা হয় সর্বব্যাপী ও তুরীয়রূপে। উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিস্কার হয়ে পড়বে। এ দুনিয়ার নানা কলাকৌশলের নিদর্শন দেখে মনে হয় এতে নিশ্চয়ই কোন কারিগরের হাত রয়েছে। কাজেই তাঁরা মনে করেন এতে এক জগৎ বহির্ভূত কারিগর রয়েছেন।
\r\n
মননধর্মী মানুষ এতে দেখতে পান ন্যায়শাস্ত্রের নানানীতির প্রকাশ। মানব মন ন্যাশাস্ত্রের যে রীতি অনুসারে দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে এক ধারণায় পৌঁছে স্বস্তি লাভ করে, তেমনি জগতের মাঝেও চলেছে এক মহাদ্বন্দ্বের লীলা। আল্লাহ্কে সর্বব্যাপী মূলাধররূপে ধারণা করলেই জগতের এ মহাদ্বন্দ্বের মীমাংসা হতে পারে। কাজেই এঁরা আল্লাহ্কে ধারণা করেন সর্বব্যাপী সত্তারূপে।* ( এ সম্বন্ধে দর্শনশাস্ত্রে শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাওয়া যায়-হেগেলীয় Pan logism-এ এবং হেগেলের ইংরেজ শিষ্য ব্রাডলির সিদ্ধান্তে।)
\r\n
আল্লাহ্ সর্বব্যাপী সত্তা বলে গৃহীত হলে দুনিয়ায় পাপ-পুণ্যের আর কোন বিচার থাকে না। তিনি সর্বমূলাধার অস্তিত্ব হওয়ায় পাপ-পুণ্য সমস্তই তাঁর সত্তা থেকে সৃষ্টি হয়। কাজেই ধর্মীয় ও নৈতিক জীবনের মানগুলোর সঙ্গে তর্ক-বুদ্ধিজাত জ্ঞানের সমন্বয় সাধন করে ওরা বলেন, সর্বব্যাপী মাত্র নয়, জগতের বাইরেও তাঁর সত্তা রয়েছে সেজন্য তিনি এসব পাপ-পুণ্যের অতীত।
\r\n
মানবজীবনের সকল পর্যায়ের সঙ্গে কুরআন শরীফের গভীর যোগ থাকার জন্যই আল্লাহ্কে বিভিন্নভাবে ধারণা করা হয়েছে, যাতে সকল স্তরে এবং সকল পর্যায়ের মানুষই এ থেকে শান্তি ও স্বস্তি পেতে পারে। কুরআন শরীফে আল্লাহ্ সংক্রান্ত বিভিন্ন ধারণা তাই পরস্পরবিরোধী নয় বরং মানব-জ্ঞানের পক্ষে উপযোগী করেই তাদের পরিবেশন করা হয়েছে।
\r\n
তেমনি আল্লাহ্কে স্বতঃসিদ্ধ১৩৮ হিসেবে গ্রহণ করেও বিজ্ঞানের পথে কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয় না। বরং আল্লাহ্র এ ধারণাকে গ্রহণ না করলে অন্বেষণকারীর পক্ষে জ্ঞানের ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনা নেই।
\r\n
আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তিস্বরূপ যেসব ন্যায়শাস্ত্রের নীতি বর্তমান, সেগুলোর আলোচনা করলেই বিষয়টি আরও পরিস্কার হবে।
\r\n
জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভিত্তি তর্কশাস্ত্র। তর্কশাস্ত্রের বুনিয়াদের উপরই বিজ্ঞান গড়ে তুলেছে তার সৌধ। যা ন্যায় অনুমোদিত নয়, তা কিছুতেই বিজ্ঞানের সম্মান লাভ করতে পারে না। যে ন্যাশাস্ত্রের স্বতঃসিদ্ধ রূপে চারটি নীতি গোড়াতেই গ্রহণ করা হয়, তাদেরকে যথাক্রমে একত্বের নীতি১৩৯ , দ্বন্দ্বের নীতি১৪০ , মধ্যপন্থা অর্জনের নীতি১৪১ ও যথাযোগ্য কারণের নীতি১৪২ বলা হয়।
\r\n
একত্বের নীতিতে বলা হয়, জ্ঞানের রাজ্যে জ্ঞেয় বিষয়কে এককরূপে ধরে নেওয়া দরকার। কারণ জ্ঞেয় বিষয় সবসময়ই তার স্বরূপ অক্ষুণ্ণ রাখে। যেমন কোন গাছ সম্বন্ধে ভাবতে গেলে তাকে একক হিসেবেই ভাবতে হবে। যদি গাছকে এক না ভাবা যায় তাহলে তার সম্বন্ধে কোন কিছু বলার কোন অর্থ থাকে না। কাজেই সে গাছ সম্বন্ধে কোন চিন্তা করতে হলে বা তার সম্বন্ধে কোন যুক্তি-তর্কের অবতারণা করতে হলে তাকে সব সময়ই এক সত্তারূপে ধরে নিতে হবে।
\r\n
অথচ জগতের সর্বত্র দেখা যায় পরিবর্তন১৪৩। যে গাছে একদা মাত্র দুটো পল্লব দেখা দিয়েছিল, কালে তা-ই নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে মহামহীয়ান বৃক্ষরূপে ঊর্ধ্বে মাথা তুলে অসংখ্য পাখির আবাসে পরিণত হয়। আবার কালের করাল গতিতে সেই গাছই জীর্ণ হয়ে পত্রবিহীন, শাখাবিহীন কিম্ভূতকিমাকাররূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এ গাছের উৎপত্তি ও বিকাশের ধারায় মুহূর্তে মুহূর্তে নানাবিধ পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে। তার বিভিন্ন বয়সের ভিন্ন ভিন্ন ফটোগ্রাফ একত্র করলে দেখা যাবে, তাতে কত পরিবর্তন হয়েছে। তা সত্ত্বেও গাছের মধ্যে এমন একটা শক্তি১৪৪ কাজ করেছে, যার কার্যকারিতায় পরিবর্তনের মধ্যেও রয়েছে এক ঐক্য। সেজন্যই এতসব পরিবর্তনের মধ্যেও তাকে একই গাছেরূপে আমরা পরিচিত করতে পারি। কাজেই আমাদের ব্যবহারিক জীবনে বা মনকে তার সম্বন্ধে আলোচনায় তার পরিবর্তনকে উপেক্ষা করে, একত্বকেই গ্রহণ করতে হয়। অপরদিকে যে মানসে গাছ সম্বন্ধে কোন ধারণার সৃষ্টি হয় তাতেও মিনিটে মিনিটে দেখা দিচ্ছে পরিবর্তন। সেও চলেছে বিকাশের পথে। তাতেও দেখা দিচ্ছে নতুন নতুন রূপ। তবু মনের এত সব পরিবর্তনের মধ্যেও যদি তার ঐক্য স্বীকার করা না যায় তাহলে গাছ সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণার তুলনা করার জন্য কোন ঐক্যসূত্র না থাকলে কোন কথা বলারই অবকাশ থাকে না। পরিবর্তনকে মানব-মনের সত্যিকার রূপ বলে ধরে নিলে, মানব মন বলে কোন কিছুই থাকে না। বিভিন্ন সংবেদনের১৪৫ উৎপত্তিও লয়ের ফলে তাতে দেখা দিচ্ছে ছায়াচিত্রের মত ভাবধারার উদয় ও অস্ত, তাদের কারো সঙ্গে কারোর কোন যোগসূত্র নেই। সেইজন্য জ্ঞানের ক্ষেত্রে মানব মনকে ‘এক’ বলে ধরে নিতে আমরা বাধ্য এবং তাতে একটা একীকরণের১৪৬ শক্তি১৪৭ কার্যকরী বলে ভাবা অনিবার্য হয়ে পড়ে।
\r\n
কাজেই, আমাদের ধরে নিতে হবে-ভাববার বিষয় ও ভাববার শক্তিকে নির্বিকাররূপেই ভাবতে হবে। একেই ন্যাশাস্ত্রে ঐক্যের নীতি১৪৮ বলা হয়। এ নীতির স্বীকৃতি ব্যতীত আমাদের ভাববার বা যুক্তির অবতারণা করবার অধিকার থাকে না।
\r\n
দ্বন্দ্বের নীতিতে১৪৯ বলা হয়, কোন বস্তু বা বিষয় সম্বন্ধে ভাবতে গেলে তাতে পরস্পরবিরোধী১৫০ গুণের সমাবেশ করা যায় না। কোন বস্তুকে স্থিতিশীল১৫১ ও অস্থিতিশীল১৫২ বলে আমরা ভাবতে পারি না। কোন বস্তুকে একই সঙ্গে কালো ও কালো নয় রূপে ভাবা মানব-মনের পক্ষে অসম্ভব।
\r\n
মধ্যপন্থা বর্জনের নীতিতে১৫৩ বলা হয়, কোন বস্তুতে যেমন পরস্পরবিরোধী দুটো গুনের১৫৪ সমাবেশ ভাবা অসাধ্য, তেমনি পরস্পরবিরোধী দুটো গুণের বহির্ভূত অন্য কোন মধ্যবর্তী গুণ থাকাও কোন বস্তুতে সম্ভব নয়। রঙের দিক থেকে বিচার করলে যে কোন বস্তুই, হয় কালো না হয় কালো-নয়ই, হবে। এ দুটো গুণের বাইরে রঙের জগতে আর কিছুই নেই।
\r\n
এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, দ্বন্দ্বের নীতি বা মধ্যপন্থা বর্জনের নীতি ঐক্যের নীতির ওপর নির্ভরশীল। ভাববার বিষয় যদি তার ঐক্য বজায় রাখতে না পারে, তা হলে তার মধ্যে পরস্পরবিরোধী গুণ থাকা না থাকার কোন মানে হয় না। আমাদের চিন্তার বিষয়১৫৫ এক থাকে বলেই তাতে পরস্পরবিরোধী গুণাবলির সমাবেশ করা যায় না বা পরস্পরবিরোধী গুণের একটিকে তাতে আরোপ করতে হয়। যদি বিষয়বস্তু বলে কোন কিছুরই অস্তিত্ব না থাকে, তাহলে পরস্পরবিরোধী গুণের সমাবেশ বা তাদের কোনও একটি গ্রহণ বা বর্জনের প্রশ্নই ওঠে না। তাহলে দেখা যায়, একত্বের নীতির১৫৬ মৌলিক নীতি। প্রয়োগের জন্য স্বীকার করতে হয় দ্বন্দ্বের নীতি বা মধ্যপন্থা বর্জনের নীতিকে।
\r\n
যথাযোগ্য কারণের নীতিতে১৫৭ বলা হয়, জগতের যা কিছু ঘটেছে বা রয়েছে তার জন্য একটা উপযুক্ত কারণ আছে। এ জগৎ যদি খাপছাড়া হত, এতে যদি সবকিছুই স্বতঃউৎসারিত হত তাহলে এর স্থিতি সম্বন্ধে বা এর অন্তর্গত তার কারণ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা হত অসম্ভব। কোন বিষয়কে জানার অর্থ তার কারণ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ সম্ভব হয়। একেই ন্যায়শাস্ত্রের আরোহ বিভাগে বলা হয় কারণের নীতি। এ কার্যকারণের নীতিকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করলে একে প্রকৃতির সমরুপতা রূপেই গ্রহণ করতে হয়। প্রকৃতিতে কার্যকারণের সূত্র রয়েছে সত্য। দুনিয়ার সকল কিছুই এই কারণের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় কিন্তু কার্যকারণের মধ্যে বা গোটা পৃথিবীর মধ্যে যদি সমরূপতা না থাকে; তাহলে কেবল কারণ দ্বারা কোন কিছুর ব্যাখ্যা করা যায় না।
\r\n
কারণের নীতিতে বলা হয়-জগতে যা কিছু আছে বা ঘটেছে, তার মূলে রয়েছে একটা কারণ। একজনের হাত যদি পুড়ে যায় তাহলে আগুনকেই বলতে হবে তার কারণ। কিন্তু যদি মানুষ ও আগুন উভয়েরই প্রকৃতি বদলে যায় তাহলে আজকে পোড়ার কারণ আগুন হলেও অনাগতকালে তা আর কারণ থাকবে না। মানুষের শরীরের উত্তাপ যদি আগুনের উত্তাপ থেকে আরও বেড়ে যায়, তাহলে আগুনের স্পর্শে জ্বালা-যন্ত্রণা পাওয়া দূরের কথা, হয়ত চন্দনের প্রলেপের সুখ অনুভব করতে পারে অথবা যদি আগুন তার দাহিকা শক্তি হারায়, তাহলেও তার স্পর্শে বর্তমানেও আমরা আর জ্বালা-যন্ত্রণা পাবো না। তাহলে দাহিকা ও আগুনের মধ্যে যে কার্যকারণের সম্বন্ধে তাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে ভাবতে হবে, তাদের প্রকৃতি বদলায় না। তারা চিরদিনই এক এবং অবিকৃত থাকলেই তাদের কার্যকারণ সম্বন্ধে অব্যাহত থাকতে পারে। ন্যায়শাস্ত্রে তাকে বলা হয় Uniformity of essence অথবা সারের সমরূপতা।
\r\n
দ্বিতীয়ত-আগুন ও উত্তাপের প্রকৃতি চিরকাল অবিকৃত থাকলেও বর্তমানে তাদের যে সম্বন্ধ তাই বা কেমন করে অব্যাহত থাকবে? আমরা কি ভাবতে পারি না-আজকে না হয় কোন বস্তুতে আগুন দিলে দেখা যায় তা’ জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে যায়-আগুন ও দাহিকার সম্বন্ধে তাই বলে কি চিরদিন অব্যাহত থাকবে? ভবিষ্যতে তাদের এ কার্যকারিতার সম্বন্ধে তো নাও থাকতে পারে।
\r\n
তার জন্য আমাদের স্বীকার করে নিতে হয় যে, তাদের ব্যবহারিক দিকের কোন পরিবর্তন হয় না। আজ তারা যেভাবে কাজ করে যাচ্ছে অনাগত ভবিষ্যতে বা চিরদিনই তাদের স্বভাবে এ ব্যবহার প্রকাশ পারবে। একেই বলা হয় ব্যবহারের সমরূপতা।
\r\n
তাহলে আমাদের চিন্তাধারার জন্য এবং বৈজ্ঞানিক বা ব্যবহারিক জীবনের ব্যাখ্যার জন্য শেষ পর্যন্ত দুটো নীতির স্বীকৃতিই অবশ্য গ্রহণীয়। একত্বের নীতি১৫৮ ও প্রকৃতির সমরূপতা নীতি১৫৯ না মেনে নিলে চিন্তাও চলে না, কোন গবেষণাও চলতে পারে না।
\r\n
অথচ এ দুটোর কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব নয়। কারণ এগুলোর ব্যাখ্যা দিতে গেলেই এগুলোকে গ্রহণ করে নিতে হবে। তাতে ন্যায়শাস্ত্রের ভাষায় Petitio principal হয়ে যাবে।
\r\n
তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে, এ দুটো নীতির পশ্চাতেও রয়েছে আরও দুটো স্বতঃসিদ্ধ। একত্বের নীতিতে বলা হয়, কোন বস্তু বা বিষয় তারই মত। তাকে সাংকেতিকভবে প্রকাশ করা হয় ক=ক। অর্থাৎ বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্যেও ‘ক’ নামক বিষয়ের মধ্যে রয়েছে এক ঐক্য। এ ছাড়া আমরা ‘ক’ সম্বন্ধে কোন বিষয় ভাবতেও পারি না এবং বলতেও পারি না। যেহেতু পারি না, তাই আমদের ধরে নিতে হবে ‘ক’ নামক বিষয়ের বিভিন্ন পরিবর্তনকে তুচ্ছ করে তার একত্বকেই আমাদের গ্রহণ করতে হবে।
\r\n
সমরূপতা নীতিতে১৬০ আমারা স্বীকার করে নিচ্ছি, পৃথিবীর সর্বত্র রয়েছে সমরূপতা১৬১ , কোন বস্তু বা শ্রেণী তার প্রকৃতি বদলায় না এবং দুটো বিষয়ের মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ স্থাপিত হলে তার মধ্যেও কোন ছেদ হয় না।
\r\n
এখানে ভেবে দেখবার বিষয় এই যে, আমরা চিন্তা করতে বা তর্কশাস্ত্রে অগ্রসর হতে পারি না বলে কেন এই নীতিকে গ্রহণ করবো? না হয় না-ই ভাবলাম, না-ই তর্ক করলাম, তাতে কি যায় আসে? জ্ঞানের রাজ্যের কার্যকারণ আবিস্কার না করলে হয়ত আমাদের অগ্রসর হওয়ার পথ নেই। তাতে এমন কি হল? না-ই বা অগ্রসর হলাম!
\r\n
কিন্তু মানব-মন তাতে আশ্বস্ত হয় না। সে গোড়াতেই ধরে নেয়- এ জগৎ জ্ঞেয়১৬২ এবং মানুষ হিসাবে আমরা সকলেই জ্ঞাতা১৬৩ । মানবমন জ্ঞান অন্বেষণের আদিতেই স্বীকার করে নেয়, এ জগৎ কোন দুর্বোধ্য পুঁথি নয় এবং তাকে জানবার শক্তি মানুষের মধ্যে রয়েছে। কাজেই এটাই জ্ঞানের রাজ্যে আদিম নীতি, এটাই সবচেয়ে বড় স্বতঃসিদ্ধ। যদিও আমরা আপাতত এ স্বতঃসিদ্ধ সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল নই, তবুও জ্ঞানের রাজ্যে একে গ্রহণ করেই আমরা অগ্রসর হই।
\r\n
অপরদিকে জ্ঞানের চরম পরিণতিতে আবার এসে চরম ঐক্যে পৌঁছার প্রবৃত্তিও রয়েছে মানুষের মনে। সকল বিশৃঙ্খলা, সকল বৈসাদৃশ্যের অন্তরালেও মানুষ আবিস্কার করতে চায় এক চিরন্তন নিয়ম, এক চরম শৃঙ্খলা প্রবণতা যদি স্বতঃসিদ্ধ নয়, তবুও তাকে মানব-মনের এক বিশেষ ঝোঁক বলতে হবে।
\r\n
বিজ্ঞান ও দর্শনের ইতিহাসে রয়েছে তার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত। ভাববাদ বা জড়বাদে জগতের আদি সত্তারুপে স্বীকার করে নেয়া হয় এক আদি নীতি। ভাববাদী দর্শনে সাধারণত জ্ঞানের পদ্ধতিরুপে স্বীকার করে নেয়া হয় যুক্তিকে। সে যুক্তির ধারার দ্বন্দ্বের ফলে অবশেষে উপস্থিত হতে হয় পরম ব্রহ্মে। তার উদাহরণস্বরূপ রয়েছে হেগেলীয় দর্শন। জড়বাদে জগতের আদি উপকরনরূপে স্বীকার করে নেয়া হয় কতকগুলো অবিভাজ্য অণুকে। জড়বাদী দর্শনে জ্ঞানের একমাত্র পদ্ধতি ভূয়োদর্শন অথবা ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান। সে জ্ঞানের আলোকে জগতের সব বস্তুর বিশ্লেষণ করলে ধরা পড়ে চেতনাহীন, সমগুণ বিশিষ্ট অণু ও পরমাণুর খেলা।
\r\n
বহুবাদের বিভিন্ন রূপ থাকা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে রয়েছে এক ঐক্য। লাইবনিটজের১৬৪ বা জেমসের১৬৫ মধ্যেও রয়েছে সাদৃশ্য। লাইবনিট্জ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন তাঁর স্বতন্ত্র monad১৬৬ গুলোর মধ্যে রয়েছে এক সংস্থা১৬৭ ও ঐক্য১৬৮ ,কারণ তাদের মধ্যে সমগ্রের রূপ প্রতিভাত হয়। তারা যুক্তিসঙ্গত নীতি দ্বারা পরিচালিত এবং তাদের প্রত্যেকের মধ্যেই সেই যুক্তিসঙ্গত সংস্থা এক বিশেষ দিকে বা বিশেষ স্তরে প্রতিবিম্বিত হয়।* (Patrick: Introduction to Philosophy,p.228)
\r\n
উইলিয়াম জেম্স্ বস্তুর বা বিষয়ের স্বাতন্ত্র্যের১৬৯ ওপর গুরুত্ব আরোপ করে নিয়ম ও শৃঙ্খলা পশ্চাৎভূমিতে ঠেলে দিয়ে বলেছেন, নিয়ম জাগতিক অভ্যাস, জীবনের পদ্ধতি ব্যতীত আর কিছুই নয়। বস্তুগুলো একত্র জড়ো হয়েছে আকস্মিকভাবে এবং তাদের স্ব-ইচ্ছায়ই একত্র আছে-তারাই নিয়মগুলো সৃষ্টি করেছে। যেমনভাবে পরস্পরের মিলনের জন্য সাম্প্রদায়িক নিয়ম গঠিত হয় তেমনি তারা নিয়ম গঠন করেছে১৭০। ** ( William James: The Will to Believe.) কিন্তু তারপরেই আবার বলেছেন, ‘সেই স্বতঃউৎসারিত স্বতন্ত্র সত্তাগুলোর সমষ্টির অভ্যাসের ফলেই প্রাকৃতিক নিয়মাবলির উৎপত্তি হয় এবং সে স্বতন্ত্র সত্তাগুলো এ সব নিয়ম থেকে অধিকতর বাস্তব১৭১ । কাজেই তাদের যে সমষ্টিগত অভ্যাস থেকে জগতের নিয়ম ও শৃঙ্খলার উৎপত্তি হয়, তাকে তিনি অস্বীকার করতে পারেননি। সুতরাং শত অস্বীকার করলেও সকল চিন্তার পরিণতিতেই মান-মন নিয়ম, শৃঙ্খলা ও সংস্থা আবিস্কার করতে বাধ্য হয়।
\r\n
তা’হলে স্পষ্টই বোঝা যায়, জ্ঞানের রাজ্য চলছে চক্রাকারে। ঐক্যের নীতি সমরূপতার নীতিকে স্বতঃসিদ্ধরূপে গ্রহণ করে জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ করে।অনুসন্ধানের পরিণতিতে মানব-মনে এসে পৌঁছায় সেই নিয়ম-শৃঙ্খলা বা একত্বের নীতিতে।
\r\n
স্বতঃসিদ্ধের আলোচনায় আমরা পূর্বেই দেখেছি, সর্ব-মূলাধার স্বতঃসিদ্ধ হচ্ছে জ্ঞাতার শক্তির উপর ও জ্ঞেয়তার উপর বিশ্বাস এবং যেহেতু বিজ্ঞান বা দর্শন সেই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের সম্বন্ধে বিশ্বাসের ওপর নির্ভরশীল। বিজ্ঞান ও দর্শন আজও স্বতঃসিদ্ধের কোন প্রমাণ দিতে পারেনি। এগুলো ব্যতীত জ্ঞানের চর্চা চনে না বলে এগুলোকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। ইসলাম ধরে নিয়েছে জ্ঞাতার পক্ষে জ্ঞেয় সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ সম্ভবপর, যেহেতু উভয়ে একই কারণ থেকে উদ্ভূত। তাদের উভয়েরই উৎপত্তি একই আল্লাহ্ থেকে। আল্লাহ্ স্থিতির মূল উৎস বিধায় তাঁরই কার্যকারিতার ফলে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মধ্যে এ মিলন সম্ভবপর। ইসলামী চিন্তাধারায় তাই আল্লাহ্কে স্বতঃসিদ্ধের ভিত্তিরূপেই গ্রহণ করা হয়েছে।
\r\n
মানব-মন যে স্বাভাবিক প্রবণতার ফলে স্থিতির১৭২ মূলে আবিস্কার করে চরম ঐক্য ও শৃঙ্খলা, ইসলাম সেই শৃঙ্খলা ও ঐক্যকে মানব-মনের প্রতিভাস বলে মনে করেনি। আল্লাহ্র অস্তিত্বের ওপর বিশ্বাস করার ফলে এবং সেই ঐক্যও যে জগতের আদি সত্তায় বর্তমান তার ভিত্তি সুদৃঢ় করেছে। আল্লাহ্র অস্তিত্বে বিশ্বাস বা কুরআন শরীফের বাণীতে আস্থা স্থাপন, জ্ঞান অন্বেষণের পথে তাই বিঘ্ন নয় বরং জ্ঞানের পথকে সুগম করে-তার ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে।
\r\n
এ দুনিয়ার সমস্ত কিছুর জ্ঞান মানবের পক্ষে সম্ভবপর; জ্ঞানের পথে মানুষের কোন প্রতিবন্ধক নেই- জ্ঞানের চরম পরিণতিতে মানুষ আবিস্কার করবে নিয়ম-শৃঙ্খলা- এটাই ইসলামী জীবন-দর্শনের গোড়ার কথা।
\r\n
বৈজ্ঞানিক গবেষণার আরোহ পদ্ধতিকে১৭৩ গ্রহণ তাই ইসলামের দৃষ্টিতে বর্জনীয় নয় বরং তার মূলকে দৃঢ় করার ভিত্তিস্বরূপ। আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তিরূপ যেমন একত্বের নীতি১৭৪ বা সমরূপতা নীতি১৭৫ অবশ্য গ্রহণীয়, তেমনি জ্ঞাতা১৭৬ এবং জ্ঞেয়ের১৭৭ সম্বন্ধ স্বীকারও অবশ্য প্রয়োজনীয়। পরবর্তী নীতি স্বীকার করে নিলে আমাদের অবশ্যই মেনে নিতে হয়, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে মৌলিক ঐক্য। সে মৌলিক ঐক্যের স্বীকৃতি ব্যতীত আমাদের পক্ষে এক পা অগ্রসর হওয়ার সাধ্য নেই। ইসলামী চিন্তাধারায় তাই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মৌলিক ঐক্যস্বরূপ আল্লাহ্র অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে।
\r\n
বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার আলোচনায়ও আমরা দেখতে পাই মানব মন তার সকল চিন্তার পরিণতিতে এসে পৌঁছায় এক ঐক্যে। সে ঐক্য জড় বা চৈতন্যময়-দু’ই হতে পারে। তাকে জড়বস্তু বলে ধারণা করলে আমাদের মানসে দেখা দেয় নানাবিধ দ্বন্দ্ব- নৈতিক ও উচ্চতর মানগুলো তাতে কোন ভিত্তি খুঁজে পায় না। অপরদিকে কার্যকারণ পরস্পরা নীতির১৭৮ সুষ্ঠু ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। মানব-মনের বিভিন্ন চিন্তা নীতি ইত্যাদি বোধঃ শক্তিহীন জড়পদার্থ থেকে উৎপন্ন হলে আমাদের স্বীকার করতে হয়, আদিতে কারণে কোন গুণ না থাকলেও কার্যে যেসব গুণের উৎপত্তি হতে পারে। অথচ কার্যকারণের নীতিতে বলা হয় শূন্য থেকে শূন্যই আসে১৭৯ । সে নীতিকে কার্যকরী রাখতে হলেও আমাদের ধরে নিতে হয়, যদিও জড় বলে জগতের আদি সত্তা আমাদের ইন্দ্রিয়ের কাছে প্রতিভাত হয়, যদিও জড় হলে জগতের যাবতীয় সম্পদ তা সে মননধারারই হোক বা সামাজিকই হোক, উহ্য রয়েছে। সমাজ বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে তারা বাহ্য হয়ে পড়ে।
\r\n
ইসলাম তাই কুরআনের ভাষায় মানুষের চোখে আঙ্গুল দিয়ে এ জগতের আদি কারণকে চৈতন্যময় সত্তারুপে নির্দেশ করেছে। ইসলামের নিকট তাই আল্লাহ্র অস্তিত্ব একাধারে স্বতঃসিদ্ধ১৮০ ও মানব চিন্তার চরম পরিণতি। আল্লাহ্র অস্তিত্বের স্বীকৃতি ব্যতীত জ্ঞানের পথে মানুষ এক তিল অগ্রসর হতে পারে না। অপরদিকে আল্লাহ্র অস্তিত্ব মানুষের জ্ঞানের চরম পরিণতি। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনায় মানুষ সর্বশেষে তাঁরই অস্তিত্বে আস্থা স্থাপন করে স্বস্তিলাভ করে।
\r\n
বিজ্ঞানের প্রাথমিক ভিত্তির আলোচনায়ও আমারা দেখেছি একত্বের নীতি, সমরূপতার নীতি প্রভৃতি মৌলিক নীতিকে স্বীকার করে চিন্তার পরিণতিতে মানুষ আবার এ দুনিয়ার মধ্যে এক চরম ঐক্য আবিস্কার করে। ইসলামী চিন্তাধারার মূলসূত্র আল্লাহ্র অস্তিত্বের স্বীকৃতি তাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের পক্ষে প্রতিবন্ধক নয় বরং প্রেরণাদানকারী।
\r\n
আল্লাহ্র অস্তিত্বের প্রশ্ন
\r\n
‘আল্লাহ্ আছেন কি না’- প্রশ্নটি মানব জীবনে নতুন নয়। মানব মনের চিন্তার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে এ সম্বন্ধে মানুষ ভেবেছে, এখনও ভাবছে। এ প্রশ্নের উত্তর আল্লাহ্র সংজ্ঞার ওপরই নির্ভর করে। আল্লাহ্ বলতে যদি আমরা চতুর্দশ লুই বা হিটলারের মত এক প্রচণ্ড শক্তিশালী দণ্ডধর বা আসমানের অধীশ্বর বলে কল্পনা করি, তাহলে তাঁর অস্তিত্ব কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। আল্লাহ্ বলতে যদি মনে করা হয়-সদ্,চিদ্ ও আনন্দ স্বরূপ এক বিশ্ব-সত্তা, তাহলে জ্যামিতিক প্রমাণ না দেওয়া গেলেও একটা গ্রহণযোগ্য প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে।
\r\n
সাধারণত আল্লাহ্ বলতে আমরা বুঝতে পারি এ বিশ্বের স্রষ্টা পরম মঙ্গলময়, পরম বুদ্ধিমান, সর্বগুণাধার, বিশ্বের সকল বস্তুর নিয়ামক এক শক্তি। আল্লাহ্র এবং বিধ ধারণার পোষকতায় দর্শনশাস্ত্রে তিনটে প্রমাণ পেশ করা হয়েছে।
\r\n
আমাদের জাগতিক অভিজ্ঞতায় আমরা দেখতে পারি, জগতে যা কিছু ঘটে তার মূলে রয়েছে একটা কারণ। কারণ ব্যতীত কোন কার্যের উৎপত্তি হয় না। তাই আমরা ভাবতে বাধ্য হই, নিশ্চয়ই এ বিশ্ব-সৃষ্টির মূলে রয়েছে একটা বিরাট কারণ। কার্যকারণ-পরস্পরা-সূত্রের অমোঘতা স্বীকার করে নিলে তখন প্রশ্ন দাঁড়ায়, সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টির মূলে কার কার্যকারিতা বিদ্যমান? দর্শনশাস্ত্রে তাই এই স্রষ্টা তত্ত্ববিষয়ক প্রমাণের১৮১ উপর কোন বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়নি।
\r\n
দ্বিতীয় প্রমাণস্বরূপ বলা যায়, দুনিয়ার সর্বত্র রয়েছে বুদ্ধি ও করুণার নিদর্শন, তাতে প্রমাণিত হয় দুনিয়ার সৃষ্টির মূলে রয়েছে এক পরম মঙ্গলময়ের হস্ত। মানব জীবনের নানা ঘটনা থেকেই বুঝতে পারা যায়, এতে রয়েছে এক মহান উদ্দেশ্য। সন্তানের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই মায়ের বুকে দুধ সঞ্চিত হয়। যদি তা না হত, তাহলে পৃথিবীর এতগুলো শিশু আহারের অভাবে অকালে মারা যেত। অবুঝ ইতর প্রাণীদের মধ্যে যদি অপত্য স্নেহ না থাকত তাহলে সদ্যোজাত বাচ্চাগুলো শত্রুর আক্রমণে জন্মের সঙ্গে-সঙ্গেই লয় পেত। এতে প্রমাণ পাওয়া যায়, জীবের বিকাশের জন্য উপায়স্বরূপ১৮২ জনক-জননীর বুকে এই স্নেহ কেউ গোড়াতেই ঢেলে দিয়েছেন। এই যুক্তিকে দার্শনিক পরিভাষায় বলা হয় ধর্মতত্ত্বমূলক যুক্তি১৮৩। তার বিরুদ্ধে বলা যায়-দুনিয়ার সর্বত্র লক্ষ্য ও উপায় সুসামঞ্জস্য নেই। অনেকগুলো জীব পিতামাতার যত্নের অভাবে অকালে মারা যায়। অনেকগুলো পরিবেশের সঙ্গে যুদ্ধে লোপ পায়। আবার অনেকগুলোর জন্য পর্যাপ্ত আহারের ব্যবস্থা নেই।
\r\n
জীব-জগৎ ব্যতীত দুনিয়ায় অনেকগুলো জরা-ব্যাধি, প্রাকৃতিক উৎপাদন১৮৪ রয়েছে। তাদের অস্তিত্বের কোন প্রয়োজন আবিস্কার করা যায় না। সাহারা বা গোবি মরুভূমি দুনিয়ার কার কোন্ প্রয়োজনে সৃষ্টি হয়েছে? আগ্নেয়গিরির উৎপাত জগতের কোন্ কাজে লাগছে? যদি পৃথিবীর মঙ্গলময় দিকের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই তাকে এক আদর্শ কারিগরের সৃষ্টি বলে ধরে নেয়া হয়-তাহলে অপরদিকে অশুভ ও অকল্যাণকর দিকের বিচার করলে তাকে এক পিশাচের সৃষ্টিই বলতে হয়।
\r\n
এ দুটো বৃত্তিই আল্লাহ্ সম্বন্ধে ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ্কে ধারণা করা হয়েছে সর্বত্রুটিহীন, সর্বগুণাধার, সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তারুপে। তাই তার প্রমাণস্বরূপ বিশ্ব সৃষ্টি থেকে বিশ্বের নানাবিধ কলাকৌশল১৮৫ থেকে নযীর তুলে বলা হয় আল্লাহ্ই এসব কার্যের১৮৬ মূলাধার।
\r\n
তার তৃতীয় যুক্তিস্বরূপ বলা হয় আল্লাহ্র অস্তিত্ব নিশ্চয়ই রয়েছে। কারণ আল্লাহ্র ধারণা থেকেই তাঁর অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। যিনি সর্ব গুণাধার, তাঁর মাঝে অস্তিত্ব নামক গুণের অভাব হলে তাঁকে সর্বগুণাধার বলা পরস্পরবিরোধী উক্তি মাত্র। মধ্যযুগে সেন্ট এলসেম এ যুক্তির অবতারণা করে বেশ বাহবা পেয়েছিলেন।
\r\n
এ যুক্তিও ত্রুটিহীন নয়। আল্লাহ্কে সর্বগুণাধার বলে আমরা মাত্র তাঁর অস্তিত্ব ঘোষণা করছি-তাঁর কোন প্রমাণ দিতে পারিনি। দার্শনিক শ্রেষ্ঠ ক্যান্ট একে উপহাস করে বলেছেন, ‘আমার পকেটে একশত ডলার রয়েছে বলে যদি আমার ধারণা থাকে, তাতে কি প্রমাণ হয় যে, বাস্তবিকই একশত ডলারের অস্তিত্ব রয়েছে’।
\r\n
এসব যুক্তির দ্বারা আল্লাহ্র অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়নি। এ তিনটি প্রমাণের মধ্যে প্রণিধানযোগ্যে বিষয়টি এইঃ দুটোতে অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করতে তার অনুকূলে প্রমাণ দেয়া হয়েছে। অপরটিতে ধারণা থেকে অস্তিত্বের প্রমাণ নেয়া হয়েছে। তবে তিনটি যুক্তিতেই স্বীকার করে নেয়া হয়েছে ধারণার সত্যাসত্য বিষয়ের সঙ্গে যোগসূত্রই নির্ধারিত হবে। আল্লাহ্র অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের মনে যে ধারণা রয়েছে- যদি বাস্তব জগতে সেরূপ কোন সত্তা থেকে তাহলে এটি সত্য’। যদি না থেকে তাহলে মিথ্যা। কাজেই আল্লাহ্ সম্বন্ধে আমাদের ধারণাগুলো সত্য না মিথ্যা, এ প্রশ্নের মীমাংসা করতে হলে সত্য ও মিথ্যার সংজ্ঞা নির্দেশ করতে হয়।
\r\n
সাধারণত সত্য বলতে বোঝা যায়-প্রতিষঙ্গ১৮৭ । আমাদের মনে রয়েছে অনেকগুলো ধারণা। বাইরের জগতে রয়েছে অসংখ্য বস্তু ও গুণাবলি। কোন ধারণা সত্য হলে তার সঙ্গে বাইরের বস্তু বা গুণাবলির যোগ থাকা চাই। যেমন ধরা যাক, কারো মনে জ্বিন কোন জাত আছে বলে যদি ধারণা থাকে, তাহলে তা সত্য কি মিথ্যা বিচার করতে হলে তলিয়ে দেখতে হবে জ্বিন বলে কোন জাত আছে কি না। যদি থাকে, তাহলে এ ধারণা সত্য। যদি না থাকে, তাহলে তা মিথ্যা। একে দর্শনের পরিভাষায় সত্যের প্রতিষঙ্গমূলক মতবাদ১৮৮ বলা হয়। এখানে প্রশ্ন দাঁড়ায় পাওয়া যায়, তাহলে সেও আমাদের মনেরই একটা ধারণা হবে। কাজেই কোন ধারণার সত্যাসত্যের বিচার অপর ধারণার দ্বারাই করতে হবে।
\r\n
তার ওপর এতে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে বিষয়বস্তু বা গুণাবলি অপরিবর্তনীয়। তাদের সম্বন্ধে আমাদের ধারণা সব সময় একই থাকবে। আমাদের অভিজ্ঞতায় কিন্তু দেখতে পাই বস্তুজগতে চলছে এক দ্রুত পরিবর্তন। উদ্দীপক থেকে যে সংবেদন আমরা পাই, বিভিন্ন চিন্তার মাধ্যমে১৮৯ তাকে আমরা যেসব বস্তু সম্বন্ধে পূর্বে যেসব ধারণা করে নিয়েছি, তার সত্য বিচার করতে গিয়ে যদি পূর্বের ধারণাগুলোকে আবার বস্তুর সঙ্গে তুলনা করি, তাহলে স্পষ্টই দেখতে পাব- আমাদের ধারণার পরিবর্তন অত্যাবশ্যক। কারণ বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে বস্তু পরিবর্তিত হয়ে গেছে অথচ আমাদের ধারণার পরিবর্তন হয়নি অথবা বস্তু অপরিবর্তিত রয়েছে কিন্তু তার সম্বন্ধে আমাদের ধারণার হয়েছে পরিবর্তন।
\r\n
তাছাড়া সত্যাসত্য বিচার কেবল বাইরের বস্তুর সঙ্গে আমাদের তুলনা করেই শেষ হয় না। মানব মনের আবিষ্কৃত অনেকগুলো তত্ত্বের সঙ্গে আমাদের পরবর্তী ধারণাগুলোর সত্যাসত্য নির্ণয় করা চলে। জ্যামিতি শাস্ত্রের একটা প্রতিপাদ্য১৯০ বা সম্পাদ্য১৯১ সত্য না মিথ্যা বিচার করতে হলে পূর্ববর্তী প্রতিপাদ্য, সম্পাদ্য বা স্বতঃসিদ্ধ থেকে তাকে যুক্তিসহকারে অবরোহন করা১৯২ যায় কি না, তাই বিচার করতে হয়। কাজেই সত্যের এ সংজ্ঞা নির্দেশ নিতান্তই একদেশদর্শী।
\r\n
এ থিয়োরির সমালোচনাতেই সঙ্গতিবাদের১৯৩ উৎপত্তি। Coherence theory মতে আমাদের মনে যেসব ধারণা বর্তমান তাদের মধ্যে যদি সঙ্গতি থাকে তাহলে বুঝতে হবে তারা সত্য। যদি কোন ধারণার সঙ্গে অন্য সুপ্রতিষ্ঠিত ধারণার সংঘর্ষ বাধে, তবে সবগুলো ধারণার আলোকেই নতুন বেখাপ্পা ধারণার বিচার করতে হবে।
\r\n
এ থিয়োরি মতে অনেক অসত্যকেও সত্য বলে চালিয়ে দেয়া যেতে পারে। সাধারণত সত্য বলতে ধারণার সঙ্গে বিষয়ের যোগ বোঝা যায়। যদি ধারণার সঙ্গতি-অসঙ্গতি সত্যাসত্য বিচারের মানদন্ড হয়, তাহলে বাস্তবে অস্তিত্ব নেই এমন অনেক বিষয়কে সত্য ব’লে চালিয়ে দেয়া যেতে পারে। ধরা যাক, একটি স্কুলের ছেলে এসে তার আম্মার নিকট অভিযোগ করল যে, তাকে হেডমাস্টার কান ম’লে দিয়েছেন। তার আম্মা অনুসন্ধান করে দেখল বাস্তবিকই ছেলেটির কান লাল। তার চোখের কোণেও রয়েছে পানির দাগ। আম্মার নিশ্চয় বিশ্বাস হবে,তার ছেলের অভিযোগ সত্য। বাস্তবিক পক্ষে হেডমাস্টার তাকে মারেননি। অন্য ছেলের সঙ্গে লড়াই করতে দেখে হেডমাস্টার তাকে ধমক দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে ছেলে তার আম্মার কাছে যে জবানবন্দি দিচ্ছে, তাতে কোন অসঙ্গতি নেই। মাস্টার ছাত্রের সম্পর্ক বা হেডমাষ্টারের কড়া মেজাজের সম্বন্ধে তার আম্মার ধারণাগুলোর সঙ্গে ছেলের বিবরণ হুবহু খাপ খাচ্ছে, কাজেই আম্মার তাকে ধরে নিচ্ছে সত্য বলে। আদতে কিন্তু বর্ণনাটি নিছক কাল্পনিক ও বিদ্বেষমূলক।
\r\n
তার ওপর গোটা মনোজগতের সবগুলো ধারণার সঙ্গে নতুন ধারণার সঙ্গতি দ্বারা যদি তার সত্য বিচার করা যায়, তাহলে অন্যদিকে মস্ত অন্যায় করা হবে। কারণ আমাদের পূর্বতন ধারণাগুলোও সম্পূর্ণ অলীক হতে পারে। জগতে নানাবিধ আবিস্কারের সূচনাতে তাদের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন হয়েছে। কোপারনিকাসের১৯৪ সূর্যকেন্দ্রিক সিদ্ধান্ত১৯৫ বা ডারউনের বিবর্তনবাদের বিরুদ্ধে সমসাময়িক যুগে নানা কটূক্তি বর্ষিত হয়েছে। পরবর্তীকালে আবার সেই সব ধারণার আলোকেই জগতের মানব-কাঠামো পুনর্গঠিত হয়। সঙ্গতি কথার তাহলে অর্থ থাকে কি?
\r\n
উইলিয়াম জেমস তাই সত্য সম্বন্ধে প্রয়োগবোধ১৯৬ নামক তাঁর নিজস্ব মতবাদ প্রচার করেন। তাঁর ধারণা ছিল বাস্তব জগতে স্থিতিশীল বলে কোন কিছু নেই, সব কিছুই পরিবর্তনশীল। তাই কোন ধারণার সত্যাসত্য তার কার্যকারিতার ওপর নির্ভর করে। তাঁর পূর্ববর্তী দার্শনিকদের ধারণা ছিল, যা সত্য তাই কার্যকরী। জেমস তার বিরুদ্ধে ঘোষনা করেন, যা কার্যকরী তাই সত্য। প্রকৃতপক্ষে আমাদের মনে নানা ধারণা, নানা ভাব, নানা থিয়োরি বর্তমান। তাদের প্রত্যেকটি সম্বন্ধে আমরা সত্যের দাবি করি। তাদের কার্যকারিতা দিয়েই সত্যের বিচার করে। যদি তাদের মধ্যে কোনোটা কার্যকরী হয়, তাহলে সেটি সত্য, যদি কার্যকরী না হয়, তাহলে মিথ্যা।
\r\n
ধর্ম সম্বন্ধে সে মতবাদ অনুসারে বলা যায়, জীবনে ধর্মের কার্যকারিতা রয়েছে, কাজেই ধর্মের ধারণাগুলো সত্য। জেমস তাঁর বলিষ্ঠ ভাষায় প্রকাশ করেছেন, আমাদের প্রক্ষোভজাত প্রয়োজন দুনিয়াকে ধার্মিকের মনোবৃত্তি নিয়ে গ্রহণ করার মত দুঃসাহসিক কর্মের পোষকতা করে। ধর্ম সত্য হতে পারে, এই আশাকে পোষণ করা ধর্ম মিথ্যা, এই আশঙ্কার চেয়ে ভালো, কারণ এ দুটো বিশ্বাসের একটাকে আমাদের গ্রহণ করতেই হবে। কাজেই আল্লাহ্র অস্তিত্বের ধারণা আমাদের জীবনের অনেকগুলো কাজকর্মকে নিয়ন্ত্রিত করে, সেইজন্যই এটি আমাদের জীবনে সত্য।
\r\n
এ মতবাদের জের টানলে এক বিরূপ সিদ্ধান্তে এসে উপস্থিত হতে হয়। correspondence Theory বা Coherence Theory দুটোই সত্যের কার্যকারিতা স্বীকার করে নেয়। যা সত্য তা জীবনে কার্যকরী হবেই। কিন্তু যা কার্যকরী তা সত্য কি করে হতে পারে? যেমন ধরা যাক, গভীর রাতে কোন ব্যক্তির যদি রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, তাহলে ভ্রমের বশবর্তী হয়ে সে ভয় পায় এবং সঙ্গে সঙ্গেই দৌড়ায়। কিন্তু তা বলেই কি বুঝতে হবে সেই রজ্জু বাস্তবিকই একটা সাপ? এ যুক্তির ধারামতে একটা ভুল হলেও সাময়িকভাবে সত্য। কারণ সেই ভ্রমাত্মক ধারণা সেই ব্যক্তির জীবনে কার্যকরী। কাজের মধ্যেই সত্যের সার্থকতা। যদি রজ্জুকে সাপ মনে করে পথিক ভুল করে ভয় পায়, তাহলে একটা জীবন্ত সাপ ঠিক তার মনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, এই রজ্জুও সেই প্রতিক্রিয়ারই সৃষ্টি করে এবং এই জন্যই তা’ সত্য।
\r\n
এভাবে বিচার করলে অবশ্য জেমসের মতবাদের যৌক্তিকতা আমাদের কাছে অত্যন্ত দুর্বল মনে হয়। তাহলে সত্যাসত্যের বিচার নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। যা একজনের কাছে এক বিশেষ সময়ে সত্য, তা অপরের নিকট সত্য নাও হতে পারে। দুনিয়া তখন হয়ে পড়ে ছন্নছাড়া খেয়ালী রাজ্য। সত্য সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলাই হয়ে পড়ে অসঙ্গত।
\r\n
জেমস নিশ্চয়ই এই অর্থে সত্য শব্দের প্রয়োগ করেন নি। ব্যষ্টির ব্যক্তিগত জীবন ব্যতীত সমষ্টি জীবনে এমন কতকগুলো ধারণা কার্যকরী, যেগুলোর সপক্ষে ন্যায়শাস্ত্র অনুমোদিত কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, অথচ মানবচিন্তার সূচনা থেকে সেগুলোর ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। স্থান ও কাল আমাদের সকল চিন্তার মূলেই রয়েছে। এ দুটো ধারণাকে প্রমাণ করা সহজ নয়। অথচ কোন বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা করতে হলে স্থান-কালের মাধ্যমেই চিন্তা করতে হয়। দার্শনিক ক্যান্ট তাদের বলেছেন, Forms of Institutions.
\r\n
কার্যকারণ পরস্পরাসূত্র১৯৭ এবং বস্তু১৯৮, এগুলোও প্রামাণ্য ধারণা নয়। এগুলো ব্যতিরেকে মানবজীবনের অভিজ্ঞতা বা বিজ্ঞান এক পা-ও অগ্রসর হতে পারে না। কাজেই তাদের সত্যতা স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। আল্লাহ্র অস্তিত্ব যদি এমন কোন ধারণা হয় যা স্বীকৃতি ব্যতীত আমরা জাগতিক অভিজ্ঞতার কোন সুষ্ঠু ব্যাখ্যা করতে পারি না, তাহলে তাকে স্বীকার করতে আমরা বাধ্য। সম্ভবত এই অর্থেই জেমস বলেছিলেন, যা জীবন কার্যকরী, তা-ই সত্য।
\r\n
এখানে প্রশ্ন দাঁড়ায়, আল্লাহ্র অস্তিত্ব বাস্তবিকই সেরূপ কোন ধারণা কিনা। আমাদের অভিজ্ঞতাকে যদি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের জগতে সীমাবদ্ধ করা যায় তা’হলে অবিচার করা হবে। বিজ্ঞানের জগতে আমরা পরিচালিত হই বুদ্ধিবৃত্তি১৯৯ দ্বারা। সেখানে বোধির কোন স্থান নেই। পরিদৃশ্যমান জগতের বিভিন্ন উদ্দীপক থেকে যে সংবেদন আমরা পাই, বিভিন্ন চিন্তার মাধ্যমে তাকে আমরা সুসংবদ্ধ করে সার্বিক সিদ্ধান্তে২০০ এসে পৌঁছি। সেই সিদ্ধান্তগুলোকে ব্যবহারিক জীবনে কার্যকরী করে তোলা ফলিত বিজ্ঞানের কাজ। বৈজ্ঞানিক জগৎ ব্যতীত নৈতিক বা ধর্মীয়জীবনে নানা অভিজ্ঞতা আমাদের হয়। সেগুলোর ভিত্তিতেও নীতিবিজ্ঞান বা ধর্মীয় বিজ্ঞান গড়ে তোলা সম্ভবপর। তবে বাস্তবজীবনে তাদের প্রয়োগ ঠিক প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মত ফলপ্রসূ নয়। তাদের দ্বারা মানুষের জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান ঠিক প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পর্যায়ের নয়। মানবমনের বিকাশসাধন করে তারা সমাজজীবনে নানাভাবে উন্নত করে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ফলিত রূপের নানা দওলতে আপাতত মুগ্ধ হয়ে আমরা আমাদের অভিজ্ঞতাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতা বলে ভুল করে থাকি। এজন্যই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের সঙ্গে নৈতিক জীবনের বা ধর্মীয়জীবনের নানাবিধ দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। বুদ্ধি ও বোধির এ দ্বন্দ্ব বাস্তবিকই মারাত্মক।
\r\n
মানবজীবনের সবগুলো অভিজ্ঞতা ও তার জ্ঞানের সবগুলো পদ্ধতিকে স্বীকার করে নিলে, তবে এই দ্বন্দ্বের নিরসন হতে পারে।
\r\n
আল্লাহ্র অস্তিত্বের যেসব প্রমাণ পাওয়া যায়, তাতে মাত্র এক সুরই প্রমাণিত হয়। ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ শক্তিতে মানবমন তার প্রকৃত সত্তা খুঁজে পায় না বলে আজীবন অসীম সত্তার আশ্রয়ে সে স্বস্তিলাভ করতে চায়। এখানেই রয়েছে ধর্মের অপরিহার্যতা, যাকে ইংরেজ দার্শনিক জন কেয়ার্ড বলেছেন, Necessity of Religion.
\r\n
মানবজীবনের নানাবিধ অভিজ্ঞতায় আল্লাহ্র অস্তিত্বের স্বীকৃতি অনিবার্যরুপে দেখা দেয়। তাকে বুদ্ধির আলোকে প্রমাণ করতে চাইলে তাতে ত্রুটি দেখা দেয়া সত্য। কিন্তু যা কবির চোখে, ধ্যানীর মর্মে একান্ত বাস্তব, যা ব্যক্তি-জীবনের নানাবিধ অভিজ্ঞতার সুসামঞ্জস্য বিধানে কার্যকরী, রাষ্ট্রীয় জীবনে যে ধারণার কল্যাণে হয় ব্যষ্টি ও সমষ্টির অধিকারের সমন্বয়, তাকে অবাস্তব বলার অর্থ সত্যকে অস্বীকার করা।
\r\n
পরলোকগত ইংরেজ কবি ওয়ার্ডস ওয়ার্থ আল্লাহ্র অস্তিত্বের কোন প্রমাণ চাননি। তাঁর কাছে তাঁর নিজের অস্তিত্বের মতই তা’ই ছিল জীবন্ত সত্য। অনবদ্য ভাষায় তিনি বলেছেনঃ
\r\n
‘ যে প্রকাশ আমায় সমুন্নত চিন্তার দ্বারা বিচলিত করে, যার মহান অনুভূতি অত্যন্ত গভীরভাবে (আমার সত্তায়) অনুপ্রবেশ করে, যার আবাস অস্তগামী সূর্যের রশ্মিতে, সমুদ্রের দিকবলয়ে, মুক্ত জীবন্ত বাতাসে, ঘন-নীল আকাশে এবং মানব মনে (রয়েছে বিরাজমান) যে গতি ও আত্মা সকল চিন্তাশীল জীবকে ও চিন্তার বিষয়বস্তুকে দোলা দেয় এবং সকল বস্তুতে প্রবাহিত তা আমার কাছে জীবন্ত সত্য।২০১
\r\n
উইলিয়াম জেমসও ঠিক ওয়ার্ডস ওয়ার্থের মত আল্লাহ্র অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁর ধারণা প্রকাশ করেছেনঃ
\r\n
“ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান যেভাবে বিশ্বসংস্থাকে জানবার চেষ্টা করে তাতে তার মাঝে সুসংবদ্ধ পারমার্থিক অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। ( এভাবে দেখলে) তাকে চন্সি রাঈটের ভাষায় আবহ বলতে হয়- উদ্দেশ্যবিহীন ভাঙ্গা গড়াই তার খেলা।
\r\n
আর কিছু হোক না কেন- এটি নিশ্চিত যে, বর্তমান কালের প্রাকৃতিক বিজ্ঞানজাত জ্ঞানের দ্বারা আমরা পৃথিবীর যে সন্ধান পাই, সে পৃথিবী অন্য এক বৃহত্তর পৃথিবী দ্বারা পরিবেষ্টিত। তার সেই অবশিষ্ট গুণাবলী সম্বন্ধে বর্তমানে আমরা কোন সার্থক ধারণা করতে পারি না।*২০২
\r\n
কেন পারি না তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি আবার বলেছেনঃ
\r\n
‘যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা জাতিকে এবং সার্বিক (সত্য) নিয়ে আলোচনা করি ততক্ষণ আমরা সত্যের সংকেত নিয়েই আলোচনা করি। যেই ব্যক্তিগত ও ব্যক্তিত্বগত বিষয় নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হই তখনই মাত্র সত্যের সর্বাঙ্গীণ রূপের আলোচনা আমাদের দ্বারা হয়।২০৩
\r\n
আমাদের জীবনে অনেকগুলো আদর্শ বর্তমান, সত্য শিব ও সুন্দর সব সময়েই জ্ঞানের রাজ্যে, কর্মের ক্ষেত্রে ও সৌন্দর্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে আমাদের প্রেরণা যোগায়। এগুলোর মূল্য কি? বাস্তব জগতে পরম সত্য ও পরম শুভ বা পরম সুন্দর বলে কিছু আছে কিনা এ প্রশ্ন আমাদের মনে ওঠে। এগুলো সম্বন্ধেও ন্যায়শাস্ত্রসম্মত কোন প্রমাণ দেওয়া যায় না। তবু এগুলো জীবনে কার্যকরী। কেবল ব্যক্তিজীবনে এগুলো কার্যকরী নয়, সমষ্টি জীবনেও কার্যকরী, কাজেই এগুলোর স্থিতি সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত, তাই আমরা ভাবতে বাধ্য হই-বিশ্বসত্তায় সেগুলো বর্তমান। ব্যবহারিক জীবনে আল্লাহ্র অস্তিত্বে আস্থা স্থাপন অনেক ক্ষেত্রেই হয়ে পড়ে অপরিহার্য। জীবনের নানবিধ সংকট-সঙ্কুল অবস্থায়, নানা বিপর্যয় ও সংঘর্ষের মধ্যে কেবল আল্লাহ্র অস্তিত্বের ওপর প্রচণ্ড বিশ্বাসের ফলে মানুষ বেঁচে থাকতে পারে। আদর্শের অনুসরণ ও রুপায়ণে আল্লাহ্র অস্তিত্বে আস্থা স্থাপন হয়ে পড়ে অনিবার্য। আল্লাহ্র অস্তিত্বে বিশ্বাস নৈতিক জীবন যাপন করার পক্ষে অত্যাবশ্যক। ‘আল্লাহ্ আছেন’ বলার সোজা অর্থ দাঁড়ায় দুনিয়া এমনভাবেই তৈরি যাতে পাপের ক্ষয় ও পুণ্যের জয় হয়। অর্থাৎ এ দুনিয়ায় রয়েছে এক নৈতিক শাসন ব্যবস্থা। সকল আইন-কানুনকে ফাঁকি দেওয়া চলে কিন্তু একে ফাঁকি দেওয়া চলে না। এই যে নৈতিক শাসনব্যবস্থা২০৪ যার ওপর বিশ্বাস স্থাপনের ফলে মুজাহিদ জ্বলন্ত অনলের লেলিহান শিখা তুচ্ছ করে তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে, এ বিশ্বাসের ফলেই সত্য-অনুসন্ধানী নানা উত্থান ও পতনের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও অকুতোভয়ে আদর্শের অনুসরণ করে।
\r\n
রাজনৈতিক জীবনেও সত্য, শিব ও সুন্দরের আদর্শ গ্রহণ আরও প্রয়োজনীয়। জগতের সত্তা যদি অণু-পরমাণুর লীলাক্ষেত্রই হয়, জীব-জগৎ যদি ডারউইনের বিবর্তনবাদের সূত্র অবলম্বন করেই চলে, তা’হলে কেবল উপযুক্ততমের উদ্বর্তনের নীতিই গ্রহণ করতে হয়। যারা এ জীবন-যুদ্ধে উপযুক্ততম কেবল তারাই বেঁচে থাকবে-যারা দুর্বল, যারা পঙ্গু তাদের মরতে হবে। এবং বিধ মতবাদে বিশ্বাসী লোকদের পক্ষে রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব নয়। কারণ রাষ্ট্র হবে সকল লোকেরই রক্ষাকর্তা। তার মাঝে সবলের সঙ্গে দুর্বলও আশ্রয় পাবে। রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য সবলের অত্যাচার থেকে দুর্বলকে রক্ষা করা। তা’ রাষ্ট্র কেন করবে? এ জগতের মূলে নৈতিক শাসন আছে বলেই রাষ্ট্র তা’করতে বাধ্য, যদি কোন নৈতিক শাসন না থাকে তাহলে দুর্বলকে রক্ষার কোন প্রশ্নই ওঠে না।
\r\n
তাই সকল রাষ্ট্র বা সরকার গঠন করার মূলে একটা অদৃশ্য নৈতিক শাসন স্বীকার করে নেয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। দুনিয়ার সম্পদের অধিকার নিয়েও ব্যষ্টি ও সমষ্টির মধ্যে দ্বন্দ্বের অন্ত নেই। ব্যষ্টির হাতে সম্পদের অধিকার ছেড়ে দিলে দু’দিনেই এক শ্রেণী চল্লিশ তলার উপর দাঁড়ায়, আর অন্য এক শ্রেণী বেওয়ারিশ কুকুরের মত পথে-ঘাটে ধুঁকে মরে। সমষ্টির হাতে সমস্ত অধিকার ছেড়ে দিলে ব্যষ্টি তার স্বাধীনতা হারায় আর সমস্ত অধিকার আল্লাহ্র হাতে ছেড়ে দিলে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রেখেও মানুষ পৃথিবীর সম্পদ ভোগ করতে পারে। অপরদিকে রাষ্ট্র জনমতের দ্বারা গঠিত হলেও জন্মের পরে জনসমষ্টি থেকে তার সত্তা পৃথক হয়ে পড়ে। পুঁজিবাদ বা সমাজতান্ত্রিক মতবাদ দ্বারা গঠিত রাষ্ট্রে সর্বসাধারণের কর্তৃত্ব থাকে না। তার নিয়ামকরূপে রাষ্ট্র পরিচালনা করে মুষ্টিমেয় লোক। তাদের ব্যক্তিগত জীবনের ছায়া সর্বাবস্থায়ই রাষ্ট্রের ওপর পড়া অপরিহার্য। কাজেই এদের মনে যদি কোন বৃহত্তর আদর্শের চেতনা কার্যকরী না থাকে তাহলে তাতে জনগণের নানা অমঙ্গল ঘটাবার সম্ভাবনা।
\r\n
সর্বাবস্থায়ই আদর্শকেন্দ্রিক রাষ্ট্র সর্বশ্রেষ্ঠ। সেই আদর্শ যদি মানবজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ গুণগুলো- যেমন ব্যক্তিত্ব, শক্তি,ন্যায়-বিচার প্রভৃতির আলোকে গ্রহণ করা যায়, তাহলেই রাষ্ট্র পরিচালনায় পারদর্শিতা দেখা দিতে পারে।
\r\n
এখন উপসংহারে আমরা এ সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছতে পারি। আল্লাহ্র অস্তিত্বের প্রমাণের মূলে রয়েছে মানব-মনের এক চিরন্তন নির্ভরশীলতা।
\r\n
মানুষ আপনাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে না বলে স্বয়ংসম্পূর্ণ কোন সত্তাকে আশ্রয়রূপে গ্রহণ করতে চায়। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানই জ্ঞানের একমাত্র পথ নয়। বিচার-বুদ্ধির বাইরে, বোধির মাধ্যমে জ্ঞানলাভ সম্ভবপর। সে জ্ঞানের আলোকে দেখলে আল্লাহ্র অস্তিত্বের জন্য কোন প্রমাণের প্রয়োজন নেই, কারণ সেটি বোধিলব্ধ জ্ঞানের ব্যাপার এবং তা সরাসরি অভিজ্ঞতার২০৫ উপর নির্ভরশীল।
\r\n
নানাবিধ বৈজ্ঞানিক প্রত্যয়ের মত আল্লাহ্র অস্তিত্বের ধারণা আমাদের ভূয়োদর্শনকে সুসংবদ্ধ করার জন্য প্রয়োজন। সমাজজীবনে ও রাজনৈতিক জীবনে এ প্রত্যয়ের মূল্য সর্বাপেক্ষা অধিক। সুতরাং তথাকথিত বিজ্ঞানের দ্বারা সে প্রত্যয়ের অনুকূলে কোন সত্তার অস্তিত্ব না পাওয়া গেলেও আল্লাহ্র অস্তিত্ব আমাদের জীবনে কেবল সত্যি নয় জলজ্যান্ত সত্যি। এজন্যই ইসলাম গোড়াতেই আল্লাহ্র অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েছে।
\r\n
আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের মানুষের অধিকারের সমন্বয়
\r\n
আল্লাহ্র অস্তিত্বের স্বীকৃতি ব্যতীত অনেকগুলো অভিজ্ঞতার কোন সুষ্ঠু ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না বলে এবং সমাজজীবন বা রাষ্ট্রজীবনে চরম নৈরাজ্য দেখা দেয় বলে ইসলাম গোড়াতেই এ দুনিয়ার সকল অধিকার, সকল সম্পদ আল্লাহ্র হাতে তুলে দিয়েছে। পবিত্র কুরআন শরীফে ঘোষণা করা হয়েছে- ‘আসমান যমীনে যা কিছু রয়েছে তার মালিক আল্লাহ্’ (নিসা ৪:১৯:১৩১)। তাহলে স্বীকার করে নিতে হবে, এ দুনিয়ার একমাত্র সার্বভৌম অধিকার আল্লাহরই। অথচ এই কুরআন শরীফের অন্যত্র বলা হয়েছেঃ
\r\n
‘হু আল্লাযি খালাকালাকুম মা’ফিল আরদে জামিয়া’- আল্লাহ্ দুনিয়ার সবই মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন।
\r\n
তা’হলে আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের মধ্যেও মানুষের ভোগের অধিকার রয়েছে। এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ আলিম মাওলানা মাহমুদুল হাসান বলেনঃ
\r\n
‘সব জিনিসই মানুষের সম্পত্তিবিশেষ অর্থাৎ আল্লাহ্ সকল জিনিসই মানুষের প্রয়োজন মিটাবার জন্য সৃষ্টি করেছেন। কোন জিনিসই সৃষ্টির দিক থেকে ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি নয়, পক্ষান্তরে সকলেরই সম্পত্তি। সব জিনিসই মানুষের মঙ্গলের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে- তাই সকল জিনিসেই মানুষের দখল-ভোগের অধিকার আছে। যখন কোন জিনিস কারো ভোগ-দখলে থাকবে তখন তাকেই কেবল সে জিনিসের একমাত্র মালিক বলে গণ্য করা হবে। অন্য কেউ তার ওপর আধিপত্য স্থাপন করতে পারবে না। হাঁ! কোন জিনিসের দখলকারীর জেনে রাখা উচিত, সে নিজের প্রয়োজনে অতিরিক্ত বস্তু অনর্থক নিজ কবলে না রেখে অন্যকে অবাধে ভোগ-দখল করতে দেবে। কেননা, মানুষ হিসেবে সৃষ্টির ভোগ প্রত্যেক মানুষেরই প্রাপ্য’।
\r\n
এ কারণেই রীতিমত যাকাত আদায় করা সত্ত্বেও প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাল সঞ্চয় করা সঙ্গত নয়। নবীগণ ও ধর্মভীরু লোকগণ এ কারণেই ধন সঞ্চয়ে বিরত রয়েছেন। এমনকি হাদীস দ্বারা পরিস্কার বোঝা যায়, সাহাবা ও তাবেয়ীগণ প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তু রাখা বা ব্যবহার করাকে হারাম বলেছেন।
\r\n
প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তু সঞ্চয় বা ব্যবহার অনুচিত বা অসঙ্গত তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। কারণ প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তুতে তার কোন আবশ্যকতা নেই। ‘সব সৃষ্টিই মানুষের জন্য’ নীতিতে (সব কিছুতেই) সকলের দাবি রয়েছে, বরং প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তু ভোগ দখলকারী (তার নিজের প্রয়োজনের অংশের অতিরিক্ত ভোগ করার দরুন) অন্যায় দখলকারীরূপে মালিক বটে।* ( ইজাহুল আদিল্লাঃ পৃ,২৬৮। ইসলাম কা ইকতেসাধি নিজাম পৃ,৪২।)
\r\n
ব্যষ্টিকে তাই দুনিয়ার সম্পদ যথেচ্ছ ভোগ করার অধিকার ইসলাম দেয়নি। যে দুনিয়ার সমস্ত মালিকানা আল্লাহ্র, যে রাজ্যে মানুষ তার প্রতিনিধি,হিসাব রক্ষক, সেখানে আল্লাহ্র খলীফা হিসেবে সে তার প্রয়োজনমত ভোগ করবে---
\r\n
প্রয়োজনের অতিরিক্ত একতিলও সে অপব্যয় করবে না।
\r\n
স্পষ্ট বোঝা যায়-আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের সঙ্গে ব্যক্তি-স্বাধীনতার নীতি স্বীকার করা হয়েছে। তবে যাতে এ স্বাধীনতা আধুনিক কালের বীজমন্ত্র Laissez Faire- এ পরিণত না হয়, তার জন্য কুরআন শরীফে নানাবিধ নৈতিক কানুনের প্রবর্তন করা হয়েছে।
\r\n\r\n
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
\r\n
ইসলামী নীতির রূপায়ণ-ব্যক্তিগত জীবনে সমাজে ও রাষ্ট্রে
\r\n
ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র
\r\n
\r\n
ইসলামের ব্যক্তি-জীবন ও সমাজ-জীবনের জন্য কোন পৃথক আইন নেই। আদেশ রয়েছে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই আল্লাহ্র আদর্শে জীবন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। জনাব রাসূলে আকরাম (সঃ) বলেছেন- ‘তাখাল্লাকু বি আখলাকিল্লাহ’। আল্লাহ্র গুনে গুণান্বিত হও। সে আদেশ ব্যক্তি-জীবনের পক্ষে যেমন প্রযোজ্য, সমাজ-জীবনে ও রাষ্ট্র-জীবনের পক্ষেও তেমনই সমানভাবে প্রযোজ্য। সোজা কথায় ব্যক্তি যেমন আল্লাহ্র আদর্শে জীবন গঠন করবে, তেমনি সমাজ ও রাষ্ট্র ও গঠিত হবে আল্লাহ্র আদর্শেই। ইসলামের নানাবিধ প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য ব্যক্তিকে তার ব্যক্তিগত জীবনে, সমাজে ও রাষ্ট্রে আদর্শরুপে গড়ে তোলা। সমাজকে রাষ্ট্রের মধ্যে বিলীন করে দেওয়ার জন্য ইসলামের কোন আদর্শ না থাকলেও ইসলামের শাসন-অনুশাসন যাতে সর্বদা সহজভাবে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়জীবনে চালু হতে পারে, তার জন্য রয়েছে পরিস্কার নির্দেশ। সালাত, সিয়াম, হজ্জ, যাকাত প্রভৃতির প্রাথমিক উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত জীবনের বিশুদ্ধি, দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ব্যক্তি-জীবনকে সংঘ-জীবনের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী করে তোলা।
\r\n
ইসলামী নীতির প্রয়োগ-ব্যক্তিগত জীবনেঃ সালাত
\r\n
আমাদের দুর্ভাগ্যই বলতে হবে- আমারা আমাদের বাংলা ভাষায় ‘সালাত’ শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে ‘নামায’ শব্দ ব্যবহার করি। কুরআন-উল-করীমে যে ‘সালাত’ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তার প্রতিশব্দ হিসেবে ফারসি ‘নামায’ শব্দ ব্যবহৃত হতে পারে না। ‘নামায’ শব্দের উৎপত্তিগত অর্থ উপাসনা। এ উপাসনা অগ্নিউপাসক পার্সিদের মধ্যে ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেও প্রচলিত ছিল। সে উপাসনার বিষয়বস্তু ছিল অগ্নি। কুরআন-উল-করীমে ব্যবহৃত ‘সালাত’ শব্দের অর্থ শুধু উপাসনা নয়। তার অর্থ হচ্ছে যে সর্বশক্তিমান ও সার্বভৌম সৃষ্টিকর্তার আদেশ-নির্দেশের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করে তার কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ।
\r\n
সালাতের মূল লক্ষ্য হচ্ছে একদিকে জীবনকে নানান রিপু এবং অসৎ প্রবৃত্তির প্ররোচনা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে সেই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র ওপর নির্ভরশীল হওয়ার জন্য প্রস্তুতি এবং সঙ্গে সঙ্গে তার গুণাবলী এ জগতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া।
\r\n
এ সালাতের মধ্যে ইসলামের অপরাপর কর্তব্যের মত দুটো দিক রয়েছে। একটিকে বলা যায় তার পারমার্থিক দিক, অপরটিকে বলা যায় তার সামাজিক দিক। সামাজিক দিকের আলোচনা করলে দেখা যায় এতে দিনে পাঁচবার সকল মুমিন-মুসলিমকে একত্রিত হওয়ার জন্য তাগিদ রয়েছে। আল্লাহ্র রসূল (সঃ) নির্দেশ নিয়েছিলেন, ‘যদি কেউ মসজিদে সালাত আদায় না করে বাড়িতে আদায় করে তা হলে তার ঘর পুড়িয়ে দাও’। এতে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে সালাতের উদ্দেশ্যে মুমিন মুসলিমদের একত্রিত হওয়াও তার একটা লক্ষ্য ছিল। মুসলিমদের জীবনে ঐক্য,প্রেম,মৈত্রী,সৌহার্দ্য প্রভৃতি সৃষ্টির জন্য তাদের প্রত্যেক দিবারাত্রিতে অন্ততপক্ষে পাচঁবার একত্রিত হওয়ার সুযোগ দান করে বলে সালাতের রয়েছে এক সামাজিক গুরুত্ব। প্রকৃতপক্ষে হযরত রসূল-ই-আকরাম (সঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে মসজিদ ছিল একাধারে মুসলিমদের পার্লিয়ামেন্ট, সুপ্রীম কোর্ট, গবেষণাগার ও বিশ্ববিদ্যালয়। মসজিদকে কেন্দ্র করেই জীবনবিকাশের ধারাগুলো চালু ছিল। এজন্য আল্লাহ্র আদেশ পালন করার জন্যতো বটেই, পরোক্ষে মুসলিম জীবনের নানাবিধ আইন-কানুন প্রণয়ন করার জন্য বা বিচার লাভের জন্য মসজিদে জমায়েত হওয়া ছিল অবশ্য প্রয়োজনীয়। এ মসজিদে অবস্থান করেই মুসলিমরা এ সৃষ্টিতত্ত্ব বা এ দুনিয়ার বিকাশের আদি কারণ সম্বন্ধে গবেষণা করতেন। এ মসজিদে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে শিক্ষালাভ করতেন। কাজেই এ দুনিয়ার নানা বিষয়ে খাঁটি জ্ঞান লাভের জন্য সালাত সম্পাদন উপলক্ষে মসজিদে সমবেত হওয়া মুসলিমদের জীবনে অবশ্য কর্তব্য ছিল।
\r\n
অপরদিকে সালাতের মধ্যে মানব-জীবনের যে পূর্ণ আত্মসমর্পণের ভার রয়েছে সে সূত্রে মানুষের পক্ষে আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভেরও সম্ভাবনা রয়েছে। আল্লাহ্র কাছে আত্মসমর্পণের মাধ্যমেই আল্লাহ্র প্রকৃতরূপের পরিচয় পাওয়া যায় বলে মানব-জীবনে রয়েছে দৃঢ় প্রত্যয়। ইসলামের অপর দিক হচ্ছে মারিফত। তাতে বলা হয় সালাতের মাধ্যমে সালাত আদায়কারীর দিলের মধ্যে রোশনী বা জ্যোতির আবির্ভাব হয় এবং সে জ্যোতির আলোকে আল্লাহ্র স্বরূপ সম্বন্ধে মানুষের পক্ষে উপলব্ধি করার সুযোগ দেখা দেয়।
\r\n
যেহেতু ইসলামের মধ্যে ইহলৌকিক অথবা পারলৌকিক বলে এমন কোন স্পষ্ট ভেদরেখা নেই, এজন্য সালাতের মধ্যে যদিও এরূপ কোন ভাগ করা হয়নি তবুও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সালাতের মধ্যে আধ্যাত্মিক জীবন বিকাশেও পদ্ধতি রয়েছে।
\r\n
সিয়াম ও রমযানের তাৎপর্য
\r\n
আমরা সওমের পরিবর্তে ‘রোযা’ শব্দ ব্যবহার করি। ‘রোযা’ ফারসি ভাষার একটি শব্দ। তার সোজা অর্থ উপবাস বা যাকে ইংরেজিতে বলে fasting। কুরআনুল কারীমের ভাষায় যাকে মুসলিমদের জীবনে আমল করার জন্য তাগিদ দেয়া হয়েছে তা কেবল উপবাস নয়, তার নাম সওম। তার অভিধানগত অর্থ নিবৃত্তি। কিসের নিবৃত্তি? এ সম্বন্ধে শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহলভী বলেছেন, ‘যেহেতু পাশবিক কামনার প্রাবল্য ফেরেশতাসুলভ চরিত্র অর্জনের পক্ষে অন্তরায়, সুতরাং উহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা পরিহার্য। যেহেতু পাশবিক শক্তির প্রাবল্য উহার উত্তেজনা ও উহার প্রতিরোধ কঠিন হওয়ার কারণ অথবা পানাহার এবং জৈবিক আসক্তি পূত চরিত্র অর্জনের পক্ষে একটি পর্দা বা অন্তরায় যে, শুধু পানাহারে স্বাধীনতা এতবড় অন্তরায় নয়। সুতরাং এই সকল উপকরণকে পরাভূত করে পাশবিক শক্তিকে আওয়ত্তাধীন করা হইতেছে সওমের সূক্ষতম তাৎপর্য। এতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় সওমের প্রকৃত লক্ষ্য হচ্ছে পাশবিক প্রবৃত্তির দমন ও উন্নততর প্রকৃতির বিকাশ।
\r\n
এজন্য দেখা যায়, এ দুনিয়ার যারা সত্যিকার মনুষ্যত্ব লাভ করেছেন অর্থাৎ নবী-মুরসালগণ তাঁর আল্লাহ্র প্রত্যাদেশ পাওয়ার পূর্বে দীর্ঘকাল সওমের সাধনা করেছেন। মরহুম মাওলানা সুলেমান নদভীর বর্ণনা থেকে পাওয়া যায় হযরত মূসা আলায়হি ওয়া সাল্লাম তুর পাহাড়ে আল্লাহ্র প্রত্যাদেশ হিসেবে তওরাত গ্রহণ করার সময় দীর্ঘ চল্লিশ দিন পর্যন্ত আহার পানীয় ত্যাগ করে মানবিক জীবনের বহু উর্ধ্বে আরোহণ করেছিলেন। হযরত ঈসা আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইনজীল প্রাপ্ত হওয়ার লগ্নে দীর্ঘ চল্লিশ দিন অনুরূপ সাধনায় জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। কুরআনুল করীম নাযিল হওয়ার পূর্বে হযরত রাসূলে আকরম (সঃ)- ও দীর্ঘ একমাস কাল হেরার গুহার সাধনায় জীবন যাপন করেছেন। এ পুণ্য সময়েই লায়লাতুল কদরের মহীয়ান রাত্রে তাঁর প্রতি কুরআন নাযিল হয়েছিল। এতে সিয়ামের গুরুত্ব সম্বন্ধে এ প্রমাণ পাওয়া যায়ঃ আল্লাহ্র তরফ থেকে তার বাণী বা নির্দেশপ্রাপ্তির পূর্বে নবী ও মুরসালদের পক্ষে চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা ছিল। প্রশ্ন হচ্ছে, কিভাবে চিত্তশুদ্ধি হয় এবং সে চিত্তশুদ্ধির মূল অর্থ কি? তার উত্তরে সৈয়দ সুলেমান নদভী বলেছেন- ‘এতে সর্বপ্রথম শিক্ষা হচ্ছেঃ মানবজীবন ভোগের জন্য নয়—মানবজীবন ত্যাগের জন্য। ত্যাগের ফলে মানবজীবনে যে তৃপ্তি দেখা দেয়- ভোগের ফলে সে তৃপ্তি দেখা দেয় না’।
\r\n
সে সওমের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আল্লামা ইকবাল বড় চমৎকার ভাষায় বলেছেন, ‘সওমকে ব্যক্তিগতজীবনে পালন করাও সম্ভব। অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধির জন্য এক ব্যক্তি হয়ত বৈশাখ মাসে অথবা মহররম মাসে সওমের নীতি পালন করবেন। অপর ব্যক্তি জ্যৈষ্ঠ মাসে বা সফর মাসে সে নীতি পালন করবেন, তাতে আপত্তি হওয়ার কারণ কি? তার উত্তরে বলা যায়-এক্ষেত্রে আল্লাহ্ সুবহানা তা’আলার উদ্দেশ্য- কেবল ব্যষ্টি জীবনের সংশোধন নয়। এক্ষেত্রে আল্লাহ্র উদ্দেশ্য গোটা মানবজাতির আত্মার শুদ্ধি। এজন্য একটা নির্দিষ্ট চান্দ্রমাসে আল্লাহ্র কালামে প্রত্যয়শীল সকল মানুষের জন্যই ‘সওম’কে অবশ্যপালনীয় কর্তব্য হিসেবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এতে বিশুদ্ধ মানবজীবন তথা মুসলিম জীবনে সাম্য-ঐক্যের নীতি প্রতিষ্ঠার প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে। সকল মানুষ যাতে একই আদর্শে উদ্ধুদ্ধ হয়ে তাদের পাশবিক প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণ দমন করে, প্রকৃত মানবিক চরিত্রের বিকাশের জন্য একসঙ্গে সাধনায় লিপ্ত হয়, তার জন্য একটা বিশেষ মাসে সকলকেই তার অনুশীলনে তাগিদ দেয়া হয়েছে।
\r\n
প্রকৃতপক্ষে সালাত(নামায) বা সিয়াম ইসলামী জীবনধারার কোন খাপছাড়া অনুশীলন নয়। ইসলামের মূল ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহ্র রব নামক গুণ ও সার্বভৌমত্বের ওপর প্রত্যয়। আল্লাহ্কে এক, অদ্বিতীয় স্রষ্টা, প্রতিপালক ও বিবর্তনকারী হিসেবে গ্রহণ করলে এবং তাকেই এ বিশ্বজগতের একমাত্র মালিক বলে স্বীকার করলে সওম বা সালাত অপরিহার্য রূপে দেখা দেয়। আল্লাহ্ যদি এ জগতের স্রষ্টা হন এবং তিনি যদি এ জগতের সকল জীবকে প্রতিপালন করেন এবং তিনিই যদি এ দুনিয়াকে অবনত পর্যায় থেকে উন্নততর পর্যায়ে নিয়ে যান এবং এ বিশ্ব বিধানে যা কিছু রয়েছে তার মালিকানা একমাত্র তাঁরই হয়-তাহলে তাঁর সেসব গুণের আলোকে এ দুনিয়াকে ঢালাই করে সাজানো-গোছানো প্রত্যেক মুমিন-মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়ে। এ দুনিয়ায় জন্মগত তারতম্য রয়েছে কেউ বা সুন্দর, কেউ বা কুৎসিত, কেউ বা কালো, কেউ বা সাদা, কেউ বা ধনী, কেউ বা নির্ধন, কেউ শক্তিশালী, কেউ বা নিতান্তই দুর্বল। সকলের স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহ্র সকলের প্রতিই রয়েছে সমান স্নেহ, সমান করুণা, সমান সহানুভূতি। অথচ মানুষ তার নিজ সম্বন্ধে এতো বেশি কেন্দ্রিক যে, সে তার নিজের সম্বন্ধে ভাবনায় সবসময়ই লিপ্ত। এজন্য যাতে সে দরিদ্র জনসাধারণের অর্থাৎ যারা সারা মাসে একবেলাও পেট ভরে আহার করতে পারে না, তাদের দুঃখ-কষ্টের অনুভূতি যাতে অপরাপর সকল মানুষের হয়, তার জন্য ধনী, দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেই যাতে ক্ষুধার যাতনা বুঝতে পারে, তার জন্য রমযান মাসে দিনের বেলা সকলের জন্যই পানাহার থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। এতে ‘রব’ হিসেবে আল্লাহ্ কেবল এ দুনিয়াকে নয়- দুনিয়ার মানুষকে বিবর্তনকারী হিসেবে উন্নততর মানসিকতার পর্যায়ে উত্তোলন করতে প্রয়াসী।
\r\n
দ্বিতীয়ত, এ মাসে ‘সওমের’ অনুশীলনে রত মানুষ যাতে সর্বাবস্থায় বুঝতে পারে,তার অধিকারে ধন-দওলত থাকলেও সে দওলত যথেচ্ছ ব্যয় করার অধিকার বা ভোগ করার অধিকার তার নেই; তাকে ভোগ করতে হবে সে সার্বভৌম শক্তির নির্দেশমতো। তাকে বুঝতে হবে তার অধিকারভুক্ত সম্পদে তার মালিকানা নেই। মালিকানা রয়েছে সর্বতোভাবে আল্লাহ্ সুবহানা তা’আলার। তাই সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও এ মাসে সে সম্পদের ভোগ থেকে বিরত থাকতে হচ্ছে।
\r\n
তাই আমাদের পক্ষে রমযান মাসকে শুধু পানাহার থেকে বিরত থাকার মাস হিসেবে গণ্য করলে চলবে না। যাতে পাশবিক প্রবৃত্তিকে দমন করে প্রকৃত মনুষ্যত্ব আমরা লাভ করতে পারি এবং আল্লাহ্র ‘রব’ ও ‘ মালিক’ নামক গুণাবলির রুপায়নে সফল ও সার্থক হতে পারি সে-ই হবে রমযান মাসে আমার সাধনা।
\r\n
হজ্জ ও কুরবানী
\r\n
ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে হজ্জের একটা বিশেষ স্থান রয়েছে। হজ্জ ও কুরবানী উভয়েই একই সূরার পাশাপাশি তিনটি আয়াতে অবতীর্ণ হয়েছে বলে তাদের মধ্যে যে পারস্পরিক যোগসূত্র রয়েছে সে সম্বন্ধেও আমাদের অবহিত হওয়া উচিত। সঙ্গে সঙ্গে তাদের মর্মও আমাদের উপলব্ধি করা কর্তব্য।
\r\n
প্রত্যেক ধর্মেরই একটা রয়েছে প্রচারিত দিক, অপরটি হচ্ছে আনুষ্ঠানিক দিক। প্রত্যেক ধর্মেরই প্রত্যয়ের মূলে থাকে ঐতিহাসিক পটভূমি ও দার্শনিক তত্ত্ব। অনুষ্ঠানে সে প্রত্যয়েরই মূর্ত রূপ দেওয়া হয়। অনুষ্ঠান প্রবল হয়ে উঠলে ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানের ভিত্তিতে অবস্থিত ঐতিহাসিক ও দার্শনিক দিকের আলোচনাও আমাদের কর্তব্য।
\r\n
কুরআন-উল-করীমের ‘হজ্জ’ নামক সূরার হজ্জ সমাপন সম্বন্ধে বলা হয়েছে-
\r\n
“ এবং যখন আমি ইবরাহীমের জন্য সেই গৃহের স্থান নির্ধারণ করিয়া বলিয়াছিলাম যে, আমার সহিত কোন বিষয়কেই অংশীদার করিও না এবং প্রশিক্ষণকারীগণের জন্য ও দন্ডায়মানগণের জন্য এবং রুকু ও সিজদাকারীগণের জন্য আমাদের গৃহকে পবিত্র রাখিও”। (সূরা হজ্জ)
\r\n
“ এবং মানবগণের মধ্যে হজ্জ সম্বন্ধে ঘোষণা কর, -তাহারা তোমার নিকট পদব্রজে ও ক্ষীণকায় উষ্ট্রোপরি সমস্ত সুদূর পথ অতিক্রম করিয়া আগমন করিবে”।(সূরা হজ্জ)
\r\n
“যেহেতু তাহারা নিজেদের উপকারের জন্য উপস্থিত হয় এবং পরিজ্ঞাত দিনসমূহে তিনি তাহাদিগকে পালিত পশু হইতে যাহা দান করিয়াছেন যেন তদুপরি তাহারা আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করে”। (সূরা হজ্জ)
\r\n
প্রথমোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ মক্কার পবিত্র কাবাগৃহের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র সঙ্গে যেন অন্য কোন কিছুকে অংশীদার না করা হয় এবং যারা মনোনীত উপাসনা, প্রার্থনা ও প্রদক্ষিণ করতে আসে তাদের জন্য এ ঘরকে পবিত্র রেখো। উপরোক্ত আয়াতের শানে নযুলে লিখা হয়েছে, আরবের অংশীবাদী পৌত্তলিকেরা এবং আরববাসী য়াহুদী ও খ্রিষ্টান সম্প্রদায় হযরত ইবরাহীম (আঃ)- কে একজন মহামান্য নবী বলে সম্মান প্রদর্শন করতো। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রতিমা পূজা থেকে বিরত হয়নি। জনাব রসূল-ই-আকরাম (সঃ) ও তাঁর অনুগামীগণ আল্লাহ্র অংশীবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না বলে কুরায়শরা তাদের কা’বাগৃহে প্রবেশ করতে দিত না। তাদের অত্যাচার ও অনাচারের বিরুদ্ধে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে ভ্রান্ত ও বিপথগামী আরবগণকে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে—“ হে আরববাসী! আমরাই আদেশে ইবরাহীম (আঃ) নবী এ ঘর তৈরি করেছিলেন এবং আমারই আদেশে বিশ্ববাসীর কাছে হজ্জ ও কুরবানীর মর্ম ঘোষণা করেছিলেন। আমি তাকে আদেশ করেছিলাম অংশবাদিতা ও পৌত্তলিকতা থেকে আমার ঘরকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে আমার ইবাদত করতে। তোমরা এতই অকৃতজ্ঞ যে, ইবরাহীমের আদেশ লঙ্ঘন করেছো এবং তার উপদেশের বিরুদ্ধে এ পবিত্র গৃহে প্রতিমা স্থাপন করে তার উপাসনা করেছো।আমি আমার সত্য উপাসকগণের জন্যই এ পবিত্র গৃহ নির্ধারিত করেছি, তোমরা তাদের বাধা দিয়ে ধর্মদ্রোহিতার চরম নিদর্শন প্রকাশ করছো। শেষোক্ত আয়াতদ্বয়ে হযরত ইবরাহীম (আঃ) কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, “তুমি সমগ্র মানবজাতির জন্য হজ্জ সম্বন্ধে ঘোষণা করে দাও, তারা যেন নিজেদের কল্যাণ ও পাপ মুক্তির জন্য প্রতি বৎসরের নির্ধারিত দিনে এ পুণ্যধামে উপস্থিত হয় এবং তাদের জন্য আমি যে গৃহপালিত পশু বৈধ করেছি, তা থেকে যেন তারা তাদের মনোনীত ও নির্ধারিত পশু আমার নামে উৎসর্গ করে”।
\r\n
এক্ষেত্রে মানুষের কল্যাণ কোথায়? নিশ্চয়ই এক বিশেষ কল্যাণ রয়েছে। কারণ হজ্জব্রত পালন উপলক্ষে দেশ-বিদেশের নানা ভাষাভাষী লোকেরা এখানে সমবেত হলে তাদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান হবে। এক দেশের সঙ্গে অপর দেশের লোকের পরিচয় হবে এবং তাদের মধ্যে ইখওয়ান বা ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে উঠবে। গৃহপালিত পশু উৎসর্গ করতে আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্য ও তার সৃষ্ট জীবকে তারই নামে উৎসর্গ করার রয়েছে মহান সুযোগ। প্রকৃতপক্ষে গৃহপালিত গরু,মহিষ,উট, দুম্বা বা বকরি মানুষের কাছে এমন প্রিয় হয়ে ওঠে যে, তাদের অনুপস্থিতিতে বা মৃতুতে মানুষ শোকে বিহ্বল হয়ে পড়ে। কুরবানীতে সেই সব মনোনীত ও প্রিয় পশুকে আল্লাহ্র নামে উৎসর্গ করতে এ প্রথার লক্ষ্য স্পষ্ট হয়ে পড়ে। এতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন আল্লাহ্র বান্দা তার সবকিছুকে আল্লাহ্র নামে উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত হয়। প্রকৃতপক্ষে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কুরবানী প্রথার সৃষ্টি হয়েছে। কুরাবানীর ঐতিহ্যের মধ্যে হযরত ইবরাহীম খলিলউল্লাহ (আঃ) কর্তৃক তাঁর পুত্র ইসমাইল (আঃ) কে কুরবানী দেওয়ার ঘটনা। যে ক্ষেত্রে পিতা হয়েও আল্লাহ্র সন্তোষ লাভের জন্য নবী মুরসাল তার পুত্রের গর্দানে ছুরি চালাতে সবসময় প্রস্তুত ছিলেন-সেক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ গরু, উট,দুম্বা,বকরি প্রভৃতি পশুকে আল্লাহ্র নামে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হবে না কেন?
\r\n
কাজেই ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে হজ্জ ও কুরবানীর সার্থকতা সম্বন্ধে অনুধাবন করলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো আমাদের কাছে পরিস্কার হয়ে পড়ে। হজ্জব্রত পালনের সঙ্গে রয়েছে হযরত ইবারাহীম (আঃ)- এর স্মৃতি বিজড়িত। আল্লাহ্ তাঁকে দিয়ে একমাত্র তাঁরই উপাসনার জন্য এ ঘর তৈরি করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।
\r\n
অথচ তাঁরই বংশধর ও তাঁর স্বদেশবাসী লোকেরা সে ঘরেই করত প্রতিমা পূজা এবং প্রকৃতপক্ষে যারা একেশ্বরবাদী তাদের সে ঘরে প্রবেশের অনুমতি দিতো না। আল্লাহ্র অভিপ্রায় অনুসারে যারা হজব্রত পালন করেন তারা একেশ্বরবাদের স্বাদ পাবেন এবং পরস্পরের সঙ্গে তারই মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের পর্যায়ে উন্নীত হবেন।
\r\n
হজ্জ ও কুরবানীর দার্শনিক দিকের আলোচনা করলে দেখা যায়, হজ্জের মূল লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহ্র তওহীদবাদের প্রতিষ্ঠা। যাতে সে তওহীদের গোড়া পত্তনকারী হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ধ্যান-ধারণার সঙ্গে মানুষ পরিচিত হয় তার জন্যই মানুষকে একালে আহ্বান করা হয়েছে। তওহীদবাদের প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এত জোরালো দাবি কেন? তওহীদের সার্থকতা হচ্ছে মানুষে মানুষে প্রভেদের বিলোপ সাধন। একই আল্লাহ্র বান্দা হিসেবে এ দুনিয়ার মানুষ সকলেই সমান। ভাষা, বর্ণ, রক্ত, আর্থিক প্রভেদ যাতে এ দুনিয়ার মানুষের মধ্যে কোন ভেদবুদ্ধি সৃষ্টি করতে না পারে, সেজন্য ভৌগোলিক পূজ্য দেবতাদের বা পিতৃপিতামহদের পূজ্য দেবতাদের বর্জন করে তওহীদের ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হওয়ার জন্য কুরআনুল করীমে তাগিদ দেয়া হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, ‘ইবরাহীম (আঃ)- এর বংশধর বলে দাবি করা সত্ত্বেও তোমরা আমার আদেশ পালন করছো না- তাতে তোমরা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হচ্ছো।
\r\n
তওহীদের ধারণা অত্যন্ত ব্যাপক। তার মধ্যে সতত সচেতন, ক্রিয়াশীল সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, বিবর্তনকারী, এক সত্তার যেমন ধারণা রয়েছে তেমনি ন্যায়বিচারক ও সার্বভৌম সত্তার ধারণাও রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তওহীদপন্থীর কাছে আল্লাহ্র নিরানব্বইটা নাম এক একটি গুণও বটে এবং মানবজীবনের পক্ষে আল্লাহ্র পরিচয়েরও এক একটি মাধ্যম বটে। সঙ্গে সঙ্গে এগুলো মানবজীবনের আদর্শও বটে। মানুষ এদের মাধ্যমে আল্লাহ্র সর্বাঙ্গীণ পরিচয় না পাক, এগুলোর অনুসরণ করে নিজের জীবনকেও উন্নত করতে পারে। এদের মধ্যে আবার অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ। রব হলে যেমন তাঁকে সৃষ্টিকর্তা, বিবর্তনকারী ও পালনকর্তা হতে হবে তেমনি তাঁকে বিচারপতিও হতে হবে, তাকে দয়ালুও হতে হবে। ন্যায়বিচারক হলে এ দুনিয়ার সকল জীবের প্রতি তাঁর সমদৃষ্টি থাকতে হবে, যাতে সকল জীবই আহার লাভ করতে পারে তার ব্যবস্থাও করতে হবে। মানুষের বেলায় শোষক ও শোষিত বলে কোন বিশেষ শ্রেণী থাকবে না। এ দুনিয়ার সম্পদ যাতে এ দুনিয়ার সকল মানুষই সমানভাবে ভাগ করে ভোগ করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। কাজেই সমাজ ব্যবস্থা সাম্যবাদমূলক হওয়া উচিত।
\r\n
কুরআনুল করীমে এ জন্যই তওহীদের ওপর এত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কারণ তওহীদ কেবল বিশুদ্ধ দার্শনিক ধারণা নয়, তওহীদ ও তার আনুষঙ্গিক নানাবিধ গুণের সঙ্গে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের সংশ্রব বর্তমান।
\r\n
কুরবানীর মূল তাৎপর্য কুরাআনুল-করীমের মধ্যেই বর্ণনা করা হয়েছে। “কুরবানীর পশুর গোশত অথবা উহাদের রক্ত আল্লাহ্র নিকট উপনীত হয় না বরং তোমাদের সংযমই উপনীত হয়ে থাকে”। এতে স্পষ্ট বোঝা যায়, কুরবানী একটা পশুহত্যার নিষ্ঠুর অনুষ্ঠান নয়। এতে প্রিয় পশুকে আল্লাহ্র পথে উৎসর্গ করাতে যে দৃঢ়চিত্ততা,কর্তব্যবোধ ও সংযমের প্রয়োজন তারই পরীক্ষার মূল।
\r\n
যাকাত
\r\n
স্বতঃপ্রণোদিত, উদ্ধৃত্ত অর্থ বা অন্য কোন সম্পদ আত্মার কল্যাণের জন্য দান করাই যাকাতের মূল উদ্দেশ্য। পূর্বেই বলা হয়েছে, আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করে নিলে এ দুনিয়ার কোন সম্পদের ওপরই মানুষের মালিকানা থাকতে পারে না।
\r\n
মানুষ নিজেকে তার কাছে অর্পিত অথবা তার উপার্জিত সম্পদের হিফাজতকারি(Custodian) বলে গণ্য করে সে সম্পদকে আল্লাহ্র নির্দেশ মতে ভোগ করবে। তবে এ নীতি গ্রহণ করেও তার চিত্তের বা রূহের বিশুদ্ধির জন্য তার কাছে সঞ্চিত বা উপার্জনকৃত সম্পদের জন্য তাকে একটা নির্দিষ্ট অংশ প্রকৃতপক্ষে যারা হকদার তাদের উদ্দেশ্য দান করতে হবে। সেসব দেশের বায়তুলমালে সে সম্পদের অংশ দান করতে হবে।
\r\n
কুরআনুল-করীমের নির্দেশ ও আল্লাহ্র রসূলের ব্যাখ্যা মতে সোনারূপা যাদের কাছে সঞ্চিত তাদের পক্ষে শতকরা আড়াই ভাগ রূহের বিশুদ্ধির জন্য দিতে হবে।
\r\n
তবে এ সর্বাবস্থায় এ দানকে ইনকাম ট্যাক্স বলে গণ্য করা যাবে না। এ ট্যাক্স হচ্ছে রূহের বা আত্মার বিশুদ্ধির জন্য। ইসলামী রাষ্ট্রের সকল সম্পদের মালিকানা একমাত্র আল্লাহ্র। কাজেই সে রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য যখনই যা প্রয়োজন রাষ্ট্র ব্যক্তিবিশেষের কাছে রক্ষিত সম্পদ থেকে অবাধে আদায় করতে পারে। ইসলামী রাষ্ট্রে ব্যক্তিবিশেষকে উপার্জনের অধিকার দান করলেও সে উৎপাদিত সম্পদ ভোগের সীমা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। এ সম্বন্ধে ইমাম ইবনে হাজম তাঁর ‘মুহাল্লা’য় বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।
\r\n
জিহাদ
\r\n
জিহাদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে কঠোর পরিশ্রম বা অবিরাম চেষ্টা বা সাধনাতে লিপ্ত হওয়া। তার সাধারণত ইসলামকে এ বিশ্বে টিকিয়ে রাখার জন্য সংগ্রামে লিপ্ত হওয়াকে জিহাদ নামে অভিহিত করা হয়। তবে এ কথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, ইসলামের পরিভাষায় জিহাদ অত্যন্ত ব্যাপক অর্থেই ব্যবহৃত হয়। মানবজীবনকে সুন্দর, সরল ও মঙ্গলময় পথে পরিচালনা করার যতগুলো প্রতিবন্ধক রয়েছে- তার বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম করাই জিহাদের মূল লক্ষ্য-সংগ্রাম ব্যক্তিবিশেষের জীবনে (ক) প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে যেমন হতে পারে, (খ) তেমনি তার দৈহিক নিরাপত্তার জন্য আততায়ীর বিরুদ্ধেও হতে পারে, (গ) স্বীয় এবং সামাজিক আর্থিক বিধানের বিরুদ্ধেও হতে পারে, (ঘ) মানবজীবনের কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধেও হতে পারে এবং (ঙ) নফস ও কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ। একে একে তার আলোচনা করা যাক।
\r\n
(ক) ব্যক্তিগত কর্তব্য পালনে জিহাদের অর্থ হচ্ছে- সকল প্রতিকূল পরিবেশে-ঈমানকে বজায় রেখে কর্তব্য পালনে সচেষ্ট থাকা অর্থাৎ মানুষের পক্ষে আল্লাহ্ যেসব কর্তব্য নির্ধারণ করেছেন- সকল প্রকার প্রতিকূল পরিবেশেও সে কর্তব্য পালন করতে মানুষ যেন কোন অবস্থায়ই নিবৃত্ত না হয়। এ প্রকার জিহাদের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় মক্কার নবদীক্ষিত মুসলিমদের উৎসর্গীকৃত জীবনে। দীর্ঘ তেরো বৎসরকাল তাঁরা মক্কার কুরায়েশদের হাতে যে অমানুষিক নির্যাতন সহ্য করেছিলেন দুনিয়ার ইতিহাসে তার কোন দৃষ্টান্ত নেই। অথচ এসব মুমিন-মুসলিমগণ তাদের প্রত্যয় থেকে একবিন্দুও বিচলিত হননি। শত অত্যাচার সহ্য করেও স্বকীয় প্রত্যয় থেকে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে তাঁরা এ বিশ্বে জিহাদের এক আদর্শ স্থাপন করেছেন।
\r\n
(খ) সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠায় ও প্রচারে প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধাচরণ যখন সীমা অতিক্রম করে এবং ন্যায়পন্থীদের জ্ঞান ও মালের নিরাপত্তার চরম সংকট দেখা দেয় তখন এ জিহাদ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। আত্মরক্ষার জন্য আততায়ীকে যেমন মানুষ হত্যা করতে পারে,তেমনি ধর্মের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপকারীদের হাত থেকে ধর্ম রক্ষার্থে তাদের সাথে জিহাদ করাও অবশ্য কর্তব্য।
\r\n
আত্মরক্ষায় সশস্ত্র যুদ্ধ করার অনুমতি দিয়ে এই আয়াত নাযিল হয়। “ যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয় তারা অত্যাচারিত বলে তাদের (যুদ্ধের) অনুমতি দেয়া হলো। আর এ কথা নিশ্চিত যে, আল্লাহ্ তাদের জয়যুক্ত করতে সম্পূর্ণ ক্ষমতাবান। (যুদ্ধ দ্বারা অত্যাচারিত তারাই) যাদেরকে তাদের দেশ থেকে অন্যায়ভাবে বহিস্কার করা হয়েছে-শুধু এই কথা বলার অপরাধে যে, “আমাদের রব(প্রভু) আল্লাহ্”।
\r\n
(গ) এই কথা আজ সর্বজনস্বীকৃত যে, আর্থিক সংস্থান ব্যতীত কোন মহৎ কর্মই সম্পাদিত হতে পারে না। এজন্য আর্থিক দিক থেকে জিহাদের প্রয়োজন রয়েছে। আর্থিক জিহাদের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্র রাজত্ব এ দুনিয়ার প্রতিষ্ঠা করার জন্য সর্বপ্রকার আর্থিক সম্পদ ত্যাগের জন্য প্রস্তুতি। মানুষ অন্যায়ভাবে ধনসম্পদকে জীবনযাত্রার মাধ্যম হিসেবে গণ্য না করে জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য বলে জ্ঞান করে সকল সময়েই তাকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়। তবে যারা এ জীবনে আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বে সম্পূর্ণ প্রত্যয়শীল তাদের পক্ষে তাদের কাহচে সঞ্চিত ধন-দওলত গচ্ছিত সামগ্রীর মত। তারা অবাধেই আল্লাহ্র রাস্তায় সবকিছু বিলিয়ে দিতে পারে। তবে যেহেতু সকল মানুষই একই জীবনের অধিকারী তাই যাতে সকল মানুষই একইভাবে আল্লাহ্র পথে ধনসম্পদে বিতরণের জন্য প্রস্তুত হয়- এজন্যই এ আর্থিক জিহাদের জন্যও তাগিদ দেয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে কুরআনুল-কারীমে বলা হয়েছে, “যুদ্ধোপকরণ অল্প হোক আর অধিক হোক-তোমরা বহির্গত হও এবং তোমাদের ধনসম্পদ ও জীবন উৎসর্গ করে আল্লাহ্র পথে জিহাদ কর। ইহা তোমাদের পক্ষে উত্তম যদি তোমরা বিজ্ঞ হয় (সূরা তওবাঃ ৬)”। অন্যত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, “নিশ্চয়ই মুমিন তারাই, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তৎপর তারা এ বিষয়ে কোন সন্দেহ করেনি এবং ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করেছে, তারাই (ঈমানের দাবিতে) সত্যবাদী (হুজুরাতঃ ২)”।
\r\n
(ঘ) এ কথা সর্ববাদীসম্মত যে, যখনই কোন জাতি জ্ঞানচর্চায় পরাংমুখ হয়েছে, তখনই সে জাতির জীবনে নেমে এসেছে চরম দুর্ভোগ। পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায়, সত্য ও অসত্যের মধ্যে প্রভেদ করতে না পেরে তখনই সে জাতি তার জীবনে ডেকে এনেছে ঘোর অমঙ্গল। কথিত আছে- মিসরের সম্রাট যখন খোদায়ীর দাবি করতে প্রস্তুতি নিচ্ছিল তখন তার পূর্বে সে তার রাজ্যে জ্ঞানচর্চা বন্ধ করে দিয়েছিল। শুধু তাই নয়-সবগুলো শিক্ষাকেন্দ্র ধ্বংস করে দিয়েছিল। তার ফলে সমগ্র দেশ অজ্ঞানতার অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয়ে গেল তখনই তার পক্ষে খোদায়ী দাবি করা সহজ হয়ে পড়লো। এজন্য খাঁটি মুমিনের পক্ষে সর্বদা জ্ঞানের দীপশিখা প্রজ্বলিত করার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত হতে হবে। জ্ঞানের জন্য জিহাদের অর্থ হচ্ছে-সর্বপ্রকার অজ্ঞানতা ও আদর্শ বিচ্যুতির বিরুদ্ধে জিহাদ। ইসলাম মানবজীবনের আলোকেই এ জিহাদের নীতির প্রবর্তন করেছে। এ জিহাদের অর্থ হচ্ছে কোন অবস্থায়ই মানবজীবনের অজ্ঞানতার অন্ধকার ঘনীভূত হওয়ার সুযোগ দান না করা, ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনকে সর্বদাই-সর্বাবস্থায় অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে মুক্ত রাখা।
\r\n
(ঙ) নাফস বা কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ-মানব জীবনে প্রবৃত্তির স্বেচ্ছাচারিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতাই নৈতিক ও আত্মিক অবনতির একমাত্র কারণ। মানুষ যদি নাফসকে বল্গাহীন অশ্বের মত যথাতথা বিচরণ করতে ছেড়ে দেয়-তা’হলে সে প্রবৃত্তির দ্বারা তার ব্যক্তিগত জীবনের যেমন অমঙ্গল হতে পারে, তেমনি সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় জীবনেরও সর্বপ্রকার অকল্যাণ হতে পারে। বল্গাবিহীন অশ্বের দ্বারা যেমন অঘটন ঘটতে পারে তেমনি বল্গাবিহীন নাফসের দ্বারাও নানা সংকট দেখা দিতে পারে। এজন্য শুধু ইসলাম ধর্মে নয়, জগতের সকল ধর্মেই সংযত জীবন যাপন করার জন্য উপদেশ দেয়া হয়েছে। তবে ইসলামে এ নাফসের বিরুদ্ধে জিহাদকে সর্বোত্তম জিহাদ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ইসলামে এ জিহাদকে বলা হয়েছে ‘জিহাদ-ই-আকবার’। ইসলামের ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে – একদা একদল সাহাবা যখন কোনও এক ধর্মযুদ্ধ থেকে ফিরে এলেন, তখন হযরত রসূলই আকরম (সঃ) তাঁদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন, “এইবার তোমার ছোট জিহাদ থেকে প্রত্যাবৃত্ত হলে”। অর্থাৎ নিজের নাফসের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য তোমাদের প্রস্তুতি নিতে হলো। এক হাদীসের বর্ণনায় রয়েছে- একদা হযরত নবী করীম (সঃ) সাহাবাগণকে জিজ্ঞেস করলেন, “তোমরা মল্লবীর বা পাহ্লোয়ান কাকে বলে থাকো-? সাহাবাগণ আরয করলেন- যাকে কুস্তিতে কেউ পরাভূত করতে পারে না আমার তাকেই পাহলোয়ান বলে থাকি। জনাব রসূলল্লাহ (সঃ) বললেন- না, তা নয়, বরং যে ব্যক্তি তীব্র ক্রোধের সময়ও নিজের নাফসকে সংযত রাখতে পারে সে-ই (প্রকৃত) পাহলোয়ান”।
\r\n
এতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয়, ইসলামের দৃষ্টিতে আমাদের পাশবিক প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই প্রকৃষ্টতম জিহাদ।
\r\n
সামাজিক জীবনে নর-নারী সম্পর্কঃ ইসলামী সমাজে নারীর মর্যাদা ও অধিকার
\r\n
ইসলামের দৃষ্টিতে আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশের বেলা নরনারীর মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। স্ত্রী-পুরুষের দাবী দাওয়াও পরস্পরের ওপর সমান। বরং দেনমোহর ইত্যাদি বাবত স্ত্রীর দাবি পুরুষের ওপর প্রবল। স্ত্রীর খোরপোশ প্রভৃতি সম্পূর্ণ বহন করা পুরুষের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে নারীকে পুরুষের সমান অধিকার দেওয়া হয়নি-যেমন উত্তরাধিকার, বহুবিবাহ ইত্যাদি নারীর অধিকার পুরুষের সমান নয়।
\r\n
কেন নারীর অধিকার পুরুষের সমান নয়- এ সম্বন্ধে আলোচনা করলে দেখা যায় অনেকটা কারণ বর্তমান। সকল সমাজেই এবং সকল দেশেই মর্যাদা ও অধিকারের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কোন ব্যক্তিকে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা দান করলে তাকে সর্বশ্রেষ্ঠ অধিকার নাও দেওয়া যেতে পারে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ অধিকার দান করলেও সর্বোচ্চ মর্যাদা দান নাও করা হতে পারে। পুরাকালে সকল দেশেই রাজাকে সর্বশ্রেষ্ঠ অধিকার দান করা হত। এখনও যেসব দেশে রাজতন্ত্র টিকে রয়েছে, সে সব দেশে রাজার অধিকার সর্বোচ্চ। তবে সেসব দেশের জনগণ আন্তরিকভাবে রাজাকে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা দান করতে প্রস্তুত নাও হতে পারে। রাজার মর্যাদা নির্ভর করে তার কৃতকর্মের ওপর। তিনি মানবপ্রেমিক বা মানবদরদী হলে অবশ্যই সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী হবেন। তবে তার আচার-ব্যবহার কুৎসিৎ এ জঘন্য হলে তাকে কেউই গুরুজনে মর্যাদা দান করতে প্রস্তুত হবে না।
\r\n
মর্যাদা ও অধিকারের এ পার্থক্য আমাদের এ উপমহাদেশেই বিশেষভাবে ফলে উঠেছে। প্রায় সবসময়েই রাজন্যবর্গকে সকল রকমের অধিকার দেয়া হয়েছে। তবে রাজন্যবর্গ আধ্যাত্মিক সাধনায় উন্নত থেকে, সন্ন্যাসী বা পীর-দরবেশগণের নিকট সর্বদাই কৃতাঞ্জলিপুটে উপস্থিত হয়েছেন। অবদান শতকের একটা তরজমা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেনঃ
\r\n
নৃপতি বিম্বিসার-
\r\n
নামিয়া যুদ্ধে মাগিয়া লইয়া পদ-নখ-কণা তার-
\r\n
এত বড় রাজা বিম্বিসার, যার অধিকারের কোন সীমা ছিল না, সেই রাজা বিম্বিসার মর্যাদার দিক থেকে মহাজ্ঞানী বুদ্ধের পদ নখ-কণা সংগ্রহের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন।
\r\n
আমরা সাধারণত মর্যাদা ও অধিকারের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না বলে অনেক সময় আমাদের বিচারের মধ্যে ভ্রান্তি দেখা দেয়। আমাদের দেশে সাম্প্রতিক নারীজাগরণের আলোকে ইসলামী সমাজে নারীর অধিকার নিয়ে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এ অধিকারের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে অনেকেই অধিকারের সঙ্গে মর্যাদাকে এক পর্যায়ভুক্ত করে এ সমস্যাটিকে আরও জটিল করে তুলেছেন। তাই এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা উচিত। ইসলামী সমাজে নারীর মর্যাদা ও অধিকার সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করতে হলে আমাদের কুরআনুল-করীম ও হাদীসের উক্তিগুলোকে বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে। কারণ কুরআন-উল-করীম ও হাদীস শাস্ত্র হচ্ছে ইসলামের বুনিয়াদ। ইসলাম এক কালে ( অর্থাৎ খুলাফায়ে রাশেদীনের সময়) এ দুই বুনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। বর্তমানে এ দুনিয়ার কোথাও ইসলামী সমাজ বা রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নেই, তবে অদূর ভবিষ্যতে ইসলামী সমাজ গঠিত হলে এ দুটো মূল ভিত্তির ওপরই গঠিত হবে। পাক কুরআনুল-করীমে বলা হয়েছে, “তাদের জন্য তোমাদের ওপর সেই অধিকার তোমাদের জন্য যেমন তাদের ওপর রয়েছে। (সূরা নিসা)”
\r\n
এ সূরা নিসাতেই আবার বলা হয়েছে,
\r\n
“পুরুষ জাতির নেতৃত্ব রয়েছে নারীদের ওপর”।
\r\n
আবার অপর এক সূরায় বলা হয়েছেঃ
\r\n
“ তোমরা গৃহে অবস্থান কর এবং জাহিলী যুগের নারীদের মত উচ্ছৃঙ্খলভাবে চলাফেরা করো না”। (সূরা আহযাব)
\r\n
ইসলাম জগতে আল্লাহ্র রসূল (সঃ)-কে গণ্য করা হয় জীবন্ত কুরআন রূপে। কুরআনুল-করীমের প্রতিটি অক্ষর তাঁর জীবনে রূপায়িত হয়েছে বলে তিনি এ দুনিয়ার কুরআনুল-করীমের অতুলনীয় ভাষ্যকার। নারী জাতি সম্বন্ধে তাঁর উক্তির মধ্যে নিন্মলিখিত কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্যঃ
\r\n
১. সন্তানের বেহেশ্ত মায়ের পদতলে।
\r\n
২. পিতামাতার মধ্যে কাকে প্রথম সম্মান প্রদর্শন করবে, এ প্রসঙ্গে কোন এক ছেলের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেনঃ প্রথমে তোমার আম্মাকে, তারপর তোমার আম্মাকে, তারপরে তোমার আম্মাকে, তারপরে তোমার আব্বাকে।
\r\n
৩. স্ত্রীলোকেরা পুরুষের যময অর্ধেক।
\r\n
৪. একজন স্ত্রীলোকের চারটি গুণের জন্য বিয়ে হতে পারেঃ
\r\n
(ক) সে ধনী হলে, (খ) কুল গৌরবে উচ্চস্থানীয় হলে, (গ) সুন্দরী হলে ও (ঘ) পুণ্যশীলা হলে। কাজেই যে স্ত্রীলোক পুণ্যশীলা তার সন্ধান কর; যদি তুমি অন্য চিন্তা দ্বারা প্রভাবান্বিত হও, তাহলে তোমার দু’হাত কর্দমাক্ত হবে।
\r\n
৫.এ পৃথিবী ও তার অন্তর্গত সবকিছুই সম্পদ, তবে এ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ ধার্মিক নারী।
\r\n
৬. আরব দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ স্ত্রীলোক কুরায়েশদের মধ্যে সে নারীগণ যারা শিশুদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ ও তাদের স্বামীদের সম্পদের দিকে সতর্ক দৃষ্টি।
\r\n
৭.আল্লাহ্র আদেশ তোমরা তোমাদের নারীদের প্রতি উত্তম ব্যবহার করবে। কারণ, তারা তোমাদের মাতা, কন্যা ও স্ত্রী।
\r\n
৮. নারীদের অধিকার পবিত্র। যাতে তাদের অধিক কষ্ট না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রেখো।
\r\n
৯. তোমাদের নারীদের মসজিদে আসতে বাধা দিও না। তবে তাদের বাড়ি তাদের পক্ষে উত্তম স্থান।
\r\n
কুরআনুল করীম ও হাদীসের এসব উক্তিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়-নারীর মর্যাদা ও অধিকারের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। যখন বলা হয়েছে পুরুষের ওপর নারীর, নারীর ওপর পুরুষের অধিকার সমান তখন এ বিশ্বে নারীর অধিকার পুরুষের অধিকারের সমান বলে গণ্য হয়েছে। এ আয়াতের পোষকতায় রয়েছে আল্লাহ্র রসূল (সঃ)-এর হাদীসঃ স্ত্রীলোকেরা পুরুষের যময অর্ধেক। নারীদের অধিকার পবিত্র। যাতে তাদের অধিক কষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবে।
\r\n
কাজেই অধিকারের বেলায় নারী, পুরুষের মধ্যে কোন ভেদাভেদ ইসলামী সমাজে হতে পারে না। প্রশ্ন হচ্ছে কিসের অধিকার? সে অধিকারের যখন কোন সীমার মধ্যে আবদ্ধ করা হয়, তখন তাকে জীবনের সকল খেত্রের অধিকার বলেই গণ্য করতে হবে। মানবজীবনের প্রাথমিক চাহিদা হচ্ছে অন্ন-বস্ত্রের সন্ধান। অন্ন-বস্ত্র বিতরণের সময় যেমন নারী-পুরুষের মধ্যে কোন ভেদাভেদ থাকতে পারে না, তেমনি শিক্ষা, সংস্কৃতি বা জীবনের অন্যান্য অধিকার লাভের ক্ষেত্রেও তাদের অধিকার ক্ষুণ্ন করা হবে না। বর্তমান কালের গনতন্রের যুগে প্রতিনিধি নির্বাচনেও নারীর অধিকারকে পুরুষের সমতুল্য অধিকার বলেই গণ্য করতে হবে। একথা অবশ্য সত্যি যে, আল্লাহ্র রসূলের ইন্তেকালের পরে খলীফা নির্বাচনে কোন নারী অংশগ্রহণ করেন নি। সে যুগে নারীরা রাজনীতি বা রাষ্ট্রনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেননি বলে তাতে তাঁরা অগ্রসর হননি। অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অবতীর্ণ হতেও দ্বিধাবোধ করেননি। হযরত উসমান (রাঃ)- এর শাহাদাতের পরে উমাইয়াদের প্রচারণার ফলে মুসলিম জননী হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁর এ কার্যকলাপে ইজতিহাদী গলদ থাকতে পারে, তবে এতে যে নারীর রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সূচনা হয়েছে তা’অনায়াসেই বলা যায়। বর্তমান কালের রাজনীতিতে নারীরা ন্যায়-অন্যায়বোধে কেন সংগ্রামে অবতীর্ণ হবেন না তার কোন সদুত্তর নেই।
\r\n
কেবল রাজনীতি নয়, জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে যেখানে নারী ধর্মের বিপরীত কোন কাজকর্মে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে, সেখানে নারীর অধিকারকে কোন অবস্থায়ই পুরুষের অধিকারের চেয়ে খাটো করা হয়নি।
\r\n
এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে নারীর উত্তরাধিকার নিয়ে। নারীকে পুরুষের সমান উত্তরাধিকার দেয়া হয়নি। আম্মা অথবা আব্বার সম্পত্তিতে ছেলেরা যে অংশ পায়, মেয়েদের জন্য তার অর্ধেক নির্ধারিত রয়েছে। একজন পুরুষের স্ত্রী তার পরিত্যাজ্য সম্পত্তিতে সন্তান-সন্ততি থাকলে দুই আনা অংশের মালিক হয়। অথচ একজন নারী তার স্বামীর আগে মৃত্যুবরণ করলে, স্বামী তার সম্পত্তির চার আনার উত্তরাধিকার লাভ করবে।
\r\n
সাক্ষীদানকালে শুধু নারীর সাক্ষ্য ইসলামী বিধানমতে গণ্য হয় না। শতাধিক নারী হলেও তার সঙ্গে একজন পুরুষ মানুষের সাক্ষ্যের প্রয়োজন। বিয়ের বেলায় একজন পুরুষের চার স্ত্রী গ্রহণ করাও চলে। অপরদিকে নারীর পক্ষে একাধিক স্বামী একসঙ্গে গ্রহণ করার কোন উপায় নেই।
\r\n
এ সব বিষয়ে আলোচনা করতে হলে আমাদের মনে রাখতে হবে, ইসলামী সমাজ পিতৃপ্রধান বা Patriarchal। সুদূর অতীতে এবং আমাদের রসূল-ই-আকরমের (সঃ) জন্মের একশত বৎসর পূর্বেও সারা আরব দেশে মাতৃপ্রধান (Matriarchal Society) সমাজ ছিল। এমনকি হযরতের জন্মের সময়ও ইয়েমেনে মাতৃপ্রধান সমাজ প্রচলিত ছিল। পুরুষেরা নানাবিধ সংগ্রামের মধ্যে তাদের স্বাধীনতা লাভ করেছিল এবং তারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ জাহিলিয়াতের যুগে মাতৃজাতির ওপর নানাবিধ নির্যাতন করা হত। জাহিলিয়াতের যুগে পর্যুদস্ত নারী সমাজকে পুরুষের বিলাসসামগ্রী বলে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হত। সে প্রতিক্রিয়াশীলতার যুগে জন্মগ্রহণ করেও হযরত রাসূল-ই-আকরাম (সঃ) নারীকে পরম মর্যাদা দান করেছেন।
\r\n
উত্তরাধিকারের বেলায় নারীকে কেন পুরুষের সমান অধিকার দান করা হয়নি, তার উত্তরে বলা যায়-নারীদের পক্ষে পিতার সম্পত্তিতে অধিকার লাভ করার পরও স্বামীর কাছে তাদের নিরাপত্তার জন্য কাবিন লাভ করার সুযোগ রয়েছে। পুরুষের পক্ষে এরূপ সুযোগ নেই। তার ওপর নিজের স্ত্রীর ও সন্তানের ভরণ-পোষণের জন্য পরিবারের কর্তা হিসেবে পুরুষই সম্পূর্ণ দায়ী। নারীকে ভরণ-পোষণের দায়িত্ব থেকে মুক্ত করা হয়েছে। এমনকি সন্তানকে স্তন্য দান করাও নারীর পক্ষে অবশ্য কর্তব্য নয়। সে ইচ্ছা করলে সন্তানকে দুগ্ধ দান করতেও পারে, নাও করতে পারে। তার গর্ভজাত সকল সন্তানের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তার স্বামীর।
\r\n
জাহিলিয়ার নারীদের মত মুসলিম নারীগণ ভবঘুরের বা আওয়ারার মত চলাফেরা করবে না বলে তারা যাতে তাদের বাড়িতেই অবস্থান করে এরূপ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নারীরা আদেশ পালন করুন বা অন্য কোন কাজে লিপ্ত থাকুন, তাদের চলাফেরা বা অভিজ্ঞতা পুরুষ মানুষের মত এতো ব্যাপক না হওয়ারই কথা। এ জন্য তাদের সাক্ষ্যের পরিপূরক হিসেবে একজন পুরুষের সাক্ষ্যের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করা হয়েছে।
\r\n
তবে ইসলামে ‘অধিকার’ শব্দটি সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। ইসলামে ‘অধিকার’ শব্দের অর্থ কোন কিছুর ওপর ব্যক্তির মালিকানা নয়, তার হিফাজত মাত্র। যাকে ইংরাজীতে বলে Custodianship। ইসলামী সমাজে নর অথবা নারী কেউই তার ইচ্ছামত কোন সম্পদ ব্যয় বা ধ্বংস করতে পারে না। তাকে সে সম্পদের রক্ষক হিসেবে আল্লাহ্র পথে মানুষের কল্যাণের জন্য ব্যয় করতে হবে।
\r\n
বিবাহের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের অধিকারের তারতম্য সম্বন্ধে বলা যায়-ইসলামের দৃষ্টিতে যিনা বা ব্যভিচার হচ্ছে মহাপাপ। তাই যাতে কোন অবস্থায়ই নর অথবা নারী এ কাজে লিপ্ত না হয় সেজন্যই পুরুষকে বহুবিবাহের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এ দুনিয়ার মানবজাতির সংখ্যা নিয়ে আলোচনাকালে দেখা গিয়েছে, প্রত্যেক দেশেই নারীর সংখ্যা থেকে পুরুষের সংখ্যা অধিক। সাধারণভাবে শীতপ্রধান দেশে বিবাহযোগ্য পুরুষের বয়স ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ এবং বিবাহযোগ্য নারীর বয়স পঁচিশ থেকে চল্লিশ এবং বিবাহযোগ্য নারীর বয়স পনের থেকে ত্রিশ বৎসর বলা যায়। শীতপ্রধান বা গ্রীষ্মপ্রধান উভয় অঞ্চলেই বিবাহযোগ্য পুরুষের সংখ্যা নারীর চেয়ে কম। কারণ এ বয়সে পুরুষেরা নানাবিধ কাজকর্মে লিপ্ত থেকে প্রাকৃতিক বা যান্ত্রিক গন্ডগোলের জন্য প্রাণ হারায়। জগৎব্যাপী মহাসমরের সময় যুদ্ধে লিপ্ত দেশসমূহের বিবাহযোগ্য পুরুষ মানুষের সংখ্যা গুরুতরভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। কাজেই এসব সংকটকালীন সময়ের ব্যবস্থার জন্য ইসলামে একাধিক বিবাহের অনুমতি বা provision রয়েছে। তবে এসব সুযোগ দেয়া সত্ত্বেও কুরআনুল করীমে ঘোষণা করা হয়েছে, “তোমরা যদি আশঙ্কা কর যে, ইয়াতিমদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে বিয়ে করবে নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে, দু’তিন বা চার”। যেহেতু কোন ব্যক্তির পক্ষেই একাধিক স্ত্রীর সঙ্গে সমান ব্যবহার করা সম্ভব নয়, এজন্য প্রয়োজনে ব্যতীত প্রকারান্তরে তাতে নিষেধ আরোপ করা হয়েছে।
\r\n
সমানভাবে ব্যবহার করতে সক্ষম না হলে যে কোন পুরুষের পক্ষে একাধিক বিবাহ জায়েয নয় ইমাম আবু হানীফা (রঃ) বহু পুর্বেই রায় দিয়েছেন। তাঁর সমসাময়িক আব্বাসী বংশের তথাকথিত খলীফা আবু মনসুর প্রৌঢ় বয়সে এক কিশোরীর সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে তাকে বিয়ে করতে চাইলে তাঁর স্ত্রী তা সম্পূর্ণভাবে নাজায়েয বলে বাধা দেন। উভয়ের সম্মতিতে ইমাম আবু হানীফা (রঃ) কে রায় দানের জন্য আহ্বান করা হলে তিনি বলেন, “ এ সম্বন্ধে আপনি (অর্থাৎ আল-মনসুরও) রায় দিতে পারেন”। সূরা নিসার তৃতীয় আয়াতে রয়েছে- “তোমরা যদি আশংকা কর যে, ইয়াতিমদের প্রতি অবিচার করতে পারবে না, তবে বিয়ে করবে নারীদের মধ্যে যাকে, তোমাদের ভাল লাগে দু’তিন বা চার”। এতটুকু পর্যন্ত শুনে আল-মনসুর উল্লসিত হয়ে বলেন – “শুনুন বেগম সাহেবা”। তার পরে ইমাম সাহেব বলেন,- “তবে যদি মনে কর, তাদের সঙ্গে সমান ব্যবহার করতে পারবে না- তাহলে তাদের মধ্য থেকে একজনকে বিয়ে করবে। একথা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে বেগম সাহেবা উল্লসিত হয়ে বলেন- ‘শুনুন খলীফা’। তাহলে এ দুটো উক্তির মধ্যে কোনটা গ্রহণীয়-এ প্রশ্ন করা হলে ইমাম আবু হানীফা (রঃ) বলেন- যদি উভয়ের সঙ্গে সমান ব্যবহার করতে না পারেন তাহলে পুনরায় বিবাহ আপনার পক্ষে জায়েয হবে না। আল-মনসুর স্বীকার করেন-তিনি উভয়ের সঙ্গে সমান ব্যবহার করতে পারবেন না। কাজেই ইমাম সাহেব তার পক্ষে পুনরায় বিবহ নাজায়েয বলে ঘোষণা করেন। এতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয়, এক স্ত্রী উপস্থিত থাকাকালে পুনরায় বিবাহ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি যদি উভয়ের সঙ্গে সমান ব্যবহার করতে পারবে না বলে পূর্বেহ্নেই ওয়াকিফহাল হয়, তা হলে তার পক্ষে পুনরায় বিয়ে করা জায়েয হবে না। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়- আমাদের সমাজে বিবাহের এ মূল সূত্রের প্রথম দিকের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে শেষের দিকের প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে বহুবিবাহের প্রচলন হয়েছে।
\r\n
পুরুষের সঙ্গে স্ত্রী একই সমতলে বা একই কাজ করতে পারবে না-তার পক্ষে কুরআনুল-করীম ও হাদীস শরীফে কোন নির্দেশ নেই। শাসন বা বিচার বিভাগীয় কাজে, শিক্ষা ক্ষেত্রে, সাংস্কৃতিক জীবনের নানা পর্যায়ে নারীরা কেন পুরুষের সমান মর্যাদা ভোগ করবেন না। বিপক্ষে কুরআনুল-করীম বা হাদীসে কোন উক্তি নেই। কাজেই জীবনে কোন ক্ষেত্রেই নারীর অধিকারকে ক্ষুণ্ন করা হয়নি। মর্যাদার বেলায় বলা হয়েছে-পুরুষ জাতির নেতৃত্ব রয়েছে নারীর ওপর। এ নেতৃত্ব ব্যাপক অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে। বাস্তবজীবনে পুরুষের পক্ষে জীবনের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে অধিকতর অগ্রণী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে পুরুষদের পক্ষেই নেতৃত্ব গ্রহণ করার রয়েছে সমূহ সম্ভাবনা। এ নেতৃত্বের অর্থ এ নয় যে, পুরুষেরা যা বলবে বা যা করবে তা’কুরআনুল করীম বা হাদীসের বিরুদ্ধে হলেও নারী তা অবনত মস্তকে স্বীকার করবে। আর সোজা অর্থ হচ্ছে শারীরিক দিক দিয়ে পুরুষেরা অধিকতর শক্তিশালী বলে এবং জীবনের চলার পথে পুরুষদের অধিকতর অভিজ্ঞ হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় পুরুষের পক্ষে নেতৃত্ব গ্রহণ করা উচিত। তবে সর্বাবস্থায় সে নেতৃত্ব যেন নাসের (কুরআনুল-করীম ও হাদীসের) বিরুদ্ধে না হয়।
\r\n
কুরআনুল-করীমের অপর যে আয়াতে নারীদের আপন গৃহে অবস্থার করার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছে, তা এ আধুনিক বিশ্বেও নারীদের প্রতি প্রযোজ্য। জাহিলিয়া বা অন্ধকার যুগে নারীরা রাত্রিতে উচ্ছৃঙ্খলভাবে ঘোরাফেরা করতো এবং তাদের মধ্যে আবার বীরাঙ্গনা পেশারও প্রচলন ছিল। কাজেই মুসলিম মহিলা কেন, যে কোন নারীর পক্ষে তা সর্বক্ষণ পরিত্যাজ্য। এ স্থলে মর্যাদা বা অধিকারের প্রশ্ন তোলা হয়নি। নারীকে উপদেশ দেয়া হয়েছে। নারীদের পক্ষে যেমন সৎ জীবন যাপন করা কর্তব্য- পুরুষদের পক্ষেও তেমনি কর্তব্য। প্রশ্ন হচ্ছে, তা’হলে পুরুষদের উদ্দেশ না করে শুধু নারীদের সম্বোধন করে এ উপদেশ দেয়া হয়েছে কেন? তার উত্তরে বলা যায়-নারী চরিত্রকে যে কোন সমাজে সূচি বা (Index) বলা যায়। সে সমাজের নারী-জীবনে যৌন অভিশাপ দেখা দেয়, সে সমাজে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ধ্বংস হয়। নারী-সমাজে যৌনকাতরতা ব্যাপকভবে দেখা না দিলে, পুরুষ সমাজ সহজে ধ্বংস হয় না। একথা এজ সর্বজনস্বীকৃত যে, যৌন- জীবনের আবেগে পুরুষ যেভাবে অস্থির হয় নারীরা সেভাবে হয় না। তাদের মধ্যে সংযম,ধৈর্য ও সহ্যক্ষমতা অনেক বেশি। যখন নারী-সমাজ থেকে এসব গুণ অন্তর্হিত হয়, তখন নারীরাই অগ্রসর হয়ে পুরুষের সঙ্গ কামনা করে। দুর্বলচিত্ত পুরুষ তাতে অতিসহজেই সাড়া দেয় এবং সমাজজীবনে ব্যভিচারের বন্যাস্রোত হইতে থাকে। এজন্য কেবল সূরা আহযাবের মধ্যে নয়, সূরা ইউসুফের মধ্যেও প্রকারান্তরে নারীদের সাবধান করে দেয়া হয়েছে। হযরত ইউসুফের (আঃ) রূপে মুগ্ধ ইসরাতুল আযীয বা আযীযের স্ত্রী মুসলিম সমাজে জোলায়খা নামে পরিচিত। সে যখন নানাভাবে হযরত ইউসুফকে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করছিল, তখন মিসরের সম্ভ্রান্ত বংশীয়া নারীগণ তাকে ভৎর্সনা করে বলেছিল- ছি, ছি, তুমি এক গোলামের রূপে আসক্ত হয়ে আমাদের অর্থাৎ মিসরের সম্ভ্রান্ত বংশীয় নারীদের অপমান করেছো। ইসরাতুল আযীয তাঁর এ আকর্ষণ যে অনিবার্য তা প্রমাণ করার জন্য চল্লিশজন ভদ্র মহিলাকে দাওয়াত দিয়ে তাদের চল্লিশটি লেবু ও চল্লিশটি মেওয়াতরাশ হাতে দিয়ে লেবুগুলো কেটে খেতে অনুরোধ করেন। সঙ্গে সঙ্গে হযরত ইউসুফকে নাম ধরে ডাকতে থাকেন। তিনি উপস্থিত হলে তাঁর সৌন্দর্য অভিভূত কামার্ত মহিলাগন লেবু না কেটে তাদের হাতের আঙ্গুল কাটতে শুরু করে। এতে প্রত্যক্ষে বলা হয়েছে- “হে মুমিনগণ, সাবধান হও, তোমরা তোমাদের নারীগণকে কামাতুরা হতে দিও না; যদি দাও, তা’হলে মিসরের আযীযের স্ত্রীর সখিগণের মতই তাদের দশা হবে”।
\r\n
পূর্বেই বলা হয়েছে-নারী-জীবন হচ্ছে সমাজের সূচি। কাজেই তাকে পবিত্র রাখার দায়িত্ব কেবল নারীর নয়, পুরুষেরও। কারণ নারীরা পুরুষেরই মা, ভগ্নি, স্ত্রী ও কন্যা। এভাবে সরাসরি নারীদের উল্লেখ করে সূরা আহযাবে এবং পরোক্ষে সূরা ইউসুফে যে উপদেশ দেয়া হয়েছে- তা সর্বকালের এবং সর্বদেশের নারীদের পালন করা উচিত। এক্ষেত্রে নারীদের সহায়ক হিসেবে পুরুষদের সর্বতোভাবে সাহায্য করা উচিত।
\r\n
মর্যাদা প্রসঙ্গে হাদীসে যেসব উক্তি রয়েছে, তাতে স্পষ্টই বোঝা যায়, নারীর স্থান পুরুষের ঊর্ধ্বে, মাতার সম্মান পিতার সম্মানের তিনগুণ। এ পৃথিবীর স্রেষ্ঠ সম্পদ হিসেবে ধার্মিক পুরুষকে নয়, ধার্মিক নারীকে গণ্য করা হয়েছে। সে ধার্মিক নারীকে যাতে কোন ধন-দওলতের মোহে আকৃষ্ট না হয়ে পুরুষেরা বিয়ে করে তার জন্য উপদেশ দান করা হয়েছে।
\r\n
প্রশ্ন হচ্ছে নারীকে এত ঊর্ধ্বে সম্মান দান করা সত্ত্বেও অধিকারের ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয়ে পুরুষের সমান আসন দেয়া হয়নি কেন? তার উত্তরে বলা যায়-নারীর শারীরিক ও মানসিক দিকের প্রতি লক্ষ্য রেখেই তাকে কোন কোন অধিকারের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। পূর্বেই বলা হয়েছে, ইসলামের দৃষ্টিতে এ দুনিয়ার সবকিছুর একমাত্র মালিকানা আল্লাহ্ সুবহানাতা’আলার। মানুষকে তার কাছে গচ্ছিত বিষয়ের ভোগ-দখলের অধিকার দেয়া হয়েছে বটে, তবে সে ভোগ-দখলকে সে যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পারে না। সে ভোগ- দখলের জন্য যে নীতি নির্ধারিত হয়েছে তারই নির্দেশিত পথে তাকে ভোগ করতে হবে। এজন্য মুমিন মুসলিমদের অধীন সম্পদ ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তির মত আল্লাহ্র আইন মুতাবিক পরিচালিত হবে। এ পরিচালনা অত্যন্ত কঠিন কাজ এবং এর দায়িত্ব ততোধিক কঠিন। নারীদের শারীরিক দুর্বলতা এবং সন্তান লালন-পালনে তাদের অধিক দায়িত্ব থাকায় তাদের কোন কোন বিষয়ের দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যেই তাদের হিফাজতকারী বা (Custodian)-এর দায়িত্ব থেকে সরিয়ে রাখা হয়েছে। তবে মর্যাদার দিক থেকে তাদের স্থান পুরুষের ঊর্ধ্বে নির্দেশিত হয়েছে।
\r\n
ইসলামের দৃষ্টিতে সুদপ্রথা
\r\n
দুনিয়ার সবকিছুর স্বত্ব-স্বামিত্ব আল্লাহ্র ন্যস্ত করার ফলে যাতে মানুষের পক্ষে মানুষকে পীড়নের কোন সুবিধা না থাকে, তার জন্য রিবা বা সুদ প্রথাকে ইসলাম গোড়াতেই বাতিল করে দিয়েছে। কুরাআনুল-করীমের আল্লাহ্ আদেশ করেছেন, “যারা সুদ খায় তারা টিকে থাকতে পারে না, কেবল সে ব্যক্তির মতই টিকে থাকে, যাকে শয়তান তার স্পর্শ দ্বারা পাগলামিতে ঠেলে দিয়েছে”। (সূরা বাকারা ২:৩৮:২৭৫)
\r\n
অন্য এক স্থানে সুদের বিরুদ্ধে অভিসম্পাত বর্ষণ করা হয়েছে “আল্লাহ্ সুদকে সমস্ত নিয়ামত থেকে বঞ্চিত করবেন, কিন্তু দান সংক্রান্ত কার্যাবলিকে বিশাল করবেন”। (সূরা বাকারা ১:৩৮:২৭৬)
\r\n
কুরআনুল করীমের উপরোক্ত বাণীর মধ্যে ‘সে ব্যক্তির মতই টিকে থাকতে পারে-যাকে শয়তান তার স্পর্শ দ্বারা পাগলামিতে ঠেলে দিয়েছে’-বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, মানুষের প্রবৃত্তির মধ্যে প্রেম,স্নেহ, দয়া, মায়া প্রভৃতি উচ্চ পর্যায়ের প্রবৃত্তি। এগুলো অনুশীলন ব্যতীত মানুষের মধ্যে সত্যিকার মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় না। অথচ সুদ গ্রহণ ও সুদ দান দ্বারা মানুষের সেসব প্রবৃত্তির বিকাশে নানাবিধ অন্তরায় দেখা দেয়। মানুষ যখন নানাবিধ বিপদের সম্মুখীন হয় এবং তার পক্ষে তার কাছে রক্ষিত অর্থের দ্বারা তা সংকুলান হয়ে ওঠে না, তখনই সে ধার পাওয়ার জন্য অন্যের দ্বারস্থ হয়। মানুষ হিসেবে আমাদের কর্তব্য হচ্ছে তখন তাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করা। তার এ দুর্বলতার সুযোগে তাকে ধার দিয়ে তা থেকে এক মোটা অংক আদায় করা কোন মানুষের কাজ হতে পারে না। তার একমাত্র কাজ হচ্ছে সে শয়তানের, যে মানুষকে সর্বাবস্থায় বিপথগামী করে। এক্ষেত্রে শয়তানের সে কাজকে সুদখোরকে পাগল করে দেয়া বলা হয়েছে। কারণ, পাগলামি মানুষের সাধারণ বা প্রকৃতিস্থ রূপ নয়। এ হচ্ছে মানুষের এক বিকৃত রূপ। সুদ গ্রহণ করা, এ জন্য বলা হয়েছে এতে মানুষ তার সত্যিকার রূপ সম্পূর্ণভাবে পরিহার করে মাংসাশী প্রাণীর মত অপরের রক্ত মোক্ষণে অগ্রসর হয়। যে মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হচ্ছে মানুষকে ভালবাসা বা তাকে সাহায্য করা, এক্ষেত্রে সে মানুষই তার সে আদিম প্রবৃত্তির সম্পূর্ণভাবে অবমাননা করে তার বিপরীত দিকে ধাবিত হয় এবং রক্তলোলুপ প্রাণীর মত অপর মানুষের রক্ত শোষণ করতে চায়।
\r\n
আল্লাহ্ মানুষকে ইনসান-ই-কামিল রূপে গড়ে তুলতে চান। সে ইনসান-ই-কামিল হবে মানুষের বন্ধু। কাজেই যে প্রথা দ্বারা মানুষ ইনসানের শত্রুতা করতে অভ্যস্ত হয়, তাকে কোন অবস্থায়ই আল্লাহ্ গ্রহণ করতে পারেন না। বরং সর্বাবস্থায় তাকে পরিহার করার জন্য তাগিদ দেন।
\r\n
বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতাতে দেখা যায়, সুদখোরের সন্তান-সন্ততির মধ্যে আলস্য ও বিলাসিতা আসে। কোন কাজকর্মে না করে ঘরে বসে বিনা পরিশ্রমে প্রচুর রোজগার হয় বলে সুদখোরের সন্তান-সন্ততি বিলাসী হতে বাধ্য। পরিণামে এসব পরিবার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।
\r\n
সাম্যবাদমূলক দায়ভাগ প্রথার প্রবর্তন
\r\n
মালিকানা সম্পূর্ণ আল্লাহ্র বলে স্বীকৃতি লাভ করার পরে এ বিশ্বের সম্পদের সংরক্ষণ এবং সে সম্পদের হস্তান্তর সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় প্রশ্ন দেখা দেয়। এ বিশ্বের সমস্ত সম্পদের মালিক আল্লাহ্ তা’আলা তো বটেনই। তবে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এ সম্পদকে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। সাধারণত রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত না হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সে সম্পদ কোন না কোন ব্যক্তিবিশেষের করায়ত্ত থাকে। সে ব্যক্তির মৃত্যুর পরে, - এ সম্পদের কতটুকু কার দায়িত্বের মধ্যে অর্পিত হবে, সে সম্বন্ধে কুরআনুল করীমের পরিস্কার নির্দেশ রয়েছে।পুরুষ বা নারীর ইন্তেকালের পরে তার পুত্র, কন্যা ও স্বামী বা স্ত্রী সে সম্পদের কত অংশের হিফাজতকারী হবে তাতে কুরআনুল-করীমে নির্দেশ রয়েছে। সে নির্দেশকে সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে দেখা যায়, ইসলামের লক্ষ্য হচ্ছে সমাজের সকল স্তরের মানুষের মধ্যে অর্থের সহজ ও অবাধ গতির পথ প্রশস্তকরণ। অর্থাৎ যাতে এ জগতের ধন-দওলতে, টাকা-কড়ি অতি সহজেই সকল স্তরের লোকের কাছে পৌঁছতে পারে, ইসলামে রয়েছে তারই বিধি ব্যবস্থা অর্থাৎ ইসলাম কোন অবস্থায়ই টাকা-পয়সা কোন ব্যক্তি-বিশেষের হতে সঞ্চিত হয়ে পুঞ্জিতে পরিণত হউক এরূপ কোন ব্যবস্থার প্রশ্রয় দেয় না। একদিকে যেমন ইসলাম অলস মূলধনের (Idle Capital) অস্তিত্ব বরদাশ্ত করে না, তেমনি তাকে সঞ্চিত হওয়ারও কোন সুযোগ দিতে চায় না। এজন্য ইসলামী সমাজের দায়ভাগে সম্পত্তিকে ছোট ছোট ভাগে বণ্টন করার জন্য রয়েছে বিধি ব্যবস্থা।
\r\n
ইসলামী নীতির রুপায়ণ-রাষ্ট্রীয় জীবনেঃ মদীনার সনদের সারমর্ম
\r\n
মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর জীবনের অধিক ভাগই দুর্ধর্ষ কুরায়েশ জাতির সঙ্গে নানাবিধ যুদ্ধে অতিবাহিত হয়। কুরায়েশদের বিরোধিতার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় য়াহূদীদের বিশ্বাসঘাতকতা। তা সত্ত্বেও তিনি কোন জাতির বা ধর্মাবলম্বীর কোন মতামতের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেননি। মদীনাতে হিজরত করার পরে তিনি যে রাষ্ট্র গঠন করেন, তাতে ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার সে মর্মবাণীই ফুটে উঠেছে। মদীনা সনদের প্রথম কথাই হল-মদীনার য়াহূদী, পৌত্তলিক ও মুসলমান সকলেই এক দেশবাসী। য়াহূদী, পৌত্তলিক এবং মুসলমান সকলেই নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে, কেউ কারো ধর্মে হস্তক্ষেপ করবে না। এ ক্ষেত্রে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য বিষয় হচ্ছে এই- সে রাষ্ট্রে মুসলিমেরা সংখাগরিষ্ঠ হলেও সংখ্যালঘু য়াহূদী ও পৌত্তলিকদের নামই প্রথমে বলা হয়েছে। এতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়- তখনকার নানাবিধ অত্যাচার ও অনাচারের যুগে ইসলামী সমাজে বা রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুকে যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করা হত। দ্বিতীয়ত, সেই সনদে সংখ্যাগুরু সমাজের নেতা আল্লাহ্র রসূল (সঃ)-এর নির্দেশ পালন করার জন্য সংখ্যা
\r\n
লঘু সমাজের লোকেরা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অর্থাৎ গণতন্ত্রকে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করা হয়েছে। যদি য়াহূদী বা পৌত্তলিকেরা সংখ্যাগুরু হত তা হলে তাদের নেতার আদেশে সংখ্যালঘু মুসলিমদের পরিচালিত হওয়ার প্রতিশ্রুতি থাকতো। তবে যেহেতু মুসলিমেরাই সংখ্যাগুরু ছিল, এজন্য মুসলিমদের সর্বসম্মত জননেতা-হযরত রসূলই-আকরমের (সঃ) নেতৃত্বই স্বীকার করে নেয়া হয়েছিল। তবে যাতে কোন অবস্থায়ই বর্তমান কালের তথাকথিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অর্থের দওলতে নানাবিধ দুর্নীতির সৃষ্টি না হয়- সে দিকে ইসলামী রাষ্ট্রে প্রখন দৃষ্টি ছিল। ইসলামী রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের মধ্যে যাতে কোনকালে অর্থের দ্বারা কোন সুযোগ-সুবিধা আদায় করা না হয়, এজন্য খলীফা পদ প্রার্থীকে সাচ্চা মুসলিম হতে হবে। অর্থের প্রাধান্যের জন্য বর্তমান কালের গণতন্ত্রের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে-তা’ সত্যিই অসংস্কৃতব্য । মুখে গণতন্রের নামে নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়ে, অর্থের জোরে নরপিশাচ শ্রেণীর মানুষেরাও সফলতা লাভ করে। এতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা থেকে যে সার্বভৌমত্বের সৃষ্টি হয়, তার সঙ্গে অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্বের ভীষণ দ্বন্দ্ব দেখা দেয় বলে এ গনতন্ত্রকে অধ্যাপক হ্যারল্ড লাস্কি তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছেন। অথচ বর্তমান কালের গনতন্রে এ দ্বন্দ্ব সর্বত্রই বর্তমান। এ গণতন্রের নির্বাচন প্রার্থীর চরিত্রকে বিচার করা হয় না, তার জনপ্রিয়তাকেই বিচার করা হয় বলে নিতান্ত চরিত্রহীন লোকের পক্ষেও নির্বাচিত হওয়ার সমূহ সুযোগ থাকে। ইসলামী গণতন্ত্রে নির্বাচন প্রার্থী লোকের ব্যক্তিগত জীবনযাত্রা প্রণালি, ইসলামের রীতিনীতির সঙ্গে তার যোগ প্রভৃতি বিষয় বিচার করা হয় বলে এ দ্বন্দ্ব দেখা দেয় না।
\r\n
কাজেই দেখা যায়, ইসলামী রাষ্ট্রে রয়েছে একদিকে ব্যক্তিস্বাধীনতা। যে ব্যক্তি-স্বাধীনতার জন্য এ যুগে এত হৈ চৈ শোনা যায়-চৌদ্দশত বৎসর পূর্বেই মানুষের নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সে স্বাধীনতার চার্টার জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলেই দান করেছেন। অপরদিকে এ গণতন্রে অর্থের মাধ্যমে যাতে কোন দুর্নীতি প্রশ্রয় না পায়- তার জন্য এ গণতন্ত্রের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রকদের চরিত্র সম্বন্ধেও গুরুত্ব আরোপ করা হয়।
\r\n
পুঁজি সৃষ্টির বিরুদ্ধে অর্ডিন্যান্স
\r\n
ইসলামী নীতি অনুসারে জীবন যাপন করলে কোন অবস্থায়ই মানুষের হাতে পুঁজি সৃষ্টি হতে পারে না। যাকাত ব্যতীতও নানাবিধ দান সবসময়ই ধনী ব্যক্তিকে করতে হবে। জবিল কুরবা, ইয়াতামা, মাসাকিনা ও ইবলে সবিল অর্থাৎ পিতৃমাতৃকুলের আত্মীয়-স্বজন,অনাথ, পিতৃমাতৃহীন ছেলেমেয়ে, বিত্তহারা ও সহায়-সম্বলহীন পথিকের দাবি রয়েছে ধনীর মালের ওপর। কুরআনে শরীফে এদের প্রাপ্য প্রদান করার জন্য রয়েছে জেদ তাগিদ। কেবল কুরআন শরিফেই নয়, হাদীস শরীফেও দানের মাহাত্ম্য ঘোষণা করা হয়েছে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন-
\r\n
“ আল্লাহ্র রসূল (সঃ) বলেছেন, “কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ জিজ্ঞেস করবেন, ‘হে বনি আদম, আমি পীড়িত ছিলাম কিন্তু তুমি আমায় দেখো নি’। সে উত্তর করবে, ‘ হে আমার প্রভু, আমি তোমাকে কিভাবে দেখবো, তুমি যে নিখিল বিশ্বের প্রভু?’ তিনি (আল্লাহ্) বলবেন, ‘তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা পীড়িত ছিল, কিন্তু তুমি তাকে দেখো নি, তুমি কি জানতে না যে, যদি তুমি তাকে দেখতে ( শুস্রষা করতে) তাহলে তার মাঝেই আমাকে পেতে? হে বনি আদম! আমি তোমার কাছে আহার চেয়েছিলাম কিন্তু তুমি আমার আহার দাও নি’। সে উত্তর দেবে, ‘হে আমার প্রভু, আমি তোমাকে কিভাবে খেতে দিতে পারতাম- যেহেতু তুমি সমস্ত ভুবনের প্রভু?’ তিনি (আল্লাহ্) বলবেন, ‘তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে চাওয়া সত্ত্বেও তুমি তাকে খেতে দাওনি-তুমি কি জানতে না যদি তুমি তাকে খেতে দিতে তাহলে আমাকেই খেতে দিতে?’* (Al-Muslim….Al-Hadis,Sec.p,35,273 Maulana Fazlul Karim.)
\r\n
এতসব আইন-কানুন থাকা সত্ত্বেও যদি মানুষের মধ্যে অযথা সঞ্চয় করার প্রবৃত্তি জেগে ওঠে তাহলে প্রয়োজনবোধে খলীফা বা আমির ধনীদিগকে দরিদ্রের দায়িত্ব গ্রহণে বাধ্য করতে পারেন। ইবনে হাজম এ অর্ডিন্যান্সের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, “প্রত্যেক মহল্লার ধনীদের ওপর গরীব-দুঃখীদের জীবিকার জন্য দায়ী (জামিন) হওয়া ফরয (অবশ্য কর্তব্য)। যদি বায়তুলমালের আমদানি ঐ গরিবদের জীবিকার পক্ষে যথেষ্ট না হয়, তাহলে শাসক বা আমির ধনীদের এ কাজের জন্য বাধ্য করতে পারেন। অর্থাৎ তাদের অতিরিক্ত মাল বলপূর্বক গরিবদের প্রয়োজনে খরচ করতে পারেন। তাদের জীবিকার সংস্থানের জন্য আবশ্যক-ক্ষুধার অন্ন, পরিধানের বস্ত্র এবং ঝড়-বৃষ্টি, গরম রোদ ও প্লাবন থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে এমন বাসগৃহ’।* (মুহাল্লাঃ ৬ষ্ঠ খন্ড,পৃ,১৫৬;মিসলাঃপৃ,৭২৫,মওলানা হিফজুর রহমানঃ ‘ইসলাম কা ইক্ তেসাদি নিজাম’ থেকে গৃহীত।)
\r\n
ইসলামী গনতন্রের ফলিত রূপ
\r\n
হযরত রসূল আকরম (সঃ)-এর জীবিতকালে এবং পরবর্তী সময়ে সে আদর্শ রাষ্ট্রে স্বাধীনতা যে চরম বিকাশ লাভ করেছিল, তার নিদর্শনস্বরূপ বহু ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রসঙ্গত মাত্র দুটি ঘটনার উল্লেখ করা হচ্ছে। ইসলামী গণতন্রের স্বরূপ বর্ণনা করতে যেয়ে দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রাঃ)এক জনসভায় বক্তৃতায় বলেছিলেনঃ
\r\n
“ আমি আপনাদের একজন খাদিম মাত্র। আমার কাছ থেকে আপনাদের সর্বপ্রকার মঙ্গলজনক কাজ আদায় করার পূর্ণ অধিকার রয়েছে”।
\r\n
হযরত উমর (রাঃ)আর একদিন জনসভায় বক্তৃতাকালে শ্রোতৃমন্ডলীর মধ্য থেকে হটাৎ এক ব্যক্তি বলে উঠলো, “ হে উমর,আল্লাহ্কে ভয় করো”। সমবেত জনতা চাইলো তাকে থামিয়ে দিতে কিন্তু হযরত উমর (রাঃ) বললেন, “না, না, একে নিজের মতামত ব্যক্ত করতে দিন। নিজের মতামত ব্যক্ত না করলে ইসলাম প্রদত্ত স্বাধীনতা ভোগ ও সাম্যের সম্মান আপনারা কি প্রকারে করবেন? ইসলাম জননেতা ও জনগণের মধ্যে কোন ইতর-বিশেষ করেনি। শুধু পার্থক্য এই যে,জননেতার দায়িত্ব অধিক। সকলেরই সম্মতি ও আপত্তিতে কর্ণপাত করা রাষ্ট্রনেতা হিসেবে আমার কর্তব্য”।** (বিপ্লবী উমরঃ সম্পাদক-আবদুল গফুর।)
\r\n
সে ব্যক্তি-স্বাধীনতা যাতে স্বেচ্ছাচার ও জুলুমে পরিণত না হয় তার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেই মুসলিম রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল। সে আদর্শ সাম্যবাদে আমির-ফকিরে কোন পার্থক্য ছিল না।
\r\n
খলীফার দায়িত্ব
\r\n
সাধারণের অর্থ খলীফার তত্ত্বাবধানে থাকলেও তা থেকে যথেচ্ছ ব্যয় করার অধিকার খলীফার ছিল না। কোন কোন ক্ষেত্রে এরূপ সন্দেহের উদ্রেক হলে জনসাধারণের পক্ষে প্রকাশ্যে খলীফার সমালোচনা করার অধিকার ছিল। তাকে impeach করতে হলে অপসারণের প্রয়োজন হ’ত না। এর উদাহরণ রয়েছে ইসলামের স্বর্ণযুগের ইতিহাসে। খলীফা উসমানের (রাঃ) খিলাফতের সময় কয়েকজন দুষ্ট প্রকৃতির লোক তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করলে তিনি মুসলিমদের এক সাধারণ সভা আহ্বান করে তাঁর ওপর আরোপিত অভিযোগ খণ্ডনের উদ্দেশ্যে বলেনঃ
\r\n
“ আল্লাহ্র নামে শপথ নিয়ে বলছি- আমি কোন শহরের উপর তার সাধ্যাতীত কর ধার্য করিনি, কাজেই আমার বিরুদ্ধে আনীত এ অভিযোগ নিছক মিথ্যা। আমি সর্বসাধারণের থেকে যা গ্রহণ করছি তাদেরই হিতের জন্যই ব্যয় করছি। যে লভ্যাংশের এক-পঞ্চমাংশ আমার নিকট এসেছে তাও আমার ব্যক্তিগত ভোগের জন্য ব্যয় করা আইনসঙ্গত নয়। তাই তার সমস্তই মুসলিমরা ব্যয় করেছে- আমি করিনি। সাধারণ ধনাগারের এক কপর্দকও তসরুফ করা হয়নি, আমি তা থেকে একটি পয়সাও নিইনি। আমি আমার নিজের উপার্জনের ওপর নির্ভর করেই জীবিকা নির্বাহ করি”।
\r\n
তারপর তিনি আরও বলেন- “তোমরা জানো, খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পূর্বে আরব দেশে আমি ছিলাম উট ও ছাগীর সবচেয়ে বড় মালিক। খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর দু’টো উট ব্যতীত আমার আর কোন পশু নেই। সেগুলোও আমি হজ্জের সময় মক্কায় যাওয়ার জন্য ব্যবহার করি”।
\r\n
ইসলাম ও ডিক্টেটরশিপ
\r\n
হযরত রসূলে করীম (সঃ)-এর ইন্তেকালের পর তাঁরই আদর্শের অনুসরণে গণতান্ত্রিক ভিত্তিতেই রাষ্ট্র গঠিত হয়। নবনির্বাচিত খলীফা হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর ঘোষণাতে ন্যায়-বিচার ও খলীফার ক্ষমতা প্রয়োগের একটা স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায়। তিনি তাঁর নির্বাচনের পরে সমবেত জনতার উদ্দেশে বলেনঃ “সঙ্গীগণ, আমি তোমাদের খলীফা নির্বাচিত হয়েছি। আমি তোমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে দাবি করি না। তোমাদের মধ্যে যারা সবচেয়ে শক্তিশালী তাকেই আমি দুর্বলতম মনে করব- যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে দখলকৃত (দুর্বলদের) সামান্যতম অধিকারকে আমি ফিরিয়ে আনতে পারি এবং যারা তোমাদের মধ্যে দুর্বলতম- তারাই আমার কাছে সবলতম- যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তাদের অধিকারকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করি। ভাইগণ, আমাকে তোমাদের মতই আল্লাহ্র আইন মেনে চলতে হবে এবং আমি তোমাদের ওপর কোন নতুন আইন চাপাতে পারবো না। আমি তোমাদের উপদেশ ও সাহায্য চাই। যদি সৎপথে চলি, তোমরা আমার সহায়তা করবে, যদি ভুলপথে চলি তাহলে আমাকে সংশোধন করবে”।
\r\n
কাজেই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, খলীফার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল দুনিয়ার ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা কর। জনগণের দ্বারা নির্বাচিত খলীফা কোনদিনই জনমতকে উপেক্ষা করেননি। মানুষ হিসেবে তাঁদের ভুল-ভ্রান্তি সম্বন্ধে তাঁরা ছিলেন সততই সজাগ। ইসলামের উজ্জ্বল রত্ন খলীফা উমর (রাঃ) একদিন এক সাধারণ সভায় আদেশ করেছিলেন-মোহরানা যেন বেশি নেওয়া না হয়। তাঁর কথা শোনামাত্রই এক বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে কুরআন শরীফের এক আয়াতের উল্লেখ করে দেখিয়ে দেন যে, কুরআনে মোহরানার পরিমাণ নির্দিষ্ট করা হয়নি। খলীফা অম্লানে তাঁর ভুল স্বীকার করেন।
\r\n
কাজেই দেখা যাচ্ছে, বর্তমান যুগের রাষ্ট্র পরিচালকদের চরিত্রের সঙ্গে খলীফাদের চরিত্রের কোন তুলনাই চলে না। তাঁরা সবসময়েই নিজেদের সাধারণ মানুষ বলেই মনে করতেন-দুনিয়ার সব ত্রুটি-বিচ্যুতির উর্ধ্বে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত ‘অতিমানব’ বলে তাঁরা নিজেদের কোনদিন ভাবতে পারতেন না।
\r\n
সংখ্যালঘু সমস্যা
\r\n
দুনিয়ার সকল দেশে সকল যুগেই সংখ্যালঘু সমস্যা ছিল ও রয়েছে। আধুনিককালে গণতন্ত্রমূলক রাষ্ট্র গঠিত হলেও তাতে সংখ্যালঘু একদল লোক থেকে যায় যারা বিরোধী দল নামে পরিচিত। ইসলামী রাষ্ট্রে চার্চ ও পার্লিয়ামেন্টের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই বলে এ রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুদের দুদিক থেকে দেখা যেতে পারে। সংখ্যালঘু বলতে রাষ্ট্রের অধিকাংশ লোকদের মতাবলম্বী নয় এমন একদল লোককে যেমন বোঝা যায়- তেমনি অন্য ধর্মাবলম্বী লোককেও বোঝা যায়। ইসলামী রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুর স্থান কোথায়, তা-ই আমাদের বিবেচ্য। ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলিমদের মধ্যে সংখ্যালঘু বলে কেউ থাকতে পারে না। কারণ, মুসলিমেরা সকলেই ইসলাম ধর্মাবলম্বী বলে ইসলামেরই অনুসারী ও ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের রুপায়ণে এক মতাবলম্বী হতে বাধ্য। ভিন্ন ধর্মের লোকদের ইসলামী রাষ্ট্রে বলা হয় যিম্মি। তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি অক্ষুণ্ন রাখতে ইসলামী রাষ্ট্র সর্বতোভাবে বাধ্য। এজন্যই ইসলামের শাসন বিধান অনুসারে ইসলামী রাষ্ট্রে এমন কোন আইন গৃহীত হতে পারে না- যা যিম্মির সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতিকূল। তাই আধুনিক গণতন্ত্রের চেয়ে এক্ষেত্রে ইসলামী নীতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। কারণ, আধুনিক গনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যে কোন আইন জনমতের জোরে গৃহীত হয়ে যেতে পারে, যা সম্পূর্ণই সংখ্যালঘুর সংস্কৃতির প্রতিকূল। কাজেই শুধু ‘যিম্মি’ শব্দ শুনেই যাঁরা অস্থির হয়ে পড়েন তাঁদের প্রবোধের জন্য বলা যেতে পারে যিম্মি অর্থ রক্ষিত নয়- তার অর্থ ইসলামী শাসন বিধানে যাতে কোন অনিষ্ট বা অমঙ্গল না হয় তার জন্য রক্ষাকবচের ব্যবস্থা।
\r\n
যিম্মি সম্বন্ধে হযরত আলীর উক্তি রয়েছে- যিম্মির রক্ত আমারই রক্ত। ইসলামী রাষ্ট্রে যিম্মির মুসলিমদের মত সমান অধিকার রয়েছে। প্রশ্ন ওঠে সংখ্যালঘু ভিন্ন ধর্মাবলম্বী কোন ব্যক্তি বা ভিন্ন মতাবলম্বী হয়েও ইসলামী রাষ্ট্রের আদর্শে বিশ্বাসী হতে পারে কিনা। এরূপ ক্ষেত্রে শাসন ব্যবস্থায় মুসলমানদের মত তার সমান অধিকার থাকতে পারে কিনা। তার উত্তরে বলা যায়, ইসলাম অবিভাজ্য মতবাদ বলে ধরে নেয়া হয়-ইসলামের আংশিক দিককে গ্রহণ করে ইসলামী শাসন ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ চালু করা কারো পক্ষে সহজ নয়। আল্লাহ্র ওয়াহদানীয়ত ও সার্বভৌমত্বের ওপর ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। সে মৌলিক ভিত্তিকে অস্বীকার করে কোন ব্যক্তির পক্ষে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা চালু করা অসম্ভব। তাই ভিন্ন ধর্মাবলম্বী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তিকে ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনা করার ভার ইসলামী সমাজে দেয়া হয়নি। তবে এতে সংখ্যালঘু ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর পক্ষে অসুবিধার বিশেষ কারণ আছে বলে মনে হয় না। কারণ, রাষ্ট্রের পরিচালনা খুব সুখের বিষয় নয় এবং কোন রাষ্ট্রে বাস করে তার সকল অধিকার ভোগ করে কেবল রাষ্ট্র পরিচালনার অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে তাতে ব্যক্তিবিশেষের কোন ক্ষোভের কারণ থাকতে পারে না। আধুনিক কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রগুলোতে কমিউনিষ্ট ব্যতীত অন্য কাউকে নির্বিঘ্নে বাস করতে দেয়া হয় না- পরিচালনা তো দূরের কথা।
\r\n
খলীফার নিয়োগ
\r\n
আল্লাহ্র রসূল (সঃ)-এর পরে আল্লাহ্র রাষ্ট্রে তাঁর প্রতিনিধির নিয়োগে কখনও বা নির্বাচন, কখনও – মনোনয়ন, কখনও বা নির্বাচনের জন্য প্যানেল মনোনয়ন করা হয়েছে। মুসলিমেরা প্রত্যেকেই আল্লাহ্র প্রতিনিধি বলে তাদের প্রত্যেকেরই আল্লাহ্র প্রতিনিধি নির্বাচন করার অধিকার রয়েছে। দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারুকের নির্দেশ থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় সর্বসাধারণ মুসলিমদের নির্বাচন হবে আল্লাহ্র রসূল (সঃ)-এর প্রতিনিধি বা খলীফা নির্বাচনের ভিত্তি। তিনি আদেশ করেছিলেন-
\r\n
“ সর্বসাধারণ মুসলিমের সম্মতি ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি যদি কারো প্রভুত্ব স্বীকার করে তাহলে যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চায় এবং যে আনুগত্য স্বীকার করে তাদের দুজনেরই মৃত্যুদন্ড হওয়া উচিত* (Shaik Mushir Hussain Kidwai-Pan Islamism & Bolshevism p 212-13)- তবে এক্ষেত্রেও ইসলামী গণতন্রের সঙ্গে আধুনিক গণতন্ত্রের পার্থক্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আধুনিক গণতন্ত্রের ভিত্তি হচ্ছে প্রার্থীর জনপ্রিয়তা, কোন ব্যবস্থাপক সভা অথবা পরিষদে নির্বাচিত হতে হলে প্রার্থীর পক্ষে অধিক সংখ্যক ভোট সংগ্রহ করা প্রয়োজনীয়। প্রার্থীর জনপ্রিয়তার সঙ্গে তার ব্যক্তিগত চরিত্রের কোন যোগ নেই। তার নির্বাচকমন্ডলীর লোকদের সে যে কোনভাবেই সন্তুষ্ট করেই জনপ্রিয় হতে পারে। সে হয়ত টাকা পয়সা ঘুষ দিয়ে অথবা নানাবিধ বিলাসের সামগ্রী সরবরাহ করে জনপ্রিয় হতে পারে। ইসলামী গণতন্ত্রে এরূপ লোকের কোন স্থান হতে পারে না। যাকে শর্তবিহীন অবাধ গণতন্ত্র বলে বর্তমানে সম্মান প্রদর্শন করা হয়, তাকে সুবিখ্যাত রাষ্ট্রনীতিবিদ হ্যারলড লাস্কি ঠাট্টা করে বলেছেন- এটা দ্বন্দ্বসংকুল গণতন্ত্র। এতে একদিকে সংখ্যার সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অর্থের সার্বভৌমত্বও স্বীকার করে নেওয়া হয়। এ গণতন্ত্রে সকল মানুষের সমান অধিকার স্বীকার করা হলেও কার্যক্ষেত্রে ধনীরা তাদের অর্থের মাধ্যমে গরিবদের কাছ থেকে অতি সহজে তার ভোট কিনে নিতে পারে। কাজেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা এ গণতন্রের মূলভিত্তি হলেও সংখ্যালঘু ধনীদের দ্বারা তা নিয়ন্ত্রিত হয়। ইসলামী সমাজে এজন্য প্রার্থীর চরিত্রের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ইসলাম ধর্মের বিপরীত যে কোন কাজকর্মে লিপ্ত ব্যক্তি ইসলামী রাষ্ট্রের খলীফা পদের যেমন প্রার্থী হতে পারে না, তেমনি জনসাধারণও এরূপ ব্যক্তিকে ভোটদান করতে পারে না। ইসলামী গণতন্ত্রে মূল লক্ষ্য হচ্ছে-এ বিশ্বে আল্লাহ্র শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। এজন্য যে ব্যক্তি আল্লাহ্র শাসন কামনা করে না অথবা আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ মানতে চায় না, সে ব্যক্তি আল্লাহ্র খলীফা নির্বাচিত হতে পারে না।
\r\n
ইসলামী জীবনধারার বিপরীতমুখী জীবন যাপন করাতে অভ্যস্ত ব্যক্তির খলীফাপদে নিয়োগের প্রতিবাদ করার ফলেই কারবালা প্রান্তরে সে হৃদয়বিদারক ও মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে।
\r\n
হযরত মু’আবিয়া তারই জীবনকালে তার পুত্র ইয়াযিদকে ইসলামী জগতের খলীফা মনোনীত করার প্রতিবাদকল্পেই শহীদরাজ হাসান, হোসেন কারবার প্রান্তরে এবং আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়র মক্কাতে শাহাদাত বরণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে উমাইয়াদের শাসনকালে খলীফার পদে বংশানুক্রমিক হয়ে পড়লেও সে বংশেরই অতি ন্যায়বান ও পরম সত্যবাদী হযরত উমর ইবেনে আবদুল আযীয খানদানী সূত্রে খলীফার পদ লাভ করেও তাতে ইস্তফা দিয়ে জনগণের মত পরিক্ষা করে নিয়েছিলেন। সর্বসাধারণ মুসলিম একবাক্যে তাঁর নিয়োগ সমর্থন করার পরে তিনি সে দায়িত্ব গ্রহণ করতে সম্মত হন। তবে তিনি দীর্ঘকাল তাঁর এ পদে টিকে থাকতে পারেন নি। তাঁরই বংশের লোকদের মত প্রচলিত নানাবিধ দুষ্কর্মের উচ্ছেদ করতে যেয়ে তিনি তাদের কারসাজির ফলে নিহত হন।
\r\n
তারপরে মুসলিম সমাজে ইসলামী গণতন্ত্রে যে ছায়াটুকু মাত্র অবশিষ্ট থাকে তা’ সত্যিকার ঈমানদার কেন, অন্য মানুষের কাছেও হাস্যাস্পদ। তথাকথিত খলীফাগণ উত্তরাধিকারসূত্রে খিলাফত লাভ করে মুসলিম জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে তাদের কাছ থেকে পদপ্রাপ্তির পরে বায়’আত গ্রহণ করতেন। উমাইয়া ও আব্বাসীয় উভয় পক্ষের মধ্যে এ আচরণ প্রচলিত ছিল।
\r\n
অর্থনীতি
\r\n
এ রাষ্ট্রের অর্থনীতি পরিচালিত হয় সর্বসাধারণের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে। যুদ্ধলব্ধ বিত্ত (আল-গনীমাহ), যাকাত, সাদাকা, জিযিয়া, খিরাজ, আল-ফায়, আল-উশর প্রভৃতি বিভিন্ন কর ধার্য করে এ রাষ্ট্রের আর্থিক সৌধ গড়ে তুললেও পরিবর্তিত অবস্থায় সেগুলোর পরিবর্তনও স্বীকার করে নেওয়া হয়।
\r\n
হযরত উমর (রাঃ)-এর লক্ষ্য ছিল রাষ্ট্রের সমস্ত মুসলিম অধিবাসীকে রাষ্ট্রের অঙ্গ জ্ঞান করে রাষ্ট্রগতপ্রাণ করে তোলা। সে জন্য তিনি তাদের প্রত্যেকের বৃত্তি নির্ধারণ করেছিলেন এবং যাতে করে তারা জীবিকার সংস্থানের জন্য অন্য কোন কাজে লিপ্ত না হয় তার প্রতি কড়া দৃষ্টি রাখতেন। তাঁর খিলাফতের সময় কোন অমুসলিম মুসলমান হয়ে গেলে তার সম্পত্তি দেশের লোকের মধ্যে বেঁটে দেয়া হতো।
\r\n
এ রাষ্ট্রে যাতে কোন অবস্থায় কোন লোকের হাতে পুঁজি সঞ্চিত না হয় সেজন্য আদেশ করা হয়েছেঃ
\r\n
“ এবং যারা সোনারূপা সঞ্চয় করে, আল্লাহ্র পথে (মানবতার কল্যাণের জন্য) ব্যয় করে না-তাদের নিকট এক কষ্টদায়ক শাস্তি ঘোষণা করে দাও”। (সূরা তওবা, আয়াত ৩৪)
\r\n
এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রসূল আকরাম (সঃ) যা বলেছেন, সাহাবী আবু হুরায়রা (রাঃ) তা’ বর্ণনা করে বলেন, “রোজ কিয়ামতে এ সকল লোকদের পার্শ্বদেশ, কপাল ও পিঠে দাগ দেয়া হবে”।
\r\n
উমাইয়াদের আধিপত্য বিস্তারের সূচনায় এবং সিরিয়াতে মু’আবিয়া গভর্নর থাকাকালে এ আয়াতের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করে হযরতের প্রিয় সাহাবী হযরত আবু যর গিফারী* (রাঃ)(ইতিহাসে উপেক্ষিত একটি চরিত্রঃ মুহাম্মদ আজরফ ও এ. জেড. এম. শামসুল আলম) বিপ্লবের সূচনা করেন। তাঁর সুদৃঢ় অভিমত ছিল, প্রয়োজনে অতিরিক্ত কোন বিত্তই কেউ রাখতে পারে না।
\r\n
সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইবনে হাজম জাহেরী ‘মুহাল্লা’য় উল্লেখ করেছেন- হযরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেছেনঃ আল্লাহ্র রসূল বলেছেন, যে ব্যক্তির কাছে শক্তি ও সামর্থ্যের সরঞ্জাম নিজ আবশ্যকের অতিরিক্ত রয়েছে তার উচিত-ঐ অতিরিক্ত সামান-সরঞ্জাম দুর্বলকে দান করা। যে ব্যক্তির কাছে খাওয়া-পরার অতিরিক্ত উপাদান রয়েছে তার পক্ষে উচিত-অতিরিক্ত সামান দীন-দুঃখীকে দান করা”। আবু সাঈদ খুদরী আরও বলেছেন, “নবী করীম (সঃ) এভাবে নানা প্রকারের উল্লেখ করেছেন তাতে আমার এরূপ ধারণা জন্মেছে যে, আমাদের মধ্যে কারো কোন প্রকারের মালের দাবি থাকতে পারে না।
\r\n
হযরত রসূল করীম (সঃ)- এর প্রধান সাহাবী ও ঘনিষ্ঠতম আত্মীয় হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, ‘আল্লাহ্ তা’আলা ধনীদের ওপর গরিবদের আবশ্যকীয় জীবিকা পরিপূর্নভাবে সরবরাহ করা ফরয করেছেন। যদি তারা (গরিবেরা) ভুখা, নগ্ন থাকে অথবা জীবিকার জন্য বিপদগ্রস্ত হয় তাহলে ধনীরা দায়িত্বশীল নয় বলেই বুঝতে হবে- এজন্য আল্লাহ্র কাছে তাদের কিয়ামতের দিন জবাবদিহি হতে হবে এবং সংকীর্ণতার জন্য শাস্তি ভোগ করতে হবে। এবং বিধ আরও হাদীস ও কুরআনের দলীলের দ্বারা মুহাদ্দিস ইবনে হাজম এ বিষয় ব্যাখ্যা করে বলেছেন-
\r\n
“প্রত্যেক মহল্লার ধনীদের ওপর গরিব-দুঃখীদের জীবিকার জন্য দায়ী (জামিন) হওয়া ফরয (অবশ্য কর্তব্য) । যদি বায়তুলমালের আমদানি ঐ গরিবদের জীবিকার সরবরাহের জন্য যথেষ্ট না হয়, তাহলে শাসক বা আমীর ধনীদিগকে এ কাজের জন্য বাধ্য করতে পারেন অর্থাৎ তাদের মাল বলপূর্বক গরিবদের প্রয়োজনে খরচ করতে পারেন-তাদের জীবিকার সংস্থানের জন্য কমপক্ষে অত্যাবশ্যক প্রয়োজন অনুযায়ী ক্ষুধার অন্ন, পরিধানের বস্ত্র এবং ঝড়বৃষ্টি, গরম-রোদ ও প্লাবন থেকে রক্ষা করতে পারে এমন বাসগৃহ”।
\r\n
এ রাষ্ট্রে তাহলে বিত্ত সঞ্চয় বা শোষণের কোন অবকাশই থাকতে পারে না। রাষ্ট্র ও জনসাধারণের মধ্যবর্তী কোন বিশেষ প্রাণীও রাষ্ট্রে থাকতে পারে না। ইরাক ও সিরিয়া বিজিত হওয়ার পর সাহাবীদের শত অনুনয়-বিনয় সত্ত্বেও হযরত উমর ফারুক (রাঃ) তাদের জায়গীর দান করেননি বরং সমস্ত ভূমি সরকারের অধীনে রেখে তার আয় সকল অধিবাসীর প্রয়োজন ও আবশ্যকাদির জন্য ওয়াকফ গণ্য করেছেন।
\r\n
এমনকি, প্রয়োজনে অতিরিক্ত ভূমি যাতে কোন জোতদারের হাতে না থাকে তার জন্য হযরত বিলাল (রাঃ)-এর জায়গীর থেকেও অতিরিক্ত জমি ছিনিয়ে নিয়ে হযরত উমর ফারুক (রাঃ) চাষীদের মধ্যে বেঁটে দিয়েছেন।
\r\n
কাজেই ব্যক্তি-স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রেখে যাতে সর্ববস্থায় সমান অংশে দুনিয়ার সম্পদ মানুষ ভোগ করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই মানবসমাজে সংঘ-চেতনার পথে এগিয়ে দেয়া হয়েছে।
\r\n
\r\n
উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা
\r\n
অর্থনীতির সঙ্গে উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থার গূঢ় সম্বন্ধ বর্তমান। উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যষ্টির একাধিপত্য স্বীকৃত হলে বন্টনের ব্যাপারে তার আধিপত্যের নীতি স্বীকার করে নিতে হয়। সকল যুগেই দেখা যায়, মানুষ একাকী উৎপাদনে কোনদিনই সক্ষম হয়নি । অথচ বন্টনের ব্যাপারে উৎপাদনকারী তার যথেচ্ছ স্বাধীনতা প্রয়োগ করতে চায়। আধুনিক জগতে তাই দেখা দিয়েছে এক মহাদ্বন্দ্ব।
\r\n
ইসলাম উৎপাদনের ব্যাপারে কোন বিধি-নিষেধ আরোপ করেনি। মানুষ ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে উৎপাদন করতে পারে, তবে বন্টনের ব্যাপারে সব সময়েই তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত সবকিছু সমাজের অথবা রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য ব্যয় করতে সে বাধ্য। এ নীতি ইসলামের জীবনদর্শন থেকেই পাওয়া যায়। কারণ, ইসলামী দর্শনে আসমান জমিনের সবকিছুরই মালিদ খোদ আল্লাহ্ তা’আলা। মানুষ তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে যেমন উৎপাদন করবে,তেমনি তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর নিয়ামত সকল মানুষ সমান অংশে ভোগ করবে। আধুনিক জগতের উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার অসামঞ্জস্য তাই ইসলামে দেখা দিতে পারে না। * (আধুনিক যুগের মত তখন শিল্প এতটা বিস্তৃত হয়নি। তবুও যাতে উৎপাদন ব্যবস্থায় সমষ্টির দায়িত্ব ও কতৃত্ব অব্যাহত থাকে তার নজিরস্বরূপ হযরত রসূলে আকরাম (সঃ)-এর এক সহীহ্ হাদীদ পাওয়া যায়। ইসলামের ইতিহাসের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁআরা জানেন, মদীনায় হিজরতের পরে মুহাজিরগণ আনসারদের কাছ থেকে আশাতিরিক্ত সাহায্য ও সহানুভূতি লাভে সমর্থ হন। আনসারদের প্রত্যেকেই তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি মুহাজিরগণের সঙ্গে ভাগ করে ভোগ করতে প্রস্তুত হন। ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলতে তাদের খেজুর গাছের ফল,উট, দুম্বা ও জমিজিরাতই বোঝাত। কোন এক আনসার রসূলে আকরাম (সঃ)-কে খেজুর গাছগুলো তাদের ও আনসারদের মধ্যে ভাগ করে নিতে অনুরোধ করলে তিনি বলেন, “আমরা যে এর উপস্বত্ব ভোগ করছি তাই যথেষ্ট এবং তোমাদের দান এ ফলের সঙ্গে তোমাদের (সহানুভূতিও) আমরা পাচ্ছি”। তারা তাঁর এ আদেশ শিরোধার্য করে। এতে সুস্পষ্ট বোঝা যায়, ভ্রাতৃত্ববোধ অক্ষুণ্ন রাখার জন্য সমষ্টিগত উৎপাদন ব্যবস্থাই রসূলে আকরম (সঃ) প্রকৃষ্ট পন্থা বলে মনে করতেন। -Al-Hadis-BK 11 P 306-Fazlul Karim)
\r\n
শাসন ও বিচার বিভাগ
\r\n
অতি আধুনিক কালে শাসন বিভাগকে বিচার বিভাগ থেকে পৃথক করার জন্য প্রায় সকল দেশেই আন্দোলন দেখা দিয়েছে। একই ব্যক্তির হাতে শাসন ও বিচারের ক্ষমতা থাকলে তার হাতে সুবিচারের প্রত্যাশা কিছুতেই করা যায় না। কোন ব্যক্তির কোন দেশের বা জেলার শাসনকর্তার কোপে পতিত হলে সে শাসনকর্তা থেকে সে কোনমতেই সুবিচারের আশা করতে পারে না। এজন্য শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ সকল দেশেই একান্ত কাম্য হয়ে দেখা দিয়েছে। এক্ষেত্রেও আধুনিক শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা বা বিচার ব্যবস্থার পার্থক্য বিশেষভাবেই লক্ষণীয়।
\r\n
ইসলামী শাসন ও বিচারের মূল উৎস একই। এ দুনিয়ায় আল্লাহ্রই রয়েছে একমাত্র সার্বভৌমত্ব এবং তিনি তাঁর প্রেরিত পুস্তকে কুরআন উল-করীমের মাধ্যমে মানবজীবনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যেসব নীতি নির্দেশ দিয়েছেন তারই আলোকে খলিফা শাসন পরিচালনা করেন। সে একই নীতির আলোকে খলীফা বা তাঁর প্রতিনিধিগণ বিচার করবেন। এজন্য যারা সত্যিকার মুসলিম তাদের পক্ষে একই সঙ্গে শাসন পরিচালনা ও বিচার করা সম্ভবপর। ইসলামের গৌরবের যুগে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব হয়নি। কোনও এক জিহাদের সময় হযরত আলী এক য়াহূদীকে পর্যুদস্ত করে তার বুকের উপর সওয়ার হয়ে তার গর্দানে খঞ্জর হানতে উদ্যত হওয়াকালে, চতুর য়াহূদী তার মুখমন্ডলে থুথু ফেলে দেয়। তিনি তার এ আকস্মিক আচরণে নিতান্ত ক্রোধান্বিত হলেও তাকে মৃত্যুদণ্ড থেকে অব্যাহতি দান করে মুক্তি দান করেন। তাঁর এ অস্বাভাবিক ব্যবহারে বিস্মিত হয়ে সে প্রশ্ন করল- “আপনি আমাকে হত্যা করেননি কেন?” তার উত্তরে হযরত আলী বলেন- “এখন যদি আমি তোমাকে হত্যা করি- তাহলে আমাকে যে তুমি অপমান করেছো- এ আক্রোশের জন্যই করবো- অথচ তোমাকে আমি আল্লাহ্র দুশমন বলেই পূর্বে হত্যা করতে চেয়েছিলাম”। তাঁর এ আচরণে অভিভূত হয়ে য়াহূদী তৎক্ষণাৎ তাঁর হাতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। এতে বিচারের যে মহৎ দৃষ্টান্তের পরিচয় পাওয়া যায় এ দুনিয়ার ইতিহাসে তা সত্যিই বিরল।
\r\n
এক্ষেত্রে শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছেঃ বিচার করলে পূর্বে বিচারকের জীবনে কতকগুলো শর্ত পালনীয় হওয়া প্রয়োজন। তাকে খাঁটি মুসলিম হতে হবে। তার পক্ষে হককুল আল্লাহ্, হককুল এবাদ প্রভৃতি সম্বন্ধে পরিস্কার ধারণা থাকতে হবে এবং সেসব পালন করার জন্য আল্লাহ্ যে বিধি ব্যবস্থা করেছেন- সে সম্বন্ধে তার সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। সর্বোপরি বিচারকালে তাকে সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক মানস নিয়ে করতে হবে। অভিযুক্ত ব্যক্তির সঙ্গে তার শত বিবাদ বিসম্বাদ থাক না কেন সে কোন অবস্থায়ই সে সব ব্যক্তিগত ব্যাপার দ্বারা প্রভাবান্বিত হবে না। বাস্তব জীবনে দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রেই তা সম্ভবপর নয়। কারণ, যাদের হাতে শাসন বিভাগ রয়েছে-তারা তাদের ব্যক্তিগত আচরণের বিরোধী দলের লোকদের প্রতি প্রায়ই বিমুখ থাকেন। তারা বিচারে প্রবৃত্ত হলে তাদের ব্যক্তিগত আক্রোশের বশবর্তী হয়ে ন্যায়বিচার পরাঙ্মুখ হতে পারেন বলে শাসন বিভাগকে বিচার বিভাগ থেকে পৃথক করা সকল ক্ষেত্রেই বাঞ্ছনীয়।
\r\n
\r\n
\r\n\r\n
সপ্তম পরিচ্ছেদ
\r\n
ইসলামী রাষ্ট্রের ভাঙনের কারণ
\r\n
\r\n
আল্লাহ্র একত্ব, সার্বভৌমত্ব ও মানুষের খিলাফতের ভিত্তিতে গঠিত মানব-প্রকৃতির সম্পূর্ণ অনুকূল ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা রসূলে আকরাম (সঃ)-এর দ্বারা হলেও তাকে পূর্ণ বিকাশের পথে নিয়ে যায় দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রাঃ)। তাঁর ইন্তেকালের পরে নানাবিধ কার্যকারণের ফলে সে রাষ্ট্রে অচিরেই শাহানশাহীতে পরিণত হয়।
\r\n
পরবর্তীকালে দামিশকে উমাইয়াদের, বাগদাদে আব্বাসীয়দের, গ্রানাডায় মুরদের, ভারতে মুঘলদের বা তুর্কিতে উসমানীয়দের আধিপত্য বা রাজ্যবিস্তারকে ইসলামী রাষ্ট্র বলা যায় না। তারা ইসলামের নামে জনসাধারণের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। কোন বিশেষ রাজ্যের ভাঙ্গাগড়া তখন বিশেষ বংশের উত্থান-পতনের অপর নাম হয়ে দাঁড়ায়।
\r\n
এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, মানব প্রকৃতির সম্পূর্ণ অনুকূল সে আদর্শ রাষ্ট্র-ব্যবস্থা অকালে ধ্বংস হয়ে গেল কেন? তাতে কি প্রমাণ হয় না যে, হয়ত সে রাষ্ট্র ব্যবস্থা মানব-প্রকৃতির সম্পূর্ণ অনুকূল ছিল না অথবা তার অর্থনৈতিক ভিত্তি এতই দুর্বল ছিল যে, তাতে মহান আদর্শ থাকলেও তার দুর্বলতার জন্যেই অকালে লয় পেয়ে গেছে?
\r\n
বস্তুতান্ত্রিক সাম্যবাদীরা মনে করেন, ইতিহাসের ধারায় অর্থনৈতিক কার্যকারণের ফলেই মানুষের সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে মানুষের সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে পড়ে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে আরবের মাটিতে উৎপাদনের যে ব্যবস্থা ছিল- তার পরিবর্তন হওয়ায় ইসলামী সমাজেও তার কার্যকারিতার প্রতিফলন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। ইসলামের অভ্যুদয়ের সময় একদিকে যাযাবর বেদুঈনেরা ছিল পশুচারিক পর্যায়ের২০৬ অপরদিকে মক্কা ও মদীনার অপেক্ষাকৃত উন্নত কেন্দ্রগুলোয় ছিল একদল ব্যবসায়ী। ইসলামের বিস্তৃতির ফলে ইরাক, সিরিয়া, বাহরাইন বিজিত হলে মুসলিমেরা ভূমির সংস্পর্শে আসে। তাই ভূমিতে উৎপাদনের ব্যবস্থাতে তারা অভ্যস্ত হওয়ার ফলে আস্তে আস্তে তাদের সমাজে সামন্ততন্ত্রের ভাবধারা প্রবেশ করে। কাজেই সমস্ত জগৎ যে ভাবধারা ধরে চলেছিল, সে ধারা ইসলামের মধ্যেও প্রবেশ করে। ইসলামের বিশিষ্ট অর্থনীতি তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। কাজেই ধর্ম হিসেবে ইসলামের বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে কিন্তু অর্থনীতিতে ইসলামের কোন বৈশিষ্ট্য নেই। যে অর্থনৈতিক সূত্র ধরে দুনিয়া বস্তুতান্ত্রিক সমাজবাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছে-ইসলামপন্থীকেও সেই পথেই অগ্রসর হতে হবে। ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের ভাঙনের কারণের মধ্যে তাই আশ্চর্য কোন কিছুই নেই। এ ভাঙ্গন তার কাছে ছিল অবধারিত।
\r\n
মাত্র সেদিন প্রকাশিত (Modern Islam in India) নামক পুস্তক উইলফ্রেড কেন্টওয়েল স্মিথ এ তত্ত্বই প্রমাণ করতে চেয়েছেন। তাঁর মতে ভারতের মুসলিমদের মতবাদও যুগে যুগে অর্থনৈতিক কারণের ফলে পরিবর্তিত হয়েছে।
\r\n
এঁদের যুক্তির মধ্যে রয়েছে এক বিরাট ফাঁক। তার জন্যই আপাতত অবিশ্বাসী মানব-মনকে মুগ্ধ করলেও ন্যায়শাস্ত্রের কষ্টিপাথরে এঁদের যুক্তি কিছুতেই টেকে না। তাঁদের পক্ষে প্রমাণ করা উচিত (১) ইসলামী অর্থনীতি মানবজীবনে কার্যকরী হতে পারে না, তাকে সমাজে প্রয়োগ করলেও সে অন্য অর্থনীতিতে লয় পেতে বাধ্য। (২) সে অর্থনীতি গ্রহণ করে এবং তাকে বাস্তবজীবনে রূপায়িত করেও ইসলামী সমাজ টিকে থাকেনি।
\r\n
এ দুটো বিষয় প্রমাণ না করে যদি জোর করে বলা হয়-যেহেতু ইসলামী অর্থনীতি টিকে থাকেনি- সেজন্যই তা অচল-তা’হলে কি বলতে হবে দুনিয়ার বুকে যা-ই ঘটে, তা-ই সচল ও সত্যি, আর যা এককালে ফলে ওঠেনি অথচ পরে রূপায়িত হয়েছে তা তখন ছিল অসত্য এবং বর্তমানে সত্য? মার্কসীয় অর্থনীতির সূত্র জগতে প্রথম প্রচারিত হয় Das Capital প্রকাশিত হওয়ার পরে। তাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য মার্কস ও এঞ্জেলস কমিউনিষ্ট মেনিফেষ্টো প্রকাশ করেন ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে। তার ফলে ফরাসী রাষ্ট্র বিপ্লবের পরিণতিতে প্যারিস কমিউন প্রতিষ্ঠিত হয় সে অর্থনীতিকে রূপায়িত করার জন্য, কিন্তু তা টিকে থাকেনি। মাত্র সেদিন ১৯৭১ সালে মার্কসীয় মতবাদের প্রতিষ্ঠাকল্পে রাশিয়ায় রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে। সে জন্য কি বলতে হবে- মানব জীবনের পক্ষে মার্কসীয় মতবাদ তখন ছিল অকার্যকরী বা মার্কসীয় মতবাদ গ্রহণ করার ফলেই প্যারিস কমিউন ভেঙ্গে গেছে ?
\r\n
তার উত্তরে যদি বলা যায়, প্যারিস কমিউন ভেঙ্গে যাওয়ার কারণ সমাজজীবন যেসব ধাপের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজন, সে ধাপগুলো তখন ডিঙ্গিয়ে যায়নি বলে অর্থনীতি গ্রহণ করতে পারেনি, তার অর্থনৈতিক বা সামাজিক কাঠামো ভেঙ্গে যায়নি- তা’হলে ইসলামী সমাজের বেলায়ও তো এই যুক্তিই প্রয়োগ করে বলা যেতে পারে-মানবজীবনের পূর্ন বিকাশের পক্ষে ইসলামী অর্থনীতি গ্রহণযোগ্য বলে তখনকার সমাজে তা আর দীর্ঘকাল কার্যকরী হয়নি।
\r\n
জগৎ সভ্যতার আলোচনা করলে বিশেষভাবে এ সত্যই প্রমাণিত হয়। মানব সভ্যতার ইতিহাসের আলোচনায় দেখা যায়, মানবজীবনের বিকাশের সহায়করুপে ক্রমেই কতকগুলো মৌলিক অধিকারের২০৭ নীতি স্বীকৃত হয়েছে। বর্তমান জগতে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতাকে মানবজীবনে বিকশিত করার জন্য ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের দার্শনিক ভিত্তির ওপর গড়ে উঠেছে পুঁজিবাদী সমাজ। তার অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের ফলে বস্তুতান্ত্রিক সমাজবাদী প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে অবশ্যম্ভাবীরূপে। তার ফলে সমাজবাদী রাষ্ট্র গঠনের চলছে প্রচেষ্টা, তাতে সাম্য, মৈত্রী বিশেষভাবে ফলে উঠলেও স্বাধীনতাকে দেয়া হয়েছে বিসর্জন। মানবজীবনের মৌলিক অধিকার মানব-মনে দানা বাঁধতে থাকলে অনাগত বিশ্বসংস্থা গড়ে উঠবে এই তিনটে মৌলিক অধিকারের ভিত্তিতে-যা কেবল ইসলামী ব্যবস্থাতেই সম্ভব।
\r\n
দ্বিতীয়ত ইসলামী সমাজ ইসলামের অর্থনৈতিক ভিত্তি অক্ষুণ্ন রেখেই ধ্বংস হয়নি, বরং বর্জন করেই ধ্বংস হয়েছে। এইটেই আজকের দিনে বিশেষভাবে প্রণিদানের বিষয়। যদি সে অর্থনীতি গ্রহণ করে ইসলামী সমাজ তলিয়ে যেতো, তা’হলে অবশ্য বলবার কারণ হতো-ইসলামের অর্থনৈতিক ভিত্তির দুর্বলতার জন্য ইসলামী সমাজ লয় পেতে বাধ্য হয়েছে।
\r\n
সত্যিকার ইতিহাস পাঠকমাত্রেই জানেন, ইসলামী অর্থনীতি যতদিন পর্যন্ত সমাজজীবনে চালু ছিল, ততদিন রাষ্ট্রে অভাব-অভিযোগ বলে কিছুই ছিল না। যেই তাতে শাহানশাহীর ভাবধারার প্রবর্তন হয়, তখনই তাতে জনগণের দুঃখ-দারিদ্র্যের সৃষ্টি হয় । খলীফা উমর (রাঃ)-এর খিলাফতের সময়কে ইসলামী সমাজে সুবর্ণ যুগ বলা যেতে পারে, সে সময় বায়তুল মালের আমদানি সব সময়ই উদ্ধৃত্ত থাকতো। কাজেই, যাঁরা ইসলামের অর্থনীতি সম্বন্ধে এরূপ মন্তব্য করেন তাঁদের এসব মন্তব্য বিদ্ধেষপ্রসূতই বলতে হবে।
\r\n
খোলা চোখে বিচার করলে দেখা যায়, অর্থনৈতিক দুর্বলতার জন্য নয়, নানাবিধ কারণেই ইসলামী রাষ্ট্র ভেঙ্গে গেছে। ইসলামী রাষ্ট্রের ভাঙনের কারণঃ
\r\n
১.যে জীবন দর্শনের ওপর ইসলাম প্রতিষ্ঠিত, তা আরব-জীবনে রূপায়িত হয়নি। তার পক্ষে নানা প্রতিবন্ধকতা ছিল বর্তমান। ইসলামের মূল ভিত্তি আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব ও মানুষের প্রতিনিধিত্ব। সে ভিত্তিতে রাষ্ট্রকে রূপায়িত করতে হলে মানুষকে আল্লাহ্র গুনে গুণান্বিত হতে হয়। আল্লাহ্র প্রতিনিধিত্ব দুনিয়ার বুকে তার রাষ্ট্র রূপায়িত করার জন্য গুণের মাপকাঠিতে আল্লাহ্র রসূলের খলীফা বা প্রতিনিধি নির্বাচন করতে বাধ্য। তাতে আধুনিক গণতন্ত্রে২০৮ যেমন সংখার দিক দিয়ে গুরুত্ব আরোপ করে প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়, তা না করে গুণের ভিত্তিতে খলীফা নির্বাচন করা ছিল সুযোগ ও সুবিধা। এতে সর্বসাধারণের ভোটের অধিকার স্বীকৃত হয়েছিল। পরবর্তীকালে বিস্তৃতির ফলে ইসলাম আরব থেকে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়লে বিজিত দেশের লোকেরা ইসলামী সমাজে তাদের কোন প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। তাই ইসলাম ক্রমেই আরবকেন্দ্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় পরিণত হয়। ইসলামের বিস্তারের ফলে ক্রমশ সিরিয়া, ইরাক, ইরান, মিসর প্রভৃতি দেশ ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে এলে পর, সে দেশের সদ্য ধর্মান্তরিত মুসলিমেরা আরব দেশীয় নানা গোত্রের সঙ্গে এক কাল্পনিক রক্ত সম্পর্ক স্থাপনে হয় উৎসুক। এ প্রথাকে মাওলি প্রথা বলা হয়।
\r\n
এতে একদিকে মুসলিমদের মধ্যে সম্পর্ক গাঢ়তর হলেও অন্যদিকে তার ফল বিষের মত দেখা দেয়। কারণ এভাবে আরব গোত্রের লোকের সঙ্গে রক্ত সম্পর্ক স্থাপন করার ফলে তারা খলীফা নির্বাচনে আরবের মাটিতে তাদের মাওলাদের ওপর সমস্ত ভার ছেড়ে দিত। ইসলামের মূলনীতি অস্বীকার করে স্বয়ং তাতে হস্তক্ষেপ না করে মাওলাদের মারফতে তাদের অভিমত ব্যক্ত করত। তার ফলে খলীফার নির্বাচনে আরবেরা সরাসরি নির্বাচনে২০৯ ও আরব জাতিরা পরোক্ষ নির্বাচনে২১০ অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। গোটা মুসলিম জাতি তার জন্য অখন্ড জাতিতে পরিণত হতে পারেনি। বলা বাহুল্য, সে জন্য নির্বাচনের ব্যাপারে আরব দেশীয় অভিজাত সম্প্রদায়ের মতামতই ছিল বেশি গ্রহণযোগ্য।
\r\n
হযরত আবুবকর (রাঃ) ও হযরত উমর (রাঃ)-এর খিলাফতের সময় আরবের মাটিতে বনি হাশিম ও বনি উমাইয়ার আধিপত্য প্রতিষ্ঠার কোন সুবিধা না হওয়ায় আরবের লোকের প্রাধান্যের জন্য কোন ক্ষতি হয়নি। তাদের ইন্তিকালের পরে ক্রমেই বনি হাশিম ও বনি উমাইয়ার দ্বন্দ্ব প্রকট মূর্তি ধারণ করায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রকৃতপক্ষে বনি হাশিম ও বনি উমাইয়ার মত দুই শিবিরে বিভক্তে হয়ে পড়ে। তার ফলে (ক) ইসলামী রাষ্ট্রে আরবের গৃহযুদ্ধ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে (খ) ইসলামের মূলনীতি সর্বসাধারন মুসলিমের খলীফা নির্বাচনে সাধারণ অধিকার প্রকারান্তরে অস্বীকৃত হয় এবং (গ) সর্বসাধারণ মুসলিমের মনে সংঘ-চেতনা দানা বাঁধতে পারেনি।
\r\n
খলীফার নির্বাচনে মদিনার উচ্চ শ্রেণীর মতামত গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হওয়ায় আরবের মাটির অন্যান্য অবজ্ঞাত সমাজেও বিদ্রোহ দেখা দেয়। হযরত আলী (রাঃ) ও মু’আবিয়ার দ্বন্দ্বে খারিজিরা তখনকার দিনের মুসলিম জনসাধারণের বিক্ষুব্ধ মানসেরই পরিচয় দিয়েছে। তারা চেয়েছিল সবসময়ই খলীফা নির্বাচনে সর্বসাধারণ মুসলিম অভিমতই গ্রহণ করা হবে। ধর্ম সংক্রান্ত অন্যান্য মতবাদে খারিজিরা অন্ধত্বের পরিচয় দিয়েছে সত্য, তবু তাদের রাজনৈতিক মতবাদের সত্যিকার ইসলামী নীতির প্রতি শ্রদ্ধা আজও আমাদের বিস্ময়ের বিষয়।
\r\n
তখন পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্রে দাস-প্রথা এবং কুরায়েশদের প্রাধান্য অক্ষুণ্ন থাকায় তাদের এ অভিমত বৈপ্লবিক ঘোষণার মত শুনিয়েছিল। ইসলামী সমাজে সে কালে কিছুতেই দাসপ্রথা থাকতে পারে না, এ সত্য মুসলিম জনসাধারণ বুঝতে পারেনি বলে খারিজিরা তখন সমাজজীবনে অপাংক্তেয় হয়ে পড়ে। খারিজিদের নীতি গৃহীত হলে ইসলামী রাষ্ট্র এভাবে আরবদেশীয় বিভিন্ন গোত্রের দ্বন্দ্বে বিচ্ছিন্ন হত না, অপরদিকে মাওলি প্রথার প্রবর্তন না হলে গোটা মুসলিম অখন্ড জাতিরুপেই পরিগণিত হতে পারত।
\r\n
২. হযরত রসূলে আকরাম (সঃ)-এর আহ্বানে যারা ইসলাম কবুল করেছিল তাদের মধ্যে অনেকেই ছিল মুনাফিক। ইসলামের সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার আদর্শ তাদের মুগ্ধ করেনি। নব-প্রবর্তিত বৈপ্লবিক জীবনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ব্যর্থকাম হয়েই তারা ইসলামে প্রবেশ করে। ঘরের শত্রু হয়ে ইসলামের ধ্বংস ত্বরান্বিত করার দুরভিসন্ধি ছিল তাদের মনে বদ্ধমূল। এদের হাতেই ইসলাম পরবর্তীকালে শাহানশাহীতে পরিণত হয় এবং এদের হাতেই অমুসলিমদের চেয়ে ইসলামের অবমাননা হয় বেশি। এদের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে যুগে যুগে সত্যিকার ইসলামপন্থীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন।
\r\n
আমীর মুআবিয়ার জীবনেই ইসলামী সমাজে শাহানশাহীর ভাবধারা প্রথম প্রকাশিত হয়। হযরত উসমান (রাঃ)-এর সরলতার সুযোগ নিয়ে দামিশ্কে তিনি পুঁজিবাদী নীতির প্রবর্তন করলে তার বিরুদ্ধে রসূলে আকরাম (সঃ)-এর প্রিয় সাহাবী হযরত আবু যর গিফারী (রাঃ) বিদ্রোহ ঘোষণা করে, ইসলামের শৈশবাবস্থা স্মরণ করে স্বেচ্ছায় নির্জনবাসে চলে যান। হযরত আলী (রাঃ) ও তাঁর প্রিয় পুত্র হোসেন (রাঃ) ইসলামী আদর্শকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্য শাহাদাত বরণ করেন।
\r\n
পরবর্তীকালে উমাইয়া ও আব্বাসীয় আমলে মুসলিম রাষ্ট্র প্রগতির পথে আর অগ্রসর হতে পারেনি। তার স্রোত উল্টো বইতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে যে বিপ্লবের প্রেক্ষাপটে প্রথম দুই খলীফার সময় ইসলামী রাষ্ট্র প্রবল গতিতে আদর্শ বাস্তবায়নে ছুটে চলে হযরত উসমান (রাঃ)-এর খিলাফতের সময় থেকেই প্রতিবিপ্লবের২১১ ফলে আস্তে আস্তে উল্টোদিকে চলতে শুরু করে। বনি উমাইয়া ও বনি আব্বাসীয়ের মধ্যে উমর ইবনে আব্দুল আযীয বা আব্দুল্লাহ আল-মামুন তাঁদের বংশের ব্যক্তিক্রম হলেও সে সময়কার বাদশাহী স্রোতের তলায় তাঁদের ব্যক্তিগত সদিচ্ছা কার্যকরী হতে পারেনি।
\r\n
৩. ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভাঙনের কারণস্বরূপ বলা যেতে পারে- ভূমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার নীতি গ্রহণের২১২ ফলেই ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনীতির মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। ইসলাম কোন অবস্থাতেই মাটির ওপর ব্যক্তির মালিকানা স্বীকার করেনি। আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের সঙ্গে ব্যক্তিগত মালিকানা কিছুতেই খাপ খায় না। ইসলামী সমাজে ব্যক্তিকে রক্ষক২১৩ বা ভোগদখলকারী হিসাবে তার প্রয়োজনমত আল্লাহ্র নিয়ামত ভোগ করতে দেওয়া হয়।
\r\n
ইসলামী রাষ্ট্রের সুবর্ণ যুগে হযরত উমর (রাঃ) সে নীতিই গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর আদর্শ ছিল সর্বাবস্থায় মুসলিম জনসাধারণকে রাষ্ট্রের অঙ্গ জ্ঞান করে তাদের খোরাক-পোশাক প্রভৃতি জীবন যাপনের সমস্ত উপকরণ রাষ্ট্র থেকে সরবরাহ করা। তাঁর বিজিত দেশের ভূমি তিনি মুসলমানদের মধ্যে ভাগ করেননি, বিজিত জাতির মধ্যে তিনি সে ভূমি ভাগ করে দেন। সে আদর্শ রাষ্ট্র সকল সময়েই জনসাধারণের সুখ-দুঃখের জন্য দায়ী থাকায় ব্যক্তিগত শোষণ বা ভোগ-বিলাসের যাতে কোন সুবিধা না হয়, তার সকল ব্যবস্থাই তিনি করেছিলেন। তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রাঃ)-এর সরলতার সুযোগ নিয়ে সিরিয়ার গভর্নর মুআবিয়া সিরিয়াতে এক বিস্তৃত ভুখন্ড জায়গীর স্বরূপ আদায় করেন। মুআবিয়া তাঁর শাসনকালে মিসরের সমস্ত রাজস্ব আমর বিন’আসকে দান করেন।
\r\n
এসব কার্যকারণের ফলেই আল্লাহ্র রাষ্ট্রের মালিকানা অবশেষে ব্যক্তিবিশেষ বা বংশবিশেষের হাতে চলে যায় ও ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। যার ফলে জায়গীরপ্রাপ্ত ভূমি থেকে আয় বন্ধ হয়ে ক্রমেই সেই রাষ্ট্রের অন্যান্য নানা প্রয়োজনীয় খাতে ব্যয় করার পক্ষে উপযুক্ত অর্থের অভাব দেখা দেয়।
\r\n
৪.ইসলামী রাষ্ট্রের ভাঙনের সর্বপ্রধান কারণ তার অগ্রবর্তিতা। ইসলাম যে আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা দুনিয়ায় কায়েম করতে চেয়েছে, সে সময়কার সাধারণ মানুষ সে ব্যবস্থ মোটেই বুঝতে পারেনি। মানব জীবনকে ব্যাপক ও পূর্ণভাবে বিকশিত করে তুলতে হলে যে মানবিক অধিকার গোড়াতেই স্বীকার করে নিতে হয়, সেগুলো তখনকার আরব সমাজে মোটেই স্বীকৃত হয়নি।
\r\n
মানবজীবনের এই সন্ধিক্ষণে এসে দেখা দিয়েছিল মানুষের নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)। জীবন বিকাশের যে চাবিকাঠি তিনি নিয়ে এসেছিলেন তখনকার অনুন্নত আরব সমাজ তার প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করতে পারেনি। আল্লাহ্র ওয়াহ্দানীয়ত ও সার্বভৌমত্ব মন্ত্র তারা গ্রহণ করেছিল বটে তবে তার সুদূরপ্রসারী ফলে মানবজীবনে বিভিন্ন সমস্যার কিভাবে সমাধান করা যায় এবং তার প্রয়োগে জীবনধারা কিভাবে সরলরেখায় অগ্রসর হতে পারে সে তত্ত্ব উপলব্ধি করার শক্তি তাদের ছিল না। কাজেই আল্লাহ্র রসূলের ব্যক্তিগত চরিত্রমাধুর্য ও নিষ্কলঙ্ক জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েই তারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল। ইসলামের বৈপ্লবিক প্রেরণায় তারা উদ্ধুদ্ধ হয়নি। খুলাফায়ে রাশেদীন, হযরত আবু যর গিফারী (রাঃ) বা আরও দু’একজন দূরদর্শী মহাপ্রাণ ব্যক্তি ব্যতীত মানবজীবনের কল্যাণ সাধনে ইসলাম কিভাবে কার্যকরী সে তত্ত্ব অনেকের কাছেই সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল।
\r\n
ইসলামের বাইরের খোলস দেখে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল, পরবর্তীকালে উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে তাদের মনেই আবার গায়ের ইসলামী ভাবধারা প্রবল হয়ে পড়ে।
\r\n
কুরআন শরীফের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল মনোবৃত্তিতে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। কুরআন শরীফে মানবজীবনকে চিরকাল পরিচালিত করার জন্য রয়েছে কতগুলো আদর্শ নীতি। আবার কতগুলোতে আরবের তৎকালীন সমাজজীবনের রীতিনীতি পরবর্তিত অবস্থায় গ্রহণ করা হয়। সেগুলো যে জীবন বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানবজীবন থেকেক নিশ্চিহ্ন হতে বাধ্য তার ইঙ্গিতও কুরআন শরীফে রয়েছে। সুদ,ব্যভিচার,শরাব,শূকরের গোশত ইসলামে চিরকালই অকল্যাণকর। তাই সকল যুগেই তা’ হারাম ও নিষিদ্ধ। দাসপ্রথা, বহুবিবাহ প্রথা সে আরব সমাজে ছিল বিশেষভাবে প্রচলিত। সেগুলো কুরআন শরীফে নিষিদ্ধ হয়নি সত্য কিন্তু তাদের ওপর যে শর্ত আরোপ করা হয়েছে, তা প্রতিপালন করা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই কুরআন শরীফে বাহ্যত নিষিদ্ধ নয়, এমন কতকগুলো নীতি যে পরবর্তী সমাজব্যবস্থায় নিশ্চিহ্ন করা হবে, তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।
\r\n
সামাজিক রীতিনীতির মধ্যেও কুরআন শরীফের আদেশ-নিষেধগুলোর মধ্যে একটি পার্থক্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যে সকল কার্যকলাপ ইসলাম চিরকালের জন্য নিষিদ্ধ করে দিয়েছে, সেগুলো প্রচলনের কোন সুবিধা নেই। সুদ,যিনা (ব্যভিচার)শরাব- কোনকালে কোন অবস্থাতেই জায়েয হতে পারে না। কিন্ত কতগুলো জায়েয কাজকে পরবর্তীকালের মুসলিমদের সর্ববাদীসম্মত অভিমত (ইজমা) দ্বারা পরিবর্তন করা না-জায়েয নয়। চার স্ত্রীর পরিবর্তে এক স্ত্রী গ্রহণ বা দাস প্রথারবিলোপ ইসলামের চোখে নিন্দনীয় নয়।
\r\n
অনেক ক্ষেত্রেই স্বীয় বিচার-বুদ্ধির ব্যবহার ইসলাম অনুমোদন করেছে। আফসোসের বিষয়, পতন যুগে ইসলামের মূল আদর্শ হারিয়ে কুরআন শরীফ অথবা হাদিস শরীফের শাব্দিক ব্যাখ্যা নিয়ে মাথা ঘামানো মুসলিম সমাজে অভ্যাসে পরিণত হয়। ফলে যে বৈপ্লবিক জীবনধারার প্রবর্তনের জন্য ইসলাম নাযিল হয়েছিল তা’ ব্যর্থ হয়। এর জন্য দায়ী ছিল অনুন্নত সমাজজীবন। সে সমাজজীবন মানবতার পারিপার্শ্বিক আদর্শ গ্রহণ করে সে সমাজ ব রাষ্ট্র সামন্ততন্ত্রের আওতায় চলে যায়।
\r\n
\r\n\r\n
অষ্টম পরিচ্ছেদ
\r\n
ইসলামী সমাজের ভূমিনীতি ও তার প্রয়োগ
\r\n
ইসলামী জীবনদর্শন ও তার ফলিত রূপ
\r\n
ইসলামী জীবনদর্শনের আলোকেই ইসলামী সমাজের ভূমি-নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব ইসলামী রাষ্ট্রের চরম ও পরম তত্ত্ব। মানুষ আল্লাহ্র প্রতিনিধি হিসাবে সে আদর্শ রাষ্ট্র গড়ে তুলবে। সেখানে ব্যক্তিগত অথবা সমাজগৎ সুখ-সুবিধার জন্য বিলাসিতা প্রশ্রয় পেতে পারে না।
\r\n
ইসলামী সমাজ অথবা রাষ্ট্রের কোন বস্তুর ওপরই কারো ব্যক্তিগত মালিকানা নেই, আছে শুধু ভোগের জন্য দখলের অধিকার। রাব্বুল আলামীনের খলীফা হিসেবে ব্যক্তিগত জীবনে অথবা সামাজিক জীবনে মানুষ আল্লাহ্র মালিকানাকে মেনে নিয়ে সেই সম্পদকে ভোগ করতে পারে, এর অতিরিক্ত কোন দাবিই করতে পারে না।
\r\n
তাই, ইসলামী সমাজে মানবসাধারণকে জীবন ধারণের জন্য উপযুক্ত জমিরক্ষক হিসেবে ভোগ করতে দেওয়া হয়। অতিরিক্ত সম্পত্তি রাষ্ট্রের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়, অথবা গো-চারণ ভূমি, কবরস্থান, সর্বসাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত হয়, যাতে ভূমি ব্যক্তিবিশেষের বা বংশবিশেষের সম্পত্তিতে পরিণত না হয়, তার প্রতি লক্ষ্য রেখেই ইসলামী রাষ্ট্রের ভূমি বন্টনের নিয়ম প্রবর্তন করা হয়েছে।
\r\n
\r\n
\r\n
ইসলামী সমাজে ভোগ দখলের অধিকার
\r\n
নবী করীম (সঃ)-এর মক্কা থেকে মদীনাতে হিজরতের পর ভূ-সম্পত্তিতে যে ইতিহাস পাওয়া যায় তা থেকে দেখা যায়, “আনসার ও মুহাজিরগণের ভূ-সম্পত্তির স্বত্বাধিকারের অর্থ এই যে, নবী করীম (সঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীন দান ও জায়গীরস্বরূপ যে জমি তাদের দিয়েছেন তাই তাদের সরল জীবন যাপনেও কাজে লাগতো”।
\r\n
“বনজর’ (অনাবাদী) ভূমিকে আবাদ করে তাঁরা ফসলের উপযোগী করতেন। এগুলোও আয়তনের দিক থেকে বর্তমান যুগের বড় বড় গ্রাম বা মৌজার মত ছিল না। মাত্র কতক আবাদী জমির সমষ্টি ছিল-কাজেই দেখা যায়, ইসলামী সমাজে দুইভাবে রক্ষক হিসেবে জমির উপর মানুষের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। (১) যে সকল জমি কৃষকেরা নবী করীম (সঃ) অথবা খুলাফায়ে রাশেদীনের কাছ থেকে দান অথবা জায়গীরস্বরূপ পেয়েছিলেন অথবা (২) যে সকল অনাবাদী জমিকে তাঁরা আবাদ করে ফসলের উপযোগী করে তুলেছিলেন, মাত্র সেসব জমিতেই তাঁদের ভোগ দখলের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কোন কোন শর্তে বনজর জমিতে জোত স্বত্ব বর্তাতে পারে, তার নজিরস্বরূপ দেখা যায়, কৃষিকার্যের উন্নতি এবং আবাদীর প্রচেষ্টাকে ইসলামী অর্থনীতিতে মৃতের জীবন দানের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। পতিত, অনাবাদী জমিকে কৃষি উপযোগী করে তুললে তাতে রক্ষক হিসেবে চাষীর জোতস্বত্ব বর্তাতে পারে। ... “পতিত জমিকে চাষের উপযোগী করার অর্থ তাকে পূর্ণ জীবন দেওয়া। নীরস, অনুর্বর জমি, বালুকাময় জমি, প্রস্তরপূর্ণ জমি বা টিলা সাধারণভাবে অনুপযুক্ত জমিরুপে পরিগণিত। শক্ত পরিশ্রমের দ্বারা অধিক পরিমিত ভূমিকে কৃষির উপযুক্ত করা সম্ভব। এরূপ অনুপযুক্ত সমস্ত জমিজমাকে কৃষিকার্যের উপযুক্ত করা এবং কাচাঁমাল দ্বারা দেশের সমৃদ্ধি সাধন ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রধানতম অংশ। যথাসাধ্য পতিত জমি থাকতে না দেয়া, যেসব জমি কৃষির উপযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও পতিত পড়ে রয়েছে তাকে কৃষির উপযুক্ত করে তোলা-প্রভৃতির জন্য ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় দুটো উপায় রয়েছেঃ
\r\n
১.প্রথমত আমিরুল মুমিনিন দেশের জনসাধারণকে উৎসাহিত করবেন এবং এই মর্মে প্রচার করবেন যে, যে যতখানি পতিত জমি আবাদ করবে সে-ই তার অধিকারী হবে।
\r\n
২.ইমামের কর্তব্য-পতিত জমিকে অথবা উত্তরাধিকারবিহীন, অধিকারীহীন জমিকে জায়গীরের মত দেশের লোকের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া, যাতে ঐ সব জমি কৃষির উপযুক্ত হতে পারে এবং এগুলোর বিলি ব্যবস্থায় সর্বসাধারণ মুসলমানের উপকার হয়।
\r\n
ফিকাহ শাস্ত্রকারগণের মতে-যদি এরূপ বনজর জমি তৈরি করা অধিক ব্যয়সাপেক্ষ হয়, তাহলে দু’তিন বছরের খাজনা মাফ করার অধিকার ইমামের রয়েছে। এ সমস্ত জমি সম্বন্ধে জনাব রসূলে করীম (সঃ) ফরমায়েছেন-যে জমির কোন স্বত্বাধিকারী নেই, এরূপ জমিকে কেউ কৃষিকার্যের উপযুক্ত করে নিলে- সে ব্যক্তিই এ জমিনের স্বত্বাধিকারী (অবশ্য রক্ষক অর্থে) হওয়ার অধিকারী। যে ব্যক্তি মৃত জমিকে পুনর্জীবিত করে সে জমি তারই।
\r\n
তিনটি শর্ত রয়েছে
\r\n
(ক) জমি যেন শহরতলীতে না হয়, শহরের প্রয়োজনে না লাগে এবং গ্রামবাসীগণের ফায়, গোবর ও কবরস্থান না হয়। আব্বাসীয় খলীফা হারুন-অর-রশিদকে সম্বোধন করে ইমাম আবু ইউসুফ বলেছেন, “ হে আমিরুল মুমিনিন, যে সব জমি যুদ্ধ বিগ্রহ অথবা সন্ধির দ্বারা বিজিত হয়েছে সে সব জমি ও যেসব গ্রাম-অঞ্চলের জমি এমন অবস্থায় পড়ে রয়েছে যে, তাতে ঘর-বাড়ি বা ক্ষেত-খামারের কোন চিহ্ন নেই, সে জমি সম্বন্ধে আপনি আমার অভিমত জানতে চেয়েছেন। তার উত্তরে বলা যায়-যেসব জমিতে কোন ঘর-বাড়ির চিহ্ন না থাকে, গ্রামবাসীগণের কোন ‘ফায়’ সম্পত্তি, কবরস্থান চারণভূমি যা নয়, কারো স্বত্বাধিকার অথবা দখলাধিকার নয়-এরুপ জমিকে মৃত জমি বলা হয়। যে ব্যক্তি এরূপ জমিকে অথবা কোন অংশকে পুনর্জীবিত অর্থাৎ কৃষিকার্যের উপযোগী করে তুলে তার স্বত্ব (ভোগ দখলের) বর্তাবে। আপনার বিবেচনা মত এসব ভূমি জায়গীরের মত বন্দোবস্ত দিতে পারেন। ‘কিতাবুল খারাজ’ ‘ইসলাম কা একতেসাদি নেজামে’ ‘ফায় সম্পত্তির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, যদি ইসলামী সেনার কাছে পরাজিত হয়ে অথবা ভয় পেয়ে যুদ্ধ না করে বিধর্মী তাদের সম্পত্তি ফেলে পলায়ন করে অথবা যুদ্ধের ভয়ে তাদের আপন জমি তাদের হাতে রেখেই ইসলামী রাষ্ট্রকে নির্দিষ্ট কর দিতে চায় অথবা যদি তাদের খাজনা বা জিযিয়া নির্দিষ্ট করে তাদের কাছেই তাদের জমি বন্দোবস্ত দেওয়া যায়- তাহলে সেই নির্দিষ্ট কর, খাজনা অথবা জিযিয়াকে ‘কর’বলে। এ নীতি অনুসারে জিযিয়া বা খাজনাকে ‘ফায়’ বলে গণ্য করা হয়
\r\n
(খ) যদি কেউ ইমামের কাছ থেকে এ জমি অধিকার করার পর তিনি বছর পর্যন্ত পতিত ফেলে রাখে আর জায়গীর দেওয়ার যে উদ্দেশ্য ছিল, তা পূর্ণ না করে তা’হলে তার হাত থেকে এ জমি ছিনিয়ে নিয়ে অন্য ব্যক্তিকে বন্দোবস্ত দেওয়া যাবে।
\r\n
(গ) তৃতীয় শর্ত- এই জমির মধ্যে শহর, তালাব, জলাশয়, ‘হবীম’ বা মসজিদ-সংলগ্ন ভূমি থাকবে না। সে ‘হবীমের’ পরিমাণ ৪০ গজ এবং ক্ষেতের জন্য নির্দিষ্ট ভূমির পরিমাণ ৬০ গজ।
\r\n
এবং বিধ শর্তসাপেক্ষে যে কেউ-মুসলিম অথবা অমুসলিম-পতিত জমিকে আবার করলে তাতেও তার ভোগ-দখলের অধিকার বর্তাবে।
\r\n
ভোগ-দখলের জমির পরিমাণ
\r\n
সে জমির পরিমাণ হবে কোন ব্যক্তির বা তার পরিবারের জীবিকার পক্ষে উপযুক্ত, তার বেশি জমিতে তাকে কোন মতেই ভোগ-দখলের অধিকার দেওয়া যাবে না। হযরত উমর ফারুক (রাঃ)-এর কার্যাবলি থেকে এ নীতিরই সমর্থন পাওয়া যায়। যাতে কোন অবস্থায়ই জমিদারি বা বড় বড় জোতদারির সৃষ্টি না হয়, তার প্রতি দৃষ্টি রেখে তিনি ইসলামী সমাজে ভূমি বিলির ব্যবস্থা করেছেন। ইরাক ও সিরিয়া বিজিত হলে তিনি সাহাবীদের শত আবেদন সত্ত্বেও সেসব দেশের জমি তাদের জায়গিরস্বরূপ দান করেননি, তার ওপর প্রয়োজনের অতিরিক্ত বলে হযরত বিলালের জায়গিরপ্রাপ্ত জমি থেকে একটি অংশ কেটে নিয়ে প্রকৃত হকদারের হাতে তুলে দিয়েছেন।
\r\n
জমি থেকে ফসল উৎপাদনের নীতি
\r\n
সে জমিতে চাষী কিভাবে ফসল উৎপাদন করবে, তার স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে ইসলামী সমাজে। চাষী তার জমি নিজে চাষাবাদ করে তা’ থেকে ফসল উৎপাদন করবে। যদি কোন কারণবশত তাতে অসমর্থ হয় তা’হলে তার অপর ভাইকে সহানুভূতি প্রদর্শনপূর্বক চাষ করতে দেবে।
\r\n
উঁচু স্তরের সাহাবীরা জমি থেকে উপস্বত্ব ভোগের এ পদ্ধতিকেই খাঁটি ইসলামী পদ্ধতি বলে গ্রহণ করেছে। এ সম্বন্ধে হযরত রাফে বিন খাদিজ (রাঃ) বলেন-আল্লাহ্র রসূল (সঃ) আমাদের এমন কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন, যাতে বাহ্যত আমাদের উপকার হতে পারে। যেমন আমাদের মধ্যে যদি কারো জমি থাকে, তবে সে জমিকে ভাগে অথবা লগ্নিতে দিতে পারবে না। হযরত (সঃ) ফরমিয়েছেন-যার জমি আছে, সে নিজেই তা চাষ-আবাদ করবে অথবা অন্য মুসলমান ভাইকে বিনালাভে সহানুভূতি প্রদর্শনপূর্বক চাষ করতে দেবে।
\r\n
রাফে-বিন খাদিজের মতে, ভাগে চাষাবাদের প্রবর্তন হলে নানা ঝঞ্ঝাটের সৃষ্টি হতে পারে। কারণ জমি যদি ভাগে দেওয়ার প্রচলন হয়, তা’হলে ভোগ-দখলকারী চাইবে জমির উর্বর অংশ থেকে ফসল নিতে। অপরদিকে যে আবাদ করেছে, সেও চাইবে অনুরূপ অংশ। তার ফলে নানা ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টির ভয়ে আল্লাহ্র রসূল এ প্রথাকে নিষিদ্ধ করেছেন।
\r\n
হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেছেন- “আল্লাহ্র রসূল ফরমিয়েছেন-যার জমি আছে সে নিজেই তা চাষাবাদ করবে বা, অন্যকে বিনালাভে সহানুভূতি প্রদর্শন করে চাষ করতে দেবে। অস্বীকারকারীর প্রতি হযরত (সঃ) অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিলেন”।
\r\n
হযরত জাবির (রাঃ) বলেছেন- “আল্লাহ্র রসূল (সঃ) জমির পরিবর্তে কোন কিছু গ্রহণ বা ইজারা দ্বারা উপকৃত হতে নিষেধ করেছেন”।
\r\n
হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) তাঁর জমিকে হযরত (সঃ)-এর আমল থেকে মু’আবিয়ার আমলের প্রথম ভাগ পর্যন্ত চাষীদের মধ্যে লগ্নিতে বন্দোবস্ত দিতেন, কিন্তু যখন তিনি রাফে (রাঃ)-এর হাদীস শুনতে পেলেন তখন তিনি এ কাজ ভয়ে ছেড়ে দিলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হল-সম্ভবত হযরত (সঃ) তাঁর শেষজীবনে এ সম্পর্কে এ মীমাংসায় উপনীত হয়েছেন।
\r\n
হযরত আবুযর গিফারী (রাঃ)-এর মত এই যে, ‘জমি নগদ লগ্নি বা ভাগে দেওয়া নাজায়েয এবং জমিদারি প্রথা কোন অবস্থায়ই জায়েয নয়”।
\r\n
হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন- ‘নবী করীম (সঃ)-এর নিষেধের অর্থ মুসলমান নিজে চাষাবাদ করবে অথবা একে অন্যের সৌহার্দ্য বা বন্ধুত্ত স্থাপনের উদ্দেশ্যে অন্যের প্রয়োজন অনুযায়ী অন্য ভাইকে বিনালাভে দেবে।
\r\n
শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভীও ইজারা দেওয়াকে বিশেষ গর্হিত কাজ বলে অভিহিত করেছেন।
\r\n
প্রশ্ন উঠতে পারে, যদি কোন ব্যক্তি অসুস্থতার দরুন অথবা কোন কার্য উপলক্ষে স্বয়ং উপস্থিত না থেকে চাষাবাদ করতে না পারে অথচ জমির উপস্বত্ব ব্যতীত তার বেঁচে থাকবারও অন্য কোন উপায় না থাকে-সেরূপ অবস্থায় জমির কি ব্যবস্থা করা হবে?
\r\n
ইসলামের মূলনীতি ভ্রাতৃত্ববোধের আলোকে তার মীমাংসা করতে হলে বলতে হবে, তার পাড়া-পড়শি অন্য ভাইরা তার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে কোন মুনাফা না নিয়েই তার জমি চাষ করে দেবে। যাতে কোন অবস্থায় মুনাফা স্বীকারের কোন সুযোগ ও সুবিধা না থাকে, ইসলামী সমাজে সে নীতিই গ্রহণ করা হয়েছে।
\r\n
উৎপাদনের পদ্ধতি
\r\n
আবার প্রশ্ন দাঁড়ায়-চাষী একাকী চাষ-আবাদ করবে না প্রয়োজনবোধে সমষ্টিগতভাবে২১৪ ফসল উৎপাদন করবে? এ সম্বন্ধে ইসলামী সমাজে দুটো পদ্ধতিই স্বীকৃত হয়েছে-
\r\n
এ প্রশ্ন মীমাংসার জন্য অংশীদারের স্বত্ব২১৫ এবং চুক্তিকৃত২১৬ স্বত্বের মধ্যে প্রভেদ বিশেষ লক্ষণীয়। কোন সম্পত্তিতে কারো স্বত্ব তখনই বর্তে, যখন সে সম্পত্তিতে অন্যের সঙ্গে কোন ব্যক্তির ন্যায্য অংশ থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোন ব্যক্তি সম্পত্তি রেখে পরলোকগমন করলে তার সম্পত্তিতে তার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সকলেরই অংশ স্বীকৃত হয়। অপরদিকে দশজন লোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাদের সম্পত্তি আরও বিশজনের মধ্যে ভাগ করে নিতে পারে বা সে সম্পত্তির সমান অংশে ভোগ করার জন্য চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারে।
\r\n
ইসলামের মূলনীতি দুনিয়ার সম্পদ রক্ষক২১৭ হিসেবে মানুষ ভোগ দখল করবে, এতে কোন মালিকানা থাকবে না। তাই উৎপাদন ব্যবস্থার অংশীদারি স্বত্ব যেমন থাকতে পারে চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার ফলেও স্বত্বের সৃষ্টি হতে পারে। চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ায় কিভাবে ভোগ-দখলের স্বত্বের সৃষ্টি হয় তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন রয়েছে ইসলামের ইতিহাসে। মদীনাতে হযরত (সঃ)-এর হিজরতের পরে আনসাররা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাদের খেজুর গাছগুলো ফল মুহাজিরদের সঙ্গে সমভাবে ভোগ করতে স্বীকৃত হন। তার ফলে উৎপন্ন খেজুর তাঁরা সমানভাবেই ভোগ করতেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, ‘(তারপরে) আনসাররা আল্লাহ্র রসূল (সঃ)-কে এসে বললেন- আমরা ও আমাদের ভাইগণের (মুহাজিরগণের) মধ্যে আপনি গাছগুলো ভাগ করে দিন’। তার উত্তরে আল্লাহ্র রসূল (সঃ) বলেন, ‘না আমরা যে উপস্বত্ব পাচ্ছি, তা-ই যথেষ্ট এবং তোমাদের সঙ্গে ফলের অংশ আমরা ভোগ করছি এই ভালো’। তাঁরা বলেন, ‘আমরা আপনার কথা শুনেছি- আদেশও প্রতিপালন করবো’।
\r\n
কাজেই চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে অন্যের সঙ্গে সম শরীকানা ভোগ করা ইসলাম অনুমোদন করে। বন্টনের নীতি ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত যে কোনোভাবেই উৎপাদন করুক না কেন, উৎপন্ন ফসল চাষীর নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত হলে তার কি ব্যবস্থা করা হবে- এ প্রশ্নটিও অত্যন্ত স্বাভাবিক। তার উত্তরে বলা যায়, তার বা তাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে অতিরিক্ত দ্রব্যে আত্মীয়-স্বজন, দীন-দুঃখীদের হক রয়েছে।
\r\n
কুরআন শরীফে রসূল (সঃ)-কে লক্ষ্য করে আল্লাহ্ বলেছেন, “তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে তারা (আল্লাহ্র পথে) কত (অংশ) ব্যয় করবে। তাদের বলো- তোমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা কিছু”।
\r\n
কেবল কুরআন শরীফেই নয়, হাদীসেও প্রয়োজনের অতিরিক্ত সবকিছু আল্লাহ্র পথে অর্থাৎ মানুষের কল্যাণের জন্য ব্যয় করা কর্তব্য বলে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইবনে হাজম জাহেরী তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ ‘মুহাল্লা’তে উল্লেখ করেছেন- হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, “আল্লাহ্র রসূল (সঃ) বলেছেন যে, যে ব্যক্তির কাছে শক্তি ও সামর্থ্যের সরঞ্জাম নিজেদের আবশ্যকের অতিরিক্ত রয়েছে, তাদের উচিত অতিরিক্ত সামান দীন-দুঃখীকে বিতরণ করা”। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেছেন- ‘নবী করীম (সঃ) এভাবে নানা প্রকারের উল্লেখ করেছেন, তাতে আমার এরূপ ধারণা জন্মেছে যে, আমাদের মধ্যে কারো কোন প্রকার মালের উপর দাবি থাকতে পারে না”।
\r\n
হযরত উমর ফারুক (রাঃ) বলেছেন- “যে-যে বিষয়ে আজ আমার ধারণা জন্মেছে সে সম্পর্কে যদি প্রথম থেকে অনুরূপ ধারণা জন্মাতো- তাহলে আমি কখনও দেরি করতাম না এবং নিঃসন্দেহে ধনীদের অতিরিক্ত ধন এনে গরিব মুহাজিরদের মধ্যে বিলিয়ে দিতাম”।
\r\n
হযরত আবু উবায়দা (রাঃ) ও তিনশত সাহাবা দ্বারা সত্য বলে গৃহীত বর্ণনা থেকে জানা যায়, কোন এক সময়ে যখন খাওয়া-পরার দ্রব্যাদির শেষ হওয়ার উপক্রম হয়, তখন হযরত রসূল করীম (সঃ) হুকুম দেন, ‘যার যা কিছু আছে,এনে উপস্থিত করো’। তারপর সমস্ত দ্রব্য এক জায়গায় জড়ো করে সকল কিছু তাদের মাঝে সমানভাবে বেঁটে সকলের জীবন ধারণের উপযুক্ত পরিমাণ বন্দোবস্ত করে দেন।
\r\n
হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন- “ আল্লাহ্ তা’আলা ধনীদের ওপর গরিবের আবশ্যকীয় জীবিকা সরবরাহ করা ফরয করেছেন। যদি তারা (গরিবেরা) ভুখা থাকে, নগ্ন থাকে অথবা জীবিকার জন্য বিপদগ্রস্ত হয় তাহলে ধনীরা দায়িত্বশীল নয় বলেই বুঝতে হবে এবং সংকীর্ণতার জন্য তাদের শাস্তি ভোগ করতে হবে। নানাবিধ হাদীস ও কুরআন শরীফের দলীল দ্বারা মুহাদ্দিস ইবনে হাজম এ বিষয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছেন- “প্রত্যেক মহল্লার ধনীদের ওপর গরিব-দুঃখীদের জীবিকার জন্য জামিন (দায়ী) হওয়া ফরয (অবশ্য কর্তব্য)। যদি বায়তুলমালের আমাদানি গরিবদের জীবিকা সরবরাহের জন্য যথেষ্ট না হয়, তাহলে (সময়ের) শাসক বা আমীর (সামন্ততন্ত্রীয় অর্থে নয়) ধনীদিগকে এ কাজের জন্য বাধ্য করতে পারেন। অর্থাৎ তাদের মাল বলপূর্বক গরিবদের প্রয়োজনে ব্যয় করতে পারেন। তাদের জীবিকার সংস্থানের জন্য কমপক্ষে অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য জরুরি আবশ্যক অনুযায়ী ক্ষুধার অন্ন, পরিধানের বস্ত্র এবং ঝড়, বৃষ্টি, গরম , রোদ ও প্লাবন থেকে রক্ষা করতে পারে এমন বাসগৃহ”। কাজেই সর্ববস্থায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপাদিত শস্য কোন চাষী ইসলামী সমাজে মুনাফার জন্য ব্যবহার করতে পারে না। উদ্ধৃত্ত সবকিছুই তাকে সমাজের কল্যাণের জন্য ব্যয় করতে হয়।
\r\n
ইসলামী সমাজের ভূমিনীতি
\r\n
উপরের আলোচনা থেকে ইসলামী সমাজের ভূমি-নীতির ছ’টি সূত্র পাওয়া যায়ঃ
\r\n
১.রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণেই ভূমির বিলি-ব্যবস্থা হবে। চাষীকে রাষ্ট্রের নিকট থেকে দানপত্র ভোগ-দখলের অধিকার হিসেবে অথবা রাষ্ট্রের অনুমতি নিয়ে অনুর্বর ভূমিকে আবাদের যোগ্য করে তাতে ভোগ-দখলের অধিকার পেতে হবে ।
\r\n
২. যারা নিজেরা চাষাবাদ করে না, তাদের ভূমির ওপর ভোগ দখলের অধিকার নেই। এক্ষেত্রে ‘লাঙ্গল যার মাটি তার’ নীতিই গ্রহণীয় হয়েছে।
\r\n
৩.রাষ্ট্রের বিবেচনায় কোনও কৃষকের জমি প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিবেচিত হলে রাষ্ট্রে অবাধে সেই জমিকে আয়ত্ত করে নিতে পারে।
\r\n
৪.জমি থেকে উপস্বত্ব ভোগ করার অধিকার চাষীর আছে, তবে শোষণের কোন সুযোগ নেই।
\r\n
৫. উৎপাদন ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবেও চলতে পারে।
\r\n
৬.প্রয়োজনের অতিরিক্ত ফসল চাষীকে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়েই অপর গরিব লোকদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে হবে, তাতে ত্রুটি দেখা দিলে রাষ্ট্র আইন প্রয়োগে২১৮ তা কার্যকরী করতে পারে।
\r\n
আধুনিক যুগে ইসলামী নীতির প্রয়োগ
\r\n
বর্তমানকালে শুধু হাতের দ্বারা মানুষ কোন কাজই করতে পারে না। শিল্প-বিপ্লবের পরে জীবনযাত্রার প্রত্যেক কাজকর্মেই যন্ত্রের প্রয়োগে সল্প পরিশ্রমে প্রচুরতম উৎপাদন করা যায়। যন্ত্রপাতি প্রয়োগের আর একটি বিশেষ সুবিধা এই যে, তাতে ব্যক্তিজীবনের সুখ-দুঃখ, আরাম-ব্যারামের ফলে উৎপাদন-ব্যবস্থায় কোন তারতম্য হয় না।
\r\n
উৎপাদন-ব্যবস্থায় যন্ত্রপাতি প্রয়োগ করতে গেলেই সংঘবদ্ধভাবে২১৯ উৎপাদন করতে হয়। কেননা, যন্ত্রপাতি প্রয়োগের জন্য বহু লোকের শ্রম ও তার বিভাগ দরকার। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে লাঙ্গল এক ব্যক্তি চালনা করতে সক্ষম। কিন্তু একটা ট্রাক্টর চালনা করতে হলে অনেক লোকের প্রয়োজন। লাঙ্গল দ্বারা জমি যে সময়ের মধ্যে এবং যেভাবে কর্ষিত হয় ট্রাক্টর দ্বারা তার কম সময়ে কর্ষিত হতে পারে। জমি ফসলের পক্ষেও উপযোগী হয় বেশি। এতে শ্রম ও সময় দু’ই ই বাঁচে।
\r\n
দ্বিতীয়ত, সেচের বা বাঁধের জন্য সবসময় যন্ত্রপাতির সাহায্য নেওয়া অবশ্য প্রয়োজনীয়। আমাদের দেশে বর্তমানে যেভাবে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সেচ অথবা বাঁধের কাজ চলে তাতে জমির পক্ষে উপযুক্ত সেচ অথবা বাঁধের ব্যবস্থা করা হয় না।
\r\n
কাজেই, এ যন্ত্রযুগে কৃষিকার্যের উন্নতির জন্য যে যন্ত্রের সাহায্য নিতেই হবে, যন্ত্রের সাহায্য নিতে গেলেই বহু লোকের সাহায্য ও সহযোগিতার দরকার। সুতরাং ব্যক্তিগতভবে উৎপাদন-ব্যবস্থার নীতি ত্যাগ করে সংঘবদ্ধভাবে উৎপাদন-ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে।
\r\n
তার জন্য সর্বপ্রথম দরকার সমস্ত জমিকে রাষ্ট্রের করায়ত্ত করে লোকসংখ্যার অনুপাতে জমি বিলির ব্যবস্থা করা। জমি বিলিতে যারা চাষী, চাষ-আবাদ করে জীবিকা নির্বাহ করা যাদের জীবনের কাম্য, তাদের মাঝেই জমি বেঁটে দেয়া দরকার। পতিত অনাবাদী ‘বনজর’ জমিকে চাষ-আবাদ করার উপযুক্ত করে তোলার জন্য উৎসাহ দান করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের পক্ষে খাজনা না দিয়ে এসব জমি পত্তন করা উচিত। বাঁধ, সেচ অথবা যন্ত্রপাতি ক্রয় করার জন্য অগ্রিম টাকা ধারে দেওয়া কর্তব্য। প্রত্যেকটি গ্রামকে কেন্দ্র করে যাতে সমবায়মূলক পদ্ধতিতে২২০ উৎপাদন চলতে থাকে, তার জন্য একটি সরকারি বিভাগ খোলা উচিত। সেই বিভাগের প্রধান কাজ হবে চাষীদের সংঘবদ্ধভাবে উৎপাদনের জন্য প্রস্তুত করা। তারা যাতে যন্ত্রপাতির সাহায্যে অল্প শ্রমে অধিক উৎপাদনে সমর্থ হয় তার জন্য সংগঠনের ব্যবস্থা করা। চাষের পক্ষে উপযুক্ত যন্ত্রপাতি সংগ্রহ পূর্বে প্রয়োজনবোধে গরু-মহিষাদি দ্বারা হাল চালনা দরকার হলে প্রত্যেক গ্রামের জন্য কতক জমি গোচারণভূমি রিজার্ভ রাখতে হবে। উৎপাদিত শস্য যাতে কোন অবস্থায়ই নষ্ট না হয় তার জন্য প্রত্যেক গ্রামেই সরকারি খরচে একটি গোলা গড়ে তোলা দরকার। অতিরিক্ত শস্যাদি যাতে চাষীদের মুনাফা শিকারের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে না পারে তার জন্য প্রত্যেক সংঘের ওপর কড়া দৃষ্টি রাখতে পারে এরূপ নৈতিক চরিত্র-বলে উন্নত সরকারি কর্মচারী নিয়োগ প্রয়োজন।
\r\n
সকলের উপরে প্রয়োজন মানুষের মন থেকে স্বার্থপরতা, নিচাশয়তা প্রভৃতি দূরীকরণের জন্য শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তন। রাষ্ট্রকে যাতে চাষী ভাইরা অপ্রয়োজনীয় মনে না করে, তার জন্য চাই রাষ্ট্রেরও তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার। আপদে-বিপদে রাষ্ট্র তাদের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে তাদের জীবনের সুখ-দুঃখের ভাগী হলে তবেই রাষ্ট্রের প্রতি তাদের দরদ ও সহানুভূতির সৃষ্টি হতে পারে।
\r\n
ইসলামী সমাজে ব্যক্তিস্বাধীনতার নীতি স্বীকার করে নিয়েও কিভাবে শোষণের পথ বন্ধ করা যায় তার ব্যবস্থা নবী করীম (সঃ) ও প্রথম দুই খলীফার জীবন ও কার্যাবলি থেকে বিশেষভাবে পাওয়া যায়। বর্তমানে যুগের পুঁজিবাদী ও বস্তুতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার মাঝখানে সিরাতুল মুস্তাকিম হল ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা। সেখানে সাম্য-মৈত্রী ও স্বাধীনতার সমন্ব্য করা হয়েছে বলে ব্যক্তি স্বাধীনতার মৌলিক অধিকার স্বীকার করেও শোষণের পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অনাগত বিশ্বসংস্থা গড়ে উঠবে মানবিক অধিকারের এই নীতিকে স্বীকার করেই। ইসলাম চৌদ্দশত বছর পূর্বেই এ নীতিগুলোকে স্বীকার করে গড়ে তুলেছিল তার রাষ্ট্র, প্রতিকূল পরিবেশে তা টিকে থাকেনি সত্য কিন্তু সেদিন দূরে নয়, যখন আবার এ মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েই জগৎসভ্যতাকে হতে হবে অগ্রসর।
\r\n
\r\n\r\n
নবম পরিচ্ছেদ
\r\n
ইসলামের বিকাশ
\r\n
\r\n
ইসলামকে ধারণা করা হয় পূর্ণ মানবতার ধর্ম বলে। মানবজীবনের সর্বাঙ্গিণ মঙ্গলের জন্য তার নানাবিধ সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করতে পারে বলেই ইসলামের সার্থকতা। ইসলামের ইতিহাসে কিন্তু দেখা যায়, যে পূর্ণ বিকশিত মানবজীবনের আদর্শ সম্মুখে রেখে ইসলাম উল্কার গতিতে অগ্রসর হয়েছিল, দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রাঃ)-এর খিলাফতের পরে তাতে প্রতিবিপ্লবের সূচনা দেখা দেয় এবং আমীর মুআবিয়ার হাতে ইসলামী রাষ্ট্র সম্পূর্ণ উল্টা দিকে চলতে শুরু করে। তার পরিণতিতে এখনও মুসলিম প্রধান দেশগুলোতে ইসলামের নামে চলছে অপব্যবহার। এখন তা হলে প্রশ্ন ওঠেঃ ইসলামের পক্ষে কি বিকাশের কোন সম্ভাবনা আছে? ইসলাম কি আবার সত্যিকার রূপ ফিরে পেতে পারে?
\r\n
এ সম্বন্ধে অনেকেই সন্দিহান। এঁরা বলেন, ইসলামী রাষ্ট্রের এরূপ পরিবর্তনের মূলে দুনিয়ার অর্থনৈতিক কারণগুলো কার্যকরী। সে উৎপাদন ব্যবস্থার মূলে দুনিয়ার সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো যুগে যুগে পরিবর্তিত হচ্ছে, ইসলামের মধ্যেও তার ছাপ পড়েছে। কাজেই, সামন্ততন্ত্রের যুগে ইসলামী রাষ্ট্রের যে রূপ ছিল, ধনতন্রের যুগে তার সে রূপ থাকেনি। সমাজতন্ত্রের যুগে আবার তার জন্য অন্য রূপ দেখা দিতে বাধ্য। ইসলামের নানাবিধ সমাধান থেকে নজির তুলে বলা হয়, ইসলাম মধ্যযুগে সে সমাধান দিতে সক্ষম হয়েছিল, বর্তমানে যুগে তাতে আর কৃতকার্য হতে পারবে না। কেননা সমাজতন্ত্রের যুগে ইসলাম যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল-বর্তমান কালের মত সেগুলো এত জটিল ছিল না। দুনিয়ার পুঁজিবাদের উত্থানের ফলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে সে সময় এরূপ পরিস্থিতি ছিল না বলে ইসলামের পক্ষে তা সম্ভব হয়েছে। এখনকার বিরূপ পরিস্থিতিতে তা সম্ভব নয়।
\r\n
প্রথমেই আমাদের বিচার করতে হবে- ইসলাম বলতে ওঁরা কি মনে করেন। ইসলাম একাধারে এক ধর্মবিশ্বাস, দার্শনিক মতবাদ, জীবন-পদ্ধতি। ইসলাম জীবনকে গ্রহণ করেছে পূর্ণভাবে। তাই মানবজীবনের নানাবিধ সমস্যার সমাধানে তৎপর হয়েছে। একথা অবশ্য সত্য যে, অর্থনৈতিক বা অন্যান্য কারণে দুনিয়ার পরিস্থিতি যুগে যুগে ভিন্ন রূপ ধারণ করে। তবুও বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্যে মানুষের সত্যিকার রূপের কোন পরিবর্তন হয়নি,হতে পারে না। মানুষ গোড়াতে ক্ষুধা-তৃষ্ণার তাড়নায় অধীর হত, বর্তমানেও হয়। মানুষের মধ্যে তখনও কাম-প্রবৃত্তি সহজ ছিল-বর্তমানেও রয়েছে। অপত্য-স্নেহ সুখচারী প্রবৃত্তি২২১ প্রভৃতি যেমন ছিল, বর্তমানেও রয়েছে। সেগুলোর পরিতৃপ্তিতে হয়ত পদ্ধতির পরিবর্তন হতে পারে কিন্তু তাদের সত্যিকার রূপের কোন পরিবর্তন হয়নি। মানুষের স্বভাবের যদি কোন পরিবর্তন না হয়, তাহলে তার বিকাশের উপায় ও পথের পরিবর্তন হলেও তাতে কিছু যায় আসে না।
\r\n
ইসলাম চায় মানবজীবনের সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক বিকাশ, সে বিকাশের পক্ষে অনুকূল পরিস্থিতিতে ইসলাম তার মূলনীতি পরিত্যাগ না করে যে কোন পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারে।
\r\n
ইসলামে এক আদর্শ রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনের জন্য তাকিদ রয়েছে। সে আদর্শ রাষ্ট্রের ভিত্তিপ্রস্তর হযরত রসূলে আকরম (সঃ) স্থাপন করেছিলেন। দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রাঃ)-এর খিলাফতের সময় সে রাষ্ট্র বিশেষ বিকাশ লাভ করে। আমীর মু’আবিয়ার কার্যকারিতার ফলে তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রাঃ)-এর খিলাফতের সময় প্রতিবিপ্লবের বীজ উপ্ত হয় এবং আমীর মু’আবিয়ার শাসনকালে তা সম্পূর্ণ উল্টা দিকে ধাবিত হয়। তাই ইসলামের রাষ্ট্রীয় আদর্শ সম্পূর্ণ রূপায়িত হতে পারেনি।
\r\n
প্রতিপক্ষ ইসলামী রাষ্ট্র বলতে বিভিন্ন কালের মুসলিম রাষ্ট্রকে মনে করে এক মস্ত বড় ভুল করে থাকেন। ইসলামের মূলনীতি আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব২২২ ও মানুষের প্রতিনিধিত্ব২২৩। এই দুই ভিত্তি ব্যতীত গঠিত কোন রাজ্য বা রাষ্ট্রকে ইসলামী রাষ্ট্র বলা যায় না। কাজেই ইসলামের নামে ব্যক্তিগত বা বংশগত আধিপত্যের যাঁরা প্রতিষ্ঠা করেছেন তাঁদের রাজ্যকে কিছুতেই ইসলামী রাষ্ট্র বলা যায় না। গ্রানাডার মুরদের, ভারতীয় মোগল বা উসমানী তুর্কিদের রাজ্যকে কিছুতেই ইসলামী বলা যায় না। তাদের রাজ্যগুলো ইসলামী রাষ্ট্র নয় বলেই বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে এ প্রভাব বাড়তে পারে না। কারণ ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনীতিকে কোন ছকের মধ্যে ফেলা যায় না। তাকে সামন্ততন্রীয়, ধনতন্ত্রীয় বা বস্তুবাদী সমাজতন্ত্রীয় বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। দুনিয়ার বুকে যেসব অর্থনৈতিক অসামঞ্জস্যের দরুন এসব মতবাদের সৃষ্টি হয়েছিল ইসলাম গোড়াতেই সে অর্থনীতিকে বর্জন করে এমন এক অর্থনৈতিক মতবাদ গ্রহণ করেছে,যার ফলে মানবসভ্যতাকে সামন্ততন্ত্র, ধনতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র নামক বিভিন্ন ধাপ ডিঙিয়ে অগ্রসর হতে হয় না। মানবজীবনের পূর্ণ বিকাশের পক্ষে অনুকূল অর্থনীতি গ্রহণ করার ফলে একই সূত্র ধরে সে অগ্রসর হতে পারে। ইসলাম যে আদর্শ রাষ্ট্র গঠনের নীতি নির্ধারণ করেছিল, তারই আলোকে বর্তমানে বা অদূর ভবিষ্যতে সে রাষ্ট্র রূপায়িত হওয়ার বিস্তর সম্ভাবনা করেছে। এ সম্বধে শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলভী বা মাওলানা উবায়েদ উল্লাহ সিন্ধির বক্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তাঁদের দুজনের কাছেই ইসলামী রাষ্ট্র একটি আদর্শ জীবনসংস্থা, যা এখনও সম্পূর্ণ রূপায়িত হয়নি, ভবিষ্যতে হতে বাধ্য।
\r\n
সে আশা আমরা পাই ইসলামের প্রতিকৃতির মধ্যে। সে প্রতিকৃতি সফল হতে বাধ্য। কারণ ইসলামের পরিস্থিতিতে তার বিকাশের পক্ষে অনুকূল পদ্ধতি গ্রহণ করার সুবিধা রয়েছে। সকলেই জানেন, ইসলামী আইন-কানুনের বুনিয়াদ চারটি স্তরের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ্র বাণী কুরআনের বাণীর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে যেসব কথা বলেছিলেন বা যেসব কাজ করেছিলেন পরবর্তীকালে তা-ই হাদীস হয়ে পড়ে। কুরআনের আদেশ-নিষেধ ব্যতীত হাদীসের আইন-কানুনগুলোও ইসলামপন্থীর পক্ষে অবশ্য পালনীয়। ইসলামী আইনের তৃতীয় স্তম্ভ ইজমা বা সর্বসাধারণ মুসলিম কর্তৃক গৃহীত আইন এবং চতুর্থ কিয়াস। এ চারটি উৎস থেকেই পরবর্তীকালে ফিকাহ শাস্ত্র গড়ে ওঠে। ইসলামের পতন যুগে যুক্তিকে অগ্রাহ্য করে এই চারটি উৎসের মধ্যেই আইন-কানুনকে সীমাবদ্ধ করা হয়। তবুও আনন্দের কথা এই যে, ইসলামের মধ্যেই রয়েছে বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগের তাকিদ। এই বিচার-বুদ্ধির আলোকে মুসলিম মানস সর্বাবস্থায় চিন্তা করার প্রয়াস পেয়েছে এবং নতুন পরিস্থিতিতে পুরাতন জীবনকে আবার নতুন জ্ঞানের আলোকে দেখবার জন্য সচেষ্ট হয়েছে। জাতিগত না হলেও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার মধ্যে মুসলিম মানসের সে পরিচয় রয়েছে ইতিহাসের পৃষ্ঠায়। হিজরী শতকের মধ্যভাগ থেকে চতুর্থ হিজরীর সূচনা পর্যন্ত মুসলিমদের মধ্যে উনিশটি আইন সংক্রান্ত মতবাদের সৃষ্টি হয়েছিল এবং তাদের প্রেরণার উৎস ছিল ইজতিহাদ।
\r\n
প্রশ্ন করেন, ‘যদি আল্লাহ্র রসূলের জীবন থেকে পূর্ববর্তী কোন উদাহরণ না পাও? তার উত্তরে মা’আজ বলেন, তাহলে আমি আমার বিচার-বুদ্ধির প্রয়োগ করবো’। তাঁর এ উত্তরে আল্লাহ্র রসূল (সঃ) বিশেষ সন্তোষ লাভ করেন।
\r\n
এ ইজতিহাদের জোরে ইসলামপন্থীরা নানা যুগে জীবন সমস্যার সমাধান করতে সমর্থ হয়েছে। চারটা সুন্নী মতবাদ, অসংখ্য শিয়া মতবাদের উৎপত্তি ও স্থায়িত্বের পরে মুসলিম-মানস যুগে যুগে জীবনকে আবার নতুন করে দেখবার চেষ্টা করেছে।
\r\n
এ জন্যেই বোধ হয় এ যুগের মনীষী জর্জ বার্নার্ড শ’র মত সূক্ষ্ম সমালোচক বলতে বাধ্য হয়েছেন- “ It is the only religion which appears to me to prosses assimilating capacity to the changing phase of existence which can make its appeal to every age. I believe if a man like Mohammad were to assume the dictatorship of the world, he would succeed in solving the problem in a way that would bring in much needed peace and happiness.”
\r\n
বুদ্ধির প্রয়োগের দ্বারা যদি যুগে যুগে পরিবর্তিত অবস্থার মধ্যে নানবিধ সমস্যার সমাধান করার সুবিধা ইসলামের মধ্যে থাকে, তাহলে মৌলিক নীতি পরিত্যাগ না করে এ পরিবর্তনের যুগেও উপায় ও পদ্ধতি গ্রহণের বেলায় ইসলাম ইজতিহাদের সাহায্য নিতে পারে। ইসলামের পক্ষে তাই কোন পরিস্থিতিতেই অবরুদ্ধ থাকার কোন কারণ নেই। প্রায় চৌদ্দ শত বছর আগে বছর ত্রিশেক বিকশিত হয়ে তার গতি রোধ হলেও বর্তমান পরিস্থিতিতে ইজতিহাদকৃত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বা রাজনৈতিক কাঠামো তৈরি তার পক্ষে খুবই সম্ভব-এইটেই সবচেয়ে বড় আশার কথা।
\r\n
\r\n\r\n
দশম পরিচ্ছেদ
\r\n
অনাগত বিশ্ব-সংস্থা ও ইসলাম
\r\n
\r\n
দুনিয়া আজ শতধা-বিচ্ছিন্ন। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, ব্যক্তিতে রাষ্ট্রে এবং রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে চলছে অবিরাম সংগ্রাম। এ সংগ্রাম আপাতত বিভিন্ন মানুষের জাতীয় সংগ্রাম বলে মনে হলেও আসলে তা মতবাদেরই সংগ্রাম-মানব জীবনকে বিভিন্ন সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার ফলে যে একদেশদর্শী মতবাদের সৃষ্টি হয়, তার ফলে ভিন্নমত পোষণকারী লোকদের মধ্যে শুরু হয় ভীষণ যুদ্ধ।
\r\n
আধুনিক কালে ধনতন্ত্র ও বস্তুবাদী সমাজতন্ত্রের সংঘর্ষে দুনিয়ার আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠেছে। ধনতন্ত্রের দার্শনিক ভিত্তি ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদে। তার গোড়ার কথা প্রত্যেক মানুষের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সমষ্টি থেকে তার পার্থক্য। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের মূলে রয়েছে ব্যষ্টির স্বার্থপরতার স্বীকৃতি। সমাজতন্ত্রের দার্শনিক ভিত্তি পরার্থপরতা। ধনতন্র স্বার্থপরতাকেই মানুষের আদি ও কৃত্রিম মনোবৃত্তি বলে মেনে নিয়েছে। সমাজতন্ত্র তার স্বার্থপরতাকে স্বাভাবিক প্রধান বৃত্তি বলে গ্রহণ করেছে। বর্তমান জগতের এ সংগ্রামের মূলে রয়েছে মানুষের এক বৃত্তির সঙ্গে অপর বৃত্তির সংগ্রাম। বিশ্লেষণ করলে স্পষ্টই বোঝা যায়, এই দ্বন্দ্বের মূলে (১) মানব জীবন সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা, (২) তারই অবশ্যম্ভাবী ফল ভুয়া অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যান্য দাবি, (৩) প্রকৃত মৌলিক অধিকারগুলোর মাঝে সমন্বয়ের ব্যর্থতা, (৪) জ্ঞানের রাজ্যে সামঞ্জস্যের অভাব।
\r\n
১. ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের সমাজের আদি-উপকরণরূপে ব্যষ্টির সত্তাকেই স্বীকার করে নেওয়া হয়ছে। মতের সামান্য ভিন্নতা সত্ত্বেও ইংরেজ দার্শনিক লক থেকে শুরু করে এ্যাডাম স্মিথ পর্যন্ত যে চিন্তাধারা পাওয়া যায়, তার সারসংক্ষেপ এই বলা যায়ঃ মানুষের চিন্তারাজ্যে চলেছে অণুর খেলা। একটা সংবেদন অন্য একটা সংবেদন২২৪ থেকে ভিন্ন। একটা ধারণা অপর ধারণা থেকে ভিন্ন। একটা অণু অন্য একটা অণু থেকে ভিন্ন। অনেকগুলো ধারণার কার্যকারিতার ফলে গড়ে ওঠে মনোজগৎ। আবার অনেকগুলো অণুর সমবায়ে সৃষ্টি হয় জড়জগৎ। তেমনি সমাজে বা রাষ্ট্রে চলেছে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বা প্রাধান্যের চেষ্টা। মানুষ সর্বদাই একক। সেই একক মানুষের সঙ্গে অন্যান্য মানুষের সংস্পর্শে গড়ে ওঠে তার সমাজ, জাতি বা রাষ্ট্র। মানুষের আদি সত্তায় রয়েছে অহংবোধ ও স্বার্থপরতা।
\r\n
তাই সেই আদি মানুষের চলাফেরা, ব্যবসা-বাণিজ্য, চিন্তাধারায় অবাধ স্বাধীনতা দিতে হবে। তার কাজ-কর্ম বা গতিবিধিতে যাতে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না হয়, তার প্রতি লক্ষ্য রেখেই রাষ্ট্র গড়ে উঠবে। ফরাসি দার্শনিক রুশো এ মতবাদের বিরোধিতা করলেও তাঁর মতবাদও ব্যষ্টিকেন্দ্রিক। শুধু পার্থক্য এই যে, লক প্রমুখ ইংরেজ দার্শনিক মানবমনের মননশীলতার ওপর জোর দিয়েছেন, রুশো গুরুত্ব আরোপ করেছেন তার প্রক্ষোভের ওপর। তিনি আক্ষেপের সঙ্গে বলেছেন, ‘মানুষ স্বাধীন হয়েই জন্মগ্রহণ করে; কিন্তু সে সর্বত্রই শিকলাবদ্ধ থাকে’। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের ওপর কোন আইন-কানুন চাপানো যায় না। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে নানা আইন মেনে চলতে হয় এবং তার ফলে তার জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। রুশো মানুষকে আবার তার স্বাভাবিক ধর্মে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আহ্বান করেছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল, প্রকৃতির কোলে স্বাভাবিক পরিবেশে মানুষের প্রক্ষোভ পূর্ণ বিকাশ লাভ করতে পারে। অপ্রাকৃত মানব-সৃষ্ট পরিবেশে তা হওয়া সম্ভব নয়। প্রকৃতিতে পশু, পাখি কারো কোন দুঃখ-দৈন্য নেই। তারা অবাধে বিহার করে। তাদের অভাবেরও কোন তাড়না নেই, কারণ অভাবের উৎপত্তি হলেই তারা নিবৃত্তির উপায়ও তার পক্ষে সহজলভ্য। মানুষ তার বুদ্ধির প্যাঁচে গড়ে তুলেছে তার সমাজ, তার রাষ্ট্র, নানবিধ আচার-অনুষ্ঠান। এতে মানবজীবনের পরিপূর্ণ স্ফূর্তি লাভ হয় না বলেই জীবনে দুঃখের হয় উৎপত্তি। তার ধারণা ছিল, প্রকৃতি থেকে বিকাশের ধারায় কোন এক সময়ে মানুষকে তার জন্মগত স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে হয়। তার আত্মরক্ষার জন্য অন্য মানুষের সঙ্গে মিলিত হয়ে সে গড়ে তোলে তার গোত্র, সম্প্রদায় ও রাষ্ট্র। রুশোর জীবনে তাই সর্বপ্রধান সমস্যা ছিল অন্যান্য লোকের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে রাষ্ট্র গঠন করেও ব্যষ্টি কিভাবে তার স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা বজায় রাখতে পারে তার উপায় উদ্ভাবন।
\r\n
মানুষের সত্যিকার স্বরূপ সম্বন্ধে এতে যে কল্পনা-প্রবণতা স্থান পেয়েছে তা সহজেই বুঝতে পারা যায়। ইতিহাসের ধারার আলোচনা করলেই দেখা যায় মানুষ কোনকালেই একক ছিল না। তার উৎপত্তি যেভাবেই হোক না কেন সে স্বভাবতই যূথচারী জীব। অন্যের সংশ্রব ও সংস্পর্শ ব্যতিরেকে সে এক মুহূর্তেও তিষ্ঠাতে পারে না। শরীরের মধ্যে যেমন বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের একত্র সমাবেশের ফলে শরীরযন্ত্র কার্যক্ষম থাকে, তেমনি বিভিন্ন মানুষের সমবায়মূলক কার্যকারিতায় গড়ে ওঠে মানুষের সমাজ, তার রাষ্ট্র। তলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারা যায়,মানুষের চিন্তাধারায় যুগ-যুগান্তর মননের রয়েছে স্পষ্ট ছাপ, বহু যুগের বিবর্তন। সে কোন সময়েই সম্পূর্ণ একা নয়।
\r\n
আপাতদৃষ্টিতে ষড়রিপু মানুষকে সমষ্টি-চেতনা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। কাম, ক্রোধ প্রভৃতি রিপু ব্যক্তিকে অন্য দশজন মানুষ থেকে পৃথক করে বলেই আমাদের ধারণা। বাস্তবিক পক্ষে তা নয়। কাম রিপু স্বভাবতই বহির্মুখী। একেবারে নিছক বিকল্প না হলে আপনার দেহেই কেউ মজে থাকতে পারে না। আত্মকাম সুস্থ মনের লক্ষণ নয়। কাম জাগৃতিক সময়২২৫ থেকেই বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গ কামনা মনের মাঝে স্ফুরিত হয়। সে ব্যক্তির সংশ্রবে যে তৃতীয় জীবের সৃষ্টি হয় তার উপর নারী, পুরুষ উভয়ের গরজ হয় কেন্দ্রীভূত।
\r\n
যে কোন রিপু নিয়েই আলোচনা চলুক না কেন, আমাদের বাধ্য হয়েই স্বীকার করতে হয়, নিছক আত্মকেন্দ্রিক ভোগসর্বস্ববাদ বলে দুনিয়ায় কিছু নেই। ব্যক্তি নিয়ে রওয়ানা দিলে তার পরিণতি সমষ্টিতে এসে থামতে হয়। কাজেই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ যেমন ধরে নেয়া হয়, ব্যক্তিমাত্রেই একক২২৬ বাস্তবিক পক্ষে দুনিয়ার বুকে তেমন কোন ইউনিট নেই।
\r\n
অপরদিকে বস্তুতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রে যেভাবে ইউনিট হিসেবে শ্রেণীগুলোকে নেয়া হয়েছে, তাও এক মহাভ্রান্তির ফল। বস্তুতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদের পিতা কার্ল মার্কস ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর শোষণের ভয়াবহ রূপ দেখে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মূল উচ্ছেদ করার জন্য তিনি তাকে পুঁজিবাদের উৎস বলে ধরে নিয়েছেন।
\r\n
বাস্তবিক পক্ষে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যবোধ শোষণের কোন কারণ হতে পারে না। দুনিয়ায় যাঁরা মনীষী, মননধর্মী, যাঁদের গবেষণার ফলে দুনিয়ার প্রগতি হয়েছে সম্ভবপর-তাঁরা সকলেই ছিলেন আত্মপ্রচারবাদী কিন্তু কেউই স্বার্থপর ছিলেন না। মননধর্মী মানুষমাত্রেরই স্রষ্টা হিসেবে বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে, কিন্তু তাই বলে তাঁরা স্বার্থপর নন।
\r\n
কাজেই বস্তুতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রবাদীরা যেভাবে মনে করেন ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যবোধ, স্বার্থপরতা এক ও অবিভাজ্য- তা কোন মতেই মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে টিকতে পারে না।
\r\n
স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতার মধ্যে কোন মৌলিক প্রভেদ নেই। তাদের সবসময়ই আপেক্ষিকতার সূত্রে বিচার করতে হয় । কোন ব্যক্তি যখন কেবল তার নিজের সুখ-সুবিধার জন্যই মরিয়া হয়ে পরিশ্রম করে, তখন তাকে বলা হয় স্বার্থপর। আবার সেই ব্যক্তিই যখন তার পরিবারের জন্য পরিশ্রম করে তখন তাকে বলা হয় পরার্থপর। তার ঐ পরার্থপরতা ও কওমের পরার্থপরতার তুলনায় স্বার্থপর ও সংকীর্ণ, যে স্বদেশ-প্রেমিক স্বজাতি ও স্বদেশের মঙ্গলের জন্য হাসিমুখে আত্মোৎসর্গ করে, তাকে বলা হয় নিঃস্বার্থ ব্যক্তি, কিন্তু বিশ্বপ্রেম ও বিশ্বমৈত্রীর তুলনায় তাও অকিঞ্চিৎকর।
\r\n
মানুষের জীবন এক ও অবিভাজ্য। মনে হয় স্বার্থপরতার সৃষ্টি সংস্কৃতি ও বৈদগ্ধের ফলে তারই হয় প্রসার। তখন আত্মকেন্দ্রিক সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ত্যাগ করে সে বৃহত্তর সত্তার মধ্যে তার আত্মার দোসর খুঁজে পায়। আমাদের সকল শিক্ষারই আসল লক্ষ্য মনের সম্প্রসারণ।
\r\n
২. সমাজে বা রাষ্ট্রে প্রাথমিক ইউনিট, না সমষ্টিই প্রাথমিক সংখ্যা- এ প্রশ্নের মীমাংসার পর রাষ্ট্রের স্বরূপ সম্পূর্ণ নির্ভর করে। ব্যষ্টির দাবি অগ্রগণ্য হলে দুনিয়ার সমস্ত অধিকার ব্যষ্টির হাতেই ছেড়ে দিতে হয়। অপরপক্ষে সমষ্টির দাবি প্রধান হলে ব্যষ্টির অধিকার বলে কিছুই থাকে না। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ব্যষ্টিকেই আদি সংখ্যা হিসেবে গণ্য করায় দুনিয়ার সম্পদের ওপর ব্যষ্টির অখন্ড অধিকার স্বীকার করে নিয়েছে। অপরদিকে সমাজতন্ত্রবাদে ব্যষ্টির কোন অস্তিত্বই স্বীকার করা হয় না। কাজেই সমাজতন্ত্রবাদের মতানুযায়ী রাষ্ট্র গঠিত হলে সেখানে ব্যষ্ট্রি স্বীকৃত অধিকার বলে কোন কিছু থাকে না। প্রকৃতপক্ষে ব্যষ্টি ব্যতীত সমষ্টি একটা সাধারণ ধারণা মাত্র, আবার সমষ্টি-জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যষ্টি-জীবন কল্পনাই করা যায় না। উভয়েই উভয়ের পরিপূরক ও পরিবর্ধক। আমরা পূর্বেই দেখেছি, ব্যক্তি-জীবনে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যে স্থান, সমষ্টি-জীবনে ব্যষ্টিরও সেই স্থান। কাজেই ব্যষ্টি বা সমষ্টির স্বার্থ পরস্পরবিরোধী নয়। অথচ দুনিয়ার ইতিহাসের পাতায় পাতায় রয়েছে ব্যষ্টি ও সমষ্টির দ্বন্দ্বের রক্তচিহ্ন।
\r\n
ব্যষ্টি ও সমষ্টির বিরুদ্ধ ও বৈরীভাবের পরেই বর্তমানে চলছে দুনিয়ার হত্যাকাণ্ড। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় স্বীকৃত হয়েছে ব্যষ্টির একমাত্র অধিকার, অপরপক্ষে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ব্যষ্টির অধিকার করা হয়েছে সম্পূর্ণ বিলোপ।
\r\n
ব্যষ্টি ও সমষ্টির এ ভুয়ো দ্বন্দ্বের তখনই নিরসন হতে পারে, যখন তাদের প্রকৃত স্বরূপের আলোকে তাদের অধিকারের ব্যবস্থা করা হয়। ব্যষ্টি ও সমষ্টির স্বার্থ যদি প্রকৃতপক্ষে পরস্পরবিরোধী না হয়, তাহলে তাদের এ মৌলিক পার্থক্য অস্বীকার করার সঙ্গে তাদের ভুয়ো অধিকার বিলোপ করাও প্রয়োজন।
\r\n
৩. ব্যষ্টি বা সমষ্টির অধিকার ভুয়ো হলে মানব জীবনে কতকগুলো মৌলিক অধিকার সর্বত্রই স্বীকৃত হয়েছে, যে সকল অধিকারের বলে মানুষ ব্যক্তিজীবনে বা সমাজজীবনে পূর্ণ বিকশিত হতে পারে তাদের মধ্যে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা সর্বপ্রধান। ফরাসী রাষ্ট্র-বিল্পবের পর থেকে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে মানুষের মৌলিক অধিকার বলে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। নিতান্ত দুঃখের বিষয়, আধুনিককালে দুনিয়ার বুকে এমন কোন রাষ্ট্র গঠন সম্ভব হয়নি, যাতে মানবজীবনের এই তিনটি মৌলিক অধিকারের সমন্বয় সাধন সম্ভবপর হয়েছে। কোথাও স্বাধীনতার নামে সাম্য ও মৈত্রিকে দেয়া হয়েছে বলিদান-কুরবানী, সাম্য ও মৈত্রীর জন্য স্বাধীনতাকে দেয়া হয়েছে বিসর্জন।
\r\n
একথা অবশ্য সত্য যে, রাষ্ট্র গঠিত হলে তার একটা নিজস্ব শক্তি সঞ্চিত হয় এবং তার নিজস্ব একটা অস্তিত্বের সৃষ্টি হয়। গনতন্ত্রমূলক রাষ্ট্রেও রাষ্ট্রের একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের অস্তিত্ব স্বীকার করে নেয়া হয়। সেখানে যে কোন ব্যক্তিকে যা’তা করতে দেবার অধিকার দেয়া হয় না। তার গতিবিধি কার্যকলাপ অনেক স্থলেই রাষ্ট্র কতৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। এমন যে অবাধ স্বাধীনতার মন্ত্র বা ‘একা থাকতে দাও’ নীতি সেখানেও ব্যষ্টিকে অবাধ উৎপাদন ও যদৃচ্ছ বণ্টনের স্বাধীনতা দেয়া আপাতত স্বীকৃত হলেও তার মধ্যে নানা শর্ত আরোপ করা হয়। পুঁজিবাদী দেশগুলোতেও রাষ্ট্রের পক্ষে অকল্যাণকর কোন দ্রব্য কোন ব্যক্তিকে বা প্রতিষ্ঠানকে উৎপাদন করবার স্বাধীনতা দেয়া হয় না।
\r\n
কাজেই সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতাকে আপক্ষিকভাবেই গ্রহণ করতে হবে। যেসব দেশে মানুষের জীবনের ক্ষেত্রে রয়েছে অপেক্ষাকৃত বেশী স্বাধীনতার সুযোগ সেগুলোকে বলতে হবে- স্বাধীনতার সুযোগদানকারী। আর যেসব রাষ্ট্রে জীবনযাত্রার প্রাথমিক চাহিদা পূরণের ব্যাপারে ইতর-ভদ্র ভেদাভেদ নেই, সেখানে সাম্যবাদ বা মৈত্রী ফলে উঠেছে বলেই ধরে নিতে হবে।
\r\n
বর্তমানকালে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোতে সাম্য ও মৈত্রী বলতে কিছুই নেই। অপরদিকে বস্তুতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রীয় রাষ্ট্রে স্বাধীনতাকে অত্যন্ত সংকুচিত করা হয়েছে। দুনিয়ার বুকে আব্র শান্তি ফিরিয়ে আনতে হলে এমন কোন সমাজ বা রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রবর্তনের দরকার যাতে সাম্য ও মৈত্রীর স্বাধীনতাও পাশাপাশি স্থান পায়।
\r\n
৪.মানব জীবনের জ্ঞানের ক্ষেত্রগুলোকে পৃথকীকরণের ফলে মানব সভ্যতার ইতিহাসে হয়েছে একটা বিকট দ্বন্দ্বের উৎপত্তি। মধ্যযুগে যাজক সম্প্রদায় সর্বসাধারন মানুষের ওপর অকথ্য নির্যাতন করতো বলে রাষ্ট্রকে চার্চ থেকে পৃথক করার নীতি গৃহীত হয়। সে নীতি এখনও দুনিয়ার বুকে চালু রয়েছে। ইতালির রেনেসাঁয় তার সূচনা হয়। জার্মানিতে রিফরমেশন সে চিন্তাধারা আরো বিকাশ লাভ করে এবং ফরাসি রাষ্ট্রবিপ্লবে তা’ পূর্ণ পরিণতি লাভ করে।
\r\n
এর ফলে যাজকের অন্তর্ধানে সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের প্রভাব থেকেও রাষ্ট্র মুক্তি পায়। মানব-মনের আদিম বৃত্তি ধর্মপ্রবণতা থেকে রাজনীতি বিচ্ছিন্ন হওয়ার রাজনৈতিক জীবনে নানাবিধ দুর্নীতি অবাধে প্রবেশ করে।
\r\n
প্রত্যেক ধর্মের মধ্যেই রয়েছে কতকগুলো নৈতিক আইন, যেগুলোর প্রয়োগ নির্ভর করে প্রয়োগকারীর ব্যক্তিগত চরিত্রের ওপর। সে উন্নত চরিত্রের লোক হঁলে সেই নৈতিক আইনগুলো সমাজ-জীবনকে উচ্ছৃঙ্খলতার পঙ্কিল প্রবাহ থেকে মুক্ত রাখে। অপরদিকে প্রয়োগকারী স্বয়ং দুষ্কৃতকারী হলে সমাজজীবনে চলে অন্যায় ও অবিচারের বন্যা।
\r\n
মধ্যযুগীয় যাজক সম্প্রদায় নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির বাসনায় উন্মত্ত হয়ে পড়লে রাষ্ট্রকে তাদের প্রভাব থেকে মুক্ত করার অদম্য উৎসাহে ধর্মের প্রভাব থেকেও রাজনীতিকে মুক্ত করার হয়েছে। তার ফলে ব্যক্তিগত জীবনে যেসব নীতি অবশ্য পালনীয় বলে সবাই একবাক্যে স্বীকার করে, রাজনীতিতে সে সব নীতি মোটেই গ্রহণীয় হয় না। অনেকেই রাজনীতিকে ধর্মের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করার উৎসাহে বলে থাকেন, “সীজারের যা প্রাপ্য সীজারকে দাও, খোদার প্রাপ্য খোদাকে দাও”। ভেবে দেখবার বিষয়-এভাবে মানব-মনকে কি দুটো কামরায় ভাগ করা যেতে পারে? যে ব্যক্তি সীজারের প্রাপ্য সীজারকে দিতে চাইবে, তার মনের নিভৃত কোণে কি এ প্রশ্ন জাগবে না? বাস্তবিকপক্ষে সীজারের প্রাপ্য কি আল্লাহ্কে বঞ্চিত করার ওপরই নির্ভর করে? কেবল রাষ্ট্র-জীবনকে ধর্ম-জীবন থেকে পৃথক করার ফলেই দুনিয়ার অশান্তির আগুন জ্বলে ওঠে না। জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত না হলেও তাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বে মানব-জীবন নানা অশান্তির সৃষ্টি হয়। ধর্মজতৎ, কর্মজগৎ, মনোজগৎ, বাইরের জগৎ, অন্তরের জগৎ- যে কোন জগতেই হোক না কেন সকল জগতে একই জীবন, একই মন থাকে ক্রিয়াশীল। জ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে যোগসূত্র ও সামঞ্জস্যের সৃষ্টি না হলেও তাতে নানা সংঘর্ষ বাধে। তার ফলে ব্যক্তিজীবনে বা সমাজজীবনের ভারসাম্য হয় নষ্ট।
\r\n
জ্ঞানের রাজ্যে সামঞ্জস্যের সৃষ্টি করতে হলে জ্ঞানের সবগুলো সিদ্ধান্তের মধ্যে সংহতি সৃষ্টি হওয়া দরকার। সেই সংহতির আলোকে জীবনের নানাবিধ সমস্যার সমাধান হলে তবেই মানবজীবনে শান্তি ও স্বস্তি ফিরে আসতে পারে।
\r\n
কোন ব্যক্তির জীবনে পরস্পরবিরোধী ভাবধারা বর্তমান থাকলে বুঝতে হবে, তার জীবনে রয়েছে সংহতির অভাব। সেরূপ সমাজজীবনে নানাবিধ বিরোধী ভাবের সৃষ্টি হলেও সেই জীবনে জ্ঞানের মধ্যে সামঞ্জস্যের সৃষ্টি হয় নাই বলে স্বীকার করতে হবে।
\r\n
তাই মানবজীবনে শান্তি ফিরিয়ে আনতে হলে মানবজীবনকে গভীরভাবে পাঠ করতে হবে সর্বপ্রথমে। খোলা মন নিয়ে তার জীবনের প্রতিটি দিককে তলিয়ে দেখতে হবে।
\r\n
এ ব্যাপারে অবরোহ পদ্ধতিতে আমাদের অগ্রসর হতে হবে। মানবজীবন সম্বন্ধে কোন এক স্বতঃসিদ্ধকে ধ্রুব সত্য বলে প্রথমে ধরে নিয়ে আরোহ পদ্ধতিতে কোন সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছলে পূর্বতন ভুলেরই পুনরাবৃত্তি হবে।
\r\n
মানবজীবনের ছোটখাটো তুচ্ছ অভিজ্ঞতা ও উপকরণকে স্বীকার করে তারই ভিত্তিতে সঠিক সত্যে উপনীত হওয়াই জ্ঞানের চরম লক্ষ্য। মানবজীবনের বিভিন্ন জ্ঞানের ক্ষেত্রে এভাবে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত এসে পৌঁছে, সেগুলোর মধ্যে সংহতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে যেসব নীতি বা সত্তাকে স্বীকার করে প্রয়োজন তাকে কার্যকরী সিদ্ধান্ত হিসেবে ধরে নিয়ে হতে হবে অগ্রসর। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বর্তমানকালের পদার্থবিদ্যার সিদ্ধান্ত অনিশ্চয়তাবাদের সঙ্গে জীববিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের সামঞ্জস্য বিধান করতে গেলে কী পাওয়া যায়? অনিশ্চয়তাবাদের পরমাণুর মধ্যে এক সাশ্রয়ী লীলাই আবিষ্কৃত হয়েছে, অপরদিকে জীববিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত অনুসারে শক্তিমানের উদ্বর্তন ও জীবনযুদ্ধের সূত্র ধরেই জীবন চলছে তার বিকাশের পথে। এ দুটো মতবাদকে সুসমঞ্জস করে তুলতে হলে আমাদের ধরে নিতে হবে-বিশ্বের আদিতে রয়েছে এক সাশ্রয়ী শক্তির স্থিতি-সেই শক্তিই জড় পদার্থরূপে, জীবনরূপে ক্রমবিকাশের ধারায় নানাবিধ মান সৃষ্টি করে চলছে।
\r\n
তার সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের বা সমাজবিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলো যুক্ত করলে সেই পূর্বেকার সার্বিক সিদ্ধান্তকে আরও ব্যাপক আকারে পরিবর্ধিত করতে গেলে এবং তাদের নিদ্দগিএ সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করলে, সে সিদ্ধান্তের আরও পরিবর্তন বা পরিবর্ধনের প্রয়োজন হতে পারে।
\r\n
মোটামুটি আমাদের জীবনের প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতাকে স্বীকার করে তার ব্যাখ্যার জন্য এমন একটি সার্বিক সত্যে এসে পৌঁছা দরকার, যাতে জীবনের সকল দিকের প্রতি সুবিচার করা হয় এবং জীবনের বিভিন্ন জ্ঞানের ক্ষেত্রে হয় সামঞ্জস্য সাধন।
\r\n
ইসলামে মানবজীবনকে সূক্ষ্মভাবে অধ্যয়ন করার জন্য রয়েছে বিশেষ তাগিদ। দ্বিতীয়ত যে দ্বন্দ্বে আজকের দিনের দুনিয়া রক্তকলুষিত সে দ্বন্দ্বের নিরসনের উপায় উদ্ভাবনেরও চেষ্টা ইসলাম করেছে। জ্ঞানের রাজ্যে কৃত্রিম ভেদরেখা তুলে নিয়ে একই সূত্রে জীবনের সকল ক্ষেত্রের করা হয়েছে ব্যাখ্যা এবং মানবীয় বিভিন্ন অধিকারের করা হয়েছে সমন্বয় সাধন। ইসলাম গোড়াতেই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে স্বার্থপরতার যোগ স্বীকার করেনি, ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যকে ইসলাম সবসময়েই তার বিকাশের হেতু বলে ধরে নিয়েছে। সেই ব্যক্তিত্ব বিকাশের অর্থ এ নয় যে, অপরকে শোষণ করে সে তার উদর পূর্তি করবে। তার পরিস্কার অর্থ এই- জীবনের সবগুলো বৃত্তির পরিপূর্ণ বিকাশের পর তাদের আসল কর্তব্যে নিয়োগ করা। ইসলামী পরিভাষায় খুদীর অর্থ কোন কালের স্বার্থপরতা নয়। মরহুম আল্লামা ইকবাল যে খুদীর বিকাশের জন্য মানবতাকে আহ্বান করেছিলেন, তা স্বার্থপরতা তো নয়ই-বরং তার উল্টো বৃত্তি। সে খুদী বিকশিত হলে মানুষ আর মানুষ থাকে না, সে হয় ইনসান-ই-কামিল। তখন সে অপরকে শোষণ করতে চায় না বরং আপনারই মত বিকাশের পথে টেনে নেয়। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের যে সূত্রপাত লক থেকে হয়েছিল, তারই পূর্ণ পরিণতিতে পাওয়া যায় নীটশের অতিমানবকে। সে অতি-মানবকে অতিদানবও বলা যায়। কারণ তার মাঝে মানবীয় গুণের দেয়ে দানবীয় গুণেরই প্রাধান্য বেশি। ইনসান-ই-কামিলের মাঝে মানব-জীবনের সবগুলো বৃত্তির সুষ্ঠু বিকাশই তার সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়। রাজনৈতিক জীবনে সে যেমন আপনার স্বার্থের জন্য নয় তৎপর, তেমনি আপনার সঙ্গে অপরের অচ্ছেদ্য যোগসূত্র স্বীকার করে বলে আপনার ও সমাজের স্বার্থে কোন তারতম্য দেখতে পায় না।
\r\n
যে অধিকার নিয়ে ব্যষ্টি ও সমষ্টিতে চলছে অবিরাম সংগ্রাম, ব্যষ্টি ও সমষ্টির এরূপ পরস্পরবিরোধী পার্থক্য স্বীকার না করার ফলে ইসলামের মধ্যে এ সমস্যা এমন উগ্ররুপ ধারণ করেনি। ব্যষ্টি ও সমষ্টিকে একই ইউনিট হিসেবে ধরে নেয়ার জন্য তাদের তথাকথিত অধিকার লোপ করা হয়েছে। আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব স্বীকার করার ফলে ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনের দ্বন্দ্বের হয়েছে নিরসন।
\r\n
অপরদিকে দুনিয়ার মালিকানা ও সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ্র –স্বীকার করে নিয়েও মানবজীবনে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার সমন্বয় সাধনের জন্য ইসলাম দিয়েছে পূর্ণ সুযোগ-ইসলামী জীবন দর্শনের মূল কথাঃ এ বিশ্বের আদি কারণ সব মঙ্গলময় পরম শক্তিশালী আল্লাহ্তা’আলা তাঁর সত্তা থেকে বিশ্বের সবকিছুর উৎপত্তি এবং তাঁর মাঝেই সবকিছুর লয়, মানবজাতির উৎপত্তিও তার থেকেই হওয়ায় তারা পরস্পর ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ। পবিত্র কুরআন শরীফে বলা হয়েছে এবং পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে-প্রকৃতপক্ষে তোমাদের এ ভ্রাতৃত্ব এক (অবিভাজ্য) এবং আমি তোমাদের প্রভু (আল-মুমিন ২৩-৩-৫২-৫৩)। আরও বলা হয়েছেঃ নিশ্চয়ই মানুষের ভ্রাতৃত্ব- একই ভ্রাতৃত্ব। (আম্বিয়া ২১-৬-৯২) কাজেই ইসলাম সর্বাবস্থায় সাম্য ও মৈত্রীর রুপায়নে মানুষকে উদ্ধুদ্ধ করে। মানুষের মাঝে সাম্য ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠা হওয়া সত্ত্বেও যাতে তাদের মধ্যে কাজে-কর্মে বা উৎপাদন ব্যবস্থায় আপেক্ষিক স্বাধীনতা বজায় থাকে তার জন্য ইসলাম কোন অবস্থায়ই কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেনি। ব্যক্তিগত বা সমাজগৎ জীবনে যাতে মানুষ স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পারে বা উৎপাদন ব্যবস্থায় স্বীয় অভিমত অনুসারে চলতে পারে, তার জন্য ইসলামী সমাজে রয়েছে প্রচুর সুযোগ। ব্যষ্টি ইচ্ছা করলেই যেমন একা উৎপাদন করতে পারে, তেমনি সংঘবদ্ধভাবে অপর দশজনের সঙ্গে মিলিত হয়েও সে উৎপাদন করতে পারে। ইসলামের মধ্যে এ সুযোগ থাকার দরুন মানব জীবনের বিকাশের পথের এক মস্ত বড় সুযোগ স্বাধীনতা ভোগ করার রয়েছে প্রচুর সম্ভাবনা।
\r\n
জ্ঞানের রাজ্যে প্রয়োগ, যুক্তি ও স্বজ্ঞা, প্রত্যেক পন্থাকেই স্বীকার করে নেওয়ায় জগতের জ্ঞানের রাজ্যে ইসলাম কোন ভেদরেখা টেনে দেয়নি। যে কোন উপায়েই জ্ঞান লাভ হতে পারে এবং বিভিন্ন পদ্ধতিতে লব্ধ জ্ঞানরাজিকে সুসংবদ্ধ করা যায়, ইসলাম তা গোড়াতেই স্বীকার করে নিয়েছে। তার ফলে প্রায়োগিক, যুক্তিসর্বস্ব ও সজ্ঞালব্ধ জ্ঞানের ভিত্তির ওপর নির্ভর করে সার্বিক সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছার পক্ষে রয়েছে সুবিধা।
\r\n
বর্তমান জগতে যেমন ক্ষেত্রগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে তাদের মধ্যে পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্তে পৌঁছার রয়েছে সুযোগ, ইসলাম মানব-মনকে এভাবে বিভক্ত করেনি বলে তার পক্ষে জ্ঞানের ক্ষেত্রে নৈরাজ্যের উৎপত্তি হয়নি।
\r\n
বাস্তবিক পক্ষে ইহলোকিক, পারলৌকিক, রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয়, বৈজ্ঞানিক বা নৈতিক-ইত্যাদিরূপ ভেদরেখা সৃষ্টির মূলে রয়েছে আমাদের জ্ঞানের ক্ষেত্রে কাল্পনিক বিভাগ। মানব মন সর্বদাই এক ও অবিভাজ্য। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের মাধ্যমে কোন সত্যে উপনীত হলে তাতে যদি কোন ত্রুটি ধরা পড়ে, তা হলে আমরা অনতিবিলম্বে তাকে শুধরে নেই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় সূর্য পূর্বদিকে ওঠে-এ অভিজ্ঞতা আমাদের নিত্যকার ব্যাপার। কিন্তু যখন এ অভিজ্ঞতাকে আমরা যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করি, তখন তাকে সংশোধিত আকারে গ্রহণ করতে হয়। বলতে হয় আমরা দেখি বটে সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে তবে প্রকৃতপক্ষে সূর্য ওঠে না। পৃথিবীর আবর্তনের ফলেই আমাদের এ ভ্রান্তি হয়।
\r\n
যুক্তি ও লব্ধজ্ঞানেরও সংশোধন করা অনেক সময় প্রয়োজন হয়ে পড়ে। জগতে যা কিছু আমরা দেখতে পাই তাতে দেখি পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। এক বিরাট পরিবর্তন চলছে দুনিয়ার বুকে। আজ যে শিশু,কাল সে যুবা। আবার দু’দিন যেতে না যেতে সে বৃদ্ধ হয়ে কবরের পথে অগ্রসর হয়। কাজেই মানবজীব অসার, অনিত্য। আজ আমি বেঁচে আছি, কাল হয়ত থাকবো না। কাল কেন, হয়ত পরমুহূর্তেই থাকবো না। আমার পক্ষে তা হলে কোন কিছু করার কি অর্থ থাকতে পারে? খাওয়া-পরা, ভোগ-বিলাস, আয়াস-আরাম সবকিছুই অনিত্ব ও অসার। তাই- হয় নিস্ক্রিয়, নিরস থেকে তিলে তিলে মরে যাওয়াই ভাল। না হয় যা খুশি তাই করে দু’দিনের এ ভবখেলা সাঙ্গ করে যাওয়াই ভালো। যুক্তিধারার এ প্রবল স্রোতে কিন্তু মানুষ ভেসে যেতে চায় না। কারণ এভাবে চিন্তা করলে মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না। তার বেঁচে থাকার ইচ্ছা তাকে এ সংকটজনক পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করেছে, সে তাকে অভয় দিচ্ছে- তোমাকে বাঁচতেই হবে। জীবনযুদ্ধে তোমাকে বুঝতেই হবে। তার জীবনধর্মই তাকে কর্মের পথে, প্রেরণার পথে এগিয়ে দিচ্ছে। এ জ্ঞান সে যুক্তি থেকে পাচ্ছে না, পাচ্ছে সহজাত জ্ঞান থেকে।
\r\n
ধর্মজগতে বা নৈতিক-জগতে স্বজ্ঞাজাত জ্ঞান সবসময়ই মানুষের হয়ে থাকে। সেজন্য যুক্তি-জ্ঞানকে ধর্মীয় ও নৈতিক জ্ঞান দ্বারা পরিশোধিত করে তোলা দরকার। সেই পরিশোধনের ফলে যে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির সৃষ্টি হয়, সে জ্ঞানই মানব জীবনের চরম ও পরম জ্ঞান।
\r\n
ইসলাম গোড়াতেই ইহলৌকিক, পারলৌকিক, ধর্মীয় বা রাষ্ট্রীয় বলে জ্ঞানের কোন পৃথক জগৎ স্বীকার করেনি। সমগ্র জীবন দিয়ে সত্য লাভের চেষ্টা ইসলামের কাম্য। ইসলাম মানবজীবনকে পূর্ণ বিকাশের পথে এগিয়ে দিতে চায় বলে জ্ঞানের প্রত্যেকটি পদ্ধতি স্বীকার করে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে জীবন সমস্যার সমাধান করতে চায়, তার ফলে ধর্ম-জীবনের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় জীবনের, কর্ম জীবনের সঙ্গে নৈতিক জীবনের দ্বন্দ্বের হয় অবসান।
\r\n
বিভিন্ন জ্ঞানের উপকরণকে সমন্বয় করে ইসলাম এসে উপনীত হয় এক সার্বিক সিদ্ধান্তে- যেখানে মানব মনের সবগুলো দাবি সন্তোষ লাভে হয় সমর্থ। বর্তমান কালে ধর্ম ও রাষ্ট্রের যে দ্বন্দ্ব তার মূলে রয়েছে আমাদের একদেশদর্শী জ্ঞানের কার্যকারিতা। যুক্তিসর্বস্ব জ্ঞানের আলোকে আমরা গড়ে তুলি রাষ্ট্র। তাতে কোথাও ব্যষ্টির, আবার কোথাও সমষ্টির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করি। ধর্ম-জীবনকে রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে পৃথক করে দেখি বলে রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয়জীবনে শুরু হয় ভীষণ দ্বন্দ্ব। ধর্মজীবনে যা ন্যায়-নীতি বলে সর্বত্র স্বীকৃত হয় রাষ্ট্রজীবনে তা অনেক স্থলেই উপহাসের বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। তার প্রধান কারণ, আমরা একই সত্যকে কোথাও দেখি বিশুদ্ধ জ্ঞানের আলোকে, আবার কোথাও দেখি স্বজ্ঞার মাধ্যমে। সামগ্রিক দৃষ্টি নিয়ে একে বুঝবার চেষ্টা করলে একই সত্যের দুটো রূপ বলে ধরা পড়বে। রাষ্ট্রজীবনে জীবনকে দেখা হয় শুধু বুদ্ধির আলোকে। সে জন্য এখানে ধর্মীয় ও নৈতিক মানগুলো কোন স্থান পায় না। ধর্মীয় ও নৈতিক জীবনের মানগুলো স্বজ্ঞার মাধ্যমেই পাওয়া যায়। বুদ্ধির সঙ্গেই বোধির যোগ হলে তবেই সত্যের সমগ্র রূপ ধরা পড়ে। সেই যোগসূত্র স্থাপনের জন্য রয়েছে তাগিদ। সে জন্যই ইসলাম রাজনীতিকে ধর্মনীতি থেকে পৃথক করে কোন কালেও দেখেনি। কেবল ধর্ম ও রাজনীতি নয় আধ্যাত্মিক বা জাগতিক বলে ইসলামের কোন বিভাগ নেই। আল্লামা ইকবাল সত্যিই বলেছেন- “ ইসলামে আধ্যাত্মিক ও জাগতিক বলে দুটো ভিন্ন ক্ষেত্র নেই। যতই জাগতিক (উদ্দেশ্য প্রণোদিত) হোক না কেন, কর্তার মনের ভাবধারার আলোকেই কর্মের নির্ধারণ হয়ে থাকে। ইসলামে একই সত্যকে এক দৃষ্টিভঙ্গিতে চার্চ বলা হয়, অন্য দৃষ্টিভঙ্গিতে বলা হয় রাষ্ট্র। চার্চ ও রাষ্ট্রকে একটি বস্তুর দুটো দিক বললে ঠিক বলা হবে না। ইসলাম বিশ্লেষণের অতীত এক সত্য। আমাদের দৃষ্টিকোণের পরিবর্তনের ফলে তাকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখায়। এই ভুলের কারণস্বরূপ বলা যেতে পারে, ঐক্যকে দ্বিখণ্ডিত করে দুটো ভিন্ন সত্যের সৃষ্টির ফলেই এর উৎপত্তি। আসল সত্য হল জড় পদার্থ, স্থান-কালের সম্বন্ধে আত্মা বৈ কার কিছু নয়”।
\r\n
কাজেই সব দেখে শুনে মনে হয়, অনাগত বিশ্ব সংস্থার জন্য যে কয়টি মৌলিক নীতির স্বীকৃতির প্রয়োজন এবং যে মানসিকতার অত্যন্ত প্রয়োজন- ইসলামের মধ্যে তার সমস্ত রয়েছে। তাই এ ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ দুনিয়ার বুকে আবার শান্তি ফিরিয়ে আনতে হলে মানব-সভ্যতাকে ইসলামের নীতি গ্রহণ করতে হবে।
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n\r\n
ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ
\r\n
প্রথম পরিচ্ছদে
\r\n\r\n
- \r\n
- প্রজাতির উৎপত্তি Origin of species
- \r\n
- মানুষের উৎপত্তি Descent of man
- \r\n
- লিনেয়াস Lenneus
- \r\n
- প্রজাতি Species
- \r\n
- ব্যতিক্রম Variation
- \r\n
- প্রকৃতির মনোনয়ন Natural selection
- \r\n
- আকস্মিক প্রকারণ Accidental variations
- \r\n
- সহজাত প্রবৃত্তি Instincts
- \r\n
- অভিযোজন Adaptation
- \r\n
- সংবেদনশীল Sensitive
- \r\n
- বুশম্যান Bushman
- \r\n
- উইজম্যান Weisman
- \r\n
- জননকোষ Germ cell
- \r\n
- লেমার্ক Lamarck
- \r\n
- লব্ধগুণ Acquired characteristic
- \r\n
- প্রজাতি Species
- \r\n
- উপাদান Elements
- \r\n
- প্রাকৃতিক নির্বাচন Natural selection
- \r\n
- জাতি Kind
- \r\n
\r\n
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
\r\n\r\n
- \r\n
- কামসর্বস্ববাদ Pan-sexualism
- \r\n
- কার্ল জুঙ Carl jung
- \r\n
- এডলার Adler
- \r\n
- প্রক্ষোভ Emotion
- \r\n
- উদ্বায়ুজ লক্ষণ Neuric symptom
- \r\n
- প্রহরী Censor
- \r\n
- আপতিক Accidental
- \r\n
- অবদমিত বাসনা Repressed desire
- \r\n
- লিবিডো Libido
- \r\n
- আত্মকামী Narcissist
- \r\n
- অস্ফুট চিত্ততার কাল Lateny period
- \r\n
- বৈকল্য Perverse
- \r\n
- স্থিতাবস্থা Fixation
- \r\n
- প্রতিসরণ Regression
- \r\n
\r\n
(ক) ধ্বজচ্ছেদ কূটেশা Castration complex
\r\n\r\n
- \r\n
- ধর্ষকাম Sadism
- \r\n
- মর্ষকাম Masochism
- \r\n
- উপস্থ ঈর্ষা Penis envy
- \r\n
- দ্বিমেরুত্ব Polarity
- \r\n
- উদগতি Sublimation
- \r\n
- আত্মপ্রকাশ Self- assertion
- \r\n
- লিবিডো Libido
- \r\n
- বিষয়কেন্দ্রিক Objective
- \r\n
- উদ্বায়ু Psychosis
- \r\n
- স্থায়ী অবস্থা Fixed state
- \r\n
- প্রহরী Censor
- \r\n
\r\n
তৃতীয় পরিচ্ছেদ
\r\n\r\n
- \r\n
- ভূমিদাস Serf
- \r\n
- ম্যাকিয়াভেলি Machiavelli
- \r\n
- লক Locke
- \r\n
- এ্যাডাম স্মিথ Adam smith
- \r\n
- অহংবোধ Egoism
- \r\n
- স্বার্থপরতা Selfishness
- \r\n
- সামাজিক চুক্তিবাদ Social cantract theory
- \r\n
- সার্বভৌমত্ব Sovereignty
- \r\n
- রাষ্ট্র State
- \r\n
- শক্তি Power
- \r\n
- পরার্থপর Altruistic
- \r\n
- অহংবোধ Egoism
- \r\n
- ব্যষ্টির স্বাতন্ত্র্য Individualism
- \r\n
- ব্যক্তিকে একা থাকতে দাও Laissez Faire-Let alone
- \r\n
\r\n
চতুর্থ পরিচ্ছেদ
\r\n\r\n
- \r\n
- যূথচারী Gregarious animal
- \r\n
- মত দলীয় Group
- \r\n
- অনুগৃহীত Chosen
- \r\n
- সংঘ চেতনা Collective consciousness
- \r\n
- রিপাবলিক Republic
- \r\n
- আদর্শ সুখরাজ্যে Uthopia
- \r\n
- স্বতঃসিদ্ধ Postulate
- \r\n
- চরম নাস্তিবাদ Absoulute Nihilism
- \r\n
- অস্তিত্ব Being
- \r\n
- অন-অস্তিত্ব Non-being
- \r\n
- সূচনা Starting point
- \r\n
- অন্ব্য় Thesis
- \r\n
- মাধ্যম Category
- \r\n
- অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ Apriori
- \r\n
- অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ Empirical aposteriori
- \r\n
- গুহামানব Cave man
- \r\n
- পশুচারী Pastoral
- \r\n
- প্রস্তর যুগ Neolithic age
- \r\n
- অধিকার Right
- \r\n
- প্রয়োজন অনুসারে সমস্তই পাবে To each according to his capacity and to each according to his needs
- \r\n
- উদারনৈতিক মতবাদ Liberalism
- \r\n
- ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ Individualism
- \r\n
- বৃত্তিগত শ্রেণী বৈষম্য Professional class distinction
- \r\n
- সন্ধিক্ষণ Transition period
- \r\n
- অর্থনৈতিক নিশ্চয়তাবাদ Economic determinism
- \r\n
- দুনিয়ার মজদুর সব একত্র হও Working men of all countries unite
- \r\n
- সম্মতি Acquiescence
- \r\n
- ব্যষ্টি চৈতন্য Egoism
- \r\n
- নির্বিত্তের নেতৃত্ব Dictatorship of the Proletariate
- \r\n
- জাগতিক আশাবাদ Cosmic optimism
- \r\n
- আত্মপ্রচারবাদী Self-assertive
- \r\n
- স্রষ্টা Creator
- \r\n
\r\n
পঞ্চম পরিচ্ছেদ
\r\n\r\n
- \r\n
- আরোহ Inductive
- \r\n
- মূল লক্ষ্য বিশেষ The particular good
- \r\n
- সার্বিক Universal
- \r\n
- অবরোহ পদ্ধতি Deductive method
- \r\n
- জীবজগতের যুদ্ধ Struggle for existence
- \r\n
- স্ববোধ Egoism
- \r\n
- পরার্থপরতা Altruism
- \r\n
- মনন-ক্ষমতা Power of intellection
- \r\n
- প্রক্ষোভ Emotion
- \r\n
- ইচ্ছাশক্তি Will
- \r\n
- বোধি Instution
- \r\n
- ভূয়োদর্শন Experience
- \r\n
- যুক্তি Reason
- \r\n
- কার্যকরণ-পরস্পরা সূত্র Low of causality
- \r\n
- আপেক্ষিকতবাদ Theory of relativity
- \r\n
- উদ্দীপক Stimulus
- \r\n
- জ্ঞানের অন্যান্য শক্তিগুলো The other faculties of knowledge
- \r\n
- যোগসূত্র Co-ordination
- \r\n
- সমাজ ব্যবস্থা Social order
- \r\n
- প্রয়োগ Experience
- \r\n
- বুদ্ধি Intellect
- \r\n
- বোধি Intitution
- \r\n
- প্রত্যাদেশ Revelation
- \r\n
- প্রয়োগ Experience
- \r\n
- যুক্তি Reason
- \r\n
- অবরোহ Deductive
- \r\n
- বিবর্তনকারী Evolver
- \r\n
- সর্বব্যাপী সত্তারুপে Immanent principle
- \r\n
- সর্বব্যাপী ও তুরীয় সত্তারুপে Immanent and transcendent
- \r\n
- জগৎ-বহির্ভূত স্রষ্টা Deistic conception
- \r\n
- রব্ Creator, Evolver & Sustainer
- \r\n
- সর্বব্যাপী Immanent
- \r\n
- তুরীয় Transcendent
- \r\n
- গোঁড়া Orthodox
- \r\n
- আরোহ পদ্ধতি Inductive method
- \r\n
- দড়ি Data
- \r\n
- অবরোহ Deductive
- \r\n
- অবরোহ Deductive
- \r\n
- সঙ্গতি Consistency
- \r\n
- স্বতঃসিদ্ধ Postulate
- \r\n
- সৃষ্টিকর্তা Creator
- \r\n
- সর্বব্যাপী Immanent
- \r\n
- সর্বব্যাপী ও তুরীয় Immanent and transcendent
- \r\n
- স্বতঃসিদ্ধ Axiom
- \r\n
- জ্ঞেয়েতা Knowability
- \r\n
- অভিজ্ঞতা Experience
- \r\n
- সর্বব্যাপীরুপে As an Immanent principle
- \r\n
- স্বতঃসিদ্ধ Postulate
- \r\n
- একত্বের নীতি Law of Identity
- \r\n
- দ্বন্দ্বের নীতি Law of contradiction
- \r\n
- মধ্যপন্থা বর্জনের নীতি Law of excluded midle
- \r\n
- যথাযোগ্য কারণের নীতি Law of sufficient reason
- \r\n
- পরিবর্তন Change
- \r\n
- শক্তি Power
- \r\n
- সংবেদন Sensation
- \r\n
- একীকরণ Assimilation
- \r\n
- শক্তি Power
- \r\n
- ঐক্যের নীতি Law of identity
- \r\n
- দ্বন্দ্বের নীতি Law of contradiction
- \r\n
- পরস্পর বিরোধী Contradictory
- \r\n
- স্থিতিশীল Static
- \r\n
- অ-স্থিতিশীল Dynamic
- \r\n
- মধ্যপন্থা বর্জনের নীতি Law of excluded middle
- \r\n
- দুটো গুণ Two qualities
- \r\n
- চিন্তার বিষয় Object of thought
- \r\n
- একত্বের নীতি Law of identity
- \r\n
- যথাযোগ্য কারণের নিতি Law of sufficient reason
- \r\n
\r\n
158.একত্বের নীতি Law of identity
\r\n
159.সমরূপতার নীতি Law of unoformity
\r\n
160.সমরূপতার নীতি la w of uniformity
\r\n
161.সমরূপতা Uniformity
\r\n
162.জ্ঞেয় Knowable
\r\n
163জ্ঞাতা Knower
\r\n
164.লাইবনিটজ Leibnitz
\r\n
165.জেম্স James
\r\n
166.মনাড Monad
\r\n
167.এক সংস্থা One order
\r\n
168.ঐক্য Unity
\r\n
169.স্বাতন্ত্র্য Individuality
\r\n\r\n
- \r\n
- তারা নিয়ম গঠন করছে They are framing laws
- \r\n
- অধিকতর বাস্তব Much more real
- \r\n
- স্থিতি Existence
- \r\n
- আরোহ পদ্ধতি Inductive method
- \r\n
- একত্বের নীতি Law of identity
- \r\n
- সমরূপতার নীতি Law of uniformity of nature
- \r\n
- জ্ঞাতা Knower
- \r\n
- জ্ঞেয় Knowable
- \r\n
- কার্যকারণ পরস্পরা নীতি Law of causation
- \r\n
- শুন্য থেকেই শুন্য আসে Exnhilo nihilfit
- \r\n
- স্বতঃসিদ্ধ Axiom
- \r\n
- তত্ত্ববিষয়ক প্রমাণ Casual proof
- \r\n
- উপায়স্বরূপ Means of an end
- \r\n
- ধর্মতত্ত্বমূলক যুক্তি Teleological argument
- \r\n
- প্রাকৃতিক উৎপাত Natural calamities
- \r\n
- কলাকৌশল Design
- \r\n
- কার্য Effect
- \r\n
- প্রতিষঙ্গ Correspondencde
- \r\n
- প্রতিষঙ্গমূলক মতবাদ Correspondence theory
- \r\n
- চিন্তার মাধ্যমে Categories
- \r\n
- প্রতিপাদ্য Theorem
- \r\n
- সম্পাদ্য Problem
- \r\n
- অবরোহণ করা Deduction
- \r\n
- সঙ্গতিবাদ Coherence theory
- \r\n
- কোপারনিকাস Copernicus
- \r\n
- সূর্যকেন্দ্রিক সিদ্ধান্ত Heloi Centric Theory
- \r\n
- প্রয়োগবাদ Pragmatism
- \r\n
- কার্যকারন পরস্পরা সূত্র Law of causation
- \r\n
- বস্তু Object
- \r\n
- বুদ্ধিবৃত্তি Intellect
- \r\n
- সার্বিক সিদ্ধান্ত General conclusion
- \r\n
- A presence that disturbs me with Joy of elevated thoughts, e sense of sublime of something far more deeply interfused, whose dwelling is light of setting uns and the round ocean and the living air ad the blue sky, and the mind of man, a motion and a spirit that impels all thinking things, all objects of all thoughts and rolls though all things.
- \r\n
- The Physical order of nature taken simply as science knows it canot be held to reveal any one harmonious spiritual intent. It is a more weather as Chauncey Wright called it doing and undoing without an end.
- \r\n
\r\n
Whatever else be certain this at least is certain that the world of our present natural knowledge is enveloped in larger world of some sort of whose residula properties we at present can form no positive idea-
\r\n\r\n
- \r\n
- So long as dea only with the cosmic and general, we deal with the symbols of reality but as soon as we deal with private and personal phenomena as such we deal with realities in the complete sense of the terms…..,
- \r\n
- নৈতিক শাসন ব্যবস্থা Moral Government of the universe
- \r\n
- সরাসরি অভিজ্ঞতা Direct experience
- \r\n
\r\n
যষ্ঠ পরিচ্ছেদ
\r\n
*
\r\n
সপ্তম পরিচ্ছেদ
\r\n\r\n
- \r\n
- পশুচারিক পর্যায় Pastoral stage
- \r\n
- মৌলিক অধিকার Fundamental rights
- \r\n
- আধুনিক গণতন্ত্র Modern democracy
- \r\n
- সরাসরি নির্বাচন Direct election
- \r\n
- পরোক্ষ নির্বাচন Indirect election
- \r\n
- প্রতিবিপ্লব Counter revolution
- \r\n
- মালিকানার নীতি Proprietory rights
- \r\n
- রক্ষক Custodian
- \r\n
\r\n
অষ্টম পরিচ্ছেদ
\r\n\r\n
- \r\n
- সমষ্টিগতভাবে Collectively
- \r\n
- অংশীদারের স্বত্ব The rights of partnership
- \r\n
- চুক্তিস্বত্ব Rights of contract
- \r\n
- রক্ষক Custodian
- \r\n
- আইন প্রয়োগ By the enforcement of laws
- \r\n
- সংঘবদ্ধভাবে Collectively
- \r\n
- সমবায়মূলক পদ্ধতি In a Co-operative method
- \r\n
\r\n
নবম পরিচ্ছেদ
\r\n\r\n
- \r\n
- সুখচারী প্রবৃত্তি Gregarious Instinct
- \r\n
- আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব Sovereignty of Allah
- \r\n
- মানুষের প্রতিনিধিত্ব Vicegerency of man
- \r\n
\r\n
\r\n
\r\n
দশম পরিচ্ছেদ
\r\n\r\n
- \r\n
- সংবেদন Sensation
- \r\n
- কাম জাগৃতির সময় Phallic stage
- \r\n
- একক সংখ্যা Unit
- \r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও দার্শনিক জনাব অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ লিখিত ‘জীবন সমস্যার সমাধানে ইসলাম’ নামক জনপ্রিয় পুস্তকটিতে ওহী ও প্রত্যাদেশের স্বরূপ বর্ণনা সম্পর্কে জনৈক সুধী পাঠকের সমালোচনা পাঠ করলাম। আমার ধারণা ওহী বা প্রত্যাদেশ ও এলহাম প্রভৃতি বিষয়গুলোর স্বরূপ এবং বাংলা ভাষাভাষী পাঠকগণকে তা বোঝানোর জন্য এর চাইতে সহজ এবং বোধগম্য কোন ভাষা ব্যবহার করা যায় না। জনাব দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের লেখায় ওহী সম্পর্কিত ইসলামের মৌলিক আকীদা ক্ষুন্ন হয়েছে বলে আমি মনে করি না। এ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানতে হলে সমকালীন মুসলিম বিশ্বের দুজন শীর্ষস্থানীয় দার্শনিক আলেম মুফতী আবদুহুর আকীদা সম্পর্কিত পুস্তিকা এবং সাঈদ আহমদ আকবরাবাদী লিখিত ‘ওয়াহীয়ে-ইলাহী’ নামক দুটি পুস্তক দেখা যেতে পারে। -মাওলানা মুহিউদ্দীন খান
\r\n
', 0, 'http://icsbook.info/?p=2571', 0, 'post', '', 0); INSERT INTO `bulxm_posts` (`ID`, `post_author`, `post_date`, `post_date_gmt`, `post_content`, `post_title`, `post_excerpt`, `post_status`, `comment_status`, `ping_status`, `post_password`, `post_name`, `to_ping`, `pinged`, `post_modified`, `post_modified_gmt`, `post_content_filtered`, `post_parent`, `guid`, `menu_order`, `post_type`, `post_mime_type`, `comment_count`) VALUES (2572, 1, '2014-08-21 17:48:13', '2014-08-21 11:48:13', '', 'Slide1', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', 'slide1-61', '', '', '2014-08-21 17:48:13', '2014-08-21 11:48:13', '', 2571, 'http://icsbook.info/wp-content/uploads/2014/08/Slide132.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0); INSERT INTO `bulxm_posts` (`ID`, `post_author`, `post_date`, `post_date_gmt`, `post_content`, `post_title`, `post_excerpt`, `post_status`, `comment_status`, `ping_status`, `post_password`, `post_name`, `to_ping`, `pinged`, `post_modified`, `post_modified_gmt`, `post_content_filtered`, `post_parent`, `guid`, `menu_order`, `post_type`, `post_mime_type`, `comment_count`) VALUES (2574, 1, '2014-08-21 17:50:29', '2014-08-21 11:50:29', '
খতমে নবুয়্যাত
সাইয়েদ আবুল আ’লা মওদূদী
অনুবাদক: আবদুল মান্নান তালিব
স্ক্যান কপি ডাউনলোড
বর্তমান যুগে ইসলামের বিরুদ্ধে যে সকল ফেৎনার উদ্ভব হয়েছে তন্মধ্যে নতুন নবুয়্যাতের দাবী অতি মারাত্মক। এই নতুন নবুয়্যাতের দাবী মুসলিম জাতির মধ্যে বিরাট গোমরাহীর সৃষ্টি করে চলছে। সাধারণত দ্বীন সম্পর্কে মুসলমানদের পরিপূর্ণ ও সঠিক ধারণা না থাকার কারণেই এই ফেৎনার উদ্ভব ও তার বিকাশ সম্ভব হয়েছে। দ্বীন সম্পর্কে যদি মুসলমানগণ অনভিজ্ঞ না হ’তো এবং খত্মে নবুয়্যাতকে ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারতো তবে কিছুতেই বিংশ শতাব্দীতে এই ফেৎনার উদ্ভব ও বিকাশ সম্ভব হতো না বলেই আমাদের বিশ্বাস।
খত্মে নবুয়্যাত বিশ্বাসের তাৎপর্য ও তার গুরুত্ব সম্পর্কে জনগণকে অবগত ও অবহিত করানোই হচ্ছে এই ফেৎনাকে নির্মূল করার সঠিক কার্যপন্থা। এ ছাড়া অন্যকোন পথ নেই এবং হতেও পারেনা। এ ব্যাপারে মুসলমানদের মনে যে সকল সশয় সন্দেহের সৃষ্টি করা হয় তার যুক্তিপূর্ণ ও যথার্থ সমালোচনা এবং জবাবের প্রয়োজন।
আধুনিক বিশ্বের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তানায়ক আল্লামা সাইয়েদ আবুল আ’লা মওদূদী ১৯৬২ সা?লে “খত্মে নবুয়্যাত” নামক একটি পুস্তিকা রচনা করেন। উর্দু আত্মপ্রকাশের অব্যবহিত পরেই উপরোক্ত বইটির বাংলা তরজমা পাঠকদের খেদমতে পেশ করা হয়। অতি স্বল্প সময়ের মধ্যেই বইটি নিঃশেষ হয়ে যায়। পাঠক সমাজের বারবার তাগাদার কারণে ১৯৬৭ সালে বইটির ২য় সংস্করণ এবং ১৯৭৭ সালে ৩য় সংস্করণ পাঠক সমাজের সম্মুখে পেশ করা সম্ভবপর হয়নি, কিন্তু এ সংস্করণও শিগগিরই নিঃশেষ হয়ে যায়। বিভিন্ন বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে বর্তমানে এর চতুর্থ সংস্করণ পাঠক সমাজের সম্মুখে উপস্থাপিত করা হলো। খত্মে নবুয়্যাত সম্পর্কে মুসলিম সমাজে যে বিভ্রান্তিকর মতবাদ সৃষ্টি করা হচ্ছে তাকে প্রতিহত করার কাজে সুধীবৃন্দ এই পুস্তিকা হতে সামান্যতম উপকৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক মনে করবো।
-প্রকাশক
শেষ নবী
(আরবী **********)
“মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের কারুর পিতা নন। বরং তিনি আল্লাহর রসূল এবং শেষ নবী। এবং আল্লাহ সব জিনিসের ইলম রাখেন।”
আয়াতটি সূরা আহ্যাবের পঞ্চম রুকুতে উদ্ধৃত হয়েছে। হযরত জয়নবের (রা) সঙ্গে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বিবাহের বিরুদ্ধে যেসব কাফের ও মুনাফিক মিথ্যা প্রচারণা শুরু করে দিয়েছিলো এই রুকুতে আল্লাহতায়ালা তাঁদের জবাব দিয়েছেন। তাদের বক্তব্য ছিল এই: জয়নব (রা) হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পালিত পুত্র হযরত জায়েদের (রা) স্ত্রী। অর্থাৎ তিনি রসূলুল্লাহর (স) পুত্রবধু। কাজেই জায়েদের তালাক দেবার পর রসূলুল্লাহ (স) নিজের পুত্রবধুকে বিয়ে করেছেন। এর জবাবে আল্লাহতায়ালা উপরোক্ত সূরার ৩৭ নম্বর আয়অতে বলেন: আমার নির্দেশেই এই বিবাহ সম্পাদিত হয়েছে এবং এজন্য হয়েছে যে, নিজের পালিত পুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিবাহ করায় মুসলমানদের কোনো দোষ নেই। অতঃপর ৩৮ এবং ৩৯ নম্বর আয়াতে বলেন: নবীর ওপর যে কাজ আল্লাহ ফরয করে দিয়েছেন কোন শক্তি তাঁকে তা সম্পাদন করা থেকে বিরত রাখতে পারেনা। নবীদের কাজ মানুষকে ভয় করা নয়, আল্লাহকে ভয় করা। নবীদের ব্যাপারে আল্লাহর চিরাচরিত পদ্ধতি হলো এই যে, কারুর পরোয়া না করেই তাঁরা সব সময় আল্লাহর পয়গাম দুনিয়ায় পৌঁছান এবং নিঃসংশয় চিত্তে তাঁর নির্দেশ পালনস করে থাকেন। এরপরই পেশ করেছেন আলোচ্র আয়াতটি। এই আয়াতটি বিরুদ্ধবাদীদের যাবতীয় প্রশ্ন এবং অপপ্রচারের মূলোৎপাটন করে দিয়েছে।
তাদের প্রথম প্রশ্ন হলো: আপনি নিজের পুত্রবধুকে বিবাহ করেছেন। অথচ আপনার নিজের শরীয়তও একথা বলে যে, পুত্রের বিবাহিত স্ত্রী পিতার জন্য হারাম।এর জবাবে বলা হলো: “মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের কারুর পিতা নন।” অর্থাৎ যে ব্যক্তি তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে বিবাহ করা হলো, সে কি মুহাম্মদের (সা) পুত্র ছিল? তোমরা সবাই জান যে, মুহাম্মদের (সা) কোন পুত্র নেই।
তাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো: পালিত পুত্র নিজের গর্ভজাত পুত্র নয়, একথা মেনে নিয়েও বলা যায় যে, তার তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে বিবাহ করা জায়েজ হতে পারে, কিন্তু তাকে অবশ্যই বিবাহ করতে হবে এবং প্রয়োজনটা কোথায়? এর জবাবে বলা হলো: “কিন্তু তিনি আল্লাহর রসূল।” অর্থাৎ যে হালাল বস্তু তোমাদের রসম-রেওয়াজের বদৌলতে অযথা হারামে পরিণত হয়েছে, সে সম্পর্কে যাবতীয় বিদ্বেষ এবং পক্ষপাতিত্ব খতম করে তার হালাল হওয়াকে নিঃসন্দেহ এবং নিঃসংশয় করে তোলা রসূলের অবশ্য করণীয় কাজ। [‘খত্মে নবুয়্যাত’ অস্বীকারকারীরা এখানে প্রশ্ন উঠায় যে, কাফের এবং মুনাফেকদের এই প্রশ্নটি কোন্ হাদীসে উল্লিীখত হয়েছে? কিন্তু এই প্রশ্নটি আসলে কোরআন সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতারই ফল। কোরআন মজীদের বহু জায়গায় আল্লাহতায়ালা বিরোধীদলের প্রশ্ন নকল না করেই তাদের জবাব দিয়ে গেছেন এবং জবাব থেকেই একথা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ হয়েছে যে, যে প্রশ্নটির জবাব দেয়া হচ্ছে সেটি কি ছিলো। এখানেও একই ব্যাপার। এখানেও জবাব নিজেই প্রশ্নের বিষয়বস্তু বিবৃত করছে। প্রথম বাক্যটির পর শব্দ দিয়ে দ্বিতীয় বাক্যটি শুরু করার প্রমাণ হলো যে, প্রথম বাক্যে প্রশ্নকারীর একটি কথার জবাব হয়ে যাবার পরও তার আর একটি প্রশ্ন বাকি রয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় বাক্যে তার জবাব দেয়া হয়েছে।মুহাম্মদ (স) নিজের পুত্রবধুকে বিবাহ করেছেন- তাদের এই প্রশ্নের জবাব তারা প্রথম বাক্যে পেয়ে গেছে। অতঃপর তাদের প্রশ্ন ছিল যে, একাজটা করার এমন কি প্রয়োজন ছিল? এর জবাবে বলা হলো: “কিন্তু তিনি আল্লাহর রসূল এবং শেষ নবী।” অন্য কথায় বলা যায়, যেমন কেউ বললো, জায়েদ দাঁড়ায়নি কিন্তু বকর দাঁড়িয়েছে। এর অর্থ হলো এই যে, “জায়েদ দাঁড়ায়নি” কথা থেকে একটি প্রশ্নের জবাব পাওয়ার পরও প্রশ্নকারীর আর একটি প্রশ্ন বাকি রয়ে গেছে। অর্থাৎ যদি জায়েদ না দাঁড়িয়ে থাকে, তবে কে দাঁড়ালো? এই প্রশ্নের জবাবে “কিন্তু বকর দাঁড়িয়েছে” বাক্যটি বলা হলো।]
আবার অতিরিক্ত জোর দেবার জন্য বলেন: “এবং শেষ নবী।” অর্থাৎ তাঁর যুগে আইন এবং সমাজ সংস্কারমূলক কোনো বিধি প্রবর্তিত না হয়ে থাকলে, এই কাজ সমাধা করার জন্য তাঁর পর কোনো রসূল তো নয়ই, কোনো নবীও আসবেন না। কাজেই জাহেলী যুগের রসম-রেওয়াজ খতম করে দেবার প্রয়োজন এখনই দেখা দিয়েছে এবং তিনি নিজেই একাজটা সমাধা করে যাবেন।
অতঃপর আরো জোর দিয়ে বলেন: “এবং আল্লাহ সব জিনিসের ইলম রাখেন।” অর্থাৎ এই মুহূর্তে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সাহায্যে এই বদ রসমটা খতম করিয়ে দেবার প্রয়োজনটা কি এবং এটা না করায় কি ক্ষতি-একথা একমাত্র আল্লাহই জানেন। তিনি জানেন যে, তাঁর পক্ষথেকে আর কোন নবী আসবেন না। কাজেই শেষ নবীর সাহায্যে যদি এই বদ রসমটা খতম করিয়ে না দেয়া হয়, তাহলেএর পরে আর দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি আসবেন না, যিনি একে নির্মূল করে দিতে চাইলে সমগ্র দুনিয়ায় মুসলমানদের মধ্য হতে চিরকালের জন্য এটি নির্মুল হয়ে যাবে। পরবর্তীকালেল সংস্কারকগণ এটা নির্মূল করে দিলেও তাঁদের কারুর কাজের পেছনে এমন কোন চিরন্তন এবং বিশ্বজনীন কর্তৃত্ব থাকবেনা, যার ফলে প্রত্যেক দেশ এবং প্রত্যেক যুগের লোকেরা তাঁদের অনুসরণ করতে বাধ্য হবে এবং তাঁদের কারুর ব্যক্তিত্বও এতোটা পাক-পবিত্র বলে গণ্য হবেনা যে, কোনো কাজ নিছক তাঁর সুন্নাত হবার দরুন মানুষের হৃদয় হতে সে সম্পর্কে যাবতীয় ঘৃণা, দ্বিধা এবং সন্দেহ মুহূর্তের মধ্যে নির্মল হয়ে যাবে।
কোরআনের পূর্বাপর বিবৃতির ফায়সালা
বর্তমান যুগে একটি দল নতুন নবুয়্যাতের ফিত্না সৃষ্টি করেছে। এরা ‘খাতিমুন নাবিয়ীন’ শব্দের অর্থ করে “নবীদের মোহর”। এরা বুঝাতে চায় যে, রসূলুল্লাহ (স) তাঁর মোহরাংকিত হয়ে আরো অনেক নবী দুনিয়ায় আগমন করবেন। অথবা অন্য কথায় বলা যায়,যতক্ষণ পর্যন্ত কারুর নবুয়্যাত রসূলুল্লাহর মোহরাংকিত না হয়, ততক্ষণ তিনি নবী হতে পারবেন না।
কিন্তু “খাতিমুন নাবিয়ীন” শব্দ সম্বলিত আয়াতটি যে ঘটনা পরম্পরায় বিবৃত হয়েছে, তাকে সেই বিশেষ পরিবেশে রেখে বিচার করলে, তা থেকে এ অর্থ গ্রহণের কোন সুযোগই দেখা যায় না। অধিকন্তু এ অর্থ গ্রহণ করার পর এ পরিবেশে শব্দটির ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তাই বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং বক্তব্যের আসল উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়। এটা কি নিতান্ত অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক কথা নয় যে, জয়নবের নিকাহর বিরুদ্ধে কথিত প্রতিবাদ এবংতাথেকে সৃষ্ট নানাপ্রকার সংশয়-সন্দেহের জবাব দিতে দিতে হঠাৎ মাঝখানে বলে দেয়া হলো: মুহাম্মদ (সা) নবীদের মোহর। অর্থাৎ ভবিষ্যতে যত নবী আসবেন তাঁরা সবাই তাঁর মোহরাংকিত হবেন। আগে পিছের এই ঘটনার মাঝখানে একথাটির আকস্মিক আগমন শুধু অবান্তরই নয়, এ থেকে প্রতিবাদকারীদের জবাবে যে যুক্তি পেশ করা হচ্ছিল, তাও দুর্বল হয়ে পড়ে। এহেন পরিস্থিতিতে প্রতিবাদকারীদের হাতে একটা চমৎকার সুযোগ আসতো এবং তারা সহজেই বলতে পারতো যে, আপনার জীবনে যদি এ কাজটা সম্পন্ন না করতেন, তাহলে ভালই হতো, কোন বিপদের সম্ভাবনা থাকতো না, এই বদ রসমটা বিলুপ্ত করার যদি এতোই প্রয়োজন হয়ে থাকে, তাহলে আপনার পরে আপনার মোহরাংকিত হয়ে যেসব নবী আসবেন, এ কাজটা তাঁদের হাতেই সম্পন্ন হবে।
উল্লিখিত দলটি শব্দটির আর একটি বিকৃত অর্থ নিয়েছে: ‘খাতিমুন নাবিয়ীন” অর্থ হলো: “আফজালুন নাবিয়ীন।” অর্থাৎ নবুয়্যাতের দরজা উন্মুক্তই রয়েছে, তবে কিনা নবুয়্যাত পূর্ণতা লাভ করেছে রসূলুল্লাহর ওপর। কিন্তু এ অর্থ গ্রহণ করতে গিয়েও পূর্বোল্লিখিত বিভ্রান্তির পুনাবির্ভাবের হাত থেকে নিস্তার নেই। অগ্র-পশ্চাতের সাথে এরও কোন সম্পর্ক নেই।বরং এটি পূর্বাপরের ঘটনা পরম্পরার সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থবহ। কাফের ও মুনাফিকরা বলতে পারতো: ‘জনাব, আপনার চাইতে কম মর্যাদার হলেও আপনার পরে যখন আরোনবী আসছেন, তখন একাজটা না হয় তাদের ওপরই ছেড়ে দিতেন। এই বদ রসমটাও যে আপনাকেই মিটাতে হবে, এরই বা কি এমন যৌক্তিকতা আছে!
আভিধানিক অর্থ
তাহলে পূর্বাপর ঘটনাবলীল সাথে সম্পর্কের দিক দিয়ে একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, এখানে খাতিমুন নাবিয়ীন শব্দের অর্থ নবুয়্যাতের সিলসিলার পরিসমাপ্তি ঘোষণা। অর্থাৎ রসূলুল্লাহর (স) পর আর কোন নবী আসবেননা। কিন্তু শুধু পূর্বাপর সম্বন্ধের দিক দিয়েই নয়, আভিধানিক অর্থের দিক দিয়েও এটিই একমাত্র সত্য। আরবী অভিধান এবং প্রবাদ অনুযায়ী ‘খতম’ শব্দের অর্থ হলো: মোহর লাগানো, বন্ধ করা, শেষ পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া এবং কোনো কাজ শেষ করে দায়িত্বথেকে অব্যাহতি লাভ করা।
খাতামাল আমাল (******) অর্থ হলো: ফারেগা মিনাল আমল (*****) অর্থাৎ কাজ শেষ করে ফেলেছৈ। খাতামাল এনায়া (*****) অর্থ হলো: পাত্রের মুখ বন্ধ করে দিয়েছে এবং তার ওপর মোহর লাগিয়ে দিয়েছে, যাতে করে তার ভেতর থেকে কোনো জিনিস বাইরে আসতে এবং বাইরে থেকে কিছু ভেতরে যেতে না পারে।
খাতামাল কিতাব (*****) অর্থ হলো: পত্র বন্ধ করে তার ওপর মোহর লাগিয়ে দিয়েছে, ফলে পত্রটি সংরক্ষিত হবে।
খাতামা আলাল কাল্ব (******) অর্থ হলো: দিলের ওপর মোহর লাগিয়ে দিয়েছে। এরপর বাইরের কোনো কথা আর সে বুঝতে পারবে না এবং তার ভেতরের স্থিতিশীল কোনো কথা বাইরে বেরুতে পারবে না।
খিতামুল কুল্লি মাশরুব (****) অর্থ হলো: কোনো পানীয় পান করার পর যে স্বাদ অনুভূত হয়।
খাতিমাতু কুল্লি শাইয়েন আকিবাতুহু ওয়া আখিরাতুহ (আরবী ***********) অর্থাৎ] প্রত্যেক জিনিসের খাতিমা অর্থ হলো তার পরিণাম এবং শেষ।
খাতামাশ্ শাইয়ে বালাগা আখিরাহ (আরবী ***********) অর্থাৎ কোনো জিনিসকে খতম করার অর্থ হলো তা শেষ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। -খত্মে কোরআন বলতে এই অর্থ গ্রহণ করা হয় এবং এর অর্থের ভিত্তিতেই প্রত্যেক সূরার শেষ আয়াতকে বলা হয় ‘খাওয়াতিম’।
খাতিমুল কওমে আখেরুহুম (আরবী *********) অর্থাৎ খাতিমুল কওম অর্থ জাতির শেষ ব্যক্তি (দ্রষ্টব্য: লিসানুল আরব, কামুস এবং আকরাবুল মাওয়ারিদ।) [এখানে আমি মাত্র তিনটি অভিধানের উল্লেখ করলাম। কিন্তু শুধু এই তিনটি অভিধানই কেন, আরবী ভাষার যে কোন নির্ভরযোগ্য অভিধান খুলে দেখুন সেখানে ‘খতম’ শব্দের উপরোল্লিখিত ব্যাখ্যাই পাবেন। কিন্তু ‘খতমে নবুয়্যাত’ অস্বীকারকারীরা খোদার দ্বীনের সুরক্ষিত গৃহে সিঁদ লাগাবার জন্য এক আভিধানিক অর্থকে পুর্ণরূপে এড়িয়ে গেছেন। তারা বলতে চান, কোন ব্যক্তিকে ‘খাতামুশ শোয়ারা’, খাতামুল ফোকাহা’ অথবা ‘খাতামুল মুফাসসিরিন’ বললে এ অর্থ গ্রহণ করা হয় না যে, যাকে ঐ পদবী দেয়া হয়, তার পরে আর কোনো শায়ের কোন ফকিহ অথবা মুফাস্সরি পয়দা হননি। বরং এর অর্থ এই হয় যে, ঐ ব্যক্তির ওপররে উল্লিীখত বিদ্যা অথবা শিল্পের পূর্ণতার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। অথবা কোন বস্তুকে অত্যাধিক ফুটিয়ে তুলবার উদ্দেশ্যে এই ধরনেসর পদবী ব্যবহারের ফলে কখনো খতম-এর আভিধানিক অর্থ ‘পূর্ণ’ অথবা ‘শ্রেষ্ঠ’ হয় না এবং ‘শেষ’ অর্ এর ব্যবহার ত্রুটিপূর্ণ বলৌ গন্য হয় না।
একমাত্র ব্যাকরণ-রীতি সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তিই এ ধরনের কথা বলতে পারেন। কোন ভাষারই নিয়ম এ নয় যে, কোন একটি শব্দ তার আসল অর্থের পরিবর্তে কখনো কখনো দূর সম্পর্কের অন্য কোন অর্থে ব্যবহৃরিত হলেসেটাই আসল অর্থে পরিণত হবে এবং আসল আভিধানিক অর্থে তার ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। আপনিয খন কোন আরবের সম্মুখে বলবেন:
(জাআ খাতামুল কওম)-তখন কখনো সে মনে করবে না যে গোত্রের শ্রেষ্ঠ অথবাপ কামেল ব্যক্তি এসেছে। বরং সে মনে করবে যে, গোত্রের সবাই এসে গেছে, এমনকি শেষ ব্যক্তিটি পর্যন্তও।]
এজন্যই সমস্ত অভিধান বিশারত এবং তাফসীরকারগণ একযোগে ‘খাতিমুন নাবিয়ীনা’ শব্দের অর্থ নিয়েছেন, আখেরুন নাবিয়ীন-অ অর্থাৎ নবীদের শেষ। আরবী অভিধান এবং প্রবাদ অনুযায়ী ‘খাতিম’ –এর অর্থ যাকঘরের মোহর নয়, যা চিঠির ওপর লাগিয়ে চিঠি পোস্ট করা হয়; বরং সেই মোহর যা খামের মুখে এই উদ্দেশ্যে লাগানো হয় যে, তার ভেতর থেকে কোনো জিনিস বাইরে বেরুতে পারবে না এবং বাইরের কোনো জিনিস ভেতরে প্রবেশ করতে পারবে না।
রাসূলুল্লাহর বাণী
পূর্বাপর সম্বন্ধ এবং আভিধানিক অর্থের দিক দিয়ে শব্দটির যে অর্থ হয়, রসুলুল্লাহর (স) বিভিন্ন ব্যাখ্যাও এর সমর্থন করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে কতিপয় হাদীসের উল্লেখ করছি:
(আরবী *********)
(১) রসূলুল্লাহ (স) বলেন: বনি ইসরাঈলদের নেতৃত্ব করতেন্ আল্লাহর রসূলগণ। যখন কোনো নবী ইন্তেকাল করতেন, তখন অন্য কোনো নবী তার স্থলাভিষিক্ত হতেন। কিন্তু আমার পরে কোনো নবীহবে না, হবে শুধু খলিফা।
(আরবী *********)
(২) রসূলুল্লাহ (স) বলেন: আমি আমার পূর্ববর্তী নবীদের দৃষ্টান্ত হলো এই যে, এক ব্যক্তি একটি দালান তৈরী করলো এবং খুব সুন্দর ও শোভনীয় করে সেটি সজ্জিত করলো।কিন্তু তার এক কোণে একটি ইটের স্থান শূন্য ছিল। দালানটির চতুর্দিকে মানুষ ঘুরে ঘুরে তার সৌন্দর্য দেখে বিস্ময় প্রকাশ করছিল এবং বলছিল, ‘এ স্থানে একটা ইট রাখা হয়নি কেন? কাজেই আমি সেই ইট এবং আমিই শেষ নবী।’ (অর্থাৎ আমার আসার পর নবুয়্যাতের দালান পূর্ণতা লাভ করেছে, এখন এর মধ্যে এমন কোন শূন্যস্থান নেই যাকে পূর্ণ করার জন্য আবার কোনো নবীর প্রয়োজন হবে)।
এই ধরনের চারটি হাদীস মুসলিম শরীফে কিতাবুল ফাজায়েলের বাবু খাতিমুন নাবিয়ীনে উল্লিখিত হয়েছে। এবং শেষ হাদীসটিতে এতোটুকুন অংশ বর্ধিত হয়েছে: (আরবী *********) “অতঃপর আমি এলাম এবং আমি নবীদের সিলসিলা খতম করে দিলাম।”
হাদীসটি তিরমিজী শরীফে একই শব্দ সম্বলিত হয়ে ‘কিতাবুল মানাকিবের বাবু ফাজলিন নবী’ এবং কিতাবুল আদাবের ‘বাবুল আমসালে’ বর্ণিত হয়েছে।
মুসনাদে আবু দাউদ তিয়ালাসীতে হাদীসটি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণিত হাদীসের সিলসিলায় উল্লিখিত হয়েছে এবং এর শেষ অংশটুকু হলো (আরবী *********) “আমার মাধ্যমে নবীদের সিলসিলা খতম করা হলো।”
মুসনাদে আহমদে সামান্য শাব্দিক হেরফেরের সাথে এই ধরনের হাদীস হযরত উবাই ইবনে কা’ৎব, হযরত আবু সাঈদ খুদরী এবং হযরত আবু হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে।
(আরবী *********)
(৩) রসূলুল্লাহ (স) বলেন: “ছ’টা ব্যাপারে অন্যান্য নবীদের ওপর আমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে: (১) আমাকে পূর্ণ অর্থব্যঞ্জক সংক্ষিপ্ত কথা বলার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। (২) আমাকে শক্তিমত্তা ও প্রতিপত্তি দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে। (৩) আমাকে গনীমাতের অর্থ-সম্পদ আমার জন্য হালাল করা হয়েছে। (৪) পৃথিভীর জমীনকে আমার জন্য মসজিদে (অর্থাৎ আমার শরীয়তে নামায কেবল বিশেষ ইবাদতগাহে নয়, দুনিয়ার প্রত্যেক স্থানে পড়া যেতে পারে) এবং মাটিকে পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যমে (শুধু পানিই নয়, মাটির সাহায্যে তায়াম্মুম করেও পবিত্রতা হাসিল অর্থাৎ অজু এবং গোসলের কাজ সম্পন্ন করা যেতে পারে) পরিণত করা হয়েছে। (৫) সমগ্র দুনিয়ার জন্য আমাকে রসূল হিসাবে পাঠানো হয়েছে এবং (৬) আমার ওপর নবীদের সিলসিলা খতম করে দেয়া হয়েছে।”
(৪) রসূলুল্লাহ (স) বলেন: ‘রিসালাত এবং নবুয়্যাতের সিলসিলা খতম করে দেয়া হয়েছে। আমার পর কোনো রসূল এবং নবী আসবে না।”
(আরবী *********)
(৫) রসূলুল্লাহ (স) বলেন: “আমি মুহাম্মদ। আমি আহমদ। আমি বিলুপ্তকারী, আমার সাহায্যে কুফরকে বিলুপ্ত করা হবে। আমি সমবেতকারী, আমার পরে লোকদেরকে হাশরের ময়দানে সমবেত করা হবে (অর্থাৎ আমার পরে শুধু কিয়ামতই বাকি আছে) আমি সবার শেষে আগমনকারী (এবং সবার শেষে আগমনকারী হলো সেই) যার পরে আর নবী আসবে না।”
(আরবী *********)
রসূলুল্লাহ (স) বলেন: “আল্লাহ নিশ্চয়ই এমন কোনো নবী পাঠাননি যিনি তাঁর উম্মতকে দাজ্জাল সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করেননি। (কিন্তু তাদের যুগে সে বহির্গত হয়নি)। এখন আমিই শেষ নবী এবং তোমরা শেষ উম্মত। দাজ্জাল নিঃসন্দেহে এখন তোমাদের মধ্যে বহির্গত হবে।”
(আরবী *********)
(৭) আবদুর রহমান ইবনে জোবায়ের বলেন: আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে আস্’কে বলতে শুনেছি যে, একদিন রসূলুল্লাহ (সা) নিজের গৃহ থেকে বের হয়ে আমাদের মধ্যে তাশরীফ আনলেন। তিনি এভাবে আসলেন যেন আমাদের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে যাচ্ছেন। তিনি তিনবার বললেন, আমি উম্মী নবী মুহাম্মদ। অতঃপর বললেন, আমার পর আর কোন নবী নেই।
(আরবী *********)
(৮) রসূলুল্লাহ (স) বলেন: আমার পরে আর কোনো নবুয়্যাত নেই। আছে শুধু সুসংবাদ দানকারী কথার সমষ্টি। জিজ্ঞেস করা হলো, হে খোদার রসূল, সুসংবাদ দানকারী কথাগুলো কি? জবাবে তিনি বললেন: ভালো স্বপ্ন। অথবা বললেন, কল্যাণময় স্বপ্ন। (অর্থাৎ খোদার অহি নাযীল হবার এখন আর সম্ভাবনা নেই। বড় জোর এতোটুকু বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে যদি কাউকে কোনো ইঙ্গিত দেয়া হয়, তাহলে শুধু ভালো স্বপ্নের মাধ্যমেই তা দেয়া হবে)।
(আরবী *********)
(৯) রসূলুল্লাহ (স) বলেন: আমার পরে যদি কোনো নবী হতো, তাহলে উমর ইবনে খাত্তাম সে সৌভাগ্য লাভ করতো।
(আরবী *********)
(১০) রসূলুল্লাহ (স) হযরত আলীকে (রা) বলেন: আমার সাথে তোমার সম্পর্ক মুসার সাথে হারুনের সম্পর্কের মতো। কিন্তু আমার পরে আর কোনো নবী নেই।
বুখারী এবং মুসলিম তাবুক যুদ্ধের বর্ণনা প্রসংগেও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মুসনাদে আহমদে এই বিষয়বস্তু সম্বলিত দু’টি হাদীস হযরত সা’দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস থেকে বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে একটি বণনার শেষাংশ হলো: (আরবী *********) “কিন্তু আমার পরে আর কোনো নবুয়্যাত নেই।” আবু দাউদ তিয়ালাসি, ইমাম আহমদ এবং মুহাম্মদ ইসহাক এ সম্পর্কে যে বিস্তারিত বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন তা থেকে জানা যায় যে, তাবুক যুদ্ধে রওয়ানা হবার পূর্বে রসূলুল্লাহ (স) হযরত আলীকে (রা) মদীনা তাইয়েবার হেফাজত এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রেখে যাবার ফায়সালা করেন। এ ব্যাপারটি নিয়ে মুনাফিকরা বিভিন্ন কথা বলতে লাগলো। হযরত আলী (রা) রসূলুল্লাহকে (স) বললেন, ‘হে খোদার রসূল, আপনি কি আমাকে শিশু এবং মেয়েদের মধ্যে ছেড়ে যাচ্ছেন? রসূলুল্লাহ (স) তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন: ‘আমার সাথে তোমার সম্পর্কতো মূসার সাথে হারুনের সম্পর্কের মতো। অর্থাৎ কোহেতুরে যাবার সময় হযরত মূসা (আ) যেমন বনী ইসরাঈলদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য হযরত হারুনকে পেছনে রেখে গিয়েছিলেন অনুরূপভাবে মদীনার হেফাজতের জন্য আমি তোমাকে পেছনে রেখে যাচ্ছি। কিন্তু সংগে সংগে রসূলুল্লাহর মনে এই সন্দেহও জাগলো যে, হযরত হারুনের সংগে এভাবে তুলনা করার ফলে হয়তো পরে এ থেকে কোনো ফিত্না সৃষ্টি হতে পারে। কাজেই পরমুহূর্তেই তিনি কথাটা স্পষ্ট করে দিলেন যে, ‘আমার পর কোনো ব্যক্তি নবী হবে না।’
(আরবী *********)
(১১) হযরত সাওবান বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (স) বলেন: আর কথা হচ্ছে এই যে, আমার উম্মতের মধ্যে ত্রিশজন মিথ্যাবাদী হবে। তাদের প্রত্যেকেই নিজেকে নবী বলে দাবী করবে। অথচ আমার পর আর কোনো নবী নেই।
এই বিষয়বস্তু সম্বলিত আর একটি হাদীস আবু দাউদ ‘কিতাবুল মালাহেমে’ হযরত আবু হোরায় (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিরমিযীও হযরত সাওবান এবং হযরত আবু হোরায় (রা) থেকে এ হাদীস দু’টি বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় বর্ণনাটির শব্দ হলো এই:
(আরবী *********)
অর্থাৎ এমন কি তিরিশ জনের মতো প্রতারক আসবে। তাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকেই দাবীকরবে যে, সে আল্লাহর রসূল।
(১২) রসূলুল্লাহ (স) বলেন: আমাদের পূর্বে যেসব বনি ইসরাঈল গুজরে গেছেন, তাঁদের মধ্যে অনেক লোক এমন ছিলেন, যাঁদের সংগে কালাম করা হয়েছে, অথচ তাঁরা নবী ছিলেন না। আমার উম্মতের মধ্যে যদি এমন কেউ হয়, তাহলে সে হবে উমর।
মুসলিমে এই বিষয়বস্তু সম্বলিত যে হাদীস উল্লিখিত হয়েছে, তাতে (****) এর পরিবর্তে (****) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু মুকাল্লিম এবং মুহাদ্দিস শব্দ দুটি সমার্থক। অর্থাৎ এমন ব্যক্তি যার সংগে আল্লাহতায়ালা কালাম করেছেন অথবা যার সাথে পর্দার পেছন থেকে কথা বলা হয়। এ থেকে জানা যায় যে, নবুয়্যাত ছাড়াও যদি এই উম্মতের মধ্যে কেউ আল্লাহর সাথে কালাম করার সৌভাগ্যঅর্জন করেন, তাহলে তিনি একমাত্র হযরত উমরই হবেন।
(আরবী *********)
(১৩) রসূলুল্লাহ (স) বলেন: আমার পরে আর কোনো নবী নেই এবং আমার উম্মতের পর আর কোনো উম্মত (অর্থাৎ কোনো ভবিষ্যত নবীর উম্মত) নেই।
(আরবী *********)
(১৪) রসূলুল্লাহ (স) বলেন: আমি শেষ নবী এবং আমার মসজিদ (অর্থাৎ মসজিদে নববী) শেষ মসজিদ। [খত্মে নবুয়্যাত অস্বীকারকারীরা এই হাদীস থেকে প্রমাণ করে যে, রসূলুল্লাহ (স) যেমন তাঁর মসজিদকে শেষ মসজিদ বলেছেন, অথচ এটি শেষ মসজিদ নয়; এর পরও দুনিয়ার বেশুমার মসজিদ নির্মিত হয়েছে অনুরূপভাবে তিনি বলেছেন, যে তিনি শেষ নবী। এর অর্থ হলো এই যে, তাঁর পরেও নবী আসবেন। অবশ্য শ্রেষ্ঠত্বের দিক দিয়ে তিনি হলেন শেষ নবী এবং তাঁর মসজিদ শেষ মসজিদ। কিন্তু আসলে এ ধরনের বিকৃত অর্থই একথা প্রমাণ করে যে, এই লোকগুলো আল্লাহ এবং রসূলের কালামের অর্থ অনুধাবন করার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে। মুসলিম শরীফের যে স্থানে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে সেখানে এই বিষয়ে সমস্ত হাদীস সম্মুখে রাখলেই একথা পরিস্ফূট হবে যে, রসূলুল্লাহ (স) তাঁর মসজিদকে শেষ মসজিদ কোন্ অর্থে বলেছেন। এখানে হযরত আবুহোরায় (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) এবং হযরত মায়মুনার (রা) যে বর্ণনা ইমাম মুসলিম উদ্ধৃত করেছেন, তাতে বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার মাত্র তিনটি মসজিদ এমন রয়েছে যেগুলো সাধারণ মসজিদগুলোর ওপর শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার। সেখানে নামায পড়লে অন্যান্য মসজিদের চেয়ে হাজার গুণ বেশী সওয়াব হাসিল হয় এবং এজন্য একমাত্র এই তিনটি মসজিদে নামায পড়ার জন্য সফর করা জায়েজ। দুনিয়ার অবশিষ্ট মসজিদগুলোর মধ্যে সমস্ত মসজিদকে বাদ দিয়ে বিশেষ করে একটি মসজিদে নামায পড়বার জন্য সেদিকে সফর করা জায়েজ নয়। এর মধ্যে ‘মসজিদুল হারাম’ হলো প্রথম মসজিদ। হযরত ইবরাহীম (আ) এটি বানিয়েছিলেন। দ্বিতীয়টি হলো ‘মসজিদে আক্সা’। হযরত সুলায়মান (আ) এটি নির্মাণ করেছিলেন এবং তৃতীয়টি মদীনা তাইয়েবার ‘মসজিদে নববী’। এটি নির্মাণ করেন রসূলুল্লাহ (স)। রসূলুল্লাহ (স) এরশাদের অর্থ হলো এই যে, এখন যেহেতু আমার পর আর কোনো নবী আসবেনা, সেহেতু আমার মসিজদের পর দুনিয়ায় আর চতুর্থ এমন কোনো মসজিদ নির্মিত হবেনা, যেখানে নামায পড়ার সওয়াব অন্যান্য মসজিদের তুলনায় বেশী হবে এবং সেখানে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে সেদিকে সফর করা জায়েজ হবে।
রসূলুল্লাহ (স) নিকট থেকে বহু সাহাবা হাদীসগুলো বর্ণনা করেছেন এবং বহু মুহাদ্দিস অত্যন্ত শক্তিশালী এবং নির্ভরযোগ্য সনদসহ এগুলো উদ্ধৃত করেছেন। এগুলো অধ্যয়ন করার পর স্পষ্ট জানা যায় যে, রসুল্লাহ (স) বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন শব্দের ব্যবহার করে একথা পরিষ্কার করেদিয়েছেন যে, তিনি শেষ নবী। তাঁর পর কোনো নবীআসবে না। নবুয়্যঅতের সিলসিলা তাঁর ওপর খতম হয়ে গেছে এবং তাঁর পরে যে ব্যক্তি রসূল অথবা নবী হবার দাবী করবে, সে হবে দাজ্জাল এবং কাজ্জাব। কোরআনের ‘খাতিমুন নাবিয়ীন’ শব্দের এর চাইতে বেশী শক্তিশালী, নির্ভরযোগ্য এবং প্রমাণ্য ব্যাখ্যা আর কি হতে পারে। রসূলুল্লাহ বাণীই এখঅনে চরম সনদ এবং প্রমাণ। উপরন্তু যখন তা কোরআনের একটি আয়াতের ব্যাখ্যা করে তখন তা আরো অধিক শক্তিশালী প্রমাণে পরিণত হয়। এখন প্রশ্ন হলো এই যে, মুহাম্মদের (স) চেয়ে বেশী কে কোরআনকে বুঝেছে এবং তাঁর চাইতে বেশী এর ব্যাখ্যার অধিকার কার আছে? এমন কে আছে যে, খতমে নবুয়্যাতের অন্য কোনো অর্থ বর্ণনা করবে এবং তা মেনে নেয়া তো দূরের কথা, সে সম্পর্কে চিন্তা করতেও আমরা প্রস্তুত হবো?
সাহাবাদের ইজমা
কোরআন এবং সুন্নাহর পর সাহায়ে কেরামের ইজমা বা মতৈক্য হলো তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সমস্ত নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক বর্ণনা থেকে প্রমাণ হয় যে, রসূলুল্লাহর (স)। ইন্তেকালের অব্যবহিত পরেই যেসব লোক নবুয়্যাতের দাবী করে এবং যারা তাদের নবুয়্যাত স্বীকার করে নেয়, তাদের সবার বিরুদ্ধে সাহাবায়ে কেরাম সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ করেছিলেন। এসম্পর্কে মুসাইলামা কাজ্জাবের ব্যাপারটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সে রসূলুল্লাহর (স) নবুয়্যাত অস্বীকার করছিল না; বরং সে দাবী করছিল যে, রসূলুল্লাহ্র নবুয়্যাতে তাকেও অংশীদার করা হয়েছে। রসূলুল্লাহর ইন্তেকালের পূর্বেসে তাঁর নিকট যে চিঠি পাঠিয়েছিল তার আসল শব্দ হলো এই:
“অর্থাৎ আল্লাহর রসূল মুসাইলামার তরফ হতে আল্লাহর রসূল মুহাম্মদের নিকট। আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আপনি জেনে রাখুন, আমাকে আপনার সাথে নবুয়্যাতের কাজে শরীক করা হয়েছে।”
এভাবে স্পষ্ট করে রিসালাতে মুহাম্মদীকে স্বীকার করে নেবার পরও তাকে ইসলাম বহির্ভূত বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয়েছে। ইতিহাস থেকে একথাও প্রমাণ হয় যে, বনূ হোনায়পা সরল অন্তঃকরণে তার ওপর ঈমান এনেছিল। অবশ্য তারা এই বিভ্রান্তির মধ্যে পড়েছিল যে, মুহাম্মদ (স) নিজেই তাকে তার নবুয়্যাতের কাজে শরীক করেছেন। এ ছাড়াও আর একটা কথা হলো এই যে, মদীনা তাইয়েবা থেকে এক ব্যক্তি কোরআনের শিক্ষা গ্রহণ করেছিল এবং বনু হোনায়ফার নিকটে গিয়ে সে কোরআনের আয়াতকে মুসাইলামার নিকট অবতীর্ণ আয়াতরূপে পেশ করেছিল।
(আরবী *********)
কিন্তু এ সত্ত্বেও সাহাবায়ে কেরাম তাকে মুসলমান বলে স্বীকার করেননি এবং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। [শেষ নবুয়্যাতে অবিশ্বাসীরা নবী করিমের (স)-হাদীসেরবিপরীতে হযরত আয়েশার (রা) বলে কথিত নিম্নোক্ত বর্ণনা উদ্ধৃতি দেয়: “বল নিশ্চয়ই তিনি খাতামুন নাবিয়ীন, এ কথা বলো না যে তার পর নবী নেই।” প্রথমত নবী করিমের (স) সুস্পষ্ট আদেশকে অস্বীকার করার জন্রহযরত আয়েশার (রা) উদ্ধৃতি দেয়া একটা ধৃষ্টতা। অধিকন্তু হযরত আয়েশার (রা) বলে কথিত উপরোক্ত উদ্ধৃতি মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়। হাদীস শাস্ত্রের কোন প্রামাণিক গ্রন্থেই হযরত আয়েশার (রা) উপরোক্ত উক্তির উল্লেখ নেই। কোন বিখ্যাত হাদীস লিপিবদ্ধকারী এ হাদীসটি লিপিবদ্ধ বা উল্লেখ করেননি।
উপরোক্ত হাদীসটি ‘দার-ই মানহুর’ নামক তাফসীর এবং ‘তাকমিলাহ মাজমা-উল-বিহার’ নামক অপরিচিত হাদীস সংকলণ থেকে নেয়া হয়েছে; কিন্তু এর উৎপত্তি বা বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে কিছুই জানা নেই। রসূল (স) সুস্পষ্ট হাদীস বা বিখ্যাত হাদীস বর্ণনাকারীরা খুবই নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে বর্ণনা করেছেন, তাকে অস্বীকার করার জন্য হযরত আয়েশার (রা) কথার উল্লেখ চূড়ান্ত ধৃষ্টতা মাত্র।] অতঃপর একথা বলার সুযোগ নেই যে, ইসলাম বহির্ভূত হবার কারণে সাহাবাগণ তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেননি বরং বিদ্রোহ ঘোষণা করার কারণেই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয়েছিল। ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে বিদ্রোহী মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হলেও তাদের যুদ্ধবন্দীদেরকে গোলামে পরিণত করা যেতে পারে না। বরং শুধু মুসলমানই নয়, জিম্মীও (অমুসলিম) বিদ্রোহ ঘোষণা করলে, গ্রেফতার করার পর তাকে গোলামে পরিণত করা জায়েজ নয়। কিন্তু মুসাইলামা এবং তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রা) ঘোষণা করেন যে, তাদের মেয়েদের এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেদেরকে গোলাম বানানো হবে এবং গ্রেফতার করার পর দেখা গেলো, সত্যি সত্যিই তাদেরকে গোলাম বানানো হয়েছে। হযরত আলী (রা) তাদের মধ্যথেকেই জনৈক যুদ্ধ বন্দিনীর মালিক হন। এই যুদ্ধ বন্দিনীর গর্ভজাত পুত্র মুহাম্মদ ইবনে হানিফাই হলেন পরবর্তীকালে ইসলামের ইতিহাসে সর্বজন পরিচিত ব্যক্তি।
(আরবী *********) এ থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সাহাবায়ে কেরাম যে অপরাধের কারণে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, তা কোন বিদ্রোহের অপরাধ ছিলনা বরং সে অপরাধ ছিল এইযে, এক ব্যক্তি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পরে নবুয়্যাতের দাবী করে এবং অন্য লোকেরা তার নবুয়্যাতের ওপর ঈমান আনে। রসূলুল্লাহর ইন্তেকালের অব্যবহিত পরেই এই পদক্ষেপ গৃহীত হয়। এর নেতৃত্ব করেন হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রা) এবং সাহাবাদের সমগ্র দলটি একযোগে তাঁর নেতৃত্বাধীনে এ কাজে অগ্রসর হন। সাহাবাদের ইজমার এর চাইতে সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত আর কি হতে পারে।
আলেম সমাজের ইজমা
শরীয়াতে সাহাবাদের ইজমার পর চতুর্থ পর্যায়ের সব চাইতে শক্তিশালী দলিল হলো সাহাবাগণের পরবর্তী কালের আলেম সমাজের ইজমা। এদিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায়, হিজরীর প্রথম শতাব্দী থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত প্রত্যেক যুগের এবং সমগ্র মুসলিম জাহানের প্রত্যেক এলাকার আলেম সমাজ হামেশাই এ ব্যাপারে একমত রয়েছেন যে,
“মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পরে কোনো ব্যক্তি নবী হতে পারে না। এবং তাঁর পর যে ব্যক্তি নবুয়্যাতের দাবী করবে এবং যে ব্যক্তি এই মিথ্যা দাবীকে মেনে নেবে, সে কাফের এবং মিল্লাতে ইসলামের মধ্যে তার স্থান নেই।”
এ ব্যাপারে আমি কতিপয় প্রমাণ পেশ করছি:
(১) ইমাম আবু হানিফার যুগে (৮০-১৫০হি) এক ব্যক্তি নবুয়্যাতের দাবী করে এবংবলে: “আমাকে সুযোগ দাও, আমি নবুয়্যাতের সংকেত চিহ্ন পেশ করব।”
একথা শুনে ইমাম সাহেব বলেন: যে ব্যক্তি এর কাছ থেকে নবুয়্যাতের কোনো সংকেত চিহ্ন তলব করবে সেও কাফের হয়ে যাবে। কেননা রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন: (******) আমার পর আর কোন নবী নেই।
(আরবী *********)
(২) আল্লামা ইবনে জারীর তাবারী (২২৪-৩১০ হি) তাঁর বিখ্যাত কোরআনের তাফসীরে (আরবী *******) আয়াতটির বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন:
(আরবী *******)
অর্থাৎ “যে নবুয়্যাতকে খতম করে দিয়েছে এবং তার ওপর মোহর লাগিয়ে দিয়েছে, কিয়ামত পর্যন্ত এর দরজা আর কারুর জন্য খুলবেনা।” (তাফসীরে ইবনে জারীর, দ্বাবিংশ খণ্ড, ১২ পৃষ্ঠা)
(৩) আল্লামা ইবনে হাজাম আন্দালুসী (৩৮৪-৪৫৬ হি) লিখেছেন: নিশ্চয়ই রসূলুল্লাহর (স) পর অহীর সিলসিলা খতম হয়ে গেছে। এর সপক্ষে যুক্তি এই যে, অহী আসে একমাত্র নবীর কাছে এবং মহান আল্লাহ বলেছেন, “মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারুর পিতা নয়। কিন্তু সে আল্লাহর রসূল এবং সর্বশেষ নবী।” (আল মুহাল্লা, প্রথম খণ্ড, ২৬ পৃষ্ঠা)।
(৪) ইমাম গাজ্জালী (৪৫০-৫০৫ হি) বলেন: “সমগ্র মুসলিম সমাজ এই বাক্য থেকে একযোগে এই অর্থ নিয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (স) তাঁর পরে কোন রসূল এবং নবী না আসার কথাটি স্পষ্ট করে ব্যক্ত করেছেন এবং এর কোনো বিশেষ অর্থ গ্রহণ অথবা বাক্যটিকে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে এবং টেনে-হিঁচড়ে এ থেকে কোনো দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণের সুযোগই এখানে নেই। অতঃপর যে ব্যক্তি টেনে-হিঁচড়ে এথেকে কোনো দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করবে, তার বক্তব্য হবে উদ্ভট ও নিছক কল্পনা প্রসূত এবং তার বক্তব্যের ভিত্তিতে তার ওপর কুফরীর ফতোয়া দেবার ব্যাপারে কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই। কেননা কোরআনে যে আয়াত সম্পর্কে সমগ্র মুসলিম সমাজ একযোগে এই মত পোষণ করেন যে, তার কোনো দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করা যেতে পারে না এবং টেনে-হিঁচড়ে অন্য কোনো অর্থও তা থেকে বের করা যেতে পারেনা, সে আয়াতকে সে মিথ্যা প্রমাণ করেছে।” (আল ইকতিসাদ ফিল ইতিকাদ, ১১৩ পৃষ্ঠা)
(৫) মুহিউদ সূন্নাহ বাগাবী (মৃত্যু ৫১০ হি) তাঁর তাফসীরে আলিমুত তানজীল-এ লিখেছেন: রসূলুল্লাহ্র (স) মাধ্যমে আল্লাহতায়ালা নবুয়্যাতের সিলসিলা খতম করেছেন। কাজেই তিনি সর্বশেষ নবী এবং ইবনে আব্বাস বলেন যে, আল্লাহতায়ালা এই আয়াতে ফায়সালা করে দিয়েছেন যে, মুহাম্মদের (স) পর কোন নবী নেই। (তৃতীয় খণ্ড, ১৫৮ পৃষ্ঠা)
(৬) আল্লাম জামাখশরী (৪৬৭-৫৩৮ হি) তাফসীরৈ কাশ্শাফে লিখেছেন: যদি তোমরা বল যে, রসূলুল্লাহ (স) শেষ নবী কেমন করে হলেন, কেননা হযরত ঈসা(আ) শেষ যুগে অবতীর্ণ হবেন, তাহলে আমি বলবোযে, রসূলুল্লাহর শেষ নবী হবার অর্থ হলো এই যে, তাঁর পরে আর কাউকে নবীর পদে প্রতিষ্ঠিত করা হবেনা। হযরত ঈসাকে (আ) রসূলুল্লাহর (স) পূর্বে নবী বানানো হয়েছে। অবতীর্ণ হবার পর তিনি রসূলুল্লাহর অনুসারী হবেন এবং তাঁর কেবলার দিকে মুখ করে নামায পড়বেন। অর্থাৎ তিনি হবেন রসূলুল্লাহর উম্মতের মধ্যে শামিল। (দ্বিতীয় খণ্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা)
(৭) কাজী ইয়অয (মৃত্যু: ৫৪৪ হি) লিখেছেন: যে ব্যক্তি নিজে নবুয়্যাতের দাবী করে অথবাএ কথাকে বৈধ মনে করে যে, যে কোনো ব্যক্তি নিজের প্রচেষ্টায় নবুয়্যাত হাসিল করতে পারে এবং অন্তত পরিশুদ্ধির মাধ্যমে নবীর পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে (যেমন কোনো কোনো দার্শনিক এবং বিকৃতমনা সূফী মনে করেন) এবং এভাবে যে ব্যক্তি নবুয়্যাতের দাবীকরেনা অথচ একথার দাবী জানায় যে, তার ওপর অহী নাযিল হয়, -এ ধরনের সমস্ত লোক কাফের এবং তারা রসূলুল্লাহর নবুয়্যাতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে। কেননা তিনি খবর দিয়েছেন যে, তিনি শেষ নবী এবং তাঁর পর কোনো নবী আসবে না এবং তিনি আল্লাহতায়ালার তরফ থেকে এ খবর পৌঁছিয়েছেন যে, তিনি নবুয়্যাতকে খতম করে দিয়েছেন এবং সমগ্র মানব জাতির জন্য তাঁকে পাঠানো হয়েছে। সমগ্র মুসলিম সমাজ এ ব্যাপারে একমত যে, এখানে কথাটির বাহ্যিক অর্থটিই গ্রহণীয় এবং এ ব্যাপারে একমত যে, এখানে কথাটির বাহ্যিক অর্থটিই গ্রহণীয় এবং এর দ্বিতীয় কোনো অর্থ গ্রহণ করার সুযোগই এখানে নেই। কাজেই উল্লিখিত দলগুলোর কাফের হওয়া সম্পর্কে কোরআন, হাদীস এবং ইজমার দৃষ্টিতে কোনো সন্দেহ নেই। (শিফা দ্বিতীয় খণ্ড, ২৭০-২৭১ পৃষ্ঠা)
(৮) আল্লামা শাহারিস্তানী (মৃত্যু: ৫৪৮ হি) তাঁর মশহুর কিতাব আল মিলাল ওয়ান নিহালে লিখেছেন: এবং যে এভাবেই বলে যে, “মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পরও কোনো নবী আসবে (হযরত ঈসা (আ) ছাড়া) তাহলে তার কাফের হওয়া সম্পার্কে যে কোন দু’জন ব্যক্তি মধ্যেই কোনো মতবিরোধ থাকতে পারে না। (তৃতীয় খণ্ড ২৪৯ পৃষ্ঠা)
(৯) ইমাম রাজী (৫৪৩-৬০৬ হি) তাঁর তাফসীরে কবীরে ‘খাতিমুন নাবিয়ীন’ শব্দের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন: এ বর্ণনায় খাতিমুন নামিয়ীন শব্দ এজন্য বলা হয়েছে যে, যে নবীর পর অন্য কোনো নবী আসবেন তিনি যদি উপদেশ এবং নির্দেশাবলীর ব্যাখ্যার ব্যাপারে কিছু অতৃপ্তি রেখে যান, তাহলে তাঁর পর আগমনকারী নবীতা পূর্ণ করতে পারেন। কিন্তু যার পর আর কোনো নবী আসবে না, তিনি নিজের উম্মতের ওপর খুব বেশী স্নেহশীল হন এবং তাদেরকে সুস্পষ্ট নেতৃত্ব দান করেন। কেননা তাঁর দৃষ্টান্ত এমন একটি পিতার ন্যায় যিনি জানেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর পুত্রের দ্বিতীয কোনো অভিভাবক এবং পৃষ্ঠপোষক থাকবে না। (ষষ্ঠ খণ্ড, ৫৮১ পৃষ্ঠা)
(১০) আল্লামা বায়জাবী (মৃত্যু: ৬৮৫ হি) তাঁর তাফসীরে আনওয়ারুত্ তানজীল-এ লিখেছেন: অর্থাৎ তিনিই শেষ নবী। তিনি নবীদের সিলসিলা খতম করে দিয়েছেন। অথবা তাঁর কারণেই নবীদের সিলসিলার ওপর মোহর লাগানো হয়েছে। এবং তাঁর পর হযরত ঈসার (আ) নাযীল হবার কারণে খতমে নবুয়্যাতের ওপর কোনো দোষ আসছে না। কেননা তিনি রসূলুল্লাহর (স) দ্বীনের মধ্যেই নাযিল হবেন। (চতুর্থ খণ্ড, ১৬৪ পৃষ্ঠা)
(১১) আল্লামা হাফিজ উদ্দীন নাসাফী (মৃত্যু: ৮১০ হি) তাঁর তাফসীরে মাদারেকুত তানজীল-এ লিখেছেন: এবং রসূলুল্লাহ (স) খাতিমুন নাবিয়ীন। অর্থাৎ তিনিই সর্বশেষ নবী। তাঁর পর আর কোনো ব্যক্তিকে নবী করা হবে না। হযরত ঈসা (আ) হলো এই যে, তাঁকে রসূলুল্লাহ্র পূর্বে নবীর পদে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। এবং পরে যখন তিনি নাযিল হবেন, তখন তিনি হবেন রসূলুল্লাহর শরীয়তের অনুসারী। অর্থাৎ তিনি হবেন রসূলুল্লাহর উম্মত। (৪৭১ পৃষ্ঠা)
(১২) আল্লামা আলাউদ্দীন বাগদাদী (মৃত্যু: ৭২৬ হি) তাঁর তাফসীরে ‘খাজিন’-এ লিখেছেন: (আরবী *****) অর্থাৎ আল্লাহর রসূলুল্লাহ্র নবুয়্যাত খতম করে দিয়েছেন। কাজেই তাঁর পরে আর কোনো নবুয়্যাত নেই এবং এ ব্যাপারে কেউ তাঁর অংশীদারও নয়।
(আরবী ********) অর্থাৎ আল্লাহ একথা জানেন যে, তাঁর পর আর কোনো নবী নেই’ (৩৭১-৪৭২ পৃষ্ঠা)
(১৩) আল্লামা ইবনে কাসীর (মৃত্যু: ৭৭৪ হি) তাঁর মশুহর তাফসীরে লিখেছেন: অতঃপর আলোচ্য আয়াত থেকে একথা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, যখন রসূলুল্লাহ্র পর কোনো নবী নেই, তখন অপর কোনো রসূলের প্রশ্নই উঠতে পারে না। কেননা রিসালাত একটা বিশেষ পদমর্যাদা এবং নবুয়্যাতের পদমর্যাদা এর চাইতে বেশী সাধারণধর্মী। প্রতেক রসূল নবী হন, কিন্তু প্রত্যেক নবী রসূল হন না। রসূলুল্লাহর পর যে ব্যক্তিই এই পদমর্যাদার দাবী করবে, সেই হবে মিথ্যাবাদী, প্রতারক, দাজ্জাল এবং গোমরাহ। যতোই সে প্রাকৃতিক নিয়মে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ও যাদুর ক্ষমতাসম্পন্ন হোক না কেন, তার দাবী মানবার নয়। কিয়ামত পর্যন্ত যেসব ব্যক্তি এই পদমর্যাদার দাবী করবে, তাদের প্রত্যেকেরই অবস্থা হবে এই ধরনের। (তৃতীয় খণ্ড, ৪৯৩-৪৯৪ পৃষ্ঠা)
(১৪) আল্লামা জালালুদ্দীন সিউতী (মৃত্যু: ৯১১ হি) তাঁর তাফসীরে জালালায়েন-এ লিখেছেন: ‘অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা জানেন যে রসূলুল্লাহর (স) পর আর কোনো নবী নেই। এবং হযরত ঈসা (আ) নাযীল হবার পর রসূরুল্লাহর শরীয়ত মোতাবেকই আমল করবেন।’ (৭৬৮ পৃষ্ঠা)
(১৫) আল্লামা ইবনে নাজীম (মৃত্যু: ৯৭০ হি) উসুলে ফিকাহর বিখ্যাত পুস্তক আল ইশবাহ ওয়ান নাজায়েরে ‘কিতাবুস সিয়ারের’ ‘বাবুর রুইয়ায়’ লিখেছেন: যদি কেউ একথা না মনে করে যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম শেষ নবী, তাহলে সে মুসলমান নয়। কেননা কথাগুলো জানা এবং স্বীকার করে নেয়া দ্বীনের অত্যধিক প্রয়োজনের মধ্যে শামিল। (১৭৯ পৃষ্ঠা)
(১৬) মুল্লা আলী কারী (মৃত্যু: ১০১৬ হি) ‘শারহে ফিকহে আকবর’-এ লিখেছেন: ‘আমাদের রসূলের (স) পর অন্য কোনো ব্যক্তির নবুয়্যাতের দাবী করা সর্ববাদীসম্মতভঅবে কুফর। (২০২ পৃষ্ঠা)
(১৭) শায়খ ইসমাইল হাক্কী (মৃত্যু: ১১৩৭ হি) তাফসীরে রুহুল বয়ান-এ উল্লিখিত ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেছেন: আলেম সমাজ ‘খাতাম’ শব্দটির তে-এর উপর জবর লাগিয়ে পড়েছেন, -এর অর্থ হয় খতম করবার যন্ত্র, যার সাহায্যে মোহর লাগানো হয়।
অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (স) সমস্ত নবীর শেষে এসেছেন এবং তাঁর সাহায্যে নবীদের সিলসিলার ওপর মোহর লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। ফারসীতে আমরা একে বলবো ‘মোহর পয়গম্বর’ অর্থাৎ তাঁর সাহায্যে নবুয়্যাতের দরজার মোহর লাগিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং পয়গম্বরদের সিলসিলা খতম করে দেয়া হয়েছে। অন্য পাঠকরাতো এর নীচে জের লাগিয়ে পড়েছেন ‘খাতিমুন নাবিয়ীন’। অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ ছিলেন মোহর দানকারী। অন্য কথায় বলা যাবে পয়গম্বরদের ওপর মোহরকারী। এভাবে এ শব্দার্থ ‘খাতাম’-এর সমার্থক হয়ে দাঁড়াবে। তাহলে রসূলুল্লাহর (স) পর তাঁর উম্মতের আলেম সমাজ তাঁর কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাবেনএকমাত্র তাঁর প্রতিনিধিত্ব। তাঁর ইন্তেকালের সাথে সাথেই নবুয়্যাতের উত্তরাধিকারেরও পরিসমাপ্তি ঘটেছে এবং তাঁর পরে হযরত ঈসার (আ) নাযিল হবার ব্যাপারটি তাঁর নবুয়্যাতকে ত্রুটিযুক্ত করবেনা। কেননা খাতিমুন নাবিয়ীন হবার অর্থ হলো এই যে, তাঁর পর আর কাউকে নবী বানানো হবেনা এবং হযরত ঈসাকে (আ) তাঁদের পূর্বেই নবী বানানো হয়েছে। কাজেই তিনি রসূলুল্লাহ্র অনুসারীর মধ্যে শামিল হবেন, রসূলুল্লাহর কিবলার দিকে মুখ করে নামায পড়বেনএবং তাঁরই উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হবেন। তখন হযরত ঈসার (আ) নিকট অহী নাযীল হবেনা এবং তিনি কোনোনতুন আহকামও জারি করবনে না, বরং তিনি হবেন রসূলুল্লাহর প্রতিনিধি। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এ ব্যাপারে একমত যে, আমাদের নবীর পর আর কোনো নবী নেই। কেননা আল্লাহতায়ালা বলেছেন: মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম শেষ নবী। এবং রসূলুল্লাহ বলেছেন: আমার পরে কোনো নবী নেই। কাজেই এখনযে বলবে যে মুহাম্মদ (স) এর পর নবী আছে, তাকে কাফের বলা হবে। কেননা সে কোরআনকে অস্বীকার করেছে এবং অনুরূপভবেসেই ব্যক্তিকেও কাফের বলা হবে যে এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করবে। কেননা সুস্পষ্ট যুক্তি প্রমাণের পর হক বাতিল থেকে পৃথক হয়ে গেছে। এবং যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (স)-এর পর নবুয়্যাতের দাবী করবে, তার দাবী বাতিল হয়ে যাবে। (দ্বাবিংশ খণ্ড, ১৮৮ পৃষ্ঠা)
(১৮) শাহানশাহ আওরঙ্গজেব আলমগীরের নির্দেশে বার’শ হিজরীতে পাক-ভারতের বিশিষ্ট আলেমগণ সম্মিলিতভাবে ‘ফতোয়া আলমগিরী’ নামে যে কিতাবটি লিপিবদ্ধ করেন তাতে উল্লিখিত হয়েছে: যদি কেউ মনে করে যে, মুহাম্মদ (স) শেষ নবী নয়, তাহলেসে মুসলমান নয় এবং যদি সে বলে যে, সে আল্লাহর রসূল অথবা পয়গম্বর, তাহলে তার ওপর কুফরীর ফতোয়া দেয়া হবে। (দ্বিতীয়খণ্ড, ২৬৩ পৃষ্ঠা)
(১৯) আল্লামা শওকানী (মৃত্যু: ১২৫৫ হি) তাঁর তাফসীর ফাতহুল কাদীরে লিখেছেন: সমগ্র মুসলিম সমাজ ‘খাতিম’ শব্দটির তে-এর নীচে জের লাগিয়ে পড়েছেন এবং একমাত্র আসে জবরের সাথে পড়েছেন। প্রথমটা অর্থ হলো এই যে, রসূলুল্লাহ সমস্ত পয়গম্বরকে খতম করেছেন অর্থাৎ তিনি সবার শেষে এসেছেন এবং দ্বিতীয়টির অর্থ হলো এই যে, তিনি সমস্ত পয়গম্বরদের জন্য মোহর স্বরূপ্ এবং এর সাহায্যে নবীদের সিলসিলা মোহর এঁটে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ফলে তাঁদের দলীটর সর্বাঙ্গসুন্দর হয়েছে। (চতুর্থ খণ্ড, ২৭৫ পৃষ্ঠা)
(২০) আল্লামা আলুসি (মৃত্যু: ১২৮০ হি) তাফসীরে রুহুল মায়ানীতে লিখেছেন: নবী শব্দটি রসূলের চাইতে বেশী সাধারণ অর্থব্যঞ্জক। কাজেই রাসূলের খাতিমুন নাবিয়ীন হবার অর্থ হলো এই যে, তিনি খাতিমুল মুরসালীনও। তিনি শেষ নবী এবং শেষ রসূল-একথার অর্থ হলো এই যে, দুনিয়ায় তাঁর নবুয়্যাতের গুণে গুণান্বিত হবার পরেই মানুষ এবং জিনের মধ্য থেকে এ গুণটি চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। (দ্বাবিংশ খণ্ড, ৩২ পৃষ্ঠা)
রসূলুল্লাহর পর যে ব্যক্তি নবুয়্যাতের অহীর দাবী করবে, তাকে কাফের বলে গণ্য করা হবে। এ ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে দ্বিমতের অবকাশ নেই। (দ্বাবিংশ খণ্ড, ৩৮ পৃষ্ঠা)
“রসূলুল্লাহ শেষ নবী-একথাটি কোরআন দ্ব্যার্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছে, রসূলুল্লাহর সুন্নাত এটিকে সুস্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করেছে এবং সমগ্র মুসলিম সমাজ এর ওপর আমল করেছে। কাজেই যে ব্যক্তি এর বিরোধী কোনো দাবী করবে, তাকে কাফের বলে গণ্য করা হবে।” (দ্বাবিংশ খণ্ড, ৩৯ পৃষ্ঠা)
বাংলা পাক-ভারত উপমহাদেশ থেকে মররোক্ত ও আন্দালুসিয়া এবং তুর্কী থেকে ইয়েমেন পর্যন্ত মুসলিম জাহানের শ্রেষ্ঠ আলেম, ফকীহ, মুহাদ্দিস এবং তাফসীরকারগণের ব্যাখ্যা এবং মতামত আমি এখানে উল্লেখ করলাম। তাঁদের নামের সাথে সাথে তাঁদের জন্ম এবং মৃত্যু তারিখও উল্লেখ করেছি। এ থেকেই ধারণা করা যাবে যে, হিজরীর প্রথম শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইসলামের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ আলেমগণ এর মধ্যে শামিল আছেন। হিজরীর চতুর্দশ শতাব্দীর আলেম সমাজের মতামতও আমি এখানে উল্লেখ করতে পারতাম, কিন্তু ইচ্ছা করেই তাঁদেরকে ছেড়ে দিয়েছি। কেননা তাঁরা মীর্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর সমসাময়িক। এবং হয়তো অনেকে বলতে পারেন যে, মীর্জা সাহেবের বিরোধিতার মনোভাব নিয়েই তাঁরা খতমে নবুয়্যাতের এই অর্থ বিবৃত করেছেন। এজন্য মীর্জা সাহেবের পূর্ববর্তী যুগের আলেম সমাজের মতামতের উদ্ধৃতিই এখানে পেশ করেছি- যেহেতু মীর্জা সাহেবের সাথে তাঁদের বিরোধের প্রশ্নই উঠতে পারে না। এইসব মতামত থেকে একথা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, হিজরীর প্রথম শতাব্দী থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত সমগ্র মুসলিমজাহান একযোগে খাতিমুন নাবিয়ীন শব্দের অর্থ নিয়েছে শেষ নবী। প্রত্যেক যুগের মুসলমানই এই একই আকীদা পোষণ করেছেন যে, রসূলুল্লাহর পর নবুয়্যাতের দরজা চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে। একথা তাঁরা একযোগে স্বীকার করে নিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পর নবী অথবা রসূল হবার দাবী করেএবং যে তার দাবীকে মেনে নেয়, সে কাফের হয়ে যায়, এ ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে কোনো যুগে তুচ্ছতম মতবিরোধেরও সৃষ্টি হয়নি। কাজেই এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেক বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিই ফায়সালা করতে পারেন যে, ‘খাতিমুন নাবিয়ীন’ শব্দের যে অর্থ আরবী অভিধান থেকে প্রমাণিত হয়, কোরআনের আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনা থেকে যে অর্থ প্রতীয়মান হয়, রসূলুল্লাহ (স) নিজেই যা ব্যাখ্যা করেছেন, সাহাবায়ে কেরাম যে সম্পর্কে মতৈক্য পোষণ করেছেন এবং সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত সমগ্র মুসলিমসমাজ একযোগে দ্ব্যার্থহীনভাবে যা স্বীকার করে আসছেন, তার বিপক্ষে দ্বিতীয় কোনো অর্থ গ্রহণ অর্থাৎ কোনো নতুন দাবীদারের জন্য নবুয়্যাতের দরজা উন্মুক্ত করার অবকাশ ও সুযোগ থাকে কি? এবং এই ধরনের লোকদেরকে কেমন করে মুসলমান বলে স্বীকার করা যায়, যারা নবুয়্যাতের দরজা উন্মুক্ত করার নিছক ধারণাই প্রকাশ করেনি বরং ঐ দরজা দিয়ে এক ব্যক্তি নবুয়্যাদের দালানে প্রবেশ করেছে এবং তারা তার ‘নবুয়্যাতের’ ওপর ঈমান পর্যন্ত এনেছে?
এ ব্যাপরে তিনটি কথা বিবেচনা করতে হবে।
আমাদের ঈমানের সংগে খোদার কি কোনো শত্রুতা আছে?
প্রথম কথা হলো এই যে, নবুয়্যাতের ব্যাপারটি বড়ই গুরুত্বপূর্ণ। কোরআনের দৃষ্টিতে এ বিষয়টি ইসলামের বুনিয়াদী আকিদার অন্তর্ভুক্ত, এটি স্বীকার করার বা না করার ওপর মানুষের ঈমান ও কুফরী নির্ভর করে। যদি কোনো ব্যক্তি নবী থাকেন এবং লোকেরা তাঁকে না মানে, তাহলে তারা কাফের হয়ে যায়। আবার কোনো ব্যক্তি নবী না হওয়া সত্ত্বেও যারা তাকে নবী বলে স্বীকার করে, তারাও কাফের হয়ে যায়। এ ধরনের জটিল পরিস্থিতিতে আল্লাহ তায়ালার নিকট থেকে যে কোনো প্রকার অসতর্কতার আশা করা যায় না। যদি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পর কোনো নবী আসার কথা থাকতো তাহলে আল্লাহ নিজেই কোরআনে স্পষ্ট এবং দ্ব্যার্থহীন ভাষায় তা ব্যক্ত করতেন, রসূলুল্লাহর মাধ্যমে প্রকাশ্যভাবে তা ঘোষণা করতেন এবং রসূলুল্লাহ কখনো এ দুনিয়া থেকে তাশরীফ নিয়ে যেতেন না; যতক্ষণ না তিনি সমগ্র উম্মতকে এ ব্যাপারে পুরোপুরি অবগত করতেন যে, তাঁর পর আরো নবী আসবেন এবং আমরা সবাই তাঁদেরকে মেনে নিতে বাধ্য থাকবো। রসূলুল্লাহর পর নবুয়্যাতের দরজা উন্মুক্ত থাকবে এবং এই দরজা দিয়ে কোনো নবী প্রবেশ করবে, যার ওপর ঈমান না আনলে আমরা মুসলমান থাকতে পারি না অথচ আমাদেরকে এ সম্পর্কে শুধু বেখবরই রাখা হয়নি বরং বিপরীতপক্ষে আল্লাহ এবং তাঁর রসূল একযোগে এমন সব কথা বলেছৈন, যার ফলে তের’শ বছর পর্যন্ত সমস্ত উম্মত একথা মনে করেছিলো এবং আজও মনে করে যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পর আর কোনো নবী আসবেন না- আমাদের সাথে আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের এ ধরনের ব্যবহার কেন? আমাদের দ্বীন এবং ঈমানের বিরুদ্ধে আল্লাহ এবংতাঁর রসূলের তো কোনো শত্রুতা নেই!
তর্কের খাতিরে যদি একথা মেনে নেয়া যায় যে, নবুয়্যাতের দরজা উন্মুক্ত আছে এবং কোনোনবী আসার পর আমরা যদি নির্ভয়ে এবং নিশ্চিন্তে তাঁকে অস্বীকার করে বসি, তাহলে ভয় থাকতে পারে একমাত্র আল্লাহর দরবারে জিজ্ঞাসাবাদের! কিন্তু কিয়ামতের দিনতিনি আমাদের নিকট থেকে এ সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করলে, আমরা সোজাসুজি উল্লিখিত রেকর্ডগুলো তাঁর আদালতে পেশকরবো। এ থেকে অন্তত প্রমাণহয়েযাবে যে, (মায়াযাল্লাহ) আল্লাহ্র কিতাব এবং রসূলের সুন্নাতই আমাদেরকে এই কুফরীর মধ্যে নিক্ষেপ করছে! আমরা নির্ভয়ে বলতে পারি যে, এইসব রেকর্ড দেখার পর কোনো নতুন নবীর ওপর ঈমান না আনার জন্য আল্লাহ আমাদেরকে শাস্তি দেবেন না। কিন্তু যদি সত্যি সত্যি নবুয়্যাতের দরজাবন্ধ গিয়ে থাকে এবং কোনো নবুন নবী যদি না আসতে পারে এবং এইসব সত্ত্বেও কেউ কোনো নবুয়্যাতের দাবীদারদের ওপর যদি ঈমান আনে, তাহলে তার চিন্তা করা উচিত যে, এই কুফরীর অপরাধ থেকে বাঁচার জন্য সে আল্লাহর দরবারে এমনকি রেকর্ড পেশ করতে পারবে, যার ফলে সে মুক্তি লাভের আশা করতে পারে। আদালতে হাযির হবার পূর্বে তার নিজের জবাবদিহির জন্য সংগৃহীত দলিল প্রমাণগুলো এখানেই বিশ্লেষণ করে নেয়া উচিত। এবং আমরা যেসব দলিল-প্রমাণ পেশ করেছি, তার পরিপ্রেক্ষিতে তার বিচার করা উচিত যে, নিজের জন্য যে সাফাইয়ের ওপর নির্ভল করে সে একাজ করছে, কোনো বুদ্ধিশান ব্যক্তি কি এর ওপর নির্ভর করে কুফরীর শাস্তি ভোগ করার বিপদকে স্বাগতম জানাতে পারে?
এখন নবীর প্রয়োজনটা কেন?
দ্বিতীয় কথা হলো এই যে, ইবাদাত এবংনেক কাজে তরক্কী করে কোনো ব্যক্তি নিজের মধ্যে নবুয়্যাতের গুণ পয়দা করতে পারে না। নবুয়্যাতের যোগ্যতা কোনো অর্জন করার জিনিস নয়। কোনো বিরাট খেদমতের পুরস্কার স্বরূপ মানুষকে নবুয়্যাত দান করা হয় না। বরং বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে আল্লাহতায়ালা কোনো বিশেষ ব্যক্তিকে এই মর্যাদা দান করে থাকেন। এই প্রয়োজনের সময় যখন উপস্থিত হয় তখনই আল্লাহতায়ালা এক ব্যক্তিকে এই মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন এবং যখন প্রয়োজন পড়ে না অথবা থাকে না, তখন খামাখা আল্লাহতায়ালা এক ব্যক্তিকে এই মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন এবং যখন প্রয়োজন পড়ে না অথবা থাকে না, তখন খামাখা আল্লাহতায়ালা নবীর পর নবী প্রেরণ করতে থাকেন না। কোরআন মজিদ থেকে যখন আমরা একথা জানবার চেষ্টা করি যে, কোন্ পরিস্থিতিতে নবী প্রেরণের প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন সেখানে এ ধরনের চারটি অবস্থার সন্ধান পাওয়া যায়:
** কোনো বিশেষ জাতির মধ্যে নবী প্রেরণের প্রয়োজন এজন্য দেখা যায় যে, তাদের মধ্যে ইতিপূর্বে কোন নবী আসেননি এবং অন্য কোনো জাতির মধ্যে প্রেরিত নবীর পয়গামও তাদের নিকট পৌঁছেনি।
** নবী পাঠাবার প্রয়োজন এজন্য দেখা যায় যে, সংশ্লিষ্ট জাতি ইতিপূর্বৈ প্রেরিত নবীদের শিক্ষা ভুলে যায় অথবা তা বিকৃত হয়ে যায় এবং তাঁদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ অসম্ভব হয়ে পড়ে।
**ইতিপূর্বে প্রেরিত নবীদের মাধ্যমে জনগণের শিক্ষা পূর্ণতা লাভ করতে পারেনি এবং দ্বীনের পূর্ণতার জন্য অতিরিক্ত নবীর প্রয়োজন হয়।
** কোনো নবীল সংগে তাঁর সাহায্য-সহযোগিতার জন্য আর একজন নবীর প্রয়োজন হয়।
উপরের আলোচনা থেকে একথা পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, রসূলুল্লাহ্র পর কোনো নবীর প্রয়োজন নেই।
কোরআন নিজেই বলছে যে, রসূলুল্লাহকে সমগ্র দুনিয়ার জন্য হেদায়াতকারী হিসেবে পাঠানো হয়েছে। দুনিয়ার সাংস্কৃতিক ইতহিাস একথা বলে যে, তাঁর নবুয়্যাত প্রাপ্তির পর থেকে সমগ্র দুনিয়ায় এমন অবস্থা বিরাজ করছে, যাতে করে তাঁর দাওয়াত সব সময় দুনিয়ার সকল জাতির মধ্যে পৌঁছতে পারে। এর পরেও প্রত্যেক জাতির মধ্যে পৃথক পৃথক পয়গাম্বর প্রেরণের কোনো প্রয়োজন থাকে না।
কোরআন একথাও বলে এবং একই সংগে হাদীস এবং সীরাতের যাবতীয় বর্ণনাও একথার সাক্ষ্যবহ যে, রসূলুল্লাহর শিক্ষা পুরোপুরি নির্ভুল এবং নির্ভেজাল আকারে সংরক্ষিত রয়েছে। এর মধ্যে কোনো প্রকার বিকৃতি বা রদবদল হয়নি। তিনি যে কোরআন এনেছিলেন, তার মধ্যে আজ পর্যন্ত একটি শব্দেরও কম-বেশী হয়নি। এবং কিয়ামত পর্যন্তও তা হতে পারে না। নিজের কথা ও কর্মের মাধ্যমে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাও আজ আমরা এমনভাবে পেয়ে যাচ্ছি, যেন আমরা তাঁরই যুগে বাস করছি। কাজেই দ্বিতীয় প্রয়োজনটাও খতম হয়ে গেছে।
আবার কোরআন মজীদ স্পষ্টভাষায় একথাও ব্যক্ত করে যে, রসূলুল্লাহর মাধ্যমে খোদার দ্বীনকে পূর্ণতা দান করা হয়েছে। কাজেই দ্বীনের পূর্ণতার জন্যও এখন আর কোনো নবীর প্রয়োজন নেই।
এখন বাকি থাকে চতুর্থ প্রয়োজন। এ সম্পর্কে আমার বক্তব্য হলো এই যে, এজন্য যদি কোনো নবীর প্রয়োজন হতো তাহলে রসূলুল্লাহর যুগে তাঁর সংগেই তাকে প্রেরণ করা হতো।কিন্তু একথা সবাই জানেন যে, এমনকোনো নবী রসূলুল্লাহর যুগে প্রেরণ করা হয়নি কাজেই এ কারণটা বাতিল হয়ে গেছে।
এখন আমরা জানতে চাই যে, রসূলুল্লাহর পর আর একজন নতুন নবী আসবার পঞ্চম কারণটা কি? যদি কেউ বলেন যে, সমগ্র উম্মত বিগড়ে গেছে, কাজেই তাদের সংস্কারের জন্য আর একজন নতুন নবীর প্রয়োজন, তাহলে তাকে আমরা জিজ্ঞেস করবো: নিছক সংস্কারের জন্য দুনিয়ায় আজ পর্যন্ত কি কোন নবী এসেছে যে শুধু এই উদ্দেশ্যেই আর একজন নতুন নবীর আবির্ভাব হলো? অহী নাযিল করার জন্যই তো নবী প্রেরণ করা হয়। কেননা নবীর নিকটেই অহী নাযিল করা হয়। আর অহীর প্রয়োজন পড়ে কোনো নতুন পয়গাম দেবার অথবা পূর্ববর্তী পয়গামকে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য। আল্লাহর কোরআন এবং রসূলুল্লাহর সুন্নাত সংরক্ষিত হয়ে যাবার পর যখন আল্লাহর দ্বীন পরিপূর্ণ হয়েগেছে এবং অহীর সমস্ত সম্ভাব্য প্রয়োজন খতম হয়ে গেছে, তখন সংস্কারের জন্য একমাত্র সংস্কারকে প্রয়োজনই বাকী রয়ে গেছে- নবীর প্রয়োজন নয়।
নতুন নবুয়্যাত বর্তমানে মুসলমানদের জন্য রহমত নয়, লা’নতের শামিল
তৃতীয় কথা হলো এই যে, যখনই কোনো জাতির মধ্যে নবীর আগমন হবে, তখনই সেখানেই প্রশ্ন উঠবে কুফর ও ঈমানের। যারা ঐ নবীকে স্বীকার করে নেবে, তারা এক উম্মতভুক্ত হবে এবং যারা তাকে অস্বীকার করবে তারা অবশ্যই একটি পৃথক উম্মতের শামিল হবে। এই দুই উম্মতের মতবিরোধ কোনোআংশিক মতবিরোধের পর্যায়ে নেমে আসবে, যার ফলে তাদের একটি দল যতদিন না নিজেদের আকীদা-বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করবে, ততদিন পর্যন্ত তারা দুই দল কখনো একত্রিত হতে পারবে না। এ ছাড়াও কার্যত তাদের প্রত্যেকের জন্য হেদায়াত এবং আইনের উৎস হবে বিভিন্ন। কেননা একটি দল তাদের নিজেদের নবীর অহী এবং সুন্নাত থেকে আইন প্রণয়ন করবে এবং দ্বিতীয়দলটি এদু’টিকে তাদের আইনের উৎস হিসেবে মেনে নিতেই প্রথমত অস্বীকার করবে। কাজেই তাদের উভয়ের সম্মিলনে একটি সমাজ সৃষ্টি কখনো সম্ভব হবেনা।
এই প্রোজ্জ্বল সত্যগুলো পর্যবেক্ষণ করার পর যে কোনো ব্যক্তি স্পষ্ট বুঝতে পারবেন যে, ‘খত্মে নবুয়্যাত’ মুসলিম জাতির জন্য আল্লাহ তায়ালার একটি বিরাট রহমত স্বরূপ। এর বদৌলতেই সমগ্র মুসলিম জাতি একটি চিরন্তন বিশ্বব্যাপী ভ্রাতৃত্বে শামিল হতে পেরেছে। এ জিনিসটা মুসলমানদেরকে এখন সব মৌলিক মতবিরোধ থেকে রক্ষা করেছে, যা তাদের মধ্যে চিরন্তন বিচ্ছেদের বীজ পবন করতো। কাজেই যেব্যক্তি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে হেদায়াত দানকারী এবং নেতা বলে স্বীকার করে এবং তিনি যে শিক্ষা দিয়েছেন তাছাড়া অন্য কোন হেদায়াত উৎসের দিকে ঝুঁকে পড়তে চায় না, সে আজ এই ভ্রাতৃত্বের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে। নবুয়্যাতের দরজা বন্ধ না হয়ে গেলে মুসলিম জাতি কখনো এই ঐক্যের সন্ধান পেতোনা। কেননা প্রত্যেক নবীর আগমনের পর এ ঐক্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতো।
মানুষের বিবেক-বুদ্ধিও একথাই সমর্থন করে যে, একটি বিশ্বজনীন এবং পরিপূর্ণ দ্বীন দিয়ে দেবার এবং তাকে সকল প্রকার বিকৃতি ও রদবদল থেকে সংরক্ষিত করার পর নবুয়্যাতের দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়াই উচিত। এর ফলে সম্মিলিতভাবে এই শেষ নবীর আগমন করে সমগ্র দুনিয়ার মুসলমান চিরকালের জন্য একই উম্মতের অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারবে এবং বিনা প্রয়োজনে নতুন নতুন নবীদের আগমনে উম্মতের মধ্যে বারবার বিভেদ সৃষ্টি হতে পারবে না। নবী ‘যিল্লী’ হোক অথবা ‘বুরুজী ওম্মতওয়ালা শরীয়ত ওয়ালা এবং কিতাবওয়ালা- যে কোন অবস্থায়ই যিনি নবী হবেন এবং খোদার পক্ষহতে তাঁকে প্রেরণ করা হবে, তাঁর আগমনের অবশ্যম্ভাবী ফল দাঁড়াবে এই যে, তাকে যারা মেনে নেবে, তারা হবে একটি উম্মত আর যারা মানবেনা তারা কাফের বলে গণ্য হবে। যখন নবী প্রেরণের সত্যিকার প্রয়োজন দেখা যায়, তখন-শুধুমাত্র তখনই-এই বিভেদ অবশ্যম্ভাবী হয়। কিন্তু যখন তার আগমনের কোন প্রয়োজন থাকেনা, তখন খোদার হিকমত এবংতাঁর রহমতের নিকট কোনক্রমেই আশা করা যায়না যে, তিনি নিজের বান্দাদেরকে খামাখা কুফর ও ঈমানের সংঘর্ষে লিপ্ত করবেন এবং তাদেরকে সম্মিলিতভাবে একটি উম্মতভুক্ত হবার সুযোগ দেবেননা। কাজেই কোরআন, সুন্নাহ এবং ইজমা থেকে যা কিছু প্রমাণিত হয়, মানুষের বিবেক-বুদ্ধিও তাকে নির্ভুল বলে স্বীকার করে এবং তাথেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, বর্তমান নবুয়্যঅতের দরজা বন্ধ থাকাই উচিত।
‘প্রতিশ্রুত মসীহ’ এর তাৎপর্য
নতুন নবুয়্যাতের দিকে আহ্বানকারীরা সাধারণত অজ্ঞ মুসলমানদের বলে থাকে যে, হাদীসে ‘প্রতিশ্রুত মসীহ’ এর আগমনের খবর দেয়া হয়েছে। আর মসীহ নবী ছিলেন। কাজেই তাঁর আগমনের ফলে খতমে নবুয়্যাত কোনো দিক দিয়ে প্রভাবিত হচ্ছেনা। বরং খত্মে নবুয়্যাত এবং ‘প্রতিশ্রুত মসীহ’ এর আগমন দুটোই সমপর্যায়ে সত্য।
এই প্রসংগে তারা আরো বলে যে, হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম ‘প্রতিশ্রুত মসীহ’ নন। তাঁর মৃত্যু হয়েছে। হাদীসেযাঁর আগমনের খবর দেয়া হয়েছে তিনি হলেন ‘মসীলে মসীহ’ –অর্থাৎ হযরত ঈসার অনুরূপ একজন মসীহ। এবং তিনি ‘অমুক’ ব্যক্তি যিনি সম্প্রতি আগমন করেছেন। তাঁকে মেনে নিলে খত্মে নবয়্যাত বিশ্বাসের বিরোধিতা করা হয়না।
এই প্রতারণার পর্দা ভেদ করবার জন্য আমি এখানে হাদীসের নির্ভরযোগ্য কিতাবগুলো থেকে এই ব্যাপারে উল্লিখিত প্রমাণ্য হাদীস সমূহ সূত্রসহ নকল করছি। এই হাদীসগুলো প্রত্যক্ষ করে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই বুঝতে পারবেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কি বলেছিলেন এবং আজ তাকে কিভাবে চিত্রিত করা হচ্ছে।
হযরত ঈসা (আ) নুযুল সম্পর্কিত হাদীস
(আরবী **********)
(১) হযরত আবু হোরায় (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন: সেই মহান সত্তার কছম যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে ইবনে মরিয়ম ন্যায়বিচারক শাসকরূপে অবতীর্ণ হবেন। অতঃপর তিনি ক্রশ ভেঙ্গে ফেলবেন, শূকর হত্যা করবেন। [ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলার এবং শুকর হত্যা করার অর্থ হলো এই যে, একটি পৃথক ধর্ম হিসেবে ধর্মের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে। ঈসায়ী ধর্মের সমগ্র কাঠামো এই আকীদার ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে যে, আল্লাহ তাঁর একমাত্র পুত্রকে (অর্থাৎ হযরত ঈসাকে (আ) ক্রশে বিদ্ধ কলে ‘লানত’ পূর্ণ মৃত্যু দান করেছেন। এবং এতেই সমস্ত মানুষেরগোনাহর কাফ্ফারা হয়ে গেছে। অন্যান্য নবীদের উম্মতের সংগে ঈসায়ীদের পার্থক্য হলো এই যে, এরা শুধু আকীদাটুকু গ্রহণ করেছে, অতঃপর খোদার সমস্ত শরীয়ত নাকচ করে দিয়েছে। এমনকি শুকরকেও এরা হালাল করে নিয়েছে- যা সকল নবীর শরীয়তে হারাম।
কাজেই হযরত ঈসা (আ) নিজে এসে যখন বলবেন, আমি খোদার পুত্র নই, আমাকে ক্রুশে বিদ্ধ করে হত্যা করা হয়নিএবং আমি কারুর গোনাহর কাফফারা হইনি, তখন ঈসায়ী ধর্মবিশ্বাসের বুনিয়াদ সমূলে উৎপাটিত হবে। অনুরূপভাবে যখন তিনি বলবেন, আমার অনুসারীদের জন্র আমি শুকুর হালাল করিনি এবং তাদেরকে শরীয়তের বিধিনিষেধ থেকে মুক্তিও দেইনি, তখন ঈসায়ী ধর্মের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যও নির্মূল হয়ে যাবে।
অন্য কথায় বলা যায়, তখন ধর্মের বৈষম্য ঘুচিয়ে মানুষ একমাত্র দ্বীন ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হবে। এর ফলে আর যুদ্ধের প্রয়োজন হবেনা এবং কারুর জিজিয়াও আদায় করা হবেনা। পরবর্তী ৫ এবং ১৫ নং হাদীস একথাই প্রমাণ করেছে।] এবং যুদ্ধ খতম করে দেবেন (বর্ণনান্তরে যুদ্ধের পরিবর্তে ‘জিজিয়া’ শব্দটি উল্লিখিত হয়েছে অর্থাৎ জিজিয়া খতম করে দেবেন)। তখন ধনের পরিমাণ এতো বৃদ্ধি পাবে যে, তা গ্রহণ করার লোক থাকবে না এবং (অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছবে যে, মানুষখোদার জন্য) একটি সিজদা করে নেয়াটাকেই দুনিয়া এবং দুনিয়ার বস্তুর চাইতে বেশী মূল্যবান মনে করবে।
(২) অন্য একটি হাদীসে হযরত আবু হোরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে (আরবী **********)
ঈসা ইবনে মরিয়ম অবতীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না....” এবং এর পর বলা হয়েছে তা উপরোল্লিখিত হাদীসের সংগে পুরোপুরি সামঞ্জস্যশীল।– (বুখারী, কিতাবুল মাজালেম, বাবু কাসরিক সালিব, ইবনে মাজা, কিতাবুল ফিতান, বাবু ফিতনাতিদ দাজ্জাল)
(আরবী **********)
(৩) হযরত আবু হোরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (স) বলেন, কেমনহবে তোমরা যখন তোমাদের মধ্যে ইবনে মরিয়ম অবতীর্ণ হবেন এবং তোমাদের ইমাম নিজেদের মধ্য থেকেই নিযুক্ত হবেন? [অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ) নামাজে ইমামতি করবেননা। মুসলমানদের পূর্ব নিযুক্ত ইমামের পেছনে তিনি এক্তেদা করবেন।]
(আরবী **********)
(৪) হযরত আবু হোরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেন: ঈসাইবনে মরিয়ম অবতীর্ণ হবেন। অতঃপর তিনি শুকর হত্যা করবেন। ক্রুশ ধ্বংস করবেন। তাঁর জন্য একাধিক নামাজ এক ওয়াক্তে পড়া হবে। তিনি এতো ধন বিতরণ করবেন যে, অবশেষে তা গ্রহীতা পাওয়া যাবে না। তিনি খিরাজ মওকুফ করে দেবেন। রওহা [রওহা মদীনা থেকে ২৫ মাইল দূরে একটি স্থানের নাম।] নামক স্থানে অবস্থান করেতিনি সেখান থেকে হজ্ব অথবা ওমরাহ করবেন অথবা দুটোই করবেন। (রসূলুল্লাহ এর মধ্যে কোন্টি বলেছিলেন- এ ব্যাপারে বর্ণনাকারীর সন্দেহ রয়ে গেছে)।
(আরবী **********)
(৫) হযরত আবু হোরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, দাজ্জালের নির্গমন বর্ণনার পর রসূলুল্লাহ বলেন: ইত্যবসরে যখন মুসলমানরা তাঁর সংগে লড়াইয়ের প্রস্তুতি করতে থাকবে, কাতারবন্দি করতে থাকবে এবং নামাজের জন্য ‘একমত’ পাঠ করা শেষ হবে, তখন ঈসা ইবনে মরিয়ম অবতীর্ণ হবেন এবং নামাজে মুসলমানদের ইমামতি করবেন। খোদার দুশমন দাজ্জালতাঁকে দেখতেই এমনভাবে গলিত হতে থাকবে যেমন পানিতে লবণ গলে যায়। যদি ঈসা (আ) তাকে এই অবস্থায় পরিত্যাগ করেন, তাহলেও সে বিগলিত হয়ে মৃত্যু বরণ করবে। কিন্তু আল্লাহতায়ালা তাকে হযরত ঈসার (আ) হাতে কতল করবেন। তিনি দাজ্জালের রক্তে রঞ্জিত নিজের বর্শাফলক মুসলমানদের দেখাবেন।
(আরবী **********)
(৬) হযরত আবু হোরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন: আমার এবং তাঁর (অর্থাৎ হযরত ঈসার) মাঝখানে আর কোনো নবী নেই। এবং তিনি অবতীর্ণ হবেন। তাঁকে দেখা মাত্রই তোমরা চিনে নিয়ো। তিনি মাঝারি ধরনের লম্বা হবেন। বর্ণ লাল সাদায় মেশানো। পরনে দু’টো হলুদ রঙের কাপড়। তাঁর মাথার চুল থেকে মনে হবে এই বুঝি পানি টপকে পড়লো। অথচ তা মোটেই সিক্ত হবেনা। তিনি ইসলামের জন্য মানুষের সংগে যুদ্ধ করবেন। ক্রুশ ভেঙ্গে টুক্রো টুক্রো করবেন। শূকর হত্যা করবনে। জিজিয়া কর রহিত করবেন। তাঁর জামানায় আল্লাহ সমস্ত মিল্লাতকেই নির্মূল করবেন। তিনি মসীহ দাজ্জালকে হত্যা করবেন এবং দুনিয়া চল্লিশ বছর অবস্থান করবেন। অতঃপর তাঁর ইন্তেকাল হবে এবং মুসলমানরা তাঁর জানাযায় নামাজ পড়বে।
(আরবী **********)
(৭) হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহকে (স) বলতে শুনেছি:... অতঃপর ঈসা ইবনে মরিয়ম অবতীর্ণ হবেন। মুসলমানদের আমীর তাঁকে বলবেন, আসুন, আপনি নামাজ পড়ান। কিন্তু তিনি বলবেন, না, তোমরা নিজেরাই একে অপরের আমীর। [অর্থাৎ তোমাদের আমীর তোমাদের নিজেদের মধ্যথেকে হওয়া উচিত।] আল্লাহ তায়ালা এই উম্মতকে যে ইজ্জত দান করেছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি একথা বলবেন।
(আরবী **********)
(৮) হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (ইবনে সাইয়াদ প্রসংগে) বর্ণনা করেছেন যে, অতঃপর উমর ইবনে খাত্তাব আরজ করলেন, হে রসূলুল্লাহ। অনুমতি দিন, আমি তাকে কতল করি। রসূলুল্লাহ (স) বললেন, যদি এ সেই ব্যক্তি (অর্থাৎ দাজ্জাল) হয়ে থাকে, তাহলে তোমরা এর হত্যাকারী নও, বরং ঈসা ইবনে মরিয়ম একে হত্যা করবেন এবং যদি এ সেই ব্যক্তি না হয়েথাকে, তাহলে জিম্মীদের মধ্য থেকে কাউকে হত্যা করার তোমাদের কোনো অধিকার নেই।
(আরবী **********)
(৯) হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণনা করেছেন যে, (দাজ্জাল প্রসংগে রসূলুল্লাহ বলেছেন:) সেইসময় ঈসা ইবনে মরিয়ম হঠাৎ মুসলমানদের মধ্যে এসে উপস্থিত হবেন। অতঃপর লোকেরা নামাজের জন্য দাঁড়িয়ে যাবে। তাঁকে বলা হবে, হে রুহুল্লাহ! অগ্রসর হন। কিন্তু তিনি বলবেন, না, তোমাদের ইমামের অগ্রবর্তী হওয়া উচিত, তিনিই নামাজ পড়াবেন। অতঃপর ফজরের নামাজের পর মুসলমানরা দাজ্জালের মুকাবিলায় বের হবে। (রসূলুল্লাহ) বলেছেন: যখন সেই কাজ্জাব (মিথ্যাবাদী) হযরত ঈসাকে দেখবে, তখন বিগলিত হতে থাকবে যেমন লবণ পানিতে গলে যায়। অতঃপর তিনি দাজ্জালের দিকে অগ্রসর হবেন এবং তাকে কতল করবেন। তখন অবস্থা এমন হবে যে, গাছপালা এবং প্রস্তরখন্ড ফুকারে বলবে, হে রুহুল্লাহ! ইহুদীটা এই আমার পিছনে লুকিয়ে রয়েছে! দাজ্জালের অনুগামীদের কেউ বাঁচবেনা, সবাইকে কতল করা হবে।
(আরবী **********)
(১০) হযরত নওয়াস ইবনে সাময়ান কেলাবী (দাজ্জাল প্রসংগে) বর্ণনা করছেন যে, (রসূলুল্লাহ বলেছেন:) দাজ্জাল তখন এসব করতে থাকবে, ইত্যবসরে আল্লাহতায়ালা মসীহ ইবনে মরিয়মকে প্রেরণ করবেন। তিনি দামেশকের পূর্ব অংশে সাদা মিনারের সন্নিকটে দুটো হলুদ বর্ণের কাপড় পরিধান করে দুজনফেরেশতার কাঁধে হাত রেখে নামাবেন। তিনি মাথা নীচু করলে পানি টপকাচ্ছে বলে মনে হবে। আবার মাথা উঁচু করলে মনে হবে যেন বিন্দু বিন্দু পানি মোতির মতো চমকাচ্ছে। তাঁর নিঃশ্বাসের হাওয়া যে কাফেরের গায়ে লাগবে- এবং এর গতি হবে তাঁর দৃষ্টিসীমাপর্যন্ত-সে জীবিত থাকবে না। অতঃপর ইবনে মরিয়ম দাজ্জালের পশ্চাদ্ধাবন করবেন এবং লুদের [এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, লূদ (Lydda) ফিলিস্তিনের অন্তর্গত বর্তমান ইসরাঈল রাষ্ট্রের রাজধানী তেলআবীব থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত। ইহুদীরা এখানে একটি বিরাট বিমান বন্দর নির্মাণ করেছে] দ্বারপ্রান্তে তাকে গ্রেফতার করে হত্যা করবেন।
(আরবী **********)
(১১) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (স)বলেন: দাজ্জাল আমার উম্মতের মধ্যে বের হবে এবং চল্লিশ (আমি জানিনা চল্লিশদিন, চল্লিশ মাস অথবা চল্লিশ বছর) [এটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমরের কথা] অবস্থান করবে। অতঃপর আল্লাহ ঈসা ইবনে মরিয়মকে পাঠাবেন।তাঁর চেহারা উরওয়া ইবনে মাসউদের (জনৈক সাহাবী) মতো। তিনি দাজ্জালের পশ্চাদ্ভাবন করবেন এবং তাকে হত্যা করবেন। অতঃপর সাত বছর পর্যন্ত মানুষ এমন অবস্থায় থাকবে যে, দুজনলোকের মধ্যে শত্রুতা থাকবেনা।
(আরবী **********)
(১২) হযরত হোজায়ফা ইবনে আসীদ আল গিফারী (রা) বর্ণনা করেছেনযে, একবার রাসূলুল্লাহ (স) আমাদের মজলিসে তাশরীফ আনলেন। তখন আমরা নিজেদের মধ্যে আলোনায় লিপ্ত ছিলাম। রসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞেস করলেন: তোমরা কি আলোচনা করছো? লোকেরা বললো, আমরা কিয়ামতের কথা আলোচনা করছি। তিনি বললেন: দশটিনিশানা প্রকাশ না হবার পূর্বে তা কখনো কায়েম হবেনা। অতঃপর তিনি দশটি নিশানা বলে গেলেন। এক: ধোঁয়া, দুই: দাজ্জাল, তিন: মৃত্তিকার প্রাণী, চার: পশ্চিম দিক হতে সুর্যোদয়, পাঁচ ঈসা ইবনে মরিয়মের অবতরণ, ছয়: ইয়াজুজ ও মাজুজ, সাত: তিনটি প্রকাণ্ড জমি ধ্বংস (Landslide) একটি পূর্বে, আট: একটি পশ্চিমে, নয়: আর একটি আরব উপদ্বীপে, দশ: সর্বশেষ একটি প্রকাণ্ড অগ্নি ইয়েমেন থেকে উঠবে এবং মানুষকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে হাশরের ময়দানের দিকে।
(আরবী **********)
(১৩) রসূলুল্লাহর (স) আজাদকৃত গোলাম সাওবান (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ বলেন: আমার উম্মতের দু’টো সেনাদলকে আল্লাহতায়ালা দোজখের আগুন থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন। তাদের মধ্যে একটি হলো- যারা হিন্দুস্থানের ওপর হামলা করবে আর দ্বিতীয়টি ঈসা ইবনে মরিয়মের সংগে অবস্থানকারী।
(আরবী **********)
(১৪) মাজমা ইবনে জারিয়া আনসারী (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহকে (স) বলতে শুনেছি: ইবনে মরিয়ম দাজ্জালকে লুদের দ্বারপ্রান্তে কতল করবেন।
(আরবী **********)
(১৫) আবু উমামা বাহেলী (এক দীর্ঘ হাদীসে দাজ্জাল প্রসংগে) বর্ণনা করেছেন যে, ফজরের নামায পড়বার জন্য মুসলমানদের ইমাম যখন অগ্রবর্তী হবেন, ঠিক সেইসময় ঈসা ইবনে মরিয়ম তাদের ওপর অবতীর্ণ হবেন। ইমাম পিছনে সরে আসবেনঈসাকে (আ) অগ্রবর্তী করার জন্য কিন্তু ঈসা (আ) তাঁর কাঁধে হাত রেখে বলবেন: না, তুমিই নামাজ পড়াও। কেননা এরা তোমার জন্যই দাঁড়িয়েছে। কাজেই তিনিই (ইমাম) নামাজ পড়াবেন। সালাম ফেরার পরঈসা (আ) বলবেন: দরজা খোলো। দরজা খোলা হবে। বাইরে দাজ্জাল ৭০ হাজার সশষ্ত্র ইহুদী সৈন্য নিয়ে অপেক্ষা করবে। তার দৃষ্টি হযরত ঈসার (আ) ওপর পড়া মাত্রই সে এমনভাবে বিগলিত হতে থাকবে, যেমন লবণ পানিতে গলে যায়। এবং সে পৃষ্ঠদর্শন করবে। ঈসা (আ) বলবেন: আমার নিকট তোর জন্য এমন এক আঘাত আছে যার হাত থেকে তোর কোনক্রমেই নিষ্কৃতি নেই। অতঃপর তিনি তাকে লূদের পূর্ব দ্বারদেশে গিয়ে গ্রেফতার করবেন এবং আল্লাহতায়ালা ইহুদীদেরকে পরাজয়দান করবেন..... এবং জমিন মুসলমানদের দ্বারা এমনভাবে ভরপুর হবে যেমন পাত্র পানিতে ভরে যায়। সবাই একই কালেমায় বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং দুনিয়ায় আল্লাহ ছাড়া আর কারুর বন্দেগী করা হবেনা।
(আরবী **********)
(১৬) উসমান ইবনে আবিল আস (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহকে (স) বলতে শুনেছি:...... এবংঈসা ইবনে মরিয়ম আলাইহিস সালাম ফজরের নামাজের সময় অবতরণ করবেন। মুসলমানদের আমীর তাঁকে বলবেন, হে রুহুল্লাহ! আপনি নামাজ পড়ান! তিনি জবাব দেবেন: এই উম্মতের লোকেরা নিজেরাই নিজেদের আমীর। তখন মুসলমানদের আমীর অগ্রবর্তী হয়ে নামায পড়াবেন। অতঃপর নামাজ শেষ করে ঈসা (আ) নিজের সেনাবাহিনী নিয়ে দাজ্জালের দিকে অগ্রসর হবেন। তিনি নিজের অস্ত্র দিয়ে দাজ্জালকে কতল করবেন এবং তার দলবল পরাজিত হয়ে পৃষ্ঠপদর্শন করবে। কিন্তু কোথাও তারা আত্মগোপন করার জায়গা পাবেনা। এমন কি বৃক্ষও ফুকারে বলবে: হে মুমিন, এখানে কাফের লুকিয়ে আছে। এবং প্রস্তর খণ্ডও ফুকারে বলবে: হে মুমিন, এখানে কাফের লুকিয়ে আছে।
(আরবী **********)
(১৭) সামুরা ইবনে জুনদুব (এক দীর্ঘ হাদীসে) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (স) বলেন: অতঃপর সকাল বেলা ঈসা ইবনে মরিয়ম মুসলমানদের মধ্যে আসবেন এবং আল্লাহতায়ালা দাজ্জাল এবং তার সেনাবাহিনীকে পরাজয় দান করবেন। এমন কি প্রাচীর এবং বৃক্ষের কাণ্ডও ফুকারে বলবে: হে মুমিন, এখানে কাফের আমার পেছনে লুকিয়ে রয়েছে। এসো, একে কতল করো!
(আরবী **********)
(১৮) ইবনে হোসাইন বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (স) বলেন: আমাদের উম্মতের মধ্যে হামেশা একটি দল হকের ওপর কায়েম থাকবে এবং তারা বিরোধী দলের ওপর প্রতিপত্তি বিস্তার করবে। অবশেষে আল্লাহতায়ালার ফয়সালা এসে যাবে এবং ঈসা ইবনে মরিয়ম আলাইহিস সালাম অবতীর্ণ হবেন।
(আরবী **********)
(১৯) হযরত আয়েশা রাজিআল্লাহ আন্হা (দাজ্জাল প্রসংগে) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ বলেন: অতঃপর ঈসা আলাইহিস সালাম অবতীর্ণ হবেন। তিনি দাজ্জালকে কতল করবেন। অতঃপর ঈসা(আ) চল্লিশ বছর আদিল ইমাম এবং ন্যায়নিষ্ঠ শাসক হিসেবে দুনিয়ায় অবস্থান করবেন।
(আরবী **********)
(২০) রসূলুল্লাহর আজাদকৃত গোলাম সাফীনা (রা) (দাজ্জাল প্রসংগে) বর্ণনা করেছেন, যে রসূলুল্রাহ (স) বলেন: অতঃপর ঈসা আলাইহিস সালাম অবতীর্ণ হবেন এবং আল্লাহতায়ালা উফায়েকের পর্বতে পথের [উফায়েককে বর্তমান ফায়েক বলা হয়। সিরিয়া এবং ইসরাইল সীমান্তে বর্তমান সিরিয়া রাষ্ট্রের সর্বশেষ শঞর। এর পরে পশ্চিমের দিকেকয়েক মাইল দূরে তাবারিয়া নামক একটি হ্রদ আছে। এখানে জর্দান নদরি উৎপত্তিস্থল। এর দক্ষিণ-পশ্চিমে পাহাড়েরর মধ্যভাগে নিম্ন ভূমিতে একটি রাস্তা রয়েছে। এই রাস্তাটি প্রায় দেড় হাজার ফুট গভীরে নেমে গিয়ে সেই স্থানে পৌঁছায় যেখানথেকে জর্দান নদী তাবারিয়া মথ্যহতে নির্গত হচ্ছে। এই পার্বত্য পথকেইবলা ‘আকাবায়ে উফায়েক” (উফায়েকের নিম্ন পার্বত্য পথ)।] সন্নিকটে তাকে (দাজ্জালকে) মেরে ফেলবেন।
(আরবী **********)
(২১) হযরত হোজায়ফা ইবনে ইয়ামান (দাজ্জাল প্রসংগে) বর্ণনা করেছেনযে, রসূলুল্লাহ বলেন: অতঃপর যখন মুসলমানরা নামাজের জন্য তৈরী হবে, তখন তাদের চোখের সম্মুখে ঈসা ইবনে মরিয়ম অবতীর্ণ হবেন। তিনি মুসলমানদের নামাজ পড়াবেন অতঃপর সালাম ফিরিয়ে লোকদের বলবেন যে, আমার এবং খোদার এই দুশমনের মাঝখান থেকে সরেযাও.... এবং আল্লাহতায়ালা দাজ্জালের দলবলের ওপর মুসলমানদেরকে প্রতিপত্তি দান করবেন।
মুসলমানরা তাদেরকে বেধড়ক হত্যা করতে থাকবে। অবশেষে বৃক্ষ এবং প্রস্তর খণ্ডও ফুকারে বলবে: হে আল্লাহর বান্দা, হে রহমানেসর বান্দা, হে মুসলমান!দেখো, এখানে একজন ইহুদী, একে হত্যা করো। এভাবে আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করে দেবেন এবং মুসলমানগণ বিজয় লাভ করবে। তারা ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবে, শুকর হত্যা করবে এবং জিজিয়া মওকুফ করে দেবে। [মুসলিমেও হাদীসটি সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে এবং হাফেজ ইবনে হাজার আসকালীণ ফাতহুল বারীর ষষ্ঠ খণ্ডে ৫৫০ পৃষ্ঠায় এটিকে ‘ছহীহ’ বলে গণ্য করেছেন।
এই ২১টি হাদীস ১৪ জন সাহাবায়ে মারফত নির্ভুল সনদসহ হাদীসের নির্ভরযোগ্য কিতাবগেুলোয় উল্লিখিত হয়েছে। এছাড়াও এ ব্যাপারে আরো অসংখ্য হাদীস অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু আলোচনা দীর্ঘ হবার ভয়ে আমি সেগুলো এখানে উল্লেখ করলাম না। বর্ণনা এবং সনদের দিক অধিকতর শক্তিশালী এবং নির্ভরযোগ্য হাদীসগুলোই শুধু এখানে উদ্ধৃত করলাম।
এই হাদীসগুলো থেকে কি প্রমাণ হয়?
যে কোনো ব্যক্তি এ হাদীসগুলো পড়ে নিজেই বুঝতে পারবেনযে, এখানে কোনো ‘প্রতিশ্রুত মসীহ’, “মছীলে মসীহ” বা “বুরুজী মসীহ”র কোনো উল্লেখই করা হয়নি। এমন কি বর্তমান কালে কোনো পিতার ঔরসে মায়ের গর্ভ জন্মগ্রহণ করে কোনো ব্যক্তির একথা বলার অবকাশ নেই যে, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যে মসীহ সম্পর্কে ভবিষদ্বাণী করেছিলেন তিনিই সেই মসীহ। আজ থেকে দু’হাজার বছর আগে পিতা ছাড়াই হযরত মরিয়মের (আ) গর্ভে যে ঈসা আলাইহিস সালামের জন্ম হয়েছিল এই হাদীসগুলোর দ্ব্যার্থহীন বক্তব্যথেকে তাঁরই অবতরণের সংবাদ শ্রুত হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে তিনি ইন্তেকাল করেছেন, না জীবিত অবস্থায় কোথাও রয়েছেন- এ আলোচনা সম্পূর্ণ অবান্তর। তর্কের খাতিরে যদি এ কথা মেনে নেয়া হয় যে, তিনি ইন্তেকাল করেছেন তাহলেও বলা যায় যে, আল্লাহ তাঁকে জীবিত করার ক্ষমতা রাখেন। [যারা আল্লাহর এই পুনরুজ্জীবনের ক্ষমতা অস্বীকার করেন তাদের সূরা বাকারার ২৫৯ নম্বর আয়াতটির অনুধাবন করাউচিত। এ আয়াতে আল্লাহ বলেন যে, তিনি তাঁর এক বান্দাকে ১০০ বছর পর্যন্ত মৃত অবস্থায় রাখার পর আবার তাকে জীবিত করেন।] উপরন্তু আল্লাহ তাঁর এক বান্দাকে তাঁর এই বিশাল সৃষ্টি জগতের কোনো এক স্থানে হাজার বছর জীবিত অবস্থায় রাখার পর নিজের ইচ্ছামতো যে কোনো সময়তাঁকে এই দুনিয়ায় ফিরিয়ে আনতে পারেন। আল্লাহর অসীম ক্ষমতার প্রেক্ষিতে একথা মোটেই অস্বাভাবিক মনে হয়না। বলা বাহুল্য, যে ব্যক্তি হাদীসকে সত্য বলে স্বীকার করে তাকে অবশ্যই ভবিষ্যতে আগমনকারী ব্যক্তিকে উল্লিখিত ঈসা ইবনে মরিয়ম বলে স্বীকার করতেই হবে। তবে যে ব্যক্তি হাদীস অস্বীকার করে সে আদতে কোনো আগমনকারীর অস্তিত্বই স্বীকার করতে পারেনা। কারণ আগমনকারীর আগমন সম্পর্কে যে বিশ্বাস জন্ম নিয়েছে হাদীস ছাড়া আর কোথাও তার ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যাবেনা। কিন্তু এই অদ্ভূত ব্যাপারটি শুধু এখানেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, আগমনকারীর আগমন সম্পর্কিত ধারণা বিশ্বাস গ্রহণ করা হচ্ছে হাদীস থেকে কিন্তু সেই হাদীসগুলোই আবার যখন সুস্পষ্ট করে এ বক্তব্য তুলে ধরছে যে, উক্ত আগমনকারী কোনো ‘মছীলে মসীহ’ (মসীহ-সম ব্যক্তি) নন বরং তিনি হবেন স্বয়ং ঈসা ইবনে মরিয়ম আলাইহস সালাম তখন তা অস্বীকার করা হচ্ছে।
এই হাদীসগুলো থেকে দ্বিতীয় যে বক্তব্যটি সুস্পষ্ট ও দ্ব্যার্থহীনভাবে ফুটে উঠেছে তা হচ্ছে এই যে, হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ) দ্বিতীয়বার নবী হিসেবে অবতরণ করবেন না। তাঁর ওপর অহী নাযিল হবেনা। খোদার পক্ষ থেকে তিনি কোনো নতুন বাণী বা বিধান আনবেন না। শরীয়তে মুহাম্মদীর মধ্যেও তিনি হ্রাস বৃদ্ধি করবেননা। দ্বীন ইসলামের পুনরুজ্জীবনের জন্যও তাঁকে দুনিয়ায় পাঠানো হবে না। তিনি এসে লোকদেরকে নিজের ওপর ঈমান আনার আহ্বান জানাবেননাএবং তাঁর প্রতি যারা ঈমান আনবে তাদেরকে নিয়ে পৃথক উম্মতও গড়ে তুলবেননা। [পূর্বপবর্ত আলেমগণ এ বিষয়টিকে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। আল্লামা আফ্তাবানী (হিঃ ৭২২-৭৯২) শরহে আকায়েদে নাসাফী গ্রন্থে লিখেছেন: “মুহাম্মদ (স) সর্বশেষ নবী, একথা প্রমাণিত সত্য... যদি বলা হয়, তাঁর পর হাদীসে হযরত ঈসার (আ) আগমনের কথা বর্ণিত হয়েছে তাহলে আমি বলবো, হাঁ হযরত ঈসা (আ) আগমনের কথা বলা হয়েছে সত্য, তবে তিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অনুসারী হবেন। কারণ তাঁর শরীয়ত বাতিল হয়ে গেছে। কাজেই তাঁর ওপর অহী নাযিল হবেনা এবং তিনি নতুন বিধানও নির্ধারণ করবেন না। বরং তিনি মুহাম্মদ রসূলুল্লাহর (স) প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করবেন।” (মিসরে মুদ্রিত, ১৩৫ পৃষ্ঠা)
আল্লামা আলুসী তাঁর ‘রুহুল মা’নী’ নামক তাফসীর গ্রন্থেও প্রায় একই বক্তব্য পেশ করেছেন। তিনি বলেছেন: “অতঃপর ঈসা আলাইহিস সালাম অবতীর্ণ হবেন। তিনি অবশ্য তাঁর পূর্ব প্রদত্ত নবুয়্যাতের পদমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত থাকবেন। কাণ তিনি নিজের আগের পদমর্যাদা থেকেতো অপসারিত হবেননা। কিন্তু নিজের পূর্বের শরীয়তের অনুসারী হবেননা। কারণ তা তাঁর নিজের ও অন্যসব লোকদের জন্য বাতিল হয়ে গেছে। কাজেই বর্তমানে তিনি মূলনীতি থেকে খুঁটিনাটি ব্যাপার পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়তের বিধানও নির্ধারণ করবেননা। “বরং তিনি মুহাম্মদ রসূলুল্লাহর (স) প্রতিনিধি এবং তাঁর উম্মতের মধ্যস্থিত মুহাম্মদী মিল্লাতের শাসকদের মধ্য থেকে একজন শাসক হবেন।”) (২২শ খণ্ড, ৩২ পৃষ্ঠা)
ইমাম রাজী এ কথাটিকে আরো সুস্পষ্ট করে নিম্নোক্ত ভাষায় পেশ করেছেন: “মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম পর্যন্ত নবীদের যুগ শেষ হয়ে গেছে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আগমনের পর নবীদের আগমন শেষ হয়ে গেছে। কাজেই বর্তমানে ঈসার (আ) অবতহরণের পর তিনি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অনুসারী হবেন একথা মোটেই অযৌক্তিক নয়।” (তাফসীরে কবীর, ৩য় খণ্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা)] তাঁকে কেবলমাত্র একটি পৃথক দায়িত্ব দিয়ে দুনিয়ায় পাঠানো হবে। অর্থাৎ তিনি দাজ্জালের ফিত্নাকে সমূহে বিনাশ করবেন। এজন্য তিনি এমনভাবে অবতরণ করবেন যার ফলে তাঁর অবতরণের ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশ থাকবেনা। যেসব মুসলমানের মধ্যে তিনি অবতরণ করবেন তারা নিঃসংশয়ে বুঝতে পারবে যে, রসূলুল্লাহ (স) যে ঈসা ইবনে মরিয়ম সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তিনিই সেই ব্যক্তি এবং রসূলুল্লাহর কথা অনুযায়ী তিনি যথা সময়ে অবতরণ করেছেন, তিনি এসে মুসলমানদের দলে শামিল হয়ে যাবেন। মুসলমানদের তদানীন্তন ইমামের পিছনে তিনি নামাজ পড়বেন। [যদিও দুটি হাদীসে (৫ ও ২১ নং) বলা হয়েছে যে, ঈসা আলাইহিস সালাম অবতরণ করার পর প্রথম নামাজটি নিজে পড়াবেন। কিন্তু অধিকাংশ এবং বিশেষ করে শক্তিশালী কতিপয় হাদীস (৩, ৭, ৯, ১৫ ও ১৬ নয়) থেকে জানা যায় যে, তিনি নামাজে ইমামতি করতে অস্বীকার করবেন এবং মুসলমানদের তৎকালীন ইমাম ও নেতাকে অগ্রবর্তী করবেন। মুহাদ্দিস ও মুফাস্সিরগণ সর্বসম্মতভাবে এ মতটি গ্রহণ করেছেন।] তৎকালে মুসলমানদের যিনি নেতৃত্ব দেবেন তিনি তাঁকেই অগ্রবর্তী করবেন যাতে এই ধরনের সন্দেহের কোনো অবকাশই না থাকে যে, তিনি নিজের পয়গম্বরী পদমর্যাদা সহকারে পুনর্বার পয়গম্বরীর দায়িত্ব পালন করার জন্য ফিরে এসেছেন। নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, কোনো দলে খোদার পয়গম্বরের উপস্থিতিতে অন্য কোনো ব্যক্তি ইমাম বা নেতা হতে পারেন না। কাজেই নিছক এক ব্যক্তি হিসেবে মুসলমানদের দলে তাঁর অন্তর্ভুক্তি স্বতঃস্ফুর্তভাবে এ কথাই ঘোষণা করবে যে, তিনি পয়গম্বর হিসেবে আগমন করেননি। এজন্যতাঁর আগমনে নবুয়্যাতের দুয়ার উন্মুক্ত হবার কোনো প্রশ্নই ওঠেনা।
নিঃসন্দেহে তাঁর আগমন বর্তমান ক্ষমতাসীন রাষ্ট্রপ্রধানের আমলে প্রাক্তন রাষ্ট্রপ্রধানের আগমনের সাথে তুলনীয়। এ অবস্থায় প্রাক্তন রাষ্ট্রপ্রধানের অধীনে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে অংশগ্রহণ করতে পারন। সাধারণ বোধ সম্পন্ন কোনো ব্যক্তি সহজেই এ কথা বুঝতে পারেন যে, এক রাষ্ট্রপ্রধানের আমলে অন্য একজন প্রাক্তন রাষ্ট্রপ্রধানের নিছক আগমনেই আইন ভেঙ্গে যায় না। তবে দুটি অবস্থায় আইনের বিরুদ্ধাচরণ অনিবার্য হয়ে পড়ে। এক, প্রাক্তন রাষ্ট্রপ্রধান এসে যদি আবার নতুন করে রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করেন। দুই, কোনো ব্যক্তি যদি তাঁর প্রধান রাষ্ট্রপ্রধানের মর্যাদা ও দায়িত্ব অস্বীকার করে বসেন। কারণ এটা হবে তাঁর রাষ্ট্র থাকাকালে যেসব কাজ হয়েছিল সেগুলোর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করার নামান্তর। এই দু’টি অবস্থার কোনো একটি না হলে প্রাক্তন রাষ্ট্র-প্রধানের নিছক আগমনেই আইনগত অবস্থাকে কোনো প্রকারে পরিবর্তিত করতে পারেনা। হযরত ঈসার (আ) দ্বিতীয় আগমনের ব্যাপারটিও অনুরূপ। তাঁর নিছক আগমনেই খতমে নবুয়্যাতের দুয়ার ভেঙ্গে পড়েনা। তবে তিনি এসে যদি নবীর পদে অধিষ্ঠিত হন এবং নবুয়্যাতের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন অথবা কোনো ব্যক্তি যদি তাঁর প্রাক্তন নবুয়্যাতের মর্যাদাও অস্বীকার করে বসে, তাহলে এক্ষেত্রে আল্লাহর নবুয়্যাত বিধি ভেঙ্গে পড়ে। হাদীসে একদিকে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হচ্ছে যে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহর (স) পর আর কোনো নবী নেই এবং অন্যদিকে জানিয়ে দিচ্ছে যে, ঈসা আলাইহিস সালাম পুনর্বার অবতরণ করবেন। এ থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, তাঁর এ দ্বিতীয় আগমন নবুয়্যাতের দায়িত্ব পালন করার উদ্দেশ্যে হবেনা।
অনুরূপভাবে তাঁর আগমনে মুসলমানদের মধ্যে কুফর ও ঈমানের কোনো নতুন প্রশ্ন দেখা দেবেনা। আজও কোনো ব্যক্তি তাঁর পূর্বের নবুয়্যাতের ওপর ঈমান না আনলে কাফের হয়ে যাবে। মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (স) নিজেও তাঁর ঐ নবুয়্যাতের প্রতি ঈমান রাখতেন। মুহাম্মদ রসূলুল্লাহর (স) সমগ্র উম্মতও শুরু থেকেই তাঁর ওপর ঈমান রাখে। হযরত ঈসার (আ) পুনর্বার আগমনের সময়ও এই একই অবস্থা অপরিবর্তিত থাকবে। মুসলমানরা কোনো নতুন নবুয়্যাতের প্রতি ঈমান আনবে না, বরং আজকের ন্যায় সেদিনও তারা ঈসা ইবনে মরিয়মের (আ) পূর্বের নবুয়্যাতের ওপরই ঈমান রাখবে। এ অবস্থাটি বর্তমানে যেমন খতমে নবুয়্যাত বিরোধী নয়, তেমনি সেদিনও বিরোধীহবেনা।
সর্বশেষ যে কথাটি এই হাদীসগুলো এবং অন্যান্য বহুবিধ হাদীস থেকে আনা যায় তা হচ্ছে এই যে, হযরত ঈসাকে (আ) যে দাজ্জালের বিশ্বব্যাপী ফিত্না নির্মূল করার জন্য পাঠানো হবে সে হবে ইহুদী সংশোদ্ভূত। সে নিজেকে ‘মসীহ’ রূপে পেশ করবে। ইহুদীদের ইতিহাস ও তাদের ধর্মীয় চিন্তা-বিশ্বাস সম্পর্কে অনবহিত কোনো ব্যক্তি এ বিষয়টির তাৎপরর্য অনুধান করতে সক্ষম হবেনা। হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালামের মৃত্যুর পর যখন বনি ইসরাঈলরা সামাজিক ধর্মীয় অবক্ষয় ও রাজনৈতিক পতনের শিকার হলো এবং তাদের এ পতন দীর্ঘায়িত হতে থাকলো, এমন কি অবশেষে ব্যবিলেন ও আসিরিয়া অধিপতিরা তাদেরকে পরাধীন করে দেশ থেকে বিতাড়িত করলো এবং দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষিপ্ত করে দিলো, তখন বনি ইসরাইলের নবীগণ তাদেরকে সুসংবাদ দিতে থাকলেন যে, খোদার পক্ষ থেকে একজন ‘মসীহ’ এসে তাদেরকে এই চরম লাঞ্চনা থেকে মুক্তি দেবেন। এইসব ভবিষ্যদ্বাণীর প্রেক্ষিতে ইহুদীরা একজন মসীহের আগমনের প্রতীক্ষারত ছিল। তিনি হবেন বাদশাহ। তিনি যুদ্ধ করে দেশ জয় করবেন। বনি ইসরাঈলদেরকে বিভিন্ন দেশ থেকে এনে ফিলিস্তিনে একত্রিত করবেন এবং তাদের একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র কায়েম করবেন। কিন্তু তাদের এসব আশা-আকাংখাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে যখন ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ) খোদার পক্ষ থেকে ‘মসীহ’ হয়ে আসলেন এবং কোনো সেনাবাহিনী ছাড়াই আসলেন, তখন ইহুদীরা তাঁকে ‘মসীহ’ বলে মেনে নিতে অস্বীকার করলো। তারা তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হলো। সে সময় থেকে আজ পর্যন্ত ইহুদী দুনিয়া সেই প্রতিশ্রুত মসীহর প্রতীক্ষা করছে, যার আগমনের সুসংবাদ তাদেরকে দেয়া হয়েছিল। তাদের সাহিত্য সেই বাঞ্চিত যুগের সুখ-স্বপ্ন কল্প-কাহিনীতে পরিপূর্ণ। তালমুদ ও রাববীর সাহিত্য গ্রন্থসমূহে এর যে নক্শা তৈরী করা হয়েছে তার কল্পিত স্বাদ আহরণ করে শত শত বছর থেকে ইহুদী জাতি জীবন ধারণ করছে। তাদের বুক ভরা আশা নিয়ে বসে আছে যে, এই প্রতিশ্রুত মসীহ হবেন একজন শক্তিশালী সামরিক ও রাজনৈতিক নেতা। তিনি নীল নদ থেকে ফোরাত পর্যন্ত সমগ্র এলাকা, যে এলাকাটিকে ইহুদীরা নিজেদের ‘উতর্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এলাকা’ মনে করে, আবার ইহুদীদের দখলে আনবেন এবং সারা দুনিয়া থেকে ইহুদীদেরকে এনে এখানে একত্রিত করবেন।
বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করে রসূলুল্লাহর (স) ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, মহানবীর (স) কথামত ইহুদীদের ‘প্রতিশ্রুত মসীহর’ ভূমিকা পালনকারী প্রধানতম দাজ্জালের আগমনের জন্য মঞ্চ সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হয়ে গেছে। ফিলিস্তিনের বৃহত্তম এলাকা থেকে মুসলমানদের বেদখল করা হয়েছে। সেখানে ইরাঈল নামে একটি ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সারা দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে ইহুদীরা দলে দলে এখানে বাসস্থান গড়ে তুলছে। আমেরিকা, বৃটেন ও ফ্রান্স তাকে একটি বিরাট সামরিক শক্তিকে পরিণত করেছে। ইহুদী পুঁজিপতিদের সহায়তায় ইহুদী বৈজ্ঞানিক ও শিল্পবিদগণ দ্রুত উন্নতির পথে েএগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। চারপাশের মুসলিম দেশগুলোর জন্য তাদের এ শক্তি এক মহাবিপদে পরিণত হয়েছে। এই রাষ্ট্রের শাসকবর্গ তাদের এই ‘উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত দেশ’ দখল করার আকাংখাটি মোটেই
(মানচিত্র *****************)
লুকিয়ে রাখেননি। দীর্ঘকাল থেকে ভবিষ্যত ইহুদী রাষ্ট্রের যে নীল নক্শা তারা প্রকাশ করে আসছে পরের পাতায় তার একটি প্রতিকৃতি দেয়া হলো। এ নক্শায় দেখা যাবে, সিরিয়া, লেবানন ও জর্দানের সমগ্র এলাকা এবং প্রায় সমগ্র ইরাক ছাড়াও তুরস্কের ইস্কান্দোরুন, মিসরের সিনাই ও ব-দ্বীপ এলাকা এবং মদীনা মুনাওয়ারাসহ আরবের অন্তর্গত হেজাজ ও নজ্দের উচ্চভূমি পর্যন্ত তারা নিজেদের সাম্রাজ্র বিস্তার করতে চায়। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, আগামীতে কোনোএকটি বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোলে তারা ঐসব এলাকা দখল করার চেষ্টার করবে এবং ঐ সময়ই কথিত প্রধানতম দাজ্জাল তাদের প্রতিশ্রুত মসীহরূপে আগমন করবে। রসূলুল্লাহ (স) কেবল তার আগমন সংবাদ দিয়েই ক্ষান্ত হননি বরং এই সংগে একথাও বলেছেন যে, সে সময় মুসলমানদের ওপর বিপদের পাহাড় ভেঙে পড়বে এবং এক একটি দিন তাদের নিকট এক একটি বছর মনে হবে। এজন্য তিনি নিজে মসীহ দাজ্জালের ফিত্না থেকে খোদার নিকট আশ্রয় চেয়েছেন এবং মুসলমানদেরকেও আশ্রয় চাইতে বলেছেন।
এই মসীহ দাজ্জালের মোকাবিলা করার জন্য আল্লাহ কোনো ‘মসীলে মসীহ’কে পাঠাবেন না বরং আসল মসীহকে পাঠাবেন। দু’হাজার বছর আগে ইহুদীরা এই আসল মসীহকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছিলএবং নিজেদের জানা মতে তারা তাঁকে শূলবিদ্ধ করে দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে দিয়েছিল। এই আসল মসীহ ভারত, আফ্রিকা বা আমেরিকায় অবতরণ করবেন না বরং তিনি অবতরণ করবেন দামেশ্কে। কারণ তখন সেখানেই যুদ্ধ চলতে থাকবে। মেহেরবানী করে পরের পাতার নকশাটিও দেখুন। এতে দেখা যাচ্ছে, ইসরাঈলের সীমান্ত থেকে দামেশক মাত্র ৫০ থেকে ৬০ মাইলের মধ্যে অবস্থিত। ইতিপূর্বে আমি যে হাদীস উল্লেখ করে এসেছি, তার বিষয়বস্তু মনে থাকলে সহজেই একথা বোধগম্য হবে যে, মসীহ দাজ্জাল ৭০ হাজার ইহুদী সেনাদল নিয়ে সিরিয়ায় প্রবেশ করবে এবং দামেশকের সামনে উপস্থিত হবে। ঠিক সেই মুহুর্তে দামেশকের পূর্ব অংশের একটি সাদা মিনারের নিকট সুব্হে সাদেকের পর হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম অবতরণ করবেন এবং ফজর নামায শেষে মুসলমানদের নিয়ে দাজ্জালের মুকাবিলায় বের হবেন। তাঁর প্রচণ্ড আক্রমণে দাজ্জাল পশ্চাদপসরণ করে উফাইকের পার্বত্য পথ দিয়ে (২১১ নম্বর হাদীসে দেখুন) ইসরাঈলের দিকে ফিরে যাবে। কিন্তু তিনি তার পশ্চাদ্ধাবন করতেই থাকনে। অবশেষে লিড্ডা বিমান বন্দরে সে তাঁর হাতে মারা পড়বে (১০, ১৪ ও ১৫ নং হাদীস)। এরপর ইহুদীদেরকে সব জায়গা থেকে ধরে ধরে হত্যা করা হবে এবং ইহুদী জাতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে (৯, ১৫ ও ২১ নম্বর হাদীস)। হযরত ঈসার (আ) পক্ষ থেকে সত্য প্রকাশের পর ঈসায়ী ধর্মও বিলুপ্ত হয়ে যাবে (১, ২, ৪ ও ৬ নম্বর হাদীস( এবং মুসলিম মিল্লাতের মধ্যে সমস্ত মিল্লাতে একীভূত হয়ে যাবে (৬ ও ১৫ নম্বর হাদীস)।
কোনোপ্রকার জড়তা ও অস্পষ্টতা ছাড়াই এই দ্ব্যার্থহীন সত্যটিই হাদীস থেকে ফুটে উঠেছে। এই সুদীর্ঘ আলোচনার পর এ ব্যাপারে কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশ থাকেনা যে, “প্রতিশ্রুত মসীহ”র নামে আমাদের দেশে যে কারবার চালানো হচ্ছে তা একটি প্রকাণ্ড জালিয়াতি ছাড়া আর কিছুই নয়।
এই জালিয়অতির সবচাইতে হাস্যকর দিকটি এবার আমি উপস্থাপিত করতে চাই। যে ব্যক্তি নিজেকে এই ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লিখিত মসীহর সাথে অভিন্ন বলে ঘোষণা করেছেন, তিনি নিজে ঈসা ইবনে মরিয়ম হবার জন্য নিম্নোক্ত রসালো বক্তব্যটি পেশ করেছেন:
“তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ) বারাহীনে আহমদীয়ার তৃতীয় অংশে আমার নাম রেখেছেন মরিয়ম। অতঃপর যেমন বারাহীনে আহামদীয়ায় প্রকাশিত হয়েছে, দু’বছর পর্যন্ত আমি মরিয়মের গুণাবলী সহকারে লালিত হই.... অতঃপর ..... মরিয়মের ন্যায় ঈসার রহ আমার মধ্যে ফুৎকারে প্রবেশ করানো এবং রূপকার্থে আমাকে গর্ভবতী করা হয়। অবশেষে কয়েকমাস পরে, যা দশ মাসের চাইতে বেশী হবেনা, সেই এলহামের মাধ্যমে, যা বারাহীনে আহমাদীয়ার চতুর্থ অংশে উল্লিখিত হয়েছে, আমাকে মরিয়ম থেকে ঈসায় পরিণত করা হয়েছে। কাজেই এভাবে আমি হলাম ঈসা ইবনে মরিয়ম।” (কিশতীয়ে নুহ, ৮৭, ৮৮, ৮৯ পৃষ্ঠা)
অর্থাৎ প্রথমে তিনি মরিয়ম হন অতঃপর নিজে নিজেই গর্ভবতী হন। তারপর নিজের পেট থেকে নিজেই ঈসা ইবনে মরিয়ম রূপে জন্ম নেন। এরপরও সমস্যা দেখা দিলো যে, হাদীসের বক্তব্য অনুযায়ী ঈসা ইবনে মরিয়ম দামেশকে অবতরণ করবে। দামেশকে কয়েক হাজার বছর থেকে সিরিয়ার একটি প্রসিদ্ধ ও সর্বজন পরিচিত শহর। পৃথিবীর মানচিত্রে আজও এই শহরটি এই নামেই চিহ্নিত। কাজেই অন্য একটি রসাত্মক বক্তব্যের মাধ্যমে এ সমস্যাটির সমাধান দেয়া হয়েছে:
“উল্লেখ্য যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে দামেশকে শব্দের অর্থ আমার নিকট এভাবে প্রকাশ করা হয়েছে যে, এ স্থানে এমন একটি শহরের নাম দামেশ্ক রাখা হয়েছে যেখানে এজিদের স্বভাব সম্পন্ন ও অপবিত্র এজিদের অভ্যাস ও চিন্তার অনুসারী লোকদের বাস।..... এই কাদিয়ান শহরটি এখানকার অধিকাংশ এজিদী স্বভাব সম্পন্ন লোকের অধিবাসের কারণে দামেশকের সাথে সামঞ্জস্র ও সম্পর্ক রাখে।” (এযালায়ে আওহাম, ফুটনোট: ৬৩ থেকে ৭৩ পৃষ্ঠা)।
আর একটি জটিলতা এখনো রয়ে গেছে। হাদীসের বক্তব্য অনুসারে ইবনে মরিয়ম একটি সাদা মিনারের নিকট অবতরণ করবেন। এ সমস্যার সমাধান সহজেই করে ফেলা হয়েছে অর্থাৎ মসহি সাহেব নিজেই এসে নিজের মিনারটি তৈরী করে নিয়েছেন। এখন বলুন, কে তাঁকে বুঝাতে যাবে যে, হাদীসের বর্ণনা অনুসারে দেখা যায় ইবনে মরিয়মের অবতরণের পূর্বে মিনারটি সেখানে মওজুদ থাকবে। অথচ েএখানে দেখা যাচ্ছে প্রতিশ্রুত মসীহ সাহেবের আগমনের পর মিনারটি তৈরী হচ্ছে।
সর্বশেষ ও সবচাইতে জটিল সসনস্যাটি এখনো রয়ে গেছে। অর্থাৎ হাদীসের বর্ণনা মতে ঈসা ইবচনে মরিয়ম (আ) লিড্ডার প্রবেশ দ্বারো দাজ্জালকে হত্যা করবেন। এ সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে প্রথমে আবোল তাবোল অনেক কথাই বলা হয়েছে। কখনো স্বীকার করা হয়েছে যে, বায়তুল মুকাদ্দাসের একটি গ্রামের নাম লিড্ডা (এযালায়ে আওহাম, আঞ্জুমানে আহমদীয়া, লাহোর কর্তৃক প্রকাশিত, ক্ষুদ্রাকার, ২২০ পৃষ্ঠা)। আবার কখনো বলা হয়েছে, “লিড্ডা এমন সব লোককে হয় যারা অযথা ঝগড়া করে।... যখন দাজ্জালের অযথা ঝগড়া চরমে পৌঁছে যাবে তখন প্রতিশ্রুত মসীহের আবির্ভাব হবে এবং তার সমস্ত ঝগড়া শেষ করে দেবে” (এযালায়ে আওহাম, ৭৩০ পৃষ্ঠা)। কিন্তু এত করেও যখন সমস্যার সমাধান হলো তখন পরিষ্কার বলে দেয়া হলো যে, লিড্ডা (আরবীতে লুদ) অর্থ হচ্ছে পাঞ্জাবের লুদিয়ানা শহর। আর লুদিয়ানার প্রবেশ দ্বারে দাজ্জালকে হত্যা করার অর্থ হচ্ছে দুষ্টুদের বিরোধিতা সত্ত্বেও মীর্জা গোলাম আহমদ সাহেবের হাতে এখানেই সর্বপ্রথম বাইয়াত হয়। (আলহুদা, ৯১ পৃষ্ঠা)।
যে কোনো সুস্থ বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি এইসব বক্তব্য বর্ণনার নিরপেক্ষ পর্যালোচনা করলে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে বাধ্য হবেন যে, এখানে প্রকাশ্য দিবালোকে মিথ্যুক ও বহুরূপীর অভিনয় করা হয়েছে।
-:সমাপ্ত:-
', 'খতমে নবুয়্যাত', '', 'publish', 'closed', 'closed', '', '%e0%a6%96%e0%a6%a4%e0%a6%ae%e0%a7%87-%e0%a6%a8%e0%a6%ac%e0%a7%81%e0%a7%9f%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%a4', '', '', '2015-07-12 11:22:21', '2015-07-12 05:22:21', '
\r\n
খতমে নবুয়্যাত
\r\n
সাইয়েদ আবুল আ’লা মওদূদী
\r\n
অনুবাদক: আবদুল মান্নান তালিব
\r\n\r\n\r\n
\r\n\r\n
স্ক্যান কপি ডাউনলোড
\r\n
বর্তমান যুগে ইসলামের বিরুদ্ধে যে সকল ফেৎনার উদ্ভব হয়েছে তন্মধ্যে নতুন নবুয়্যাতের দাবী অতি মারাত্মক। এই নতুন নবুয়্যাতের দাবী মুসলিম জাতির মধ্যে বিরাট গোমরাহীর সৃষ্টি করে চলছে। সাধারণত দ্বীন সম্পর্কে মুসলমানদের পরিপূর্ণ ও সঠিক ধারণা না থাকার কারণেই এই ফেৎনার উদ্ভব ও তার বিকাশ সম্ভব হয়েছে। দ্বীন সম্পর্কে যদি মুসলমানগণ অনভিজ্ঞ না হ’তো এবং খত্মে নবুয়্যাতকে ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারতো তবে কিছুতেই বিংশ শতাব্দীতে এই ফেৎনার উদ্ভব ও বিকাশ সম্ভব হতো না বলেই আমাদের বিশ্বাস।
\r\n
খত্মে নবুয়্যাত বিশ্বাসের তাৎপর্য ও তার গুরুত্ব সম্পর্কে জনগণকে অবগত ও অবহিত করানোই হচ্ছে এই ফেৎনাকে নির্মূল করার সঠিক কার্যপন্থা। এ ছাড়া অন্যকোন পথ নেই এবং হতেও পারেনা। এ ব্যাপারে মুসলমানদের মনে যে সকল সশয় সন্দেহের সৃষ্টি করা হয় তার যুক্তিপূর্ণ ও যথার্থ সমালোচনা এবং জবাবের প্রয়োজন।
\r\n
আধুনিক বিশ্বের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তানায়ক আল্লামা সাইয়েদ আবুল আ’লা মওদূদী ১৯৬২ সা?লে “খত্মে নবুয়্যাত” নামক একটি পুস্তিকা রচনা করেন। উর্দু আত্মপ্রকাশের অব্যবহিত পরেই উপরোক্ত বইটির বাংলা তরজমা পাঠকদের খেদমতে পেশ করা হয়। অতি স্বল্প সময়ের মধ্যেই বইটি নিঃশেষ হয়ে যায়। পাঠক সমাজের বারবার তাগাদার কারণে ১৯৬৭ সালে বইটির ২য় সংস্করণ এবং ১৯৭৭ সালে ৩য় সংস্করণ পাঠক সমাজের সম্মুখে পেশ করা সম্ভবপর হয়নি, কিন্তু এ সংস্করণও শিগগিরই নিঃশেষ হয়ে যায়। বিভিন্ন বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে বর্তমানে এর চতুর্থ সংস্করণ পাঠক সমাজের সম্মুখে উপস্থাপিত করা হলো। খত্মে নবুয়্যাত সম্পর্কে মুসলিম সমাজে যে বিভ্রান্তিকর মতবাদ সৃষ্টি করা হচ্ছে তাকে প্রতিহত করার কাজে সুধীবৃন্দ এই পুস্তিকা হতে সামান্যতম উপকৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক মনে করবো।
\r\n
-প্রকাশক
\r\n\r\n
শেষ নবী
\r\n
(আরবী **********)
\r\n
“মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের কারুর পিতা নন। বরং তিনি আল্লাহর রসূল এবং শেষ নবী। এবং আল্লাহ সব জিনিসের ইলম রাখেন।”
\r\n
আয়াতটি সূরা আহ্যাবের পঞ্চম রুকুতে উদ্ধৃত হয়েছে। হযরত জয়নবের (রা) সঙ্গে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বিবাহের বিরুদ্ধে যেসব কাফের ও মুনাফিক মিথ্যা প্রচারণা শুরু করে দিয়েছিলো এই রুকুতে আল্লাহতায়ালা তাঁদের জবাব দিয়েছেন। তাদের বক্তব্য ছিল এই: জয়নব (রা) হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পালিত পুত্র হযরত জায়েদের (রা) স্ত্রী। অর্থাৎ তিনি রসূলুল্লাহর (স) পুত্রবধু। কাজেই জায়েদের তালাক দেবার পর রসূলুল্লাহ (স) নিজের পুত্রবধুকে বিয়ে করেছেন। এর জবাবে আল্লাহতায়ালা উপরোক্ত সূরার ৩৭ নম্বর আয়অতে বলেন: আমার নির্দেশেই এই বিবাহ সম্পাদিত হয়েছে এবং এজন্য হয়েছে যে, নিজের পালিত পুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিবাহ করায় মুসলমানদের কোনো দোষ নেই। অতঃপর ৩৮ এবং ৩৯ নম্বর আয়াতে বলেন: নবীর ওপর যে কাজ আল্লাহ ফরয করে দিয়েছেন কোন শক্তি তাঁকে তা সম্পাদন করা থেকে বিরত রাখতে পারেনা। নবীদের কাজ মানুষকে ভয় করা নয়, আল্লাহকে ভয় করা। নবীদের ব্যাপারে আল্লাহর চিরাচরিত পদ্ধতি হলো এই যে, কারুর পরোয়া না করেই তাঁরা সব সময় আল্লাহর পয়গাম দুনিয়ায় পৌঁছান এবং নিঃসংশয় চিত্তে তাঁর নির্দেশ পালনস করে থাকেন। এরপরই পেশ করেছেন আলোচ্র আয়াতটি। এই আয়াতটি বিরুদ্ধবাদীদের যাবতীয় প্রশ্ন এবং অপপ্রচারের মূলোৎপাটন করে দিয়েছে।
\r\n
তাদের প্রথম প্রশ্ন হলো: আপনি নিজের পুত্রবধুকে বিবাহ করেছেন। অথচ আপনার নিজের শরীয়তও একথা বলে যে, পুত্রের বিবাহিত স্ত্রী পিতার জন্য হারাম।এর জবাবে বলা হলো: “মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের কারুর পিতা নন।” অর্থাৎ যে ব্যক্তি তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে বিবাহ করা হলো, সে কি মুহাম্মদের (সা) পুত্র ছিল? তোমরা সবাই জান যে, মুহাম্মদের (সা) কোন পুত্র নেই।
\r\n
তাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো: পালিত পুত্র নিজের গর্ভজাত পুত্র নয়, একথা মেনে নিয়েও বলা যায় যে, তার তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে বিবাহ করা জায়েজ হতে পারে, কিন্তু তাকে অবশ্যই বিবাহ করতে হবে এবং প্রয়োজনটা কোথায়? এর জবাবে বলা হলো: “কিন্তু তিনি আল্লাহর রসূল।” অর্থাৎ যে হালাল বস্তু তোমাদের রসম-রেওয়াজের বদৌলতে অযথা হারামে পরিণত হয়েছে, সে সম্পর্কে যাবতীয় বিদ্বেষ এবং পক্ষপাতিত্ব খতম করে তার হালাল হওয়াকে নিঃসন্দেহ এবং নিঃসংশয় করে তোলা রসূলের অবশ্য করণীয় কাজ। [‘খত্মে নবুয়্যাত’ অস্বীকারকারীরা এখানে প্রশ্ন উঠায় যে, কাফের এবং মুনাফেকদের এই প্রশ্নটি কোন্ হাদীসে উল্লিীখত হয়েছে? কিন্তু এই প্রশ্নটি আসলে কোরআন সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতারই ফল। কোরআন মজীদের বহু জায়গায় আল্লাহতায়ালা বিরোধীদলের প্রশ্ন নকল না করেই তাদের জবাব দিয়ে গেছেন এবং জবাব থেকেই একথা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ হয়েছে যে, যে প্রশ্নটির জবাব দেয়া হচ্ছে সেটি কি ছিলো। এখানেও একই ব্যাপার। এখানেও জবাব নিজেই প্রশ্নের বিষয়বস্তু বিবৃত করছে। প্রথম বাক্যটির পর শব্দ দিয়ে দ্বিতীয় বাক্যটি শুরু করার প্রমাণ হলো যে, প্রথম বাক্যে প্রশ্নকারীর একটি কথার জবাব হয়ে যাবার পরও তার আর একটি প্রশ্ন বাকি রয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় বাক্যে তার জবাব দেয়া হয়েছে।মুহাম্মদ (স) নিজের পুত্রবধুকে বিবাহ করেছেন- তাদের এই প্রশ্নের জবাব তারা প্রথম বাক্যে পেয়ে গেছে। অতঃপর তাদের প্রশ্ন ছিল যে, একাজটা করার এমন কি প্রয়োজন ছিল? এর জবাবে বলা হলো: “কিন্তু তিনি আল্লাহর রসূল এবং শেষ নবী।” অন্য কথায় বলা যায়, যেমন কেউ বললো, জায়েদ দাঁড়ায়নি কিন্তু বকর দাঁড়িয়েছে। এর অর্থ হলো এই যে, “জায়েদ দাঁড়ায়নি” কথা থেকে একটি প্রশ্নের জবাব পাওয়ার পরও প্রশ্নকারীর আর একটি প্রশ্ন বাকি রয়ে গেছে। অর্থাৎ যদি জায়েদ না দাঁড়িয়ে থাকে, তবে কে দাঁড়ালো? এই প্রশ্নের জবাবে “কিন্তু বকর দাঁড়িয়েছে” বাক্যটি বলা হলো।]
\r\n
আবার অতিরিক্ত জোর দেবার জন্য বলেন: “এবং শেষ নবী।” অর্থাৎ তাঁর যুগে আইন এবং সমাজ সংস্কারমূলক কোনো বিধি প্রবর্তিত না হয়ে থাকলে, এই কাজ সমাধা করার জন্য তাঁর পর কোনো রসূল তো নয়ই, কোনো নবীও আসবেন না। কাজেই জাহেলী যুগের রসম-রেওয়াজ খতম করে দেবার প্রয়োজন এখনই দেখা দিয়েছে এবং তিনি নিজেই একাজটা সমাধা করে যাবেন।
\r\n
অতঃপর আরো জোর দিয়ে বলেন: “এবং আল্লাহ সব জিনিসের ইলম রাখেন।” অর্থাৎ এই মুহূর্তে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সাহায্যে এই বদ রসমটা খতম করিয়ে দেবার প্রয়োজনটা কি এবং এটা না করায় কি ক্ষতি-একথা একমাত্র আল্লাহই জানেন। তিনি জানেন যে, তাঁর পক্ষথেকে আর কোন নবী আসবেন না। কাজেই শেষ নবীর সাহায্যে যদি এই বদ রসমটা খতম করিয়ে না দেয়া হয়, তাহলেএর পরে আর দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি আসবেন না, যিনি একে নির্মূল করে দিতে চাইলে সমগ্র দুনিয়ায় মুসলমানদের মধ্য হতে চিরকালের জন্য এটি নির্মুল হয়ে যাবে। পরবর্তীকালেল সংস্কারকগণ এটা নির্মূল করে দিলেও তাঁদের কারুর কাজের পেছনে এমন কোন চিরন্তন এবং বিশ্বজনীন কর্তৃত্ব থাকবেনা, যার ফলে প্রত্যেক দেশ এবং প্রত্যেক যুগের লোকেরা তাঁদের অনুসরণ করতে বাধ্য হবে এবং তাঁদের কারুর ব্যক্তিত্বও এতোটা পাক-পবিত্র বলে গণ্য হবেনা যে, কোনো কাজ নিছক তাঁর সুন্নাত হবার দরুন মানুষের হৃদয় হতে সে সম্পর্কে যাবতীয় ঘৃণা, দ্বিধা এবং সন্দেহ মুহূর্তের মধ্যে নির্মল হয়ে যাবে।
\r\n\r\n
কোরআনের পূর্বাপর বিবৃতির ফায়সালা
\r\n
বর্তমান যুগে একটি দল নতুন নবুয়্যাতের ফিত্না সৃষ্টি করেছে। এরা ‘খাতিমুন নাবিয়ীন’ শব্দের অর্থ করে “নবীদের মোহর”। এরা বুঝাতে চায় যে, রসূলুল্লাহ (স) তাঁর মোহরাংকিত হয়ে আরো অনেক নবী দুনিয়ায় আগমন করবেন। অথবা অন্য কথায় বলা যায়,যতক্ষণ পর্যন্ত কারুর নবুয়্যাত রসূলুল্লাহর মোহরাংকিত না হয়, ততক্ষণ তিনি নবী হতে পারবেন না।
\r\n
কিন্তু “খাতিমুন নাবিয়ীন” শব্দ সম্বলিত আয়াতটি যে ঘটনা পরম্পরায় বিবৃত হয়েছে, তাকে সেই বিশেষ পরিবেশে রেখে বিচার করলে, তা থেকে এ অর্থ গ্রহণের কোন সুযোগই দেখা যায় না। অধিকন্তু এ অর্থ গ্রহণ করার পর এ পরিবেশে শব্দটির ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তাই বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং বক্তব্যের আসল উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়। এটা কি নিতান্ত অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক কথা নয় যে, জয়নবের নিকাহর বিরুদ্ধে কথিত প্রতিবাদ এবংতাথেকে সৃষ্ট নানাপ্রকার সংশয়-সন্দেহের জবাব দিতে দিতে হঠাৎ মাঝখানে বলে দেয়া হলো: মুহাম্মদ (সা) নবীদের মোহর। অর্থাৎ ভবিষ্যতে যত নবী আসবেন তাঁরা সবাই তাঁর মোহরাংকিত হবেন। আগে পিছের এই ঘটনার মাঝখানে একথাটির আকস্মিক আগমন শুধু অবান্তরই নয়, এ থেকে প্রতিবাদকারীদের জবাবে যে যুক্তি পেশ করা হচ্ছিল, তাও দুর্বল হয়ে পড়ে। এহেন পরিস্থিতিতে প্রতিবাদকারীদের হাতে একটা চমৎকার সুযোগ আসতো এবং তারা সহজেই বলতে পারতো যে, আপনার জীবনে যদি এ কাজটা সম্পন্ন না করতেন, তাহলে ভালই হতো, কোন বিপদের সম্ভাবনা থাকতো না, এই বদ রসমটা বিলুপ্ত করার যদি এতোই প্রয়োজন হয়ে থাকে, তাহলে আপনার পরে আপনার মোহরাংকিত হয়ে যেসব নবী আসবেন, এ কাজটা তাঁদের হাতেই সম্পন্ন হবে।
\r\n
উল্লিখিত দলটি শব্দটির আর একটি বিকৃত অর্থ নিয়েছে: ‘খাতিমুন নাবিয়ীন” অর্থ হলো: “আফজালুন নাবিয়ীন।” অর্থাৎ নবুয়্যাতের দরজা উন্মুক্তই রয়েছে, তবে কিনা নবুয়্যাত পূর্ণতা লাভ করেছে রসূলুল্লাহর ওপর। কিন্তু এ অর্থ গ্রহণ করতে গিয়েও পূর্বোল্লিখিত বিভ্রান্তির পুনাবির্ভাবের হাত থেকে নিস্তার নেই। অগ্র-পশ্চাতের সাথে এরও কোন সম্পর্ক নেই।বরং এটি পূর্বাপরের ঘটনা পরম্পরার সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থবহ। কাফের ও মুনাফিকরা বলতে পারতো: ‘জনাব, আপনার চাইতে কম মর্যাদার হলেও আপনার পরে যখন আরোনবী আসছেন, তখন একাজটা না হয় তাদের ওপরই ছেড়ে দিতেন। এই বদ রসমটাও যে আপনাকেই মিটাতে হবে, এরই বা কি এমন যৌক্তিকতা আছে!
\r\n\r\n
আভিধানিক অর্থ
\r\n
তাহলে পূর্বাপর ঘটনাবলীল সাথে সম্পর্কের দিক দিয়ে একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, এখানে খাতিমুন নাবিয়ীন শব্দের অর্থ নবুয়্যাতের সিলসিলার পরিসমাপ্তি ঘোষণা। অর্থাৎ রসূলুল্লাহর (স) পর আর কোন নবী আসবেননা। কিন্তু শুধু পূর্বাপর সম্বন্ধের দিক দিয়েই নয়, আভিধানিক অর্থের দিক দিয়েও এটিই একমাত্র সত্য। আরবী অভিধান এবং প্রবাদ অনুযায়ী ‘খতম’ শব্দের অর্থ হলো: মোহর লাগানো, বন্ধ করা, শেষ পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া এবং কোনো কাজ শেষ করে দায়িত্বথেকে অব্যাহতি লাভ করা।
\r\n
খাতামাল আমাল (******) অর্থ হলো: ফারেগা মিনাল আমল (*****) অর্থাৎ কাজ শেষ করে ফেলেছৈ। খাতামাল এনায়া (*****) অর্থ হলো: পাত্রের মুখ বন্ধ করে দিয়েছে এবং তার ওপর মোহর লাগিয়ে দিয়েছে, যাতে করে তার ভেতর থেকে কোনো জিনিস বাইরে আসতে এবং বাইরে থেকে কিছু ভেতরে যেতে না পারে।
\r\n
খাতামাল কিতাব (*****) অর্থ হলো: পত্র বন্ধ করে তার ওপর মোহর লাগিয়ে দিয়েছে, ফলে পত্রটি সংরক্ষিত হবে।
\r\n
খাতামা আলাল কাল্ব (******) অর্থ হলো: দিলের ওপর মোহর লাগিয়ে দিয়েছে। এরপর বাইরের কোনো কথা আর সে বুঝতে পারবে না এবং তার ভেতরের স্থিতিশীল কোনো কথা বাইরে বেরুতে পারবে না।
\r\n
খিতামুল কুল্লি মাশরুব (****) অর্থ হলো: কোনো পানীয় পান করার পর যে স্বাদ অনুভূত হয়।
\r\n
খাতিমাতু কুল্লি শাইয়েন আকিবাতুহু ওয়া আখিরাতুহ (আরবী ***********) অর্থাৎ] প্রত্যেক জিনিসের খাতিমা অর্থ হলো তার পরিণাম এবং শেষ।
\r\n
খাতামাশ্ শাইয়ে বালাগা আখিরাহ (আরবী ***********) অর্থাৎ কোনো জিনিসকে খতম করার অর্থ হলো তা শেষ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। -খত্মে কোরআন বলতে এই অর্থ গ্রহণ করা হয় এবং এর অর্থের ভিত্তিতেই প্রত্যেক সূরার শেষ আয়াতকে বলা হয় ‘খাওয়াতিম’।
\r\n
খাতিমুল কওমে আখেরুহুম (আরবী *********) অর্থাৎ খাতিমুল কওম অর্থ জাতির শেষ ব্যক্তি (দ্রষ্টব্য: লিসানুল আরব, কামুস এবং আকরাবুল মাওয়ারিদ।) [এখানে আমি মাত্র তিনটি অভিধানের উল্লেখ করলাম। কিন্তু শুধু এই তিনটি অভিধানই কেন, আরবী ভাষার যে কোন নির্ভরযোগ্য অভিধান খুলে দেখুন সেখানে ‘খতম’ শব্দের উপরোল্লিখিত ব্যাখ্যাই পাবেন। কিন্তু ‘খতমে নবুয়্যাত’ অস্বীকারকারীরা খোদার দ্বীনের সুরক্ষিত গৃহে সিঁদ লাগাবার জন্য এক আভিধানিক অর্থকে পুর্ণরূপে এড়িয়ে গেছেন। তারা বলতে চান, কোন ব্যক্তিকে ‘খাতামুশ শোয়ারা’, খাতামুল ফোকাহা’ অথবা ‘খাতামুল মুফাসসিরিন’ বললে এ অর্থ গ্রহণ করা হয় না যে, যাকে ঐ পদবী দেয়া হয়, তার পরে আর কোনো শায়ের কোন ফকিহ অথবা মুফাস্সরি পয়দা হননি। বরং এর অর্থ এই হয় যে, ঐ ব্যক্তির ওপররে উল্লিীখত বিদ্যা অথবা শিল্পের পূর্ণতার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। অথবা কোন বস্তুকে অত্যাধিক ফুটিয়ে তুলবার উদ্দেশ্যে এই ধরনেসর পদবী ব্যবহারের ফলে কখনো খতম-এর আভিধানিক অর্থ ‘পূর্ণ’ অথবা ‘শ্রেষ্ঠ’ হয় না এবং ‘শেষ’ অর্ এর ব্যবহার ত্রুটিপূর্ণ বলৌ গন্য হয় না।
\r\n
একমাত্র ব্যাকরণ-রীতি সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তিই এ ধরনের কথা বলতে পারেন। কোন ভাষারই নিয়ম এ নয় যে, কোন একটি শব্দ তার আসল অর্থের পরিবর্তে কখনো কখনো দূর সম্পর্কের অন্য কোন অর্থে ব্যবহৃরিত হলেসেটাই আসল অর্থে পরিণত হবে এবং আসল আভিধানিক অর্থে তার ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। আপনিয খন কোন আরবের সম্মুখে বলবেন:
\r\n
(জাআ খাতামুল কওম)-তখন কখনো সে মনে করবে না যে গোত্রের শ্রেষ্ঠ অথবাপ কামেল ব্যক্তি এসেছে। বরং সে মনে করবে যে, গোত্রের সবাই এসে গেছে, এমনকি শেষ ব্যক্তিটি পর্যন্তও।]
\r\n
এজন্যই সমস্ত অভিধান বিশারত এবং তাফসীরকারগণ একযোগে ‘খাতিমুন নাবিয়ীনা’ শব্দের অর্থ নিয়েছেন, আখেরুন নাবিয়ীন-অ অর্থাৎ নবীদের শেষ। আরবী অভিধান এবং প্রবাদ অনুযায়ী ‘খাতিম’ –এর অর্থ যাকঘরের মোহর নয়, যা চিঠির ওপর লাগিয়ে চিঠি পোস্ট করা হয়; বরং সেই মোহর যা খামের মুখে এই উদ্দেশ্যে লাগানো হয় যে, তার ভেতর থেকে কোনো জিনিস বাইরে বেরুতে পারবে না এবং বাইরের কোনো জিনিস ভেতরে প্রবেশ করতে পারবে না।
\r\n\r\n
রাসূলুল্লাহর বাণী
\r\n
পূর্বাপর সম্বন্ধ এবং আভিধানিক অর্থের দিক দিয়ে শব্দটির যে অর্থ হয়, রসুলুল্লাহর (স) বিভিন্ন ব্যাখ্যাও এর সমর্থন করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে কতিপয় হাদীসের উল্লেখ করছি:
\r\n
(আরবী *********)
\r\n
(১) রসূলুল্লাহ (স) বলেন: বনি ইসরাঈলদের নেতৃত্ব করতেন্ আল্লাহর রসূলগণ। যখন কোনো নবী ইন্তেকাল করতেন, তখন অন্য কোনো নবী তার স্থলাভিষিক্ত হতেন। কিন্তু আমার পরে কোনো নবীহবে না, হবে শুধু খলিফা।
\r\n
(আরবী *********)
\r\n
(২) রসূলুল্লাহ (স) বলেন: আমি আমার পূর্ববর্তী নবীদের দৃষ্টান্ত হলো এই যে, এক ব্যক্তি একটি দালান তৈরী করলো এবং খুব সুন্দর ও শোভনীয় করে সেটি সজ্জিত করলো।কিন্তু তার এক কোণে একটি ইটের স্থান শূন্য ছিল। দালানটির চতুর্দিকে মানুষ ঘুরে ঘুরে তার সৌন্দর্য দেখে বিস্ময় প্রকাশ করছিল এবং বলছিল, ‘এ স্থানে একটা ইট রাখা হয়নি কেন? কাজেই আমি সেই ইট এবং আমিই শেষ নবী।’ (অর্থাৎ আমার আসার পর নবুয়্যাতের দালান পূর্ণতা লাভ করেছে, এখন এর মধ্যে এমন কোন শূন্যস্থান নেই যাকে পূর্ণ করার জন্য আবার কোনো নবীর প্রয়োজন হবে)।
\r\n
এই ধরনের চারটি হাদীস মুসলিম শরীফে কিতাবুল ফাজায়েলের বাবু খাতিমুন নাবিয়ীনে উল্লিখিত হয়েছে। এবং শেষ হাদীসটিতে এতোটুকুন অংশ বর্ধিত হয়েছে: (আরবী *********) “অতঃপর আমি এলাম এবং আমি নবীদের সিলসিলা খতম করে দিলাম।”
\r\n
হাদীসটি তিরমিজী শরীফে একই শব্দ সম্বলিত হয়ে ‘কিতাবুল মানাকিবের বাবু ফাজলিন নবী’ এবং কিতাবুল আদাবের ‘বাবুল আমসালে’ বর্ণিত হয়েছে।
\r\n
মুসনাদে আবু দাউদ তিয়ালাসীতে হাদীসটি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণিত হাদীসের সিলসিলায় উল্লিখিত হয়েছে এবং এর শেষ অংশটুকু হলো (আরবী *********) “আমার মাধ্যমে নবীদের সিলসিলা খতম করা হলো।”
\r\n
মুসনাদে আহমদে সামান্য শাব্দিক হেরফেরের সাথে এই ধরনের হাদীস হযরত উবাই ইবনে কা’ৎব, হযরত আবু সাঈদ খুদরী এবং হযরত আবু হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে।
\r\n
(আরবী *********)
\r\n
(৩) রসূলুল্লাহ (স) বলেন: “ছ’টা ব্যাপারে অন্যান্য নবীদের ওপর আমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে: (১) আমাকে পূর্ণ অর্থব্যঞ্জক সংক্ষিপ্ত কথা বলার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। (২) আমাকে শক্তিমত্তা ও প্রতিপত্তি দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে। (৩) আমাকে গনীমাতের অর্থ-সম্পদ আমার জন্য হালাল করা হয়েছে। (৪) পৃথিভীর জমীনকে আমার জন্য মসজিদে (অর্থাৎ আমার শরীয়তে নামায কেবল বিশেষ ইবাদতগাহে নয়, দুনিয়ার প্রত্যেক স্থানে পড়া যেতে পারে) এবং মাটিকে পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যমে (শুধু পানিই নয়, মাটির সাহায্যে তায়াম্মুম করেও পবিত্রতা হাসিল অর্থাৎ অজু এবং গোসলের কাজ সম্পন্ন করা যেতে পারে) পরিণত করা হয়েছে। (৫) সমগ্র দুনিয়ার জন্য আমাকে রসূল হিসাবে পাঠানো হয়েছে এবং (৬) আমার ওপর নবীদের সিলসিলা খতম করে দেয়া হয়েছে।”
\r\n
(৪) রসূলুল্লাহ (স) বলেন: ‘রিসালাত এবং নবুয়্যাতের সিলসিলা খতম করে দেয়া হয়েছে। আমার পর কোনো রসূল এবং নবী আসবে না।”
\r\n
(আরবী *********)
\r\n
(৫) রসূলুল্লাহ (স) বলেন: “আমি মুহাম্মদ। আমি আহমদ। আমি বিলুপ্তকারী, আমার সাহায্যে কুফরকে বিলুপ্ত করা হবে। আমি সমবেতকারী, আমার পরে লোকদেরকে হাশরের ময়দানে সমবেত করা হবে (অর্থাৎ আমার পরে শুধু কিয়ামতই বাকি আছে) আমি সবার শেষে আগমনকারী (এবং সবার শেষে আগমনকারী হলো সেই) যার পরে আর নবী আসবে না।”
\r\n
(আরবী *********)
\r\n
রসূলুল্লাহ (স) বলেন: “আল্লাহ নিশ্চয়ই এমন কোনো নবী পাঠাননি যিনি তাঁর উম্মতকে দাজ্জাল সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করেননি। (কিন্তু তাদের যুগে সে বহির্গত হয়নি)। এখন আমিই শেষ নবী এবং তোমরা শেষ উম্মত। দাজ্জাল নিঃসন্দেহে এখন তোমাদের মধ্যে বহির্গত হবে।”
\r\n
(আরবী *********)
\r\n
(৭) আবদুর রহমান ইবনে জোবায়ের বলেন: আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে আস্’কে বলতে শুনেছি যে, একদিন রসূলুল্লাহ (সা) নিজের গৃহ থেকে বের হয়ে আমাদের মধ্যে তাশরীফ আনলেন। তিনি এভাবে আসলেন যেন আমাদের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে যাচ্ছেন। তিনি তিনবার বললেন, আমি উম্মী নবী মুহাম্মদ। অতঃপর বললেন, আমার পর আর কোন নবী নেই।
\r\n
(আরবী *********)
\r\n
(৮) রসূলুল্লাহ (স) বলেন: আমার পরে আর কোনো নবুয়্যাত নেই। আছে শুধু সুসংবাদ দানকারী কথার সমষ্টি। জিজ্ঞেস করা হলো, হে খোদার রসূল, সুসংবাদ দানকারী কথাগুলো কি? জবাবে তিনি বললেন: ভালো স্বপ্ন। অথবা বললেন, কল্যাণময় স্বপ্ন। (অর্থাৎ খোদার অহি নাযীল হবার এখন আর সম্ভাবনা নেই। বড় জোর এতোটুকু বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে যদি কাউকে কোনো ইঙ্গিত দেয়া হয়, তাহলে শুধু ভালো স্বপ্নের মাধ্যমেই তা দেয়া হবে)।
\r\n
(আরবী *********)
\r\n
(৯) রসূলুল্লাহ (স) বলেন: আমার পরে যদি কোনো নবী হতো, তাহলে উমর ইবনে খাত্তাম সে সৌভাগ্য লাভ করতো।
\r\n
(আরবী *********)
\r\n
(১০) রসূলুল্লাহ (স) হযরত আলীকে (রা) বলেন: আমার সাথে তোমার সম্পর্ক মুসার সাথে হারুনের সম্পর্কের মতো। কিন্তু আমার পরে আর কোনো নবী নেই।
\r\n
বুখারী এবং মুসলিম তাবুক যুদ্ধের বর্ণনা প্রসংগেও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মুসনাদে আহমদে এই বিষয়বস্তু সম্বলিত দু’টি হাদীস হযরত সা’দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস থেকে বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে একটি বণনার শেষাংশ হলো: (আরবী *********) “কিন্তু আমার পরে আর কোনো নবুয়্যাত নেই।” আবু দাউদ তিয়ালাসি, ইমাম আহমদ এবং মুহাম্মদ ইসহাক এ সম্পর্কে যে বিস্তারিত বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন তা থেকে জানা যায় যে, তাবুক যুদ্ধে রওয়ানা হবার পূর্বে রসূলুল্লাহ (স) হযরত আলীকে (রা) মদীনা তাইয়েবার হেফাজত এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রেখে যাবার ফায়সালা করেন। এ ব্যাপারটি নিয়ে মুনাফিকরা বিভিন্ন কথা বলতে লাগলো। হযরত আলী (রা) রসূলুল্লাহকে (স) বললেন, ‘হে খোদার রসূল, আপনি কি আমাকে শিশু এবং মেয়েদের মধ্যে ছেড়ে যাচ্ছেন? রসূলুল্লাহ (স) তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন: ‘আমার সাথে তোমার সম্পর্কতো মূসার সাথে হারুনের সম্পর্কের মতো। অর্থাৎ কোহেতুরে যাবার সময় হযরত মূসা (আ) যেমন বনী ইসরাঈলদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য হযরত হারুনকে পেছনে রেখে গিয়েছিলেন অনুরূপভাবে মদীনার হেফাজতের জন্য আমি তোমাকে পেছনে রেখে যাচ্ছি। কিন্তু সংগে সংগে রসূলুল্লাহর মনে এই সন্দেহও জাগলো যে, হযরত হারুনের সংগে এভাবে তুলনা করার ফলে হয়তো পরে এ থেকে কোনো ফিত্না সৃষ্টি হতে পারে। কাজেই পরমুহূর্তেই তিনি কথাটা স্পষ্ট করে দিলেন যে, ‘আমার পর কোনো ব্যক্তি নবী হবে না।’
\r\n
(আরবী *********)
\r\n
(১১) হযরত সাওবান বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (স) বলেন: আর কথা হচ্ছে এই যে, আমার উম্মতের মধ্যে ত্রিশজন মিথ্যাবাদী হবে। তাদের প্রত্যেকেই নিজেকে নবী বলে দাবী করবে। অথচ আমার পর আর কোনো নবী নেই।
\r\n
এই বিষয়বস্তু সম্বলিত আর একটি হাদীস আবু দাউদ ‘কিতাবুল মালাহেমে’ হযরত আবু হোরায় (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিরমিযীও হযরত সাওবান এবং হযরত আবু হোরায় (রা) থেকে এ হাদীস দু’টি বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় বর্ণনাটির শব্দ হলো এই:
\r\n
(আরবী *********)
\r\n
অর্থাৎ এমন কি তিরিশ জনের মতো প্রতারক আসবে। তাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকেই দাবীকরবে যে, সে আল্লাহর রসূল।
\r\n
(১২) রসূলুল্লাহ (স) বলেন: আমাদের পূর্বে যেসব বনি ইসরাঈল গুজরে গেছেন, তাঁদের মধ্যে অনেক লোক এমন ছিলেন, যাঁদের সংগে কালাম করা হয়েছে, অথচ তাঁরা নবী ছিলেন না। আমার উম্মতের মধ্যে যদি এমন কেউ হয়, তাহলে সে হবে উমর।
\r\n
মুসলিমে এই বিষয়বস্তু সম্বলিত যে হাদীস উল্লিখিত হয়েছে, তাতে (****) এর পরিবর্তে (****) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু মুকাল্লিম এবং মুহাদ্দিস শব্দ দুটি সমার্থক। অর্থাৎ এমন ব্যক্তি যার সংগে আল্লাহতায়ালা কালাম করেছেন অথবা যার সাথে পর্দার পেছন থেকে কথা বলা হয়। এ থেকে জানা যায় যে, নবুয়্যাত ছাড়াও যদি এই উম্মতের মধ্যে কেউ আল্লাহর সাথে কালাম করার সৌভাগ্যঅর্জন করেন, তাহলে তিনি একমাত্র হযরত উমরই হবেন।
\r\n
(আরবী *********)
\r\n
(১৩) রসূলুল্লাহ (স) বলেন: আমার পরে আর কোনো নবী নেই এবং আমার উম্মতের পর আর কোনো উম্মত (অর্থাৎ কোনো ভবিষ্যত নবীর উম্মত) নেই।
\r\n
(আরবী *********)
\r\n
(১৪) রসূলুল্লাহ (স) বলেন: আমি শেষ নবী এবং আমার মসজিদ (অর্থাৎ মসজিদে নববী) শেষ মসজিদ। [খত্মে নবুয়্যাত অস্বীকারকারীরা এই হাদীস থেকে প্রমাণ করে যে, রসূলুল্লাহ (স) যেমন তাঁর মসজিদকে শেষ মসজিদ বলেছেন, অথচ এটি শেষ মসজিদ নয়; এর পরও দুনিয়ার বেশুমার মসজিদ নির্মিত হয়েছে অনুরূপভাবে তিনি বলেছেন, যে তিনি শেষ নবী। এর অর্থ হলো এই যে, তাঁর পরেও নবী আসবেন। অবশ্য শ্রেষ্ঠত্বের দিক দিয়ে তিনি হলেন শেষ নবী এবং তাঁর মসজিদ শেষ মসজিদ। কিন্তু আসলে এ ধরনের বিকৃত অর্থই একথা প্রমাণ করে যে, এই লোকগুলো আল্লাহ এবং রসূলের কালামের অর্থ অনুধাবন করার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে। মুসলিম শরীফের যে স্থানে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে সেখানে এই বিষয়ে সমস্ত হাদীস সম্মুখে রাখলেই একথা পরিস্ফূট হবে যে, রসূলুল্লাহ (স) তাঁর মসজিদকে শেষ মসজিদ কোন্ অর্থে বলেছেন। এখানে হযরত আবুহোরায় (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) এবং হযরত মায়মুনার (রা) যে বর্ণনা ইমাম মুসলিম উদ্ধৃত করেছেন, তাতে বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার মাত্র তিনটি মসজিদ এমন রয়েছে যেগুলো সাধারণ মসজিদগুলোর ওপর শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার। সেখানে নামায পড়লে অন্যান্য মসজিদের চেয়ে হাজার গুণ বেশী সওয়াব হাসিল হয় এবং এজন্য একমাত্র এই তিনটি মসজিদে নামায পড়ার জন্য সফর করা জায়েজ। দুনিয়ার অবশিষ্ট মসজিদগুলোর মধ্যে সমস্ত মসজিদকে বাদ দিয়ে বিশেষ করে একটি মসজিদে নামায পড়বার জন্য সেদিকে সফর করা জায়েজ নয়। এর মধ্যে ‘মসজিদুল হারাম’ হলো প্রথম মসজিদ। হযরত ইবরাহীম (আ) এটি বানিয়েছিলেন। দ্বিতীয়টি হলো ‘মসজিদে আক্সা’। হযরত সুলায়মান (আ) এটি নির্মাণ করেছিলেন এবং তৃতীয়টি মদীনা তাইয়েবার ‘মসজিদে নববী’। এটি নির্মাণ করেন রসূলুল্লাহ (স)। রসূলুল্লাহ (স) এরশাদের অর্থ হলো এই যে, এখন যেহেতু আমার পর আর কোনো নবী আসবেনা, সেহেতু আমার মসিজদের পর দুনিয়ায় আর চতুর্থ এমন কোনো মসজিদ নির্মিত হবেনা, যেখানে নামায পড়ার সওয়াব অন্যান্য মসজিদের তুলনায় বেশী হবে এবং সেখানে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে সেদিকে সফর করা জায়েজ হবে।
\r\n
রসূলুল্লাহ (স) নিকট থেকে বহু সাহাবা হাদীসগুলো বর্ণনা করেছেন এবং বহু মুহাদ্দিস অত্যন্ত শক্তিশালী এবং নির্ভরযোগ্য সনদসহ এগুলো উদ্ধৃত করেছেন। এগুলো অধ্যয়ন করার পর স্পষ্ট জানা যায় যে, রসুল্লাহ (স) বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন শব্দের ব্যবহার করে একথা পরিষ্কার করেদিয়েছেন যে, তিনি শেষ নবী। তাঁর পর কোনো নবীআসবে না। নবুয়্যঅতের সিলসিলা তাঁর ওপর খতম হয়ে গেছে এবং তাঁর পরে যে ব্যক্তি রসূল অথবা নবী হবার দাবী করবে, সে হবে দাজ্জাল এবং কাজ্জাব। কোরআনের ‘খাতিমুন নাবিয়ীন’ শব্দের এর চাইতে বেশী শক্তিশালী, নির্ভরযোগ্য এবং প্রমাণ্য ব্যাখ্যা আর কি হতে পারে। রসূলুল্লাহ বাণীই এখঅনে চরম সনদ এবং প্রমাণ। উপরন্তু যখন তা কোরআনের একটি আয়াতের ব্যাখ্যা করে তখন তা আরো অধিক শক্তিশালী প্রমাণে পরিণত হয়। এখন প্রশ্ন হলো এই যে, মুহাম্মদের (স) চেয়ে বেশী কে কোরআনকে বুঝেছে এবং তাঁর চাইতে বেশী এর ব্যাখ্যার অধিকার কার আছে? এমন কে আছে যে, খতমে নবুয়্যাতের অন্য কোনো অর্থ বর্ণনা করবে এবং তা মেনে নেয়া তো দূরের কথা, সে সম্পর্কে চিন্তা করতেও আমরা প্রস্তুত হবো?
\r\n\r\n
সাহাবাদের ইজমা
\r\n
কোরআন এবং সুন্নাহর পর সাহায়ে কেরামের ইজমা বা মতৈক্য হলো তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সমস্ত নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক বর্ণনা থেকে প্রমাণ হয় যে, রসূলুল্লাহর (স)। ইন্তেকালের অব্যবহিত পরেই যেসব লোক নবুয়্যাতের দাবী করে এবং যারা তাদের নবুয়্যাত স্বীকার করে নেয়, তাদের সবার বিরুদ্ধে সাহাবায়ে কেরাম সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ করেছিলেন। এসম্পর্কে মুসাইলামা কাজ্জাবের ব্যাপারটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সে রসূলুল্লাহর (স) নবুয়্যাত অস্বীকার করছিল না; বরং সে দাবী করছিল যে, রসূলুল্লাহ্র নবুয়্যাতে তাকেও অংশীদার করা হয়েছে। রসূলুল্লাহর ইন্তেকালের পূর্বেসে তাঁর নিকট যে চিঠি পাঠিয়েছিল তার আসল শব্দ হলো এই:
\r\n
“অর্থাৎ আল্লাহর রসূল মুসাইলামার তরফ হতে আল্লাহর রসূল মুহাম্মদের নিকট। আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আপনি জেনে রাখুন, আমাকে আপনার সাথে নবুয়্যাতের কাজে শরীক করা হয়েছে।”
\r\n
এভাবে স্পষ্ট করে রিসালাতে মুহাম্মদীকে স্বীকার করে নেবার পরও তাকে ইসলাম বহির্ভূত বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয়েছে। ইতিহাস থেকে একথাও প্রমাণ হয় যে, বনূ হোনায়পা সরল অন্তঃকরণে তার ওপর ঈমান এনেছিল। অবশ্য তারা এই বিভ্রান্তির মধ্যে পড়েছিল যে, মুহাম্মদ (স) নিজেই তাকে তার নবুয়্যাতের কাজে শরীক করেছেন। এ ছাড়াও আর একটা কথা হলো এই যে, মদীনা তাইয়েবা থেকে এক ব্যক্তি কোরআনের শিক্ষা গ্রহণ করেছিল এবং বনু হোনায়ফার নিকটে গিয়ে সে কোরআনের আয়াতকে মুসাইলামার নিকট অবতীর্ণ আয়াতরূপে পেশ করেছিল।
\r\n
(আরবী *********)
\r\n
কিন্তু এ সত্ত্বেও সাহাবায়ে কেরাম তাকে মুসলমান বলে স্বীকার করেননি এবং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। [শেষ নবুয়্যাতে অবিশ্বাসীরা নবী করিমের (স)-হাদীসেরবিপরীতে হযরত আয়েশার (রা) বলে কথিত নিম্নোক্ত বর্ণনা উদ্ধৃতি দেয়: “বল নিশ্চয়ই তিনি খাতামুন নাবিয়ীন, এ কথা বলো না যে তার পর নবী নেই।” প্রথমত নবী করিমের (স) সুস্পষ্ট আদেশকে অস্বীকার করার জন্রহযরত আয়েশার (রা) উদ্ধৃতি দেয়া একটা ধৃষ্টতা। অধিকন্তু হযরত আয়েশার (রা) বলে কথিত উপরোক্ত উদ্ধৃতি মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়। হাদীস শাস্ত্রের কোন প্রামাণিক গ্রন্থেই হযরত আয়েশার (রা) উপরোক্ত উক্তির উল্লেখ নেই। কোন বিখ্যাত হাদীস লিপিবদ্ধকারী এ হাদীসটি লিপিবদ্ধ বা উল্লেখ করেননি।
\r\n
উপরোক্ত হাদীসটি ‘দার-ই মানহুর’ নামক তাফসীর এবং ‘তাকমিলাহ মাজমা-উল-বিহার’ নামক অপরিচিত হাদীস সংকলণ থেকে নেয়া হয়েছে; কিন্তু এর উৎপত্তি বা বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে কিছুই জানা নেই। রসূল (স) সুস্পষ্ট হাদীস বা বিখ্যাত হাদীস বর্ণনাকারীরা খুবই নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে বর্ণনা করেছেন, তাকে অস্বীকার করার জন্য হযরত আয়েশার (রা) কথার উল্লেখ চূড়ান্ত ধৃষ্টতা মাত্র।] অতঃপর একথা বলার সুযোগ নেই যে, ইসলাম বহির্ভূত হবার কারণে সাহাবাগণ তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেননি বরং বিদ্রোহ ঘোষণা করার কারণেই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয়েছিল। ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে বিদ্রোহী মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হলেও তাদের যুদ্ধবন্দীদেরকে গোলামে পরিণত করা যেতে পারে না। বরং শুধু মুসলমানই নয়, জিম্মীও (অমুসলিম) বিদ্রোহ ঘোষণা করলে, গ্রেফতার করার পর তাকে গোলামে পরিণত করা জায়েজ নয়। কিন্তু মুসাইলামা এবং তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রা) ঘোষণা করেন যে, তাদের মেয়েদের এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেদেরকে গোলাম বানানো হবে এবং গ্রেফতার করার পর দেখা গেলো, সত্যি সত্যিই তাদেরকে গোলাম বানানো হয়েছে। হযরত আলী (রা) তাদের মধ্যথেকেই জনৈক যুদ্ধ বন্দিনীর মালিক হন। এই যুদ্ধ বন্দিনীর গর্ভজাত পুত্র মুহাম্মদ ইবনে হানিফাই হলেন পরবর্তীকালে ইসলামের ইতিহাসে সর্বজন পরিচিত ব্যক্তি।
\r\n
(আরবী *********) এ থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সাহাবায়ে কেরাম যে অপরাধের কারণে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, তা কোন বিদ্রোহের অপরাধ ছিলনা বরং সে অপরাধ ছিল এইযে, এক ব্যক্তি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পরে নবুয়্যাতের দাবী করে এবং অন্য লোকেরা তার নবুয়্যাতের ওপর ঈমান আনে। রসূলুল্লাহর ইন্তেকালের অব্যবহিত পরেই এই পদক্ষেপ গৃহীত হয়। এর নেতৃত্ব করেন হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রা) এবং সাহাবাদের সমগ্র দলটি একযোগে তাঁর নেতৃত্বাধীনে এ কাজে অগ্রসর হন। সাহাবাদের ইজমার এর চাইতে সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত আর কি হতে পারে।
\r\n\r\n
আলেম সমাজের ইজমা
\r\n
শরীয়াতে সাহাবাদের ইজমার পর চতুর্থ পর্যায়ের সব চাইতে শক্তিশালী দলিল হলো সাহাবাগণের পরবর্তী কালের আলেম সমাজের ইজমা। এদিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায়, হিজরীর প্রথম শতাব্দী থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত প্রত্যেক যুগের এবং সমগ্র মুসলিম জাহানের প্রত্যেক এলাকার আলেম সমাজ হামেশাই এ ব্যাপারে একমত রয়েছেন যে,
\r\n
“মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পরে কোনো ব্যক্তি নবী হতে পারে না। এবং তাঁর পর যে ব্যক্তি নবুয়্যাতের দাবী করবে এবং যে ব্যক্তি এই মিথ্যা দাবীকে মেনে নেবে, সে কাফের এবং মিল্লাতে ইসলামের মধ্যে তার স্থান নেই।”
\r\n
এ ব্যাপারে আমি কতিপয় প্রমাণ পেশ করছি:
\r\n
(১) ইমাম আবু হানিফার যুগে (৮০-১৫০হি) এক ব্যক্তি নবুয়্যাতের দাবী করে এবংবলে: “আমাকে সুযোগ দাও, আমি নবুয়্যাতের সংকেত চিহ্ন পেশ করব।”
\r\n
একথা শুনে ইমাম সাহেব বলেন: যে ব্যক্তি এর কাছ থেকে নবুয়্যাতের কোনো সংকেত চিহ্ন তলব করবে সেও কাফের হয়ে যাবে। কেননা রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন: (******) আমার পর আর কোন নবী নেই।
\r\n
(আরবী *********)
\r\n
(২) আল্লামা ইবনে জারীর তাবারী (২২৪-৩১০ হি) তাঁর বিখ্যাত কোরআনের তাফসীরে (আরবী *******) আয়াতটির বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন:
\r\n
(আরবী *******)
\r\n
অর্থাৎ “যে নবুয়্যাতকে খতম করে দিয়েছে এবং তার ওপর মোহর লাগিয়ে দিয়েছে, কিয়ামত পর্যন্ত এর দরজা আর কারুর জন্য খুলবেনা।” (তাফসীরে ইবনে জারীর, দ্বাবিংশ খণ্ড, ১২ পৃষ্ঠা)
\r\n
(৩) আল্লামা ইবনে হাজাম আন্দালুসী (৩৮৪-৪৫৬ হি) লিখেছেন: নিশ্চয়ই রসূলুল্লাহর (স) পর অহীর সিলসিলা খতম হয়ে গেছে। এর সপক্ষে যুক্তি এই যে, অহী আসে একমাত্র নবীর কাছে এবং মহান আল্লাহ বলেছেন, “মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারুর পিতা নয়। কিন্তু সে আল্লাহর রসূল এবং সর্বশেষ নবী।” (আল মুহাল্লা, প্রথম খণ্ড, ২৬ পৃষ্ঠা)।
\r\n
(৪) ইমাম গাজ্জালী (৪৫০-৫০৫ হি) বলেন: “সমগ্র মুসলিম সমাজ এই বাক্য থেকে একযোগে এই অর্থ নিয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (স) তাঁর পরে কোন রসূল এবং নবী না আসার কথাটি স্পষ্ট করে ব্যক্ত করেছেন এবং এর কোনো বিশেষ অর্থ গ্রহণ অথবা বাক্যটিকে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে এবং টেনে-হিঁচড়ে এ থেকে কোনো দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণের সুযোগই এখানে নেই। অতঃপর যে ব্যক্তি টেনে-হিঁচড়ে এথেকে কোনো দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করবে, তার বক্তব্য হবে উদ্ভট ও নিছক কল্পনা প্রসূত এবং তার বক্তব্যের ভিত্তিতে তার ওপর কুফরীর ফতোয়া দেবার ব্যাপারে কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই। কেননা কোরআনে যে আয়াত সম্পর্কে সমগ্র মুসলিম সমাজ একযোগে এই মত পোষণ করেন যে, তার কোনো দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করা যেতে পারে না এবং টেনে-হিঁচড়ে অন্য কোনো অর্থও তা থেকে বের করা যেতে পারেনা, সে আয়াতকে সে মিথ্যা প্রমাণ করেছে।” (আল ইকতিসাদ ফিল ইতিকাদ, ১১৩ পৃষ্ঠা)
\r\n
(৫) মুহিউদ সূন্নাহ বাগাবী (মৃত্যু ৫১০ হি) তাঁর তাফসীরে আলিমুত তানজীল-এ লিখেছেন: রসূলুল্লাহ্র (স) মাধ্যমে আল্লাহতায়ালা নবুয়্যাতের সিলসিলা খতম করেছেন। কাজেই তিনি সর্বশেষ নবী এবং ইবনে আব্বাস বলেন যে, আল্লাহতায়ালা এই আয়াতে ফায়সালা করে দিয়েছেন যে, মুহাম্মদের (স) পর কোন নবী নেই। (তৃতীয় খণ্ড, ১৫৮ পৃষ্ঠা)
\r\n
(৬) আল্লাম জামাখশরী (৪৬৭-৫৩৮ হি) তাফসীরৈ কাশ্শাফে লিখেছেন: যদি তোমরা বল যে, রসূলুল্লাহ (স) শেষ নবী কেমন করে হলেন, কেননা হযরত ঈসা(আ) শেষ যুগে অবতীর্ণ হবেন, তাহলে আমি বলবোযে, রসূলুল্লাহর শেষ নবী হবার অর্থ হলো এই যে, তাঁর পরে আর কাউকে নবীর পদে প্রতিষ্ঠিত করা হবেনা। হযরত ঈসাকে (আ) রসূলুল্লাহর (স) পূর্বে নবী বানানো হয়েছে। অবতীর্ণ হবার পর তিনি রসূলুল্লাহর অনুসারী হবেন এবং তাঁর কেবলার দিকে মুখ করে নামায পড়বেন। অর্থাৎ তিনি হবেন রসূলুল্লাহর উম্মতের মধ্যে শামিল। (দ্বিতীয় খণ্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা)
\r\n
(৭) কাজী ইয়অয (মৃত্যু: ৫৪৪ হি) লিখেছেন: যে ব্যক্তি নিজে নবুয়্যাতের দাবী করে অথবাএ কথাকে বৈধ মনে করে যে, যে কোনো ব্যক্তি নিজের প্রচেষ্টায় নবুয়্যাত হাসিল করতে পারে এবং অন্তত পরিশুদ্ধির মাধ্যমে নবীর পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে (যেমন কোনো কোনো দার্শনিক এবং বিকৃতমনা সূফী মনে করেন) এবং এভাবে যে ব্যক্তি নবুয়্যাতের দাবীকরেনা অথচ একথার দাবী জানায় যে, তার ওপর অহী নাযিল হয়, -এ ধরনের সমস্ত লোক কাফের এবং তারা রসূলুল্লাহর নবুয়্যাতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে। কেননা তিনি খবর দিয়েছেন যে, তিনি শেষ নবী এবং তাঁর পর কোনো নবী আসবে না এবং তিনি আল্লাহতায়ালার তরফ থেকে এ খবর পৌঁছিয়েছেন যে, তিনি নবুয়্যাতকে খতম করে দিয়েছেন এবং সমগ্র মানব জাতির জন্য তাঁকে পাঠানো হয়েছে। সমগ্র মুসলিম সমাজ এ ব্যাপারে একমত যে, এখানে কথাটির বাহ্যিক অর্থটিই গ্রহণীয় এবং এ ব্যাপারে একমত যে, এখানে কথাটির বাহ্যিক অর্থটিই গ্রহণীয় এবং এর দ্বিতীয় কোনো অর্থ গ্রহণ করার সুযোগই এখানে নেই। কাজেই উল্লিখিত দলগুলোর কাফের হওয়া সম্পর্কে কোরআন, হাদীস এবং ইজমার দৃষ্টিতে কোনো সন্দেহ নেই। (শিফা দ্বিতীয় খণ্ড, ২৭০-২৭১ পৃষ্ঠা)
\r\n
(৮) আল্লামা শাহারিস্তানী (মৃত্যু: ৫৪৮ হি) তাঁর মশহুর কিতাব আল মিলাল ওয়ান নিহালে লিখেছেন: এবং যে এভাবেই বলে যে, “মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পরও কোনো নবী আসবে (হযরত ঈসা (আ) ছাড়া) তাহলে তার কাফের হওয়া সম্পার্কে যে কোন দু’জন ব্যক্তি মধ্যেই কোনো মতবিরোধ থাকতে পারে না। (তৃতীয় খণ্ড ২৪৯ পৃষ্ঠা)
\r\n
(৯) ইমাম রাজী (৫৪৩-৬০৬ হি) তাঁর তাফসীরে কবীরে ‘খাতিমুন নাবিয়ীন’ শব্দের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন: এ বর্ণনায় খাতিমুন নামিয়ীন শব্দ এজন্য বলা হয়েছে যে, যে নবীর পর অন্য কোনো নবী আসবেন তিনি যদি উপদেশ এবং নির্দেশাবলীর ব্যাখ্যার ব্যাপারে কিছু অতৃপ্তি রেখে যান, তাহলে তাঁর পর আগমনকারী নবীতা পূর্ণ করতে পারেন। কিন্তু যার পর আর কোনো নবী আসবে না, তিনি নিজের উম্মতের ওপর খুব বেশী স্নেহশীল হন এবং তাদেরকে সুস্পষ্ট নেতৃত্ব দান করেন। কেননা তাঁর দৃষ্টান্ত এমন একটি পিতার ন্যায় যিনি জানেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর পুত্রের দ্বিতীয কোনো অভিভাবক এবং পৃষ্ঠপোষক থাকবে না। (ষষ্ঠ খণ্ড, ৫৮১ পৃষ্ঠা)
\r\n
(১০) আল্লামা বায়জাবী (মৃত্যু: ৬৮৫ হি) তাঁর তাফসীরে আনওয়ারুত্ তানজীল-এ লিখেছেন: অর্থাৎ তিনিই শেষ নবী। তিনি নবীদের সিলসিলা খতম করে দিয়েছেন। অথবা তাঁর কারণেই নবীদের সিলসিলার ওপর মোহর লাগানো হয়েছে। এবং তাঁর পর হযরত ঈসার (আ) নাযীল হবার কারণে খতমে নবুয়্যাতের ওপর কোনো দোষ আসছে না। কেননা তিনি রসূলুল্লাহর (স) দ্বীনের মধ্যেই নাযিল হবেন। (চতুর্থ খণ্ড, ১৬৪ পৃষ্ঠা)
\r\n
(১১) আল্লামা হাফিজ উদ্দীন নাসাফী (মৃত্যু: ৮১০ হি) তাঁর তাফসীরে মাদারেকুত তানজীল-এ লিখেছেন: এবং রসূলুল্লাহ (স) খাতিমুন নাবিয়ীন। অর্থাৎ তিনিই সর্বশেষ নবী। তাঁর পর আর কোনো ব্যক্তিকে নবী করা হবে না। হযরত ঈসা (আ) হলো এই যে, তাঁকে রসূলুল্লাহ্র পূর্বে নবীর পদে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। এবং পরে যখন তিনি নাযিল হবেন, তখন তিনি হবেন রসূলুল্লাহর শরীয়তের অনুসারী। অর্থাৎ তিনি হবেন রসূলুল্লাহর উম্মত। (৪৭১ পৃষ্ঠা)
\r\n
(১২) আল্লামা আলাউদ্দীন বাগদাদী (মৃত্যু: ৭২৬ হি) তাঁর তাফসীরে ‘খাজিন’-এ লিখেছেন: (আরবী *****) অর্থাৎ আল্লাহর রসূলুল্লাহ্র নবুয়্যাত খতম করে দিয়েছেন। কাজেই তাঁর পরে আর কোনো নবুয়্যাত নেই এবং এ ব্যাপারে কেউ তাঁর অংশীদারও নয়।
\r\n
(আরবী ********) অর্থাৎ আল্লাহ একথা জানেন যে, তাঁর পর আর কোনো নবী নেই’ (৩৭১-৪৭২ পৃষ্ঠা)
\r\n
(১৩) আল্লামা ইবনে কাসীর (মৃত্যু: ৭৭৪ হি) তাঁর মশুহর তাফসীরে লিখেছেন: অতঃপর আলোচ্য আয়াত থেকে একথা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, যখন রসূলুল্লাহ্র পর কোনো নবী নেই, তখন অপর কোনো রসূলের প্রশ্নই উঠতে পারে না। কেননা রিসালাত একটা বিশেষ পদমর্যাদা এবং নবুয়্যাতের পদমর্যাদা এর চাইতে বেশী সাধারণধর্মী। প্রতেক রসূল নবী হন, কিন্তু প্রত্যেক নবী রসূল হন না। রসূলুল্লাহর পর যে ব্যক্তিই এই পদমর্যাদার দাবী করবে, সেই হবে মিথ্যাবাদী, প্রতারক, দাজ্জাল এবং গোমরাহ। যতোই সে প্রাকৃতিক নিয়মে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ও যাদুর ক্ষমতাসম্পন্ন হোক না কেন, তার দাবী মানবার নয়। কিয়ামত পর্যন্ত যেসব ব্যক্তি এই পদমর্যাদার দাবী করবে, তাদের প্রত্যেকেরই অবস্থা হবে এই ধরনের। (তৃতীয় খণ্ড, ৪৯৩-৪৯৪ পৃষ্ঠা)
\r\n
(১৪) আল্লামা জালালুদ্দীন সিউতী (মৃত্যু: ৯১১ হি) তাঁর তাফসীরে জালালায়েন-এ লিখেছেন: ‘অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা জানেন যে রসূলুল্লাহর (স) পর আর কোনো নবী নেই। এবং হযরত ঈসা (আ) নাযীল হবার পর রসূরুল্লাহর শরীয়ত মোতাবেকই আমল করবেন।’ (৭৬৮ পৃষ্ঠা)
\r\n
(১৫) আল্লামা ইবনে নাজীম (মৃত্যু: ৯৭০ হি) উসুলে ফিকাহর বিখ্যাত পুস্তক আল ইশবাহ ওয়ান নাজায়েরে ‘কিতাবুস সিয়ারের’ ‘বাবুর রুইয়ায়’ লিখেছেন: যদি কেউ একথা না মনে করে যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম শেষ নবী, তাহলে সে মুসলমান নয়। কেননা কথাগুলো জানা এবং স্বীকার করে নেয়া দ্বীনের অত্যধিক প্রয়োজনের মধ্যে শামিল। (১৭৯ পৃষ্ঠা)
\r\n
(১৬) মুল্লা আলী কারী (মৃত্যু: ১০১৬ হি) ‘শারহে ফিকহে আকবর’-এ লিখেছেন: ‘আমাদের রসূলের (স) পর অন্য কোনো ব্যক্তির নবুয়্যাতের দাবী করা সর্ববাদীসম্মতভঅবে কুফর। (২০২ পৃষ্ঠা)
\r\n
(১৭) শায়খ ইসমাইল হাক্কী (মৃত্যু: ১১৩৭ হি) তাফসীরে রুহুল বয়ান-এ উল্লিখিত ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেছেন: আলেম সমাজ ‘খাতাম’ শব্দটির তে-এর উপর জবর লাগিয়ে পড়েছেন, -এর অর্থ হয় খতম করবার যন্ত্র, যার সাহায্যে মোহর লাগানো হয়।
\r\n
অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (স) সমস্ত নবীর শেষে এসেছেন এবং তাঁর সাহায্যে নবীদের সিলসিলার ওপর মোহর লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। ফারসীতে আমরা একে বলবো ‘মোহর পয়গম্বর’ অর্থাৎ তাঁর সাহায্যে নবুয়্যাতের দরজার মোহর লাগিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং পয়গম্বরদের সিলসিলা খতম করে দেয়া হয়েছে। অন্য পাঠকরাতো এর নীচে জের লাগিয়ে পড়েছেন ‘খাতিমুন নাবিয়ীন’। অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ ছিলেন মোহর দানকারী। অন্য কথায় বলা যাবে পয়গম্বরদের ওপর মোহরকারী। এভাবে এ শব্দার্থ ‘খাতাম’-এর সমার্থক হয়ে দাঁড়াবে। তাহলে রসূলুল্লাহর (স) পর তাঁর উম্মতের আলেম সমাজ তাঁর কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাবেনএকমাত্র তাঁর প্রতিনিধিত্ব। তাঁর ইন্তেকালের সাথে সাথেই নবুয়্যাতের উত্তরাধিকারেরও পরিসমাপ্তি ঘটেছে এবং তাঁর পরে হযরত ঈসার (আ) নাযিল হবার ব্যাপারটি তাঁর নবুয়্যাতকে ত্রুটিযুক্ত করবেনা। কেননা খাতিমুন নাবিয়ীন হবার অর্থ হলো এই যে, তাঁর পর আর কাউকে নবী বানানো হবেনা এবং হযরত ঈসাকে (আ) তাঁদের পূর্বেই নবী বানানো হয়েছে। কাজেই তিনি রসূলুল্লাহ্র অনুসারীর মধ্যে শামিল হবেন, রসূলুল্লাহর কিবলার দিকে মুখ করে নামায পড়বেনএবং তাঁরই উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হবেন। তখন হযরত ঈসার (আ) নিকট অহী নাযীল হবেনা এবং তিনি কোনোনতুন আহকামও জারি করবনে না, বরং তিনি হবেন রসূলুল্লাহর প্রতিনিধি। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এ ব্যাপারে একমত যে, আমাদের নবীর পর আর কোনো নবী নেই। কেননা আল্লাহতায়ালা বলেছেন: মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম শেষ নবী। এবং রসূলুল্লাহ বলেছেন: আমার পরে কোনো নবী নেই। কাজেই এখনযে বলবে যে মুহাম্মদ (স) এর পর নবী আছে, তাকে কাফের বলা হবে। কেননা সে কোরআনকে অস্বীকার করেছে এবং অনুরূপভবেসেই ব্যক্তিকেও কাফের বলা হবে যে এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করবে। কেননা সুস্পষ্ট যুক্তি প্রমাণের পর হক বাতিল থেকে পৃথক হয়ে গেছে। এবং যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (স)-এর পর নবুয়্যাতের দাবী করবে, তার দাবী বাতিল হয়ে যাবে। (দ্বাবিংশ খণ্ড, ১৮৮ পৃষ্ঠা)
\r\n
(১৮) শাহানশাহ আওরঙ্গজেব আলমগীরের নির্দেশে বার’শ হিজরীতে পাক-ভারতের বিশিষ্ট আলেমগণ সম্মিলিতভাবে ‘ফতোয়া আলমগিরী’ নামে যে কিতাবটি লিপিবদ্ধ করেন তাতে উল্লিখিত হয়েছে: যদি কেউ মনে করে যে, মুহাম্মদ (স) শেষ নবী নয়, তাহলেসে মুসলমান নয় এবং যদি সে বলে যে, সে আল্লাহর রসূল অথবা পয়গম্বর, তাহলে তার ওপর কুফরীর ফতোয়া দেয়া হবে। (দ্বিতীয়খণ্ড, ২৬৩ পৃষ্ঠা)
\r\n
(১৯) আল্লামা শওকানী (মৃত্যু: ১২৫৫ হি) তাঁর তাফসীর ফাতহুল কাদীরে লিখেছেন: সমগ্র মুসলিম সমাজ ‘খাতিম’ শব্দটির তে-এর নীচে জের লাগিয়ে পড়েছেন এবং একমাত্র আসে জবরের সাথে পড়েছেন। প্রথমটা অর্থ হলো এই যে, রসূলুল্লাহ সমস্ত পয়গম্বরকে খতম করেছেন অর্থাৎ তিনি সবার শেষে এসেছেন এবং দ্বিতীয়টির অর্থ হলো এই যে, তিনি সমস্ত পয়গম্বরদের জন্য মোহর স্বরূপ্ এবং এর সাহায্যে নবীদের সিলসিলা মোহর এঁটে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ফলে তাঁদের দলীটর সর্বাঙ্গসুন্দর হয়েছে। (চতুর্থ খণ্ড, ২৭৫ পৃষ্ঠা)
\r\n
(২০) আল্লামা আলুসি (মৃত্যু: ১২৮০ হি) তাফসীরে রুহুল মায়ানীতে লিখেছেন: নবী শব্দটি রসূলের চাইতে বেশী সাধারণ অর্থব্যঞ্জক। কাজেই রাসূলের খাতিমুন নাবিয়ীন হবার অর্থ হলো এই যে, তিনি খাতিমুল মুরসালীনও। তিনি শেষ নবী এবং শেষ রসূল-একথার অর্থ হলো এই যে, দুনিয়ায় তাঁর নবুয়্যাতের গুণে গুণান্বিত হবার পরেই মানুষ এবং জিনের মধ্য থেকে এ গুণটি চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। (দ্বাবিংশ খণ্ড, ৩২ পৃষ্ঠা)
\r\n
রসূলুল্লাহর পর যে ব্যক্তি নবুয়্যাতের অহীর দাবী করবে, তাকে কাফের বলে গণ্য করা হবে। এ ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে দ্বিমতের অবকাশ নেই। (দ্বাবিংশ খণ্ড, ৩৮ পৃষ্ঠা)
\r\n
“রসূলুল্লাহ শেষ নবী-একথাটি কোরআন দ্ব্যার্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছে, রসূলুল্লাহর সুন্নাত এটিকে সুস্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করেছে এবং সমগ্র মুসলিম সমাজ এর ওপর আমল করেছে। কাজেই যে ব্যক্তি এর বিরোধী কোনো দাবী করবে, তাকে কাফের বলে গণ্য করা হবে।” (দ্বাবিংশ খণ্ড, ৩৯ পৃষ্ঠা)
\r\n
বাংলা পাক-ভারত উপমহাদেশ থেকে মররোক্ত ও আন্দালুসিয়া এবং তুর্কী থেকে ইয়েমেন পর্যন্ত মুসলিম জাহানের শ্রেষ্ঠ আলেম, ফকীহ, মুহাদ্দিস এবং তাফসীরকারগণের ব্যাখ্যা এবং মতামত আমি এখানে উল্লেখ করলাম। তাঁদের নামের সাথে সাথে তাঁদের জন্ম এবং মৃত্যু তারিখও উল্লেখ করেছি। এ থেকেই ধারণা করা যাবে যে, হিজরীর প্রথম শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইসলামের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ আলেমগণ এর মধ্যে শামিল আছেন। হিজরীর চতুর্দশ শতাব্দীর আলেম সমাজের মতামতও আমি এখানে উল্লেখ করতে পারতাম, কিন্তু ইচ্ছা করেই তাঁদেরকে ছেড়ে দিয়েছি। কেননা তাঁরা মীর্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর সমসাময়িক। এবং হয়তো অনেকে বলতে পারেন যে, মীর্জা সাহেবের বিরোধিতার মনোভাব নিয়েই তাঁরা খতমে নবুয়্যাতের এই অর্থ বিবৃত করেছেন। এজন্য মীর্জা সাহেবের পূর্ববর্তী যুগের আলেম সমাজের মতামতের উদ্ধৃতিই এখানে পেশ করেছি- যেহেতু মীর্জা সাহেবের সাথে তাঁদের বিরোধের প্রশ্নই উঠতে পারে না। এইসব মতামত থেকে একথা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, হিজরীর প্রথম শতাব্দী থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত সমগ্র মুসলিমজাহান একযোগে খাতিমুন নাবিয়ীন শব্দের অর্থ নিয়েছে শেষ নবী। প্রত্যেক যুগের মুসলমানই এই একই আকীদা পোষণ করেছেন যে, রসূলুল্লাহর পর নবুয়্যাতের দরজা চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে। একথা তাঁরা একযোগে স্বীকার করে নিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পর নবী অথবা রসূল হবার দাবী করেএবং যে তার দাবীকে মেনে নেয়, সে কাফের হয়ে যায়, এ ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে কোনো যুগে তুচ্ছতম মতবিরোধেরও সৃষ্টি হয়নি। কাজেই এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেক বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিই ফায়সালা করতে পারেন যে, ‘খাতিমুন নাবিয়ীন’ শব্দের যে অর্থ আরবী অভিধান থেকে প্রমাণিত হয়, কোরআনের আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনা থেকে যে অর্থ প্রতীয়মান হয়, রসূলুল্লাহ (স) নিজেই যা ব্যাখ্যা করেছেন, সাহাবায়ে কেরাম যে সম্পর্কে মতৈক্য পোষণ করেছেন এবং সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত সমগ্র মুসলিমসমাজ একযোগে দ্ব্যার্থহীনভাবে যা স্বীকার করে আসছেন, তার বিপক্ষে দ্বিতীয় কোনো অর্থ গ্রহণ অর্থাৎ কোনো নতুন দাবীদারের জন্য নবুয়্যাতের দরজা উন্মুক্ত করার অবকাশ ও সুযোগ থাকে কি? এবং এই ধরনের লোকদেরকে কেমন করে মুসলমান বলে স্বীকার করা যায়, যারা নবুয়্যাতের দরজা উন্মুক্ত করার নিছক ধারণাই প্রকাশ করেনি বরং ঐ দরজা দিয়ে এক ব্যক্তি নবুয়্যাদের দালানে প্রবেশ করেছে এবং তারা তার ‘নবুয়্যাতের’ ওপর ঈমান পর্যন্ত এনেছে?
\r\n
এ ব্যাপরে তিনটি কথা বিবেচনা করতে হবে।
\r\n\r\n
আমাদের ঈমানের সংগে খোদার কি কোনো শত্রুতা আছে?
\r\n
প্রথম কথা হলো এই যে, নবুয়্যাতের ব্যাপারটি বড়ই গুরুত্বপূর্ণ। কোরআনের দৃষ্টিতে এ বিষয়টি ইসলামের বুনিয়াদী আকিদার অন্তর্ভুক্ত, এটি স্বীকার করার বা না করার ওপর মানুষের ঈমান ও কুফরী নির্ভর করে। যদি কোনো ব্যক্তি নবী থাকেন এবং লোকেরা তাঁকে না মানে, তাহলে তারা কাফের হয়ে যায়। আবার কোনো ব্যক্তি নবী না হওয়া সত্ত্বেও যারা তাকে নবী বলে স্বীকার করে, তারাও কাফের হয়ে যায়। এ ধরনের জটিল পরিস্থিতিতে আল্লাহ তায়ালার নিকট থেকে যে কোনো প্রকার অসতর্কতার আশা করা যায় না। যদি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পর কোনো নবী আসার কথা থাকতো তাহলে আল্লাহ নিজেই কোরআনে স্পষ্ট এবং দ্ব্যার্থহীন ভাষায় তা ব্যক্ত করতেন, রসূলুল্লাহর মাধ্যমে প্রকাশ্যভাবে তা ঘোষণা করতেন এবং রসূলুল্লাহ কখনো এ দুনিয়া থেকে তাশরীফ নিয়ে যেতেন না; যতক্ষণ না তিনি সমগ্র উম্মতকে এ ব্যাপারে পুরোপুরি অবগত করতেন যে, তাঁর পর আরো নবী আসবেন এবং আমরা সবাই তাঁদেরকে মেনে নিতে বাধ্য থাকবো। রসূলুল্লাহর পর নবুয়্যাতের দরজা উন্মুক্ত থাকবে এবং এই দরজা দিয়ে কোনো নবী প্রবেশ করবে, যার ওপর ঈমান না আনলে আমরা মুসলমান থাকতে পারি না অথচ আমাদেরকে এ সম্পর্কে শুধু বেখবরই রাখা হয়নি বরং বিপরীতপক্ষে আল্লাহ এবং তাঁর রসূল একযোগে এমন সব কথা বলেছৈন, যার ফলে তের’শ বছর পর্যন্ত সমস্ত উম্মত একথা মনে করেছিলো এবং আজও মনে করে যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পর আর কোনো নবী আসবেন না- আমাদের সাথে আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের এ ধরনের ব্যবহার কেন? আমাদের দ্বীন এবং ঈমানের বিরুদ্ধে আল্লাহ এবংতাঁর রসূলের তো কোনো শত্রুতা নেই!
\r\n
তর্কের খাতিরে যদি একথা মেনে নেয়া যায় যে, নবুয়্যাতের দরজা উন্মুক্ত আছে এবং কোনোনবী আসার পর আমরা যদি নির্ভয়ে এবং নিশ্চিন্তে তাঁকে অস্বীকার করে বসি, তাহলে ভয় থাকতে পারে একমাত্র আল্লাহর দরবারে জিজ্ঞাসাবাদের! কিন্তু কিয়ামতের দিনতিনি আমাদের নিকট থেকে এ সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করলে, আমরা সোজাসুজি উল্লিখিত রেকর্ডগুলো তাঁর আদালতে পেশকরবো। এ থেকে অন্তত প্রমাণহয়েযাবে যে, (মায়াযাল্লাহ) আল্লাহ্র কিতাব এবং রসূলের সুন্নাতই আমাদেরকে এই কুফরীর মধ্যে নিক্ষেপ করছে! আমরা নির্ভয়ে বলতে পারি যে, এইসব রেকর্ড দেখার পর কোনো নতুন নবীর ওপর ঈমান না আনার জন্য আল্লাহ আমাদেরকে শাস্তি দেবেন না। কিন্তু যদি সত্যি সত্যি নবুয়্যাতের দরজাবন্ধ গিয়ে থাকে এবং কোনো নবুন নবী যদি না আসতে পারে এবং এইসব সত্ত্বেও কেউ কোনো নবুয়্যাতের দাবীদারদের ওপর যদি ঈমান আনে, তাহলে তার চিন্তা করা উচিত যে, এই কুফরীর অপরাধ থেকে বাঁচার জন্য সে আল্লাহর দরবারে এমনকি রেকর্ড পেশ করতে পারবে, যার ফলে সে মুক্তি লাভের আশা করতে পারে। আদালতে হাযির হবার পূর্বে তার নিজের জবাবদিহির জন্য সংগৃহীত দলিল প্রমাণগুলো এখানেই বিশ্লেষণ করে নেয়া উচিত। এবং আমরা যেসব দলিল-প্রমাণ পেশ করেছি, তার পরিপ্রেক্ষিতে তার বিচার করা উচিত যে, নিজের জন্য যে সাফাইয়ের ওপর নির্ভল করে সে একাজ করছে, কোনো বুদ্ধিশান ব্যক্তি কি এর ওপর নির্ভর করে কুফরীর শাস্তি ভোগ করার বিপদকে স্বাগতম জানাতে পারে?
\r\n\r\n
এখন নবীর প্রয়োজনটা কেন?
\r\n
দ্বিতীয় কথা হলো এই যে, ইবাদাত এবংনেক কাজে তরক্কী করে কোনো ব্যক্তি নিজের মধ্যে নবুয়্যাতের গুণ পয়দা করতে পারে না। নবুয়্যাতের যোগ্যতা কোনো অর্জন করার জিনিস নয়। কোনো বিরাট খেদমতের পুরস্কার স্বরূপ মানুষকে নবুয়্যাত দান করা হয় না। বরং বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে আল্লাহতায়ালা কোনো বিশেষ ব্যক্তিকে এই মর্যাদা দান করে থাকেন। এই প্রয়োজনের সময় যখন উপস্থিত হয় তখনই আল্লাহতায়ালা এক ব্যক্তিকে এই মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন এবং যখন প্রয়োজন পড়ে না অথবা থাকে না, তখন খামাখা আল্লাহতায়ালা এক ব্যক্তিকে এই মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন এবং যখন প্রয়োজন পড়ে না অথবা থাকে না, তখন খামাখা আল্লাহতায়ালা নবীর পর নবী প্রেরণ করতে থাকেন না। কোরআন মজিদ থেকে যখন আমরা একথা জানবার চেষ্টা করি যে, কোন্ পরিস্থিতিতে নবী প্রেরণের প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন সেখানে এ ধরনের চারটি অবস্থার সন্ধান পাওয়া যায়:
\r\n
** কোনো বিশেষ জাতির মধ্যে নবী প্রেরণের প্রয়োজন এজন্য দেখা যায় যে, তাদের মধ্যে ইতিপূর্বে কোন নবী আসেননি এবং অন্য কোনো জাতির মধ্যে প্রেরিত নবীর পয়গামও তাদের নিকট পৌঁছেনি।
\r\n
** নবী পাঠাবার প্রয়োজন এজন্য দেখা যায় যে, সংশ্লিষ্ট জাতি ইতিপূর্বৈ প্রেরিত নবীদের শিক্ষা ভুলে যায় অথবা তা বিকৃত হয়ে যায় এবং তাঁদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ অসম্ভব হয়ে পড়ে।
\r\n
**ইতিপূর্বে প্রেরিত নবীদের মাধ্যমে জনগণের শিক্ষা পূর্ণতা লাভ করতে পারেনি এবং দ্বীনের পূর্ণতার জন্য অতিরিক্ত নবীর প্রয়োজন হয়।
\r\n
** কোনো নবীল সংগে তাঁর সাহায্য-সহযোগিতার জন্য আর একজন নবীর প্রয়োজন হয়।
\r\n
উপরের আলোচনা থেকে একথা পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, রসূলুল্লাহ্র পর কোনো নবীর প্রয়োজন নেই।
\r\n
কোরআন নিজেই বলছে যে, রসূলুল্লাহকে সমগ্র দুনিয়ার জন্য হেদায়াতকারী হিসেবে পাঠানো হয়েছে। দুনিয়ার সাংস্কৃতিক ইতহিাস একথা বলে যে, তাঁর নবুয়্যাত প্রাপ্তির পর থেকে সমগ্র দুনিয়ায় এমন অবস্থা বিরাজ করছে, যাতে করে তাঁর দাওয়াত সব সময় দুনিয়ার সকল জাতির মধ্যে পৌঁছতে পারে। এর পরেও প্রত্যেক জাতির মধ্যে পৃথক পৃথক পয়গাম্বর প্রেরণের কোনো প্রয়োজন থাকে না।
\r\n
কোরআন একথাও বলে এবং একই সংগে হাদীস এবং সীরাতের যাবতীয় বর্ণনাও একথার সাক্ষ্যবহ যে, রসূলুল্লাহর শিক্ষা পুরোপুরি নির্ভুল এবং নির্ভেজাল আকারে সংরক্ষিত রয়েছে। এর মধ্যে কোনো প্রকার বিকৃতি বা রদবদল হয়নি। তিনি যে কোরআন এনেছিলেন, তার মধ্যে আজ পর্যন্ত একটি শব্দেরও কম-বেশী হয়নি। এবং কিয়ামত পর্যন্তও তা হতে পারে না। নিজের কথা ও কর্মের মাধ্যমে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাও আজ আমরা এমনভাবে পেয়ে যাচ্ছি, যেন আমরা তাঁরই যুগে বাস করছি। কাজেই দ্বিতীয় প্রয়োজনটাও খতম হয়ে গেছে।
\r\n
আবার কোরআন মজীদ স্পষ্টভাষায় একথাও ব্যক্ত করে যে, রসূলুল্লাহর মাধ্যমে খোদার দ্বীনকে পূর্ণতা দান করা হয়েছে। কাজেই দ্বীনের পূর্ণতার জন্যও এখন আর কোনো নবীর প্রয়োজন নেই।
\r\n
এখন বাকি থাকে চতুর্থ প্রয়োজন। এ সম্পর্কে আমার বক্তব্য হলো এই যে, এজন্য যদি কোনো নবীর প্রয়োজন হতো তাহলে রসূলুল্লাহর যুগে তাঁর সংগেই তাকে প্রেরণ করা হতো।কিন্তু একথা সবাই জানেন যে, এমনকোনো নবী রসূলুল্লাহর যুগে প্রেরণ করা হয়নি কাজেই এ কারণটা বাতিল হয়ে গেছে।
\r\n
এখন আমরা জানতে চাই যে, রসূলুল্লাহর পর আর একজন নতুন নবী আসবার পঞ্চম কারণটা কি? যদি কেউ বলেন যে, সমগ্র উম্মত বিগড়ে গেছে, কাজেই তাদের সংস্কারের জন্য আর একজন নতুন নবীর প্রয়োজন, তাহলে তাকে আমরা জিজ্ঞেস করবো: নিছক সংস্কারের জন্য দুনিয়ায় আজ পর্যন্ত কি কোন নবী এসেছে যে শুধু এই উদ্দেশ্যেই আর একজন নতুন নবীর আবির্ভাব হলো? অহী নাযিল করার জন্যই তো নবী প্রেরণ করা হয়। কেননা নবীর নিকটেই অহী নাযিল করা হয়। আর অহীর প্রয়োজন পড়ে কোনো নতুন পয়গাম দেবার অথবা পূর্ববর্তী পয়গামকে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য। আল্লাহর কোরআন এবং রসূলুল্লাহর সুন্নাত সংরক্ষিত হয়ে যাবার পর যখন আল্লাহর দ্বীন পরিপূর্ণ হয়েগেছে এবং অহীর সমস্ত সম্ভাব্য প্রয়োজন খতম হয়ে গেছে, তখন সংস্কারের জন্য একমাত্র সংস্কারকে প্রয়োজনই বাকী রয়ে গেছে- নবীর প্রয়োজন নয়।
\r\n\r\n
নতুন নবুয়্যাত বর্তমানে মুসলমানদের জন্য রহমত নয়, লা’নতের শামিল
\r\n
তৃতীয় কথা হলো এই যে, যখনই কোনো জাতির মধ্যে নবীর আগমন হবে, তখনই সেখানেই প্রশ্ন উঠবে কুফর ও ঈমানের। যারা ঐ নবীকে স্বীকার করে নেবে, তারা এক উম্মতভুক্ত হবে এবং যারা তাকে অস্বীকার করবে তারা অবশ্যই একটি পৃথক উম্মতের শামিল হবে। এই দুই উম্মতের মতবিরোধ কোনোআংশিক মতবিরোধের পর্যায়ে নেমে আসবে, যার ফলে তাদের একটি দল যতদিন না নিজেদের আকীদা-বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করবে, ততদিন পর্যন্ত তারা দুই দল কখনো একত্রিত হতে পারবে না। এ ছাড়াও কার্যত তাদের প্রত্যেকের জন্য হেদায়াত এবং আইনের উৎস হবে বিভিন্ন। কেননা একটি দল তাদের নিজেদের নবীর অহী এবং সুন্নাত থেকে আইন প্রণয়ন করবে এবং দ্বিতীয়দলটি এদু’টিকে তাদের আইনের উৎস হিসেবে মেনে নিতেই প্রথমত অস্বীকার করবে। কাজেই তাদের উভয়ের সম্মিলনে একটি সমাজ সৃষ্টি কখনো সম্ভব হবেনা।
\r\n
এই প্রোজ্জ্বল সত্যগুলো পর্যবেক্ষণ করার পর যে কোনো ব্যক্তি স্পষ্ট বুঝতে পারবেন যে, ‘খত্মে নবুয়্যাত’ মুসলিম জাতির জন্য আল্লাহ তায়ালার একটি বিরাট রহমত স্বরূপ। এর বদৌলতেই সমগ্র মুসলিম জাতি একটি চিরন্তন বিশ্বব্যাপী ভ্রাতৃত্বে শামিল হতে পেরেছে। এ জিনিসটা মুসলমানদেরকে এখন সব মৌলিক মতবিরোধ থেকে রক্ষা করেছে, যা তাদের মধ্যে চিরন্তন বিচ্ছেদের বীজ পবন করতো। কাজেই যেব্যক্তি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে হেদায়াত দানকারী এবং নেতা বলে স্বীকার করে এবং তিনি যে শিক্ষা দিয়েছেন তাছাড়া অন্য কোন হেদায়াত উৎসের দিকে ঝুঁকে পড়তে চায় না, সে আজ এই ভ্রাতৃত্বের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে। নবুয়্যাতের দরজা বন্ধ না হয়ে গেলে মুসলিম জাতি কখনো এই ঐক্যের সন্ধান পেতোনা। কেননা প্রত্যেক নবীর আগমনের পর এ ঐক্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতো।
\r\n
মানুষের বিবেক-বুদ্ধিও একথাই সমর্থন করে যে, একটি বিশ্বজনীন এবং পরিপূর্ণ দ্বীন দিয়ে দেবার এবং তাকে সকল প্রকার বিকৃতি ও রদবদল থেকে সংরক্ষিত করার পর নবুয়্যাতের দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়াই উচিত। এর ফলে সম্মিলিতভাবে এই শেষ নবীর আগমন করে সমগ্র দুনিয়ার মুসলমান চিরকালের জন্য একই উম্মতের অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারবে এবং বিনা প্রয়োজনে নতুন নতুন নবীদের আগমনে উম্মতের মধ্যে বারবার বিভেদ সৃষ্টি হতে পারবে না। নবী ‘যিল্লী’ হোক অথবা ‘বুরুজী ওম্মতওয়ালা শরীয়ত ওয়ালা এবং কিতাবওয়ালা- যে কোন অবস্থায়ই যিনি নবী হবেন এবং খোদার পক্ষহতে তাঁকে প্রেরণ করা হবে, তাঁর আগমনের অবশ্যম্ভাবী ফল দাঁড়াবে এই যে, তাকে যারা মেনে নেবে, তারা হবে একটি উম্মত আর যারা মানবেনা তারা কাফের বলে গণ্য হবে। যখন নবী প্রেরণের সত্যিকার প্রয়োজন দেখা যায়, তখন-শুধুমাত্র তখনই-এই বিভেদ অবশ্যম্ভাবী হয়। কিন্তু যখন তার আগমনের কোন প্রয়োজন থাকেনা, তখন খোদার হিকমত এবংতাঁর রহমতের নিকট কোনক্রমেই আশা করা যায়না যে, তিনি নিজের বান্দাদেরকে খামাখা কুফর ও ঈমানের সংঘর্ষে লিপ্ত করবেন এবং তাদেরকে সম্মিলিতভাবে একটি উম্মতভুক্ত হবার সুযোগ দেবেননা। কাজেই কোরআন, সুন্নাহ এবং ইজমা থেকে যা কিছু প্রমাণিত হয়, মানুষের বিবেক-বুদ্ধিও তাকে নির্ভুল বলে স্বীকার করে এবং তাথেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, বর্তমান নবুয়্যঅতের দরজা বন্ধ থাকাই উচিত।
\r\n\r\n
‘প্রতিশ্রুত মসীহ’ এর তাৎপর্য
\r\n
নতুন নবুয়্যাতের দিকে আহ্বানকারীরা সাধারণত অজ্ঞ মুসলমানদের বলে থাকে যে, হাদীসে ‘প্রতিশ্রুত মসীহ’ এর আগমনের খবর দেয়া হয়েছে। আর মসীহ নবী ছিলেন। কাজেই তাঁর আগমনের ফলে খতমে নবুয়্যাত কোনো দিক দিয়ে প্রভাবিত হচ্ছেনা। বরং খত্মে নবুয়্যাত এবং ‘প্রতিশ্রুত মসীহ’ এর আগমন দুটোই সমপর্যায়ে সত্য।
\r\n
এই প্রসংগে তারা আরো বলে যে, হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম ‘প্রতিশ্রুত মসীহ’ নন। তাঁর মৃত্যু হয়েছে। হাদীসেযাঁর আগমনের খবর দেয়া হয়েছে তিনি হলেন ‘মসীলে মসীহ’ –অর্থাৎ হযরত ঈসার অনুরূপ একজন মসীহ। এবং তিনি ‘অমুক’ ব্যক্তি যিনি সম্প্রতি আগমন করেছেন। তাঁকে মেনে নিলে খত্মে নবয়্যাত বিশ্বাসের বিরোধিতা করা হয়না।
\r\n
এই প্রতারণার পর্দা ভেদ করবার জন্য আমি এখানে হাদীসের নির্ভরযোগ্য কিতাবগুলো থেকে এই ব্যাপারে উল্লিখিত প্রমাণ্য হাদীস সমূহ সূত্রসহ নকল করছি। এই হাদীসগুলো প্রত্যক্ষ করে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই বুঝতে পারবেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কি বলেছিলেন এবং আজ তাকে কিভাবে চিত্রিত করা হচ্ছে।
\r\n\r\n
হযরত ঈসা (আ) নুযুল সম্পর্কিত হাদীস
\r\n
(আরবী **********)
\r\n
(১) হযরত আবু হোরায় (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন: সেই মহান সত্তার কছম যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে ইবনে মরিয়ম ন্যায়বিচারক শাসকরূপে অবতীর্ণ হবেন। অতঃপর তিনি ক্রশ ভেঙ্গে ফেলবেন, শূকর হত্যা করবেন। [ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলার এবং শুকর হত্যা করার অর্থ হলো এই যে, একটি পৃথক ধর্ম হিসেবে ধর্মের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে। ঈসায়ী ধর্মের সমগ্র কাঠামো এই আকীদার ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে যে, আল্লাহ তাঁর একমাত্র পুত্রকে (অর্থাৎ হযরত ঈসাকে (আ) ক্রশে বিদ্ধ কলে ‘লানত’ পূর্ণ মৃত্যু দান করেছেন। এবং এতেই সমস্ত মানুষেরগোনাহর কাফ্ফারা হয়ে গেছে। অন্যান্য নবীদের উম্মতের সংগে ঈসায়ীদের পার্থক্য হলো এই যে, এরা শুধু আকীদাটুকু গ্রহণ করেছে, অতঃপর খোদার সমস্ত শরীয়ত নাকচ করে দিয়েছে। এমনকি শুকরকেও এরা হালাল করে নিয়েছে- যা সকল নবীর শরীয়তে হারাম।
\r\n
কাজেই হযরত ঈসা (আ) নিজে এসে যখন বলবেন, আমি খোদার পুত্র নই, আমাকে ক্রুশে বিদ্ধ করে হত্যা করা হয়নিএবং আমি কারুর গোনাহর কাফফারা হইনি, তখন ঈসায়ী ধর্মবিশ্বাসের বুনিয়াদ সমূলে উৎপাটিত হবে। অনুরূপভাবে যখন তিনি বলবেন, আমার অনুসারীদের জন্র আমি শুকুর হালাল করিনি এবং তাদেরকে শরীয়তের বিধিনিষেধ থেকে মুক্তিও দেইনি, তখন ঈসায়ী ধর্মের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যও নির্মূল হয়ে যাবে।
\r\n
অন্য কথায় বলা যায়, তখন ধর্মের বৈষম্য ঘুচিয়ে মানুষ একমাত্র দ্বীন ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হবে। এর ফলে আর যুদ্ধের প্রয়োজন হবেনা এবং কারুর জিজিয়াও আদায় করা হবেনা। পরবর্তী ৫ এবং ১৫ নং হাদীস একথাই প্রমাণ করেছে।] এবং যুদ্ধ খতম করে দেবেন (বর্ণনান্তরে যুদ্ধের পরিবর্তে ‘জিজিয়া’ শব্দটি উল্লিখিত হয়েছে অর্থাৎ জিজিয়া খতম করে দেবেন)। তখন ধনের পরিমাণ এতো বৃদ্ধি পাবে যে, তা গ্রহণ করার লোক থাকবে না এবং (অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছবে যে, মানুষখোদার জন্য) একটি সিজদা করে নেয়াটাকেই দুনিয়া এবং দুনিয়ার বস্তুর চাইতে বেশী মূল্যবান মনে করবে।
\r\n
(২) অন্য একটি হাদীসে হযরত আবু হোরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে (আরবী **********)
\r\n
ঈসা ইবনে মরিয়ম অবতীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না....” এবং এর পর বলা হয়েছে তা উপরোল্লিখিত হাদীসের সংগে পুরোপুরি সামঞ্জস্যশীল।– (বুখারী, কিতাবুল মাজালেম, বাবু কাসরিক সালিব, ইবনে মাজা, কিতাবুল ফিতান, বাবু ফিতনাতিদ দাজ্জাল)
\r\n
(আরবী **********)
\r\n
(৩) হযরত আবু হোরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (স) বলেন, কেমনহবে তোমরা যখন তোমাদের মধ্যে ইবনে মরিয়ম অবতীর্ণ হবেন এবং তোমাদের ইমাম নিজেদের মধ্য থেকেই নিযুক্ত হবেন? [অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ) নামাজে ইমামতি করবেননা। মুসলমানদের পূর্ব নিযুক্ত ইমামের পেছনে তিনি এক্তেদা করবেন।]
\r\n
(আরবী **********)
\r\n
(৪) হযরত আবু হোরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেন: ঈসাইবনে মরিয়ম অবতীর্ণ হবেন। অতঃপর তিনি শুকর হত্যা করবেন। ক্রুশ ধ্বংস করবেন। তাঁর জন্য একাধিক নামাজ এক ওয়াক্তে পড়া হবে। তিনি এতো ধন বিতরণ করবেন যে, অবশেষে তা গ্রহীতা পাওয়া যাবে না। তিনি খিরাজ মওকুফ করে দেবেন। রওহা [রওহা মদীনা থেকে ২৫ মাইল দূরে একটি স্থানের নাম।] নামক স্থানে অবস্থান করেতিনি সেখান থেকে হজ্ব অথবা ওমরাহ করবেন অথবা দুটোই করবেন। (রসূলুল্লাহ এর মধ্যে কোন্টি বলেছিলেন- এ ব্যাপারে বর্ণনাকারীর সন্দেহ রয়ে গেছে)।
\r\n
(আরবী **********)
\r\n
(৫) হযরত আবু হোরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, দাজ্জালের নির্গমন বর্ণনার পর রসূলুল্লাহ বলেন: ইত্যবসরে যখন মুসলমানরা তাঁর সংগে লড়াইয়ের প্রস্তুতি করতে থাকবে, কাতারবন্দি করতে থাকবে এবং নামাজের জন্য ‘একমত’ পাঠ করা শেষ হবে, তখন ঈসা ইবনে মরিয়ম অবতীর্ণ হবেন এবং নামাজে মুসলমানদের ইমামতি করবেন। খোদার দুশমন দাজ্জালতাঁকে দেখতেই এমনভাবে গলিত হতে থাকবে যেমন পানিতে লবণ গলে যায়। যদি ঈসা (আ) তাকে এই অবস্থায় পরিত্যাগ করেন, তাহলেও সে বিগলিত হয়ে মৃত্যু বরণ করবে। কিন্তু আল্লাহতায়ালা তাকে হযরত ঈসার (আ) হাতে কতল করবেন। তিনি দাজ্জালের রক্তে রঞ্জিত নিজের বর্শাফলক মুসলমানদের দেখাবেন।
\r\n
(আরবী **********)
\r\n
(৬) হযরত আবু হোরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন: আমার এবং তাঁর (অর্থাৎ হযরত ঈসার) মাঝখানে আর কোনো নবী নেই। এবং তিনি অবতীর্ণ হবেন। তাঁকে দেখা মাত্রই তোমরা চিনে নিয়ো। তিনি মাঝারি ধরনের লম্বা হবেন। বর্ণ লাল সাদায় মেশানো। পরনে দু’টো হলুদ রঙের কাপড়। তাঁর মাথার চুল থেকে মনে হবে এই বুঝি পানি টপকে পড়লো। অথচ তা মোটেই সিক্ত হবেনা। তিনি ইসলামের জন্য মানুষের সংগে যুদ্ধ করবেন। ক্রুশ ভেঙ্গে টুক্রো টুক্রো করবেন। শূকর হত্যা করবনে। জিজিয়া কর রহিত করবেন। তাঁর জামানায় আল্লাহ সমস্ত মিল্লাতকেই নির্মূল করবেন। তিনি মসীহ দাজ্জালকে হত্যা করবেন এবং দুনিয়া চল্লিশ বছর অবস্থান করবেন। অতঃপর তাঁর ইন্তেকাল হবে এবং মুসলমানরা তাঁর জানাযায় নামাজ পড়বে।
\r\n
(আরবী **********)
\r\n
(৭) হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহকে (স) বলতে শুনেছি:... অতঃপর ঈসা ইবনে মরিয়ম অবতীর্ণ হবেন। মুসলমানদের আমীর তাঁকে বলবেন, আসুন, আপনি নামাজ পড়ান। কিন্তু তিনি বলবেন, না, তোমরা নিজেরাই একে অপরের আমীর। [অর্থাৎ তোমাদের আমীর তোমাদের নিজেদের মধ্যথেকে হওয়া উচিত।] আল্লাহ তায়ালা এই উম্মতকে যে ইজ্জত দান করেছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি একথা বলবেন।
\r\n
(আরবী **********)
\r\n
(৮) হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (ইবনে সাইয়াদ প্রসংগে) বর্ণনা করেছেন যে, অতঃপর উমর ইবনে খাত্তাব আরজ করলেন, হে রসূলুল্লাহ। অনুমতি দিন, আমি তাকে কতল করি। রসূলুল্লাহ (স) বললেন, যদি এ সেই ব্যক্তি (অর্থাৎ দাজ্জাল) হয়ে থাকে, তাহলে তোমরা এর হত্যাকারী নও, বরং ঈসা ইবনে মরিয়ম একে হত্যা করবেন এবং যদি এ সেই ব্যক্তি না হয়েথাকে, তাহলে জিম্মীদের মধ্য থেকে কাউকে হত্যা করার তোমাদের কোনো অধিকার নেই।
\r\n
(আরবী **********)
\r\n
(৯) হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণনা করেছেন যে, (দাজ্জাল প্রসংগে রসূলুল্লাহ বলেছেন:) সেইসময় ঈসা ইবনে মরিয়ম হঠাৎ মুসলমানদের মধ্যে এসে উপস্থিত হবেন। অতঃপর লোকেরা নামাজের জন্য দাঁড়িয়ে যাবে। তাঁকে বলা হবে, হে রুহুল্লাহ! অগ্রসর হন। কিন্তু তিনি বলবেন, না, তোমাদের ইমামের অগ্রবর্তী হওয়া উচিত, তিনিই নামাজ পড়াবেন। অতঃপর ফজরের নামাজের পর মুসলমানরা দাজ্জালের মুকাবিলায় বের হবে। (রসূলুল্লাহ) বলেছেন: যখন সেই কাজ্জাব (মিথ্যাবাদী) হযরত ঈসাকে দেখবে, তখন বিগলিত হতে থাকবে যেমন লবণ পানিতে গলে যায়। অতঃপর তিনি দাজ্জালের দিকে অগ্রসর হবেন এবং তাকে কতল করবেন। তখন অবস্থা এমন হবে যে, গাছপালা এবং প্রস্তরখন্ড ফুকারে বলবে, হে রুহুল্লাহ! ইহুদীটা এই আমার পিছনে লুকিয়ে রয়েছে! দাজ্জালের অনুগামীদের কেউ বাঁচবেনা, সবাইকে কতল করা হবে।
\r\n
(আরবী **********)
\r\n
(১০) হযরত নওয়াস ইবনে সাময়ান কেলাবী (দাজ্জাল প্রসংগে) বর্ণনা করছেন যে, (রসূলুল্লাহ বলেছেন:) দাজ্জাল তখন এসব করতে থাকবে, ইত্যবসরে আল্লাহতায়ালা মসীহ ইবনে মরিয়মকে প্রেরণ করবেন। তিনি দামেশকের পূর্ব অংশে সাদা মিনারের সন্নিকটে দুটো হলুদ বর্ণের কাপড় পরিধান করে দুজনফেরেশতার কাঁধে হাত রেখে নামাবেন। তিনি মাথা নীচু করলে পানি টপকাচ্ছে বলে মনে হবে। আবার মাথা উঁচু করলে মনে হবে যেন বিন্দু বিন্দু পানি মোতির মতো চমকাচ্ছে। তাঁর নিঃশ্বাসের হাওয়া যে কাফেরের গায়ে লাগবে- এবং এর গতি হবে তাঁর দৃষ্টিসীমাপর্যন্ত-সে জীবিত থাকবে না। অতঃপর ইবনে মরিয়ম দাজ্জালের পশ্চাদ্ধাবন করবেন এবং লুদের [এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, লূদ (Lydda) ফিলিস্তিনের অন্তর্গত বর্তমান ইসরাঈল রাষ্ট্রের রাজধানী তেলআবীব থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত। ইহুদীরা এখানে একটি বিরাট বিমান বন্দর নির্মাণ করেছে] দ্বারপ্রান্তে তাকে গ্রেফতার করে হত্যা করবেন।
\r\n
(আরবী **********)
\r\n
(১১) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (স)বলেন: দাজ্জাল আমার উম্মতের মধ্যে বের হবে এবং চল্লিশ (আমি জানিনা চল্লিশদিন, চল্লিশ মাস অথবা চল্লিশ বছর) [এটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমরের কথা] অবস্থান করবে। অতঃপর আল্লাহ ঈসা ইবনে মরিয়মকে পাঠাবেন।তাঁর চেহারা উরওয়া ইবনে মাসউদের (জনৈক সাহাবী) মতো। তিনি দাজ্জালের পশ্চাদ্ভাবন করবেন এবং তাকে হত্যা করবেন। অতঃপর সাত বছর পর্যন্ত মানুষ এমন অবস্থায় থাকবে যে, দুজনলোকের মধ্যে শত্রুতা থাকবেনা।
\r\n
(আরবী **********)
\r\n
(১২) হযরত হোজায়ফা ইবনে আসীদ আল গিফারী (রা) বর্ণনা করেছেনযে, একবার রাসূলুল্লাহ (স) আমাদের মজলিসে তাশরীফ আনলেন। তখন আমরা নিজেদের মধ্যে আলোনায় লিপ্ত ছিলাম। রসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞেস করলেন: তোমরা কি আলোচনা করছো? লোকেরা বললো, আমরা কিয়ামতের কথা আলোচনা করছি। তিনি বললেন: দশটিনিশানা প্রকাশ না হবার পূর্বে তা কখনো কায়েম হবেনা। অতঃপর তিনি দশটি নিশানা বলে গেলেন। এক: ধোঁয়া, দুই: দাজ্জাল, তিন: মৃত্তিকার প্রাণী, চার: পশ্চিম দিক হতে সুর্যোদয়, পাঁচ ঈসা ইবনে মরিয়মের অবতরণ, ছয়: ইয়াজুজ ও মাজুজ, সাত: তিনটি প্রকাণ্ড জমি ধ্বংস (Landslide) একটি পূর্বে, আট: একটি পশ্চিমে, নয়: আর একটি আরব উপদ্বীপে, দশ: সর্বশেষ একটি প্রকাণ্ড অগ্নি ইয়েমেন থেকে উঠবে এবং মানুষকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে হাশরের ময়দানের দিকে।
\r\n
(আরবী **********)
\r\n
(১৩) রসূলুল্লাহর (স) আজাদকৃত গোলাম সাওবান (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ বলেন: আমার উম্মতের দু’টো সেনাদলকে আল্লাহতায়ালা দোজখের আগুন থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন। তাদের মধ্যে একটি হলো- যারা হিন্দুস্থানের ওপর হামলা করবে আর দ্বিতীয়টি ঈসা ইবনে মরিয়মের সংগে অবস্থানকারী।
\r\n
(আরবী **********)
\r\n
(১৪) মাজমা ইবনে জারিয়া আনসারী (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহকে (স) বলতে শুনেছি: ইবনে মরিয়ম দাজ্জালকে লুদের দ্বারপ্রান্তে কতল করবেন।
\r\n
(আরবী **********)
\r\n
(১৫) আবু উমামা বাহেলী (এক দীর্ঘ হাদীসে দাজ্জাল প্রসংগে) বর্ণনা করেছেন যে, ফজরের নামায পড়বার জন্য মুসলমানদের ইমাম যখন অগ্রবর্তী হবেন, ঠিক সেইসময় ঈসা ইবনে মরিয়ম তাদের ওপর অবতীর্ণ হবেন। ইমাম পিছনে সরে আসবেনঈসাকে (আ) অগ্রবর্তী করার জন্য কিন্তু ঈসা (আ) তাঁর কাঁধে হাত রেখে বলবেন: না, তুমিই নামাজ পড়াও। কেননা এরা তোমার জন্যই দাঁড়িয়েছে। কাজেই তিনিই (ইমাম) নামাজ পড়াবেন। সালাম ফেরার পরঈসা (আ) বলবেন: দরজা খোলো। দরজা খোলা হবে। বাইরে দাজ্জাল ৭০ হাজার সশষ্ত্র ইহুদী সৈন্য নিয়ে অপেক্ষা করবে। তার দৃষ্টি হযরত ঈসার (আ) ওপর পড়া মাত্রই সে এমনভাবে বিগলিত হতে থাকবে, যেমন লবণ পানিতে গলে যায়। এবং সে পৃষ্ঠদর্শন করবে। ঈসা (আ) বলবেন: আমার নিকট তোর জন্য এমন এক আঘাত আছে যার হাত থেকে তোর কোনক্রমেই নিষ্কৃতি নেই। অতঃপর তিনি তাকে লূদের পূর্ব দ্বারদেশে গিয়ে গ্রেফতার করবেন এবং আল্লাহতায়ালা ইহুদীদেরকে পরাজয়দান করবেন..... এবং জমিন মুসলমানদের দ্বারা এমনভাবে ভরপুর হবে যেমন পাত্র পানিতে ভরে যায়। সবাই একই কালেমায় বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং দুনিয়ায় আল্লাহ ছাড়া আর কারুর বন্দেগী করা হবেনা।
\r\n
(আরবী **********)
\r\n
(১৬) উসমান ইবনে আবিল আস (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহকে (স) বলতে শুনেছি:...... এবংঈসা ইবনে মরিয়ম আলাইহিস সালাম ফজরের নামাজের সময় অবতরণ করবেন। মুসলমানদের আমীর তাঁকে বলবেন, হে রুহুল্লাহ! আপনি নামাজ পড়ান! তিনি জবাব দেবেন: এই উম্মতের লোকেরা নিজেরাই নিজেদের আমীর। তখন মুসলমানদের আমীর অগ্রবর্তী হয়ে নামায পড়াবেন। অতঃপর নামাজ শেষ করে ঈসা (আ) নিজের সেনাবাহিনী নিয়ে দাজ্জালের দিকে অগ্রসর হবেন। তিনি নিজের অস্ত্র দিয়ে দাজ্জালকে কতল করবেন এবং তার দলবল পরাজিত হয়ে পৃষ্ঠপদর্শন করবে। কিন্তু কোথাও তারা আত্মগোপন করার জায়গা পাবেনা। এমন কি বৃক্ষও ফুকারে বলবে: হে মুমিন, এখানে কাফের লুকিয়ে আছে। এবং প্রস্তর খণ্ডও ফুকারে বলবে: হে মুমিন, এখানে কাফের লুকিয়ে আছে।
\r\n
(আরবী **********)
\r\n
(১৭) সামুরা ইবনে জুনদুব (এক দীর্ঘ হাদীসে) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (স) বলেন: অতঃপর সকাল বেলা ঈসা ইবনে মরিয়ম মুসলমানদের মধ্যে আসবেন এবং আল্লাহতায়ালা দাজ্জাল এবং তার সেনাবাহিনীকে পরাজয় দান করবেন। এমন কি প্রাচীর এবং বৃক্ষের কাণ্ডও ফুকারে বলবে: হে মুমিন, এখানে কাফের আমার পেছনে লুকিয়ে রয়েছে। এসো, একে কতল করো!
\r\n
(আরবী **********)
\r\n
(১৮) ইবনে হোসাইন বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (স) বলেন: আমাদের উম্মতের মধ্যে হামেশা একটি দল হকের ওপর কায়েম থাকবে এবং তারা বিরোধী দলের ওপর প্রতিপত্তি বিস্তার করবে। অবশেষে আল্লাহতায়ালার ফয়সালা এসে যাবে এবং ঈসা ইবনে মরিয়ম আলাইহিস সালাম অবতীর্ণ হবেন।
\r\n
(আরবী **********)
\r\n
(১৯) হযরত আয়েশা রাজিআল্লাহ আন্হা (দাজ্জাল প্রসংগে) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ বলেন: অতঃপর ঈসা আলাইহিস সালাম অবতীর্ণ হবেন। তিনি দাজ্জালকে কতল করবেন। অতঃপর ঈসা(আ) চল্লিশ বছর আদিল ইমাম এবং ন্যায়নিষ্ঠ শাসক হিসেবে দুনিয়ায় অবস্থান করবেন।
\r\n
(আরবী **********)
\r\n
(২০) রসূলুল্লাহর আজাদকৃত গোলাম সাফীনা (রা) (দাজ্জাল প্রসংগে) বর্ণনা করেছেন, যে রসূলুল্রাহ (স) বলেন: অতঃপর ঈসা আলাইহিস সালাম অবতীর্ণ হবেন এবং আল্লাহতায়ালা উফায়েকের পর্বতে পথের [উফায়েককে বর্তমান ফায়েক বলা হয়। সিরিয়া এবং ইসরাইল সীমান্তে বর্তমান সিরিয়া রাষ্ট্রের সর্বশেষ শঞর। এর পরে পশ্চিমের দিকেকয়েক মাইল দূরে তাবারিয়া নামক একটি হ্রদ আছে। এখানে জর্দান নদরি উৎপত্তিস্থল। এর দক্ষিণ-পশ্চিমে পাহাড়েরর মধ্যভাগে নিম্ন ভূমিতে একটি রাস্তা রয়েছে। এই রাস্তাটি প্রায় দেড় হাজার ফুট গভীরে নেমে গিয়ে সেই স্থানে পৌঁছায় যেখানথেকে জর্দান নদী তাবারিয়া মথ্যহতে নির্গত হচ্ছে। এই পার্বত্য পথকেইবলা ‘আকাবায়ে উফায়েক” (উফায়েকের নিম্ন পার্বত্য পথ)।] সন্নিকটে তাকে (দাজ্জালকে) মেরে ফেলবেন।
\r\n
(আরবী **********)
\r\n
(২১) হযরত হোজায়ফা ইবনে ইয়ামান (দাজ্জাল প্রসংগে) বর্ণনা করেছেনযে, রসূলুল্লাহ বলেন: অতঃপর যখন মুসলমানরা নামাজের জন্য তৈরী হবে, তখন তাদের চোখের সম্মুখে ঈসা ইবনে মরিয়ম অবতীর্ণ হবেন। তিনি মুসলমানদের নামাজ পড়াবেন অতঃপর সালাম ফিরিয়ে লোকদের বলবেন যে, আমার এবং খোদার এই দুশমনের মাঝখান থেকে সরেযাও.... এবং আল্লাহতায়ালা দাজ্জালের দলবলের ওপর মুসলমানদেরকে প্রতিপত্তি দান করবেন।
\r\n
মুসলমানরা তাদেরকে বেধড়ক হত্যা করতে থাকবে। অবশেষে বৃক্ষ এবং প্রস্তর খণ্ডও ফুকারে বলবে: হে আল্লাহর বান্দা, হে রহমানেসর বান্দা, হে মুসলমান!দেখো, এখানে একজন ইহুদী, একে হত্যা করো। এভাবে আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করে দেবেন এবং মুসলমানগণ বিজয় লাভ করবে। তারা ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবে, শুকর হত্যা করবে এবং জিজিয়া মওকুফ করে দেবে। [মুসলিমেও হাদীসটি সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে এবং হাফেজ ইবনে হাজার আসকালীণ ফাতহুল বারীর ষষ্ঠ খণ্ডে ৫৫০ পৃষ্ঠায় এটিকে ‘ছহীহ’ বলে গণ্য করেছেন।
\r\n
এই ২১টি হাদীস ১৪ জন সাহাবায়ে মারফত নির্ভুল সনদসহ হাদীসের নির্ভরযোগ্য কিতাবগেুলোয় উল্লিখিত হয়েছে। এছাড়াও এ ব্যাপারে আরো অসংখ্য হাদীস অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু আলোচনা দীর্ঘ হবার ভয়ে আমি সেগুলো এখানে উল্লেখ করলাম না। বর্ণনা এবং সনদের দিক অধিকতর শক্তিশালী এবং নির্ভরযোগ্য হাদীসগুলোই শুধু এখানে উদ্ধৃত করলাম।
\r\n\r\n
এই হাদীসগুলো থেকে কি প্রমাণ হয়?
\r\n
যে কোনো ব্যক্তি এ হাদীসগুলো পড়ে নিজেই বুঝতে পারবেনযে, এখানে কোনো ‘প্রতিশ্রুত মসীহ’, “মছীলে মসীহ” বা “বুরুজী মসীহ”র কোনো উল্লেখই করা হয়নি। এমন কি বর্তমান কালে কোনো পিতার ঔরসে মায়ের গর্ভ জন্মগ্রহণ করে কোনো ব্যক্তির একথা বলার অবকাশ নেই যে, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যে মসীহ সম্পর্কে ভবিষদ্বাণী করেছিলেন তিনিই সেই মসীহ। আজ থেকে দু’হাজার বছর আগে পিতা ছাড়াই হযরত মরিয়মের (আ) গর্ভে যে ঈসা আলাইহিস সালামের জন্ম হয়েছিল এই হাদীসগুলোর দ্ব্যার্থহীন বক্তব্যথেকে তাঁরই অবতরণের সংবাদ শ্রুত হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে তিনি ইন্তেকাল করেছেন, না জীবিত অবস্থায় কোথাও রয়েছেন- এ আলোচনা সম্পূর্ণ অবান্তর। তর্কের খাতিরে যদি এ কথা মেনে নেয়া হয় যে, তিনি ইন্তেকাল করেছেন তাহলেও বলা যায় যে, আল্লাহ তাঁকে জীবিত করার ক্ষমতা রাখেন। [যারা আল্লাহর এই পুনরুজ্জীবনের ক্ষমতা অস্বীকার করেন তাদের সূরা বাকারার ২৫৯ নম্বর আয়াতটির অনুধাবন করাউচিত। এ আয়াতে আল্লাহ বলেন যে, তিনি তাঁর এক বান্দাকে ১০০ বছর পর্যন্ত মৃত অবস্থায় রাখার পর আবার তাকে জীবিত করেন।] উপরন্তু আল্লাহ তাঁর এক বান্দাকে তাঁর এই বিশাল সৃষ্টি জগতের কোনো এক স্থানে হাজার বছর জীবিত অবস্থায় রাখার পর নিজের ইচ্ছামতো যে কোনো সময়তাঁকে এই দুনিয়ায় ফিরিয়ে আনতে পারেন। আল্লাহর অসীম ক্ষমতার প্রেক্ষিতে একথা মোটেই অস্বাভাবিক মনে হয়না। বলা বাহুল্য, যে ব্যক্তি হাদীসকে সত্য বলে স্বীকার করে তাকে অবশ্যই ভবিষ্যতে আগমনকারী ব্যক্তিকে উল্লিখিত ঈসা ইবনে মরিয়ম বলে স্বীকার করতেই হবে। তবে যে ব্যক্তি হাদীস অস্বীকার করে সে আদতে কোনো আগমনকারীর অস্তিত্বই স্বীকার করতে পারেনা। কারণ আগমনকারীর আগমন সম্পর্কে যে বিশ্বাস জন্ম নিয়েছে হাদীস ছাড়া আর কোথাও তার ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যাবেনা। কিন্তু এই অদ্ভূত ব্যাপারটি শুধু এখানেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, আগমনকারীর আগমন সম্পর্কিত ধারণা বিশ্বাস গ্রহণ করা হচ্ছে হাদীস থেকে কিন্তু সেই হাদীসগুলোই আবার যখন সুস্পষ্ট করে এ বক্তব্য তুলে ধরছে যে, উক্ত আগমনকারী কোনো ‘মছীলে মসীহ’ (মসীহ-সম ব্যক্তি) নন বরং তিনি হবেন স্বয়ং ঈসা ইবনে মরিয়ম আলাইহস সালাম তখন তা অস্বীকার করা হচ্ছে।
\r\n
এই হাদীসগুলো থেকে দ্বিতীয় যে বক্তব্যটি সুস্পষ্ট ও দ্ব্যার্থহীনভাবে ফুটে উঠেছে তা হচ্ছে এই যে, হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ) দ্বিতীয়বার নবী হিসেবে অবতরণ করবেন না। তাঁর ওপর অহী নাযিল হবেনা। খোদার পক্ষ থেকে তিনি কোনো নতুন বাণী বা বিধান আনবেন না। শরীয়তে মুহাম্মদীর মধ্যেও তিনি হ্রাস বৃদ্ধি করবেননা। দ্বীন ইসলামের পুনরুজ্জীবনের জন্যও তাঁকে দুনিয়ায় পাঠানো হবে না। তিনি এসে লোকদেরকে নিজের ওপর ঈমান আনার আহ্বান জানাবেননাএবং তাঁর প্রতি যারা ঈমান আনবে তাদেরকে নিয়ে পৃথক উম্মতও গড়ে তুলবেননা। [পূর্বপবর্ত আলেমগণ এ বিষয়টিকে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। আল্লামা আফ্তাবানী (হিঃ ৭২২-৭৯২) শরহে আকায়েদে নাসাফী গ্রন্থে লিখেছেন: “মুহাম্মদ (স) সর্বশেষ নবী, একথা প্রমাণিত সত্য... যদি বলা হয়, তাঁর পর হাদীসে হযরত ঈসার (আ) আগমনের কথা বর্ণিত হয়েছে তাহলে আমি বলবো, হাঁ হযরত ঈসা (আ) আগমনের কথা বলা হয়েছে সত্য, তবে তিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অনুসারী হবেন। কারণ তাঁর শরীয়ত বাতিল হয়ে গেছে। কাজেই তাঁর ওপর অহী নাযিল হবেনা এবং তিনি নতুন বিধানও নির্ধারণ করবেন না। বরং তিনি মুহাম্মদ রসূলুল্লাহর (স) প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করবেন।” (মিসরে মুদ্রিত, ১৩৫ পৃষ্ঠা)
\r\n
আল্লামা আলুসী তাঁর ‘রুহুল মা’নী’ নামক তাফসীর গ্রন্থেও প্রায় একই বক্তব্য পেশ করেছেন। তিনি বলেছেন: “অতঃপর ঈসা আলাইহিস সালাম অবতীর্ণ হবেন। তিনি অবশ্য তাঁর পূর্ব প্রদত্ত নবুয়্যাতের পদমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত থাকবেন। কাণ তিনি নিজের আগের পদমর্যাদা থেকেতো অপসারিত হবেননা। কিন্তু নিজের পূর্বের শরীয়তের অনুসারী হবেননা। কারণ তা তাঁর নিজের ও অন্যসব লোকদের জন্য বাতিল হয়ে গেছে। কাজেই বর্তমানে তিনি মূলনীতি থেকে খুঁটিনাটি ব্যাপার পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়তের বিধানও নির্ধারণ করবেননা। “বরং তিনি মুহাম্মদ রসূলুল্লাহর (স) প্রতিনিধি এবং তাঁর উম্মতের মধ্যস্থিত মুহাম্মদী মিল্লাতের শাসকদের মধ্য থেকে একজন শাসক হবেন।”) (২২শ খণ্ড, ৩২ পৃষ্ঠা)
\r\n
ইমাম রাজী এ কথাটিকে আরো সুস্পষ্ট করে নিম্নোক্ত ভাষায় পেশ করেছেন: “মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম পর্যন্ত নবীদের যুগ শেষ হয়ে গেছে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আগমনের পর নবীদের আগমন শেষ হয়ে গেছে। কাজেই বর্তমানে ঈসার (আ) অবতহরণের পর তিনি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অনুসারী হবেন একথা মোটেই অযৌক্তিক নয়।” (তাফসীরে কবীর, ৩য় খণ্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা)] তাঁকে কেবলমাত্র একটি পৃথক দায়িত্ব দিয়ে দুনিয়ায় পাঠানো হবে। অর্থাৎ তিনি দাজ্জালের ফিত্নাকে সমূহে বিনাশ করবেন। এজন্য তিনি এমনভাবে অবতরণ করবেন যার ফলে তাঁর অবতরণের ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশ থাকবেনা। যেসব মুসলমানের মধ্যে তিনি অবতরণ করবেন তারা নিঃসংশয়ে বুঝতে পারবে যে, রসূলুল্লাহ (স) যে ঈসা ইবনে মরিয়ম সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তিনিই সেই ব্যক্তি এবং রসূলুল্লাহর কথা অনুযায়ী তিনি যথা সময়ে অবতরণ করেছেন, তিনি এসে মুসলমানদের দলে শামিল হয়ে যাবেন। মুসলমানদের তদানীন্তন ইমামের পিছনে তিনি নামাজ পড়বেন। [যদিও দুটি হাদীসে (৫ ও ২১ নং) বলা হয়েছে যে, ঈসা আলাইহিস সালাম অবতরণ করার পর প্রথম নামাজটি নিজে পড়াবেন। কিন্তু অধিকাংশ এবং বিশেষ করে শক্তিশালী কতিপয় হাদীস (৩, ৭, ৯, ১৫ ও ১৬ নয়) থেকে জানা যায় যে, তিনি নামাজে ইমামতি করতে অস্বীকার করবেন এবং মুসলমানদের তৎকালীন ইমাম ও নেতাকে অগ্রবর্তী করবেন। মুহাদ্দিস ও মুফাস্সিরগণ সর্বসম্মতভাবে এ মতটি গ্রহণ করেছেন।] তৎকালে মুসলমানদের যিনি নেতৃত্ব দেবেন তিনি তাঁকেই অগ্রবর্তী করবেন যাতে এই ধরনের সন্দেহের কোনো অবকাশই না থাকে যে, তিনি নিজের পয়গম্বরী পদমর্যাদা সহকারে পুনর্বার পয়গম্বরীর দায়িত্ব পালন করার জন্য ফিরে এসেছেন। নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, কোনো দলে খোদার পয়গম্বরের উপস্থিতিতে অন্য কোনো ব্যক্তি ইমাম বা নেতা হতে পারেন না। কাজেই নিছক এক ব্যক্তি হিসেবে মুসলমানদের দলে তাঁর অন্তর্ভুক্তি স্বতঃস্ফুর্তভাবে এ কথাই ঘোষণা করবে যে, তিনি পয়গম্বর হিসেবে আগমন করেননি। এজন্যতাঁর আগমনে নবুয়্যাতের দুয়ার উন্মুক্ত হবার কোনো প্রশ্নই ওঠেনা।
\r\n
নিঃসন্দেহে তাঁর আগমন বর্তমান ক্ষমতাসীন রাষ্ট্রপ্রধানের আমলে প্রাক্তন রাষ্ট্রপ্রধানের আগমনের সাথে তুলনীয়। এ অবস্থায় প্রাক্তন রাষ্ট্রপ্রধানের অধীনে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে অংশগ্রহণ করতে পারন। সাধারণ বোধ সম্পন্ন কোনো ব্যক্তি সহজেই এ কথা বুঝতে পারেন যে, এক রাষ্ট্রপ্রধানের আমলে অন্য একজন প্রাক্তন রাষ্ট্রপ্রধানের নিছক আগমনেই আইন ভেঙ্গে যায় না। তবে দুটি অবস্থায় আইনের বিরুদ্ধাচরণ অনিবার্য হয়ে পড়ে। এক, প্রাক্তন রাষ্ট্রপ্রধান এসে যদি আবার নতুন করে রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করেন। দুই, কোনো ব্যক্তি যদি তাঁর প্রধান রাষ্ট্রপ্রধানের মর্যাদা ও দায়িত্ব অস্বীকার করে বসেন। কারণ এটা হবে তাঁর রাষ্ট্র থাকাকালে যেসব কাজ হয়েছিল সেগুলোর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করার নামান্তর। এই দু’টি অবস্থার কোনো একটি না হলে প্রাক্তন রাষ্ট্র-প্রধানের নিছক আগমনেই আইনগত অবস্থাকে কোনো প্রকারে পরিবর্তিত করতে পারেনা। হযরত ঈসার (আ) দ্বিতীয় আগমনের ব্যাপারটিও অনুরূপ। তাঁর নিছক আগমনেই খতমে নবুয়্যাতের দুয়ার ভেঙ্গে পড়েনা। তবে তিনি এসে যদি নবীর পদে অধিষ্ঠিত হন এবং নবুয়্যাতের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন অথবা কোনো ব্যক্তি যদি তাঁর প্রাক্তন নবুয়্যাতের মর্যাদাও অস্বীকার করে বসে, তাহলে এক্ষেত্রে আল্লাহর নবুয়্যাত বিধি ভেঙ্গে পড়ে। হাদীসে একদিকে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হচ্ছে যে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহর (স) পর আর কোনো নবী নেই এবং অন্যদিকে জানিয়ে দিচ্ছে যে, ঈসা আলাইহিস সালাম পুনর্বার অবতরণ করবেন। এ থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, তাঁর এ দ্বিতীয় আগমন নবুয়্যাতের দায়িত্ব পালন করার উদ্দেশ্যে হবেনা।
\r\n
অনুরূপভাবে তাঁর আগমনে মুসলমানদের মধ্যে কুফর ও ঈমানের কোনো নতুন প্রশ্ন দেখা দেবেনা। আজও কোনো ব্যক্তি তাঁর পূর্বের নবুয়্যাতের ওপর ঈমান না আনলে কাফের হয়ে যাবে। মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (স) নিজেও তাঁর ঐ নবুয়্যাতের প্রতি ঈমান রাখতেন। মুহাম্মদ রসূলুল্লাহর (স) সমগ্র উম্মতও শুরু থেকেই তাঁর ওপর ঈমান রাখে। হযরত ঈসার (আ) পুনর্বার আগমনের সময়ও এই একই অবস্থা অপরিবর্তিত থাকবে। মুসলমানরা কোনো নতুন নবুয়্যাতের প্রতি ঈমান আনবে না, বরং আজকের ন্যায় সেদিনও তারা ঈসা ইবনে মরিয়মের (আ) পূর্বের নবুয়্যাতের ওপরই ঈমান রাখবে। এ অবস্থাটি বর্তমানে যেমন খতমে নবুয়্যাত বিরোধী নয়, তেমনি সেদিনও বিরোধীহবেনা।
\r\n
সর্বশেষ যে কথাটি এই হাদীসগুলো এবং অন্যান্য বহুবিধ হাদীস থেকে আনা যায় তা হচ্ছে এই যে, হযরত ঈসাকে (আ) যে দাজ্জালের বিশ্বব্যাপী ফিত্না নির্মূল করার জন্য পাঠানো হবে সে হবে ইহুদী সংশোদ্ভূত। সে নিজেকে ‘মসীহ’ রূপে পেশ করবে। ইহুদীদের ইতিহাস ও তাদের ধর্মীয় চিন্তা-বিশ্বাস সম্পর্কে অনবহিত কোনো ব্যক্তি এ বিষয়টির তাৎপরর্য অনুধান করতে সক্ষম হবেনা। হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালামের মৃত্যুর পর যখন বনি ইসরাঈলরা সামাজিক ধর্মীয় অবক্ষয় ও রাজনৈতিক পতনের শিকার হলো এবং তাদের এ পতন দীর্ঘায়িত হতে থাকলো, এমন কি অবশেষে ব্যবিলেন ও আসিরিয়া অধিপতিরা তাদেরকে পরাধীন করে দেশ থেকে বিতাড়িত করলো এবং দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষিপ্ত করে দিলো, তখন বনি ইসরাইলের নবীগণ তাদেরকে সুসংবাদ দিতে থাকলেন যে, খোদার পক্ষ থেকে একজন ‘মসীহ’ এসে তাদেরকে এই চরম লাঞ্চনা থেকে মুক্তি দেবেন। এইসব ভবিষ্যদ্বাণীর প্রেক্ষিতে ইহুদীরা একজন মসীহের আগমনের প্রতীক্ষারত ছিল। তিনি হবেন বাদশাহ। তিনি যুদ্ধ করে দেশ জয় করবেন। বনি ইসরাঈলদেরকে বিভিন্ন দেশ থেকে এনে ফিলিস্তিনে একত্রিত করবেন এবং তাদের একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র কায়েম করবেন। কিন্তু তাদের এসব আশা-আকাংখাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে যখন ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ) খোদার পক্ষ থেকে ‘মসীহ’ হয়ে আসলেন এবং কোনো সেনাবাহিনী ছাড়াই আসলেন, তখন ইহুদীরা তাঁকে ‘মসীহ’ বলে মেনে নিতে অস্বীকার করলো। তারা তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হলো। সে সময় থেকে আজ পর্যন্ত ইহুদী দুনিয়া সেই প্রতিশ্রুত মসীহর প্রতীক্ষা করছে, যার আগমনের সুসংবাদ তাদেরকে দেয়া হয়েছিল। তাদের সাহিত্য সেই বাঞ্চিত যুগের সুখ-স্বপ্ন কল্প-কাহিনীতে পরিপূর্ণ। তালমুদ ও রাববীর সাহিত্য গ্রন্থসমূহে এর যে নক্শা তৈরী করা হয়েছে তার কল্পিত স্বাদ আহরণ করে শত শত বছর থেকে ইহুদী জাতি জীবন ধারণ করছে। তাদের বুক ভরা আশা নিয়ে বসে আছে যে, এই প্রতিশ্রুত মসীহ হবেন একজন শক্তিশালী সামরিক ও রাজনৈতিক নেতা। তিনি নীল নদ থেকে ফোরাত পর্যন্ত সমগ্র এলাকা, যে এলাকাটিকে ইহুদীরা নিজেদের ‘উতর্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এলাকা’ মনে করে, আবার ইহুদীদের দখলে আনবেন এবং সারা দুনিয়া থেকে ইহুদীদেরকে এনে এখানে একত্রিত করবেন।
\r\n
বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করে রসূলুল্লাহর (স) ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, মহানবীর (স) কথামত ইহুদীদের ‘প্রতিশ্রুত মসীহর’ ভূমিকা পালনকারী প্রধানতম দাজ্জালের আগমনের জন্য মঞ্চ সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হয়ে গেছে। ফিলিস্তিনের বৃহত্তম এলাকা থেকে মুসলমানদের বেদখল করা হয়েছে। সেখানে ইরাঈল নামে একটি ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সারা দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে ইহুদীরা দলে দলে এখানে বাসস্থান গড়ে তুলছে। আমেরিকা, বৃটেন ও ফ্রান্স তাকে একটি বিরাট সামরিক শক্তিকে পরিণত করেছে। ইহুদী পুঁজিপতিদের সহায়তায় ইহুদী বৈজ্ঞানিক ও শিল্পবিদগণ দ্রুত উন্নতির পথে েএগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। চারপাশের মুসলিম দেশগুলোর জন্য তাদের এ শক্তি এক মহাবিপদে পরিণত হয়েছে। এই রাষ্ট্রের শাসকবর্গ তাদের এই ‘উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত দেশ’ দখল করার আকাংখাটি মোটেই
\r\n
(মানচিত্র *****************)
\r\n
লুকিয়ে রাখেননি। দীর্ঘকাল থেকে ভবিষ্যত ইহুদী রাষ্ট্রের যে নীল নক্শা তারা প্রকাশ করে আসছে পরের পাতায় তার একটি প্রতিকৃতি দেয়া হলো। এ নক্শায় দেখা যাবে, সিরিয়া, লেবানন ও জর্দানের সমগ্র এলাকা এবং প্রায় সমগ্র ইরাক ছাড়াও তুরস্কের ইস্কান্দোরুন, মিসরের সিনাই ও ব-দ্বীপ এলাকা এবং মদীনা মুনাওয়ারাসহ আরবের অন্তর্গত হেজাজ ও নজ্দের উচ্চভূমি পর্যন্ত তারা নিজেদের সাম্রাজ্র বিস্তার করতে চায়। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, আগামীতে কোনোএকটি বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোলে তারা ঐসব এলাকা দখল করার চেষ্টার করবে এবং ঐ সময়ই কথিত প্রধানতম দাজ্জাল তাদের প্রতিশ্রুত মসীহরূপে আগমন করবে। রসূলুল্লাহ (স) কেবল তার আগমন সংবাদ দিয়েই ক্ষান্ত হননি বরং এই সংগে একথাও বলেছেন যে, সে সময় মুসলমানদের ওপর বিপদের পাহাড় ভেঙে পড়বে এবং এক একটি দিন তাদের নিকট এক একটি বছর মনে হবে। এজন্য তিনি নিজে মসীহ দাজ্জালের ফিত্না থেকে খোদার নিকট আশ্রয় চেয়েছেন এবং মুসলমানদেরকেও আশ্রয় চাইতে বলেছেন।
\r\n
এই মসীহ দাজ্জালের মোকাবিলা করার জন্য আল্লাহ কোনো ‘মসীলে মসীহ’কে পাঠাবেন না বরং আসল মসীহকে পাঠাবেন। দু’হাজার বছর আগে ইহুদীরা এই আসল মসীহকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছিলএবং নিজেদের জানা মতে তারা তাঁকে শূলবিদ্ধ করে দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে দিয়েছিল। এই আসল মসীহ ভারত, আফ্রিকা বা আমেরিকায় অবতরণ করবেন না বরং তিনি অবতরণ করবেন দামেশ্কে। কারণ তখন সেখানেই যুদ্ধ চলতে থাকবে। মেহেরবানী করে পরের পাতার নকশাটিও দেখুন। এতে দেখা যাচ্ছে, ইসরাঈলের সীমান্ত থেকে দামেশক মাত্র ৫০ থেকে ৬০ মাইলের মধ্যে অবস্থিত। ইতিপূর্বে আমি যে হাদীস উল্লেখ করে এসেছি, তার বিষয়বস্তু মনে থাকলে সহজেই একথা বোধগম্য হবে যে, মসীহ দাজ্জাল ৭০ হাজার ইহুদী সেনাদল নিয়ে সিরিয়ায় প্রবেশ করবে এবং দামেশকের সামনে উপস্থিত হবে। ঠিক সেই মুহুর্তে দামেশকের পূর্ব অংশের একটি সাদা মিনারের নিকট সুব্হে সাদেকের পর হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম অবতরণ করবেন এবং ফজর নামায শেষে মুসলমানদের নিয়ে দাজ্জালের মুকাবিলায় বের হবেন। তাঁর প্রচণ্ড আক্রমণে দাজ্জাল পশ্চাদপসরণ করে উফাইকের পার্বত্য পথ দিয়ে (২১১ নম্বর হাদীসে দেখুন) ইসরাঈলের দিকে ফিরে যাবে। কিন্তু তিনি তার পশ্চাদ্ধাবন করতেই থাকনে। অবশেষে লিড্ডা বিমান বন্দরে সে তাঁর হাতে মারা পড়বে (১০, ১৪ ও ১৫ নং হাদীস)। এরপর ইহুদীদেরকে সব জায়গা থেকে ধরে ধরে হত্যা করা হবে এবং ইহুদী জাতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে (৯, ১৫ ও ২১ নম্বর হাদীস)। হযরত ঈসার (আ) পক্ষ থেকে সত্য প্রকাশের পর ঈসায়ী ধর্মও বিলুপ্ত হয়ে যাবে (১, ২, ৪ ও ৬ নম্বর হাদীস( এবং মুসলিম মিল্লাতের মধ্যে সমস্ত মিল্লাতে একীভূত হয়ে যাবে (৬ ও ১৫ নম্বর হাদীস)।
\r\n
কোনোপ্রকার জড়তা ও অস্পষ্টতা ছাড়াই এই দ্ব্যার্থহীন সত্যটিই হাদীস থেকে ফুটে উঠেছে। এই সুদীর্ঘ আলোচনার পর এ ব্যাপারে কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশ থাকেনা যে, “প্রতিশ্রুত মসীহ”র নামে আমাদের দেশে যে কারবার চালানো হচ্ছে তা একটি প্রকাণ্ড জালিয়াতি ছাড়া আর কিছুই নয়।
\r\n
এই জালিয়অতির সবচাইতে হাস্যকর দিকটি এবার আমি উপস্থাপিত করতে চাই। যে ব্যক্তি নিজেকে এই ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লিখিত মসীহর সাথে অভিন্ন বলে ঘোষণা করেছেন, তিনি নিজে ঈসা ইবনে মরিয়ম হবার জন্য নিম্নোক্ত রসালো বক্তব্যটি পেশ করেছেন:
\r\n
“তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ) বারাহীনে আহমদীয়ার তৃতীয় অংশে আমার নাম রেখেছেন মরিয়ম। অতঃপর যেমন বারাহীনে আহামদীয়ায় প্রকাশিত হয়েছে, দু’বছর পর্যন্ত আমি মরিয়মের গুণাবলী সহকারে লালিত হই.... অতঃপর ..... মরিয়মের ন্যায় ঈসার রহ আমার মধ্যে ফুৎকারে প্রবেশ করানো এবং রূপকার্থে আমাকে গর্ভবতী করা হয়। অবশেষে কয়েকমাস পরে, যা দশ মাসের চাইতে বেশী হবেনা, সেই এলহামের মাধ্যমে, যা বারাহীনে আহমাদীয়ার চতুর্থ অংশে উল্লিখিত হয়েছে, আমাকে মরিয়ম থেকে ঈসায় পরিণত করা হয়েছে। কাজেই এভাবে আমি হলাম ঈসা ইবনে মরিয়ম।” (কিশতীয়ে নুহ, ৮৭, ৮৮, ৮৯ পৃষ্ঠা)
\r\n
অর্থাৎ প্রথমে তিনি মরিয়ম হন অতঃপর নিজে নিজেই গর্ভবতী হন। তারপর নিজের পেট থেকে নিজেই ঈসা ইবনে মরিয়ম রূপে জন্ম নেন। এরপরও সমস্যা দেখা দিলো যে, হাদীসের বক্তব্য অনুযায়ী ঈসা ইবনে মরিয়ম দামেশকে অবতরণ করবে। দামেশকে কয়েক হাজার বছর থেকে সিরিয়ার একটি প্রসিদ্ধ ও সর্বজন পরিচিত শহর। পৃথিবীর মানচিত্রে আজও এই শহরটি এই নামেই চিহ্নিত। কাজেই অন্য একটি রসাত্মক বক্তব্যের মাধ্যমে এ সমস্যাটির সমাধান দেয়া হয়েছে:
\r\n
“উল্লেখ্য যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে দামেশকে শব্দের অর্থ আমার নিকট এভাবে প্রকাশ করা হয়েছে যে, এ স্থানে এমন একটি শহরের নাম দামেশ্ক রাখা হয়েছে যেখানে এজিদের স্বভাব সম্পন্ন ও অপবিত্র এজিদের অভ্যাস ও চিন্তার অনুসারী লোকদের বাস।..... এই কাদিয়ান শহরটি এখানকার অধিকাংশ এজিদী স্বভাব সম্পন্ন লোকের অধিবাসের কারণে দামেশকের সাথে সামঞ্জস্র ও সম্পর্ক রাখে।” (এযালায়ে আওহাম, ফুটনোট: ৬৩ থেকে ৭৩ পৃষ্ঠা)।
\r\n
আর একটি জটিলতা এখনো রয়ে গেছে। হাদীসের বক্তব্য অনুসারে ইবনে মরিয়ম একটি সাদা মিনারের নিকট অবতরণ করবেন। এ সমস্যার সমাধান সহজেই করে ফেলা হয়েছে অর্থাৎ মসহি সাহেব নিজেই এসে নিজের মিনারটি তৈরী করে নিয়েছেন। এখন বলুন, কে তাঁকে বুঝাতে যাবে যে, হাদীসের বর্ণনা অনুসারে দেখা যায় ইবনে মরিয়মের অবতরণের পূর্বে মিনারটি সেখানে মওজুদ থাকবে। অথচ েএখানে দেখা যাচ্ছে প্রতিশ্রুত মসীহ সাহেবের আগমনের পর মিনারটি তৈরী হচ্ছে।
\r\n
সর্বশেষ ও সবচাইতে জটিল সসনস্যাটি এখনো রয়ে গেছে। অর্থাৎ হাদীসের বর্ণনা মতে ঈসা ইবচনে মরিয়ম (আ) লিড্ডার প্রবেশ দ্বারো দাজ্জালকে হত্যা করবেন। এ সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে প্রথমে আবোল তাবোল অনেক কথাই বলা হয়েছে। কখনো স্বীকার করা হয়েছে যে, বায়তুল মুকাদ্দাসের একটি গ্রামের নাম লিড্ডা (এযালায়ে আওহাম, আঞ্জুমানে আহমদীয়া, লাহোর কর্তৃক প্রকাশিত, ক্ষুদ্রাকার, ২২০ পৃষ্ঠা)। আবার কখনো বলা হয়েছে, “লিড্ডা এমন সব লোককে হয় যারা অযথা ঝগড়া করে।... যখন দাজ্জালের অযথা ঝগড়া চরমে পৌঁছে যাবে তখন প্রতিশ্রুত মসীহের আবির্ভাব হবে এবং তার সমস্ত ঝগড়া শেষ করে দেবে” (এযালায়ে আওহাম, ৭৩০ পৃষ্ঠা)। কিন্তু এত করেও যখন সমস্যার সমাধান হলো তখন পরিষ্কার বলে দেয়া হলো যে, লিড্ডা (আরবীতে লুদ) অর্থ হচ্ছে পাঞ্জাবের লুদিয়ানা শহর। আর লুদিয়ানার প্রবেশ দ্বারে দাজ্জালকে হত্যা করার অর্থ হচ্ছে দুষ্টুদের বিরোধিতা সত্ত্বেও মীর্জা গোলাম আহমদ সাহেবের হাতে এখানেই সর্বপ্রথম বাইয়াত হয়। (আলহুদা, ৯১ পৃষ্ঠা)।
\r\n
যে কোনো সুস্থ বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি এইসব বক্তব্য বর্ণনার নিরপেক্ষ পর্যালোচনা করলে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে বাধ্য হবেন যে, এখানে প্রকাশ্য দিবালোকে মিথ্যুক ও বহুরূপীর অভিনয় করা হয়েছে।
\r\n
-:সমাপ্ত:-
সুচীপত্রঃ
বিষয়ক্রম
লেখকের কৈফিয়ত
সূচনা
প্রথম পরিচ্ছেদ
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
তৃতীয় পরিচ্ছেদ
চতুর্থ পরিচ্ছেদ
পঞ্চম পরিচ্ছেদ
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
সপ্তম পরিচ্ছেদ
অষ্টম পরিচ্ছেদ
নবম পরিচ্ছেদ
দশম পরিচ্ছেদ
ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ
লেখকের কৈফিয়ত
সূচনা
প্রথম পরিচ্ছেদ
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
তৃতীয় পরিচ্ছেদ
চতুর্থ পরিচ্ছেদ
পঞ্চম পরিচ্ছেদ
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
সপ্তম পরিচ্ছেদ
অষ্টম পরিচ্ছেদ
নবম পরিচ্ছেদ
দশম পরিচ্ছেদ
ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ
শেষ নবী
কোরআনের পূর্বাপর বিবৃতির ফায়সালা
আভিধানিক অর্থ
রাসূলুল্লাহর বাণী
সাহাবাদের ইজমা
আলেম সমাজের ইজমা
আমাদের ঈমানের সংগে খোদার কি কোনো শত্রুতা আছে?
এখন নবীর প্রয়োজনটা কেন?
নতুন নবুয়্যাত বর্তমানে মুসলমানদের জন্য রহমত নয়, লা’নতের শামিল
‘প্রতিশ্রুত মসীহ’ এর তাৎপর্য
হযরত ঈসা (আ) নুযুল সম্পর্কিত হাদীস
এই হাদীসগুলো থেকে কি প্রমাণ হয়?
শেষ নবী
কোরআনের পূর্বাপর বিবৃতির ফায়সালা
আভিধানিক অর্থ
রাসূলুল্লাহর বাণী
সাহাবাদের ইজমা
আলেম সমাজের ইজমা
আমাদের ঈমানের সংগে খোদার কি কোনো শত্রুতা আছে?
এখন নবীর প্রয়োজনটা কেন?
নতুন নবুয়্যাত বর্তমানে মুসলমানদের জন্য রহমত নয়, লা’নতের শামিল
‘প্রতিশ্রুত মসীহ’ এর তাৎপর্য
হযরত ঈসা (আ) নুযুল সম্পর্কিত হাদীস
এই হাদীসগুলো থেকে কি প্রমাণ হয়?

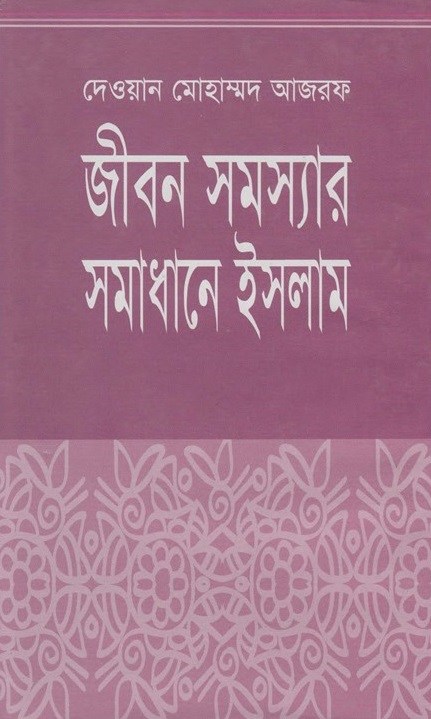 স্ক্যান কপি ডাউনলোড
স্ক্যান কপি ডাউনলোড